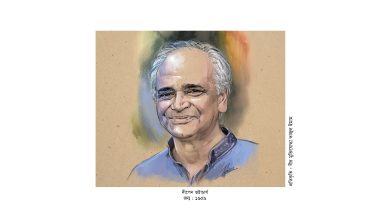‘মারে জাগাইলা ক্যান ? বাড়ি কই, কি-বা পরিচয় তোমার ?’ শত বছরের গভীর নিদ্রার অতল থেকে উঠে জবজবে গলায় জিজ্ঞেস করে আয়শা।
জলে ডোবা ফ্যাকাশে মুখ। ভেজা চুল, ভেজা বসন। সেই কবে, কোন কালে রাতের আঁধারে জদ্দন বাঈয়ের ভাড়া করা নাও মালার থেকে কুলকিনারহীন উত্তাল পদ্মাবতীর ঘোলা জলে ঝাপ দিয়েছিল সে। ঝাঁপ দিয়েছিল নির্দয় আরাকানি মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের কব্জা থেকে বাঁচার জন্য নয়, ঝাঁপ দিয়েছিল দেশীয় ডাকুদের থাবায় পড়ে কোনও কিছু না ভেবে নাওয়ের আর কারও দিকে তাকাবার একদণ্ড ফুরসত না নিয়েই।
মোগল সেনারা ধেয়ে আসছে শুনে টঙ্কাকড়ি, সোনাদানা যা কিছু জমিয়েছিলেন সব নিয়েই সুবর্ণনগর থেকে পরিবারের লোকজনসহ মায়ের বাড়ি লখনৌয়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন জদ্দন বাঈ। নাওখানাও ছিল শক্তপোক্ত আর প্রশস্ত―দূরপাল্লার জন্য খুবই উপযোগী নাও এই মালার। মালারের মাঝি-মাল্লারাও একেকজন কেউ কারও চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। তারা সঙ্গে নিয়েছিল ঢাল, সড়কি, ভাল্লা, ট্যাঁটা। এ ছাড়া রক্ষী ছিল দুজন, নিপুণ লক্ষ্যভেদী ধনুর্ধরও ছিল। দূরযাত্রায় এরকম আয়োজন ছাড়া উপায়ই-বা কী! বঙ্গালের নৌপথে ওত পেতে থাকে দস্যুর দল। তারা গায়ে কালী মেখে কালীর মন্দিরে পূজা দিয়ে এসে নামে গাঙে। শিকার পেলে কাটারি, কিরিচ, রামদা, সড়কি, ভাল্লা নিয়ে কোষায় করে রে রে রে হুংকারে জলের ওপর দৈত্যের মতো তেড়ে আসে, যেন সাক্ষাৎ যম। আর যেভাবে শাঁই শাঁই সড়কি ছোড়ে, রামদা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোপায়, কে পারে সেই ঘাই ঠেকাতে ? সর্বস্ব হারিয়ে ওই যমের হাতে বেঘোরে প্রাণ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।
প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি দিনের পথ। মাঝিরা সূর্য ওঠার আগেই বদর বদর বলে দাঁড় টেনে লাক্ষ্যা দিয়ে বের হয়ে সারাদিন ব্রহ্মপুত্র বেয়ে রাতের আঁধারে গিয়ে পড়েছিল পদ্মাবতীতে। দাঁড়ে, পালে পদ্মাবতী বেয়ে গৌড় হয়ে গিয়ে উঠবে গঙ্গায়। তারপর গঙ্গা বেয়ে পাটনা পর্যন্ত পৌঁছাবে তারা। সেখান থেকে অন্য ব্যবস্থায় যাবে লখনৌ। সেই যাওয়া আর হয়নি তাদের।
কোনও উত্তর না করে আয়শার জলধোয়া বিবর্ণ চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে ইউসুফ―তার সহোদর, তার আত্মার অংশ রুস্তমের স্বপ্নের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, রুস্তমের হৃদয় এই নারীতেই তো সমর্পিত হয়েছিল―মোগলদের কামানের গোলায় শতচ্ছিন্ন হওয়ার আগেও হয়তো এই মুখ তার অন্তরের আয়নায় ভেসে উঠেছিল।
মসনদ-ই-আলা মুসা খাঁর প্রধানমন্ত্রী হাজি শামসুদ্দিন বাগদাদির একমাত্র পুত্র আলাউদ্দিন বাগদাদির বহরে সুবর্ণনগরের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ছিল তারা দুই ভাই। বহর প্রধানের নির্দেশে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তারা। মোগল বাহিনীর উপর গোপন আক্রমণ চালাতে তার দল নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে সরে গিয়েছিল রুস্তম। আর লাক্ষ্যার মোহনায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ইউসুফ। জালিয়া নাও থেকে নেমে কোষায় চড়তে চড়তে রুস্তম বলেছিল, ‘আর যদি ফেরা না অয় ভাই, আয়শার খোঁজখান কিন্তু নিস’।
এই আয়শার ব্যাপারে তেমন কিছুই জানত না ইউসুফ। শুধু জানত তার সহোদরের আত্মা ভুলুয়ার ধর্মপাশা গাঁওয়ের এক নারীর কাছে সমর্পিত। জদ্দন বাঈয়ের আশ্রিতা সেই নারী।
মোগলরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। দীর্ঘ দিনের সেই যুদ্ধ তো আর শেষ হয় না। মসনদ-ই-আলার সৈন্যরা খালে-বিলে ঢুকে অনবরত গুপ্ত হামলা চালিয়ে তখনও বেদিশা করে রেখেছে মোগল বাহিনীকে। এরই মধ্যে একদিন কামানের গোলায় ভাই হারানোর খবর পায় ইউসুফ। যুদ্ধ চলাকালেই জনশূন্য বিধ্বস্ত সুবর্ণনগরে জদ্দন বাঈয়ের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল সে। নির্জন বাড়ির পাহারায় ছিল এক বৃদ্ধা রাঁধুনি, সে-ই দিয়েছিল জদ্দন বাঈয়ের সঙ্গে আয়শার লখনউ চলে যাওয়ার খবর। সেদিন কত কেচ্ছাই না শুনিয়েছিল সেই বুড়ি!
তখন থেকেই তো আয়শাকে খুঁজে ফিরছে ইউসুফ। সারা বাঙ্গালার জলে-স্থলে-কাব্যে-গীতে তন্ন তন্ন করে কতই না খুঁজেছে।
ভুলুয়ার, বাকলার মানুষ হাজার বছর ধরে জল-হাওয়া-ঘূর্ণির সঙ্গে লড়তে শিখে বড় হয়―মেয়ে, মা, মায়ের মা, তার মা-ও যা শেখে। শিখতে গিয়ে মরতে শেখে। মরতে মরতে সব হারিয়ে বাঁচতেও শেখে তারা। সেই শিখন হচ্ছে উপকূলের পরম্পরা। কিন্তু সেকালের মগ-হার্মাদ ঘূর্ণিতে কোনও শিখন ছিল না। কোনও লড়াই ছিল না। যা ছিল তা কেবলই মরণ।
কবেকার বাঙ্গালার হেমন্তের এক বিকেল। ভুলুয়ার ধর্মপাশা গাঁওয়ে আয়শাদের উঠানে শুকাতে দেওয়া ধানের ওপর থেকে রোদ তখনও সরেনি। পুকুর থেকে গোছল সেরে এসে সবে আহার শেষ হয়েছে তাদের। মেয়েদের ভেজা চুল তখনও গা-মোছায় পেঁচানো। এঁটো থালাবাসন গোটানো হয়নি। জোয়ারে টইটম্বুর খালের ঝোপঝাড়ের আড়ালে হঠাৎ নজরে পড়ে বড় বড় নাওয়ের গোটা কয়েক খাড়া খাড়া আগা-গলুই। সেই গলুইগুলোর প্রত্যেকটার মাথায় বাঁধা রক্তমাখা মোষের মস্ত শিং। নিমেষে বাক্যহারা হয়ে পড়ে সবাই। বুকের রক্ত হিম হওয়ার আগে দৌড়াতেও বুঝি ভুলে যায়।
নাও থেকে লাফিয়ে নামা শিকারি জন্তুগুলোর মজবুত শরীর, ক্ষিপ্র তাদের গতি। তাদের গলায় ছোট ছোট হাড়ের কয়েক প্যাঁচের মালা। থ্যাবড়া মুখের ওপর কুতকুতে নির্দয় হিংস্র চোখ। ঘোঁত ঘোঁত করা ছাড়া কণ্ঠে আর কোনও শব্দ নেই। হাতে চকচকে কিরিচ, ভল্ল, কাটারি আর দড়ি। যেখানে যাকে ধরছে নিঃশব্দে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলছে।
কোনও প্রয়োজন ছিল না। হয়তো ত্রাস সৃষ্টির জন্যই, খালি হাতে বাধা দিতে আসা আয়শার বুড়া দাদুর মাথাটা কিরিচের এক কোপে গাছ থেকে ঝুনা নারকেল ফেলার মতোই উঠানে মেলে দেওয়া ধানের মধ্যে ফেলল। মুণ্ডুহীন শরীরটা ধপাস করে পড়ে যেতেই হাত-পা আছড়াতে থাকে তাঁর। উঠান ভিজিয়ে গলগলিয়ে বয়ে চলে রক্তের ধারা। সে এক দুর্বিনীত অচিন ঘূর্ণি! এক অকহতব্য জলোচ্ছ্বাস! মুহূর্তে ধর্মপাশা গাঁওয়ের কয়েকটা বাড়ি আউলা করে, উজাড় করে, ধুয়েমুছে নাওয়ে ভরে খাল বেয়ে তরতরিয়ে গাঙে গিয়ে নামে ডাকুদের দল।
গাঙে তীব্র স্রোত, সেই স্রোতের মধ্যে টুপ করে ডুবে গেছে সূর্যটা। দূরের চরে ঘনিয়ে নামছে সন্ধ্যা। বেঁধেছেঁদে আনা গাঁয়ের নিরীহ প্রাণিগুলোকে নাও থেকে নামিয়ে তোলা হয়েছে পর্তুগিজদের মাস্তুলওয়ালা বিরাট একেকটা জাহাজের পাটাতনে। বেছে বেছে মাদিগুলোর কয়েকটাকে রেখে বাকিদের পোরা হয়েছে খোলে। আরও অনেকের সঙ্গে কোথায় যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মা, চাচি, ফুপু আর ছোট চাচাকে, কোন নাও থেকে নামিয়ে কোন জাহাজে―আয়শা তার কোনও হদিস পেল না।
সারা রাত জাহাজভরা সাদা সাদা মানুষের হল্লা, বেশুমার মদ্যপান, পোড়া গোস্তের ঘ্রাণ, মাতাল উল্লাস, খিস্তি-খেউড় আর টানাহেঁচড়া। হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে একসময় পুরো উলঙ্গ করে ফেলা হলো আয়শাকে। মানুষগুলোর আধোয়া গায়ে পাঠার বদগন্ধ, মুখে বিষ্ঠার বদবু। দুরন্ত শাবলের একেকটা তীব্র ঘাই―কুমারি ছোট্ট শরীর বেহুঁশ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওমা, ওমা বলে তড়পায়, গোঙায় আর যোনিছেঁড়া খুনে ভাসে।
দিন যায়, নোনাজলের পথ তো আর ফুরায় না। দিনের বেলায় জাহাজের খোলের আঁধারে ফাঁক গলে আলো উঁকি দেয়। সেই আলোতে এক ঘড়া জল যদি দেওয়া হয় তাই নিয়ে কত কাড়াকাড়ি। কখনও কিছু ভাত, কখনওবা কিছু চাল ছিটিয়ে দেয় মগেরা। এখানে যারা বন্দি তারা সেসব খুঁটে খুঁটে খায় আর আপন মনে বিলাপ করে। এ ওকে জিজ্ঞেস করে, তাদের নিয়ে কী করা হবে ?
মগরা বন্দিদের নিয়ে কী করে সেসব নিয়ে কত রকমের গল্প যে তারা শুনেছে তবু জিজ্ঞেস করে। কেউ বলে, দাস বানিয়ে দূরের বন্দরে বেচে দেয়। কেউ বলে, জানিসনে, মগেরা মানুষখেকো। একবার যারা মগের হাতে পড়ে আর ফেরে নাকো।
সাগর পাড়ি দিয়ে কয়েক দিন পর পাল্লা তুলে জাহাজের খোল থেকে নামানো হলে বাইরের দুনিয়ার আলো বন্দিদের চোখে সয় না। কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে দেখে, যেখানটায় তাদের নামানো হয়েছে, উথালপাথাল হাওয়ার মাঝে চারদিকের অথৈ নোনাজলের ওপর ভেসে থাকা একটা দ্বীপ―দুই-চারটা বৃক্ষের নিচে সারি সারি বাঁশের খুঁটি পোঁতা একটা মনুষ্য বিকিকিনির হট্ট। আগাগলুইয়ের মাথায় রক্তমাখা মোষের শিংবাঁধা নাওয়ে তোলার পর থেকেই তো নিজেদের আর মানুষ বলে ভাবার কোনও কারণ ছিল না আয়শাদের। এবার হট্টে ওঠার পর নিশ্চিতই জন্তুতে পরিণত হলো গাঁয়ের সরল সাধারণ নিরীহ মনুষ্যগুলো।
সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আয়শা। তলপেটের নিচে ক্ষণে ক্ষণে চিলিক দিয়ে উঠছে অকথ্য যন্ত্রণা। উপর্যুপরি কোপ খাওয়া কোমল কচি যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের পর ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, ভীষণ ভার হয়ে আছে ব্যথায়। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের গন্ধ নোনা হাওয়ায় নাকে এসে আটকাচ্ছে।
চারপাশের খুঁটিগুলোতে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে তার মতো নানা বয়সের মাদি ও মর্দা। ওদের মাঝ দিয়ে একটু দূরে ফুপুকে একঝলক মাত্র দেখতে পায় সে―এক দড়িতে গিঁট খাওয়া কয়েকজনার সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলোমেলো পায়ে এগোচ্ছে। দড়ির আগা ধরে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে গাঁট্টাগোট্টা বেঁটেমতো একটা লোক। হাঁটতে হাঁটতেই কাতর চোখের বিমর্ষ উদাস চাহনি নিয়ে বারবার পেছন ফিরছে ফুপু। তার চাহনির সেই ভাষা কিছুতেই পড়ে উঠতে পারছে না আয়শা। এই জীবনে নিজের বলে কাউকে সে-ই শেষ দেখন ছিল তার।
এত কিছুর পরও বলতে হবে ভাগ্য ভালোই আয়শার। নাকি সুরত ভালো! নাকি গতর ভালো! নাকি কচি সে! দেখে-শুনে, হাতিয়ে-গুঁতিয়ে যাচাই করতে করতে এক ক্রেতা আপনমনেই বলে, ‘হায় ভগবান, শুয়ারগুলায় দেহি এর কিচ্ছু থোয় নাই। অ্যাক্কারে ছোবড়া বানাইয়া আনছে!’
বোঝা গেল ছোবড়া হলেও বেশ পছন্দ হয়েছে লোকটার। তারপর শুরু হয় মুলামুলি। দুই পক্ষের সেই মুলামুলির অচিন ভাষা আজব হলেও অনুমান করতে পারে আয়শা। এক পর্যায়ে দামে বনলে পরে এদেশীয় বণিক ক্রেতাটি তার মখমলের খুতি থেকে বার করা তিনটি স্বর্ণমুদ্রায় কিনে নেয় তাকে। দড়ি খুলে নিয়েই গালে ঠোনা মারে বণিক। ফকফকা দাঁত বের করা হাসি হেসে মধুমাখা স্বরে বলে, ‘এবার চল মাগি, মোর বজরায় রানি হৈয়া থাকবি।’
সত্যি, এমন ঘটনা না ঘটলে পুনরায় এই বাঙ্গালার জল-হাওয়া-মাটি ফের তার বরাতে জুটত কিনা কে জানে! মগ-ফিরিঙ্গির হাতে পড়া কারই-বা কবে জুটেছে! জাহাজ ভরে মোটা দরে সব চালান হয়ে গেছে। হোক না মোছলমান ঘরের মেয়ে―এক হিন্দু বণিকের বজরায় হলেও ঠাঁই তো হয়েছে! কয়েক দিন আগের জীবনের চেয়ে কিংবা চালান হওয়ার থেকে হাজার গুণে ভালোই তো হয়েছে। বজরায় তো সে রানি হয়েই আছে!
কিন্তু যেমনই থাকুক গাঁয়ের জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এই বালিকার জীবন কিছুদিনের মধ্যে নাওয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরে ছটফট করতে শুরু করে। এছাড়া বণিক পুরুষটির ক্ষুধা অনন্ত। তার মতো ছোট্ট একটি মেয়ের পক্ষে সামাল দেওয়াও কঠিন। বাইরে প্রকাশ না করলেও তিনটি স্বর্ণমুদ্রায় কেনা দাসীটি নিয়ে ভেতরে ভেতরে সে বোধহয় হতাশ হয়ে পড়ছিল―মাগির চলনে ঠমক নেই, কামে উত্তেজনা নেই, একার পরিশ্রমে আর কতক্ষণ ? এরই মধ্যে আবার গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে খেয়ালও তো রাখতে হয় তাকে। একদিন একটা শিশি ধরিয়ে দিয়ে বলে, ‘এক দাগ করে খাবি রোজ।’
বজরায় ওঠার দুদিন পর একটা বাজারের ঘাটে ভিড়লে এক কবিরাজ এসে কয়েক দিন আয়শার চিকিৎসা করেছিল। তখন তাকে সেবন করতে হয়েছিল কত রকম দাওয়াই। এখন এর কী প্রয়োজন! আয়শা অবাক হয়ে বলে, ‘ক্যান ? মোর তো আর ব্যাদনা-ট্যাদনা নাই।’
হতভম্ব হয়ে যায় বণিক। রেগে গিয়ে গজরে ওঠে সে, ‘মাগি কয় কী! প্যাট বাজাবি তয় ? প্যাট বাজলে কৈলাম লাত্থি দিয়া ফেলামু গাঙ্গোৎ।’
মারতে উদ্যত হয়নি তবু সেদিন মার খাওয়ার ভয়ে শিউরে উঠেছিল সে। দাওয়াই খেতে বলার কারণটা বুঝতে বাকি ছিল না তার।
কিছু দিনের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আর একটি দাসীর আগমন ঘটে তাদের বজরায়। যেমন তার রূপ তেমনি রকম-সকম। তাম্বূলের রঙে রঞ্জিত ঠোঁট, সুডৌল স্তন, কালো ভোমরার মতো চোখ দুটো তার কেবলই অস্থির―খলখলানো হাসি একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। কামরূপ থেকে রপ্ত করেছে কামকলা―বিপরীত লিঙ্গ আর কুক্কুরী সঙ্গমে তার জুড়ি নেই। দেখতে দেখতেই সেই নারীর ঠাট আর ঠমকের কাছে কাবু হয়ে পড়ে আয়শা―হাসির ধরন-ধারণ নিয়ে গড়িয়ে পড়া যে তার আসে না। ঢং করতে পারে না সে। চলাফেরার মধ্যেও তেমন ছিরিছাঁদ নেই। স্তনযুগলও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বজরার এই পরিসরে এমনিতেই তো ল্যাপ্টালেপ্টি জীবন―এবার তা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল।
নতুন দাসীটি একদিন বলে, ‘ওই ছেমরি, মোরে কত দিয়া কিনছে হুনবি ?’ বুড়ো দুটি আঙুল দুই হাতের তালুতে চেপে ধরে বাকি আটটি উঁচিয়ে দেখায়, ‘গুইনা গুইনা অষ্ট স্বর্ণমুদ্রায়! নে, এবার পা টেপ।’
সেই থেকে শুরু হয় দাসী হয়ে নতুন দাসীর পা টেপা, গা টেপা, চুলে তেল ঘষা, কাপড় ধুয়ে দেওয়া, পান সাজিয়ে দেওয়া। বজরার মাঝি মাল্লাদের কাছে এটা কোনও অপরিচিত দৃশ্য নয়, তবু তারা মুখ টিপে হাসে। কানে কানে নানা কথা কয়।
এর কিছু দিন পর এক সুবেহসাদিকে আয়শা দেখে সারারাত বেশুমার মর্দামির পর বেঘোরে ঘুমোচ্ছে সব মাতাল হয়ে। সবাই ঘুমিয়ে গেলেও যে দু’একজন পাহারায় জেগে থাকে, ধেনোর নেশায় তারাও কাত হয়ে ঝিমোচ্ছে। কেবল ঘুম নেই তার দু চোখে।
এত দিনে আয়শার উপলব্ধি হয়েছে বণিক মনিবটি যত মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলুক তাকে আবার হট্টে তোলার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বজরার এই জীবনে এটাই নিয়ম, নিষ্ঠুর হলেও এটাই চরম সত্য। তেমন সত্যের চেয়ে যে মৃত্যুই উত্তম এটুকু বোঝার বয়স তার হয়েছে। এ কয়টি দিনেই জীবনের প্রতি সকল মায়া ম্লান হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে বণিকের বজরা থেকে লাক্ষ্যায় ঝাঁপ দেয় সে।
গাঙের জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনটি স্বর্ণমুদ্রায় কেনা দাসীর জীবন আয়শা নিজেই ঘোচাতে চেয়েছিল। মরতেই তো দিয়েছিল ঝাঁপ কিন্তু খোদার ইশারা প্রাণের পক্ষে গেলে কারই-বা কী করার থাকে!
সুবর্ণনগরের ডাকসাইটে নর্তকী লখনৌ সুন্দরী জদ্দন বাঈ ঈশা খাঁর দরবারে নাচতেন। ঈশার ছেলে মুসা খাঁর শাসনামলে নাচেন জদ্দনের কন্যা রওশন। সেদিন জদ্দন বাঈ সূর্য ওঠার আগে সুবেহ সাদিকে একখানা গয়না নাওয়ে আকালিয়া খাল দিয়ে বের হয়ে লাক্ষ্যার পূর্ব তীরে নবীগঞ্জের কদমরসুলে গিয়েছিলেন মোহাম্মদের পদচিহ্ন চুম্বন করতে। বহুকাল আগে হাজি বাবা সালিহ নামের এক সাধু মোহাম্মদের পায়ের ছাপওয়ালা একখণ্ড প্রস্তর মক্কা থেকে এনে ওখানে স্থাপন করেছিলেন। ওই পাথর চুম্বনে বিশ্বাসীর অন্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।
ফেরার পথে মাঝিরা দেখতে পায় ভাটার টানে পানি নেমে যাওয়া লাক্ষ্যার নির্জন চরে একটি মেয়ের দেহ পড়ে আছে, যার অর্ধেক রয়েছে কাদায় আর বাকি অর্ধেক জলে। শাড়ির আঁচল স্রোতের টানে ভাসছে। সবাই ভাবল মৃতদেহ।
মাঝিদের সর্দার বলে, ‘কোনও মউগ্যার ছোঁয়া হৈব, আম্মা। সমাজে জায়গা নাই তো কী করব! ঝাঁপ দিছে গাঙোৎ।’
মগ-ফিরিঙ্গির ছোঁয়া যে সমাজ নেয় না তা ভালো করেই জানেন জদ্দন বাঈ। তবু গয়না কূলে ভেড়াতে বললেন। কাদা ধুইয়ে চর থেকে তুলে আনার পর দেখা গেল দেহে তখনও প্রাণ আছে। শুশ্রƒষায় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পায় মেয়েটি।
মাত্র তো মোহাম্মদের পদচুম্বন করে কদমরসুল থেকে নাও ছেড়ে এলেন। মেয়েটিকে নিয়ে জদ্দন বাঈয়ের অন্তরে খটকা লাগে―নিশ্চয়ই খোদার দিক থেকে এটা কোনও ইঙ্গিত। মনের মধ্যে এমন ভাবের উদয় হতেই বললেন, ‘আজ থেকে এ আমার মেয়ে, একে ঘরে নিয়ে চলো।’
তখন থেকে নিজের মেয়ে রওশনের সঙ্গে কুড়িয়ে আনা আয়শাকে কখনও তফাত করে দেখেননি জদ্দন বাঈ।
ইউসুফকে নির্বাক দেখে আবারও জিজ্ঞেস করে আয়শা ‘কেন জাগাইলা মোরে, কি-বা জানোনের আছে, কও ?’
‘আমার ভাই রুস্তম কইছিল সে যদি আর না ফেরে যেন তোমার তালাশ লই।’ আবেগে ধরে আসা কণ্ঠে বলে ইউসুফ।
হতবাক হয়ে আয়শা দেখে আর ভাবে, সত্যিই তো এই মুখে সেই ছায়া, তেমনই গমগমা গলার স্বর, তেমনই গড়ন, আচরণ। সে বলে, ‘কী অইছিল মোর রুস্তমের ? মোতালেব তরফদারের লগে হেই যে যুদ্ধে গেছিল আর কি ফেরে নাই ? তার খবরখান আগে দেও ভাই। পরানডা জুড়াই।’
‘না ফেরে নাই। জীবনে-মরণে, কাব্যে, গীতে তাই তো তোমার সন্ধান করি। আমার ভাইয়ের পরান হইছিলা তুমি। তোমার তালাশে ভাই হারানোর ব্যাদনা ভুলতে চাই। তোমারে জানতে চাই।’
জদ্দন বাইয়ের বাড়িতে ঢোকার পর জীবনের নতুন প্রবাহে পড়ে লখনৌয়ের ওস্তাদজির কাছে কাব্যকলার সঙ্গে সুর-ছন্দ-তাল-লয়ের তালিম নিতে নিতে কিশোরবেলা পার হয়ে যৌবন শুরুর প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া সবকিছু ভুলে ছিল আয়শা।
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র আলাউদ্দিন বাগদাদির একান্ত আস্থাভাজন কর্মচারী মোতালেব তরফদারের অধীনের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল রুস্তম। সেই সূত্রে নানা প্রয়োজনে নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে জদ্দন বাঈয়ের বাড়িতে যাতায়াত ছিল ছেলেটার। আসা-যাওয়ার মাঝে আয়শা আর রুস্তমের মধ্যে কখনও কখনও একটু-আধটু কথাবার্তার সুযোগ ঘটত। কোন ফাঁকে যে দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে পরস্পরের মনের ভাষা পড়ে নিয়েছিল টেরই পায়নি তারা।
ওই বয়সে ওটাই তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আয়শা তার সমাজটাকে চিনত, নিজের সম্পর্কেও ভালো করেই জানত। আর জানত বলেই তার বিচারবোধে উদয় হয়েছিল, এই আবেগ তার চিত্তের অলিন্দে চকিতে ধরা পড়া একটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। তাই এই ভ্রান্তিকে বারবার কতভাবেই না প্রবোধ দিতে চেয়েছিল সে কিন্তু কোনও কূলকিনারা করতে পারেনি। এমনকি একদিন রুস্তমকে বলেও ছিল, ‘মুই মগ-ফিরিঙ্গির ছোঁয়া একটা মাইয়া। মোরে ভোলেন। এই মাইয়ার হপন দেহাও পাপ। সোমাজ না নেবে মোরে, না মানবে আপনেরে। অভিশপ্তরে ভোলেন রুস্তম ভাই।’
কিন্তু এমন কথায় দমবার পাত্র ছিল না রুস্তম। সে ব্যাকুল কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, ‘মুই সোমাজের কানুন মানি না। কে কিসের ছোঁয়া বুঝি না। মুই বুঝি তোমারে।’
ছলছল চোখে দু হাত জোর করে অনুনয় করেছিল আয়শা, ‘মোর কথা ছাড়েন। এই পথে আর না হাঁইটেন আপনে। খোদার কসম, নিজের সব্বোনাশ না কইরেন।’
কিন্তু কে শোনে কার কথা। রুস্তম তার কোমরে গুঁজে রাখা হাতির দাঁতের কারুকাজ খচিত একটা চুলের কাঁটা কুর্তার নিচ থেকে বার করে হাতে দিয়েছিল আয়শার, ‘এই নেও, মোরে বাইন্ধ্যো সই তোমার খোঁপার লগে।’
এর পর থেকে নানা ছলছুতায় রুস্তম যেদিনই এই দিকে আসত, যদি দেখা পাওয়ার সুযোগ পেত আয়শার হাত নিজের মুঠোয় রেখে বলত, ‘মোরে ভুইল্লো না কইলাম, কৈন্যা।’
সব বুঝেও শর্তহীন যে হৃদয় আর এক হৃদয়ের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল এখন কোন বিবেচনাবোধ দিয়ে তাকে আগলাবে ? নাকি সে-ও অবচেতনে কামনা করছিল পুরুষ ? তাছাড়া রুস্তমও তো শিশুর মতো অবুঝ, গোঁয়ারের মতো নাছোড়। মুঠোয় রাখা হাত একদিন নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলেছিল, ‘মোর পরান হইলা তুমি। তুমি নাই তো রুস্তমের এই পরানও নাই।’
অনুরাগে আহত আয়শা চোখের জল ছেড়ে দিয়ে মেহেদিরাঙা হাতে রুস্তমের মুখ চেপে ধরে বলেছিল, ‘এই কথা মুখে আনাও যে পাপ!’
মুখ থেকে আলগোছে ওর হাত সরিয়ে নিয়ে আবার মুঠোয় রেখে রুস্তম হাসতে হাসতে বলেছিল, ‘তরফদাররে কৈছি, হুজুর, যদি অনুমতি দেন তো জঙ্গ থেইকা ফিরা এইবার শাদি করতে চাই। তিনি গম্ভীর হইয়া কৈলেন―কৈন্যারে তো চিনি। শুইন্যা মুই তো ডরাইয়া মরি!’
এই কথা শুনে পরান ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল আয়শারও। ঘোর অমানিশার অন্ধকারে নিজেকে হাতড়ে কী উত্তর দেবে ভেবে দিশা পায়নি সে। রুস্তম আবার বলেছিল, ‘মোদের ছেলে হৈলে কি নাম রাখমু জানো ? নাম রাখমু সো-হ-রা-ব। সোহরাব-রুস্তমের কাহিনি তুমি হুনছ কহনও ? আইজ থাউক, আর একদিন হুনামু।’
এমন উন্মাদকে ছেড়ে জদ্দন বাঈয়ের সঙ্গে কিছুতেই যেতে চায়নি আয়শা! নিরুপায় হয়ে লখনৌয়ের উদ্দেশে মালারে উঠতে হয়েছিল তাকে। সে জানত একটিবারের জন্যও দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আর নাই। কারণ আলাউদ্দিন বাগদাদির বহরের কোষায় চড়ে মোতালেব তরফদারের হুকুমে রুস্তম তখন হয় লাক্ষ্যায়, না হয় মেঘনাদে, না হয় ব্রহ্মপুত্রে, না হয় কোনও খালে-বিলে বাঙ্গালার অতন্দ্র প্রহরী।
লখনৌ গেলে আর কোনও দিনও কি ফেরা হবে এই জল-হাওয়ায় ? দেখা কি হবে আর কোনও দিন ? ভাবতে না পেরে নিভৃতে, নীরবে যেমন কেঁদেছিল তেমনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে উথলে ওঠা হিক্কা আর থামাতে না পেরে চোখের পানি, নাকের শিকনি-সমেত ভোঁতা ভোঁতা স্বরে, ভেঙে ভেঙে রুস্তমের পাগলামির কথা বলেছিল সে সহোদরার মতো জদ্দনের মেয়ে রওশনের কাছে। এক অভাগীর কথা বলে চলেছিল সে। কারুকাজ খচিত হাতির দাঁতের চুলের কাঁটার কথা বলে চলেছিল। এক দিগ-দিশাহীনের পথ খোঁজার কথা বলে চলেছিল।
জদ্দন বাঈয়ের সঙ্গে তখন তো তার চার বছর। এই চার বছরে কত কিছুই তো বলেছিল। কী-ইবা আর বাকি ছিল বলার ? তবু বাপ-মা-মামা-চাচা-খালা-ফুপু কার না কথা বলে চলেছিল সে! বলতে বলতে ফোঁপানির সঙ্গে সব কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছিল তার―গাঁওয়ের সেই বাড়ি, ধান শুকাতে দেওয়া সেই উঠান, এক কোপে ছিটকে পড়া দাদার মুণ্ডু, শান্ত পুকুর, নিরিবিলি খাল পাড়, দুপুর ডিঙানো ঘুঘু ডাকা নিস্তব্ধ বাগান আর মুহূর্তে তছনছ হওয়া ওইটুকু একটা জীবন খুঁড়ে যেন অনন্ত এক জীবনের কথা বলে চলেছিল আয়শা।
সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ