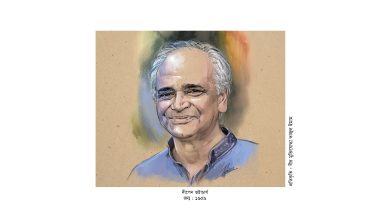প্রান্তের ডায়েরি, তারিখবিহীন
অথচ রজনীগন্ধা নয়, আমি পেয়েছিলাম দোলনচাঁপার ঘ্রাণ। মৃদু, কিন্তু খুবই স্পষ্ট। মায়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে মোবাইল ফোনটা হাতে করে নিথর হয়ে বসে আমি ডুবে যাচ্ছিলাম সেই দোলনচাঁপার ঘ্রাণের ভেতর।
কোথাও শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছিল। দোলনচাঁপার ঘ্রাণ কখন যেন হঠাৎ নাই হয়ে গেল! শরীরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠল আর ঠাস করে মনে হলো, অভিমান নাকি জিঘাংসা দেখিয়ে গেলেন মা! তাঁর তো আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবার কথা। তাছাড়া ইচ্ছাশক্তিও তো বেশ ভালোই ছিল তাঁর। কিন্তু তর সইল না, আর মাত্র মাসতিনেক বেঁচে থাকার ইচ্ছা হলো না তাঁর। সারা জীবন ধরে যত দুর্ব্যবহার করেছি, দুর্ব্যবহার করতে করতে তার মনে যত ক্রোধ জমিয়েছি, ঝোপ বুঝে আজ তার সবটুকুই ঝেড়ে রেখে গেলেন তিনি!
অবশ্য সন্তান হলে যা হয় আর কি―মনে হয়, এটা কোনও দুর্ব্যবহার হলো ? তাও মায়ের সঙ্গে ? ভুল হয়েছে বোঝার পরও এরকমই মনে হয় মানুষের। মনে হয়, মায়ের সঙ্গে এ আর এমন কী খারাপ ব্যবহার! তা ছাড়া এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই, কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই তাঁকে কেন যেন ভীষণরকম অবোধ মনে হতো। অবোধ, তবে কেমন যেন ইচ্ছাকৃত, কেমন যেন নিষ্ঠায় ভরা অবোধ। আর তাতে আমি এত অধৈর্য ও এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠতাম যে আমার কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত আসলে বেশ খারাপ ব্যবহারই হয়ে উঠত। না, বেশ খারাপ বলছি কেন! খুব খারাপই হতো। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই খারাপ ব্যবহার করতে করতে আমি টের পেতাম, মায়ের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করছি। কিন্তু কী এক ভয়ংকর একমুখো অধিকারবোধ থেকে জেগে ওঠা ক্রোধে নিজেকে বোধহয় সামলে রাখতে পারতাম না। তাই বুঝবার পরেও দুর্ব্যবহার করতেই থাকতাম। ওই সময় মাকে দেখতাম চুপচাপ নিজের কাজ করতে। যেন বধির তিনি, এই পৃথিবী তাঁকে কোনও কিছু শুনবার অধিকার দেয় নাই। প্রচণ্ড জিঘাংসা নিয়ে আমি তার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর আমার রাগ ঝাড়তেই থাকতাম। কিন্তু কেমন যেন প্রশান্ত দুই চোখ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের কাজকর্ম করে চলতেন। তাঁর সেই চোখজোড়ায় না থাকত কোনও ক্রোধ, না থাকত কোনও ঘৃণা, না থাকত কোনও বেদনা কিংবা করুণা। রাগ, ঘেন্না, করুণা একটা কিছু তো করবেন তিনি আমাকে, তা না করুন অন্তত ডুব দেবেন তো আত্মগত বেদনার জগতে। কিন্তু না, তিনি তাঁর কোনওটাই করতেন না। তাতে আমার রাগ আরও বেড়ে যেত। বয়স যখন তাঁর আরও একটু বেড়ে গেল, তখন তিনি রান্নাবান্না করতে না পারলেও রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে থাকতেন। প্রাচীন বাংলার এক অপরিবর্তনীয় সেই রান্নাঘরের সামনে এসে তিনি যেন বিশেষত আমাকেই ইন্দিরা ঠাকুরের কথা মনে করিয়ে দেবেন বলে ওইভাবে বসে থাকতেন। তাতে কখনও আমি রক্তহীন হয়ে পড়তাম। কখনও অব্যাখ্যাত এক ক্রোধে ধকধক করতাম। বয়স যখন তাঁর আরও বাড়ল, রান্নাঘর পর্যন্ত যাওয়া কষ্টকর হয়ে গেল, আবার ভাইদের মধ্যে বাড়িঘর ভাগাভাগিও হয়ে গেল, তখন তিনি বসে থাকতে শুরু করলেন তার নিজের জন্যে বরাদ্দ দেওয়া ঘরটার বারান্দাতে। এইভাবে কত যে অক্ষমতা জমতে শুরু করল আমার মায়ের! কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু তাঁর ওই চোখ দুটোর হেরফের হলো না। মনের কথা কইতে তো মানুষের চোখই নাকি অক্ষর হয়ে ওঠে; বিদ্বৎজন তো সেরকমই বলেন, কিন্তু অক্ষরজ্ঞানহীন আমি আর তার পাঠ নিতে পারলাম না।
দিন ঘনিয়ে আসছিল, অন্ধকার নামছিল আকাশজুড়ে, মা ক্রমেই পরিণত হচ্ছিলেন চলাফেরায় অক্ষম এক মানুষে। কিন্তু পৃথিবীর আলো-গান কি আর কখনও থামে ? ভুবনজুড়ে ফাঁদ পাতা রয়েছে আলো-গানের, হাসি-গানের। সময় নেই, অসময় নেই মাকে ঘিরে বসতাম আমরা সব ভাইবোন। আত্মীয়স্বজন। অবশ্য এসবই ঘটত ছুটির সময়ে, বিশেষত ঈদগুলোর সময়ে। অন্য সময়ে, অনুমান করি, মা তাঁর ঘরে বসবাস করতেন দুঃসাহসী এক টিকটিকির মতো। কেউ নাই, বাড়িজুড়ে কেউ নাই, ঘরজুড়ে কেউ নাই। আমাদের সব ভাইবোনই মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, যে কোনও সময় চলে যাবেন তিনি। সেরকমই একদিন, কী যে হলো, কেমন নিষ্প্রাণ এক সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি তার বিছানার উল্টা দিকের খাটে বসে আমি বললাম, ‘মা, মানুষের কার জীবনে কখন যে কী ঘটে, তা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না। আপনার সঙ্গে কত দুর্ব্যবহার করেছি, কত অন্যায় করেছি, আমাদের মাফ করে দিয়েন।’ একটু থেমে আমি কথাটাকে আরও সুনির্দিষ্ট করলাম, ‘আমাকেও মাফ করে দিয়েন।’ এতে কোনও সন্দেহ-সংশয় নেই, এ কথা বলার সময় আমি সত্যিই অনুতাপে ভরে উঠেছিলাম, আমার হৃদয় তখন পুড়ছিল মনস্তাপে, হৃদয়ে জেগে ওঠা ক্রন্দনকে অনেক কষ্টে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলাম আমি। কারণ, আমি নিজে তো জানি, তার কাছে আমি কতভাবে অপরাধী। কিন্তু মনে হয় না, আমার সেই অনুতাপ, মনস্তাপ আর ক্রন্দন মাকে একটুও স্পর্শ করল। তিনি চুপ করে রইলেন আর এরই মধ্যে ঘরের ভেতর অন্য কে যেন চলে এল। আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। তাঁর কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আমি যে দ্বিতীয় কিংবা আরও বহুবার কথাগুলো ফের বলব, তার আর সুযোগ হলো না। কিংবা বলা চলে, মার অন্তহীন ঔদার্য্যরে ওপর আমার এত বেশি ভরসা ছিল যে, আমি আর দ্বিতীয়বার ক্ষমা চাইতে গেলাম না। এরই মধ্যে একদিন কথায় কথায় আমার ছোটবোন জানালো, মার কাছে সে ক্ষমা চেয়েছিল। মা তখন বলেছেন, ‘মা, এই নিয়ে তোমাদের আমাকে কিছু বলতে হবে না। তোমাদের কেউ যদি আমার কাছে কোনও ভুল করে থাকো, সে জন্যে খোদার কাছে আমি মাফ চেয়ে রেখেছি। তোমরাও আমাকে মাফ করে দিও।’ যে কথাটি ছোটবোন আমাকে জানাল না তা হলো, তারপর তারা দুজন গলাগলি ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।
বোনের কথায় আমি আশ^স্ত হয়েছিলাম, নিশ্চিত হয়েছিলাম, মা নিশ্চয়ই তার আরও সব সন্তানের পাশাপাশি আমাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদিও মনের মধ্যে একটু খচ খচ থেকেই গিয়েছিল; আর মাঝেমধ্যেই মনে হতো, সেদিন আমি ওই কথা বলার পরও মা কোনও কিছু বললেন না কেন! নাকি তিনি শুনতে পাননি ? নাকি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সবগুলো যন্ত্রণাময় পত্র উড়তে শুরু করেছিল মনের মধ্যে ভীষণ বেগে! সৌজন্যবশতও তো মানুষ কথার পিঠে কথা বলে। আর মার মধ্যে তো এর ঘাটতি ছিল না কোনওদিন। কিন্তু তিনি আমার কথাটিকে জিইয়ে রেখে দিলেন নিজের ভেতর। যাতে আমি সারাটা জীবন ভয়ঙ্কর এক অনিশ্চয়তা নিয়ে বেঁচে থাকি, ভয়ঙ্কর এক হাহাকার নিয়ে ঘুরতে থাকি।
তারপর একদিন সেই গভীর রাত্রি এল। সেই রাতে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ‘অল অ্যাবাউট মাই মাদার’ সিনেমাটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত এক দীর্ঘশ^াস হয়ে স্থির হয়ে গেল। দীর্ঘশ^াস হয়ে গেল পায়ে চলার পথ। দীর্ঘশ^াস হয়ে গেল তখনও এই পৃথিবীতে না-আসা আমার কন্যার মুখ। দীর্ঘশ^াস হয়ে গেল আরও অনেক কিছু। অনেক আগে―প্রবাসজীবনে এই সিনেমাটি আমাকে প্রথম মুগ্ধ করেছিল। বিদেশ ছেড়ে চলে আসার আগেও আরেকবার ছবিটি দেখেছিলাম আমি। সেও তো প্রায় বছর সাতেক আগের কথা। মাসদেড়েক আগে থেকে আবারও বারবার ছবিটি দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। কোনও চলচ্চিত্রের কথা বললেই আমার এক সহৃদয় সহকর্মী শরীফ নামিয়ে দেয় সেটা অনলাইন থেকে। এবারও তাই ঘটল। ছবিটি সে অনেক খুঁজেপেতে ডাউনলোড করে দিল। কিন্তু তার পরও কয়েক দিন কেটে গেল; সময় এত কম পাই যে সিনেমাটি আমাকে আবারও দেখতে হলো পর পর তিন রাত মিলিয়ে। অবশেষে সেই গ্রীষ্ম ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে, জ্যৈষ্ঠ মাস এলে নাকি আসি-আসি করলে ভীষণ দাবদাহ ছড়ানো এক গভীর রাতে শেষ হলো তৃতীয়বারের মতো এই সিনেমা দেখা। তারপর এলোমেলো হিসাবনিকেশ করছি, বইপত্র দেখছি, তখনই রাত দুইটা ছয়চল্লিশ মিনিটে তারস্বরে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। এত রাতে সচরাচর আমার কাছে ফোন আসে না, এলেও সাইলেন্স মুডে থাকে বলে তা ধরা হয় না। কিন্তু সেদিন বোধহয় ভুলে গিয়েছিলাম স্তব্ধ করে রেখে দিতে। অতএব ফোন বাজতেই থাকল, আর আমি কেন যেন নির্বোধের মতো মনিটরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সেখানে ছোট ভাইয়ের নামটা দেখতে পেয়েও। তারপর হঠাৎ করেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, ফোন ধরলাম, বললাম, ‘হ্যাঁ, শান্ত…’
‘মা তো মারা গেল ভাই।’
খুবই সাদামাটা নিরীহ কণ্ঠে জানাল ও।
আমার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করছিল, তবু প্রশ্ন করলাম কখন এই ঘটনাটা ঘটেছে। জানলাম, একটু আগেই।
আচ্ছা, আমি কি সেদিন এই খবরের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম ? রাত জেগে ছিলাম ? আর নির্বোধের মতো প্রশ্নই বা করতে গেলাম কেন তখন ? কেন বললাম, ‘মার কি খুব কষ্ট হয়েছিল শান্ত ?’
কিন্তু তখন কি এই প্রশ্ন করার সময় ?
তবু কেন যেন প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু শান্ত বোধহয় প্রশ্নটা বুঝতে পারল না, তাই কেমন যেন হতভম্বের মতো বলে উঠল, মানে ? অথবা, হতে পারে, প্রশ্নটা ও ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আর সে কারণেই বিরক্তি নিয়ে ওরকম করে উঠেছিল। একজন মানুষের মৃত্যু ঘটার সময় সে কতটুকু যন্ত্রণা পায়, তা তো অন্য কারও বোঝার কথা নয়। এমনকি যারা আকাশ বাতাস না কাঁপিয়ে খুব নিস্তব্ধে ঘুমের মধ্যেই বিদায় নেয়, তাদেরও যে কোনও কষ্ট হয় না, সে কথা কি কেউ দিব্যি দিয়ে বলতে পারে! আসলে যে কী হয়, সে তো কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমি তাই আর কথা না বাড়িয়ে ফোনটা রেখে দিলাম।
সোহা ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। ওর তখন অন্তঃসত্ত্বাকাল। ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়েই আমি কেমন যেন নিঃসাড় হয়ে পড়লাম। এতক্ষণে,―এতক্ষণে মায়ের এই মৃত্যু কত যন্ত্রণাকর, তা আমি টের পেতে লাগলাম। মা আর মাত্র মাস দুয়েক বেঁচে থাকলেই আমাদের মেয়েটাকে দেখে যেতে পারতেন। কিন্তু মা তার আগেই বিদায় নিলেন। এতদিন ধরে আমি তার সঙ্গে যত দুর্ব্যবহার করেছি, যত যন্ত্রণা দিয়েছি, যত অপমান করেছি, সে সেসবের প্রতিশোধ নিয়ে গেলেন খুব নীরবে, নিঃস্তব্ধে। দুর্ব্যবহার করার পর, যন্ত্রণাহত হওয়ার পর, অপমানিত হওয়ার পর তিনি যেমন নীরব ও নিস্তব্ধ থাকতেন, ঠিক তেমনভাবে প্রতিশোধও নিয়ে গেলেন তিনি। সেরকম এক বন্দোবস্ত করে গেলেন, যাতে যতবার আমি আমার সন্তানের মুখ দেখব, ততবার মনে পড়ে যাবে, আমার মা তার মুখটা না দেখেই চলে গেছে।
আমি তো খুব ভালো করেই জানতাম, এই সিনেমাটা―এই ‘অল অ্যাবাউট মাই মাদার’ আমার মায়ের গল্প নয়, কিন্তু এটি তো আমার মায়েরই গল্প মনে হয়! এইভাবে ‘অল অ্যাবাউট মাই মাদার’ সিনেমাটি আমার ব্যক্তিগত জীবনের চূড়ান্ত দীর্ঘশ^াসময় অধ্যায় হয়ে গেল।
দুই
আগে কখনও এরকম ঘটেনি। আগে মানে তারুণ্যে, মধ্যবয়সে। যদিও জানি না, তারুণ্য হারিয়েছি কি না। যদিও জানি না, মধ্যবয়স এসেছে কি না। তা যা হোক, এখন কখনও অন্ধকার নেমে এলে আমি তার চোখে চোখ পাতি। মনে করার চেষ্টা করি, মাকে আমি প্রথম কবে দেখেছিলাম। মনে করার চেষ্টা করি, চোখ মেলে আমি কি তাকেই প্রথম দেখেছিলাম ? নাকি দাইয়ের দিকে চোখ পড়েছিল আমার ? মা তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, চোখ বুজেছিলেন, যে কারণে তাঁর চোখে চোখ পড়েনি আমার ? কিংবা এসব কোনও কিছু মনে না পড়ুক, এ-ও কি আমার মনে পড়বে না, মাকে দেখার, তাকে মা হিসেবে বুঝবার প্রথম স্মৃতিটি কেমন ? নাকি শুধু কোলের মধ্যে রেখেছেন বলে, ক্ষুধা পেলে মুখের মধ্যে স্তন্য গুঁজে দিতেন বলে স্বার্থপর এক নৈকট্য ও নির্ভরতা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমার ? যেসব প্রশ্ন কখনও মনে জাগে না, অন্ধকারের অতলে সেসবই আমার দিকে ধেয়ে আসে দূর আকাশের উল্কার মতো আর আমি সহস্র লাখ আলোকবর্ষের মতো ঘুরতে থাকি, কেবলই ঘুরতে থাকি।
একদিন অন্ধকারে হঠাৎ করে আমার কাছে একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। শান্ত এক নদীঘাট ঘেঁষা বাঁশের মাচার ওপর চুপচাপ বসে আছি ছোট্ট আমি। সামনে নদী, আপাত শান্ত, কিন্তু ভীষণ অশান্ত সেই নদী। আর আমার হৃদয়টা কেবলই ডুবে যাচ্ছে সে নদীর ঘূর্ণায়মান স্রোতে। অকস্মাৎ আমার চোখে পড়ল, ঘাট ছেড়ে চলে যাওয়া নৌকাটাকে মাঝনদী থেকে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করছে মাঝি। কিন্তু হাল ঘুরাতে পারছে না কিছুতেই, অনুকুল স্রোত পেয়ে নৌকাটা কেবলই চলে যেতে চাইছে সামনের দিকে। আর সেই নৌকার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মা প্রবল হাহাকার তুলে যেন ঝাঁপ দিতে চাইছেন জলে। কিন্তু কারা যেন তাকে ধরে রেখেছে শক্ত করে। আশপাশে কেউ নেই, নৌঘাটের একমাত্র ছোটখাটো ঘোল আর চিড়ামুড়ির দোকান, সেটাও বন্ধ এই অবেলায়―কেবল নদীতীরের বটগাছটার পাতা কেমন স্তব্ধ জমাট করে তুলছে চারপাশের বাতাসকে। আমি খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছি, কে ? ও কে, অমন করে ঝাঁপ দিতে চাইছে ?
হঠাৎই সাঁ করে যেনবা মনে পড়ে যায় আমার, মা… হ্যাঁ, মা-ই তো! বাবার বাড়ি যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে করে। কিন্তু বোঁচকা, পোটলাপুটলি আর আরও সব ছেলেমেয়েদের তুলতে তুলতে ভুলে গেছেন আমাকে নৌকায় তুলতে। বিশেষ করে, বাড়ি থেকে বেরুনোর পর থেকেই তো মাসকয়েকের ছোট মেয়েটাকে সামলাতে সামলাতে নাকাল হতে হচ্ছিল তাকে। মাঝনদীতে গিয়ে হয়ত গুনেটুনে বুঝতে পেরেছেন, একটা তো কম পড়ে গেছে! তাই চিৎকার করছেন। কিন্তু করতোয়ার মধ্যিখান থেকে নৌকা ঘুরিয়ে তীরে ফিরে আসা কি অতই সহজ ? তার ওপর স্রোত যখন প্রতিকূলে। এদিকে আমি বসে আছি নদীকূলে, বলা তো যায় না, যে কোনও মুহূর্তে নেমে পড়তে পারি নদীতে। পানির মধ্যে নেমে পড়া তো জন্মগত মুদ্রা শিশুদের। মা তাই চিৎকার করছে। কিন্তু মাঝিটা খুব শান্ত স্বরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ‘চিৎকার কইরেন না মা জননী, পোলায় ভয় পায়া কিছু একটা কইরা বসব কিন্তু। চুপচাপ বইসা থাকতে দেন।’ শান্ত স্বরে বলছে বটে, কিন্তু তার হাতের পেশি, কব্জি সবকিছু বড় বেশি অশান্ত তখন হালের নিয়ন্ত্রণ নিজের চোখের মাপে রাখতে গিয়ে।
কিন্তু এতদিন পরে মনে হয়, এই যে ভাবছি, আমার স্মরণে থাকা মাতৃমুখ দর্শনের এটাই প্রথম স্মৃতি, কথাটা হয়তো সত্যি নয়; কারণ এ-ও তো আমার মনে আছে, মা একদিন কথায় কথায় আমাকে শুনিয়েছিলেন ছোটবেলার এই দিনটির কথা; বলেছিলেন, কীভাবে আর একটু হলেই হারিয়ে যেতে বসেছিলাম আমি সেই দূর শৈশবে। মায়ের মুখ থেকে তা জানতে পেরে আমি শিহরিত হই, অজানা আতঙ্কে বিহ্বল হই, যেন আমি আবারও হারিয়ে যাচ্ছি, যেন আমি আবারও বিস্তীর্ণ এক নদীকূলে একা-একা বসে আছি, বটগাছ আছে আমার মাথার ওপর, নদীর জলে সিক্ত মাটি আর বাঁশের মাচান আছে আমার পায়ের নিচে, আছে আকাশ, আছে আকাশের বুকে উড়ন্ত বলাকা, আছে নদীতে ভাসতে থাকা রঙিন পালতোলা কত নৌকা, তবু আমার কোনওখানে কেউ নেই! আমি যতবার এই কথা ভাবি, ততবার শিহরিত হই, ততবার হারিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ভর করে আমার চোখে মুখে মনে। সত্যিই যদি ওরকম ঘটত ? সত্যিই যদি ঘটত ? কোনখানে থাকতাম আমি, কার কাছে ? মরে যেতাম ? মরে যেতাম এই আমি ? কী ভীষণ বিপন্নতায় যে আমি বার বার মাকে জড়িয়ে ধরতে চাইতাম, আবার জড়িয়ে ধরতে গেলেই মনে হতো, বড় হয়ে যাচ্ছি, এখন কি আর ঠিক হবে এইরকম ব্যাখাতীত কোনও ভয়ে তার কোলে আশ্রয় নেওয়া, প্রশ্রয় খোঁজা ?
তারপর কত দিন গেছে, মাঝেমধ্যেই আমার মনে হতো এই ঘটনার কথা। মনে হতো নির্জন দুপুরে। মনে হতো ভৈরবীময় ভোরে। মনে হতো ভীমপলশ্রীতে দুলে ওঠা বিকেলে। মনে হতো ঘুমভাঙা বসন্ত বাহার আক্রান্ত রাতে। তা হলে এমন কি হতে পারে না, আসলে এই ঘটনা আমার স্মৃতিঘরে কখনই ছিল না ? এমনকি হতে পারে না, আসলে মায়ের কাছ থেকে শোনার পর বারবার মনে করতে করতে ঘটনাটি আমার স্মৃতির অংশ হয়ে উঠেছে ? বার বার মানসচক্ষে কল্পনা করতে করতে সেই দিনটি জীবন্ত এক স্মৃতি হয়ে উঠেছে আমার কাছে! এত বেশি বার ভেবেছি সেই দিনটির কথা যে, কল্পনায় নির্মিত আর মায়ের মুখ থেকে শোনা ঘটনাটিকে নিজস্ব স্মৃতি বলে মনে হয়―কিন্তু বাস্তবতা হলো, মাকে আমি প্রথম কোনওদিন দেখেছি, তা আর আমার আদৌ মনে নেই।
আর মনে থাকবেই বা কী করে। বয়স তো আমার নিজেরও কম হলো না। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, মরে গেলে কেউ কেউ হয়তো দুঃখ পাবে, বলাবলি করবে আরও কিছুদিন কেন বাঁচতে পারলাম না। কিন্তু মৃত্যুটাকে নিশ্চয়ই অন্যায্য কিছু মনে করবে না। আর ভুলেও যাবে কোনওদিন।
তিন
কিন্তু আমি কেন ভুলতে পারি না ? আমি কেন কেবলই সাঁতরাই তপ্ত স্মৃতির ভেতর! ? হয়তো সেটা স্মৃতির সমুদ্র, হয়তো সেটা স্মৃতির ডোবা, হয়তো বা সরু নালা―তবু আমি সাঁতরাই দিনভর, রাতভর। কারণ একবার সাঁতার শেখার পরে কোনওদিন আর ভোলা যায় না। এত ব্যস্ত আমি, এত কাজে ডুবে থাকি আমি, ডুবে যাই আমি, তার পরও কান্নাহাসির দোলা কিছুতেই থামে না।
দৃশ্যটি ছিল ভীষণ দুঃসহ―দিনের পর দিন মা শুয়ে আছেন, শুয়েই আছেন। চোখ দুটো বুজে, ঠোঁট দুটো কখনও কখনও সামান্য হা হয়ে যাচ্ছে। কোনও কিছু খাচ্ছেন না, খেতে চাইছেন না, খেতে পারছেন না। সমস্ত দিনের শেষে এই পৃথিবীতে এসেছে এক কালবেলাময় সন্ধ্যা। কিন্তু শরীরটা সব সময়েই তিনি ঢেকে রেখেছেন একটা চাদর দিয়ে। চাদর দিয়ে নিজেকে যতটুকু সম্ভব আচ্ছাদিত করে রাখা, এই ব্যাপারটা ছিল বুকমার্কারের মতো―কে না কে কখন দেখতে আসে! তাঁকে যেন কখনও বিত্রস্ত অবস্থায় দেখতে না পায়। পলায়নপরতার এই প্রতীক থেকেই আমরা বুঝে নিতাম, মা আছেন―এখনও সম্পূর্ণ সজ্ঞানই আছেন। কিন্তু কে জানত, হয়ত ছিলেন না, অভ্যাসবশত এসব করে যেতেন। যেমন চিরদিনের অভ্যাসবশত, অভ্যাস থেকে গড়ে ওঠা রুচি-সংস্কৃতিবশত কখনই তিনি বিছানায় বসে প্রস্রাব বা পায়খানা করতেন না। যতদিন পেরেছেন, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বিছানার এ কোণ ও কোণ ধরে ধরে, চেয়ারের মাথায় ভর দিয়ে, দেয়ালে হাতটা ঠেসে ধরে ধীরে ধীরে পৌঁছে যেতেন বাথরুমটাতে। সেই সামর্থ্য যখন লোপাট হলো, তখন তিনি কাউকে ডাকতেন, বলতেন বাথরুমে পৌঁছে দিতে। সবাই ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিতে পারত না। ‘বিছানায় পড়ে গেছে, তার অত আহ্লাদ কিসের, প্যানে বসতে সমস্যা কী ?’ গজ-গজ করতে করতে প্রথম দিকে আড়ালে-আবডালে, তারপর একসময় তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই এইসব বলে উঠত।
ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে, সকালে নাস্তা করার পর আমি তাঁর ঘরটাতে যেতাম। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা রেখে মুখোমুখি দুটো খাট পাতা―সেগুলোর একটিতে মা থাকেন। আরেকটি কখনও শূন্য পড়ে থাকে, কোনও কোনও দিন মা খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িরই কেউ রাতের বেলায় থাকে তার সঙ্গে, অথবা মায়ের খুব নিকটের কোনও মহিলা আত্মীয়স্বজন এলে তার ঠাঁই হয় ওই খাটে। আর ছুটিছাটায়, কোনও উপলক্ষে আমরা এলে সবাই ছড়িয়েছিটিয়ে বসি হয়তো তাঁর খাটে, হয়তো সামনের খাটটাতে, কিংবা ঘরের মেঝেতে, চেয়ারে। সকালে গিয়ে আমি তাঁর মুখোমুখি খাটটায় বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম। আবার কোনও কোনও সময় তাঁকে বিছানা থেকে সরিয়ে চাদরটা ঝেড়ে নতুন করে পেতে দিতাম। বলতাম, চাদর কিংবা বালিশের কাভার এসব ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কি না। তখন, অনুমান করি, তিনি খুব প্রসন্নবোধ করতেন। একটু কথা বলার চেষ্টা করতেন। হাতের কাছে রাখা ‘তাজকিরাতুল আউলিয়া’ কিংবা ‘বেহেশতী জেওর’ বইটি এগিয়ে দিয়ে বলতেন, ‘কত বই পড়―এই বইটা একটু পড়ে দেখ।’ কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তিনি বসে থাকতেন অনুযোগহীনভাবে, অনুরোধহীন। তবে প্যান ব্যবহারের কথাটিকে তিনি কখনই ভালোভাবে নিতে পারেননি। আবার আপত্তি যে জানাবেন, সে শক্তিও ছিল না। আমি যে এই পরিবারের সবচেয়ে শক্তিহীন ব্যক্তি, সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন। তিনি জানতেন নরম কাঠে ছুতারের বল―আমার যতটুকু শক্তি তার সবটুকুরই প্রকাশ ঘটে কেবল তার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। তবু তিনি কেন যেন আমার দিকেই অসহায়ের মতো তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘আমাকে প্যানের উপর বসে পায়খানা-পেসাব করতে বলে!’
আমার ‘পারমিতার একদিনের’ কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কদিন ধরে পায়খানা প্রস্রাব না করেই শুয়ে আছেন অপর্ণা সেন। ঋতুপর্ণা এল, এসেই চারপাশ শাড়ি দিয়ে ঘিরে দিল। আর অপর্ণা নির্ভার চিত্তে পরিচ্ছন্ন করলেন নিজেকে।
আমি চুপ করে বসে থাকলাম। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা এইসব। অথচ সেদিনের কথা নয়।
তবে ওই যে মায়ের ঠিক অভিযোগ নয়, অসহায়ের মতো বলা ‘আমাকে প্যানের ওপর বসে পায়খানা-পেসাব করতে হবে!’―ওই কথাটুকু বলতে পারার পর থেকেই তিনি হয়তো আমার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছিলেন একটু একটু করে। আশপাশে অন্য কেউ না থাকলে শক্তিহীন কণ্ঠটাকে যতটুকু সম্ভব উঁচিয়ে তিনি একটু-আধটু অভিযোগ করতেন এটাসেটা নিয়ে। না, ঠিক অভিযোগ নয়, অভিযোগ বলাটা ঠিক হবে না। পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ ছিল না। বরং বলি, স্মৃতির বিবরে ফিরে যেতেন। স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু স্মৃতিচারণের ঘটনাগুলোই নিজে থেকে বলে উঠত, এগুলো তার জমিয়ে রাখা কষ্টও বটে। আমার মনে হয় না, আমাকে তিনি এসব কথা শোনাতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর হয়তো এমন কেউই আর অবশিষ্ট ছিল না, যার কাছে তিনি এসব বলতে পারতেন। গাঁয়ের বাড়িতে আমার যাওয়া হয় খুবই কম। কিন্তু চাকরিবাকরি হারিয়ে তখন আমি বলতে গেলে গ্রামেই চলে গেছি। সকাল ১০টা ১১টা হলে পুরো বাড়ি ফাঁকা হয়ে পড়ত। সেই ফাঁকা বাড়িতে মার নিঃসাড় কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আমিও অচেনা হয়ে উঠতাম আমার কাছে। আমি আবারও শহরে চলে আসার পর কিংবা আমরা কেউই না থাকার সময় তাঁকে কী ভয়ঙ্কর সময় কাটাতে হয়েছে, তা আমি চিন্তা করতেও পারি না।
এইভাবে মা দিনের পর দিন বেঁচে ছিলেন। আর আমরাও তাঁর ওই অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই হয়তো মায়ের কণ্ঠের কোনও অস্বাভাবিকতাও আর আমাদের কারও কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো না। মনে হতো না, এ ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার, এই যে কথাটা বললেন, সেটাকে একটু ভেবে দেখা দরকার। মা এখন একেবারেই শয্যাশায়ী, এখন আর উঠেও বসেন না―এটা জানতাম, কিন্তু এটা আর আমার জানা হয়ে ওঠেনি, শেষের দিনগুলোয় তিনি কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন না। খাওয়াদাওয়াও করতেন না। ছোটভাইটা নাকি অসহায়ের মতো মাঝেমধ্যে এসে শিয়রে বসে তার মুখের মধ্যে এক-দুই চামচ দুধ ঢেলে দিতো। মা কখনও খেতেন, কখনও তা ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ত। কখনও আমার ছোটভাইটা ভাত আর মাছ ছেনে ছেনে একেবারে পানি বানিয়ে ফেলত, সেই ভাত-মাছ-পানি চামচ দিয়ে চেষ্টা করত মাকে খাইয়ে দিতে। মার মৃত্যুর অনেক-অনেক দিন পর আমি দুটি ঘটনা শুনতে পাই। মৃত্যুর দিনচারেক আগে তিনি যেদিন শেষ কথা বলেছিলেন, সেদিনের কথা; আর তারও দিনসাতেক আগের একদিনের কথা, সেদিনও তিনি কথা বলেছিলেন স্বাভাবিকভাবে, স্পষ্টভাবে। এমনিতে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণেই তা হয়তো কোনও অসাধারণ বিষয় হয়ে ওঠে আমার কাছে।
শুয়ে থাকতে থাকতে, কী যেন কিসের প্রস্তুতি নিতে নিতে নির্বাক মা নাকি একদিন হঠাৎ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, ‘আচ্ছা, আমার ছেলেমেয়েরা সব কোথায় ? আমার তো এখন যাওয়ার সময়। তারা কোথায় থাকে ? তাদের তো আমার চারপাশ ঘিরে বসে থাকার কথা। তারা কোথায় ?’
এ টুকুই… আর কিছু বলেননি তিনি। আমার ভাই-ভাবিদের কারও কাছে কথাটা হয়তো তত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি তখন। শয্যাশায়ী একটা মানুষ, দিনের পর দিন কেবলই ঘুমায়, মেডিক্যালের ভাষায় হয়তো একেই বলে কোমায় চলে যাওয়া, সেরকম একটা অবস্থা আর কি; তা সেই মানুষটি যদি একদিন হঠাৎ এরকম একটা কথা বলেও থাকে, তা কি আর তেমন কোনও বার্তা দিতে পারে ? আমরা যারা বাড়িতে থাকতাম না, থাকতাম শহরে, তাদের কাউকেই এ ঘটনাটা তাই আর জানানো হয়নি। আমরা খোঁজখবর নিতাম। জানতাম, আজ তিনি একটু খারাপ আছেন। আজ খাওয়াদাওয়া করেননি। প্রতিদিনই তো এরকমই থাকছেন তিনি,―কাঁদছেন, যন্ত্রণা পাচ্ছেন, গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একে ওকে ডাকাডাকি করছেন, এরকম কোনও ঘটনা কখনই ঘটেনি―মৃত্যুর আগেও ঘটেনি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ওই স্পষ্ট কণ্ঠে অমন কিছু বলে ওঠাটা ছিল রীতিমতো অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কারও কাছে সেরকম মনে হয়নি।
তারপর দিনসাতেক আবারও বাক্যহীন দিনরাত কাটে তার। কখনও কখনও চোখ মেলেন, তাকিয়ে থাকেন, তবে কোনদিকে, কী কারণে, বোঝা যায় না। কিন্তু কোনও কথা বলেন না, হয়তো কথা বলার শক্তিও পান না। তারপর আরও একটি ঘটনা ঘটে। সেদিন তার বিছানার কাছে মেঝের ওপর খেলাধুলা করছিল আমার ছোট ভাইবোনদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ চোখ খুলে শরীরটাকে সামান্য কাত করে তিনি নাকি তাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন স্নেহময়ী চোখে, তার চোখেমুখে ঠোঁটে মিষ্টি একটু হাসি ফুটে ওঠে, আর তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন, ‘আমার সোনামণিরা―’। তারপর আস্তে আস্তে নিজের চোখ দুটিকে গুটিয়ে নেন।
তারপর দিনচারেক তিনি আর কথা বলেন না। সেদিন বিকেলের দিকে তার শরীরটা একটু গরম হয়ে ওঠে। রাতে তাকে ছোটভাই কোনওমতে চামচ দিয়ে একটু তরল খাবার খাওয়ায়। অনেক রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফের মার শিথানের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর আগেই বুঝতে পারে, মৃত্যু ঘটেছে তার।
মাঝেমধ্যেই আমি দিব্যচোখে বিশেষত শেষের দিকের এই ঘটনা দেখতে পাই। ঠোঁটে একটুকরো মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন অনন্যা, কাব্য, সন্ধিদের দিকে; আর মিষ্টি স্বরে বলছেন, ‘আমার সোনামণিরা…’
মা যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে কে জানে, তার ওই নাতি-নাতনির সঙ্গে আমার মেয়েটিও থাকতে পারত, আর সেও মায়ের বলা এই ‘আমার সোনামণিরা’ কথাটার ভাগিদার হতে পারত! কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি, সে রকম কিছু আর কখনই হবে না। শুধু মাঝেমধ্যে বেহুদাই আমার মনে পড়ে যাবে, মা ভীষণ প্রতিশোধ নিয়ে গেছেন।
চার
এতদিনে, বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারি, খুব ছোটবেলাতেই ঈশ^র আমার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। মাকে ঘিরে শত্রুতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠি আমি আর ঈশ^র। এখন, এসব লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, নিঃসন্দেহে এটিই আমার স্মরণে থাকা মাকে দেখার প্রথম স্মৃতি―ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছরের একটি মেয়ে রান্নাঘরের চুলার পাশে বসে আছে, কাটা-বাছা করছে, উনুনের মধ্যে খড়ি কিংবা শোলা ঠেলে দিচ্ছে, তুষ ছিটিয়ে দিচ্ছে আগুনের মধ্যে, খড়ি তুলে চুলার ওপরে রেখে আগুনের আঁচ কমাচ্ছে। কিংবা চুলায় ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে, ধোঁয়ায় ভরে গেছে সারা ঘর, চোখ কুঁচকে এসেছে তাঁর, মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, কিন্তু মা অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন আগুন জ্বালাবার। উঠোনে পাটির ওপর পড়ে আছি অসুস্থ আমি, রোদ এসে পড়েছে আমার মুখের ওপর, দেহের ওপর; চিৎকার করে কাঁদছি আমি, চিৎকার করে ডাকছি আমি; আমার চিৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার মুখ আরও লাল হয়ে উঠছে, চোখ ততই বুজে আসছে ধোঁয়ার তীব্র ছোঁয়ায়।
এতদিন পরে, সত্যজিৎ রায়ের মতো আমিও বলতে পারি, মা’র কথা মনে হলেই আমার মনে হয়, কাজ ছাড়া কখনই দেখিনি আমি তাকে। জানি না, কাজ করতে তিনি কতটুকু ভালোবাসতেন; কিন্তু সারাদিন নিমগ্ন থাকতেন কাজের ভেতর, কিংবা নিমগ্ন থাকতে হতো কাজের ভেতর। তাঁর যে আপন জগত, সেইখানে কাজকর্মের কোনও অভাব ছিল না, বেকারত্বের জ্বালা ছিল না, প্রতিভাধর অথবা ভালো রোজগেরে হিসেবে খ্যাতি পাওযার মতো ঈর্ষণীয় কোনও কাজ খুঁজে না পাওয়ার অতৃপ্তি ছিল না, আদিগন্ত বিস্তৃত এক জীবন্ত নদী তিনি, শান্ত থাকলেও যার প্রবাহ থেমে থাকে না, নিথর স্থির হয়ে থাকার পরও যিনি বহতা সবসময়।
সারা দিন আমি অপেক্ষা করতাম, রাতে মাকে নিশ্চয়ই ফাঁকা পাওয়া যাবে, রাতে মায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলা যাবে। আমি মানে শিশু আমি, ছোট্ট আমি, প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়া আমি। কিন্তু সকাল, দুপুর, বিকেল আর সন্ধ্যায় মোট চারবার যেমন, তেমনি রাতেও তিনি সামান্য একটু ফুরসত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজু করে এসে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়তে বসে যেতেন। ঘরের নির্জন এক কোণে আপনমনে নামাজ পড়ছেন তিনি, আর একটু দূরেই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। অপেক্ষা করতে করতে কাঁদছি আপন মনে―সারা দিনের পর সামান্য একটু অবকাশ পাওয়া সময় মায়ের, তাও কি না কেড়ে নিচ্ছে এক নিরাকার ঈশ^র! প্রথমে প্রচণ্ড অভিমান, তারপর প্রচণ্ড রাগ জন্মাতে থাকে তার ওপরে। দেখা যায় না তাকে, কথা বলা যায় না তার সঙ্গে, ছোঁয়া যায় না তাকে; তাই এই শত্রুতা যতই অসম হতে থাকে, ততই হয়ে ওঠে তীব্রতর। আমি জানি না, ঈশ^র কে, কিন্তু এটুকু জেনে যাই, বাবার চেয়েও অনেক পরাক্রমশালী সে, বাবাও নত হতে বাধ্য হয় অদৃশ্য সেই শক্তির কাছে। তাই বাবাকে কখনই দেখি না ঈশ^রের কাছে মায়ের মাথা ঠোকা নিয়ে কোনও আপত্তি তুলতে, দেখি না কখনও অধৈর্যও হতে। বরং মায়ের এই নির্ভরতায় পরম এক স্বস্তির আলো যেন বাবার মুখজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি জানতাম, ছোটবেলা থেকেই কখনও এ রোগ, কখনও-বা ও রোগে ভুগি বলে অন্য সব ভাইবোনের চেয়ে মা বোধহয় আমাকে একটু-আধটু মায়া বেশিই করে থাকে। অন্য সবাই তো সুস্থ, সবল, প্রবল পরাক্রমশালী; বাড়িঘরে তাদের কাউকে বলতে গেলে পাওয়াই যায় না খাওয়ার সময় ছাড়া। আমার ছোট ভাইটা, সকালে উঠেই চলে যায় তার ইংলিশ প্যান্টটার এক পকেটে লাটিম আর সেটার দড়ি এবং আরেক পকেটে মার্বেল নিয়ে পুকুড়পাড়ের দিকে। সেখানে বিশাল আমগাছ আর পাইঙ্গা গাছের নিচে দিনভরই পাওয়া যায় কাউকে না কাউকে। আর আমার পিঠোপিঠি বড় ভাই যেন কেমন, মনে হয় আর দুই-চার পা ফেললেই শুচিবায়ুগ্রস্ত বলা যাবে তাকে। কেন যেন সব সময়ই সে চেষ্টা করে সচেতনভাবে সবার থেকে দূরে থাকতে। শুধু তাই নয়, যতটুকু বা কাছে আসে ততটুকুও আবার পূতপবিত্র করে তুলতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কেউ তার বিছানায় বসলেই যতক্ষণ না সেটার চাদর তুলে খানিকক্ষণ রোদে রাখতে না পারে, ততক্ষণই খুব অস্থির থাকে সে। আর কেউ তার বিছানায় ঘুমালে মনে হয় তার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি উধাও হয়ে গেছে। তাও ভাগ্য ভালো, কাপড়চোপড় রোদে দেওয়ার মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটে থাকে। এ কথা ভাবতে গেলে আমি এখনও শিউরে উঠি, যদি কোনওক্রমে তাকে সেসব কাপড়চোপড় ধোয়াধুয়ির নেশা পেয়ে বসত, না জানি কী হতো! নিশ্চয়ই আমরা দেখতাম, বাড়িতে একটা মানুষের হাত-পা সারাদিনই ভেজা থাকে। কাপড়চোপড় আর বিছানার ব্যাপারে তার এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা যতই প্রবল, ততই উধাও তা বিড়ালের ব্যাপারে। যে কোনও বিড়ালকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে দ্বিধা করে না সে, রাতে নির্বিবাদে ঘুমায় বেড়ালকে কোলের মধ্যে নিয়ে এবং বেড়াল যদি তার থালা থেকে কোনও কিছু নুলো বাড়িয়ে তুলে নেয়, তাতেও সে কিছু বলে না। তার এই বিড়ালপ্রীতি অক্ষুণ্ন থাকে অনেক-অনেক দিন, তার এই বিড়ালপ্রীতি আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে যখন ছুটিছাটায় শহর থেকে আমাদের তেমন কোনও আত্মীয়স্বজন আসে, যে বা যারাও বেড়াল ভালোবাসে। তখন আমরা দেখি, বিড়ালকে আদর-যত্ন করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে এবং তা হয়তো অনন্তকালই চলত, কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই আমার সেই ভাইয়ের গলার গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে ওঠে, গলার প্রচণ্ড ব্যথায় খাওয়াদাওয়া তো বটেই, ঘুমও উধাও হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে গেলে, ডাক্তার নানা আলামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষমেষ এই সিদ্ধান্ত দেন যে, আমাদের ভাইটির পেটের মধ্যে বেড়ালের পশম ঢুকে পড়েছে। ভুগতে হবে, তাকে তাই ভুগতে হবে আরও অনেক-অনেক দিন। কী দিয়ে কী যে হয়, তারপর থেকে আমার ভাই বিড়ালকে প্রশ্রয় দিতে ভুলে যান। ভুলে যান চাদর, বালিশেও রোদ লাগাতে। তবে মায়ের প্রশ্রয়ে তেমন হেরফের ঘটে না, আগের মতোই তিনি প্রতি বেলায়ই বিড়ালটাকে খানিকটা ভাত তুলে দেন পাত থেকে। ভায়ের স্নেহ হারানো বেড়ালটা অনেক চেষ্টা করেও পারে না তাঁর কাছ থেকে বাড়তি একটু মনোযোগ আদায় করে নিতে। অতএব ওই ঈশ^রই আমার একমাত্র শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়।
এক বৈশাখে হয় কি, মা আমাদের রেখে ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে নিজের বাপের বাড়ি চলে যান; আর কী আশ্চর্যজনক ব্যাপার, তিনি চলে যাওয়ার দিন কয়েক পরেই আমি প্রচণ্ড জ্বরে বিছানা থেকে আর উঠতেই পারি না। জ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় মারাত্মক আমাশা। আমার জন্মের পর মাকে তার বাবা-মায়ের বাড়ি যেতে খুব কমই দেখেছি। যাওয়ার সুযোগ হয় না―কেন হয় না, সেটা এই জগতের সবাই বোঝে, সবাই জানে। সেই তিনি কেন যে হঠাৎ করে কার সঙ্গে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এতদিনে তাও আর মনে পড়ে না। তিনি বাপের বাড়িতে গেলেন, আমিও বিছানায় পড়লাম; বাবা বোধহয় অত বেশি নির্দয় হয়ে উঠতে পারেননি যে, চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলবেন তাঁকে। সেটাই ছিল আমার সবচেয়ে উজ্জ্বল অসুস্থতা, যাকে আমি অনুভব করেছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে। প্রচণ্ড জ্বরে আধমরা হয়ে শুয়ে আছি, কেউ যত্ন করছে কি করছে না, সেসব জানার বালাই নেই, কেউ আমার মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে কি না, তাও জানার বালাই নেই। জ্বর হতে না হতেই শুরু হওয়া তীব্র আমাশা দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে, শান্তিতে শুয়ে ঘুমাতেও পারছি না, একটু ঘুম আসতে না আসতেই পেটের মধ্যে কিসের প্রচণ্ড কামড় জাগিয়ে দিচ্ছে আমাকে। চোখ খুলে আমি হয়তো দেখছি আলোয় ধোয়া সকাল, জানালার কার্নিশে বসে আছে কেবল একটি দোয়েল পাখি, তারপরই হারিয়ে যাচ্ছি অচেতন কোন জগতে! চোখটাকে হঠাৎ খুলে আমি দেখতে পাচ্ছি ঝকঝকে রোদে ভরা একটি দুপুর, কোথাও বাতাস নেই, স্তব্ধ সেই দুপুরে ডেকে চলেছে কেবল একটি তিলা ঘুঘু, চোখ খুলে হঠাৎ আমার চোখে পড়ছে জানালা বেয়ে বিছানা অবধি চলে আসা মরা কমলা রোদের আলো, একটা শালিক পাখি দরজা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকতে না ঢুকতেই ফিরে যাচ্ছে কী না কী মনে পড়াতে! চোখ খুলে আমি দেখছি মিটমিট করে জ্বালিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলো, সে আলোর ভৌতিক ছায়ার বিস্তার এখানটায় ওখানটায়, ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, কোথায় যেন একটা রাতজাগা পাখি একবার ডাকতে না ডাকতেই চুপ হয়ে গেল। নাহ্― নেই, কেউ নেই আমাকে দেখার; ভাই আছে কয়েকজন, কিন্তু তাদের কী আর ঘরে বসে থাকার উপায় আছে! আর রোগীর শিথানের কাছে বসে থেকে তারা করবেই বা কী! আছে কেবল মেজো বোন, তিনি মনে হয় মায়ের অনুপস্থিতির এই বেলা আমাদের সবার ওপর ভর করে নিয়মানুবর্তিতার কলাকৌশল রপ্ত করার মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। অতএব তিনিও থাকেন বলতে গেলে মায়ের মতোই সারাক্ষণ রান্নাঘরে। তা বাদে আছে এক কাজের মেয়ে আনুর মা। আমাকে দেখভালের অছিলায় সেই মাঝেমধ্যে এসে গা-হাত-পা ছড়িয়ে পান খেতে বসে যায় আর পানটা মুখের মধ্যে চালান করে দিতে না দিতেই তার চোখজোড়া মুদে আসে পরম সুখে।
মা ফিরে এলেন কোনও একদিন বিকেলের দিকে গড়াতে থাকা দুপুরবেলায়। ততদিনে আমি বলতে গেলে নুলো হয়ে গেছি। দাঁড়াতে পারি, কিন্তু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। দুইবার টাইফয়েড হওয়ার ধাক্কা সামলানো তো আর মুখের কথা নয়। তার ওপর এই ভয়ানক আমাশা। বাড়ির পেছনে কাঁঠাল গাছটার নিচে একটু বাতাস লাগে বলে সেখানে একটা পাটি পেতে তার ওপর আমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কে যেন কাঁঠাল গাছটার ওপরের দিকের একটা শক্তপোক্ত ডালে মোটা রশি বেঁধে রেখেছে। বলা যায়, গরিবের দোলনা। সেই দোলনায় কখনও কখনও আনুর মার দুই মেয়ে এসে বসে দোল খায়। কিন্তু আজ এত বেলা হয়ে গেল, এখনও এই দিকে তাদের কেউ পা মাড়ায়নি। রান্নাঘরের ধোঁয়া আর উত্তাপকে সঙ্গে করে একটু বাতাস মাঝেমধ্যেই এসে চলে যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। কিন্তু বাইরের হালকা বাতাসও একেবারে কম নয়। তাই সব মিলিয়ে গরম লাগছে না। আমি তাকিয়ে আছি একেবারে মুখোমুখি পিছন বাড়ির একটার আমগাছের দিকে। এর আম আবার খাজার মতো মিষ্টি লাগে, তাই একে আমরা ডাকি খাজা আমগাছ নামে। সেই গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি একটু চোখ বুজতে যাব, তখনই মনে হয় কে যেন প্রায় দৌড়ে আসছে।
: আমার সোনামণি রে―
কথাটা কানে এসে ঢুকতেই আমার হৃৎপিণ্ড নড়ে ওঠে। বুঝতে পারি, মা ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠলেও কেন যেন হৃদয়ে কোনও সাড়া জাগে না, একটুও কান্না পায় না। অথচ এই দিনবিশেক ধরে আমি দিনরাত কতই না কেঁদেছি। এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা ঘিরে ধরে আমাকে। আমি তাকিয়ে থাকি, তাকিয়েই থাকি খাজা আমগাছের দিকে। মা এসে আমার পাশে বসে পড়েন, জড়িয়ে ধরেন, আদর করতে থাকেন, ‘সোনা আমার, সোনা আমার…’
কেমন একটা লজ্জাজড়ানো অনুতাপময় হাসিও ফুটে ওঠে মায়ের মুখে, ‘রাগ করেছেন, সোনামণি আমার রাগ করেছেন…’
কিন্তু আমি কিছু বলি না, কিছুই বলি না। মামাবাড়ি থেকে নিয়ে আসা নাড়ু খাই, মোয়া খাই, আস্ত মিছরির টুকরো খাই, কিন্তু তেমন কোনও কথা বলি না। মামাবাড়ির গল্পও শুনি না। কিছুক্ষণ পর মা উঠে রান্নাঘরে যান, ঘরগেরস্থালির খবরাখবর নিতে থাকেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর নিত্যদিনের কাজকর্মে। এর ফাঁকফোকরে অবশ্য আমাকেও দেখভাল করেন। কিন্তু নিজের কাছেই নিজেকে কেমন নিস্পৃহ লাগে আমার।
বিকেল গড়ায়। সন্ধ্যা হয়। রাত্রি আসে। যাবতীয় কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে মা আবারও পাটি বিছায় প্রার্থনায় বসতে।
আমার সারা অন্তরাত্মা এবার রাগে কেঁপে ওঠে, জ্বলতে থাকে। ঈশ^র আমার চিরশত্রু হয়ে যায়। ঈশ^রের সঙ্গে আমার চিরদূরত্ব রচিত হয়ে যায়। আর মায়ের সঙ্গেও ঐকতানের তার কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, নাড়ি কাঁটার দিনই যে মায়ের থেকে সন্তানের শরীর আলাদা হয়ে যায়, এ কথা সত্যি নয়। আলাদা হয় আরও পরে, আরও কোনও ঘটনার মধ্যে দিয়ে অন্য কোনওদিনে। কিন্তু তা আর সাদা চোখে ধরা পড়ে না, টায়-টায় বুঝতেও পারা যায় না। আজ সেই দিন, আজ মা থেকে আমি সত্যিই আলাদা হয়ে গেলাম।
কিন্তু মুশকিল হলো, আমি খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারলাম যে, আজ থেকে মায়ের থেকে আমি আলাদা হয়ে গেলাম; মুশকিল হলো, আমি বুঝতে পারছি না, মায়ের থেকে আমার এই দূরত্বে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারা সৌভাগ্যের নাকি দুর্ভাগ্যের।
হতে পারে, হামিদা সুলতানা এরকম ভাবতেন
আমাদের বাড়ি ছিল মৈত্রবাধায়। ইছামতির ঘাটের একেবারে কাছে। ভাঙতে ভাঙতে নদীকে বাড়ির কাছে চলে আসতে দেখেছি আমি। আবার নিঃস্তব্ধে কোনও কারণ ছাড়াই চলে যেতে দেখেছি ঘাট থেকে দূরে। আমি নিজেও আর চিন্তা করতে পারি না, সে নদী কেমন বিস্তীর্ণ ছিল। এখন তো শুনি কখনও কখনও নৌকা চলাই দায় ওই নদীর ওপর দিয়ে। অথচ খালি কি নৌকা-বজরা আর জেলে নাও নাকি, কত যে স্টিমার ও লঞ্চকেও যেতে দেখেছি ইছামতি দিয়ে! বাবার ছিল কাপড়ের ব্যবসা, চালের ব্যবসা―অথবা এমনও হতে পারে, আরও অনেক কিছুর; এলাকার লোকজনদের অনেকে শুনি আড়তদারও বলে বাবাকে। তার মানে আড়তও ছিল। বেড়া বাজারে আছে বিশাল গুদামঘর―হয়তো সেখানেই তাঁর আড়ত ছিল। ছিল বজরা নৌকা, ছিপ নৌকা, এমনকি ডোঙা নৌকাও। কোন নাওয়ে চড়ে বাবা আমার কোলকাতার কোনখানে যে কখন যেতেন, কী কাজে যেতেন, এখন আর মনে পড়ে না। মনে না পড়ার জন্যে অনেকের যেমন কষ্ট লাগে, সেরকম কষ্টও লাগে না। তাছাড়া কষ্ট পাওয়াও ভালো নয়। আমার এই জীবনের শুরুটা যেমন জানি না আমি, তেমনি শেষটাও তো মনে হয় না জানতে পারব কোনওদিন। এমনকি জীবন যখন পেলাম, পৃথিবীতে এলাম, তারপর বছরের পর বছর যা ঘটেছে―ধরা যাক, প্রথম তিন বা চার বছর―সে সময়ের কোনওকিছুও কি ভালো করে আর মনে আছে আমার ? আমি কি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, মরার সময়ে আমি বুঝতে পারব, মরে যাচ্ছি ? কিংবা এই যে মনে হচ্ছে, বেঁচে আছি আমি, সত্যি-সত্যিই কি বেঁচে আছি ? প্রান্তটা সেদিন শুনিয়ে গেল, ঘুমানোর পর থেকেই মানুষ নাকি অবিরাম স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু ঘুম যদি বেশ গভীর হয়, তাহলে নাকি কোনও কিছুই আর মনে থাকে না। তাহলে এমনও তো হতে পারে, ঘুমের মধ্যে যে জগৎটাকে পাওয়া যায়, মানুষের সেটাই আসল জীবন―আর জেগে থেকে এখন যা ভাবছি, যেসবের কাসুন্দি ঘাটছি, তার সবই অন্য একটা ঘোরের জীবন। এইসব চিন্তা করে কখনও কোনও থই পাইনি আমি। অতএব সিদ্ধান্তে এসেছি, এসব নিয়ে কখনই ভাবতে যাব না।
চিন্তা করে থই পাই না, আবার খেইও তো হারিয়ে ফেলি। বাড়ির কাছে নদী ছিল, এ কথা মনে করতে করতে ভেবেছিলাম, কতদিন নদী দেখি না আমি। নদী তো দূরের কথা বর্ষার জলও দেখি না। এমনিতে আমি পানিই বলি; কিন্তু বর্ষা, নদী এইসব মনে করতে গেলে জল চলে আসে। চোখের জল বলতে বা শুনতে যত ভালো লাগে, চোখের পানি বলতে আর শুনতে কি আর তত ভালো লাগে ? তা শুনে কেউ কোনওদিন শাসন করেছে, মনে পড়ে না। কিন্তু এখন শুনি, জল নাকি বলা ঠিক না, জল নাকি হিন্দুরা বলে। চোখের সামনে এখন এমন ঘটনাও ঘটেছে আমার আর এই চোখ তাও তো সয়েছে। কিন্তু আমিই বা শাসন করব কোন অধিকারে ? ছেলেমেয়েরা আমার শরীর থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তারা কি আর আমার ? খোদা চেয়েছে, তাই বেরিয়ে এসেছে আমার শরীর বেয়ে। শরীরে আমার যত লোভই থাক, মনে আমার যত চাওয়াই থাক, খোদা না চাইলে কি হতো তারা ? খুব করে চেয়েছিলাম তো বড়টাকে―খু-উ-ব করে। তা হলো বটে, কিন্তু থাকল না তো। চলে গেল। এই পৃথিবীতে মানুষের আসলে কত যে রিক্ত লাগে, নিঃস্ব লাগে, জীবনটাকে কত যে অর্থহীন মনে হয়, তা বোঝা যায় কেবল সন্তান চলে গেলে। জীবনের শুরুতেই খোদা আমাকে সেটাই বুঝিয়ে দিল। বাঁচল না,―চার না পাঁচ মাসের বেশি তো টিকল না পৃথিবীতে ও। এখন যখন আমার এত কাছের আত্মীয়স্বজনরাও আমার ছেলেমেয়ের সংখ্যা গোনে, ওকে বাদ দিয়ে হিসেব করে, তারপর ওই যে পুকুরে ডুবে চলে গেল পাঁচ বছরের হীরা, ওকেও তো বাদ দেয়। আমার মন কেমন গুমরে ওঠে, মনে মনে কই, ওদের গুনলে না ? ওরা তোমাদের ভাই ছিল না ? এই পৃথিবীর আলোবাতাসে বাড়ল না বলে ওদের কথা তোমাদের মনে থাকে না ? তা তোমাদেরই বা দোষ দেই কী করে ? আমি নিজেও তো ওদের হিসাবে ধরি না। শুধু কোনও কোনও দিন নামাজ পড়তে বসে হঠাৎ করে ওদের কথা মনে পড়ে যায়। চোখ বুজে খোদার কাছে কাঁদি আর বোঝার চেষ্টা করি, কেন সে আমাকে এই পৃথিবীর এত হাসি এত গানের মধ্যে রেখে ওদের নিয়ে গেল কোন সে আন্ধার জগতে!
নাহ্ … কী যেন বলছিলাম! এই যে আবারও খেই হারিয়ে ফেলেছি। … জল, জলের কথা বলছিলাম। তা বলব না কেন ? তুমি যে পানি বলো, তা কি কখনও আমার কানে লেগেছে ? মাথার মধ্যে চেপে রাখা এই ঘটনাটা কেন যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আমার ছেলে প্রান্তের সামনে। তা শুনে সে হই হই করে উঠল, ‘কে বলেছে মা ? কে বলেছে ?’
তা আমি কি আর অতই বোকা যে ওর কাছে নাম-ধাম বলতে যাব ? সংসারে আগুন জ্বালিয়ে আমার লাভ আছে কোনও ? যে বয়সে মানুষ আগুন জ্বালায়, সে বয়সেই ডুব মেরে থাকলাম পানির ভেতর, আর এখন একটা আস্ত পা-ই যখন কবরের মধ্যে চলে গেছে, আরেকটা যাই যাই করছে, তখন যাব আগুন জ্বালাতে ? আমার নিজের ধর্মেই দেখি একানব্বই নাকি সাতানব্বই তরিকা, সেখানে আমার এই সংসারে যদি দুই তিন তরিকার মানুষ থাকে, সমস্যা কি ? তবে কষ্ট তো লাগবেই। সারাটা জীবন গেল, কতজনকে কত কিছু শিখালাম―আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম, কিছু শিখাতে পারি নাই… কিন্তু মানুষ তো দেখে দেখেও শেখে। আমি কবে কাকে শিখিয়িছে, জল বলা যাবে না ?
এই জীবনে দুটি ব্যাপার আমি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছি। একটা হলো, খোদার ওপর ভরসা রেখেছি। আরেকটা হলো, মানুষের ওপর বিশ^াস রেখেছি। হ্যাঁ, খোদার ওপর ভরসা রেখেছি আর মানুষের ওপর বিশ^াস রেখেছি। ঠকেছি, বুঝতে পেরেছি আমার ভরসা আর বিশ^াসে গলদ আছে, বুক ভেঙে গেছে, কিন্তু ভরসা রেখেছি, বিশ^াস রেখেছি। আমি তো বিজ্ঞানী না, আবিষ্কারকও না। কোথাও না কোথাও আমাকে তো সান্ত্বনা পেতে হবে। সান্ত্বনাহীন একটা জীবন নিয়ে আমি কী করব ? অশান্তি ছাড়া আর কিছু কি ডেকে আনতে পারব এই পৃথিবীতে ? তারচেয়ে ভরসা করা ভালো, বিশ^াস করাই ভালো। সেই ছোটবেলায়, মাত্র বছর বারোতেই আমার যেদিন বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, কী ভীষণ অনিশ্চয়তায় কী ভীষণ কান্নাই না জুড়েছিলাম মায়ের কাছে। মাও কি কেঁদেছিল ? চোখে অবশ্য জল দেখি নাই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি একটুও কাঁদে নাই ? না, সেই কথাটা কোনওদিন জানা হয় নাই, জিজ্ঞেসও করা হয় নাই। আমাকে শুধু এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল, কাঁদিস না আহ্লাদী। কান্নার কী আছে ? কেন, তোর বড় বোনকে দেখছিস না ? সে কি কষ্টে আছে ? খারাপ আছে ?
মনে মনে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, না, কষ্টে তো নাই বড় বুবু। কিন্তু সবার জীবনই কি আর একজনের মতো ?
এখন, ছেলেদের কেউ কেউ, নাতি-নাতনিদের কেউ কেউ জানতে চায়, জীবন আমার কেমন কেটেছে! কী অদ্ভুত কথা, কী অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি বলতে চাই, জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে নাই, এক জীবনের সঙ্গে আরেকটা জীবনের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করতে নাই। ঠিকঠাক বুঝেছি কি না, ঠিক জানি না, কিন্তু আমি এটুকু বুঝেছি, মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে ভালোবাসার দরকার হয়, মানুষের জীবনে ভালোবাসা থাকতে হয়, কিন্তু তারও চেয়ে বেশি দরকার স্নেহের, তারও চেয়ে বেশি দরকার দায়িত্ববোধের। মানুষ যে ভালোবাসার কাঙাল, এ তো জানা কথাই; কিন্তু কাঙাল বলেই সে অবুঝের মতো কখনও কখনও এত বেশি কাঙাল হয়ে পড়ে যে, টের পায় না, তার মনে একটুও স্নেহ নাই, তার মধ্যে একটুও দায়িত্ববোধ নাই। সে খালি অভিযোগ করতে শেখে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না―তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তোমাকে আমি এত ভালোবাসি, তোমাকে আমি কী-ই না দিয়েছি, তোমার জন্যে আমি কী-ই না করেছি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসা না! এসব নিয়ে কী আর বলব, এসব নিয়ে কোনও কিছু বলতে আমার ভালো লাগে না। ভালো লাগবেই বা কেন ?―এই যে প্রেম, বিয়ে―আমরা তো আর কোনওদিন ওসব করি নাই, করার মানসিকতা ছিল না, সুযোগও ছিল না তখন। কেউ কেউ বলে, সুযোগের অভাবে ভালো থেকেছি; তা হতেও পারে, আবার নাও তো হতে পারে। সব ডিম কিন্তু একটা ঝুড়ির মধ্যে রাখতে খোদাতায়ালাই পছন্দ করে না। তা যা-ই হোক, সোজা কথা, আমরা তো আর প্রেম বিয়ে করা জানতাম না, জানার চেষ্টাও করি নাই, জানার দরকারও হয় নাই; কিন্তু এখন যারা জানে, জানে বলেই তারা নিশ্চয়ই অমন করে অভিযোগ করতে পারে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না―তুমি আমাকে ভালোবাসো না। কিন্তু তারাই আবার বলে, ভালোবাসতে হয় না কি কোনও কিছুর আশা না করে। খুবই ভালো কথা, কিন্তু কেবল ওইটুকুই যথেষ্ট না রে মালেকা,―ভালোবাসার সঙ্গে স্নেহ আর দায়িত্বও থাকতে হয়। মানুষ ভালোবাসাকে ভুলতে পারে, কিন্তু যে স্নেহ আর পরিচর্যা পায়, সেটা কখনওই ভুলতে পারে না। ভালোবাসা হারানোর পর মানুষ যে কান্না কেঁদে ফেরে, তাও আসলে ওই স্নেহ আর পরিচর্যা হারানোর কারণে কাঁদে।
তা তোমরা এখন বলতে পারো, আপনারা তো আর প্রেম-বিয়ের যুগের মানুষ না, আপনাদের বিয়ে দেওয়া হতো ধরে-বেঁধে, গলায় গামছা দিয়ে; আপনারা এইসব নিয়ে যা বলেন, তা আমরা মানতে যাব কেন ? তা সেটা বলতেই পারো। আমার আর কী বলার আছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, ভালোবাসা না থাকলে কি আর এত কষ্ট গিলে ফেলতে পারতাম ? পারতাম কষ্ট গিলে ফেলে দিনরাত এতসব কাজকর্ম করতে ? ভালোবাসা মানে বুঝতে পারার চেষ্ট করাও। যাকে ভালোবাসি সে কী চায় তা বুঝতে শেখা। এই যে তোমরা বলো, একেবারে সোজা ছাদনাতলায় গিয়ে বসা―এইটার কোনও মানে হয় ? হয়। দুজনে যদি দুজনকে বোঝার চেষ্টা করে, তা হলে ঠিকই হয়। আর যদি চেষ্টা না করে, তা হলে চেনা থাকলেই কী আর না থাকলেই কী। ভালোবাসার গল্প আমার কাছে করতে এসো না। ও আমি ভালো করেই জানি।
মাঝখানে নদী, তাও একটা দুইটা না। ইছামতি নদী, বড়াল নদ, হুরাসাগর আর করতোয়া। নদী আছে, নদ আছে, সাগরও আছে―কিন্তু সবগুলোই আবার নদী। কেমন মজার ব্যাপার না ? এত সব নদী পেরিয়ে সেই মৈত্রবাধা থেকে এই সলপ গাঁয়ে কী করে এলাম তবে! মাঝখানে এত যে নদী, তখন কিন্তু এত হিসাব করে দেখি নাই। নৌকা না হয় লঞ্চে যাচ্ছি, আবার ট্রেনে উঠছি, বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি―এই সব যে আসলে কত বড় বড় প্রাপ্তি ছিল, তা বলে বোঝাতে পারব না। বিয়ের আগে, সেই কবে কোনওকালে বড় বুবু আর দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমি কিন্তু কলকাতা গিয়েছিলাম লঞ্চ আর ট্রেনে করে। ফিরেছিলাম বাবার সঙ্গে―পুরো রাস্তাই তার সওদাগরি নৌকায়। চিন্তা করা যায়! আর আমার বিয়ে ঠিক হলো কি না সলপের রামগাঁতী গাঁয়ে―যেখানে কোনও নদী নাই, বিলঝিলও নাই। বিলঝিল নাই, সে কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। তা ছাড়া তখনও কৃষকগঞ্জ বাজারের কাছ দিয়ে একটু এগিয়ে যে সগুনা আছে, সেখানকার নদীটা মানে ওই হুরাসাগরটা এরকম মরে নাই। আবার সোনতলার নদীঘাটে নেমে―মানে করতোয়া নদীর যে একটা শাখানদী আছে―ফুলজোড়―সেই ফুলজোড় পেরিয়ে গরুর গাড়ি না হয় পালকিতে করে আসাযাওয়া করত পয়সাপাতি থাকা মানুষজন। ইছামতি দিয়ে লঞ্চে করে আমরা যেতাম বেড়া থেকে ভাঙ্গুরায়। সেই ভাঙ্গুরা থেকে উঠতাম ট্রেনে। তারপর কী কী যেন সব স্টেশন,―বড়াল ব্রিজ, দিলপাশার, শরৎনগর, মোহনপুর, উল্লাপাড়া―এইসব পেরিয়ে নামতাম সলপে। তখনও হিন্দু জমিদারদের মধ্যে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে নাই। তাই সলপ স্টেশনের দাপটও কমে নাই―এমন কোনও ট্রেন ছিল না, যেটা সলপে থামত না। তারপর তো হিন্দু জমিদাররা চলে গেল, সলপের দামও কমে গেল। সব ট্রেন আর সলপে থামত না। অতএব আমরা নামতাম সলপের আগের স্টেশন উল্লাপাড়া জংশনটায়। সেখান থেকে ওই যে পালকি না হয় গরুর গাড়ি, না হয় মহিষের গাড়ি! পুরুষ মানুষরা তো হেঁটে হেঁটেই আসাযাওয়া করত। পূর্ণিমাগাঁতী থেকে নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে সোনতলায় নেমে আমরা আবারও পালকিতে উঠতাম। আমার স্বামী ছিল রাশভারী মানুষ, কিন্তু ভারী চুপচাপ। তার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হলো, সেও তো কত কাহিনি! এখন কি আর অত শত মনে আছে!
তবু কখনও কখনও মনে পড়ে যায়, কিংবা এ-ও বলা যায়, মনে করার চেষ্টা করি। ভাতঘুমের মতো এই ঘুমটা যদি কেটে যায়, অথচ চোখ দুটো খুলতে আর ইচ্ছে করে না, তখন কোনও কিছু মনে করার চেষ্টা ছাড়া আর কি-ইবা করতে পারি আমি! ছেলেমেয়েদের মতো অত পড়াশোনা তো আর শিখতে পারি নাই। আবার যেটুকু শিখেছি, সেটাই বা আর কাজে লাগাতে পারলাম কই। আমার মায়ের ছিল লেখাপড়ার স্বভাব। কতদূর পড়েছিল, তা অবশ্য মনে নাই। তবে হবে, ওই আর কি, ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন …। এই তো অনেক তখন। তা জেনে আমার বাবা-দাদায় আবার স্কুল করে দিয়েছিল কাচারিবাড়িতে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আসত, বর্ণ চিনত, লিখতে শিখত, পড়তে শিখত। বাংলা যতটুকু না শেখে, তারও বেশি শেখে কোরআন পড়া। তবু শেখে তো! লেখাপড়ার ওপর একটু মায়া জন্মায় তো! আমিও শিখেছিলাম খানিকটা। ১০ বছর বয়সে সংসারে এলাম। তাহলে মাকে আর মনে থাকে কী করে! তার ওপর সেই শাশুড়ি যদি হয় দু দুবারের স্বামীহারা মেয়ে আর কোনও মৃত মেয়ের মা! আর সেই শাশুড়িও যদি হয় মায়ের মতো লেখাপড়ার ধাত থাকা মানুষ। দেখি, তাকেও আমার দাদাশ্বশুর একটা স্কুল করে দিয়েছে বাড়ির কাছে।
ঘটনা হলো, আমার নানির বাড়ি ছিল বেলতলি। আমার মা আর শাশুড়ি ছিল আবার আপন খালাতো বোন। মায়ের নামের চেয়ে তার সেই খালাতো বোন মানে আমার শাশুড়ি মার নামই এখন স্পষ্ট মনে ভাসে। জরিনা, তার নাম ছিল জরিনা। তাকে আমার খালাম্মা বলার সুযোগ কোনওদিনই হয় নাই। বিয়ের পরে তাকে প্রথম দেখলাম শ^শুরবাড়ি গিয়ে―যখন কি না আর খালাম্মা বলে ডাকার সুযোগ নাই, মা বলেই ডাকতে হলো তাকে। আমার এই শাশুড়ির জীবনের শুরু ভয়ানক কষ্ট দিয়ে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো―আমার বিশ^াস, আমার ওপর তিনি খুশিই ছিলেন। খুশি হবেন না কেন ? জন্মের কয়েক মাস যেতে না যেতেই তার নিজের মেয়ে মারা গিয়েছিল, তারপর শাশুড়ির পেটে এল আমার স্বামী, কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসার আগেই বিদায় নিলেন আমার শ^শুর। আর তখন আবারও জানা গেল, কপালে তার আরও দুঃখ আছে। শাশুড়ি মায়ের প্রথম বিয়ে হয়েছিল আমার জ্যাঠা শ^শুরের সঙ্গে। লোকে বলে, শরীর থেকে তার নাকি সোনা ঝরত, গায়ের রঙ এমনই সুন্দর ছিল তার। উঁচু, লম্বা মানুষ―পেটালো শরীর, দৈনিক সকালে ঘোড়াটাকে নয় মাইল ছুটিয়ে না আনতে পারলে তার নাকি সারা দিন আর ভালোই লাগত না। আমার নিজের মায়ের কাছে শুনেছি, ঘোড়া চালিয়ে কোনও কোনওদিন সোজা চলে যেতেন বেলতলিতে। আমার মা তো আমার শাশুড়ি আম্মার শুধু খালাতো বোন না, সখিও ছিল; বউয়ের মন যাতে ভালো থাকে, সেজন্যে মাকে ঘোড়ার পেছনে করে বাড়ি নিয়ে আসতেন। শ্যালিকাকে এইভাবে নিয়ে আসত, কোনও কোনও সময় আমার নানিকেও নিয়ে আসত তার সঙ্গে। তখন নিয়ে আসত পালকিতে করে। প্রায় প্রত্যেক মাসেই এরকম ঘটনা ঘটত। এই বাড়িতে যে ওই ব্রিটিশ আমলে লাইব্রেরি হলো, সে তো তার ইচ্ছাতেই। বিক্রম চৌধুরী―লোকে তাকে ডাকত বিক্রম চৌধুরী নামে। কিন্তু একদিন বলা নাই কওয়া নাই, শরীরটা তার নাকি শুলাতে লাগল। শুয়ে থাকতে পারে না, আবার দাঁড়াতেও পারে না। বসতে গেলে বসতে পারে না, কিন্তু উঠতেও পারে না আর সোজা হয়ে। গা দিয়ে নাকি দাউ দাউ আগুনের তাপ বেরুচ্ছিল। এইসব অন্য কারও মুখে শুনি নাই। মরার পর বিক্রম চৌধুরীর নাম নাকি কেউ আর মুখেই আনত না; মানে লোকটাকে মনে না করে, মানুষটার নাম মুখে না এনে কষ্ট আরও না বাড়ানোর চেষ্টা করত―এই আর কি। তবে আমার শ^াশুড়ি মাই চুপে চুপে এইসব বলেছিল আমাকে, কেন বলেছিল, সেই তা জানে। আশপাশে যখন কেউ থাকত না, ঘরদোরের বেড়া-জানালারও যখন কান দুটি ঠসা হয়ে যেত, তখন কখনও সখনও তিনি আমার কাছে বলতেন বিক্রম চৌধুরীর কথা। যে মানুষ তোমার স্মৃতির ভাগীদার, তাকে কি ভুলে যাওয়া এতই সহজ ? তার ওপর তাঁকে নিয়ে যদি কোনও কিছু বলার মতো অবস্থা না থাকে ? কিন্তু আমার শ^াশুড়ি মা তাঁর কথা বলার চেষ্টা করতেন, অন্তত আমার কাছে। অনুমান করি, যে অতীত তাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছিল, তিনি তাঁকে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসাই করতেন। আর সে প্রশংসাতেও কোনও ব্যক্তিগত মোহ জড়িয়ে আছে বলে মনে হতো না। প্রশংসার স্বরে তিনি কেবল এরকম বলতেন, ‘তাঁর মৃত্যুতে এ বংশের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। তিনি যদি অন্তত স্বাভাবিক বয়সটুকুও বেঁচে যেতে পারতেন, এই বংশটা আরও অনেক মর্যাদাবান হতো। আরও পাঁচ-সাত পুরুষ পরেও এ বংশের সুনাম শোনা যেত।’
‘কেন মা,―সুনাম তো এখনও আছে। আর আপনাদের ছেলেমেয়েদেরও তো এখনও কোনও দুর্নাম হয় নাই। পাঁচ-সাত পুরুষ পরেও সুনাম নিশ্চয়ই থাকবে।’
শাশুড়ি আম্মা চুপ করে থাকতেন। নীরবতাটুকু একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা যেত, ‘না। থাকবে না মনে হয়। বংশের সুনাম তো কেবল তোমার আয়-উন্নতির ওপর নির্ভর করে না, ভালো চাকরি-বাকরি আর কারও ভালো ছাত্রছাত্রী হওয়ার ওপরও নির্ভর করে না মা। বংশের সুনাম টিকে থাকে ছেলেমেয়েদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মায়ার টানের ওপর। বন্ধনের ওপর। এইখানে সেই বন্ধন আলগা হতে শুরু করেছে। দেখো না, এখন এক ভায়ের সুনাম হলে আরেক ভাই তা সহ্য করতে পারে না ? কেন পারে না ? টান নাই বলে, বন্ধন নাই বলে। এইভাবে যত সুনামই হোক, বংশ টেকে না।’
শুনে আমি কেঁপে উঠেছি। মনের কোথায় যেন সর্বনাশের বাঁশি বাজতে নিয়েও বাজছে না, বেজে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে―এ কেমন কথা শোনায় শাশুড়ি মা! আমিই কি তাহলে কোনও অনিষ্টের কারণ হয়ে এসেছি এই বাড়িতে! আমার মনের কথা কী করে যে বুঝত শাশুড়ি মায়ে! পাটার ওপর কয়েকটা আদা রেখে ছেঁচতে ছেঁচতে বলেছিল, ‘এই বাড়িতে তুমি ছাড়াও কিন্তু আরও পাঁচ বউ আছে বউমা। তোমার এক চাচাশ^শুরের দুই বউমা, আরেক চাচাশ^শুরের তিন বউমা। তোমার তো নিজের শ^শুরের মুখটা দেখা হলো না। তুমি আর কী জানবে!’
এইসব অবশ্য বেশ পরের ঘটনা। আমার বড় ছেলে তখন বেশ ঝরঝরা হয়ে উঠেছে। বড় মেয়েটাও। বিক্রম চৌধুরীর কথা হঠাৎ করেই তুলেছিলেন, তিনি নিজেই। দাদাশ^শুর নাকি তার চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভরসা রেখেছিলেন তার ওপরে। বাবার তৃতীয় সন্তান, কিন্তু ওই যে বললাম, চলে গেলেন। আগেকার মানুষজনের শরীরস্বাস্থ্য যত ভালোই থাক, কেন যেন পট করে চলে যেত, কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই। তিনি চলে যাওয়ায় মুশকিল হলো এই যে, জরিনা বেগম বিধবা হয়ে গেলেন। তখনও ছেলেমেয়ে হয়নি, এরই মধ্যে এই ঘটনা! লোকজন আড়ালে আবডালে কী যে বলাবলি করত, সে কথা তারাই জানে; কিন্তু হাজি সাহেব, মানে আমার দাদাশ^শুর, তিনি কিন্তু ছিলেন একেবারে অন্য ধাঁচের। ছেলের চল্লিশা হয়ে গেল, জরিনা বেগম প্রস্তুতি নিলেন কল্যাণপুরে তাঁর বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ার। সেদিন লোকজনও এল শ^শুরবাড়ি থেকে। এলেন ডাক্তার সাহেব―আমার শ^াশুড়ি মায়ের আপন ভাই ডা. দবিরউদ্দিন আহমদ। খুব সুনাম ছিল তাঁর আশপাশের গ্রামেগঞ্জে। হাজি সাহেব তার দোতলা কাছারিঘরের নিচের তলার বারান্দায় বসে গড়গড়ি টানতে টানতে দবিরউদ্দিনকে বললেন, ‘বসো দবির। তুমি ব্যস্ত মানুষ, সময় করে আসছো, খুব খুশি হলাম। তো বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?’
‘জ্বি চাচা। দেখা হয়েছে। আমরা দুপুরের পরই বের হই, নাকি বলেন ?’
‘আসছো,―থাকো কয়েক দিন। তোমরা চলে গেলেও তোমার বোনের মনটা ভালো থাকবে।’
‘আমরা কিন্তু জরিনাকে নিয়ে যেতেই এসেছি চাচা।’
দবিরউদ্দিন কথা শেষ করতে পারেননি, তার আগেই বলেছেন হাজি সাহেব, ‘কিন্তু তোমার বোনকে তো আমি এভাবে যেতে দিতে পারি না দবির।’
‘ক্যান চাচা, সমস্যা তো নাই। বয়স এখনও কম আছে। আমাদের ধর্মেও তো আর বসন্ত দাদাদের মতো ওরকম বিধিনিষেধ নাই―’
‘কিন্তু দবির, তোমার বোনকে আমি এ বাড়ির মেয়ে করে নিয়ে এসেছি। তাকে আবার আমি কী করে বের করে দেই বলো ?’
‘বের তো করে দিচ্ছেন না চাচা। আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি। ওর সামনে তো সারাটা জীবন পড়ে আছে। সেটাও তো দেখতে হবে।’
‘সেজন্যেই তো বলছি, নিজের মেয়ে করে ওকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছি। ওকে দেখার দায়িত্ব কি আমার না ?’
অতএব আমার শাশুড়ি জরিনা বেগমের আর বাবার বাড়ি ফেরা হলো না। অবশ্য বাড়িতে গিয়েছিলেন; তবে আবারও কনে সাজতে। হাজি সাহেব তাঁকে আবারও ঘরে নিয়ে আসলেন নিজের ছোট ছেলের বধূ করে। এই যে এতদিনের ঘরসংসার আমার, একবারই বাপের বাড়িতে ফিরতে দেখেছি আমার শাশুড়ি মাকে―সেই মুক্তিযুদ্ধের বছরে, এই গাঁয়ে রক্তারক্তি শুরু হওয়ার পরে। তাঁকে খালাম্মা বলতে না পারি, দবিরউদ্দিনকে কিন্তু আমি সেই ছোটকাল থেকেই মামা বলে জেনেছি। তাঁর নাকি খুব ইচ্ছা ছিল আমার আব্বার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক করার। কিন্তু মৈত্রবাধায় তাদের যাতায়াতই ছিল কম। তাছাড়া মানুষের চোখ কখন কোনখানে আটকায়, তার কি কোনও ঠিকঠিকানা আছে ? ঢাকায় যেতেন মাঝেমধ্যে, সেখানে আমাদের আত্মীয়স্বজনের ভিতরেই একজনের মেয়েকে দেখে তার সঙ্গে নিজের ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরে যখন দেখলেন, তার বোন মানে আমার শাশুড়ি মা নিজের ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজছে, তখন এই মামাই নাকি তাকে আমার সন্ধান দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘তোমার সই যত শিক্ষিত, যত ভদ্র, যত গুণী―তো তার মেয়েটাকেই নিয়ে আসো না ছেলের বউ হিসেবে!’
ঘটনা এইটুকুই, এই শান্ত ফুলজোড় নদীটার মতো; কিন্তু নদীর স্রোতের মতো ঘটনার স্রোতও তো থেমে থাকে না। শ^াস ভারী হয়ে আসে, তবু মনে হতেই থাকে, হতেই থাকে। আমার মায়ের তো আপন কোনও ভাই ছিল না। এই সইয়ের ভাই-ই তার ভাইয়ের মতো। এইভাবে আমারও একটা মামা হয়েছিল লতায়-পাতায়। খালি মামা কেন, লতায়-পাতায় আরেকটা ভাইও হয়েছিল। তার বাড়ি যে কোনখানে, তা আর বলতে পারব না। সে আছেই বা কোনখানে, তাও বলতে পারব না। মারা গেছে কি না, তাও জানি না। কলকাতা থেকে ব্যবসার কাজে এসেছিল। তার পর কী যে অসুখে পড়ল! মনে হয় বাঁচবেই না। কিন্তু তিন-চার মাস ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে উঠল, আব্বাকে ধর্ম বাপ করে নিল, মা হলো তার ধর্ম মা। সেই ভাইয়ের কথাও মনে হয় মাঝেমধ্যে। মাঝেমধ্যে বিয়ের দিনটিও একেবারে ঝকঝকে ফটোর মতো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কাঠফাটা গরমের দিন তখন। এইটুকু বুঝতে পারলাম, আমাকে দেখতে এসেছে বোধহয়। ছোট হলে কী হবে, আগেও দেখেছি না গ্রামে ? লোকজন আসছে, রান্নাবান্না হচ্ছে, মেয়েকে সাজানো হচ্ছে। আমাদের বাড়িতেও সেদিন কেমন সাজ-সাজ রব পড়েছিল। তাদের আসতে আসতে সন্ধ্যা নেমে এল। ২৪ মাইল―টানা ২৪ মাইল হেঁটে আমার স্বামী এল আমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে। নৌকা করেও আসা যেত। বিয়ের পর তো আমি সেভাবেই গিয়েছিলাম, একেবারে বজরা নাওয়ে করে। কিন্তু এরা কেন যে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিল, সেটা জানি না। মনে হয় নৌকায় চড়তে ভয় পেয়েছিল। নাকি নদীতে ঝড়বাদলার ভয় করেছিল ? কে জানে! অবশ্য মাঝখানে দুইবার থেমেছিল। একবার শাহজাদপুরে―ভূত সাহেবের বাড়িতে―মানে আবদুল কাদেরের বাড়িতে। সেখানে খেয়েদেয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে থেমেছে রতনকান্দিতে মাঙন সরকারের বাড়ি। এরা খুব বংশীয় লোক, পুরানা দিনের ধনী। সেখানে হালকা নাস্তা করে, পানি খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে বেড়ায় আমাদের বাড়িতে। বরযাত্রীদের কেউ কেউ নাকি বক বক করছিল, কত দূরে রে বাপু ? এইরকম কষ্ট করে ২৪ মাইল হেঁটে কেউ বিয়েশাদি করে নাকি ? সন্ধ্যার সময় বাপজান কিছুতেই আমাকে দেখাতে দিল না। বাপজান কোত্থেকে বিরাট এক চিতল মাছ কিনে নিয়ে এল। সেটা রান্না করা হলো। আমি অবশ্য ঘুমায়ে পড়েছিলাম। কখন মাছ কেটেছে, কখন লোকজন খেয়েছে, কখন তারা ঘুমাতে গেছে, কিছুই আমার জানা হয় না। বরযাত্রীরা রাতে থাকল, সকালে থাকল। দুপুর হওয়ার আগেই মা আমাকে সাজিয়ে তাদের সামনে নিয়ে গেলেন। কীভাবে সাজিয়েছিলেন, সেসব আর কিচ্ছু মনে নাই। আমাকে অবশ্য হাঁটাহাঁটি করায় নাই, চুল খুলেও দেখাতে হয় নাই। তবে একটা কবিতা পড়তে দিয়েছিল। পাত্রপক্ষই দিয়েছিল। কী কবিতা, সেটাও আর ভালো করে মনে নাই। অত কিছু কি আর সারাটা জীবন মনে থাকে ?
অবশ্য এর আগেও আমাকে এক পাত্রপক্ষ দেখে গিয়েছিল। মানুষজনকে প্রায়ই বলাবলি করতে দেখি, অমুকের মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখে গেল, পাত্রপক্ষের লোকজন নাকি খুবই খুস্টা―অভব্য; চুল টেনে দেখে, দাঁত নাড়িয়ে দেখে, হাঁটাহাঁটি করায়ে দেখে―তো আমাকে কিন্তু যে দুই-তিনবার পাত্রপক্ষ দেখেছিল, সে সময়ে কিন্তু সেরকম ঘটে নাই। লোকজন বলাবলি করত, মনসুর আলী দেখেশুনেই পাত্র নিয়ে এসেছিল তার মেয়েকে দেখানোর জন্যে; ঘটনা কিন্তু সেরকমও না। অনেক সময় ঠ্যাকায় পড়েও মেয়েকে দেখাতে হতো। একবারের কথা বলি, বাবার কোনও ইচ্ছাই ছিল না সেইখানে আমাকে বিয়ে দেওয়ার। পাত্র ছিল ধনাঢ্য, তাদের ঘরের ঝি-বউদের নাকি রান্নাবান্নাও করতে হতো না। ছেলেরা যত লাট-বাহাদুরই হোক না কেন, তাদের কিন্তু কোনও না কোনও কাজ করতেই হয়। মদ-নেশা করার জন্যেও কিন্তু কষ্ট করে খুঁজে-পেতে ভালো জায়গা করে নিতে হয়। কিন্তু সামাজিকতা আছে না ? শরিকান্তরের লোকজন মনে হয় একেবারে পঙ্গপালের মতো তাঁকে ঠেসে ধরল, দেখাতেই হবে―দেখাতেই হবে। কী বিশ্রী ব্যাপার! ধরো, তাদের পছন্দ হয়ে গেল! তখন কী হবে ? তিনি তাই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার এক চাচাতো চাচার কাছে বাবা মনে হয় কোনও কারণে জব্দ ছিলেন। তাই তাকে রাজি হতে হয়েছিল, মেয়ে দেখাবেন। তবে শর্ত দিয়েছিলেন, ছেলে দেখে পছন্দ না হলে কিছুতেই বিয়ে দেবেন না। তাই সই। পাত্রপক্ষ যেদিন এল, আমাদের বাড়ির মধ্যে ছিল একটা শানবাঁধানো ইঁদারা, আমাকে সেটার কিনারে বসায়ে তিনি তার আগের দিন একটা কবিতা মুখস্থ করালেন। খালি তিনি না, তার সঙ্গে কিন্তু আমার খালাম্মার মানে আমার শাশুড়ি আম্মার ভাইও ছিল সেদিন। মা তাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসছিল―কী জানি, পাত্রপক্ষ সত্যিই যদি গোঁ ধরে বসে, বিয়ে আজকেই করে নিয়ে যাবে! তখন যাতে মামা কোনও না কোনও ভাবে বিয়েভাঙানি দিতে পারে, সেইজন্যে নিয়ে আসছিল তাকে। আমাকে যে ওই পরিবারে বিয়ে দিতে চাইছিল না, তার কারণ, সেই পাত্রের টাকাপয়সা থাকলে কী হবে―লেখাপড়া ছিল না। পড়তে পারত না, লিখতে পারত না। তো বাবা আর মামা মিলে আমাকে একটা কবিতা শিখালো―মন দিয়া কর বসে বিদ্যা উপার্জন/ সকল ধনের শর বিদ্যা মহাধন/এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে/যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে/জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার/ কখনও ঘোচে না তার ঘন অন্ধকার/ রীতিমতো শিক্ষা করি যে হয় পণ্ডিত/ বহুবিধ গুণে তার মানসমন্দির,/ বিদ্যা বলে নরজন সবার প্রধান/ বিদ্যাহীন মানুষ হয় পশুর সমান।’ আমাকে দিয়ে এই কবিতা মুখস্থ করালো। পাত্রপক্ষের লোকজন এলে দু-এক কথা হতে না হতে মামাই আগ বাড়িয়ে বলল, ‘আহ্লাদী মা, শোনাও তো একটা কবিতা শুনাও তো…’। তো আমি সেই কবিতাটা মুখস্থ বললাম। সেই কবিতা পড়ার পর, কী দিয়ে কী হলো আমি কি আর অত বুঝি ? মা, নানিদের কাছ থেকে শুনেছি, পাত্র আর পাত্রের বাবার চোখ-মুখ নাকি কালো হয়ে গিয়েছিল। তা হবে না ? তারা এসেছে টাকাপয়সার দেমাগ দেখাতে, আর তাদের কি না শুনতে হলো এই কবিতা!
আমার জরিনা খালাম্মার ছেলে যে আমাকে বিয়ে করতে আসল, সেদিনও মা আমাকে কবিতা পড়তে বলেছিল। কী কবিতা সেটা আর মনে নাই। হতে পারে সুনির্মল বসুর, হতে পারে খগেন্দ্রনাথ দত্তের―তখন তো আমরা ওই সবই পড়েছি। হারাধনের ছড়া পড়ে কত যে কান্নাকাটি করেছি। শাহজাদপুরের মধ্যবাংলা স্কুল একটা বৃত্তি দিত তখন। আমার মা ছিল সেই বৃত্তি পাওয়া মেয়ে। মেয়েদের তখন আলাদা কোনও স্কুল ছিল না। বেলতৈল স্কুলের খুব নাম ছিল সেই সময়। মা আর আরও দশজন মেয়ে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিল সেই স্কুলটাতে। স্কুলে যায় নাই, স্কুলের খাতায় নাম লেখা ছিল আর কি। তবে লেখাপড়া বাড়িতেই করত। কোনও কোনওদিন মাস্টার এসে এটাসেটা বুঝিয়ে দিয়ে যেত। মায়েরা ১১ জন একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল, বৃত্তি পরীক্ষা দিতে তাদের যেতে হয়েছিল শাহজাদপুরের সেই মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে। ১১টা মেয়ে এগারো খানে বিয়ে হয়ে ছত্রখান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার আগে একসঙ্গে একটা স্বপ্নের জাল বুনেছিল, বিয়ে হয়ে যেখানেই যাক না কেন, সেইখানকার মেয়েদের জন্যে স্কুল খুলবে তারা শ^শুরবাড়িতেই।
সেই ১১ জনের কার যে কখন, কার যে কোনখানে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কে তা জানে! কে জানে, তারা আর স্কুল দিতে পেরেছিল কি না মেয়েদের জন্যে। তবে আমার মা সুফিয়া খাতুন কিন্তু ঠিকই একটা স্কুল খুলেছিল। আব্বা তাতে না করে নাই। কলকাতায় যাতায়াত ছিল তো―এর ওর সঙ্গে মেলামেশা ছিল, পাকেচক্রে কত জায়গায় কতভাবে দিনরাত কাটাতে হতো, তাঁর তাই জানা ছিল, দুনিয়াটা অনেক বড়, তবে যত বড়ই হোক না কেন, মানুষকেও এই পৃথিবীর মতোই বড় হওয়ার জন্যে পাল্লা দিতে হয়। না হলে দিনকে দিন সে কেবল ছোটই হতে থাকে, যত ছোট হতে থাকে মনের সুখও তার ততই কমে আসে। বাবা বুঝতে পেরেছিল, মেয়েদের লেখাপড়ায় কেবল লাভই আছে, একটুও ক্ষতি নাই। পুরুষ মানুষদের তখন রাজ্যের কাজকর্ম দেখতে হতো, এখনকার মতো এত রাস্তাঘাটও তো ছিল না তখন, যানবাহনও ছিল না তেমন। তার ওপর এই জলডোবা আর নদীনালার দেশ! ব্যবসা-বাণিজ্য, খেতখোলা আর অফিস-আদালতের কাজকর্ম তাই পুরুষদেরই করতে হতো। সেই পুরুষের তখন অত সময় কোনখানে যে বাড়ির চার-পাঁচটা পোলাপানকে সার ধরে বসায়ে সকাল-সন্ধ্যা লেখাপড়া শেখাবে, শেখাবে―‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি ?’ তাহলে ব্যাপার কী দাঁড়াচ্ছে ? মেয়েদের লেখাপড়াতেই লাভ বেশি না ? মায়ের চারপাশে ২৪ ঘণ্টাই তো ঘুরপাক খায় পোলাপান। আমাকে বিয়ে করতে আসছিল যে―পাবনার বিরাট সোনাগয়নার ব্যবসায়ী সে। আবার চিমনির কারখানাও নাকি ছিল একটা। তারও মনে হয়, ওইরকম একটা ধারণা ছিল। কিন্তু কবিতাটা শুনে তারা এমন চুপই হলো, রাতের খানাও খেল না―নদীর ঘাটে চলে গেল, রাতেই নৌকা-টৌকা পেলে চলে যাবে বলে।
তারপরে রামগাঁতীর এই জমিদার বংশের ছেলে দেখতে এল আমাকে। তবে খুব বড় জমিদার ছিল না। কিন্তু খুব নাম ফুটেছিল। বলেছি তো ডাক্তার সাহেবের কথা―একেবারে আপন না হোক, মায়ের খালাতো ভাই―ডা. দবিরউদ্দিন―তা তিনি তো দেখেছিলেন, এই ছেলের কোনও দেমাগ নাই। আর দেমাগ হবে কোত্থেকে, জমিদার বংশের হলে কী হবে, জন্মের আগে তার বাবা চলে গেছে দুনিয়া ছেড়ে, ভাগ্য ভালো দাদায় খানিকটা জমিদারি আর জায়গাজমি লিখে দিয়ে গিয়েছিল। তারপরও বড় তো হতে হচ্ছিল এর ওর ঠোকনা খেতে খেতে। তবে সবগুলো চাচাতো ফুফাতো ভাইই ছিল বলতে গেলে সমবয়সী, একসঙ্গে বড় হচ্ছিল। তা ছাড়া তখন তাদের মধ্যে মিলও ছিল ভীষণ। আমার দাদাশ^শুর মারা যাওয়ার পরেই না যত ঝামেলার শুরু! তখন অবস্থা তো মনে হয় একসময় এত খারাপই হয়ে যাচ্ছিল যে, গাছের পাতা কার উঠানে পড়েছে, কে সেই পাতার মালিক, তা নিয়েও ঝগড়া-বিবাদ ফ্যাঁসাদ বেঁধে যেত। কিন্তু আমার সঙ্গে ওনার যখন বিয়ে হচ্ছিল, তখন তো দেখেছি, ভীষণরকম মিল। মিল না থাকলে, চাচাতো ভাইকে বিয়ে করাতে দল বেঁধে সব ভাই সলপ-রামগাঁতী থেকে ২৪ মাইল হেঁটে হেঁটে সেই বেড়ার মৈত্রবাঁধা গ্রামে যায় ? কিন্তু আমাকে যে দেখল, তখন সন্ধ্যাবেলা। আমাকে কখন কীভাবে দেখেছিল সেদিন, কিছুই মনে নাই। খালি মনে আছে, তার আগের দিন লোকজন আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর মনে আছে, পরের দিন বিয়ের সময় কাবিন নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমার মা চেয়েছিল, কাবিনে বিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি বেঁকে বসেছিলেন, বলেছিলেন, নিজেদের মধ্যে বিয়ে করতে এসেছি, তাও কাবিন করতে হবে ? তখন কী আর করা। কী কারণে, কে জানে, বাবা মা দুজনেরই নাকি ছেলেকে পছন্দ হয়েছিল। আর হবে না ? হাতে করে ওই যে ভাইয়েরা মিলে তখন কী যেন একটা হাতে লেখা পত্রিকা বের করত―‘নওজোয়ান’―সেই ‘নওজোয়ান’ নিয়ে গিয়েছিল। ছেলের হাতের লেখা দেখে, পত্রিকার ডিজাইন দেখে, হাতে আঁকা সব ছবি দেখে বাবা-মার মন গলে গিয়েছিল। বলেছিল, ‘ঠিক আছে, দরকার নাই কাবিননামার। কবুল পাঠই যথেষ্ট।’
বিয়ের কথা, এরকমই মনে আছে, আর কি―এই এতটুকু। তবে সেদিন রাতে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল, বিয়েতে তো আমার এক হিন্দু বান্ধবীও এসেছিল। ঠিক আমার মতোই বয়স ছিল তার। আমার মায়ের ছাত্রী ছিল। কিন্তু সে যে এখন কোনখানে আছে, নাকি সেও মরে গেছে, কে বলবে। অনেক মজা করেছিল ও, ঘাঘরা পরে নেচেছিল অনেক―অনেকক্ষণ। কিন্তু কী যে নাম ছিল তার! কখন যে সে হারিয়ে গেছে! নাকি চলে গেছে ওই পাড়ে ? পয়ষট্টির সেই যুদ্ধের পরপর ? নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই যে গেল, ফিরে আর এল না এ দেশটাতে ?
কাল অনেক রাতে সেই মেয়েটির নাম হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বাদল―আমার সেই বান্ধবীর নাম ছিল বাদল। আর কী অপূর্ব সুন্দরই না ছিল সেই বাদল! কিন্তু আমি মৈত্রবাঁধা ছেড়ে চলে এলাম এই রামগাঁতীতে। বাদলের কী দিয়ে কী যে হলো মৈত্রবাঁধাতে!
কীভাবে বিয়ে হয়েছিল, কোনওদিন ভাবি নাই। আজ ভাবছি, আজ মনে হচ্ছে, বিয়েটা তো হয়েছিল কাবিন ছাড়াই। আধুনিক এই যুগের ধারায় বলতে গেলে কোনও চুক্তি ছাড়াই। সেই হিসেবে ক্ষুদ্র এই জীবনটা আমার, আজকাল লোকজন যে বলাবলি করে, লিভ টুগেদার, সেই লিভ টুগেদারের মতোই কেটে গেল। কিন্তু অস্বীকার করি কী করে, খুব খারাপ তো কাটেনি, বরং খুবই ভালোই কাটল সেই জীবন আমার।
দুই
এই যে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে গেলাম,―কাটালামই তো; এখন কি আর বলা যায়, এখনও কাটাচ্ছি ? এখন আমি অতীত হয়ে গেছি। একটা অতীত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে বিছানার ওপরে। সে কি আর এখন জীবন কাটায় না কি! কিছুদিন আগেও মনে হতো মাঝেমধ্যে, আহ্, ভালো হোক, মন্দ হোক, সৌভাগ্যের হোক, দুর্ভাগ্যের হোক, ওই অতীতটাকেও যদি ফিরে পাওয়া যেত! হারিয়ে ফেলা ওই অতীতও যদি বর্তমান হয়ে উঠত! এখন আর সেটাও মনে হয় না! অতীতের দিকে ফিরে তাকাতেও ভালো লাগে না। তবু শুয়ে থাকতে থাকতে কখনও অবচেতনের চোখ খুলে যায়, অতীতের কোনও কিছুর দিকে চোখ পড়ে যায়। আর ভাবি, কত কিছুই না ঘটল এই চোখের সামনে দিয়ে! ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান আর ভারত হলো, বাংলাদেশ আবার স্বাধীন হলো! আমার জীবনটাও ভাগ হয়ে গেল নানাভাবে। বাবা মায়ের সংসারে থাকা একটা জীবন। শাশুড়ি আর স্বামীর সংসারে কাটল আরেক জীবন। আমার শরীর ফুঁড়ে এই পৃথিবীর ঘ্রাণ নিল কত ছেলেমেয়ে! কিন্তু সবচেয়ে কষ্টের হলো মনে হয় এই ছেলেমেয়ের সংসারে থাকা জীবন। বড় খেদ রয়ে গেল, আমি যেমন আমার শাশুড়ি আম্মাকে বড় আপন ভাবতে পেরেছিলাম, খুব আপন করে নিতে পেরেছিলাম, আমাকে আমার কোনও ছেলের বউই তেমন আপন করে নিল না। আপন করে নেয় নাই, সে কথা বলব না―কিন্তু আপন ভাবতে পারে নাই। সেজন্যে তাদের দোষ দিই না, খারাপও বলি না; কিন্তু মনে যে খেদ আছে, সেটাও কি ভাবতে পারব না ? এমন তো না যে আমার পুত্রবধূদের সবাই শহরে থাকে, মাঝেমধ্যে পালাপার্বণে বাড়িতে আসে। গ্রামেই তো সারা জীবন ধরে আছে কমপক্ষে তিন ছেলের বউ। কিন্তু হলো না; ১২ বছর ৫ মাস বয়সে এসেছিলাম বলেই হয়তো আমার শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা হয়েছিল; কিন্তু ২৪/২৫ নাকি ৩০/৩২ বছর বয়সে এল বলেই হয়ত আমার সঙ্গে আমার পুত্রবধূদের কারওরই তেমন হলো না। তাদের কেউ এই সংসারে আসল এসএসসি পাশ করে, কেউ আসল ইন্টারমিডিয়েট পাস করে, কেউ কেউ আবার আসল এম.এ. বি.এ পাস করে। কেউ অশ্রদ্ধা-অভক্তি করে নাই, উপেক্ষা করে নাই, কিন্তু মেলেও নাই তেমন করে। প্রান্তটা আমাকে সান্ত্বনা দেয়, মা, এত মেলাতে চান কেন ? এদের কেউ আপনার মতো সাড়ে ১২ বছরে সংসার করতে এসেছে ? লেখাপড়া করেছে, বড় হয়েছে, প্রত্যেকের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এত কী আর মেলে ? কী জানি বাপু, আমি তো বুঝি, মানুষের লেখাপড়াই তো এই জন্যে যে সে আরেকজনকে ভালো করে বুঝতে পারবে, আরেকজনের সঙ্গে নিজেকে ভালো করে মেলাতে শিখবে। মেলাতেই যদি না পারো, আলাদাই যদি হয়ে পড়ো, তা হলে আর লেখাপড়া হয় কী করে! নাকি লেখাপড়ার ধারাই এখন ওই রকম, যত শিখবে, ততই সে দূরে সরে যাবে আরেকজনের কাছে থেকে ?
সাড়ে ১২ বছরে এই সংসারে এলাম, সাড়ে ১৩ হতে না হতেই মনে হয় মাকে ভুললাম। ভুললাম মানে কিন্তু ভুলে যাওয়া না―ভুললাম মানে এই, আমার এই প্রতিদিনের জীবন থেকে মায়ের প্রয়োজনীয়তা, মায়ের উপস্থিতি যেন নাই হয়ে গেল। তখনও আমার শোওয়া-বসা ২৪ ঘণ্টাই শাশুড়ি মার সঙ্গে। আমাকে ভারী আদর করত সে। তাকে মনে হতো কোনও কিছু হারিয়ে ফেলা এক মহিলা, মনে হতো দিনরাত কোনও কিছু খুঁজে ফিরছেন। কখনও মনে হতো দিকশূন্য। টকটকে ফর্সা মেয়ে, মনের মধ্যে একটু ওলোটপালোট হলে সেই ফর্সা রঙও দোল খেতে থাকত। কখনও হালকা লাল হয়ে উঠত। কখনও বা জমাট লালের মতো। জমিদারবাড়ি বটে, তাই বলে অত বড় তো না যে বলা যাবে, সান্যালদের মতোই প্রতাপ এতেই। তবে সান্যালদের ছোট তরফের বাড়ি ওই হাইস্কুলের পাশে, সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে এলে বড় তরফের বাড়ি এই কালীমন্দিরের পাশে, আর কালীমন্দির পেরিয়ে খানিকটা এই দিকে আসলেই এই চৌধুরীদের জমিদারবাড়ি। যত ছোট জমিদারিই হোক না চৌধুরীদের, সেই জমিদারিই তখন সান্যালদের ঘাড়ের কাছে যেন গরম নিঃশ^াসের মতো মনে হতো। সব কথা বলতে পারব না, সব কথা বলাও তো ঠিক না, আর আমি সরল সিধা মানুষ―সব সত্য কথা বলতে গেলে আমার নিজের গলার স্বরই কাঁপতে থাকবে যে। খালি বলি, সান্যালরা যে ছয়চল্লিশের আগেই চলে গিয়েছিল―তা ভালোই করেছিল। তার পরও কয়েক ঘর ছিল অবশ্য। কিন্তু ভাগ্য ভালো, তারাও বাড়িঘর জমিজমা সব ঠিকমতো বিক্রি করে যেতে পেরেছে। হিন্দুদের জমিজমার ওপর আমার শ^শুরের গোষ্ঠীর কাউকে লোভ করতে দেখি নাই। জমিজমা নিয়ে তাদের মধ্যে জিলাপির প্যাঁচ দেখা দিয়েছে আরও পরে। তবে এইটা কিন্তু সত্যি কথা, বন্দুক কেনার পর আমার দু-এক দেবর যা করেছে―তা কোনও মানুষের কাজ না। বুকে বন্দুক তাক করে মেয়েমানুষকে তুলে আনা কোনও পুরুষের কাজ না। এই যে… কী ভাবতে ভাবতে কী ভেবে ফেলছি! এই জন্যেই বলছিলাম, সব কথা বলা ঠিক না, সব কথা বলতে গেলে আমার গলার স্বরই কেঁপে কেঁপে উঠবে। আমার শাশুড়ি আর তার ছেলের জন্যে বরাদ্দ ছিল একটা মাত্র ঘর। না কোনও রান্নাঘর, না কোনও গোসলখানা! ঘরের কোণে ছিল বড় কাঁঠাল গাছ। ঘরটা আবার ছোট বড় দুই কোঠায় ভাগ করা। ছোট কোঠায় থাকত আমার স্বামী। বড় কোঠায় থাকতাম আমরা দুজন, থাকত সংসারের টুকিটাকি সব কিছু। একদিকে ছিল মাচা। সেই মাচার নিচে আর ওপরে ছিল ছোটবড় কত কোলা। কোলার মধ্যে এ ফসলের বীজ, ও ফসলের বীজ। জীবনটা তখনও ছিল খেলাঘরের মতো। শাশুড়ি মা আমাকে ধান চেনাতো, ডাল চেনাতো, ফসলের বীজ চেনাতো। এ যে কত কঠিন কাজ, কেউ জানে না। মানুষজন এখন নাকি ভার্সিটিতে যেয়ে এইসব চেনে। চিনুক না চিনুক, চেনার গরম দেখায় আর সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি বাগায়। অথচ আমরা তখন নাভি কাটতে না কাটতেই এইসব চিনেছি। তার পরও আমাদের অশিক্ষিত পরিচয় ঘুচল না কোনওদিন। পুরো বাড়িঘর জুড়ে দাপট ছিল আমার স্বামীর বড় চাচা ডাক্তার সাহেবের, দাপট ছিল মেজ চাচা দারোগা সাহেবের। সবচেয়ে ছোট হলো আমার শ^শুর―তা তিনি তো মারা গেছিলেন তার ছেলে জন্ম নেওয়ার আগেই। যতদিন আমার স্বামীর দাদা জীবিত ছিলেন, ততদিন তাও চলত একরকম―কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই সংসারে আমার শাশুড়ির হাল হলো শীতের দিনের জবুথবু ওই শালিকছানার মতো। ছোটবেলায় তো অত বুঝি নাই― এখন তাঁর কথা ভাবলে আমার মন কষ্টে ভরে যায়। দুই-দুইবার বিয়ে হলো, কিন্তু কোনও স্বামীই বাঁচল না, মরে গেল টুপ করে! পুরুষের স্মৃতি ধরে রাখা খুব কঠিন, কিন্তু তার অসম্পূর্ণ স্মৃতির সঙ্গে বসবাস করা কোনও নারীর পক্ষে যে আরও কঠিন। ভাগ্য ভালো, খোদা আছে―খোদার ওপর সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে বলতে পারি, ‘তুমি সবই জানো, তুমি সবই দেখো, তুমিই এসবের বিচার কোরো।’
মায়ের যে অভাব, সইয়ের যে অভাব, দিন দিন সেটা ভুলে গেছি আমি শাশুড়ি মায়ের পরিচর্যায়। তারপরও মা বেঁচে আছে, সদর্পেই এখনও বেঁচে আছে দেখি মনের এক গহিন কোণে। ঘন গভীর রাতের শাদা ফুল সে। চোখে পড়ে না, কিন্তু ঘ্রাণ এসে হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। মায়ের কাছ থেকে চলে আসার দুঃখ একটু একটু করে ভুলতে পারলেও ভাইবোনের কাছে না থাকার দুঃখ কিন্তু আমি কোনও ভাবেই ভুলতে পারি নাই। আমার স্বামীর তো আপন কোনও ভাইবোন নাই, কিন্তু এমন কোনও চাচাতো ভাই-বোনও ছিল না, যারা আমাকে ভাইবোন থেকে দূরে সরে আসার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। আমার বড় বোনটা তো খুব বেশিদিন বাঁচে নাই, দুই ছেলে আর এক মেয়ের জন্ম হলো, তার পরই কী করে একদিনের জ্বরেই চলে গেল দুনিয়া ছেড়ে। অথচ বড় বুবু ছিল বলেই তো আমি কলকাতা দেখতে পেরেছিলাম। এই যে এই রামগাঁতীতে সারাটা জীবন পার করে দিয়ে গেলাম, কোনওদিন আর মনেই পড়ল না, গড়ের মাঠের হাওয়া লেগেছিল আমার শরীরজুড়ে, সেই কবে বছর দশেক বয়সেই আমি ঘুরেছিলাম সেই এসপ্লানেডে। আর তাই যেদিন শুনলাম, বুবু আর নাই, দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রেখে বুবু আর নাই, তখন মনে হয়েছিল আমার নিজের সন্তানরাই যেন মাকে হারালো। এই সংসারে তেমন কেউ তো ছিল না―না ননদ না জা―যারা সেই বুবুর দুঃখ ঘোচাতে পারে, যারা আমার বাড়িতে রেখে আসা ছোট বোন দুটোর কথা ভুলিয়ে দিতে পারে। আমার স্বামীর সমবয়সী চাচাতো ভাইরা ছিল খুব আমুদে, নাটক করত, গান করত, বর্ষা আসুক বা না আসুক আষাঢ় আসার আগে থেকেই পানসী নিয়ে নৌকা বাইচের সাজ সাজ রব শুরু করত। ডাক্তার সাহেবের ছেলে―বড়ভাইজান তো ভাবিকে প্রায়ই পাঠিয়ে দিতেন, আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, আমাকে নিয়ে সান্যালদের ঘরদোর দেখাতে। আবার মেলা থেকে কোনও কিছু কিনে এনে পাঠিয়ে দিতেন স্বামীর হাত দিয়ে। কিন্তু তারাও আমার ভাই আর সেই ধর্মভাইয়ের শূন্যতা দূর করতে পারে নাই।
কিন্তু এত যে দীর্ঘ অতীত, সেসবের কোনও কিছু না, কিংবা নিজের স্বামী-সন্তানও না, আজকাল আমার কেবল ঘুরেফিরে এটুকুই মনে হয়, আচ্ছা, সেই যে ১১ জন মেয়ে, সেই যে আমার মায়ের ১০টা বান্ধবী―তাদের পরে কী হয়েছিল ? তারা কি সবাই পেরেছিল মেয়েদের জন্যে কোনও স্কুল খুলতে ? সেই স্কুল চালিয়ে নিতে ? তারা কি তাদের মনে যে স্বপ্ন জ্বলেছিল, সেই স্বপ্ন জ্বালাতে পেরেছিল আর কোনও মেয়ের মনে ?
পরলোকে আমার মা-স্বামী কেমন আছে সে কথা না, আমার মরে যাওয়া অবোধ ছোট সন্তানরা কেমন আছে সে কথা না, আমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরা কী করছে সেসব কথাও না―মনে এখন কেবল এইটুকুই জানার ইচ্ছা জাগে, আচ্ছা, সেই ১০ জন কেমন আছে ? মনে হয়, পৃথিবীতে কি সত্যিই আমার এত কাজ ছিল, এত ব্যস্ততা ছিল যে, একবারও সময় হয় নাই মার কাছে থেকে সেই কথা জানতে ? এখন মনে কেবল সামান্য একটু আভাস চোখে পড়ে, দল বেঁধে ১১টি মেয়ে হেঁটে চলেছে স্কুলের দিকে। তার পর আর কিছু চোখে পড়ে না। তার পর কেবল গভীর এক কালো পর্দা নেমে আসে, যেনবা পৃথিবীজুড়ে।
তিন
সন্ধ্যা নামছে বোধহয়। নাকি সন্ধ্যাও পেরিয়ে গেছে অনেক আগে ?
আজকাল কোনও কিছুই আর মনে পড়ে না। শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন কেবলই ডেকে চলেছে, ‘মা, মা… ও মা…’
আমার ছোট ছেলে বোধহয়। ভাত ছেনে ছেনে একেবারে নরম ভর্তা করে নিয়ে এসেছে সামান্য একটু হলেও খেতে পারি যদি! অথবা, আমার ছোট মেয়ে বোধহয়! সকালে একবার মাস্টারি করতে যাওয়ার আগে রেখে যায় এটা ওটা, যাতে গলা শুকিয়ে উঠলে মুখে দিতে পারি; আর বিকেলে নিয়ে আসে এক গ্লাস দুধ না হয় জুস। এই দুই ছেলেমেয়ে ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা আর কে-ইবা খোঁজ রাখে আমার!
একেবারে ঘরে পড়ে গেছি। এও বলা যায়, বিছানায় পড়ে গেছি। আর বুঝতে পারছি, এইভাবে আমার চারপাশকে কোনও দিনই টের পাইনি। চারপাশের মানুষগুলোকেও না। আগেও সব কিছু দেখেছি, বয়ে চলা এক নদী হয়ে দেখতে দেখতে চলে গেছি সামনের দিকে। থিতু হয়ে দেখা হয়নি, থির হয়ে চাওয়া হয়নি। আর এখন স্থির হয়ে দেখতে দেখতে ভাবি, কত কিছুই না হারিয়ে গেছে জীবন থেকে! জীবনে হয়তো তাদের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তারপরও বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ তৈরি করেছিল। বেঁচে থাকতে হলে যে ভালো লাগার আস্বাদ লাগে, আনন্দের তরঙ্গ লাগে, সেই আস্বাদ আর তরঙ্গ তারা তৈরি করেছিল। দালানের বাইরের দিকে ছিল একটা গন্ধরাজ গাছ, কাউকে সেটা লাগাতে হয়নি, হয়তো সেটার বীজ ঠোঁট কিংবা পেটে করে নিয়ে এসেছিল অজানা কোনও পাখি। অথবা সেটি বাতাসের তোড়ে উড়ে এসে কোনওমতে মুখ গুঁজেছিল এ বাড়ির মাটির ভেতর। পশ্চিমদুয়ারি দেয়ালটার কাছে একটা কামিনী গাছ আর তার ঠিক পাশেই ভেতরবাড়ির গেইট ঘেঁষে একটি মাধবীলতার গাছ লাগিয়েছিল এ পরিবারের বড় জামাই। বড় শৌখিন মানুষ ছিল সে। ভালোবাসত সানাই বাজাতে, গান গাইতে আর গান শুনতে। ভালোবাসত নিজের হাতে ফুলগাছ লাগাতে। এই বাড়িতে একটা রাধাচূড়া গাছও লাগিয়েছিল সে। কেউ একজন সেটা কেটে ফেলেছে; যেভাবে একদিন কেটে ফেলা হয়েছিল মাধবীলতা গাছটিকেও। সেই গাছটির কারণে বাড়িতে ছ্যাঙ্গা আর কেন্নোর উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছিল বলে।
‘মা―একটু খাওয়ার চেষ্টা করেন মা। ভাতের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে দিয়েছি মা।’
আমি আবারও আমার ছেলের কণ্ঠ শুনতে পাই। অন্য সবাই হাল ছেড়ে দেয়; সবাই মানে আমার ছেলের বউ থেকে শুরু করে ছোট মেয়েটা পর্যন্ত। কিন্তু এই ছেলে হাল ছাড়ে না। মা, মা করতেই থাকে। এখন সবসময় চটজলদি উত্তর দিতে পারি না, চোখটা মেলতে পারি না, তেমন করার ইচ্ছেও জাগে না। কিন্তু রাতজাগা পাখি যেমন নাছোড়বান্দা, ছেলেটাও ঠিক সেরকম। সে আমার বিছানার পাশে বসেই থাকে। আর সবাই আভাসে জানিয়ে দেয়, এভাবে ডাকাডাকি করার কোনও মানে হয় না, উনি আর খাবেন না, খেতে পারবেন না; কিন্তু তাদের কথা তার যেন বিশ^াস হয় না। আর শেষ পর্যন্ত তার ওই মনে করাকে সত্য প্রমাণের জন্যেই হয়তো বা আমার ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে যায়। সে ছোট চামচে করে আমার মুখের মধ্যে প্রথমে একটু পানি ঢেলে দেয়। পানিটুকু পেটের মধ্যেই গেছে, এটি নিশ্চিত হওয়ার পর সে এবার গলানো ভাত আস্তে আস্তে খাওয়ানোর চেষ্টা করে আর কথা বলে চলে, ‘আপনি যে খেতে চান না, না খেলে তো অবস্থা আরও কাহিল হয়ে যাবে। একটু একটু করে খাওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার খিদা লাগলে এ নাম সে নাম ধরে মানুষজনকে ডাকাডাকি করবেন। আমরা থাকি বা না থাকি, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। তাকে খাইয়ে দিতে বলবেন। না হয় আমাদের খবর দিতে বলবেন। আর কাউকে খবর না দিয়ে আমাকেই খবর দিতে বলবেন। সেটাই ভালো। আমি থাকি, না থাকি, ফোন করে ব্যবস্থা নেব।’
এইভাবে ছেলে যেসব কথা বলতে থাকে, সেসবও হয়তো আর আমার কানে ঢোকে না। মানে কানে ঢুকলেও আমি আর তা বুঝেসুঝে মনের মধ্যে নিতে পারি না। আগে এই বাড়িতে সারা বছর ফসলের খন্দ লেগে থাকত। সারাদিনই তাই বাড়িতে লোকজন থাকত। এখন সেসবের কিছুই তো হয় না, সন্তানরা জায়গাজমি ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে, সেসব জমি কেউ দিয়েছে মেদি, কেউ দিয়েছে বর্গা। বাড়িতে এখন আর কোনও আবাদই হয় না। ইরি চাষের ধান চাতাল থেকে ঘরে চলে আসে চাল হয়ে। যে কয় পুত্রবধূ বাড়িতে আছে, তারা আবার চাকরিও করে কলেজ-স্কুলে। তাহলে কে আর আমার খোঁজখবর রাখে। ছেলে তাই প্রতিদিন বারবার কানের কাছে পথ বাতলায়, বাড়িতে কেউ না থাকলে আর আমার কোনও দরকার হলে কী করতে হবে। কিন্তু শুনলেও কি আর কাজে লাগাতে পারি সে পরামর্শ! অঘোর অচৈতন্যে আমি কেবল এক স্তর থেকে অন্য কোনও স্তরে পৌঁছাই। শান্ত তবু এটা-ওটা বলতেই থাকে। ঠিক যেমন করে আমিও ছোটবেলায় আমার অবোধ বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর সময় ধৈর্য ধরে বেহুদাই নানা কথা বলতাম। প্রথম সন্তান যখন হলো, তখন ওই কাণ্ড দেখে আমার স্বামী হেসে ফেলতেন। কিন্তু কেন যেন ওই রকমই করতাম। তারপর এমন একটা সময় এল, এইসব কাণ্ড দেখে তাঁর আর হাসি পেত না। তারপর এমন একটা সময় এল, এইসব আমি কিংবা তিনি বোধহয় ভুলেই গেলাম।
এখন ছেলে আমাকে সেইরকম করে কথা বলে আর খাওয়ানোর চেষ্টা করে। ঠোঁটের ধার মুছে দেয় ন্যাকড়া নাকি ন্যাপকিন দিয়ে। উঠে বসায়। প্রস্রাব করব কি না জিজ্ঞেস করে। বউকে ডেকে আনে। এই সময় সমস্ত কিছু প্রায়বিস্মৃত হওয়ার পরও আমার মনে বোধহয় শত শত স্মৃতি ধেয়ে আসে। সেসব স্মৃতির ভারে আমার কান্না পেতে থাকে। আমার শাশুড়ি আম্মার ভাগ্য ভালো, খুবই ভালো। তিনিও চলাফেরা করতে পারতেন না বইকি। কানেও শুনতে পেতেন না। কিন্তু একেবারে বিছানায় পড়ে যাননি। জোরে গলা উঁচিয়ে ডাকতে পারতেন। অন্যের ঘাড়ে বা কাঁধে ভর করে পায়খানা-প্রস্রাব করতে যেতে পারতেন। কিন্তু জানি না কোন দোষে, কোন ভাগ্যে আমি এই বিপাকে পড়ে গেছি। আজকাল বিছানাতে বসেই এইসব সেরে ফেলতে হয়। ব্যাপারটা কারও ভালো লাগার কথা নয়। ছেলে বোধহয় সেটা বুঝতে পারে। আর সেজন্যেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বউ কিংবা বাড়ির আর কোনও মেয়েকে দিয়ে আমাকে পরিচ্ছন্ন করার কাজটি সারে। যাতে যত বিরক্তিই লাগুক না কেন, কাজটি তারা চুপচাপ করতে বাধ্য হয়। আমার এই ছেলেটা একটু রগচটাও আছে―মেজাজ খারাপ হলে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, সেটা কোনও ব্যাপার না, পেটাতে শুরু করে। বোধহয় এ কারণেই কেউ তাকে আবার বেশি ঘাটায় না।
এখন এমন দিন এসেছে যে, এই বিরাট বাড়ি সারাদিন সুনসান পড়ে থাকে। অথচ একসময় মাত্র একটি ঘর ছিল আমাদের সেই বড় কোঠা আর ছোট কোঠা মিলিয়ে। থাকতে হতো অনিচ্ছা থাকার পরও গাদাগাদি করে। আমার দাদাশ^শুর মারা যাওয়ার পর তার জীবিত দুই ছেলের মধ্যে খুব নীরবে হলেও কেমন একটা ঠোকাঠুকি শুরু হলো। এই জমিদারবাড়ির শোভা বলতে ওই একটা বড় দালান। সেখানে আছে তিনটি কোঠা। দক্ষিণদুয়ারি সে দালানের ডিজাইন কী যে সুন্দর―সবদিক দিয়েই আলোবাতাস গড়াগড়ি খায়। মাঝের খোপটা একটু ছোট বটে―কিন্তু তার উত্তর-দক্ষিণ দুই দিকেই খোলামেলা বাহারি বারান্দা। দক্ষিণের বারান্দাই বেশি বড়―গাঁয়ের মানুষজন দেনদরবার করতে এলে ওখানেই বসে পড়ত ন্যাটা দিয়ে। উত্তরেরটা একটু ছোট হলেও সামনের প্রশস্ত উঠানটাকে ধরলে বাড়ির মেয়েদের চুল বিলি কাটার জন্যে বেশ উপযুক্তই বলতে হবে। দালানের পশ্চিম আর পুবের কোঠার ভেতর দিকের দরজা রয়েছে এ বারান্দার সঙ্গে। বাইরের দিকের দরজা একটির একেবারে সরাসরি পশ্চিম দিকে, আরেকটির সরাসরি পুবের দিকে। সেই দুই দরজার সামনেও আবার শানবাঁধানো বসবার জায়গা। এই দালানেই মাঝের ঘরে মৃত্যু হয়েছিল নাকি আমার দাদাশ^শুরের। মরতে যাওয়ার আগে তিনি নাকি বলেছিলেন, ‘আমি তো আমার এতিম নাতিকে কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না। তোমরা তাকে এই দালানের মাঝখানের ঘরটাতে রেখো।’
তা কে শোনে কার কথা। দুই ছেলে তো মারাই গিয়েছিল, বেঁচে থাকা একজন বড় ছেলে ডাক্তার, আরেকজন দারোগা। তখনকার দিনে মুসলমানদের হাতে টাকা আসত ওই দারোগা হওয়ার গুণে। দালান বানানো শুরু করতে না করতেই তো মারা গেল সবচেয়ে কাজের ছেলেটা―মানে আমার শাশুড়ি মার প্রথম স্বামী বিক্রম চৌধুরী। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর দাদাশ্বশুর কেমন উদাস হয়ে গেলেন। কোনও কাজেই তার আর বসল না মন-টন। আর সর্বনাশও যেন ধেয়ে আসতে শুরু করল। ওই যে সলপ রেলস্টেশন, তার সঙ্গেই ছিল দাদাশ^শুরের বিরাট গুদাম। পাটের ব্যবসা জুড়ে তখন তার হাতে কাঁচা টাকাপয়সা আসছে বেশুমার। এদিকে সিরাজগঞ্জ থেকে মালগাড়ি চলতে শুরু করেছে কলকাতাতে। সেই মালগাড়িতে করে পাট চলে যায় সিরাজগঞ্জের জুট মিলে, যায় আরও কত জায়গায়! এই পাটের ব্যবসার দেখভাল করতে শুরু করেছিল বিক্রম চৌধুরী। কিন্তু তিনি গেলেন, ওদিকে দারোগা সাহেবের পোস্টিং তখন সেই ময়মনসিংহ শহরে। মধুপুরের জঙ্গলে থাকে ডাকাতের দল, সেই ডাকাতের দল ঠেঙিয়ে তিনিও সুনাম করেছেন। ডাক্তার সাহেব আবার একদমই পছন্দ করতেন না ব্যবসাপাতির দৌড়ঝাঁপ। আমার দাদাশ^শুরের সম্পদ যেন বারো ভূতের ভিটা হয়ে গেল। ছেলে মরে যাওয়ায় তাঁর মনটা কত যে নরম হয়ে গিয়েছিল, শুনলে বিশ^াসই করা যায় না। যে এসে যা চাইত, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতেন। কিন্তু তার সম্পদ যেন সেই দৈত্যের দেওয়া তফিলের মতো। হাত ঢুকিয়ে যত বের করা যায়, ততই বেরয়। কিন্তু মানুষ কি আর মানুষের ভালো দেখতে পারে ? একরাতে সেই রেলস্টেশনের কাছের গুদামে আগুন লেগে সব কিছু গেল। এর আগেও একবার এই গুদামে আগুন লেগেছিল। কিন্তু তখন বিক্রম চৌধুরী ছিলেন, সেই আগুনের আঁচ হাজি সাহেবের গায়ে অত লাগে নাই। এইবার লাগল। ব্যবসাপাতিতে সেই যে ধস নামল, মানুষটা আর পারল না ঘুরে দাঁড়াতে। দালানটার কাজই নাকি শেষ করতে পারছিলেন না। দারোগা সাহেব টাকা দিতে লাগলেন, তবেই না শেষ হলো এই দালান। তারপরেই না এই বাড়িটাকে পুরোপুরি জমিদারবাড়ি মনে হতে লাগল। তখনকার দিনে দারোগা মানেই টাকার ছড়াছড়ি, আর সত্যি কথাই বলি, আমাদের দারোগা সাহেবের ওসবের দিকে একটু নজরও ছিল। তবে গরিব মানুষকে ঘাটায়ে বদনামের ভাগীদার হয় নাই। স্পষ্ট করেই বলত, বড়লোকেরা যত অন্যায় করে, তাদের কাছ থেকেই যত খসানো যায়, তাতে গরিব মেরে হাতে দাগ ফেলার দরকার কী ? আমার শাশুড়ি মা অবশ্য এইসব কানে তুলতে পারতেন না। নরম মানুষ ছিলেন, ভাশুরদের কাউকে ঘাটাতে যেতেন না, কিন্তু দরকার হলে উচিত কথা বলতে পিছপাও হতেন না। দারোগা সাহেবকে নাকি তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘শোনেন ভাইজান, ধরেন দুইটা শুয়ার―একটা ধেড়ে শুয়োর, আরেকটা বাচ্চা তুলতুলে নরমসরম শুয়োর, দেখলেই মায়া লাগে―কিন্তু দুটোই কিন্তু শুয়োর। আপনি বড়লোকের হক মারেন আর ছোটলোকের হক মারেন, আপনি কিন্তু হক মারেন।’
দারোগা সাহেব নাকি খুব রুষ্ট হয়েছিলেন, ‘হক মারলাম কোনখানে ? বড়লোক অন্যায় করে। সেই অন্যায় ঢাকার জন্যে টাকা খরচ করে। আমি সেটা না নিলে আরেকজন নেবে। কেউ না কেউ যখন নেবে, তখন আমিই না হয় নিলাম।’
‘তা না হয় নিলেন। কিন্তু সেটা নিয়ে যে আরেকজনের ওপর অবিচার করলেন ? তার কী হবে ?’
‘অবিচার করলাম ?! আমি অবিচার করলাম ? তুমি ঠিকমতো জানো তো ? … শোনো বউমা, আমি এমন কিছু করি না যাতে অবিচার হয়। ধরো, ধরো―একজন ধনী লোক তার কাজের মেয়ের সর্বনাশ করেছে। হ্যাঁ, শাস্তি দেয়া যায়। নিশ্চয়ই দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে কি আসলেই তার কোনও লাভ হয় ? ন্যায়বিচার পেয়েছি―এই আনন্দ কি তার শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, নাকি কোনও কাজে লাগে ? কারাগারে যেতে যেতে তো ওই কাজের মেয়ের পরিবারটার আরও ১২টা বাজবার বন্দোবস্তো করে ফেলে সে। লাভ হয় তাতে ? তার চেয়ে যদি মেয়েটা বা তার পরিবার কিছু টাকাপয়সা পায়, সেই টাকা দিয়ে একটা ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়, অন্য কোনওখানে পরিবার নিয়ে গিয়ে তার বাপ-ভাইয়ে ভদ্র একটা জীবন কাটাতে পারে, সেটাই কি ভালো না ?’
‘থুঃ ভাইজান, আপনি আমাকে এইসব কখনও শোনাতে আসবেন না। আমার কান এইসব শোনার মতো না।’
এরকম ভাবেই নাকি কখনও সখনও আমার শাশুড়িমার সঙ্গে চাপা ঝগড়াঝাটি হয়ে যেত তাঁর ভাসুরদের। এদেরই কি না তাঁর শ^শুরমশাই আমার স্বামীর নাম করে মরে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ‘ওর বাবা নাই, তোমাদের এই ভাইটার ছেলেকে তোমরা দেখেশুনে রাখবে, মাঝখানে রাখবে, ওদের এই মাঝখানের কোঠাটা দেবে।’
তা কে আর কাকে দেয় সেই মাঝখানের কোঠা! এই পশ্চিমদিকের কামরায় ডাক্তার সাহেবরা তো আগে থেকেই থাকতেন, দাদাশ^শুর ছিলেন মাঝখানেরটাতে, আর পুবদিকের কামরাটায় থাকতেন দারোগা সাহেবের পরিবার। হাজি সাহেবের মৃত্যুর পর দারোগা সাহেব মাঝখানের ঘরটাও নিয়ে নিলেন। বললেন, ‘আমার ছেলেমেয়ে বেশি, আর এই দালান বানাতে আমি তো টাকাও দিয়েছি, এর ওপর আমার দাবিও বেশি।’ ডাক্তার সাহেব নিরীহ মানুষ, তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। আমাদের থাকাখাওয়ার সম্বল হয়ে থাকল ওই দুই কামরার এক টিনের ঘর। কিন্তু চিরদিন কি আর সবার একইরকম যায় ? ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন, দারোগা সাহেবও মারা গেলেন, তাদের ছেলেপেলেদের মধ্যে একটু-আধটু ঠোকাঠুকি শুরু হলো। দারোগা সাহেবদেরও বন্দুক ছিল, ডাক্তার সাহেবদেরও বন্দুক ছিল―তাই ঠোকাঠুকিটা মাঝেমধ্যে একটু বেশিও হয়ে যেত। কিন্তু ডাক্তার সাহেবদের দুই ছেলের মাথা একটু ঠান্ডাই ছিল। সান্যাল বংশের লোকজন তখন একজন একজন করে জায়গাজমি বিক্রি করে ওই পাড়ে চলে যাচ্ছে। তারা ঠিক করলেন, সান্যালদের মতো বাপের ভিটা ছেড়ে কলকাতা না হোক, অন্তত ধারেকাছেই অন্য কোথাও বাড়িঘর তোলা ভালো। সড়কের ধারে এক সান্যালের বাড়ির জায়গা কিনে নিলেন মিয়া ভাইরা। এই দালানের কামরা দিয়ে তখন আর কী করবেন ? বিক্রি করা ছাড়া কোনও গতি কি আছে ? রিয়াজ মিয়ার সঙ্গে সেই কামরা বিক্রির কথা হচ্ছে জানতে পেরে আমার শাশুড়ি মা গিয়ে সোজা কথা পাড়লেন মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে। ভাগ্য ভালো, মুখ ফুটে বলেছিলেন। মিয়া ভাইদের মা আবার ছোট ছেলের জন্মের পরপরই মরে গিয়েছিল। তখন তাকে দুধ দেবে কে ? দুধ দিয়েছিলেন আমারই শাশুড়ি মা। তা দুধমা তো নিজেরই মা। তারা তাই তার কথা ফেলতে পারলেন না। কামরায় তালা মেরে তারা গিয়ে উঠলেন নতুন বাড়িতে। কথা হলো, আমার স্বামী যেদিন পুরো টাকা দিতে পারবেন, তারাও সেদিন তালা খুলে দেবেন।
এখন কী যেসব ভাবি, এইসব আদিঅন্তহীন স্মৃতি … কেনই বা ভাবি! এ কি বার্ধক্যের চিহ্ন, নাকি এক অবসন্ন যাত্রা―যার গন্তব্য মৃত্যুকূপে! নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে শিখেছি আমি সেই শৈশব থেকে। মা যত না শিখিয়েছিলেন, তারও বেশি শিখিয়েছিলেন আমার শাশুড়ি মায়ে। মায়ের শেখানোর মধ্যে প্রচণ্ড শাসন ছিল, প্রচণ্ড ক্রোধও ছিল―একটু ব্যর্থ হলেই যা ঝরে পড়ত তীব্র রোষে। কিন্তু শাশুড়ি মায়ের ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। নিশ্চয়ই তারও ক্রোধ ছিল, প্রচণ্ড রোষও ছিল। কিন্তু সেই ক্রোধ বা রোষের প্রকাশ ঘটলে কে যে কী ভেবে বসবে, সেজন্যেই বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে বোঝাপড়া করেছেন। ওই যে একটা ব্যাপার আছে না, মা হয়ে মেয়ের গায়ে যতবারই হাত তোলো না কেন, কেউই তোমার ভালোবাসার ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না; কিন্তু শাশুড়ি মা হয়ে ভালোবেসেও যদি একটা চুল ধরে টান দিয়েছ, তাহলে তোমার সে ভালোবাসা যত গাঢ়ই হোক না কেন, কেউই তা বিশ^াস করবে না। বোধহয় সে কারণেই তিনি খুব সচেতন ছিলেন। তবে হ্যাঁ, রাগ তিনি দেখাতে শুরু করলেন, আমার তিন ছেলেমেয়ে হতে না হতেই আমি টের পেতে শুরু করলাম, রাগ আর অসহিষ্ণুতা তাঁর একেবারে কম নয়।
তবু তিনি যেদিন চলে গেলেন, সেদিন যেন দুনিয়ার যাবতীয় আন্ধার নেমে এল আমার চোখে। নিজেকে তো ফাঁকি দিতে পারি না, সত্যি কথাই বলি, নিজের মা মারা গেলেও এত দুঃখ পাই নাই, পরে যখন স্বামীও চলে গেলেন, তখনও এত কষ্ট পাই নাই। তিনি চলে গেলেন শিশির ঝরতে থাকা এক সন্ধ্যায়। শীতের দিনে আমরা গাঁয়ের মানুষজন রান্নাবান্না করি খোলা চুলাতে। চুলায় আগুন জ্বলে, আগুনের তাপ মাখি, কখনও ধান সিদ্ধ করি, কখনও বা এই পিঠা সেই পিঠা বানাই। কয়েক দিন হলোই তিনি একটু অসুস্থ ছিলেন। সন্ধ্যা নেমে আসার পর যখন চারপাশে অজস্র ঝিঁঝি পোকা তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে, তখন কয়েকটা নতুন পিঠা দিতে তার ঘরে গিয়ে দেখলাম, আমাদের সবার অজান্তেই তিনি শেষ নিঃশ^াস ফেলেছেন।
আমার মাথা ঘুরে উঠল। তা তোমরা বলতেই পারো, মারা তো উনি অনেক আগেই গিয়েছিলেন―একা একা চলাফেরা দূরে থাক, পায়খানাতেই যেতে পারতেন না, চোখ দুটো ঢাকা পড়েছিল ঘন ছানিতে, অথচ সাহস ছিল না অপারেশন করার, কানে শুনতে পারতেন না, একটাও দাঁত ছিল না…এরকম কত কারণই তো বলে দেওয়া যায়। কিন্তু আমি যদি বলি, ঠিক আছে, ওনার কোনও ক্ষমতা নাই―কিন্তু একজন মানুষ আছে, এখনও তার মাথাটায় রক্তের স্রোত বয়ে যায়, এখনও তার দেহটা আমাদের মধ্যে আছে,―এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুনিয়ায় ? যদি বলি, ওটুকুই যথেষ্ট একজন শিশুর কাছে ? শিশুই তো ছিলাম আমি তার কাছে, এমনকি মৃত্যুর সেই মুহূর্ততেও। দিনে দিনে আমি বড় হয়েছি, দিনে দিনে তিনি বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু এক চিরশিশুর মতো আমার সমস্ত ভয়ভীতিময় কম্পন, আমার সমস্ত অনিশ্চিতিময় শঙ্কা তো থেমেছে কেবল তিনি আছেন বলে। সেই তিনিই যদি চলে যান দৃশ্যের অন্তরালে, তাহলে আমি আর বাঁচি কী করে ? আমাকে লতিয়ে বেড়ে ওঠা আরও যত চিরশিশু আছে, তারা আর কয়দিনই বা পারবে তাদের আকাক্সক্ষা দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে ?
ডাকছে, অবিরাম ঝিঁঝিঁ ডাকছে… এই বাড়িটা, এই এলাকাটা তো এক ঝিঁঝিঁর খনি। ঝিঁঝিঁর খনি, ইলিশ পোকার খনি। সন্ধ্যা নামলেই বোঝা যায় তাদের রাজত্ব কত বিশাল। ঝিঁঝিঁ ডাকা এই বিরান গাঁয়ে, মাটির তলের ওই ঝিঁঝির ঘরে সোনার মতো এই মানুষটা গিয়ে থাকবে কেমন করে ? কেউ কি থাকতে পারে ?
আহ্, যদি আমি পারতাম কাঁদতে! খানিকক্ষণ শান্তিমতো কাঁদতে!
অনাথ অন্ধকার ও প্রান্তের দিনলিপি
মোবাইল ফোনের যুগ আসারও বহুদিন পর আমার এক ভাবি মায়ের জন্যে একদিন সেই ফোন কিনে নিয়ে এল। মা তখনও একেবারে বিছানায় পড়েনি। তারপরও একটা হুইল চেয়ার কেনা হয়েছিল তার জন্যে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন সেটায় বসে পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ি তাকে ঘুরতে দেখা গেল, কিন্তু তারপরই সেটা চিরতরে ঠাঁই নিল ঘরের কোণে। সেটার চেয়ে বরং তিনি একটা ছড়িতেই যেন বেশি আস্থা খুঁজে পেলেন। সেই ছড়িতে ভর করে খানিকটা কুঁজো হয়ে তিনি এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। খোঁজখবর নিতেন তার সন্তানদের। তবে থাকতেন তার ছোট ছেলের সংসারেই―তার ভাষায়, ‘আমার শান্তর ঘরে।’
ততদিনে আমাদের জায়গাজমি সব কিছুই ভাগাভাগি হয়ে গেছে। যদিও ততদিনেও আমার শোনা হয়ে ওঠেনি, কীভাবে আমাদের সেই পূর্বপুরুষ হাজি সাহেবের বা আমার বাবার দাদার বাড়িঘর জায়গাজমি এইসব বণ্টন হয়েছিল। যদিও মাকে একদিন বলেছিলাম, তার কাছে থেকে রেকর্ড করে রাখব এইসব কথকতা। কিন্তু মাঝেমধ্যে টেপরেকর্ডার নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও কেন যেন সব দিনই আমরা চলে যেতাম এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গতে। ফলে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিতে হতো। টেপ আর কোনওদিনই শেষ হতো না কোনও ধারাবাহিক কথামালাতে। এক অর্থে, এইসব শোনার কিংবা রেকর্ড করার কিংবা লিখে রাখার কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু যত অর্থহীনতাই থাক, মাঝেমধ্যেই আবার মনে হয় যে, এ-ও কি হয় যে, আমি কোত্থেকে এলাম, কীভাবে এলাম, কাদের সঙ্গে এলাম, সেসবের কোনও কিছু জানি না ? এ ভারী অদ্ভুত ঘটনা, এই যে আমরা এত সচেতনতার দাবি করে থাকি, মানুষ হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ব করে থাকি, অথচ নিজেই জানি না, টের পাই না, নিজেই বলতে পারি না, এক সেকেন্ড পরে আমার জীবনে কী ঘটবে। তাই সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, একেকটি মানুষ আসলে একেকটি দীর্ঘ কিংবা নাতিদীর্ঘ কিংবা স্বল্পায়ু অতীতনামা। যা কিছুই সে অর্জন করুক না কেন, একসময় তা বিলীন হয়ে যায় কালের গহ্বরে; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করুণা করে যতটুকু বাঁচিয়ে রাখে তার বেশি সেই অতীত বাঁচতে পারে না। এই যে আমি মাকে বলেছিলাম, তার কাছ থেকে অতীতের কথাবার্তা শুনতে চাই, বলেছিলাম, তার অতীতের কথা যতদূর সম্ভব আমি লিখে রাখব, সেটা আসলে সেই বাঁচিয়ে রাখারই ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু যত সময় যাচ্ছিল, সেই ক্ষীণ প্রচেষ্টাও আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল।
এদিকে আমাদের সয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। সব ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকতে থাকতেই জমিজমা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো আমাদের মধ্যে তেমন কোনও দূরত্ব দেখা দেয়নি। সম্পত্তি ভাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বসবাসের বিভাজন পাকাপোক্ত হতে সময় লাগল বেশ। মা অবশ্য প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, জমিজমা সব কিছু ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তার ছোট ছেলের সংসারে থাকবেন। সেটা নিয়ে কেউ তেমন আপত্তিও তোলেনি। অন্য কোনও ছেলের বউয়ের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর যে তেমন একটা দূরত্ব কিংবা ফাটল ধরেছিল, তা কিন্তু নয়। বাড়িতে যারা থাকতেন, দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবারই মায়ের কাছে আসা-যাওয়া হতো তাদের। কিংবা মা-ই সেই ছড়িটায় ভর করে এর-ওর বাড়ি গিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে বসে থাকতেন। হয়তো ছোট ছেলের সংসারে তার পাতে একটি কলা পড়েছিল, সেটি তিনি না খেয়ে নিপুণভাবে রেখে দিতেন নিজের কাছে। তারপর ছড়িতে ভর করে অন্য কোনও ছেলের ঘরে গিয়ে হাজির হয়ে হয়ত তার বউকে বলতেন, নাও, এটা তোমার ছেলেকে খেতে দিও।
এই নিয়ে কখনও কখনও কথা কাটাকাটি হতো। ব্যাটার বউ তাকে বলত, ‘মা, আপনাকে খেতে দিয়েছে, আপনি খেয়ে ফেলেন না। নিয়ে এসেছেন কেন ? আমাদের দরকার হলে চেয়ে নিয়ে আসব।’
কিংবা তাঁকে হয়তো তাঁর মেয়ে কিংবা পুত্রবধূরা মুড়ি-মুড়কি দিয়েছে, নাড়ু দিয়েছে, দিয়েছে বিস্কুট, তিনি সেসব না খেয়ে যত্ন করে টিনের কৌটায় তুলে রেখে দিয়েছেন খাটের নিচে। তার পর দিব্যি ভুলে গেছেন। ব্যাপারটা ধরা পড়লে আবারও একপশলা ভালো-মন্দ বর্ষণ ঘটত তার ওপর, ‘আপনাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, না ? আপনি খাওয়া বাদ দিয়ে রেখে দিয়েছেন কেন ? আপনার কাউকে কিছু খেতে দেওয়ার ইচ্ছে বলবেন, আমরা নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসব। খাওয়া বাদ দিয়ে আপনাকে ওটা ওইজন্যে জমিয়ে রাখতে দিয়েছি নাকি ?’
তিনি চুপচাপ হাসতেন। কিংবা কখনও কখনও ফ্যাকাশে একটু হাসি দিতেন। এর বেশি কিছু না। যে আবেগ থেকে, যে নিষ্ঠা ও কুণ্ঠা থেকে তিনি এরকম করতেন, সেটা বুঝে ওঠা এত সহজ ছিল না। কিংবা বুঝতে পারলেও সেটা হজম করা এত সহজ ছিল না। এ নিয়ে কোনও ঝামেলা হতো না। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি নেমে আসত সব মিলিয়ে। জমিজমা ভাগ হয়েছে, গাছগাছালিও। কিন্তু তারপরও গাছগাছালির ফলটল আগের মতোই যার যখন যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে পেড়ে নিতো, খেয়ে ফেলত। ওরই মধ্যে যখন দেখা যেত যে, মা কোনও একটা গাছের কয়েকটি আম তার খাটের নিচে পানের ডালার মধ্যে রেখে দিয়েছেন আর বলছেন, ‘ওর ভাগে তো এই গাছ পড়ে নাই, এই আমগুলা ওর ছেলেদের দিও’, তখন অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা নেমে আসত পুরো ঘরজুড়ে।
এইসব ব্যাপার কখনও শুনেছি, কখনও শুনিনি। আর শুনলেও ঘটনাগুলোকে কখনও বড় বলেও মনে হয়নি। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে এখনও কীভাবে যেন সর্বংসহা একটা ব্যাপার রয়েই গেছে। বোধহয় তা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু প্রশংসার একটা উল্টো পিঠও আছে―সবাই সব সময় তা জানতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তা জানতে পেরেছিলাম। কলেজে পড়ার পর আমি একবার অনেক রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলাম শহর থেকে। সিরাজগঞ্জ থেকে সলপ আসতে তখন মাঝখানে মাত্র তিনটি স্টেশন―রায়পুর, কালিয়াহরিপুর আর জামতৈল। আমাদের কামরায় কেন যেন কোনও আলো ছিল না। তাই বলে যাত্রী যে কম ছিল, তা কিন্তু না। রায়পুর পেরুনোর পর একবার টিকিট চেকার এল। ছোট্ট একটা টর্চ লাইট জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সে যত না টিকিট চেক করল, তারও বেশি পাঁচ-দশ টাকার নোট হাতিয়ে নিল। তবে ওই টর্চ লাইটের স্বল্পালোকে বুঝতে পারলাম, অনেক যাত্রী দাঁড়িয়েও আছে এই মাঝরাতের ট্রেনেও। টিকিট চেকার চলে যাওয়ার পর আবারও নিঃসাড় অন্ধকার কামরাটাকে গ্রাস করে ফেলল। অন্ধকারে কাকে যেন বলতে শোনা গেল, ‘ভাই, ম্যাচ আছে ? কারও কাছে ম্যাচ আছে নাকি ভাই ?’
কিন্তু কাউকে সাড়া দিতে দেখা গেল না। অতএব ট্রেনের কামরাটায় যে একটু জ্বলন্ত সিগারেটের আলো দেখা যাবে, সে সম্ভাবনাটাও নিঃশেষ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে চলন্ত ট্রেনের শোঁ শোঁ আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছিল, তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম, এইখানে রেললাইনের দুই ধারে বেশ গাছপালা রয়েছে। কালিয়াহরিপুর স্টেশনে ওই ট্রেনটার থামার কথা নয়, তবু কার যেন অঙ্গুলি হেলনে স্টেশনের খানিকটা আগে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল আর স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল, অনেকেই চাল-ডালের বস্তা আর বাক্সপেঁটরা নিয়ে নেমে যাচ্ছে ট্রেন থেকে। তারপর জামতৈল স্টেশন আসার আগ দিয়ে কে যেন সলপের সান্যাল জমিদারদের গল্প জুড়ে বসল। অন্ধকার বলে লোকটার মুখ দেখতে পারছিলাম না, কণ্ঠও চেনা বলে মনে হচ্ছিল না। শুনতে শুনতে একটু ঝিমুনি ধরেছিল। কিন্তু হঠাৎ ঝাঁকুনি লেগে সোজা হয়ে বসতে বসতে টের পেলাম, তার গল্প এখন আমাদের পরিবারের হাজি সাহেবে এসে থেমেছে। হাজি সাহেবের বয়ান শুনতে আমার ভালোই লাগছিল। আর নিজের পূর্বপুরুষের প্রশংসা শুনতে কারই না ভালো লাগে! কিন্তু ওর মধ্যেই কে যেন নাক গলালো, ‘ধৈর্য―আসলেই ধৈর্য আছে তাদের। তারা যে খারাপ কাজটা করে, সেটাও খুব ধৈর্য ধরেই করে।’
‘তা ধরেন। খারাপ ভালো মিলায়েই তো মানুষ। তাদেরও নিশ্চয়ই খারাপ ভালো আছে। তবে ওইটা, আমি বলব, বলার মতো না। ধরেন, একজন লোকের মানুষজনের সামনেই নাকের মধ্যে আঙুল দিয়ে ঘাটাঘাটির অভ্যাস। আবার আরেকজনের মেয়েমানুষের ওপর চড়াও হওয়ার অভ্যাস। এখন এই লোকের তুলনায় নাকে আঙুল দেওয়া মানুষটাকে তো ফেরেশতাই বলা যায়। না কি বলেন ?’
‘তা তো অবশ্যই। সেই জন্যেই তো বলছি, তারা যে খারাপ কাজটা করে, তাও খুব ধৈর্য নিয়েই করে। এত ধৈর্য নিয়ে এত সময় নিয়ে কাজটা করে যে, মানুষজন টেরই পায় না, একটা খারাপ কাজ হয়ে গেল। অনেক সময় বেকায়দায় ফেলেও স্বার্থসিদ্ধি করে। এমন বেকায়দায় ফেলে যে কারও কাছে আর বলার উপায় থাকে না, আমার তেইশ মারা গেছে!’
‘কীরকম ?―কীরকম ?―একটু খুইলা কন তো ঘটনাটা।’
কেমন একটা রহস্যময় তরল হাসির আভাস পাওয়া গেল। লোকটা কিছু বলবে কি না বুঝে ওঠার আগেই ট্রেন এসে থামল সলপ স্টেশনে। আর সেটা টের পেয়ে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ধাক্কাধাক্কি করে মানুষজন ঠেলে দ্রুত চলে গেলাম দরজার কাছে। কিন্তু সেখানেও লোকজন। বলতে গেলে একরকম গায়ের জোরেই নেমে পড়লাম। আর নামতে না নামতেই ট্রেন চলতে শুরু করল। তখন আরও দু-চারজনকে দেখলাম চলতি ট্রেন থেকেই প্লাটফরমে পা ফেলতে। কেন যেন মনে হলো, ট্রেনে হাজি সাহেবকে নিয়ে গল্প বলা মানুষজনগুলোও আছে এদের ভেতর।
বয়স কম ছিল, ছাত্র ছিলাম; ঘটনাটাকে তেমন বড় করে ভাবিনি। একবার ভাবতে গিয়ে ব্যাপারটাকে এই বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম যে, মানুষের যখন প্রভাব-প্রতিপত্তি আর সম্পদ হয়, তখন তাকে ঘিরে এমন অনেক ঘটনাও ছড়িয়ে পড়ে―যা থেকে মনে হয়, এরাও লোভী, নিষ্ঠুর আর কদর্য ছিল। এই ভেবে ঘটনাটা আসলে ভুলেও গিয়েছিলাম।
এমনকি একসময় নিজের গ্রামটিকেও ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু ভুলে যাওয়া কি আর অত সহজ ? একদিন এই গ্রামেই ফের আমাকে ফিরে আসতে হলো। চাকরিবাকরি নেই। সংসার শুরু করেছিলাম অনেক দেরি করে। কিন্তু সেই সংসারও তখন বলতে গেলে ভেঙেই গেছে। এমন কঠিন সময়, রাজধানী থেকে তখন দূরে থাকাই ভালো মনে হলো। দুম করে নয়, হঠাৎ করে নয়, পরিকল্পিতভাবেই একদিন তখন গ্রামে চলে এলাম।
অবশ্য কী করে যেন ততদিনে গ্রামে আমি একটা ঘর বানিয়ে ফেলেছি। সারা বছর সেখানে ছোট বোনটা স্বামী-ছেলে নিয়ে থাকে। আমি মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে গিয়ে তাদের জন্যে ঝামেলা তৈরি করি। কিন্তু এবারের ঝামেলাটা বোধহয় একটু বেশিই হয়ে গেল। আমি দিনের পর দিন থাকতে শুরু করলাম। গ্রামে থাকলে ছোট বোনের বাড়ি, ঢাকায় থাকলে মেজো বোনের বাড়ি। অবশ্য ভালো কোনও বিকল্পও ছিল না আমার হাতে। পূর্ণ বেকার আমি। সকালে নাস্তা করি। তার পর মায়ের ঘরে গিয়ে বসি। মায়ের নাস্তাপাতি অবশ্য তার আগেই হয়ে যায়। তিনি ছড়িতে ভর করে বারান্দায় গিয়ে মাদুর বিছিয়ে বসে থাকেন। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে কখনও সেই মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে পড়েন। আর আমি গিয়ে তার বিছানাটা ফের ঝেড়েঝুড়ে চাদর পাতি। ঘরটায় ঝাড়ু দিই। আর মায়ের কাছ থেকে কথাবার্তা শোনার প্রস্তুতি নিই। সেইসব কথা―যা তার হয়তো বলা হয় না। যা তার হয়ত বলতে ইচ্ছে করে না। যা হয়ত কেউ শুনতেও চায় না। আরও একটা কাজ করার চেষ্টা চালাই আমি। ভাইবোনদের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের কাছে ফোন করে মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিই। ভাবতাম, তারও নিশ্চয়ই ভালো লাগে আপনজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। কিন্তু লক্ষ করি, বেশিক্ষণ তিনি মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলতে পারেন না। হাঁপিয়ে ওঠেন, বিরক্ত হন। তার পরও আমি হাল ছাড়ি না। মায়ের সঙ্গে কথা মনে থাকলেও প্রাত্যহিক জীবনের চাপে যারা কথা বলার সময় বের করতে পারে না, তাদের যেনবা বাধ্যই করি কথা বলতে। আর মাকেও বলি, ‘মা, আপনাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে।’
‘হু-হ, মোবাইল ফোন! এইসব লাগবে না আমার!’
আমি কোনও কূলকিনারা করার আগেই ভাবি তার জন্যে একটা মোবাইল ফোন কিনে নিয়ে এলেন। মা কিছুদিন তা ব্যবহারও করলেন। তারপর একদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ছড়িতে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবির রান্নাঘর অবধি গিয়ে ফোনটা মাটির মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলেন। বললেন, ‘এইটা ভারী যন্ত্রণার জিনিস বউমা। এ জিনিস তারচে তোমরাই রেখে দাও।’
মা আরও খানিকক্ষণ নাকি বসেছিলেন সেখানে। কিন্তু ফোন নিয়ে আর কোনও কথা হতে দেননি। ভাবিও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল, কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। ব্যবহার করবেন না যখন বলে বসেছেন, কোনওদিনই ওটা নিঃসন্দেহে আর হাতে নেবেন না। আমাদের এই গ্রামের বাড়িটাতে আর কিছু না হোক, সকাল বিকাল দুই-চারটা শালিক, চড়াই কিংবা দইনাচা পাখি এসে নাচানাচি, ঘোরাঘুরি করে উঠানটাতে। তিনি তেমনই একটা শালিকের দিকে তাকিয়ে থাকেন বেশ খানিকক্ষণ। তারপর নাকি বলেন, ‘পাখিগুলাক মাঝেমধ্যে দানা-টানা দেও তো বউ মা ?’
এই পর্যন্তই। তার পর নিজেই আবার উঠে রওনা হন অন্য কোনও ছেলের বাড়ির দিকে, অন্য কোনও ছেলের বউকে হয়তো একটা কিছু বলতে।
এখন বুঝতে পারি, একটা সময় ছিল, যখন শুধু মার ওপরেই নয়, বাবা আর মা―তাদের দুজনের ওপরেই উগ্র অন্ধ কী এক ক্রোধ কাজ করত। সেই ক্রোধের উৎস এখন স্পষ্ট বুঝি। আসলে টাকাপয়সা―টাকাপয়সার সংকটই তাদের সঙ্গে ঘোরতর এক দূরত্ব তৈরি করে দিতে শুরু করেছিল। বেশ ছোটবেলার কথা এখনও মনে পড়ে, বড় দুই ভাই যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তার পর ? কী করবেন ? কোনখানে যাবেন ? ভাইদের আনা অস্ত্রশস্ত্র বেশ কিছুদিন জমে ছিল দালানের খাটের নিচে। কিন্তু একদিন কাঠাল গাছের ফাঁকে পাখির বাসায় ডিম খুঁজে পাওয়ার মহাউত্তেজনা নিয়ে বাড়ির গেইট দিয়ে ঢোকার আগেই দেখলাম, ভারী অস্ত্রশস্ত্রগুলো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে এগুতে এগুতে ক্রোধোমত্ত বাবা বার বার দোল খাচ্ছে, বার বার কষ্ট করে টাল সামলাচ্ছে আর রাগে তার কথা বুজে বুজে আসছে, ‘কতদিন―কতদিন আর এইসব শয়তানের সম্পদ ঘরের মধ্যে জমায়ে রাখতে চাও ? জমা দিতে ভালো লাগে না ? ক্যান, মুজিব কয় নাই, অস্ত্র জমা দিয়া দিতে ? কয় নাই ? যুদ্ধ করেছো―দেশ স্বাধীন করেছো, বেশ করেছো। আমাকে উদ্ধার করেছো। জাতিকে উদ্ধার করেছো। দেশকে উদ্ধার করেছো। আমি কৃতজ্ঞ। … … বুঝছো ? আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এইসব ক্যান ? ঘরের মধ্যে এইসব ক্যান ? এগুলো জমা দিতে পারো না ? এইগুলো তো শয়তানের সম্পদ―এতদিন দরকার ছিল, ব্যবহার করেছো। এখন ক্যান এসব রাইখতে চাও ? চাচাদের শয়তানি তোমাদের মাথায় ভর করতেছে ?’
এমন ক্রুদ্ধ বাবাকে আমি জীবনে আর কোনওদিন দেখিনি। না সেই দিনের আগে। না সেইদিনের পরে। তাঁর সেই ক্রোধের সামনে দাঁড়ায়, তেমন সাধ্য কার আর আছে ? মুক্তিযোদ্ধা এক ভাইকে কোথাও দেখলাম না, আরেক ভাইকে দেখলাম গোয়ালঘরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাচাদের শয়তানি বলতে বাবা কী বুঝাতে চাইছেন, তা একদমই ধরতে পারলাম না। তবে দেখলাম ছেঁচরাতে ছেঁচরাতে রাইফেল, স্টেনগান, এলএমজি, গ্রেনেড সব কিছু নিয়ে তিনি ফেলে দিলেন বাড়ির পাশের ডোবার ভেতর। তার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘যা, সলিল সমাধিতে যা।’
টলতে টলতে তিনি আবারও বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলেন। জোরে জোরে শ^াস নিচ্ছিলেন, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তখনও স্কুলে যেতে শুরু করিনি, তবে ক্লাস ওয়ানের বইপত্র বাড়িঘরেই পড়ি। অবাক হয়ে দেখছিলাম বাবাকে। দেখছিলাম, হঠাৎ গোয়ালঘরের কোণে ভাইকে দেখতে পেয়েই আবার যেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, ‘জ্যান্ত ফিরছিস ক্যান ? মরতে পারিস নাই ? মরার জন্যেই তো পাঠাইছিলাম। বলছিলাম, না, যাইস না ? যুদ্ধে যাইস না ? এখনও বেঁচে আছিস ক্যান ? মানুষ মারতে শিখে আসছো―মানুষ না মারলে এখন আর ভালো লাগে না ?’
বাবার সেই মূর্তি দেখে আমি এত ভীত হয়ে পড়লাম, কী বলব, মাধবীলতার গাছভর্তি এত কেন্নো, এত ছ্যাঙ্গা, তবু সেই মাধবীলতার গোড়ার সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আর হঠাৎ বাবা আমাকে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন, ‘সব উচ্ছন্নে যাবে―সব। পারব না, আমি আর কাউকে মানুষ করতে পারব না। এই ছোটগুলোকেও না!’
এখন এই দিনপঞ্জি লিখতে লিখতে, ডায়েরি লিখতে লিখতে একটু একটু করে টের পাচ্ছি, কী ভীষণ কষ্টে জ্বলতে হয়েছে তাঁকে ওইসব দিনগুলোয়। ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। যুদ্ধ তাদের পুরোপুরি না পারুক, খানিকটা হলেও পাল্টে দিয়েছে। তারা পারছে না সুবোধ, নিরীহ ছাত্রের মতো কলেজে ফিরে যেতে, আবার পারছে না দেশের জন্যে এমন কিছু করতে, যাতে নিজেদেরই ভালো লাগে। নিজেদের কাছে নিজেদেরই বিরক্ত লাগছে এখন তাদের। নিজেদের কাছে বিরক্তিকর, বাবা মায়ের কাছে আবার প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার। কোনদিকে যাবে তারা!
পরে শুনেছি, পরে সেই অস্ত্রশস্ত্র ডোবা থেকে তুলে আটবাকির মজু গাড়োয়ানের গরুর গাড়িতে করে থানায় নিয়ে গিয়ে সেইদিনই জমা দিয়ে এসেছিল দুইভাই। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র জমা দিলেই কি আর সমাধান মেলে ? মিলল না। ভাইরা কলেজে যাবে, হোস্টেলে থাকবে, টাকা পাওয়া যাবে কোনখান থেকে ? এদিকে অস্ত্র যে তারা জমা দিয়েছে, সে কথা বিশ^াসই করতে চায় না অনেকে। যারা এরই মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে দু-চার পয়সা কামাতে শুরু করেছে, তারাও দেখা গেল ঘোরাফেরা শুরু করেছে অস্ত্রের জন্যে। তাদের দাবিও কম যৌক্তিক নয়―‘নিজেরা তো কোনও কিছু করতে পারবি না, খালি খালি ওইগুলো মাটির নিচে রেখে নষ্ট করবি কেন ? তার চেয়ে আমাদের দিয়ে দে, করেকম্মে খাই।’ এইসব বলে বটে, কিন্তু জোরাজুরিও করতে পারে না শক্তভাবে; ভয় করে, যদি সত্যিই অস্ত্রশস্ত্র জমা না দিয়ে থাকে ? যদি রেগেমেগে ঠা ঠা করে দু-চারটা গুলি বসিয়ে দেয় বুক বরাবর! অতএব বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। অমীমাংসিত থাকতে থাকতে তামাদি হয়ে যায়। আর আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, আচ্ছা, ঠিক এরকমই কি ঘটেছিল ? নাকি ভুলে গিয়ে এলোমেলো অন্য কিছুও মিশিয়ে ফেলেছি ঘটনার সঙ্গে ?
কোনও কিছু যখন স্মৃতি হয়ে যায়, তখন এই এক সমস্যা এসে সামনে দাঁড়ায়―স্মৃতি-বিস্মৃতি একাকার হয়ে যায়। বার বার স্মৃতির নির্মাণ-বিনির্মাণ ঘটতে থাকে, যেমন নির্মাণ-বিনির্মাণ ঘটতে থাকে বিস্মৃতিরও। আমরা যে বলি, জাদুবাস্তবতা―তা আসলে এই―স্মৃতি-বিস্মৃতির জড়ন-বিজড়নের খেলা, নির্মাণ-বিনির্মাণের খেলা। আমি সেই খেলার পুতুল।
দুই
তবে এই স্মৃতিটায় এখনও কোনও খাদ লাগেনি―মায়ের জানাজায় অসংখ্য মানুষের অবিশ^াস্য উপস্থিতি আমাকে বিস্মিত করেছিল। শুধু আমাকে কেন, আরও অনেককেই।
বাবা, কিংবা আরও পরে আমাদের সেজো ভাইটি যখন বলতে গেলে বিনা নোটিশে বিদায় নিলেন, তখন তাদের জানাজায় যে অংসখ্য মানুষ হবে, সেটা আমাদের বেশ ভালো করেই জানা ছিল। বাবা যদিও আমাদের জেঠামিয়ার মতো, মায়ের মিয়াভাইয়ের মতো চেয়ারম্যান ছিলেন না, দরবার-সালিশেও যেতেন না খুব একটা, তবু কী এক স্বাতন্ত্র্য তাঁকে নীরব জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। আর সেই জনপ্রিয়তাকে এক থির মাত্রা দিয়েছিল তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। শুনেছি, ক্লাস নিতে গিয়েও তিনি এত জোরে হাসতেন যে অনেক দূরের ক্ষেতখোলা থেকেও শোনা যেত সেই হাসি। তখন চাষিরা ক্ষেতের কাজকর্ম থামিয়ে কাছা খসিয়ে হুকা টানতে বসত আর বলত, ‘হাজির নাতি কেলাস নিতেছে।’
অথচ আব্বা আমাদের কাউকেই কোনওদিন পড়তে বসাননি, পড়ার জন্যে চাপাচাপি করেননি, ফিরে তাকিয়েও দেখেননি পড়াশোনা করতে বসেছি নাকি আড্ডা দেয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে।
তা যা হোক, মায়ের জানাজায় অত মানুষের উপস্থিতি আমাকে অবাক করেছিল। এটা আমি ভালো করেই জানতাম, আমার মাকে অনায়াসেই তুলনা করা যায় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সেই নানির সঙ্গে, যিনি কি না রান্নাঘরে তার রান্নার কড়াইয়ের দিকে তাকিয়েও খবর রাখতে সক্ষম ছিলেন সারা দিনদুনিয়ার। আমার মা তার সর্বংসহা স্থিরতা দিয়ে অদৃশ্য এক সেতুমালা গড়েছিলেন আমাদের পুরো তল্লাটে। কীভাবে তাঁর এই প্রাপ্তি ঘটেছিল, তা আমরা কেউই জানি না। কিন্তু ঘটেছিল। গাঁয়ে কার ঘরে কী ঘটছে, এমনকি কার সংসারে অবৈধ সম্পর্ক ও ভাঙনের সূচনা ঘটেছে, সেটাও তিনি জেনে যেতেন নিজের রান্নাঘরে বসেই। কৈশোরেই এটা আমি আঁচ করতে পারি। বছরের ১২ মাসের নয় মাসই বলতে গেলে অসুস্থ থাকতাম বলে মা ছাড়া আমার অন্য কোনও বৃত্ত ছিল না। আমি দেখতাম, ভিক্ষা করার জন্যে যে মহিলাটি আসত অনেক দূরের কোনও এক গাঁও থেকে, তার সঙ্গেও মায়ের পরিচয় রয়েছে। সে বসে বসে তার সুখদুঃখের কথা উগরে দিচ্ছে মায়ের কাছে। মা শুনছে আর নিজের কাজ করে চলেছে। কিছুই বলছে না, শুধু শুনে চলেছে আর নিজের কাজ করছে। এইসব স্মৃতি থেকে, এখন আমার মনে হয় যে, মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা আসলে তার শুনবার ক্ষমতা। আর মনে হয়, কোনও মানুষই চায় না, তার কোনও কথা গোপন থাকুক। সে আসলে তার সবচেয়ে গোপন কথাটিও কাউকে না কাউকে শুনিয়ে যেতে চায়। কারও না কারও কাছে জমা রেখে যেতে চায়। যখন সে নিশ্চিত হয়, এখানে তার গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে, সেখানে সে তার সেই ঘটনাটিও অকপটে বলে যেতে পারে, যেটি সে নিজেও দ্বিতীয়বার আর হয়তো মনে করতে চায় না। মানুষের লিখিত ইতিহাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক হলো, ব্যক্তি-পরম্পরায় চলে আসা অলিখিত এই স্মৃতি ইতিহাস। আমার মা তেমনই এক ইতিহাসের আধার। কেবল গাঁয়ের নারীরা কেন, অনেক বয়সী পুরুষকেও দেখতাম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, সসংকোচে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে পা গুটিয়ে বসে আছেন, মা ঘরের ভেতরে বসে বসে শুনছেন তার কথা। কী করে তিনি বুঝতেন, এবার স্পর্শকাতর কোনও প্রসঙ্গ উঠবে, তাও জানি না; অকস্মাৎ তিনি আমাকে আর সেখানে উপস্থিত অন্য সবাইকে হয়তো বলতেন, ‘তোমরা একটু যাও তো বাবা, আমি একটু কথা বলি ওনার সঙ্গে…’
জানাজা থেকে ফেরার পর সারা রাত আমার মনে হলো, মায়ের বিয়ের দিনের কথা। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাদের স্কুলের ছাত্রী বাদল সেদিনের সেই বিয়েতে এসেছিল ঘাগরা পরে। ঘাগরা পরে নেচেছিল সে। নাচতে নাচতে কী গান গেয়েছিল, মায়ের সেটা একটুও মনে নেই আর। বাদলের চেহারাও তার মনে নেই আর। মনে নেই, বাদল, তার সহপাঠিনী বাদল তার গলা জড়িয়ে কেঁদেছিল কি না। কিংবা এও তার আর জানা নেই, বাদল এখনও এ দেশেই আছে, নাকি চলে গেছে ওই বাংলায়।
আচ্ছা, স্মৃতি সংরক্ষণ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি-বিস্মৃতির নির্মাণ-বিনির্মাণ ? নাকি আরও গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকে হত্যা করা কিংবা স্মৃতির মরে যাওয়া ?
আমি অন্ধকারে দুই হাতের আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ করে কপালে ঠেকিয়ে মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে কতক্ষণ যে বসেছিলাম আর কখন যে ভোরের পাখি ডেকে উঠেছিল, কিছুই মনে নেই।
তিন
একটু ধাতস্থ হওয়ার পর আমার মনে হলো সোহার কথা। আর তা বোধহয় ভোরের আলো এসে আমাকে স্পর্শ করল বলেই। সারা রাত আমি যে ঘরটায় ছিলাম, সেটা আসলে মূল বাড়ির পেছন বাড়ি। দুই অংশের মাঝখানে দূর অতীতে ছিল সরকারি এক নয়ানজুলি। কিন্তু দিনকে দিন সেটা ভরাট হয়েছে; অতএব বাড়ির পেছনের অংশ আর মূল অংশের উঠোন আর মাঠ একই সমতলে এসে দাঁড়িয়েছে। একসময় পেছনের এই অংশে আগাছা আর জঙ্গল ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন সেসব বেশ কমে গেছে। আর দুই-তিন কামরার একটি ঘর উঠেছে। ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালে দুই পাশে খোলা ফসলের মাঠ আর জলাভূমি। আরেক পাশে বাড়িঘর আছে বটে, কিন্তু এই গাছ সেই গাছ সেগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। সবুজ-সবুজে লেপা পাতার দেয়াল ছাড়া কিছু আর চোখে পড়ে না।
মাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে আমার বাবা, চাচা আত্মীয়স্বজনকে হাঁটতে হয়েছিল টানা ২৪ যোগ ২৪ মিলে ৪৮ মাইল। সোহাকে নিয়ে আসতে অবশ্য সেরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। আমরা আমাদের সুবিধামতো বিয়েটা করে নিয়েছিলাম। তখনও ঢাকার বাইরে চাকরি করে সে। গ্রামের বাড়িতে যাব, যাব করেও মাস পেরিয়ে গেল। তারপর একদিন আমি বাসে চড়ে বসলাম রাজধানী থেকে, সোহাও তার চাকরিস্থল থেকে বাসে চড়ে রওনা হলো গ্রাম-গ্রামান্তরের সেই বাসস্ট্যান্ডের দিকে। বাসস্ট্যান্ডে এক হয়ে আমরা রওনা হলাম মায়ের বাড়ির দিকে, নিজেদের ঘরের দিকে কিংবা মা অথবা আমাদের কারওরই না―নিতান্তই আত্মীয়কুলের বাড়িঘরের দিকে।
মা কি কষ্ট পেয়েছিল ?
এই কথা কোনওদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। একবার শুধু বিড় বিড় করে বলতে শুনেছিলাম, ‘দুই-দুইবার বিয়ে করলে বাবা, একবারও একটা পটকার আওয়াজ শুনলাম না, একবারও বাড়িঘরে সাজগোজ দেখলাম না।’
বিয়েতে খানিকটা হলেও সাজগোজ করতে হয় বলে আমার আব্বার লেগেছিল দুই দিন। একদিন তো যেতে যেতেই পেরিয়ে গিয়েছিল; মা আবার ঘুমিয়েও পড়েছিল সন্ধ্যা পেরুতে না পেরুতেই। ঘুম অবশ্য ভাঙানো যায়; কিন্তু এইভাবে বিয়ে হয় নাকি ? অতএব বরযাত্রীর দলও সারা রাত ঘুমালো। পরদিন সকালেও তারা আয়েশ করে নাস্তা করল। তারপর বিয়ের সাজসজ্জা শুরু হলো বটে, কিন্তু বিয়ে হতে হতে আবারও সন্ধ্যা নেমে এল ঝুপ করে। তা হলে বরযাত্রী ফের যায় কেমন করে! ? এখন এ কথা বললে লোকজন অবশ্য হাসাহাসি করবে। সলপ থেকে মৈত্রবাধা এখন দিনের মধ্যে কয়েকবার আসা-যাওয়া করা যায়। কিন্তু এখন আর তখন কি আর এক ? অতএব তাদের রাতেও থাকতে হলো।
কিন্তু বাসর হয়েছিল কি ? এই প্রশ্নের উত্তর মা কখনই সরাসরি দেননি। শুধু হাসতেন, ‘ছোট মানুষের বিয়ে হয়েছে, তার আবার বাসর!’ সকালে নাস্তার পর পালকিতে করে বাড়ি থেকে গেলেন নদীর ঘাটে। নৌকার পালে হাওয়া লাগল, নৌকায় করে তারা এসে নামলেন নলসোন্দার নদীঘাটে। খুব তাড়াতাড়িই আসতে পেরেছিলেন বলতে হবে, কারণ বাতাস ছিল ভীষণ। আর মাঝিরা তাই বাদাম উড়িয়ে দিয়েছিল। একটানে জোহরের নামাজের পরপরই এসে পৌঁছেছিলেন তারা নলসোন্দার নদীর তীরে।
অতীতের এইখানটায় এসে মায়ের মুখে বারবারই কেমন সলজ্জ হাসি ফুটে উঠত, তবু তিনি বলতেন উচ্ছ্বসিত কিন্তু আত্মমগ্ন স্বরে, ‘কিন্তু এখন বাড়ি ফিরবে কেমন করে ? যাওয়ার সময় তো সবাই হনহনিয়ে পায়ে হেঁটেই গেছে। কিন্তু এখন তো সঙ্গে বাড়ির বউ―তাকে কি আর হাঁটিয়ে নেয়া যাবে ? তার ওপর জমিদারবাড়ির আলাদা একটা মর্যাদা আছে না ? এদিকে এমন এক জমিদারবাড়ি সেটা তখন যে, তাদের আর কোনও পালকিবহর নাই। পালকি নাকি ছিল―পালকির সর্দাররা ছিল বলেই তো তোমাদের ওই পুকুরের কোণের জায়গাটার নাম সরদারবাসা হয়ে গেছে। মানে ওইখানে পালকির সরদাররা এসে পালকি নামাতো, ছাপরাঘর ছিল―সেই ছাপরাঘরে শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতো। কেমন যে ছিল এই জায়গা-বাড়িঘর! সব এখন কেমন পাল্টে গেছে। আমার বড় বাবাশ^শুর মারা গেলেন, এ বাড়ির জৌলুসেও যেন মরচে পড়তে লাগল। এর আগেও বলেছি এ কথা, না ? কী বলব! বারবার একই কথা ঘুরেফিরে আসে!’ মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে মা আবারও বলে চলতেন, ‘ডাক্তার সাহেবের ছেলেদের―ওই মিয়া ভাইদের সুনাম ছিল, বিচারআচার হলেই তাদের ডাক পড়ত―খালি এই গ্রামে না, এই থানায় না, আশপাশের থানাগুলোতেও। আর দারোগা সাহেবের ছেলেদের কথা আর কী বলব, যাত্রাদল, নৌকা বাইচের দল, গানের দল―একেক সময় একেকটা নিয়ে তারা মেতে থাকত সারাটা বছর। কিন্তু জৌলুস ব্যাপারটা তো অন্যরকম―এইসবে জৌলুস ছিল না, একপক্ষের গুরুত্ব ছিল, আরেকপক্ষের ছিল অপচয়―কিন্তু জৌলুস ছিল না। বাড়ির ঝি-বউদের চলাফেরার জন্যে একটা পালকি দরকার না ? অথচ সেই জিনিসটাই নাই। মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করারই আর কেউ নাই। মানে মেয়েদের আবার চলাফেরা কিসের ? পরের বাড়ি থেকে যে মেয়েটা এসেছে, একবারেই তো চলে এসেছে, তার আবার অন্য কোনওখানে যাতায়াতের দরকার কিসের ? আর নিজের ঘরে যে মেয়ে আছে, সে যখন যাবে, একবারে চলে যাবে, স্বামীর বন্দোবস্তেই তো যাবে, ও নিয়ে আর চিন্তার কী আছে ? মানে, ভাবখানা এরকম আর কি। শোনো, তোমরা যেন এইরকম কোরো না। এই একটাই আমার সারা জীবনের দুঃখ, তোমাদের আব্বা আমাকে নিয়ে একবারও আর আমার বাপের বাড়ি গেল না। আমাকে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা―নিজেই তো গেল মাত্র আরেকবার, তাও বাবার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর। তোমরা যেন এইরকম হয়ো না। বউ যখনই বাপের বাড়ি যেতে চায়, যেতে দিবা…’ বলতে বলতে মায়ের যেন শ^াসকষ্ট হতে থাকত। কিছুক্ষণ একেবারেই চুপসে যেতেন তিনি। তারপর আবারও বলতে থাকতেন, ‘নৌকা থেকে বরযাত্রীরা একে একে নেমে যেতে লাগল। কিন্তু মিয়া ভাইরা কি আর যেতে পারে ? তারা বলাবলি করে, ভাড়া গাড়ি কোনখানে পাওয়া যায় ? এদিকে কারও গরুর গাড়ি নাই ? পালকি নাই ?’ তখন থেকেই কিন্তু মাতব্বর-মাতব্বর স্বভাব মিয়া ভাইয়ের। তিনি খোঁজ লাগালেন লোকজনকে দিয়ে। নৌকায় থাকলাম আমি। আরও থাকল মিয়া ভাই, থাকল ওই দারোগা সাহেবের মেজো ছেলে।’
‘আব্বা কোথায় ছিল ?’
আবারও সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে মায়ের মুখে, ‘ছিল আর কি―কোনখানে আর থাকবে, ওইখানেই ছিল, নৌকার গলুইয়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল … কী সব যে শুনতে চাও না! কথা শুনে বাঁচি না। … কিছুক্ষণ পর মিয়া ভাই আবারও নৌকা থেকে নেমে হাঁটতে লাগল। একবার এদিক যায়, আরেকবার ওদিক যায়। ১২ বছর পাঁচ মাস বয়স আমার। ভারী কৌতূহল সব কিছুতেই, কিন্তু কী আর দেখব ? আমার কি আর তখন নৌকা থেকে নেমে আশপাশের ঝোপঝাড়ের কোনটায় হাস ডিম পেড়েছে আর কোনখানে বনমোরগের বাসা আছে, এইসব দেখার উপায় আছে ? তাই চোখ দুইটা ঘুরাই আর চিন্তা করি, এরা করে কী ? দেখি, একজোড়া বেহারা একটা ঢুলি নিয়ে কোথাও যাচ্ছে দেখে মিয়া ভাই যেন আত্মা ফিরে পেলেন। দৌড়ে দৌড়ে ডাকতে লাগলেন তাদের। তারপর আমাকে তুলে দিলেন সেই ডুলিতে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস, কাঁঠালপাকা গরম পড়েছে। ওই ডুলির মধ্যে থাকা যায় নাকি ? পথে তাই ডুলিকে থামতে হলো বেশ কয়েকবার। ডুলি থামে, পর্দা তুলে দেয়, একটু গরম কমাই, তারপর আবারও ডুলির পর্দা তুলে দেয়। এদিকে শাড়ি পরে আছি―’
‘শাড়ির ওপর বোরখা ছিল মা ?’
‘না―বোরখা ছিল না। নতুন বউ বোরখা পরে নাকি ? এইসব এখনকার ঢকডিল, সেজেগুঁজে, ওপরে আবার একটা বোরখা পরা! তাহলে আর সাজবার দরকার কী ? আমি পরেছিলাম মেঘদূত শাড়ি। আমার শাশুড়ি মা টাকাপয়সা দিয়েছিল, মিয়া ভাই নিজে পছন্দ করে বিয়ের বাজার করেছিল। কী যে নামডাক ছিল তখন ওই মেঘদূত শাড়ির!’
শাড়ির নামটা মনে আমার এখনও গেঁথে আছে। এতই নিবিড়ভাবে যে বিয়ের শাড়ির কথা উঠলেই আমার মেঘদূত শাড়ির কথা মনে পড়ে। যে শাড়ি কখনও দেখিনি, সেই শাড়ির জন্যে মনজুড়ে বৃষ্টি নামে।
চার
কখনও কখনও ভাবি, মা-বাবার এই বিশ^স্ত, মেদহীন দাম্পত্যজীবন অন্তত আমার জীবনকে অস্থির, টালমাটাল করে দিয়েছে। এই জীবনে যে কোনও ফাঁক থাকতে পারে, কোনও শূন্যতা থাকতে পারে, তা আমি কোনওদিন অনুভব করিনি। শৈশব থেকেই তা ছিল আমার একেবারে অজানা। তাই অবিশ^স্ততার বিন্দুমাত্র সংকেত আমাকে অস্থির করে দিয়েছে। বিয়ের আগে, যে জীবনে যৌনতাকে ঘিরে কৌতূহল থাকে, উদগ্রতা থাকে, দ্বিধাও থাকে―সেসবকেও আমি হত্যা করতে চেয়েছি অবিশ^স্ততার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; কখনও আবার নিজের অজান্তে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে এমন কিছু করে বসেছি, যাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। কচুপাতার দিকে তাকিয়ে নিমগ্ন থেকে জলবিন্দু গড়িয়ে পড়া দেখতে দেখতে আমি চেয়েছি নিজেকেই হারিয়ে যেতে দিতে। আবার একসময় পৃথিবীর সমস্ত অবদমনকে সঞ্চিত করে চেয়েছি পৃথিবীকেই উপহাস করতে।
অতএব এই নিয়ে আমি খুব এলোমেলো হয়েছিলাম, আমি যে বিয়ে করছি, মা এই ঘটনাকে কীভাবে নেবেন। কিংবা আমার মনে হয়েছিল সেই দিনের কথা, যেদিন আমি তাকে বলেছিলাম, আমি আপনাদের বউমা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি।
আমি জানি না, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনে কী ঘটেছিল। আমি যে ফের বিয়ে করতে এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেরকম না। আমি আসলে সেইসব নারী-পুরুষের মতো থাকতে চাইনি, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিচ্ছিন্ন থাকতে শুরু করে; অথচ অলিখিত, অদৃশ্যমান কোনও সুবিধার জন্যে আবার অফিসিয়ালি একজন আরেকজনকে ত্যাগ করে না। এটা ঠিক, দিনের পর দিন আমি এইভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন কাটিয়েছি। মা কোনওদিন এ নিয়ে আমাকে কোনও প্রশ্ন করেননি। যেন তার জানাই ছিল, কী ঘটছে, কী ঘটতে চলেছে। ‘তালাক দিচ্ছি’ শুনে তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।’ অনেক অনেক দিন কেটে গেল, বেশ কয়েকটা বছর। আবারও যখন বিয়ের কথা তুললাম, একটু চুপ থেকে সেই আগের মতোই তিনি বললেন, ‘সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা।’ সৃষ্টিকর্তা, ঈশ^র,―এসব তিনি এত অনায়াসে বলতেন যে, আমি বিস্মিতই হতাম। অথচ তিনি একটুও দ্বিধা না করেই বলতেন এইসব।
একটু থেমে তিনি আবারও বলেছিলেন, ‘তালাক দেওয়া হয়ে গেছে ?’
‘হয়ে গেছে। আপনাকে বলেছিলাম তো। তবে কাগজপত্র তোলা হয়নি।’
‘আগে কাগজপত্র তোলো।’
যেন কাগজপত্র তুলতে গিয়ে আমি আবার সিদ্ধান্তটা পালটাতে পারি; নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জীবনের বাদবাকি কয়দিন বিয়ে ছাড়াই কাটিয়ে দেব―তাঁর ওই কথাটাকে তখন এরকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু না, তিনি সেরকম অর্থে বলেননি। এক অদ্ভুত কঠোরতাও ছিল তাঁর মধ্যে। নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপনের জন্যে যে কঠোরতা মেনে চলতে হয়, মনে হতো, যান্ত্রিকভাবে তিনি সেই কঠোরতা মেনে চলছেন। যত কষ্টই হোক ঠিক ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করা, যখন পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন তখন ঘর ঝাড়ু দেওয়া, সকালের নাস্তা তৈরি করা থেকে একের পর এক সব কিছু যেন করে যেতেন গতানুগতিকভাবে। সেই গতানুগতিকতার মধ্যে কী যে ছন্দ ছিল, কে তা জানে! সেই ছন্দে ডুবে থাকতেন তিনি। বোধহয় সেই ছন্দের তরঙ্গেই তিনি অনায়াসে এই বিয়েকেও প্রশ্রয় দিলেন, আবার প্রশ্রয় দিয়েও যেন কোথাও উপেক্ষার সুর বাজিয়ে রেখে দিলেন।
আমি তাঁর সামনে বসেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, তিনি আমাকে অনুভব করছেন। বুঝতে পারছেন, কী অস্থিরতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। কিন্তু তিনি আমার মাথায় হাত রাখেননি। যদিও রাখতেই পারতেন।
কুরআন শরিফের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘ঘরে যাও। রাত তো অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়ো। তোমার বোন তো বাসায় নাই। বিছানা বালিশ ঠিক আছে তো ?’
আমি চুপচাপ বসেছিলাম।
কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও বলেছিলেন, ‘যাও বাবা, ঘরে যাও। সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। আমি তোমার মনের খবর জানি না। কিন্তু তিনি জানেন। তিনি যা করেন, নিশ্চয়ই ভালোর জন্যেই করেন। হয়তো তোমার বা আমার ভালো হয় না, কিন্তু পৃথিবীর নিশ্চয়ই ভালো হয়।’
তাহলে ঘটনা এই! যা ঘটল, আমার জন্যে যত কষ্টেরই হোক, হয়তো পৃথিবীর ভালোই হবে।
আর মাত্র মাসদুয়েক সময় হাতে আছে। এখন কি আর এত দূরের জার্নি করা সম্ভব ? সোহা তাই আসতে পারেনি। ঢাকাতেই রয়ে গেছে। ভোরের আলোয় একবার পূর্ব, আরেকবার পশ্চিম, একবার দক্ষিণ, আরেকবার উত্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল, কাউকে না কাউকে আমার এই কষ্টটুকুর কথা বলা দরকার। এই কথাটুকু, মা খুব নীরবে আমাকে একটা শাস্তি দিয়ে গেছেন। আর মাত্র মাস দুয়েক সময় আছে, ডাক্তার বলেছে, আমার মেয়ে হবে, অথচ তিনি আর মাত্র এই কয়েক দিন অপেক্ষা করলেন না। চলে গেলেন, সদর্পে চলে গেলেন। কারও না কারও কাছে এই কথাটা বলা দরকার। কিন্তু কাকে বলব ? কাকে বলব আমি ?
সোহাকে ?
ফোন করতে গিয়েও করি না আমি। না, থাক। মানুষের কি উচিত নিজের কষ্ট আরও অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত করা ? উচিত কি নিজের অপরাধবোধ ভবিষ্যতের মানুষের জন্যেও রেখে যাওয়া ?
তা হলে, ঘটনা তা হলে এই―যে ক্ষত আমি নিজেই তৈরি করেছি, তাকে তা হলে নিজের কাছেই রেখে দিতে হবে, যাতে বারবার বুঝে নেওয়া যায়, ক্ষতির তীব্রতা কষ্টটুকু! কেন যেন মনে হয়, আমার চোখ দুটো ধীরে ধীরে পাথর হয়ে যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে, মায়ের চোখ দুটোও আসলে পাথরই ছিল। পাথর না হলে বোধহয় এইভাবে এতগুলো ছেলেমেয়েকে তার পক্ষে মানুষ করে তোলা সম্ভবই হতো না।
কয়েকটা কবুতরকে দেখি, গাছের ডালে বসে ডাকছে আর ওড়াউড়ি করছে। কোথাও বোধহয় একটা বনবেড়াল কিংবা শেয়াল দেখতে পেয়ে অদ্ভুত ইঙ্গিতময় শব্দে একটা মুরগি ডাকতে না ডাকতেই মোরগটা জোরে জোরে ডাক দিতে লাগল আর মুহূর্তের মধ্যে মুরগিছানাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের মায়ের দুই ডানার ভেতর। কারা যেন বাজারে যাওয়ার পথে গরুর খাঁটি দুধ দিতে এসেছে বাড়ির ওপর।
তাহলে পৃথিবীর সব কিছুই দেখা যাচ্ছে, ঠিকমতোই চলছে! আগের মতোই!
সত্যিই কি ঠিকঠাক চলছে ? নাকি নতুন করে স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এক জীবনের ? অতীতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে নতুন করে ? জীবনের শেষ ভগ্নাংশটুকু আকড়ে ধরে এই যুদ্ধ করছে কেউ ফের! যুদ্ধ করতে করতে যখন আর পারবে না, তখন সে আস্তে করে মুখ গুঁজবে মৃত্যুর বুকে!
আমি কিছু বুঝতে পারি না। বুঝতেও চাই না। প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকি।
সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ