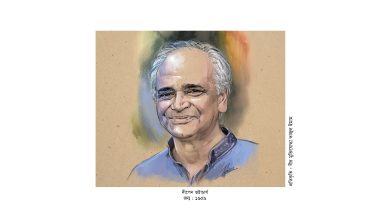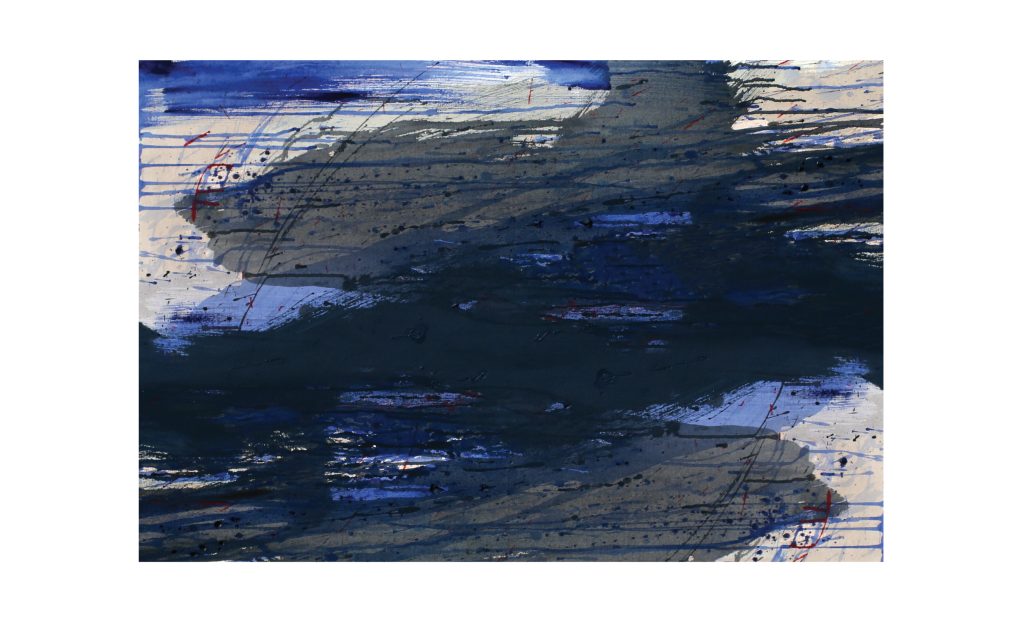
‘শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥’
১
সুবর্ণরেখা নদীধারে আমাদের সামান্য কিছু ‘পাল’ জমি। নদীর পলি জমে জমে তৈরি, তাই বলা হয় ‘পালজমি’। আছে―তবে ওই নামেই। কেননা ফি বছর বন্যায় ধাস ধাস শব্দে নদীর ‘কাতা’ ভেঙে ভেঙে জমিকে গ্রাস করতে করতে ক্রমে এগিয়ে আসছে নদী।
একদা যা ছিল আড়ে-বহরে প্রায় একবিঘার উপর, এখন তা কাঠাকালীতে দাঁড়িয়েছে কাঠা তিনেক। এ অবস্থা খালি কি আমাদের ?
উঁহু, না। আমাদের বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের বায়া, কালাচাঁদ, শম্ভুনাথ, হারান-পরাণ, অমূল্য, সর্বেশ্বরদের সরেজমিন পরিস্থিতিও তদ্রƒপ।
তবে যেটুকু জমিজমা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে আখ-অড়হর ছোলা-মুসুর খেড়ী তরমুজ বেগুন-বৈতালের চাষ হয়। চাষাবাদ না থাকলে প্রভা বিশুইয়ের ছেড়ীছাগল চরে।
ছাগলগুলো মাথা নিচু করে খুঁটে খুঁটে মুথা, ঘলঘসি, ঘাস খায়। আহারে অরুচি হলে ঘাড় তুলে নদী দেখে। থেকে থেকে মুখে মৃদুস্বরে আওয়াজ দেয়―‘অ্যা-ড়-রে-এ-এ-এ!’
আর কেউ না হোক, জমির প্রান্তে পাকুড়ের ডালে বসা একলা চিল উত্তর দেয়―‘চি-ল-কু-ড়-ড়-ড়-!’
কে জানে সেসবের কী মানে!
সুবর্ণরেখা খুব প্রাচীন নদী, ভূগোল-ইতিহাসে আছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে সিংভূম-মানভূম পুরুলিয়া-গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম-দাঁতন-সোনাকনিয়ার উপর দিয়ে গিয়ে ওড়িশার বালেশ্বর-জলেশ্বর ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।
পুঁথিপত্রেও সুবর্ণরেখার বিস্তর বিবরণ আছে। শ্রীমদ্ গোপীজনবল্লভ দাস বৈষ্ণবাচার্য রসিকানন্দের জীবন অবলম্বনে সেই কোন ষোল শ সাতান্ন থেকে ষোল শ ষাটের মধ্যে ‘শ্রীশ্রী রসিকমঙ্গল’ নামের একটা আস্ত পুঁথি রচনা করেছিলেন! যার পাতায় পাতায় নদীর নাম :
‘উৎকলেতে আছয়ে সে মল্লভূমি নাম।
তার মধ্যে রোহিণী নগর অনুপমা ॥
কটক সমান গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে।
সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্যস্থানে ॥
ডোলঙ্গ বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।
গঙ্গোদক হেন জল অতি রসকূপে ॥
রোহিণী নিকটে বারাজীত মহাস্থান।
যাতে সীতা রাম লক্ষ্মণ কৈলা বিশ্রাম ॥
দুয়াদশ লিঙ্গ রামেশ্বর শম্ভুবর।
রঘুবংশ কুলচন্দ্র পূজিলা বিস্তর ॥
বারি লৈতে কোটি লোক আইসে তথায়।
হেন পুণ্য নদী পুণ্যস্থান চারিদিকে।
রোহিণী বেড়িয়া সবে রহে লাখে লাখে ॥
(শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল ॥ পূর্ব্ব বিভাগ ॥ তৃতীয় লহরী)
আবার ‘দক্ষিণ বিভাগ ॥ তৃতীয় লহরী’তেও আছে :
সুবর্ণরেখার কূল অতি সুশোভিত।
আম কাঁঠালের বন শোভে চারিভিত ॥
পুলিন সুন্দর নদী দেখিতে সুন্দর।
যমুনার জল যেন দেখি পরিমল ॥
অতি সুকোমল স্থান কেন না যায়।
যতই বরষা করে কর্দ্দম না হয় ॥’
শাস্ত্রে বলে, ‘অধিকন্তু ন দোষায়।’ তবু অধিক উদাহরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। সাতকাহন করে যেটুকু বললাম, তার কারণ এই যে―সংবৎসর এই দু-দুটি নদী, সুবর্ণরেখা আর ডোলঙ্গ বা ডুলুঙ, পেরিয়ে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরবর্তী রোহিণীগ্রামে অবস্থিত ‘রোহিণী চৌধুরানী রু´িণী দেবী হাইস্কুলে, পড়তে যেতাম-আসতাম পায়ে হেঁটেই।
তবে একমাত্র বর্ষার মরশুম ব্যতীত তেমন আর জল কোথায়! হেথা-হোথা বিক্ষিপ্ত দশ-বিশগজ জল ছাড়া বাকি সমস্তটাই তো মরীচিকার ভ্রম সৃষ্টিকারী ধু ধু বালিয়াড়ি।
‘মরীচিকা’ বানানটাও যেমন খটোমটো, তেমনি তার অর্থও। শ্রীশ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ তার তর্জমা করে লেখে যে―‘গ্রীষ্মে বালুকাপ্রতিফলিত জলবৎ প্রতীয়মান রবিকরমালা।’
তা, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সূর্যতাতা নদীবালিতে খালি পায়ে কপা হেঁটে গেলেই ‘মরীচিকা’ শব্দটির অর্থ বোধগম্য হতে বিলম্ব হয় না। যদিও দুই নদীর মাঝবরাবর কাঁটাকুল, ফণীমনসা, আকন্দ আকীর্ণ পোয়ামাইলটাক ‘কদোপাল’ নামের একটি সুবিস্তৃত ডাঙা আছে। ডাঙা আর কোথায়, সেও তো এক বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, সুবিশাল বালির স্তূপ।
অবশ্য আগে আগে, আগে আগে মানে প্রাচীনকালে, নদীর এরূপ দুর্দশা ছিল না। নদী তখন স-সাগরা। অর্থাৎ, সুবর্ণরেখায় তখন জোয়ার-ভাটা খেলত, সওদাগরী জাহাজ চলত :
‘এসব নগরে যত সওদাগর বৈসে।
তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥’
একবার তো ‘ওক্কলবা’র ‘তপোসা’ আর ‘পালেকাথ’ নামের দুই সওদাগর নানারকম দ্রব্যাদি, বীজদানা ও মশল্লার জাহাজ নিয়ে ‘আদজেত্তা’ বন্দর থেকে ‘সুয়োমা’ বা ‘সুহ্মদেশ’-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।
‘ওক্কলবা’ তৎকালীন উৎকলদেশ। ‘আদজেত্তা’ হলো তাম্রলিপ্ত বন্দর। আর ‘সুয়োমা’ বা ‘সুহ্ম’ তো সে সময়ের মেদিনীপুরসহ এক সুবিশাল ভূখণ্ড।
সওদাগর ‘তপোসা’ ও ‘পালেকাথ’-এর জাহাজ সমুদ্রপথে এসে একদা ঢুকে পড়েছিল ‘সুয়োমা’ বা সুহ্মদেশের নদী সুবর্ণরেখার মোহানায়। তারপর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড জোয়ার ও বায়ুপ্রহারে সওদাগরী সেই মালবাহী জাহাজ আছড়ে ভেঙে পড়েছিল আমাদেরই গ্রামের অনতিদূরে থুরিয়ার মহিষাসুর ‘দঁক’-এ।
‘দঁক’ একটি আজেবাজে চলিত কথা। শ্রীশ্রী হরিচরণ বন্দ্যো’র ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ এর উল্লেখ নাই। তা বলে এটা কোনওমতেই যোড়-তাড় করে বলা নয়। এর প্রচলিত অর্থ হলো ‘কদর্মাক্ত জলাভূমি’।
আখমাড়াইয়ের মরশুমে এতদ্ অঞ্চলের আখচাষিদের মাড়াইকলে ‘পঁড়াসুর’ বা পণ্ডাসুর অর্থাৎ মহিষাসুরের পূজা করতে হয় বেশ ঘটা করেই।
সে কী আজকের কথা! সেই কোন আদ্দিকাল থেকে আখের রস জ্বাল দেওয়ার ‘ডেগ’ বা কড়াইয়ের একপাশে উনুনের ধারেই মাটির ‘ঢেলা’ হয়ে পূজা পেয়ে আসছে মহিষাসুর :
‘পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযত্রৈস্তং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যামিক্ষু বাটি নিবাসিনে।
যজমান হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধি প্রদায়িনে ॥’
আমাদের দেশে-ঘরের লোকেরা পুরুষ মোষকে ‘পঁড়া’ বলে। তদুপরি সুবর্ণরেখার খাঁড়িতে ‘মহিষাসুর দঁক’-এ অচেনা অজানা গাছ-গাছড়ার জঙ্গলে মহিষাসুরের পূজার ‘থান’ও আছে।
তাই জায়গাটা ‘মহিষাসুর দঁক’। এই দঁকেই একদা ডুবে গিয়েছিল সওদাগর ‘তপোসা’ ও ‘পালেকাথ’-এর অর্ণবপোত।
ডুবে গেল। বালিপোত হলো। মাটি চাপা পড়ল। অচেনা অজানা বীজদানা অঙ্কুরিত হলো। চারা জন্মাল। চারাগাছ কালে কালে মহীরুহে পরিণত হলো।
মহিষাসুর দঁক ভরে উঠল অর্জুন, পাকুড়, শাল, মহুলে নয়, অচেনা অজানা সেই সমস্ত মহীরুহে।
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে, ফিঙ-ফোটা-জ্যোৎস্নায়, এমনকি নিকষকালো অন্ধকারেও নাম-না-জানা গাছেদের জঙ্গলে দিনক্ষণ বুঝে সময় সময় ঝলসে উঠতে লাগল সেই আছড়ে ভেঙে পড়া, ডুবে যাওয়া জাহাজের কানা!
ভাঙা জাহাজের কানা-ঝলসানি আমরা অন্তত স্বচক্ষে কোনওদিন দেখিনি। আমাদের গ্রামের হারান-পরাণ, রামেশ্বর-পৃথ্বীনাথ, বা আর কেউ কখনও দেখেছে বলেও তো শুনিনি।
তবে শুনেছি, যে-ই দেখেছে সে-ই নাকি উন্মাদ ও বিবাগী হয়ে দেশান্তরী হয়েছে। আমাদের ‘মহিষাসুর দঁক’-ও তাই লোকমুখে রূপান্তরিত হয়েছে রহস্যময় ‘জাহাজকানার জঙ্গল’-এ।
নাকি খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০-২৬০০ সময়কালে আফগানিস্তানের হেলমান্দ নদীউপত্যকায় গড়ে উঠেছিল ‘হেলমান্দ সভ্যতা’।
আর খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০-৩২০০-র মধ্যে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুনদের অববাহিকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জদাড়োকে আশ্রয় করেই ‘সিন্ধুসভ্যতা’।
কিন্তু কস্মিনকালেও সুবর্ণরেখা নদীকে কেন্দ্র করে এমন কোনও সভ্যতার হদিস ইতিহাসবিদদের কাছে নেই। এ নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামান না।
নদীতীরের জনমানুষদেরও কি আর এই নিয়ে মাথাব্যথা ছিল, না আছে ? সভ্যতা মাথায় থাক, তারা বড়জোর চিন্তায় চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে আগ্রাসী বানবন্যা নদীর ‘কাতা’ ভেঙে ভেঙে এবার কার কতটা জমি গ্রাস করে ফেলবে!
বিশেষত বর্ষায়, আর যাদের নদীধারে জমি আছে, তাদের। কথায় বলে না―‘নদীর ধারে বাস ভাবনা বারোমাস।’ যতই ‘কড়া ধাতের দেশ’ বলা হোক না কেন, ডাক-পুরুষের বচন এদেশের ক্ষেত্রেও খাটে বৈকি।
তা, নদী-সেপারের বড় ইস্কুলে যেতে আসতে রোজ দু বেলায় আমাদের চোখে পড়ে ‘জাহাজকানার জঙ্গল’, তার বনঝাড়।
আর আর সঙ্গীসাথীরা, মানে আমাদেরই গ্রামের ইস্কুলপড়ুয়ারা, পারতপক্ষে সেদিকে চোখ তুলেও দেখে না। কিন্তু আমার আগ্রাসী চোখদুটি বড় বড় করে কেন জানি সেদিকেই তাকিয়ে থাকে।
ভাঙ্গা জাহাজের কানা ঝলসানি তো দূরঅস্ত্, দৈবাৎ একটা-দুটো পাখির ডানা ঝাপটানি যা চোখে পড়ে, বা কানে আসে। হয় তারা ডানা ফেটিয়ে জাহাজকানার জঙ্গলের দিক থেকে উড়ে আসছে, নয় তো সন্ধ্যা হব-হব সময়ে জাহাজকানার জঙ্গলে বাসায় ফিরছে।
কদোপালের ডাঙার মাথায়, একেবারে পশ্চিমে, একলা একলা একটা ছাতিম গাছ। গ্রামে-ঘরে লোকে তো বলে ‘ছাতনা গাছ’। সেই ছাতনা গাছে সকাল-সন্ধ্যায় রাজ্যের দাঁড়কাক এসে মজলিশ বসায়। বড়োই কর্কশ কণ্ঠে তারা তখন মুহুর্মুহু ডাক ছাড়ে।
সে-ডাক শ্রবণমাত্রই সুখী গৃহস্থরা অমঙ্গল আশঙ্কা করে। তবে আমাদের দেশে-ঘরের লোকেরা এ-ডাক নিত্যদিনের আয়োজন মনে করে এক কান দিয়ে শোনে, আরেক কান দিয়ে তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়।
আমাদের নদীধারের ‘পাল জমি’ থেকে সোজা পশ্চিমে ক পা হেঁটে গেলেই পড়বে সীতানালা ‘খাল মুহ্’ অর্থাৎ সীতানালা খালের মোহানা আর পড়বে ‘মশানির দহ’।
মুহ্, তার মানে মুখ। সীতানালা খালের মুখ। সীতানালা নাকি রামায়ণের জনমদুঃখী সীতারই অশ্রু দিয়ে গড়া এক ছোট নদী। সত্যি সত্যিই ছোটনদী মালিনীরই তুল্যমূল্য। সেই আছে না―‘মালিনীর জল বড় স্থির ―আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া―সকলি দেখা যেত।’
সীতানালা যেখানে এসে সুবর্ণরেখায় মিশেছে, তাকে যদি সীতানালার মুহ্ বা মোহানা ধরা যায়, তবে তার উৎসস্থল অবশ্য অবশ্যই ‘তপোবন’। তপোবন জঙ্গলমহাল। জে. এল. নং ৩৮। খেলাড় নয়াগ্রাম পরগনা।
নাকি―‘এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি…’ বাল্মিকীরই তপোবন আশ্রম। রাম কর্তৃক সীতা এখানেই বনবাসে বিবর্জিতা হয়েছিলেন।
অতঃপর এখানেই লব ও কুশের জন্ম হলো। প্রসূতি তথা পোয়াতি সীতা গায়ে হলুদ মেখে স্নান করলেন। সীতানালা খালের উৎসমুখের জল তাতেই হয়ে গেল ‘হলুদ-গাবা’।
শাল ডাঁটির দাঁতনকাঠি দিয়ে দাঁত মাজলেন। দাঁত-মাজা সেরে দাঁতনকাঠি চিরে দু-ভাগ করে জিভ ছুললেন। সেই ফেলে দেওয়া, চিরে দু ভাগ করা দাঁতনকাঠি থেকে দু-দুটো মহীরুহ শালগাছ জন্মাল। তাদের একটা তো এখনও আছে। আরেকটা জঙ্গলের কাঠ-চোরেরা এতদিনে লোপাট করে দিয়েছে।
তবু পাহাড় পর্বত না থাক, বড়-বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, শাল, পিয়াশাল, ধ, আসন, মহুল, মেহা, কেঁদ, কইম, কুড়চি, ভেলা, বাদভেলা, ভাদু―আছে বৈকি।
জঙ্গলের বুক চিরে সীতানালা খাল চাষাবাদের জমির দিকে এঁকে বেঁকে অগ্রসর হলে তার ‘হলুদ-গাবা’ বা হরিদ্রারঞ্জিত জল আর থাকে না। ভেলভেটের তুল্য চিরোল চিরোল শুশনি, সরন্তি শাকের দঙ্গল সরালেই কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার জল। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া যেমন দেখা যায়, তেমনি পুঁটি-দাঁড়িকিনি-চাঁদ-কুড়ি, ইত্যাদি ছোট ছোট মাছও খেলে বেড়ায়।
তারপর তো সীতানালা খাল বা ছোট নদী তপোবন জঙ্গলমহালের সীমানা ছেড়ে পিতাম হাঁসদা আর শীতল জানার ডিহিবাড়ির পাশ দিয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে ‘মশানির দহ’তে, সুবর্ণরেখায়।
আর এতক্ষণে এতদূর এসে সীতানালা যেন তার পুরাণ-মর্যাদা অনেকটাই ক্ষুণ্ন করেছে। দু ধারের পাড় বেঢপ উঁচু হয়ে গিয়েছে।
পাড়ে সারি সারি তাল, তমাল, শাল, পিয়াশালের পরিবর্তে চাষীদের ‘ত্যাঁড়া’ বসেছে।
‘ত্যাঁড়া’―তার মানে জমিতে সেচের জন্য জল তোলার কাঠ ও দড়ির ঘড়রি বিশেষ।
চাষিরা ত্যাঁড়া-কাঠে হরদম ঘড়রি ঘুরিয়ে জল তুলে ফুলকপি-বাঁধাকপি বেগুন-মুলো বৈতাল-বরবটি আখ-অড়হরের জমিতে ‘বাতান’ দিচ্ছে। তাতে করে সীতানালার আয়নার মতো জল অনবরত ঘোলা হচ্ছে।
তার উপর ‘মশানির দহ’-এর ঠেস-মারা জলে ধাক্কা খেতে খেতে উছুক-ডুবুক হয়ে ইতস্তত ভেসে বেড়ায় আধ-পোড়া-মড়াকাঠ। কাছেই, সীতানালা খাল-মোহানার চবুতরায় আমাদের গ্রামের মড়া-পোড়া-শ্মশান আছে যে!
মড়া পুড়ল পুড়ল, তার পারলৌকিক ঘাট-কামানোয়, বালিতে যত্রতত্র গোঁজা হয়ে পড়ে থাকল স্তূপীকৃত মাথার চুল, ভাঙা কলসির খাপরা, ঘাটে-ওঠা-নরনারীর ফেলে যাওয়া পরনের ছেঁড়া শাড়ি, ধুতি-গামছা।
সুনসান মধ্যাহ্নে, অলস অপরাহ্ণে, অথবা ভর-সন্ধ্যাবেলায়, অথবা ঘোরতর তমসা-লগ্ন নিশীথেও সীতানালার জলে গাছ থেকে টুপটাপ ছপাৎ ছপাৎ করে অঝোরঝর আছড়ে পড়ে ফাটতে থাকে পাকা যজ্ঞিডুমুরের ফল।
চাষিদের বেকার ত্যাঁড়ায় বসে একলা একলা দোল খায় কালো ভুসভুসে ঢ্যাপচু। অর্থাৎ ফিঙেপাখি। আচমকা তীক্ষè স্বরে সে ডেকে ওঠে―‘ভু-ই-চু-ঙ! ভু- ই-চু-ঙ!’
হয়তো তখনই খেড়ী-তরমুজ মুগ-মুসুরের জমির উপর দিয়ে, আখ-অড়হরের খেতি-খামারে হুড়্ ঝুড়্ আওয়াজ তুলে, সীতানালা খালমোহানার চবুতরায় উড়ে এসে জুড়ে বসে জাহাজকানার মন্দ বাতাস! আর―
অদূরে ছাতিনা গাছে গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে চামড়ায় চোখ ঢেকে দাঁড়কাকরা মটকা মেরে পড়ে থাকে। রা কাড়তে তারা আর ভরসা পায় না।
২
‘মশানির দহ’।
‘দহ’―শ্রীশ্রী হরিচরণ শর্ম্মার ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ পুনরপি তর্জমা করে যে, দহ, অর্থাৎ কালীদয় সাগর। ‘দহতে পেলায়িরো; দহ বুলী ঝাঁপ দিলো সে মোর সুখাইল।’ গভীর দহ, ইত্যাদি।
মনসামঙ্গলের ‘কালীদয় সাগর’, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘দহ’ বা গঙ্গামঙ্গলের ‘গভীর দহ’―আর আমাদের কোথায়! মাটিতে অবিরল জল পড়তে পড়তে একসময় জলের ধারাবেগ কর্ষণে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়।
তেমন আর কি! বছরের পর বছর বর্ষায় সীতানালা খালের প্রবল প্লাবনের তোড় তার ‘খাল মুহ্’ অর্থাৎ মোহানায় সুবর্ণরেখার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে গভীর খাদ রচনা করে। কালে কালে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘মশানির দহ’।
তার সন্নিকটেই আমাদের গ্রামের শ্মশান। আর কথাতেই তো আছে ‘শ্মশান-মশান’। যোড়-তাড় করে বানাতেও হয় না। শ্মশানই মশান, মশানই শ্মশান।
মশানির দহ তার মানে শ্মশানেরই দহ। শ্মশানের যাবতীয় বর্জ্য―পোড়া কাঠকয়লা, আধপোড়া মড়াকাঠ, দড়ির চারপাই, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া মশারি, বাঁশের কুলো, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা, ডাঁটি ভাঙা ফাটা কাচের চশমা―সব, সব এসে দহের জলের উড়াল ঘূর্ণিতে আছড়ে পড়ে ঘুরপাক খায়। পাক খেতে খেতে কতক তলদেশে থিতিয়ে পড়ে স্তূপীকৃত হয়। আর কতক অনুকূল স্রোতোপ্রবাহে ভেসে যায়।
যারা ভেসে গেল তারা তো গেলই। আর যারা পড়ে থাকল তাদের গায়ে ছ্যাতলা পড়ল। তারমানে শ্যাওলা ধরল।
জল জমে বরফ, আঁধার জমে ভূত। কিন্তু জলের তলদেশে স্তূপীকৃত শ্মশানের পোড়া আংরা, আধপোড়া মড়াকাঠ, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া জুতোয় শ্যাওলা ধরলে যে কী হয় ―এতদিন জানা ছিল না।
জানতে পারি উনিশ শ সাতষট্টির এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। ততদিনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটাও শেষ, হাতে বিস্তর অবসর। কী করি, কী করি!
সুবর্ণরেখা নদীধারের পালজমিতে সে বছর চাষিদের আখ চাষেরও প্রাচুর্য খুব। এপ্রিল শুরু হয়ে মাসের মাঝামাঝি এসে গেল, তবু তাদের মাড়াইকলের উড্ডীয়মান কালো ধোঁয়া তখনও থামেনি, অনর্গল উড়ে চলেছে।
আমাদের গ্রাম থেকে বাঁকে করে কুমারদের মাটির কলসি, যাকে বলে ‘কুঁদা’, মাড়াইকলে আসছে তো আসছে আর নতুন গুড়ে ভরতি হয়ে গরুর গাড়ি করে একে একে চলে যাচ্ছে বেলদা-খাকুড়দা-কেশিয়াড়িতে। সেখান থেকে আড়তদারেরা ট্রাককে-ট্রাক পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতার পোস্তা-রাজাকাটরা- বঢ়াবাজারে।
আমরা কতিপয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা বড়জোর অপরাহ্ণে নদীর পাড়ে বসে গুড়াখু সহকারে দাঁত মাজতে মাজতে নতুন গুড়ের গন্ধ শুঁকি। আর, হয়তো তিথি-নক্ষত্র মিলিয়ে দিন-ক্ষণ দেখি―কখন ওদিকে চাষিদের একলা ‘ত্যাঁড়া’য় বসে কালো ভুসভুসে ঢ্যাপচু তারস্বরে ডেকে উঠবে―‘ভু-ই-চু-ঙ! ভু-ই-চু-ঙ!’
কখন জাহাজকানার জঙ্গল থেকে মন্দ বাতাস উঠে এসে শম্ভু, সর্বেশ্বরদের, কালাচাঁদ, হারান-পরাণ, এমনকি আমাদের জমির উপরও তার গরম শ্বাস ফেলে খাল-মোহানার শ্মশান-চবুতরায় আছড়ে পড়বে, তার ধাধসে চামড়ায় চোখ ঢেকে মটকা মেরে পড়ে থাকবে ছাতিনা গাছের দাঁড়কাকেরা।
মধ্যাহ্নে, আঁইঠু দঁড়পাটদের ‘ভাতুয়া’ ভুজু-ডিবরা যখন তাদের চরানে পঁড়ামোষগুলো নিয়ে নদীর জলে ফেলে খড়ের নুড়া দিয়ে ঘষে ঘষে গা-গতর সাফা করে, পঁড়ামোষের গা-গতরে ‘বসি বসি’ করে পা ঝুলিয়ে ধারেকাছে উড়ে বেড়ায় একটি-দুটি কাক, তখনই জনা-কতক আমরা নদীর পাড় থেকে ঝুপঝাপ ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ‘মশানির দহ’তে।
ডুবসাঁতার, চিৎ-সাঁতার, এমনকি ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে তুলে আনি বালি, কখন বা হাতমুঠোয় বেঘোরে উঠে আসে শ্যাওলা-ধরা পোড়া-আঙরা, মড়াকাঠ, খাটিয়ায় বাজু―দহ ছাড়িয়ে উত্তরে গেলেই নদী খুব অগভীর, প্রায় হাঁটুজল। আমরা বন্ধুরা, এবং আর আর সঙ্গীসাথীরা, সময় সময় স্রোতের উল্টো দিকে মাছ ধরার তাগিদে ঘন সারিবদ্ধ হয়ে মানববন্ধনে বসি, তখন আমাদের ফাঁক-ফোকর দিয়ে জল বৈ মাছ গলে যাওয়ার কোনও জো থাকে না।
মাছ ধরাও পড়ে। বাটা, খয়রা, ‘দাড়ুয়া’ অর্থাৎ দাড়িওয়ালা চিংড়া। ছির্ছার করে ছিটকে উঠে মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে-ঝাপিয়ে স্রোতের অনুকূলে পালিয়েও যায় দুটো-একটা।
কখনও কখনও বেলা আড় হয়ে আসে তবু আমাদের জলে ঝাঁপাঝাঁপি সহজে থামে না। বাড়ি থেকে ডাক এসে যায়―‘অ রে অমুক রে-এ-এ-’ অ রে তমুক রে-এ-এ-এ-‘মশানির দহে অর্গলা ভূত আছে রে-এ-এ-এ-’ ‘অত ঝাঁপাস না রে-এ-এ-এ-’…ধুৎ! অর্গলা ভূত! জাহাজকানার জঙ্গলের মন্দ বাতাস! কোথায় কী! বড়জোর নদীধার দিয়ে যাতায়াতকারী মুনিশ-মাহিন্দররা, ওড়িয়াভাষী ‘হাটুয়া’ জনমানুষরা আমাদের কিত্তি-কাণ্ড দেখে হাসে ।
হয়তো কেউ কেউ জরপ করে বলেও―‘বাছুরখুঁয়ার্ড়্যা টকামানে কুক্কুল্যা খরাবেলা মশানির্দয় ঝাপাসি ঝুরেঠ্যা, হা দ্যাক্!’
কী বলল ? ‘ওঁ হ্রীং হ্রীং’ করে ভূত তাড়ানোর কোনও মন্ত্র বলল কী ? না, না। হাটুয়ারা তাদের ‘হাটুয়া’ অর্থাৎ ওড়িয়া-বাংলা মেশামেশি একরকম ভাষায় যা বলল তার তর্জমা করলে দাঁড়ায়―বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের ছেলেছোকরারা এই কুল কুল করে ঘাম ঝরানো দ্বিপ্রহরবেলায় মশানির দহে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে―ওই দ্যাখো!
যা হোক, আধপোড়া মড়াকাঠ, পোড়া আংরা, শ্মশানের ভাঙা কলসি, ভাঙা ছাতা মশানির দহে জলের তলায় পড়ে ছ্যাতলা ধরলে, আর তা মানুষের পায়ে জড়ালে যে কী হয়―জানা ছিল না।
জানা ছিল না। জানতে পারলাম উনিশ শ সাতষট্টির এপ্রিলের মাঝামাঝি, সম্ভবত তেরই কী চৌদ্দই এপ্রিল। দিনটা ছিল বোধকরি শনিবার।
তার আগের বছর আমরা খবর পাচ্ছিলাম, সম্ভবত আগস্ট মাসে সন্তরণপটু মিহির সেন জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করলেন। ফের সেপ্টেম্বরে পেরোলেন দার্দানেলস প্রণালী।
সাঁতারে বাঙালির রেকর্ডের পর রেকর্ড। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ নাথ আবার প্রথম!
কোথায় জিব্রাল্টার, দার্দানেলস, কোথায় বা পক প্রণালি―আমাদের সঠিক ধারণা ছিল না। তবু সুবর্ণরেখার মশানির দহে আমাদের দাপাদাপি যারপরনাই বেড়ে গেল। যাকে বলে ‘ঝাপাসি ঝুরেঠ্যা’।
ডুবসাঁতার, চিৎ-সাঁতার তো জানা ছিলই, শুরু হলো ‘ফ্রি স্টাইল’ ‘ব্রেস্ট স্ট্রোক’ ‘বাটার ফ্লাই’ ও ‘ব্যাক স্ট্রোক’।
তবে গ্রীষ্মের নদীতে দৌড় ওই বড়জোর মশানির দহ। নচেৎ দহের উপরে গেলেও হাঁটুজল, নিচে গেলেও হাঁটুজল, সমুখে গেলেও হাঁটুর নিচে বৈ উপরে ওঠে না। কবিতাতেই তো আছে―
‘আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।’
‘চলে বাঁকে বাঁকে’―কথাটাও আমাদের সুবর্ণরেখা নদীর ক্ষেত্রে খাপ খেয়ে যায় বেশ। গোপীবল্লভপুর-নয়াবসান থেকে নদী এসে ওই তো বাঁক নিয়েছে তালডাংরা-মলতাবনীতে।
তারপর পাতিনা-দেউলবাড়ে। মহাপাল হয়ে রগড়া-কাঠুয়াপালে। আমাদের ঘাট ছুঁয়ে নদী ফের বাঁক নিয়েছে থুরিয়া-নরসিংহপুরে―
কিন্তু ঘনঘোর বর্ষায়, মহাপ্লাবনে, সে সমস্ত বাঁকঢাঁক মুছে নিয়ে এ-কূল ও-কূল দুই কূল একাকার ও সমান্তরাল হয়ে নদী দুরন্ত বেগে ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে।
তখন ভারী কষ্টকর ও দুঃখজনক হয়ে উঠলেও বাঁকা নদী যেন আমাদের জীবনের খাপে খাপেই এঁটে থাকে। সেই একটা গান আছে না―
‘বাঁকা নদী বড়ই দাগা দ্যাল্ ব
বাঁকা নদী বড়ই দাগা দ্যাল্।
হেলা কান্তে চেলা কান্তে, মায়ে ঝিয়ে দুই কান্তে
চলিতে চলিতে মোদের জ্যাং ধরি গ্যাল্ ॥
জ্যাং ধরি গ্যাল্ ॥
বাঁকা নদী বড়ই দাগা দ্যাল্ ব
বাঁকা নদী বড়ই দাগা দ্যাল্―’
শনিবারের বারবেলায় মশানির দহের জলে বিস্তর সাঁতার কেটে স্নানান্তে পাড়ে উঠে দু পা দস্তুরমতো ঝাড়তে লাগলাম―ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আর মেজো আঙ্গুলের মাঝখানে শ্যাওলার মতো কী যেন একটা জড়িয়ে আছে না ?
কী যেন ?
কী আবার, শ্যাওলাই তো! ঝাড়াঝাড়িতে কতক ঝরে গেল আর কতক এঁটুলির মতো সেঁটে থাকল। থাক, থাক। শুকনো হলে এমনিতেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে। যেমন কীনা চাষাবাদের কালে চাষিদের পায়ে, হালের বলদের গায়ে কাদা লেপ্টে, শুকিয়ে চাগাড় বাঁধে।
ঘরে এসে ভরপেট খেয়ে একঘুম ঘুমোলাম। তারপর তো আমাদের গোঠটাঁড়ের মাঠে গিয়ে ফুটবল নিয়ে ফের একপ্রস্থ দাপাদাপি। শ্যাওলার অবশিষ্ট যেটুকু এখনও লটকে আছে, সেটুকুও উবে যাবে না কর্পূরের মতো!
আর আমাদের ফুটবল তো আদপেই চামড়ার নয়, বুনো ওলডাঁটার। অজগর সাপের মতো গায়ে ছাপছোপ আঁকা বুনো ওলগাছ কেটে এনে রৌদ্রে শুকিয়ে ছনের দড়ি দিয়ে পোঁটলা করে বাঁধা।
হাওয়া ভরে ফুলটুস করা চামড়ার ফুটবল নয় যে পায়ের সামান্য ‘টাচ’য়েই উড়ে উঠবে, ওলডাঁটার বলকে তিন-তালগাছ-সমান উচ্চতায় ‘হাই-শট’ মারতে গেলে রীতিমতো পায়ের টেংরির জোর লাগে।
কাদা তো কাদা, শ্যাওলা তো শ্যাওলা―সে গোল্লাছুটের ধাধসে সবকিছুই ছিন-ছাতুর হয়ে ঝরে পড়বে না ? কিন্তু না, খেলা শেষে পা ধোওয়ার কালেও আঙ্গুলদুটি ফাঁক করে দেখি―সবুজ বরণ বিন্দুর মতো একটা কিছু তখনও লটকে আছে না ?
‘যানে দো’ বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে হেরিকেন জ্বেলে পড়তে বসে গেলাম। পরীক্ষা তো হয়েই গিয়েছে, তাহলে আবার পড়া কিসের ? তবু প্রশ্নপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে কোন দাগে সর্বোচ্চ কত নম্বর পেতে পারি, তাই নিয়ে চুলচেরা পর্যালোচনায় মেতে উঠলাম।
কাটাকাটির পর কাটাকাটি। দরাজ হস্তে খাতা দেখলে কোনটায় কত, ফের কড়াকড়ি করে নম্বর দিলে কতয় কত। পদার্থবিজ্ঞানের একটা প্রশ্ন ছিল :
‘নিউটনের গতিসূত্রগুলি বিবৃত কর এবং প্রথম ও
তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ দাও। কিরূপে প্রথম সূত্র
হইতে বলের সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় সূত্র হইতে বলের
পরিমাপ পাওয়া যায়, ব্যাখ্যা কর।’
খুবই কমন কোশ্চেন। ঝেড়ে মুখস্ত লিখেছি। কিন্তু সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ছিল একটু বেয়াড়া ধরনের। অনেকক্ষণ ভাবতে হয়েছে। যেমন :
‘কোন উচ্চতা হইতে হাঁটু ভাঁজ না করিয়া মাটিতে
লাফাইয়া পড়িলে যত ব্যথা লাগে হাঁটু ভাঁজ করিয়া
পড়িলে কম ব্যথা লাগে কেন ?
জনৈক মজুরকে ঠেলাগাড়ি ঠেলিতে বলায় সে উত্তর
করিল, তৃতীয় গতিসূত্রানুযায়ী আমি যে বল গাড়ির
উপর প্রয়োগ করিব গাড়িও সেই বল আমার উপর
প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে ঠেলিয়া লাভ কি ?’ এই
উক্তি সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য লেখ।
অথবা
‘একটি জালিতারের খাঁচায় একটি পাখি আছে। খাঁচাটি
একটি স্প্রিং-তুলার হুক হইতে ঝুলানো। পাখি খাঁচার ভিতর
উড়িয়া বেড়াইলে স্প্রিং-তুলায় যে পাঠ পাওয়া যাইবে পাখি
খাঁচায় বসিয়া থাকা অবস্থায় পাঠ কি তাহা অপেক্ষা বেশি হইবে,
কি সমান হইবে ?’
[ যে কোন ১টি ]
হিসাব মিলুক ছাই না মিলুক। মোটের উপর নম্বর কম হবে বলে তো মনে হলো না। অতএব মহানন্দে কুরথির ডাল সহযোগে রাতের ভাত হাঁপরে খেয়ে ঘুমাতে গেলাম ।
ঘুম ঘুম! আয় ঘুম যায় ঘুম! ঘুম যেমন এল, ঘুম ভেঙেও গেল। ঘুম ভেঙে গেলে স্পষ্ট শুনলাম ―আমাদের মাটির ঘরের দোরগোড়ায় ব্যাঙ ডাকছে, টুরি ব্যাঙ। টু-ট্টু-! টু-ট্টু-র-র-র! রিঁ-রিঁ-আ পোকা ডাকছে―‘রিঁ-ই-ই-ই! রিঁ-ই-ই-ই!’
অঝোরঝর রাত। অকস্মাৎ মনে হলো―কে যেন আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে ও তার অব্যবহিত পরের আঙ্গুলে ঝিঁজরি বেঁধে অমোঘ টান দিচ্ছে। ‘ও কে!’―‘ও কে! ও কে গো!’
কই ? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! খালি যা আমাদের গোহালঘরে গবাদি পশুগুলো লৎ পৎ করে কান ঝাড়ছে। নাসিকা দিয়ে হেঁসফেঁস শব্দে মাঝেমধ্যে লম্বা শ্বাস ছাড়ছে। গোহালঘরের দোরগোড়ায় কালো ধোঁয়া উগরে একটা ডিবরি জ্বলছিল। কখন নিভে গিয়ে এখন চুপ মেরে আছে।
ঝিঁজরির টানে খাটের উপর উঠে বসলাম। খাট থেকে নেমেও পড়লাম। হাঁটছি না। তবু নিস্তার নেই―কে যেন টেনে নিয়ে চলেছে, কে যেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ―দরজার দিকে। মুহূর্তে আপনাআপনি হাট করে খুলেও গেল দরজাটা।
উঠোনে বাহির হওয়া মাত্রই মরা জ্যোৎস্নায় কোত্থেকে একটা কাক ডেকে উঠল। ‘দাঁড়াও! দাঁড়াও!’―আমিও চিৎকার করে উঠলাম। এ সময়ই কীনা ‘জনৈক মজুর ও ঠেলা-গাড়ি’র অঙ্কটার সমাধানসূত্র কত সহজেই পেয়ে গেলাম :
নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী মজুর ঠেলাগাড়িতে
বল প্রয়োগ করবে, ঠেলাও সমান ও বিপরীতমুখী বল
প্রয়োগ করবে, তাহলে সত্যিই তো ঠেলা গড়াবে না। কিন্তু
মজুর পা দিয়ে মাটিতে যে তির্যক বল প্রয়োগ করবে, তা
যদি―
কত করে মা-কাকিমাদের ডাকলাম! বাবা ও কাকাদের। তারা কি আমার ডাক শুনতেই পেল না ? নাকি গলা দিয়ে আমার কোনও আওয়াজই বেরুল না ?
রাস্তায় নেমে এক-দুজনের সঙ্গে দেখাও হলো আমার। হয়তো ‘জলঘাট’ সারতে এত রাতেও ঘর ছেড়ে তারা বেরিয়েছে। কিন্তু আমাকে দেখেও তারা যেন দেখতে পেল না।
ঝুঁকে পড়ে পায়ের আঙ্গুলদুটিতে হাত বুলালাম। কোথায় শ্যাওলা ? শ্যাওলার চিহ্নমাত্র নেই, তার পরিবর্তে লোহার ঝিঁজরি!
ছিঁড়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। ছিঁড়ল তো না-ই! উল্টে ‘সরণ’ ও ‘ত্বরন’ দুই-ই আরও দ্রুততর হলো।
দেখতে দেখতে রাতের গ্রাম পেরিয়ে ফের সেই নদীধারে শ্মশান চবুতরায় এলাম। হায়! গ্রামের চেনাজানা এতগুলো কুকুর―তাদের একটাও হ্যাল হ্যাল করে আমার পিছু পিছু আসা তো দূরঅস্ত্, ভুঁকলো পর্যন্ত না! ইধৎশ ধঃ ঃযব সড়ড়হ।
ওই, ওই তো জাহাজকানার জঙ্গল। আমাদের সামান্য কিছু ‘পাল জমি’। শুধু কি আমাদের―বায়া, কালাচাঁদ, শম্ভুনাথ, হারান-পরাণ, সর্বেশ্বরদেরও। আখ-অড়হর ছোলা-মুসুর খেড়ী-তরমুজের খেত।
শ্মশান চবুতরা।
দূরের ছাতিনাগাছে গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে চামড়ায় চোখ ঢেকে হয়তো মটকা মেরে পড়ে আছে দাঁড়কাকেরাও। ভয়ে-ত্রাসে তারা এখন রা কাড়ছে না।
‘অর্গলা ভূত’-এর ঝিঁজরি আমাকে নিয়ে মশানির দহে নামল। জলে পা ফেলার স্পষ্ট আওয়াজও পেলাম―‘হ ব্ ল স্ ফ ব্ ল স্―’ পাগলা মেহের আলির মতো একটা কেউ আর জাগ্রত নেই। যে কীনা থেকে থেকে চিৎকার করে বলে উঠবে―
‘তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।’
৩
এ যেন জল কেটে জলের ভিতরে চলে যাওয়া। তবে স্বেচ্ছায় কী আর ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ‘অর্গলা ভূত’-এর ঝিঁজরি পায়ে জড়িয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।
-হ ব্ ল স্ ফ ব্ ল স্―পায়ের পাতা ডুবছে। ডুবে গেল! এবার জল উঠবে হাঁটু অবধি। হাঁটুও ডুবে যাবে। তারপর কোমর। বুক, গলা―
‘টেন্টেলাস কাপ’-এর মতো জল এখন চিবুক পেরিয়ে ঠোঁটের তলায় খেলা করছে, ছোট ছোট ঢেউ তরঙ্গ। আওয়াজ উঠছে―
খল্ বল্ খল্ বল্―
সে আর কতক্ষণ! একটু বাদেই তো ঝিঁজরির টানে চোখ-কপাল-মাথাও ডুবে যাবে! তবু চাঁদের মরা আলোয় ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নায় রাতের নদীকে দু চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি। আর যে কখনও দেখতে পাব―তেমন ভরসা কই ?
কার যেন একটা কবিতা পড়েছিলাম, আবৃত্তিও করেছি। লাইন কটা এখনও মুখস্থ আছে―
‘ঢলে আছে জলছবি, ডিমের হলুদ চাঁদ, কলার মান্দাস
ঝুরো বাঁশপাতা কান্নিক মেরেছে জলে উছুক ডুবুক
জলতল ঢেকে আয়নায় পেতেছে মুখ রাতটুকু
সে কেমন চেয়ে থাকা বলো, মদালস আর কাকে বলে
জলের ভেতরে জলেরও নিজস্ব খেলা আছে; ক্রীড়াময়
জলগুল্ম ভেসে যায়; মনোহর রাজহংস ডুবে গেলে
উঠে আসে নদীর বুদ্বুদ; সে কেমন শতদল বলো
হেমবৃন্তে ধরে আছে প্রেক্ষাপট জলের বৈভবমালা’
তবে রাতের হোক দিনের হোক, আমাদের সুবর্ণরেখাও কম সুন্দর না। সোনা যেমন তেমন, দিনভর নদীর বালিয়াড়িতে সূর্যের আলো পড়ে অভ্র চিক চিক করে।
এমনকি চরাচরে ফিঙ-ফোটা-জ্যোৎস্না থাকলে রাতেও তার ব্যত্যয় হয় না। এখন তো মরা আলো। জ্যোৎস্নায় ভাঁটার টান।
নদী এখানে পূর্বগামিনী। পশ্চিম থেকে চলেছে পুবে। পুবে, পুবে। দাঁতন-সোনাকনিয়াকে উত্তরে রেখে ফের ঢুকেছে দক্ষিণে, বালেশ্বরের ওলমারার দিকে। তারপর তো সাগরে!
এখান থেকে অতদূর দেখা যায় না বটে, তবে লাউদহ-কাঁটাপাল-কুলবনীর মাছমারা জেলেদের রাতের আলোর ‘ফুড়গুনি’ এতদূর থেকেও দেখা যায় বৈকি।
ওই, ওই তো ওই, ‘হাটুয়া’ মাছমারাদের ‘হ্যাজাক লাইট’ ‘টর্চ লাইট’-এর আলোর ঝলকানি নদীবক্ষে!
‘পড়িবু শুনিবু রইবু দুখে।
মাছ-অ ধরিবু খাইবু সুখে ॥’
সত্যি সত্যিই তো। লেখাপড়া শিখে আমার কী দুর্দশা হলো! ‘অর্গলা ভূত’-এর পাল্লায় পড়ে এখন আমি দুঃখের সাগরে ডুবে যাচ্ছি। অথচ ওরা―মাছমারারা। কাঁটাপাল, কুলবনী কী ঢেরাছাড়ার হরি-মধু-যদুরা। আজ সারারাত রাতভোর সুবর্ণরেখায় ‘উকা’য় মাছ মারবে। ধরামাছ কতক সকাল হলেই নদীর পাড়ে বসে বেচে দেবে। কতক এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে ফেরি করবে। আর কতক মহাসুখে বাড়ি নিয়ে যাবে খাওয়ার জন্য।
পুবের মতো পশ্চিমেও। পাতিনা-ফুলবনী-মলতাবনীর ওদিক থেকেও ‘বাঘযুগনি’ পোকার আলোর মতো টি-পি-ক টি-পি-ক করে মাছমারাদের একটি-দুটি আলো।
এরা আজ আমাকে পায়ে ঝিঁজরি বেঁধে ধরে এনেছে বলেই কি নদীপথের মাঝবরাবর মশানির দহে মাছমারাদের একটাও আলো নাই! এদিকে নদীধারের গ্রাম খান্দারপাড়ার মাধব পানি আর ঝাড়েশ্বর পানি তো জলের পোকা। হরবখত, কী দিন কী রাত, নদীর বুকেই পড়ে থাকে। আজ তাদেরই বা হলো কী ?
আরেকটু বাদেই আমার চোখদুটো ঢেকে যাবে জলে। আচমকা দেখতে পাচ্ছি―ওই তো ওই, নদীজলে ছায়া পড়েছে জাহাজকানার জঙ্গলের! ছোট ছোট তরঙ্গাভিঘাতে সে ছায়া এতই কম্পমান যে স্পষ্টত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
অথচ কী অদম্য আগ্রহ অন্ধকারময় অরণ্যের খাঁজে খাঁজে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার!
কোথায় আত্মগোপন করে আছে সলিলসমাধিপ্রাপ্ত সওদাগর ‘তপোসা’ আর ‘পালেকাথ’-এর সেই অর্ণবপোত! যার ভাঙা কানার ঝলসানি হঠাৎ-দেখে-ফেলা-অন্যমনস্ক-পথচলতি-মানুষকে করে তোলে জন্মের মতো ‘উধাস’, ঘরছাড়া ও বিবাগী।
এখনও যতটুকু অবসর-পরিসর আছে ‘জাহাজকানার জঙ্গল’-এর জলে পড়া ছায়াটুকু থেকে আবিষ্কার করার―তাই খুঁজে দেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ছাতিনাগাছে চামড়ায় চোখ ঢেকে মটকা মেরে পড়ে থাকা অলম্ভুস দাঁড়কাকটা কি এসময়ই উড়ে এসে ঝপ্ করে বসল ‘জাহাজকানার জঙ্গল’-এ ?
কিছুই বুঝতে পারলাম না। তার আগেই এক হ্যাঁচকা-টানে কে যেন মুণ্ডুটা জলের তলায় টেনে নিল! জলে কতই তো ডুবে থেকেছি, কতই তো ডুবসাঁতারে এপার-ওপার করেছি―প্রথম প্রথম ঝুঁজকো আলো, তারপরই তো অন্ধকার। একটা নিরেট দেওয়াল!
জলতলের সামান্য নিচে, ঝুঁজকো সে-আলোয় যাও বা কিছু দেখা যায়, এই যেমন ব্যাঙ, মাছ, ইত্যাদি। ব্যাঙগুলো পিছনের দু-পা ঝুলিয়ে জলের ভিতর এক অদ্ভুত কায়দায় ঝুলে থাকে। মাছগুলো সতত সঞ্চরমাণ থেকে চোখের সামনে এসে পড়লে তাদের মাথাগুলো দেহের তুলনায় বেশ বড় দেখায়।
কারণে-অকারণে জল ঈষৎ আন্দোলিত হলে জলে-ঝুলে-থাকা মৃতবৎ ব্যাঙগুলোও চোখের সামনে তাদের ঝুলন্ত পায়ে জল ঠেলে যৎকিঞ্চিৎ উপরে উঠে যায়।
মাছেদের সে ডর-ভয় নেই। জল যত নাচে তারাও তত নেচে বেড়ায়, জল যত খেলে তারাও তত খেলে বেড়ায়। খেলতে খেলতে নাচতে নাচতে তারা অনায়াসে হাত-মুঠোয় এসে যায়, বাটা-খয়রা-তেলাপিয়া। অর্থাৎ, যাকে বলে ‘মাছধরা’ বা ‘মাছমারা’।
তাছাড়া, ওই যে কবিতা―‘জলের ভেতরে জলেরও নিজস্ব খেলা আছে; ক্রীড়াময় জলগুল্ম ভেসে যায়―’ হ্যাঁ, কাতাধারে, নদীর কিনারে হাঁটুজল ডুবজলে, এমনকি জলের অতলেও শ্যাওলা, ঝাঁজি, নানাবিধ জলগুল্ম, সবুজ উদ্ভিদ থাকে। তাদের কিছু কিছু পায়ে জড়ায়। আর কতক তো ভাসমান!
তবু দিনমানে জলতলের ঝুঁজকো আলোয় ব্যাঙ, মাছ, ঝাঁজি দেখা গেলেও রাতের, সে মরা জ্যোৎস্না কী ফিঙ-ফোটা- জ্যোৎস্নাই হোক অথবা ঘুটঘুটে অন্ধকার―কোন কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।
তাই, স্বভাবতই দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে এখন তো কেবলই ভয়াবহ মায়াময় অন্ধকার।
মশানির দহের জল। এ তো আর আমাদের সীতানালা খালের ‘পায়রা-চঁচরা-জল’ কী আমাদের গ্রামের চিনিবাস কুমহারের গাড়িয়া বা পুষ্করিণীর জল নয় যে তলদেশে যা আছে সবকিছুই দেখা যাবে। এই যেমন―পাঁক, পাঁকাল মাছ, কেঁচো, কেঁচোর গমনপথ, গেঁড়ি-গুগলি, শামুক, সাপের খোলস, টুট্টুরি ব্যাঙ, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, জলঘুন্নিপোকা―জলকলমি, নুড়নুড়ি পাথর, চুড়িভাঙা, কাচভাঙা, আঙরা, ঘুঙুর, নিমসাবানের খোপ ফেতিকাঁকড়া, লুবুকাঁকড়া, বাঁশকাঁটা, পচা পাতা, খড়ের মানুষ, মেঘ-চাঁদ-সূর্য, ভালবাসা, হত্যা, আত্মহত্যা―আরও যে কত কী!
আমাদের লোকায়ত একটা টুসুগানেও আছে―
‘জলে জলে যাইও টুসু জলে তোমার কে আছে।
মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো জলে শ্বশুরঘর আছে ॥’
টুসু। কোথাও দু-হাত, কোথাও বা চারহাত। মাটির নারীমূর্তি। আমাদের ঘরের মেয়ে। অঘ্রাণসংক্রান্তি থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত সে শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে আসে। আমাদেরই তল্লাটের কুমারী মেয়েরা মাটির একটি সরার মধ্যে ধানের তুষ আর গোবরের নাড়ু রেখে তার আবাহন ও পূজা করে।
মাথায় খোঁপা, চুলে বেলকুঁড়ি কাঁটা। হাতে টিকলি আর রাঙতার ফুল। আ হা! কী অপরূপ তার সাজ! তদুপরি গানে ও কথকতায় ‘জল জল’―তার যেন উপরন্তু একটা ‘বাঈ’ আছে। মেয়েরাও নদীপাড়ে মশানির দহে পৌষসংক্রান্তিতে তাকে বিসর্জন দিতে এসে অভিমান ভরে ‘জল জল যে কর টুসু’ বলে সমস্বরে একযোগে তাকে খোঁটাও দেয়।
টুসু প্রতি বছর আসে, প্রতি বছরই জলের তলায় তলিয়ে যায়। আজ আমি যাচ্ছি জলে, ‘জল জল’ কী আমারও বাঈ ?
জলের তলায় নাকি একবার ঢুকে পড়েছিল আমাদেরই গ্রামের বকড়ী সাধু শ্রীশ্রীঁ-নিত্যানন্দ বেহেরা। উঁহু, ঢুকে পড়েছিল বলাটা ঠিক না। তাকে ইশারা আর ছলনা করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রূপসী ‘সাতভউনী’রা।
আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিগরে কদমডাঙা ‘হুড়ি’। ‘হুড়ি’―তার মানে ছোটখাটো পাহাড়। পাহাড়ের সানুদেশে এক পাতালফোঁড় কুণ্ডি বা ঝরনা। অহোরাত্র সেখানে ‘ভুড় ভুড়’ করে জল ওঠে। সে জল শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে হিমশীতল।
সেখানেই থাকে ‘সাতভউনী’রা। ‘সাতভউনী’―তার মানে এক মায়েরই গর্ভজাত পিঠোপিঠি সাত বোন। সুনসান মধ্যাহ্নে কী ফিঙ-ফোটা-জ্যোৎস্নারাতে দিনক্ষণ দেখে ও বুঝে সাত-সাতটা সোনার গাগরা কাঁখে তারা বেরোয়।
বকড়ী নিত্যানন্দও ঝরনার জলে স্নান ও আচমন সেরে পূর্বাহ্নে ভোর ভোর আর সায়াহ্নে ঝুঁজকো অন্ধকারে সেখানেই জপতপ করে।
পায়ে নূপুরনিক্কণ, নৃত্যায়িত দেহবল্লরী, কাঁখে সোনার গাগরা, মুখে গীত―সাত-সাতটা অসাধারণ সুন্দরী রমণীকে একদিন দেখে ফেলল নিত্যানন্দ! ইশারায় তারা তাকে ডাকল।
যত না ইশারায় তার থেকেও সোনার গাগরার লোভে লোভে বকড়ী সাধু নিত্যানন্দ নাকি ঢুকে পড়েছিল জলের তলায় সাতভউনীদের ডেরায়।
মাত্রই একরাত। পরের দিন ভোর ভোর তাকে নাকি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল ভুড়ভুড়ি ঝরনাতলায়!
হয়তো কেউ বিশ্বাসই করেনি। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে লোকটা গীত বা গানের ‘গ’ও জানত না, সে কী করে তাদের সেই গাওয়া গানটাই নির্ভুল ভাবে গেয়ে দিল ? এখনও গেয়ে বেড়াচ্ছে―
‘একজন পথে মথুরা হইতে,
আইল তাহারে দেখি।
সেই হতে মন করে উচাটন
সঘনে ঝূরএ আঁখি ॥’
৪
মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে―জলের তলায় নিরেট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। উঁহু হেঁটে চলেছি কী আর, যেন কে বা কারা পায়ে ঝিঁজরি বেঁধে আমাকে টানতে টানতে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।
আবার সময় সময় এরকমও বোধ হচ্ছে―না, হাঁটছি তো না। পায়ে লোহার ঝিঁজরি বেঁধে কেউ আমাকে টানতে টানতে নিয়েও যাচ্ছে না। আসলে বন্দি হয়ে আছি নিরেট একটা অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে।
কাকেও দেখতে পাচ্ছি না। কেউ আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। জল কোথায় ? সব তো চাগড়া চাগড়া স্তূপীকৃত অন্ধকার। আমার চারধারেই হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেদার!
তবে এ অন্ধকারের স্পর্শ ততটা ভয়ঙ্কর নয়। কেমন যেন মেদুর ও মোহময়। শরৎচন্দ্রের ‘নৈশ অভিযান’-এর ‘আঁধারের রূপ’ পড়েছি―
‘কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া
একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরাল
প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র―
গতিশীলতা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক।
প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার
বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সেকথা আমি আজও ভুলিতে পারি
নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন
এক বিরাট্ কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক
আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া
করাল দংষ্ট্রা রেখার ন্যায় দিগন্ত বিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে
কি একপ্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত
বিচ্ছুরিত হইতেছে।’
নাবালকোত্তীর্ণ প্রায় যুবক হয়ে ওঠা আমার পক্ষেও হয়তো এই অন্ধকারের ‘অপরিমেয় গম্ভীর রূপ’ উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। তবু, তবু তো!
চাগড়া চাগড়া স্তূপাকার অন্ধকারের মধ্যেও কোথাও যেন ফাটাফুটো থেকে গিয়েছে। গহন-ঘন-অন্ধকার অরণ্যানীর মধ্যেও যেমন ফাঁক-ফোকর।
তার ভিতর দিয়ে, তার ভিতর দিয়ে মেদুর ও মোলায়েম অন্ধকারের আদর হল্কার মতো ভেসে আসছে। আমার হাত ধরে নাড়া দিচ্ছে, চুল নেড়ে দিচ্ছে, নাক টিপে দিচ্ছে, চিবুক ধরে এ-পাশ ও-পাশ করছে।
নাকে-কানেও অন্ধকার যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এই বুঝি বেদম হেঁচে উঠব! অকস্মাৎ কোথাও একটা কাক ডেকে উঠল।
এমন তো হয়েই থাকে। হয়তো মধ্যরাত্রি অথবা ভোরের দিকে সামান্যই ঢল নেমেছে।
মরা ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না কিংবা ঝুঁজকো অন্ধকার।
কাকেরও ভ্রম হলো, প্রাতঃকাল আসন্ন ভেবে সে হঠাৎ ডেকে উঠল। সে ডাকল ডাকল, ঘুমন্ত প্রতিবেশী কাকটাও যে ঘুম ভেঙে তার সঙ্গে সঙ্গত করল! একবার নয়, দু-দুবার ডাকল।
তবে কি কুটুস পিঁপড়ের দল কাকেদের কামড় বসিয়েছে ? সময় সময় কাক কী শালিকের বাচ্চার লোভে সাপও তো ঢুকে পড়ে পাখিদের বাসায়!
পিঁপড়ে কী সাপের অতর্কিত আক্রমণে হোক, ভ্রমে-বিভ্রমে হোক, কাক রাত্রিবেলায় ডেকে উঠলেও উঠতে পারে। তাবলে মশানির দহের তলায় ঘোর অন্ধকার প্রদেশে কাক এল কোত্থেকে ?
তবে কি গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে চামড়ায় চোখ ঢেকে ছাতিনাগাছে বসে থাকা অলম্ভুস দাঁড়কাকটা সারা দিনমান একবার ছাতিনাগাছ একবার জাহাজকানার জঙ্গল করে কাটিয়ে দিলেও রাত্রিতে সে নেমে আসে মশানির দহের তলদেশে ?
এ সময়ই কাকটা আবারও একবার ডেকে উঠল। পাতিকাকের ডাক না দাঁড়কাকের গলা―জলজ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আসা ঠিক বুঝা গেল না। জলের ভিতর দিয়ে আসা ডাক তো কানে জলদগম্ভীরই শোনাল!
কাকের ডাক থেমে গেলে আবারও সেই অন্ধকারময় হাওয়ারই ফিসফিসানি। জলের তলায় এত হাওয়াই বা এল কী করে ?
অবশ্য জল তো হাওয়ারই সংমিশ্রণ। এইচ২ অ১=জল। জলে হাইড্রোজেন (ঐ২) অক্সিজেন (ঙ১) তো আছেই। বায়ু বা ২-এর মধ্যে ঐ২ জ্বলে জল উৎপন্ন করে। পৃথিবীর চারভাগের মধ্যে তিনভাগই তো জল!
জলই জীবন। জল নিয়েই কত হাজার হাজার কবিতা। রবীন্দ্রনাথের ‘বধূ’ যেমন―
‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল’
পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে―
কোথা সে ছায়াসখী, কোথা সে জল।’
পাতিকাক হোক দাঁড়কাক হোক, জলের ভিতর দিয়েই তাদের আনাগোনা। তবু, তবু তাদের ডানার পালকে জল লাগল না ছিটেফোঁটাও ?
আমার অবস্থাও তদ্রƒপ। জলেরই ভিতর দিয়ে পায়ে ঝিঁজরি বেঁধে ওরা আমাকে এতক্ষণ টানতে টানতে নিয়ে এল, এখনও টেনে নিয়ে চলেছে। অথচ আমার গায়ের গেঞ্জি পরনের পাতলুন যেমনকার তেমনই থাকল, শুকনা খড়খড়ে। কোথাও জলের দাগ লাগল না কিছুমাত্র ? এ যেন সেই―‘আমার যেমনি বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাবো না―’
এবার ঘরের কথা, মা-কাকিমাদের কথা, পরীক্ষার কথা মনে পড়ে গেল হুদ্ হুদ্ করে। রাত পোহালেই আমাদের গ্রামের সঙ্গে চাঁদাবিলা গ্রামের একটা ফুটবল ম্যাচ আছে―
আমিই গোলে খেলব। কিন্তু আমার অবর্তমানে হয়তো গোটা ম্যাচটাই পণ্ড হবে। নতুবা পরিবর্ত গোলকিপার নিবারণ মাঠে নামবে। সে আমাদের দখিণসোলের সোঁতায় বুলান-হদহদিতে যত না মাছ ধরার ‘ঘুনি’ আটকে মাছ ধরতে পারে, তুলনায় গোলে দাঁড়িয়ে বল ধরতে ততটা দড় নয়।
পরের পর গোল খেয়ে আমরা অবধারিতভাবেই হেরে যাব। গ্রামের পক্ষে সেটা খুব সম্মানের হবে না। ‘প্রেসটিজ’-এর দফারফা হয়ে যাবে! অথচ চাঁদাবিলার নামকরা স্ট্রাইকার বীরবল মাহাতো আমি গোলে দাঁড়ালে গোল দেওয়া তো দূরঅস্ত্, এতদিনে একটা বল নিয়ে গোলের চৌহদ্দিতেও ঢুকতে পারে নি!
মা-কাকিমারা বাবা-কাকারা এখনও জানতেই পারেনি। কী করেই বা জানবে ? তারা তো এখন ঘুমাচ্ছে! আমি জানি, কাল সকালে সবার আগে উঠবে আমাদের মেজোকাকা। উঠেই ভোর ভোর চলে যাবে বিলে-বাতানে। জমিজমার তদারকি করতে। আল কেটে জমির অতিরিক্ত জমা জল বের করে দিতে। কখন বা পাশের ঝরনা থেকে নালা কেটে জল নিয়ে আসবে বতর দিতে রুখাশুখা জমিতে। ঘরে ফিরতে তার বেলা হবে।
পরে পরেই উঠবে মা। উঠেই প্রথমে খোঁড়লের ঝাঁপ খুলে বের করে দেবে হাঁস আর মুরগিগুলোকে। ‘চিঁ-চিঁ’ ‘চ্ই-চই’ করতে করতে তারা বেরিয়ে যাবে। তারপরই ডাক পড়বে আমার―‘ও রে ওঠ্ রে! আর কত ঘুমাবি ? বেলা ঢের হলো বাবা!’
একবার দুবার তিনবার। সাড়া না পেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে আসবে মা। হাণ্ডুলমাণ্ডুল হয়ে খোঁজাখুঁজি করবে―‘এত ভোরে না বলে কোথায় গেল ছেলেটা ?’
একে তাকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে আমাদের ঘর তো আমাদের ঘর, গোটা বাখুল তো গোটা বাখুল―মায় গোটা গ্রামটাকেই মাৎ করে ছাড়বে না আমার মা ? গ্রামের সমস্ত মানুষকে উদব্যস্ত করে মারবে না আমাদের মা ?
তারপর তো কান্না―কান্না―অঝোরঝর―অঝোরঝর― ‘রাতে খেয়ে দেয়ে ভালো ছেলে আমার ভালোয় ভালোয় ঘুমাতে গেল আর সকাল হতে না হতেই জলজ্যান্ত ছেলেটা হাওয়া!’
অতঃপর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা-কাকারাও কাঁদুলমাদুল মুখ করে যে পারবে যেদিকে খুঁজতে বেরুবে।
‘তাই তো! আজ চাঁদাবিলার সঙ্গে আমাদের গ্রামের জব্বর ফুটবল ম্যাচ আছে। ভোর ভোর উঠে প্রাকটিসে গেল না তো ছেলেটা গোঠটাঁড়ের মাঠে! যা তো ‘পুরিয়া’ দৌড়ে একবারটি দেখে আয়!’
‘পুরিয়া’ অর্থাৎ পুরুষোত্তম কাকা দৌড়ুবে আমাদের ফুটবল খেলার মাঠে। ‘কোথায় ছেলেটা ? কোথায় ? গোঠটাঁড়ের মাঠে তো কতকগুলো গরু বসে বসে জাবর কাটছে!’
তাদের গায়ের ‘কেতুর’ খুঁটে খেতে কয়েকটা কাক উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঞ্ছাদের মেয়েটা বগলে ঝুড়ি নিয়ে গোবরের নাদি কুড়োচ্ছে।
‘কই, জিজ্ঞেস করায় সেও তো বলল না―বল নিয়ে লোফালুফি খেলতে ছেলেটাকে দেখেছে সে ?’
বাবা-কাকারা কেউ পুবে যাবে কেউ পশ্চিমে যাবে, এমনকি দক্ষিণের লাটায়-পাটায় খোঁজাখুঁজি করবে। কিন্তু উত্তরে মশানির দহের কথা হয়তো তাদের মাথাতেই আসবে না।
কী করেই বা আসবে ? তারা তো আর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না―‘তেনারা’ শ্যাওলার নাম করে পায়ে লোহার ঝিঁজরি পরিয়ে টানতে টানতে আমাকে মশানির দহে, একেবারে জলের তলায় নিয়ে এসেছে!
বাবা-কাকারা মা-কাকিমারা আমার বন্ধুবান্ধবদের―টুম্পা, চামটু, ফাটাদার, ক্ষুদিরাম, অমিয়-মহেনদের ঘরে ঘরে গিয়ে তল্লাশি করবে, জনে জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে―
গতকাল আমার সঙ্গে তাদের যখন শেষ দেখা, শেষ কথা হলো, তখন ভোর ভোর বা গতরাতে আমি কোথাও চলে যাবার কথা তাদের বলেছি কীনা―
সব দিক থেকে যখন একই উত্তর আসবে―‘না, কোথাও দেখছি না’ ‘কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না’ ‘কই কিচ্ছু তো বলে যায়নি’ ইত্যাদি ইত্যাদি―
তখন শোকে মুহ্যমান আমার মা তার পায়ের কাছে টিঁ টিঁ আওয়াজ এক-পা দু-পা করে এসে পড়া আমাদের ‘কটকটি কাটুল’টা অর্থাৎ সদ্য সদ্য ডিম পাড়তে শুরু করা মুরগিটা, যে কীনা এসময় ‘কট কট’ শব্দ করে হামেশাই আওয়াজ দেয়, সেই তাকেও মা অভিযোগ করে বসবে―
‘সময় নেই অসময় নেই ‘কট্ কট্’ করে এত ডাকিস, আর তোদের খোঁড়লের পাশ দিয়ে আমার ছেলেটা ‘অগস্ত্য যাত্রা’ করল তুই মুখপুড়ী একবারও ডাকলি না ?’
সেই যেমনটা ‘নিমাইসন্ন্যাস’ যাত্রাপালায় আছে―
সন্তর্পণে ঘুমন্ত স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার শাড়ির গিঁট খুলে, ঘুমন্ত মা শচীরানিকে পাশ কাটিয়ে নিমাই সন্ন্যাসযাত্রা করল। কাকপক্ষীটিও টের পেল না।
অতঃপর ঘুম থেকে উঠে প্রাণের নিমাইকে দেখতে না পেয়ে শোকাতুরা শচীরানি পশুপাখিকেও অভিযোগপূর্বক দোষারোপ করে বিলাপ করছে―
‘আমার নিমাই যাবার কালে।
কোকিল কেন ডাকলি না রে ॥’
কোকিল ডাকল না, মুরগিও ডাকল না। মা-ও কিছু জানতে পারল না। অথচ আমাকে মাঝরাত্তিরে নিরুপায় হয়ে যেন নিশির পাল্লায় পড়ে আসতেই হলো মশানির দহের জলে, রসা-তলে!
কীনা, সেই কোন মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ণের সন্ধিক্ষণে, চামড়ায় চোখ ঢেকে মটকা মেরে দাঁড়কাকটা ছাতিনাগাছে উড়ে এসে জুড়ে বসল। অজস্র তালচড়ুই হুরহার ফুরফার করে গাছটার চারধারে উড়ে-ঘুরে বেড়াল। তখনই শ্যাওলার মতো কী একটা যে আমার পায়ের দু আঙ্গুলের ফাঁকে জড়িয়ে গেল! জড়িয়ে থাকল। জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে থাকছে―
অকস্মাৎ কোথাও কারও হাত থেকে যেন ঝন ঝন করে গাদাগুচ্ছের বাসন পড়ল! কাঁসা-পিতলের বাসন জলে পড়লে কি ‘ঝন ঝন’ আওয়াজ ওঠে ? কেউ কি ডাঙার উপর থেকে বাসনকোসনগুলো ছুড়ে ফেলল জলে ? নাকি,জলের ভিতরেই কাঁসা-পিতলের তৈজসগুলো হাত ফসকে জলেই পড়ে গেল ?
বাসনকোসনগুলো ডাঙা থেকে জলে ছুড়ুক আর নাহয় জল থেকে জলেই পড়ুক, একটা ঝনঝনানি আওয়াজ তো জলতরঙ্গের মতো তরঙ্গায়িত হতে হতে আমার কানেও এসে পৌঁছেছে। যেমনটা পৌঁছেছিল কাকের ডাক।
একটা কথা আমরা সকলেই জানি। স্থির জলাশয়ে একটা ঢিল ছুড়লে ঢিলটি যেখানে জল স্পর্শ করে সেখানে একটি আলোড়ন বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সে তরঙ্গ ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে জলাশয়ের কিনারায় পৌঁছে যায়।
তেমনটাই শব্দ। শব্দও যেখানে সৃষ্টি হয় তার চারধারে শব্দতরঙ্গও ছড়িয়ে পড়ে। উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব কম হলে শব্দের প্রাবল্যও বাড়ে। আবার শ্রোতার দূরত্ব বেশি হলে প্রাবল্য কমে।
তদুপরি মাধ্যম। মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতার উপরও শব্দতরঙ্গের গতিবেগ ও প্রাবল্য নির্ভর করে। কেননা তরঙ্গ বা কম্পন একটি আন্দোলন যা কোনও মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়।
বাতাস বইলে যেমনটা ঘটে ধানের খেতে―
‘কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা খেতে।’
এখানে মাধ্যম তো জল। মনে হয় আমিও শব্দ-উৎসের কাছাকাছিই আছি। না হলে স্পষ্ট, এত জোরে জোরে কাকের ডাক, বাসনকোসনের ঝনঝনানি শুনব কী করে ? তবে এদের এখানে কি আর ‘নিউটন’ ‘আর্কিমিডিস’ ‘ল্যাভয়সিয়ের’-এর থিসিস ‘অ্যাভাগাড্রো’র হাইপোথিসিস খাটে ?
যা হোক জলে তো জলে, ডাঙায়ও হঠাৎ হঠাৎ হাত থেকে বাসনকোসন পড়ে যায়। তারপর ঝন ঝন করে বিকট আওয়াজ হয়।
সুনসান মধ্যাহ্ন। বাইরে খাঁখাঁ রৌদ্র। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে রান্নাঘর গুছিয়ে রেখে গৃহস্থ নির্ধুমসে ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠোনে মাচানতলে ছায়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে কুকুরটা―
বিড়ালটাও বিশ্রামরত।
আচমকা রান্নাঘরের তাক থেকে একটার পর একটা বাসনকোসন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ঝন ঝন করে বাজতে লাগল! গৃহস্থ তো গৃহস্থ, মায় কুকুরটা-বিড়ালটাও চমকে জেগে উঠে এদিক সেদিক দৌড়তে লাগল।
দরজা খুলে গৃহস্থ দেখল―কোথায় কী ? কেউ নেই, মেঝেতে বাসন পড়ে শুধুশুধুই গড়াগড়ি খাচ্ছে!
এ তো গেল গৃহস্থের কথা, গ্রামের মধ্যে। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে ফাঁকা মাঠে কবেকার পোড়োবাড়ি একটা! লোকজন ঘর ফেলে চলে গেছে অন্যত্র। তার ধারেকাছে থাকে বলতে মোটের উপর একটা খেজুরগাছ আর একটা বিরুদবৃক্ষ।
ধূ ধূ হাওয়া এসে লাট খেতে খেতে হঠাৎ হঠাৎ ঢিস্ ঢিস্ করে ধুলো ওড়ায়, বিরুদ বৃক্ষের ডাল ভেঙে দেয় মট মট করে!
অধিকন্তু সুনসান মধ্যাহ্নে কী মধ্যরাতে আলো জ্বলতে দেখা যায়। ঝন ঝন করে গড়িয়ে পড়তে থাকে থালাবাসন, হাতাখুন্তি, ডেকচি-হাঁড়া।
এদিক দিয়ে মশানির দহ আরেক কাঠি সরেস। থালাবাসন হাতাখুন্তি ডেকচি-হাঁড়া এদেরও পর্যাপ্ত আছে বটে। সময় সময় জলের ভিতর জলদগম্ভীর ঝন ঝন আওয়াজ করে হাত থেকে পড়েও যায়।
এই এখন যেমন।
তবে এইসব তৈজস বাসনসামগ্রী আমাদের গ্রামের তথা আশপাশের গ্রামের, এমনকি সমগ্র তল্লাটের গরিবগুর্বো মানুষজনের ভারী উপকারে আসে!
ধরা যাক, দেখেশুনে মেয়ের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছে কুঁকড়াকুপী গ্রামের পাশের গ্রাম মহাপালে। নদীধারের গ্রাম, আখ-অড়হর-মুগ-ছোলার চাষসহ মোটামুটি সম্পন্ন পরিবার।
কিন্তু মেয়ের হবু শ্বশুরমশাই লোকটি এক নম্বর চশমখোর। পণ নয়, যৌতুক হিসেবে হয়তো চেয়ে বসেছে সোনাদানাসহ বস্তাদুয়েক কাঁসা-পিতলের বাসনকোসন আর হাঁড়া-কড়া বারকোশ।
মেয়ের বাপের তেমন আর সংগতি কোথায় ? ওই তো কটা গরু, ছেড়ী-ছাগল হাঁস-মুরগি, জঙ্গলের ধারে ডাঙা-ডুঙোড় কাঠাকতক জমি!
সোনাদানা ভরিকতক যাও বা জোগাড় হলো, বাসনকোসন তো ঢু ঢু! শূন্য শূন্য। অগত্যা ধূপ-ধুনো-সিঁদুর আর গোটাকতক গোটা সুপারি উৎসর্গ করে সকাল-সন্ধ্যা মশানির দহের ধারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে না মেয়ের বাপ ?
হাতে হাতেই ফল। একদিন ভরসন্ধ্যায়, ওই যখন চামড়ায় চোখ ঢেকে ছাতিনাগাছে মটকা মেরে বসেছিল অলম্ভুস দাঁড়কাকটা, তখনই কীনা মশানির দহের জলে ভুস করে ভেসে উঠল একের পর এক যত সব থালাবাসন হাঁড়া-কড়া-বারকোশ!
মেয়ের বাপের আনন্দ আর ধরে না। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় উতরে গেল। শুধু কী যৌতুকের দ্রব্যাদি ? চাওয়ার মতো চাইতে পারলে বিয়েসাদি, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনে ব্যবহার্য ডেকোরেটারের বাসনকোসন হাঁড়াকড়া হাতাখুন্তিও পাওয়া যায়।
তবে তা ফেরত দিতে হয় নির্দিষ্ট সময়েই, গুনে গুনে। গুনতিতে একটা তৈজসও যদি কম পড়ে, তখন মশানির দহ তাকে ছাড়বে না! হয়তো আমারই মতো পায়ে শ্যাওলা ওরফে লোহার ঝিঁজরি বেঁধে জলের তলায় টেনে আনবেই আনবে।
অতএব নিরেট কালো জলআঁধারে একটু আগে হাত ফসকে বাসনকোসন পড়ে যাবার যে জলদগম্ভীর ঝনঝনানি শুনেছিলাম, তা যে থালাবাসনেরই আওয়াজ, তা তো দেখছি মিথ্যে নয়। বরঞ্চ সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।
তা বলে রব―‘হাম্বা’―‘হাম্বা’―?
একবার নয়, দু-দুবার শোনা গেল। জলের ভিতর গরুর ডাক―কোত্থেকে এল ? এখানে শ্রীশ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ পুনরপি তর্জমা করে যে―
‘হাম্বা’,―ম্মা বি [সং হম্বা,―ম্ভ] গাভীর ডাক।
‘গরু মধ্যে মধ্যে হাম্বা হাম্বা করিতেছে’ [আলালের
ঘরে দুলাল]। ‘বৎসহারা যেন গাই, হাম্বা রবে
ফিরে যাই’ [দুর্গাপঞ্চরাত্রি]। ‘হাম্বা রবে ধেনু ধাইল
শুনি’ [বঙ্গসাহিত্য পরিচয়]
৫
পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগেই সৃষ্টি হয়। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাতের পরিমাণও ২ : ১ ।
তবু নদীর জলে বা সমুদ্রের জলে দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকতে হলে অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়। কেননা, নদীর জলে বা সমুদ্রের জলে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন ছাড়াও তো আরও অনেক কিছুই থাকে। যেমন―
সোডিয়াম পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আয়রন, ইত্যাদি ধাতুর সালফেট, ক্লোরাইড, কার্বনেট, বাই-কার্বনেটও থাকে।
আমাদের মশানির দহের জলে এত সব একসঙ্গে না থাকলেও কোনও কোনওটা, কিছু কিছু তো আছেই। তাছাড়া এখানকার জলতল বা পাতালের বাসিন্দারা এমন সব তুক-গুণ জানে, সময় সময় নিজেদের প্রয়োজনে জলের সঙ্গে এমন সব ‘অনুপান’ মিশিয়ে দেয় যে, এখানে তাবড় বিজ্ঞানও ফেল মেরে যায়।
তাই কাক তো কাক, গরু তো গরু, আস্ত মানুষও সল সল করে জলের তলায় ঢুকে পড়ে―আহা! আহা! স্ব-ইচ্ছায় কী আর! পায়ে ঝিঁজরি বেঁধে ‘তেনারা’ই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। কবিতায় পড়েছি―
‘এভাবে এইভাবে নয়, যেন যেতে হবে
কোথাও, কোথাও যাবার ঠিক ছিল, যার জন্য
অন্যতম ট্রেনের অপেক্ষায় পোশাক পাল্টে আছি
সংকেত এলেই স্টেশন আড়াল করে যাব
এ যেন, জল ঘেঁটে জলের ভিতরে চলে যাওয়া’
মনে হচ্ছে আশপাশে কোথাও গরুর গোঠ আছে। গরু চরছে, চুরনী গরুর গলায় কাঠের ‘ঠরকা’ বাজছে―‘ঠ-র-ক! ঠ-র-ক!―’
চরতে চরতে কোনও কোনও গরু হঠাৎ হঠাৎ দলছুট হয়ে জঙ্গলের গভীরে চলে যায় এদিকে সেদিকে। হয়তো কোনও উন্নততর ঘাস কী পাতার লোভে ও সন্ধানে। অথবা, পাছে মুখ দিয়ে দেয় ‘চুরনী’টা অন্যের খেতি-খামারে―ধানবিলে―
তাই তাকে ‘চুরনী’ সাব্যস্ত ও ‘চিহ্নত’ করে তার গলায় ঘন্টি বাঁধতে হয়। কুড়চি কী ডকাকাঠের ‘ঠরকা’ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। চরৈবেতি। যেখানেই যাক না―‘ঠ-র-ক’ ‘ঠ-র-ক’ আওয়াজ তার পিছু ছাড়বে না!
‘খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি’―খুঁজে পেতে আর কোনও অসুবিধাই হয় না। হ্যাঁ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ‘পালামৌ’-এ এহেন ‘কাষ্ঠঘণ্টা’র কথা পড়েছি বটে। ওই যে―
‘…বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠ-
ঘন্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল; কাষ্ঠঘণ্টা
পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত
পশু বনে পথ হারাইলে শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের
অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি।
কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে।
পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরও যেন অবসন্ন
করে…’
প্রথমে ‘হাম্বা’ ‘হাম্বা’, তারপরে ‘ঠ-র-ক’ ‘ঠ-র-ক’ই তো শুনলাম! সে আওয়াজ তো এখনও শুনছি―ওই তো ওই―‘ঠ-র-ক’ ‘ঠ-র-ক’―আর কেমন অবসন্ন বোধ করছি!
একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডেকে উঠল কোথাও! ‘কিচ কিচ’ ‘কিচির মিচির!’ অনেক পাখির ডানা ফেটানোর আওয়াজ! ‘ হুর্ র্হা’ ‘ফুর্ র্ফা’!
চড়ুই-টড়ুই হবে হয়তো। চটি-বনিরা, তালচড়ুইরা তো সকাল-সন্ধ্যা তালগাছের চারধারে, ঝোপঝাড় ঘিরে ধরে অনবরত ডানা ফেটিয়ে কীসব আওয়াজ করে! কত কী কথা বলে!
কথা বলে কী ? না, কিচ কিচ কিচির মিচির করে গান করে ? নাকি পূর্বাহ্নে সায়াহ্নে মন্ত্র উচ্চারণ করে তারা ?
যাই করুক না কেন, সে তো পূর্বাহ্নে-অপরাহ্নে, দিনের বেলায়। তা বলে এহেন ঘোর নিশীথে ? তদুপরি জলের তলায় ? পাতালে ?
হ্যাঁ, শীতের মরশুমে আমাদের সুবর্ণরেখা নদীকিনারে সকাল-সন্ধ্যা পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে যায় বটে। কোন সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে খড়হাঁস বালিহাঁস বিগড়িহাঁস!
উপরন্তু তাদের সঙ্গে জুটে যায় আমাদের দেশী সরাল, শামুকখোল, জলপিপি―জলপিপি তো এক পা দু পা করে একেবারে জলের ভিতর ঢুকে আসে! জলকাক বা পানকৌড়ি মাঝনদীতে ঘন ঘন মাথা ডুবিয়ে মাথা উঁচিয়ে সাঁতারও কাটে।
তবে তারা কি আর আমার মতো কখনও জলের তলায় অতলে এই অন্ধকারময় মহাপ্রদেশে এসে ‘ইনাদের’ কব্জায় পড়ে বন্দি হয়েছে ? ‘কারিকুরি’ বা পরিযায়ী পাখিরা, মুক্ত বিহঙ্গ তারা―‘যথা ইচ্ছা তথা যা’ ‘যাও পাখি বলো তারে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই আছে না ?―
‘যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুন্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।’
আসলে কী, ভয়ই পাচ্ছি ? পাখির ডাক তো পাখির ডাক, এহো বাহ্য, কানে ভুলভাল শুনছি কী ? পাখির ডাক নয়, পাখির ডাক নয়, জলঝিঁঝির ডাক ? ‘রিঁ-ই-রিঁ’ ‘রিঁ-ই-রিঁ’ ? জলে একজাতের ঝিঁঝিপোকাও থাকে নাকি ? যারা অনবরত নিজেদের পেট টিপে-রিঁ-ই-রিঁ করে ডাকতে থাকে ?
না, না। তা কেন ? এই তো এখন আর পাখির ডাক নয়, পাখির ডাক নয়। শুনছি তো একটানা ঘণ্টাধ্বনি! যে সে ঘন্টা নয়, এমনকি আমাদের রোহিণী চৌধুরানী রু´িণী দেবী হাইস্কুলের আর্দালি পিওন কার্তিক মাইতির হাতের ঘণ্টাধ্বনিও নয়। এ যে পাগলা-ঘণ্টির মতো বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে!
মনে তো হয়―কোনও মঠ বা মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে কোনও দেবারতি হচ্ছে। জলের তলায়ও দেবদেবীর পূজাপাঠ ? জলের তলায় কাকেশ্বর কুচকুচ্, চড়ৈ-চটি, ‘হাম্বা’ রবে গরু ডাকতে পারে, ‘ঝন ঝন’ করে থালাবাসন পড়ে যাবার আওয়াজ উঠতে পারে, সেখানে ঘণ্টা বাজিয়ে কোনও মঠ-মন্দিরে কোনও দেবদেবীর আরাধনা হবে―তাতে আর আশ্চর্য কী!
জলের দেবী তো গঙ্গা। পড়েছি বৈকি―‘দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে। শঙ্কর মৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।’ তাছাড়া, আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রীঅমূল্যচরণ মিশ্র কী শ্রাদ্ধে, ঘাটক্রিয়াদিতে, কী পূজার ঘটোত্তলনে এই সুবর্ণরেখা নদীকিনারে বসেই তো জলশোধনের নিমিত্ত মন্ত্র আওড়ান―
‘ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিংকুরু ॥’
হাতে জল নিয়ে জল ছিটাতে ছিটাতে বলেন―‘ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ’ ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো এক্ষণে গঙ্গারতিই হচ্ছে। জলের তলায় তারই ঘণ্টাধ্বনি।
পরক্ষণেই মনে হলো, ধুৎ! ‘এনাদের’ আবার গঙ্গারতি! শ্রীশ্রী হরিচরণ বন্দ্যো-র বঙ্গীয় শব্দকোষ চৈতন্যভাগবত তর্জমা করে বলে, ‘বোলে’ জান ভাই! কি গীত বাজন। কিবা কারও বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন ॥ হ্যাঁ, ঘণ্টাধ্বনি সহকারে বোধকরি ভূতের কীর্তনই হচ্ছে।
যেন একসঙ্গে অনেকের গলার আওয়াজও তো পাচ্ছি! সে-আওয়াজ যত মৃদুই বা ফিসফিসানি হোক। কী বলে তারা কীর্তন করছে ? নামগান করছে কী ? ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে’ ‘হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ ?
না, না। তাও কী হয় ? সেই বলে না―‘ভূতের মুখে রামনাম’! আমাদের গ্রামের তামাম লোকই তো জানে, জানেও মানেও যে, রামের নাম করলে ভূত তো ভূত, ভূতের বাপও পালিয়ে যায়!
‘রাম রাম!―পাপকথা শ্রবণে, ঘৃণায়, ভূতের ভয়ে উচ্চারণীয় রামনাম।’―তাই যদি সত্য হবে, তবে আমি কেন রামনামের শরণ নিচ্ছি না ? আসলে, প্রকৃত প্রস্তাবে, আমার গলা দিয়ে কোনও কথাই তো বেরোচ্ছে না, রামনামের শরণ নেব কী করে ?
তবু। তবু আরেকবার গলা ফুলিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে ডাক দিলাম, ‘রাম! রাম’ কোথায় কী, গলা দিয়ে বিন্দুমাত্র স্বরাগমই তো স্ফুরিত হলো না!
অথচ জলের ভিতর ডুব দিয়ে মুখের কাছে দু হাতের চেটো জড়ো করে কত আওয়াজ দিয়েছি, ‘কু-ব! ক-ব!’ তার প্রতিধ্বনিও শুনতে পেয়েছি, ‘কু-উ-ব! কু-উ-ব!’ যেন ‘কুবোপাখি কুব্ কুব্ ডাক দেয় লুকায়ে কোথাও―’
ঘণ্টাধ্বনি তো এখনও বেজে চলেছে! রাত কত হলো ?―কে জানে! রাত যখন ভোর হবে, চারধারে আলো ফুটবে, রাতচরারা ফিরে এসে সন্তর্পণে এ-ডাল সে-ডাল করবে, ঝোপঝাড়ের চারধারে তালগাছটাকে ঘিরে ধরে অজস্র তালচড়ুই, চটি-বনি প্রাতঃকাল আসন্ন ভেবে হুর্ র্হা ফুর্ ফার্ উড়েঘুরে বেড়াবে। তা বলে মশানির দহের জলে, জলতলেও কী অনুরূপ রাত্রি শেষের দৃশ্যাবলি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাবে ?
কে বলবে ?―সে সমস্ত তো মশানির দহের ‘তেনারা’ই জানে! জলে কখন কী জড়িবুটি, অনুপান মেশাবে বা ‘মূল্য ধরে দেবে’ যার প্রভাবে রাত দিন হয়ে যাবে, দিন রাত হবে। নয়কে ছয় করবে, ছয়কে নয়।
মনে মনে এত কিছু ভাবছি বটে। কিন্তু কই, কাউকেই তো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না ? অথচ মাঝেমধ্যেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে কে বা কারা আমাকে পায়ে ঝিঁজরি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে!
টানছে তো টানছেই! ‘আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ? বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।’ সোনার কী আর, লোহার। লোহার ঝিঁজরি। তাও তো হাতড়ে হাতমুঠোয় নাগাল পাচ্ছি না! কীসব কলকব্জা দিয়ে তৈরি!
মাঝে মাঝে ঝিমুনি আসছিল। তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব। কিন্তু ‘তেনাদের’ হ্যাঁচকা টানে ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছিল। ঘুম কী আর―ওই ঘুম-ঘুম ভাব।
তবে কি ভয় পাচ্ছি না ? উঁহু, ভয়ডর তো আছে ষোলোআনাই। তবু একটা জেদ, চাপা উত্তেজনা―দেখিই না শেষ পর্যন্ত কী হয়! কথাতেই তো আছে―‘পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।’
মনে হলো, হঠাৎ ঝড় উঠেছে, ঝড়! নদীর জল তোলপাড় হচ্ছে। জলতল প্রকম্পিত করে গর্জন। গর্জনটা যেন এদিকেই ক্রমে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে!
সমুদ্রে ‘টর্নেডো’ বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কথা তো ভূগোলেই পড়েছি। এর উৎপত্তির সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনেক বিজ্ঞানীদের মতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিশালাকার ঝড়ই এর উৎপত্তির মূল।
ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে উত্থিত ফানেল আকৃতির বজ্রবিদ্যুৎসহ মেঘ ও ঝড়ই টর্নেডোর কারণ। এর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ শো কিলোমিটার। গতিপথে যা পায় সব কিছুকে ধ্বংস ও তার তোল মাটি ঘোল্ করে ছাড়ে!
তা বলে নদীগর্ভেও কি ‘টর্নেডো’ হয় ? হয় হয়। এমন হয় যে নদীকে জলসহ উৎপাটিত করে অন্য কোনও খাতে আছড়ে ফেলে দেয়। পরিবর্তে সেখানে হয়তো আস্ত কোনও জনপদ বা নগরকে বসিয়ে দেয়।
এমনি কোনও সামুদ্রিক ঝড় কী নদীঝড়েই তো একদা ডুবে গিয়েছিল ‘ওক্কলবা’ তথা উৎকলের সওদাগর ‘তপোসা’ ও ‘পালেকাথ’-এর ‘আদজেত্তা’ বা তাম্রলিপ্ত বন্দরগামী অর্ণবপোত!
টর্পেডো, টাইফুন, টর্নেডো কী সাইক্লোন আজ সুবর্ণরেখা নদীবক্ষে তথা মশানির দহে যুগপৎ আছড়ে পড়ুক, জলস্তম্ভ উঠুক, জলঝড়। তোল মাটি ঘোল হোক। নদীতল উপরে উঠুক, জলের উপরিতল নিচে নামুক।
তবেই তো আমার লোহার-ঝিঁজরি-বাঁধা বন্দিদশা এবারের মতো ঘুচে যাবে! এক বার যদি উপরে উঠতে পারি আর আমাকে পায় কে! হারান-পরাণ-মন্মথ-পরিতোষদের মুগচনা ছোলামটরের খেতের উপর দিয়ে কুদি মেরে এমন দৌড় দৌড়ুব! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গুপ্তধন’ গল্পে যেমনটা আছে―
‘সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন’, মৃত্যুঞ্জয়,
কী চাও।’ সে বলিয়া উঠিল, ‘আমি আর কিছুই
চাই না―এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলক-
ধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির
হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি
চাই।
সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে
মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না ?’
মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ‘না, যাইব না।’
সন্ন্যাসী কহিলেন, ‘একবার দেখিয়া আসিবার
কৌতূহলও নাই ?’
মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ‘না, আমি দেখিতেও চাই না।
আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে
হয় তবু আমি এখানে একমুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।’
হাঁড়া হাঁড়া গর্জন তেল ‘অনুপান’ হিসাবে জলে মিশিয়েও হয়তো কাজের কাজ কিসসু হলো না। ঝড় উঠলই। প্রলয়ঙ্করী ঝড়। সে-ঝড়ে যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সবকিছুই। মড় মড় করে কতক হাড়গোড় ভাঙল আর আমি মূর্ছিত হলাম।
যাত্রাপালা বা নাটকের ‘পতন’ ও ‘মূর্ছা’ নয়, সত্যি সত্যিই আমি জ্ঞান হারালাম। তবে সে কতক্ষণ বলতে পারি না। জ্ঞান যখন ফিরল তখন শুনি পাখি ডাকছে। ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল―’
তবে এসব কী পাখি ? চারিভিতে তালীবন আছে বটে, তার চারধারে হুর্ হার্ ফুর্ ফার্ করে তালচটা-চড়ৈ উড়েঘুরে বেড়াচ্ছেও। তবে তারা এত নধরগতর হৃষ্টপুষ্ট হলো কী করে ?
তালগাছগুলোই বা এত দীর্ঘ আর ঘন পাতাসন্নিবিষ্ট কবে হলো ? আমাদের গ্রামের মুচিরামদের বসতবাটির পশ্চাতে যে তিন-তিনটি সিড়িঙ্গে তালগাছ আছে, মরাহাজা, তাদের তো কভু এত লালিত্যময় দেখি না।
তবু শ্রাবণ-ভাদ্রে তাল যখন পাকে, মুচিরামের পিসি পদ্মবুড়ির তখন কী আহ্লাদ। কী আনন্দ! ‘আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!’ ঘন ঘন তালতলায় যায়, তাল পায়, তাল কুড়ায় আর উপর্যুপরি ছড়া কাটে―‘উপরন্তু পড়ল দুম্। দুম্ বলে মোর পোঁদ শুঙ্ ॥’
তাছাড়া আমাদের গ্রামের মাথায় আর তালগাছ কোথায় ? আছে তো বড়জোর একটা কুসুমগাছ, কুসুমতলা। একটা মহুয়া বা মুহুলগাছ, মহুলতলা। কটা লাল ভেরেণ্ডা, বাঘনখী আর বিরি-বাইগনের ঝাড়।
কাঁকুরে-এঁটেল মাটির সমুন্নত ছোটখাটো পাহাড় বৈ আর কিছু না আমাদের গাঁমুড়ো, গ্রামের মাথা। পা টিপে টিপে সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। আসতে যেতে চড়াই-উৎরাই-এর পথ। তার মধ্যেই অরণ্যদেবের খুলিগুহার মতো আমাদের গ্রামের মৃৎশিল্পী কুম্ভকারদের ‘মাটিখানা’। হাঁড়ি-কলসি কুঁদা-কুঁজো গড়বার মাটির কারখানা।
এখানে, এই ‘তেনাদের’ ভূখণ্ডে তেমন দেখি না। চেনাজানার মধ্যে তালগাছ আছে বটে। পাকুড়, বাঁশ, ইক্ষু, ভুট্টাগাছও দেখছি এদিক-ওদিক। তিলগাছ, তুলোগাছ, নারকেল-গাছও আছে। কিন্তু বাকি সব উদ্ভিজ্জ কেমন নতুন নতুন, আর বৃহদাকার।
প্রথমটায় ভেবেছিলাম ঝড়ঝঞ্ঝা জলঘূর্ণির মারণ-উচাটনের ধাক্কায় মশানির দহের উপরে উঠে আমাদের শ্মশানেই আছড়ে পড়েছি, ঘোর কেটে গেলেই গ্রামের দিকে কুদি মেরে দৌড়ুব―দৌড় দৌড়―হা হতোস্মি! আমাদের গ্রাম কোথায় ?―‘ঐ যে গাঁ’টি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের আড়ে, প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়াঝাড়ে।’
না না, এ তো অন্য কোনওখানে। অন্য কোনও গঞ্জে কী অন্য কোনও নগরে এসে পড়েছি! গঞ্জের পুরোভাগে বাঁশের ঝাড়, পাকুড়গাছ, পাটকাঠির বেড়া ও খড়ের ছাউনি দেওয়া পানের বরোজ অবশ্য আছে।
তদুপরি অদূরে গোচরভূমি―ওই তো ওই, সে-মাঠে গরুছাগলও চরে বেড়াচ্ছে। তবে তাদের আকার-আয়তনও অন্যরকম। অন্য রকম, অন্য রকম। একেকটা বৃহদাকার গাছপালা যেমন, ছাগল-গরুগুলোও তেমন। বেশ বড় বড়।
পর্যটক মার্কো পোলো নাকি সেবার বাংলায় এসে হাতির মতো বড় আর লম্বা লম্বা ষাঁড় দেখেছিলেন! ‘আইন-ই-আকবরী’তেও আছে―সেকালে শরিফাবাদে খুব সুন্দর সুন্দর সাদা ষাঁড়ের জন্ম দেওয়া হতো। একেকটার আকারও ছিল বিরাট বিরাট। একটা ষাঁড় নাকি একসঙ্গে ১৫ জন মানুষকে অবলীলায় টেনে নিয়ে যেতে পারত। সেকালের শরিফাবাদ তো একালের বর্ধমান!
প্রাগৈতিহাসিক যুগে গরুছাগলের চেহারা-চরিত্র ছিল তো হাতির মতোই। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সন নাগাদ গরু-ছাগল-ভেড়া আকারে ছোট হতে শুরু করল। আর মার্কো পোলোর যুগ ১২৮৮-১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ তো এই সেদিন!
যা হোক এই গঞ্জটি আকারে-প্রকারে সুবিশাল হলেও কেমন যেন পোড়ো পোড়ো। হরিদ্রা আভা ধরেছে। ইতস্তত কতক পতিত বাস্তুভিটা, উইয়ের ঢিবির মতো উঁচু নিচু। দেখে তো মনে হয় ধ্বংসস্তূপ।
তা সত্ত্বেও, কী আশ্চর্য! কাছেপিঠের চাষাবাদের জমিতে ধান ফলেছে। শুধু কী ধান, আখ-ইক্ষু-নানাবিধ সর্ষপ-তাল-খেজুর- নারিকেল-পান-সুপারি। ঘরগুলোও খড়, নল-খাগড়া, পাতার ছাউনি দেওয়া দো-চালা চৌ-চালা কী আট-চালা। কাঁচা-পোড়া ইটের ব্যবহারও আছে দেখছি।
কিন্তু, এহো বাহ্য! কী ঘরে কী মাঠে, গোচারণেও এ পর্যন্ত একটাও লোক দেখি না। আমাকে যে বা যারা পায়ে ঝিঁজরি পরিয়ে মশানির দহের জলে ছলে-বলে-কৌশলে টেনে এনেছিল, তারাই বা গেল কোথায় ? ঝড়ের ঝাপটে তারা কি হাড়-গোড়-ভাঙা ‘দ’ হয়ে পড়ে আছে কোথাও ?
এদিকে-সেদিকে নড়েচড়ে বসলাম। এক-পা দু-পা হাঁটাহাঁটির চেষ্টাও করলাম। অনন্যোপায়। না না, পালিয়ে যাবার কোনও উপায়ই দেখি না। পায়ের ঝিঁজরি যেমনকার তেমন অটুটই আছে।
বোধকরি, এখান থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয়। জোয়ারবাহী নদীও হয়তো ধারেকাছেই। হাওয়ায় উড়ে আসছে, ভেসে আসছে ঢেউ-গর্জনের শোঁ শোঁ আওয়াজ। নদীর কল খল্। জলের গুঁড়ো।
মাথার উপর উড়েঘুরে বেড়াচ্ছে কাক-চিল-সমুদ্রপাখি। জমির খাঁড়িতে বাবলা-বাবুলের গাছে ঘুরপাক খাচ্ছে চড়ৈ-চটা―ওই তো নলখাগড়ার দঁকে নড়নচড়ন নট একটা ‘মাছরাঁকা’! মাছরাঙা তো নয়, মাছের ‘রাঁকা’। ‘রাঁকা’ তার মানে লোভী।
জোয়ারবাহী নদীধারের জমির নোনাপ্রকৃতি। ‘নুনিয়া’-ভাব কাটাতে চাষিদের তাই জমির আল বরাবর বাবলা-বাবুল-সুবাবুলের চাষ। তাছাড়াও জমিতে তারা গর্ত বা মাদা করে রাখে, জোয়ারের জমা জল শুকিয়ে যাতে নুন করতে পারে।
সেহেতু মাঠেঘাটে অষ্টপ্রহর লোক থাকারই তো কথা, তবু যে চারধার জনমানবহীন সুনসানই দেখি! দরিয়াদারী নদীধারের মাছমারা ‘জালুয়া’রাই বা গেল কোথায় ? তাদের তো রাত থাকতে ‘বেড়া-বেহুঁদি-সাবাড়-সারানি’ কী খেপলা জাল নিয়ে নদীতে মাছধরার ‘ভেউরি-জালিবোট’ কী বাছাড়ি নৌকোয় যেতে হয়।
আর তাদের ঘরের বউড়িঝিউড়ি এণ্ডাগণ্ডা গেঁড়িগুগলিরাও তো ঘর থেকে নদীঘাট পর্যন্ত ভোর হতে না হতেই হাট বসিয়ে দেয়। এরকম ছবি আমাদের বড়োডাঙা গ্রামের বধুক-বিশুইদের পরিবারেও কি কম দেখেছি!
রাস্তায় ঘাটে লোকজন না থাকুক, হাওয়া-বাতাসে কেমন যেন ‘আঁধারঘরে গাঁদার-গুঁদুর’ হিসহিসানি ফিসফিসানির আওয়াজ তো আছে! আছে, আছে।
আবার কোথাও কোনও মঠে বা মন্দিরে লাগাতার ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগল, যেমনটা কাল রাতেও শোনা যাচ্ছিল।
এমন সময়ই একটা জবরদস্ত গরুর গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। কাঠের খাঁচাওয়ালা গাড়ি, মাত্র একটাই বলদ। হাতির মতো বড় না হলেও বেশ বড়সড়ই। এমনটা কোথায় যেন দেখেছি ? কোথায় যেন ?
হুবহু একরকম। একই রকম। পিঠের তথা ‘শিব’-এর বা কুঁজের ওদিকটা ভুসভুসে কালো। পা, পেট সাদা। বাঁকানো সিং,বড়সড় গলকম্বল। হ্যাঁ, এটা যেন মহেঞ্জাদাড়োর ছাপ্পা-মারা সেই ‘ষাঁড়’।
এক্ষণে, এই চালকবিহীন কেবল ষাঁড়পরিবাহিত এক্কা শকটটিই কি আমাকে বলির নিমিত্ত পূজাস্থানে, সেই ‘অর্গলা ভূতের হাড়িকাঠ’-এ পৌঁছে দেবে ?
‘―সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্তি।’
৬
গো-শকটে আরোহণ মাত্রই শরীরে ও মনে বোধকরি নতুন ভাবের সঞ্চার হলো। অন্তত জলতল বা পাতালপ্রবাস থেকে উত্থিত হওয়ার পরে পরেই অনুরূপ ভাবই তো স্বাভাবিক। হালকা-পুলকা বোধই হচ্ছিল।
অথচ, গো-শকটে আরোহণ ও ভ্রমণের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ততটা সুখের নয় মোটেও। আড়ায় গাড়ায় পড়ে গো-শকটের চাকা পুনঃপুন ঘূর্ণন ও ঘর্ষণে এমন রগড়ে যায় যে ভ্রমণ-অন্তে সারা শরীরে, হাড়ে ও মজ্জায় ভয়ানক পীড়ার উদ্রেক করে।
কতই তো গো-শকটে চড়েছি! কার্তিক-অগ্রহায়ণে ধানকাটার মরশুমে ধানের খেত থেকে ধানের ‘বিঁড়া’ খামারে আনয়নের প্রাক্কালে, বন থেকে কাষ্ঠাদি আহরণের সময়ে, আরও নানাবিধ কৃতকর্মে।
চড়াই-উৎরাইয়ের পথে চলমান বোঝাই গাড়ির ভারসাম্য বজায় রাখতে, অর্থাৎ কিনা ‘উলার’ বা ‘ডাবু’ ধরতে একজন কাউকে না কাউকে, সে ছোট হোক বড় হোক, গাড়িতে থাকতেই হয়!
গাড়ি যখন খাদ থেকে উচ্চাবচে উঠছে, অথবা উচ্চাবচ থেকে খাদে অবতরণ করছে, তখন স্বাভাবিক কারণেই শকটের ভারসাম্য ঠিক থাকে না। উচ্চাবচে ওঠার প্রাক্কালে শকটের সম্মুখভাগ বলদের গলার দড়িদড়াসহ উপরে উঠতে চায়, উঠতেই চায়, যাকে বলে ‘উলার’। তখন দরকার হয় শকটের মাথায় অর্থাৎ অগ্রভাগে কারও না কারও চড়ে বসার।
আবার, অবতরণ সময়ে শকটের পশ্চাদভাগ অনুরূপভাবেই উপরের দিকে উঠতে চায়, উঠতেই চায়, যাকে বলে ‘ডাবু’। ভারসাম্য বজায় রাখতে তখন কাউকে না কাউকে চড়ে বসতেই হয় শকটের পশ্চাতে।
তা, এ তো গেল গো-শকটের শর্টকাট এক-দু ক্রোশের ভ্রমণকাহিনি। ততটা কষ্টের নয় বটে। কিন্তু একদা আমাদের যেতে হয়েছিল ক্রোশের পর ক্রোশ, তা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ক্রোশ দূরের বেলিয়াবেড়া রাজবাড়ির ‘রাসটাঁড়’-এ।
সেখানে রাসপূর্ণিমা তিথিতে রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসেছিল রাসটাঁড়ে। মেলায় যেমন এসেছিল ‘ভাণুমতীর খেল’ তেমনি তাঁবু গেড়ে ডায়নামো ফিট করে দেখানো হচ্ছিল ‘টকিজ’।
সেবার মাকে টকি দেখাতে গো-শকটেই পাড়ি দিয়েছিলাম বেলিয়াবেড়া রাজবাড়ির রাস-টাঁড়ে। টকিজের নাম ছিল ‘বেহুলা-লখিন্দর’।
আমাদের গাড়ি সুবর্ণরেখা নদীর হাঁটুজল অতিক্রম করে গড়ধরা-কাঠুয়াপাল হয়ে রগড়া গ্রামে পৌঁছাল। নদীজলে গাড়ি ডুবে যাওয়া ত দূরঅস্ত্, শুধুই বলদজোড়ার উদরমাত্র কিঞ্চিৎ ডুবেছিল।
গো-শকটের গাড়োয়ান ছিল আমাদেরই ঘরের সংবৎসর ভাত-কাপড়ের ‘ভাতুয়া’ মুর্মু সনাতন। সে ছিল গাড়োয়ানের গাড়োয়ান, রাজা গাড়োয়ান। বলদজোড়ার সঙ্গে তার ছিল ভারী ভাব। সে ‘হিঁ-ই ব-হঁ’ বলে এক অদ্ভুত ভাষায় তাদের সঙ্গে সারা রাস্তায় আলাপ জুড়ত। আর তারাও তার কথা শুনত।
গাড়ি চলত দুলকি চালে। একবার এদিকে গড়ায় তো একবার সেদিকে। গাড়ির ছইয়ের টুঙিতে একটা হেরিকেন বাঁধা ছিল, রাতের অন্ধকারে আলোর জন্য। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা দুলত ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো।
অযথা শরীরে যাতে পীড়ার উদ্রেক না হয়, তার জন্য গো-শকটের অভ্যন্তরে বেশ পুরু করে শুষ্ক-ধান্য-তৃণ অর্থাৎ খড়ের বিছানা পাতা ছিল। সে-খড় দিয়ে বলদজোড়ার যেমন করে আহারের সংস্থান হচ্ছিল, তেমনি আমাদেরও আরামের ব্যবস্থাপনা ছিল।
খড়ের বিছানায় শুয়ে বসে মা আর আমি ক্রমাগত, ক্রমান্বয়ে দেখে যাচ্ছিলাম―সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী ‘পালচাষী জনমানুষ’দের হাতে করা রাস্তার দুধারের ইক্ষু-অড়হরের খেত, বিরি-বাদাম, মুগ-চনার খেত।
কেউ কেউ খেতের বিরিকলাই ইত্যবসরে তুলে এনে খলায়-খামারে ডাঁই করে রেখেছে। আর কেউ কেউ, বিশেষ করে বধূরা, সেই স্তূপীকৃত দানাশস্যের গাদা ভেঙে গুচ্ছ গুচ্ছ নিয়ে মাটিতে আছড়ে পাছড়ে দানা ছড়াচ্ছে। তাদের গায়ে মাথায় ভুর্ ভুর্ করছে বিরিকলাইয়ের ভুষি!
রাঙা-ভাঙা রৌদ্র এসে পড়েছে খলাখামারে। চল্লা, ডুমুর, অর্জুন, পাকুড়ের ডালে, মগডালে ঝিল ঝিল করছে পীত বর্ণের আলো। তাই দেখে মা উদব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ‘সনাতন, বাবু রে! বেলা যে পড়ে এল! বেলাবেলি রাসটাঁড়ে পৌঁছাতে হবে যে! গাড়ি টুকচার হুঁকরে চালা!’
সনাতন মুর্মু তৎক্ষণাৎ তার বলদজোড়ার ল্যাজ মুচড়ে ‘হু-ট্ হুট্! অ বে হিঁ-ই-ই ন ব- হ!’ কী যেন বলে তাদের আদেশ করল। হাজার হোক গো-শকট তো। তবু গাড়ি হুঁকরে ছুটে চলল। আমরা একে একে পশ্চাতে ফেলে এলাম মহাপাল, পেটবিন্ধি, কুচলাদাঁড়ি, কুঁকড়াকুপী, যুগীডিহা গ্রামাদি সব।
অবশেষে পৌঁছানো গেল বেলিয়াবেড়া প্রহরাজ রাজবাড়ির রাসটাঁড়ে। ততক্ষণে রাস-টাঁড় জুড়ে চতুর্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ! কলের গান বাজছে, প্যাঁ পোঁ আওয়াজ করে বাজছে ব্যাঙ-বাজনা। এখনও টকিজ শুরুই হয়নি, হব হব। নাকি যন্ত্রচালিত টকিজের ডায়নামোটাই বিগড়ে গেছে! তবে আশার কথা, মেরামতির কাজ চলছে। এই ঠিক হলো বলে!
টিকিট কাটার ঝুরকা থেকে হরিদ্রাবর্ণের দুটো টিকিট কেটে আমরা মায়ে-পোয়ে টকি ঘরের পর্দার একেবারে সামনাসামনি অর্থাৎ পুরোভাগে মাটিতে আসন গেড়ে বসে থাকলাম। যাতে করে টকির টুকিটাকি সবকিছুই চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যায়। সামনে বসলে স্পষ্ট আর দূরে পিছনে বসলে অস্পষ্ট দেখা যাবে―গ্রাম্য লোকেদের, অর্থাৎ আমার মা-কাকিমাদের ধ্যানধারণা এইরকমই।
বেলিয়াবেড়া প্রহরাজ রাজবাড়ি। কি থেকে কী! কালাপাহাড়ের কলিঙ্গ আক্রমণের কালে জনৈক নিমাইচাঁদ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছিল উৎকল থেকে মল্লভূমে। দুস্থ নিমাইচাঁদ ঘুরতে ঘুরতে একদিন মল্লভূমের রাজা সংসার মল্লদেবের কাছে এসে হাজির!
সংসার মল্ল দয়াপরবশ হয়ে একদিন তাকে ডেকে এনে খেতে দিলেন। নিমাইচাঁদ রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে লাগল। রাজা বললেন, ‘আরে আরে করছো কী ? রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না খেয়ে, কোথাও অন্তত ছাতা মাথায় বসে বসে খাও!’ বলেই তাকে একটা ছাতা দিলেন।
নিমাইচাঁদ তখন কাতর ভাবে বলল, ‘এই ছাতাটা যে কোথাও, কোনও জায়গায় পুঁতে রাখব―সেই নিজস্ব জায়গাটুকুও তো আমার নেই।’ তার কথা বুঝতে পেরে রাজা অতঃপর নিজ গৃহেই তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। খাওয়া শেষে তাকে একটা ঘোড়া দিয়ে বললেন, ‘এই ঘোড়ায় চেপে এক প্রহরের মধ্যে তুমি যতটা স্থান ঘুরে আসতে পারবে, সেই ততটা ভূখণ্ডই তোমার নিজের অধিকারে থাকবে।’
সেই একপ্রহরের রাজা। এই তার রাজবাড়ি আর রাসটাঁড়। এত কথা মায়ের মুখ থেকেই শোনা। তবে রাজরাজড়াদের সেই সময়টাও তো আর নেই। যা হোক, বিলম্ব হলেও ‘টকিজ’ শুরু হলো। পালার নাম ‘বেহুলা লখিন্দর’। আহা! কী সুন্দর! কী সুন্দর! ছবি তো নয়, যেন সবকিছুই জীবন্ত!
ওই, ওই ছিল আমার ও মায়ের প্রথম দেখা ‘টকি’।
প্রথম প্রথম টকি তো ভালোই লাগছিল। দু চোখ ভরে দেখছিলাম সবকিছুই। মাঝেমাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম মাকেও। তার চোখও যে আঠার মতো সেঁটে আছে ছবির পর্দায়!
হঠাৎ আরম্ভ হলো উৎপাত! উৎপাত বলে উৎপাত, মহোৎপাত! কোথা থেকে যে পর্দায় এত সাপ এসে আছড়ে পড়ল! ‘দূরে চল বেহুলা তুমি না কর উৎপাত।’ সাপ! সাপ! কিলবিল করে ‘দন্তবিষো’ বিষধর সাপগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল!
আচমকা মা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিল, ‘বাবু রে! অ্যাই! অ্যাই!! ওই! ওই!! ওই তো আসছে হলহলিয়ে! এই তো একটা ওদিকে গেল! ওই তো একটা এদিকে এল―‘বাবু রে! চ, পালাই! চ, চ! আর এক মুহূর্তও এখানে নয়, এখানে নয়! কখন এসে হিস হিস করে দংশে দেবে দণ্ডবিষো!’ বলতে বলতে মা তো হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।
যতই বলি, ‘ও কিছু নয় মা। সত্যিকারের সাপ কী আর ? সবই তো ছবির সাপ। নকল, নকল।’ মায়ের মোটেও বিশ্বাস হলো না। সমানে ভয়ার্ত ও ভয়ানক চিৎকার করেই যাচ্ছিল। করেই যাচ্ছিল। তাই দেখে হলভর্তি লোকজন আমাদের উপর যারপরনাই বিরক্ত হচ্ছিল।
‘বেহুলা লখিন্দর’ টকি সবে শুরু হয়েছিল। সাঙ্গ হওয়া তো দূরঅস্ত্, গোড়ার দিকেই আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, ‘যাক বাবা! বাঁচা গেল!’
পরিবর্তে আমরা ‘ভোজরাজা ও ভাণুমতীর খেলা’ দেখলাম। সেও তো নানাবিধের গ্যাঁড়াকল! ‘ডিম্বের নৃত্য’ ‘বাক্সমধ্যে একটী নর্ত্তক্য প্রবেশ করাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটী রাজহংস বাহিরকরণ’ ‘মস্তকছেদন’―
এক ঘণ্টার মধ্যে তুলসীবৃক্ষ উৎপাদন ‘মৃত মৎস্যকে পুনর্জীবিত করিবার উপায়’ ‘ডিম্ব হইতে জীবিত পক্ষী বাহির করা’ ‘দর্শকদের পকেট হইতে ডিম্ব বাহির করা’―
‘শূন্যে শুইয়া থাকিবার কৌশল’ ‘দর্শকদের সামনে তাস উড়াইবার কৌশল’ ‘টাকার নৃত্য’ ‘দর্শকদের সামনে এক গ্লাস জল উড়াইয়া দিবার কৌশল’―
‘ভোজরাজা ও ভাণুমতীর খেলা’-ঘরের দরজায় একজন লোক জোকার সেজে হ্যান্ড বিল বিলি করছিল। তাতে এ সমস্তই লেখা ছিল।
মা তবু বলল, ‘আচ্ছা, দেখা যাক।’ আমরা এখানে গৈরিক বর্ণের টিকিট কেটে ‘ভোজরাজা ও ভাণুমতীর খেলা’-ঘরে প্রবেশ করলাম।
কিন্তু শুরু হতে না হতেই সেই এক বিপত্তি। ‘মস্তকছেদন’। ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে মা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘বাবু রে! ঘর চ! এসব কাটাছেঁড়া আর দেখতে পারছি না!’
মাকে ফের বুঝালাম, ‘এসব কী আর সত্যি মা! সবই তো ভোজবাজি, হাতের কারসাজি। না হলে হরতনের বিবিকে নিমেষমধ্যে রুহিতনের বিবি করে কীভাবে ? মা বুঝল না।’
এ পর্যন্ত তাও না হয় মানা গেল। কিন্তু গো-শকটের নিকটবর্তী হয়ে সনাতন মুর্মুকে তলব করে মা যখন নির্দেশ দিল, ‘সনা মনা’, বাবু রে! গাড়ির সব খড় এক্ষুনি ফেলে দে! এতগুলো সাপের ভিতর দু-একটা তো এখানেও আসতে পারে ? পারে না ?
ভাতুয়া সনাতন তক্ষুনি তার আদরের বলদজোড়ার জন্য আঁটি কতক খড় আলাদা করে রেখে দিয়ে বাকি সমস্ত খড়ই ‘গিরিহানী’র আদেশ মোতাবেক রাসটাঁড়েই ফেলে দিল।
তারপর থেকে খড়বিহীন বিছানায় শুয়ে বসে গো-শকটে প্রায় সারারাত্রি ধরে কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ ক্রোশ চড়াই-উৎরাইয়ের পথ পেরিয়ে আসা―সে কি কম কষ্টকর ? ছইয়ের টুঙিতে ঝুলন্ত হেরিকেনটা গল গল ধোঁয়া উগরে জ্বলছিল ত জ্বলছিল, দুলছিল তো দুলছিল।
খড়হীন খালি গাড়িতে এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছিল মা। অত বড় দুঃসহ রাতে দু-চোখের পাতা নিমেষের জন্যও এক করতে পারেনি মা। আমিও কখনও সনাতনের সঙ্গে ক-দণ্ড বকর বকর, মায়ের সঙ্গে মাঝেমাঝে এটা ওটা গল্প করে নিদ্রাহীন ও কষ্টকর একটা রাত কোনও ক্রমে কাটিয়ে যাচ্ছি―
গো-শকটের ছইয়ের ভিতরে কখনও কখনও একরাশ তারাসহ ‘মেঘপাতাল’ অর্থাৎ একফালি আকাশ ঢুকে আসছিল। তাই দেখে মা আমাকে তারা চেনাচ্ছিল―উত্তাল, মঘা, ফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা―
কোনটা ধ্রুবতারা, কোনটা কালপুরুষা, কোনটা দধিভারীয়া, কোনটা সাতভায়া, কোন দুটো তারাই বা রাবণের সিং-দুয়ারের তারা, কোনটা ‘ইপিল’ বা ভোর-পোহাতি তারা―
পরের দিন প্রভাতে গো-শকট যখন গ্রামে, আমাদের গৃহে উপনীত হলো, তখন গাড়ি থেকে অবতরণের ইচ্ছাটাই মরে গিয়েছিল আমার। শরীরময় পীড়া দিচ্ছিল। ওদিকে মায়ের তো ধূম জ্বর। গাড়ি থেকে নেমেই শয্যাশায়ী।
৭
বর্তমান গো-শকটটি প্রকৃতপ্রস্তাবে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন হলেও এক্ষণে তা যেন মৃদু-মন্থর গতিতে অর্থাৎ ঢিমেতালেই চলছে। আরোহীর প্রতি আকারে-ইঙ্গিতে একটা সন্দর্ভ : বাছা, যাচ্ছ যাও, সবকিছুই ধীরেসুস্থে অবলোকন করতে করতে যাও! আর তো তোমার ফিরে দেখার অবকাশ আসবে না!
আরোহণও তেমন কষ্টকর বা পীড়াদায়ক নয়। তুলনায় বেশ আরামপ্রদই মনে হয়। তবে প্রথমাবধি এখন পর্যন্ত সেই-‘একমেবা দ্বিতীয়ম নাস্তি’। গাড়িটি আগাগোড়াই চালকবিহীন। প্রকারান্তরে এখানে দামড়া বলীর্বদ্দটাই বোধকরি একই সঙ্গে বলদ ও চালক। সে-ই তো গাড়ি চড়াইস্তক আমাকে কেমন আড়চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে যাচ্ছে।
কী আর করি! আমিও দেখতে দেখতেই যাচ্ছি। নাহ্, জল থেকে উত্থাপিত হওয়ার পরে পরেই গ্রামটিকে প্রথম দর্শনে আমার নিজেরই গ্রাম বলে ভ্রম হচ্ছিল বটে। তবে তা তো তাৎক্ষণিক! পরক্ষণেই বোধ হলো―না, না। এ তো অন্য রকম, অন্য রকম।
কেমন যেন পুরাতন, পুরাতন। প্রত্নতাত্ত্বিক। চারধারটা ধোঁয়াশামাখা। রাস্তায় ঘাটে একটাও লোক দেখি না। যতই যাই হোক, তবু গ্রামটিকে একেবারে জনহীন, লোকশূন্য বোধ হলো না।
ওই, ওই তো বেলতলা, বাবলাতলা, তালতলা। বাটীর সমুখে উঠোনের একধারে দণ্ডায়মান সুবিশাল আমগাছ, জামগাছ। কেউ যদি নাই-ই থাকে, তবে এই সাতসকালে ঝাড়ু মেরে গাছের ‘তলা’গুলি ঝেঁটিয়ে সাফা করল কে ?
তদুপরি বৃক্ষচ্ছায়াতলে দড়ির খাটিয়া পাতা। এমনকি হাত-মুখ ধোওয়ার, বাইরে কৃষিকার্যে গিয়ে, কাষ্ঠাদি আহরণে বনে গিয়ে, ঘরে ফিরে এসে ধূলাধ্বস্ত পা ধোওয়ার জলও যে আঙিনায় মাটির কলসিতে প্রস্তুত!
খামারে বোধকরি রাতভর ‘পতলি’ চলেছে। ‘পতলি’ তার মানে একাধিক গরু জুতে, তার মধ্যে একটা বয়স্ক গরুকে ‘মেনা’ অর্থাৎ মোড়ল সাজিয়ে ধান মাড়ানো। একদা ঝেড়ে নেওয়া ‘ধানবিঁড়া’র যৎকিঞ্চিৎ থেকে যাওয়া ধানের দানাগুলিকে ফের ছাড়িয়ে নেওয়া আর কি!
ছাড়ানো ধান এখনও খামারেই পড়ে আছে। একটু বাদেই হয়তো বেলার দিকে গৃহস্থের ‘মাহিন্দর’ এসে ধান ও খড় আলাদা করে দেবে। আলাদা খড় গরুমোষের খাদ্য ও ঘর ছাওয়ার কাজে লাগবে।
সময় সময় কী সময়ান্তরে এমন তো হতেই পারে। ধরো, কোনও এক সুনসান মধ্যদিনে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে আমাদেরই গ্রামে প্রবেশ করলাম। কৃত্তিকা ভরণী মেঘা অশ্বিনী―‘মেঘপাতাল’-এ অর্থাৎ আকাশে তখন কোন নক্ষত্র থাকবে, কোন তিথি হবে ―বলতে পারি না।
‘কুলহি’ রাস্তার দু ধারে ঘর, গৃহস্থের ঘরবাড়ি। গ্রামের মাথায় একধারে বাঞ্ছানিধিদের ঘর, আরেকধারে রঁভাকাকাদের ঘর। দু ধারেই উঁকি মেরে দেখলাম―নাহ্! নাই কেউ।
জঙ্গল থেকে সদ্য তুলে আনা খুঁটিতে বাঁধা গোছা গোছা শালপাতা ছেড়ীছাগলগুলো লাফিয়ে খাচ্ছিল কালীকাকাদের বাইরের উঠোনে। ওই ছাগলগুলোই―কই, কোনও মানুষজনকে তো আলাদা করে দেখলাম না ? এখন, এখান থেকে গ্রামের হরিমন্দির পর্যন্ত একটানা একদিকে ভুট্টা খেত আরেকদিকে উপর্যুপরি মানুষের ঘর-গৃহস্থালি। এতদূর হেঁটে হেঁটে এলাম―কই, কোনও মানুষজনই দৃষ্টিগোচর হলো না, দুয়েকটা কুকুর-বেড়াল কী গরু-ছাগল ছাড়া ?
অতঃপর ডাইনে মোড় নিলেই আমাদের ‘বাখুল’। চীনের প্রাচীরের মতো মাটির তৈরি দেয়াল―চলছে তো চলছেই! প্রাচীর ভেদ করে এক্ষণে লোক দেখা যাবে কী করে ? আশ্চর্য, নাচদুয়ারে এসেও খলাখামারে বসমান কী দণ্ডায়মান একটা ‘জনমাম্মি’কেও দেখা গেল না ? এমনকি, আমাদের নবতিপর পিতামহী যিনি কীনা দড়ির খাটিয়ায় বসে বসে অষ্টপ্রহর কাঁসকুটের বাটি বা তাটিয়ায় এটা-ওটা খেতে থাকেন আর উড়ে এসে জুড়ে বসা কাক-চড়ুইয়ের সঙ্গে অনর্গল কথা বলেন―তিনিও নেই! নেই, নেই। খালি যা তার ফেলে যাওয়া বাটি বা তাটিয়ায় কয়েকটা কাক ইত্যবসরে সুযোগ বুঝে মুখ গুঁজে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে চলেছে!
রাস্তার ধারে চালায় বসে কাঠমিস্ত্রি প্রমথ ঠুকঠাক করে সারা দিনই তো হাল-লাঙল-জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা-আরা-ধুরি, ঢেঁকি, হাল-ডিজাইনের চেয়ার-টেবিল তৈরি করে―সেও যেন এই মুহূর্তে চুপ! বোধকরি কক্ষান্তরে গমন করেছে।
তার বিপরীত পার্শ্বে প্রায় রাস্তার উপরেই খেজুরপাতার পাটিয়া পেতে দশরথের বউবুড়ি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা মহুল, কচড়ার বীজদানা রৌদ্রে শুকোতে দেয়। পাছে পথচলতি গরুছাগল মুখ দিয়ে গসা গসা খেয়ে ফেলে―তাই কাছেই বসে থেকে ‘হেই-হেট- হুট’ আওয়াজ করে সর্বক্ষণ পাহারা দেয়।
আজ রাস্তায় পড়ে পড়ে মহুল-কচড়া পাটিয়ার উপর যথারীতি শুকোচ্ছে। পথচলতি ছেড়ীছাগলও তার উপর দিয়ে যাচ্ছে-আসছে। তবু পাহারাদার দশরথের বউবুড়ির পাত্তা নেই! কোথায় গেল রে ? কোথায় ?
দু ধারের গৃহ-গৃহস্থালি পর্যবেক্ষণ করতে করতে দৌড় দিলাম―দৌড়, দৌড়! পেরিয়ে এলাম শ্রীমন্ত-বসন্তদের ঘর। ‘দুশা’ বা দুঃশাসন, যাত্রাপালায় ‘কৃষ্ণ’ সাজা প্রফুল্ল, হারান-পরাণদের আবাসগৃহ।
বাড়ির সামনে ক্ষেতিবাড়িতে ঝিঙা-কাঁকুড়ের চাষ করেছে উল্লু-ভুল্লুরা। এখন নয়, মধ্যাহ্ন গত হয়ে আসবে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ গড়িয়ে সায়াহ্নের মুখে মুখে রদো বদো করে ঝিঙাফুল ফুটবে।
তখন ঝিঙা-কাঁকুড়ের মাচানতলে এসে জড়ো হবে উল্লু-ভুল্লুদের বউড়িঝিউড়িরা। অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে শিংয়ের কাঁকইয়ে অর্থাৎ চিরুনিতে চুল আঁচড়াবে। পায়ে আলতা, কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর পরবে। ছেঁড়াখোঁড়া, ঝরন্তি-পড়ন্তি চুল জড়ো করে তার উপর থুতু ছিটিয়ে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়।
এই মুহূর্তে তাদের একজনকেও দেখা গেল না। খুঁটিতে বাঁধা একটা যা ছেড়ীছাগল মুখে ফেনা তুলে জাবর কাটছে। একটা কাক বুঝি বা পোকার লোভে বসি-বসি করেও বসতে পারছে না ছাগলটার গায়ে।
গ্রামের শেষ প্রান্তেও এসে পৌঁছালাম। সত্যি সত্যিই ভারী আশ্চর্য বোধ হলো। ভোজবাজির মতো লোকগুলো উধাও হয়ে গেল কোথায় ? ম্যাজিসিয়ান যেমন হাতের কারসাজিতে একটা আস্ত ট্রেনগাড়িকে ‘ভ্যানিশ’ করে দেয়, সেই আর কি!
গাঁমুড়োয় ক-ঘর সাঁওতাল পরিবার। অবশ্য সচরাচর তারা গৃহে থাকে না। প্রায়সময় ‘নামাল’ খাটতে ‘পুবাল’ যায়। ‘পুবাল’ তার মানে পুবদেশ। যেখানে সংবৎসর বিভিন্ন সময়ে ধানচাষ হয়, ধান কাটা হয়। নামাল না গেলে গাঁয়েরই মাঠেঘাটে কাজেকামে থাকে। কাজ না থাকলে জমির আল তেড়ে খুঁড়ে ‘উন্দুর’ ধরে।
এহেন সুনসান মধ্যাহ্নে গৃহে তাদের না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু যা কতক ‘ঘুসুর’ বা শূওর বাহির উঠানে জল-কাদা-জমা গর্তে পেট চুবিয়ে শুয়ে আছে। মাঝেমাঝে সুখানুভূতির যেন আওয়াজ দিচ্ছে―‘ঘোঁৎ! ঘোঁৎ!’
গ্রাম ছেড়ে আরও কিছুটা হেঁটে মুগচনার খেত অতিক্রম করে নদী সমীপে এলাম। নদী, নদী। বর্ষার মরশুম ব্যতীত প্রায় বালুকাময় এই নদী যে শুধু আমাদের গ্রামেরই বা কেন, আরও কত শত, হাজার হাজার গ্রামের, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনজীবিকার আশ্রয় ও সাশ্রয়কারী―তা কহতব্য নয়।
নৌকাপরিবহণ, ঘাটপারাপার, নদীস্নান, নদীতে মৎস্যশিকার, নদীবালিতে স্বর্ণসন্ধান, বালিখাদান, ‘রিভার-লিফটিং’ বা কৃষিকার্যে জলসেচাদি, দিনেরাতে নিত্যকর্ম পূজাপদ্ধতির মতো আরও যে কত কাজে লাগে নদী! সেদিন সেই মুহূর্তে মনুষ্যপদবাচ্য কোনও কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়নি বটে। তবে কাবা-কুইরি উড়েঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরে মাথার উপরে ভ্রাম্যমাণ চিলেরা আকাশে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ‘কূপ’ খুঁড়ছিল।
একটা নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। আরেকটা আলকাতরা মাখাবার নিমিত্ত বালিতে উপুড় করা। তার তলদেশে, তখন পৃষ্ঠদেশ, একটা ‘ঢ্যাপচু’ অর্থাৎ ফিঙেপাখি বসে বসে ‘ভু-ই-চু-ঙ’ ‘ভু-ই-চু-ঙ’ আওয়াজ দিয়ে তার লম্বা ল্যাজটা দোলাচ্ছিল তো দোলাচ্ছিল।
এ সময় দূরদেশ থেকে নদীর আড়াআড়ি কদোপালের চর অতিক্রম করে, অথবা নদীর সমান্তরালে, পূর্ব ও পশ্চিম, দুই তীর ধরে এ-গাঁয়ের সে-গাঁয়ের কুটুম্ব কেউ না কেউ আসেই―আজ একজনও এল না ? একজনও না ? কেউই না ?
ফের গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তনে সমূহ দৃশ্যপট পাল্টে গেল। ‘পাটা’-য় ছপাৎ ছপাৎ করে কাপড় কাচার আওয়াজ পেলাম। ধোপাদের দুই ভাই―সুধীর শীট আর সুবোধ শীট―শ্রাদ্ধে, বিবাহে, তেল-খোলে, নত্যায় যজমানী কাপড় কাচছে সীতানালা খালের জলে দেখতে পেলাম।
কুমোরদের ‘মাটিখানা’-য় একটানা ‘খুপ’ ‘খুপ’ শব্দ। তার মানে খুলিগুহার মতো মাটি-খানায় ঢুকে কুমোররা ‘বারশি’-কোদালে হাঁড়ি-কলসি গড়ার জন্য মাটি কোপাচ্ছে ‘খুপ্’ ‘খুপ’!
দেখতেই পাচ্ছি তাদের বাড়ির বউড়িঝিউড়িরা বগলে ঠেকা-পাছিয়া নিয়ে বসে বসে আড্ডা মারছে মাটিখানার মুখটায়। আড্ডা কী আর, কখন একেকটা ঝুড়ি-পাছিয়া মাটিভরতি হবে আর সে-মাটি মাথায় করে নিয়ে ফেলবে খলায় খামারে।
বাছাবাছি করবে, রৌদ্রে শুকোতে দেবে। কিন্তু, এতক্ষণ তারা ছিল কোথায় ? যাওয়ার সময় একজনকেও তো চোখের দেখা দেখতে পেলাম না ?
শুধু কী তাদের ? এখন উত্তর প্রান্ত দিয়ে যখন ফের গ্রামে ঢুকছি, তখন ‘মেঘপাতাল’-এ বিজ বিজ করে অজস্র তারা ফোটার মতো মানুষজনেরও উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি।
কেউ ঝিঙা-কাঁকুড়ের মাচানতলে, কেউ বা মকাইয়ের ক্ষেতিবাড়িতে। কেউ কেউ খলা-খামারে খাটিয়ায় বসে খালি গজল্লা করছে। কেউ তো মুখে ফেনা তুলে আরেকজনকে সমানে বকে যাচ্ছে। আর যে বকুনি খাচ্ছে সে একটাও কথা না বলে গালাগাল হজম করে চলেছে।
গালাগালই বা শুধু হবে কেন ? একজন তো বেড়ার এধারে দাঁড়িয়ে ওধারের মানুষটিকে ‘নাম-মাধুরী’ নাকি ‘পদাবলী কীর্ত্তন’ শোনাচ্ছে! গ্রামের হরিমন্দিরে শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে এ-হেন পদ তো কতই শুনি―
‘হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
উঠ উঠ ধনি ও চাঁদবদনি
ঘুচাব মনের ব্যথা ॥
তবে দূরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈঠহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়ন চাই ॥’
আজ এতদিন বাদে এহেন গ্রাম কী গঞ্জে এসে সেই সেদিনের মতো আজও কোথাও অনুরূপ লোক দেখি না। ভূ-ভাগটি যেন ইতিহাসের পাতা থেকেই সংগৃহীত। যেন কবেকার এক ধূসর পাণ্ডুলিপি!
তবে কী গ্রামনামও হতে পারে তথৈবচ ? ‘বল্লিকন্দর’ ‘বাল্লহিটঠা’ ‘ব্যঘ্রতটী’ ‘খেদিরবল্লী’ ‘কন্তেড়দক’ ‘নাদভদক’ ‘কুক্কুট’ ‘বিলকীন্দক’― যদিও এখন পর্যন্ত গ্রামনামের কোনও ‘বোর্ড’ কোথাও ঝুলতে দেখিনি।
গ্রাম কি গঞ্জটি আড়ে-বহরে বেশ বিস্তৃততর। গো-শকট এতক্ষণ চলছে তো চলছেই। এখন না হয়― গজ, মাইল, ক্রোশ, মিটার, কিলোমিটার। তখন তো রাস্তা মাপা হত―যোজন, ভূপাটক, দ্রোণ, আঢক, উন্মান আর কাকে।
সে হিসেবে কত কী বলতে পারি না। তবে একটা ‘শুভঙ্করী আর্যা’ পড়েছিলাম―
‘ খেতে মাঠে রশি না পাই।
সাল ছেষে কাহন বলাই ॥
চারি কানে লয়ান হয়।
পঞ্চাশ উয়ানে আছি।
চারি আড়িতে ডোন হয়।
আঠাশ হাত দড়ি ॥’
যা হোক, হয়তো সওয়া মাইলটাক আসা হলো। গঞ্জটি একেবারে নিরবচ্ছিন্ন নহে। মাঝে মাঝে বাস্তুভিটা, মাঝে মধ্যে খিলক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষিভূমি।
৮
কিম্ আশ্চর্যম্! বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষানবিশ হয়েও কলাবিভাগের যাবতীয় বিষয়াদি, অ টু ত, আমি এই মুহূর্তে অবলীলায় রপ্ত করে চলেছি কীভাবে ? যদিচ ইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই শ্রীসুধাংশুশেখর ত্রিপাঠী মহাশয়ের নিকট ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা’ ‘ব্যাকরণ কৌমুদি’ বইদুটির পাঠ কায়ক্লেশে গ্রহণ করেছি। তবু, তবু―কোথাও যেন একটা বাস্তববর্জিত অলৌকিক কিত্তিকাণ্ড তলে তলে ঘটে চলেছে, তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। এই যে গো-শকট, চালকবিহীন, একটুও দিকবিভ্রম না করে সোজাই ছুটে চলেছে―মনে তো হয় গন্তব্যহীনভাবেই।
আমাদের মাঝুডুবকার জঙ্গলরাস্তা বরাবর কী কুমারডুবির জলার ‘লিক’ বরাবর ‘উধাস’ভাবে গাড়ি চললে এতক্ষণে সে গাড়ি কোথায় কোন অঝোরঝর ‘ঢঢ়হা’ কী ‘কাঁদর’-এ ঢুকে পড়ত। পড়তই।
যা হোক, ইতিহাস বলে―অদূরে কোথাও, সন্নিকটে, একদা ‘তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্তি’ বা ‘তমোলুক-তমোলিতি- তমোলিপ্তী’ এবং ‘দণ্ডভুক্তি-তণ্ডবুত্তি-দন্তভূমি’ তথা ‘দান্তন-দাঁতন’ ―নামের পৃথক দুটি বিখ্যাত জনপদ ছিল। ছিল কি, তার ভগ্নাবশেষ তো এখনও আছে।
সেখানে যেতে হলে কি অতীতে এই পথ পরিক্রমা করেই যেতে হতো ? চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কী য়ুয়ান্-চোয়াঙ এই পথ ধরেই কি গিয়েছিলেন তাম্রলিপ্তে ? দণ্ডভুক্তিতে ?
তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া যেতে অথবা অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্ত-দণ্ডভুক্তিতে আসতে―আর কোনও বিকল্প পথ কি ছিল না ?
‘বিবরণ’-এ আছে―গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পুবে, আরও পুবে, ফা-হিয়েন প্রায় আঠার যোজন পথ অতিক্রম করে নাকি এসেছিলেন চম্পানগরে। চম্পানগর তো এখনকার ভাগলপুর! হ্যাঁ, ভাগলপুরে গঙ্গাও আছে বটে।
তারপর সেখান থেকে আরও পঞ্চাশ যোজন পথ উজিয়ে ফা-হিয়েন এসে পৌঁছেছিলেন তাম্রলিপ্তে। সেখানে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দু বৎসরকাল কাটিয়েছেন।
পাটলিপুত্র বা বর্তমান পাটনানগরের সন্নিকটে গঙ্গা এখনও বহমান। সেই পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে ভাগলপুর। ভাগলপুর থেকে সুলতানগঞ্জ-সাহেবগঞ্জ হয়ে গঙ্গা এবার দক্ষিণ-পূর্বমুখী।
কিন্তু অপর পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ পাটলিপুত্র-বুদ্ধগয়া- রাজগৃহ-নালন্দা-অঙ্গ-চম্পা হয়ে পদার্পণ করেছিলেন ‘কজঙ্গল’-এ। কোথায়, কোন ভৌগোলিক অবস্থানে―এই তৎকালীন ‘কজঙ্গল’ ?
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভূ-আন্দোলন চলছে। তোল মাটি ঘোল্ হচ্ছে। পুরাতনভূমি ভেঙে নব্যভূমি গড়ে উঠছে। রাজমহল পাহাড়, সাঁওতালভূম-মানভূম-সিংহভূম―ধলভৃমের মালভূমি, এমনকি মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত ―এই পুরাতন বা পুরাভূমি।
উত্তর-রাঢ় অর্থাৎ বাঁকুড়া-বীরভূম এবং দক্ষিণ-রাঢ়, তার মানে রানিগঞ্জ-আসানসোল, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম- গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম, তাম্রলিপ্তি-দণ্ডভুক্তিও সেই পুরাভূমি। এর মধ্যেই কোথাও আছে ‘কজঙ্গল’ যা কীনা ‘জাঙ্গলময়, আঁজলা এবং অনুর্বর’। যার তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ!
অঙ্গের রাজধানী চম্পা, অধুনা ভাগলপুর থেকে গঙ্গা ও ভাগীরথী বেয়ে গঙ্গাবন্দর বা তাম্রলিপ্ত আসার জলপথ তো তখনও ছিল, এখনও আছে। শুধু কী জলপথ, স্থলপথে গো-শকটের লহর চলত―তার প্রমাণও তো আছে।
চম্পা থেকে পঞ্চাশ যোজন পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন এসেছিলেন তাম্রলিপ্তে, সে তো জলপথে, গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে। আর য়ুয়ান-চোয়াঙ এসেছিলেন নাকি স্থলপথে চম্পা হয়ে কজঙ্গলে। কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট, সমতট হয়ে তাম্রলিপ্তে। অনেকটা ঘুরপথে।
কিন্তু এহো বাহ্য আগে কহো আর। কোথায় থাকল কজঙ্গল, কোথায় বা দণ্ডভুক্তি ? হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেব ‘রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল’ ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন, যা কীনা অজলা জাঙ্গলময়। এই কি তবে ‘কজঙ্গল’ ? ‘দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকা’র রাজ্য ?
ইতিহাসবিদেরা এর সুষ্ঠু মীমাংসা দিতে পারেননি। তবে আমার মনে হয় বর্ধমানভুক্তি আর দণ্ডভুক্তির নিকটেই কোথাও ‘কজঙ্গল’ ছিল। চম্পা বা ভাগলপুর থেকে প্রকাণ্ড স্থলপথ এসে তো মিলিত হয়েছে বর্ধমানে সেই কবে থেকে! দণ্ডভুক্তি একসময় বর্ধমানভুক্তির মধ্যেও ছিল, ছিল তাম্রলিপ্তে-উৎকলেও।
য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে আছে―কজঙ্গলের উত্তর সীমা গঙ্গা থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। বর্ধমানভুক্তির অম্বিকা-কালনাতেও গঙ্গা তো ছলাৎছল! শুধু কী কালনা, কাটোয়া-পূর্বস্থলী-মন্তেশ্বরেও গঙ্গা বিরাজিত স্বমহিমায়।
সেই সার্থবাহ গো-শকটের লহর তোলা পথেই কি তবে বর্তমান গো-শকটও চলেছে! অনুমান বর্ধমানভুক্তি ও কজঙ্গলের কাছাকাছি কোথাও ছিল দণ্ডভুক্তি রাজ্য।
সপ্তম শতকের গোড়ায় তাম্রলিপ্তের পতনের পর নাকি দণ্ডভুক্তি রাজ্য ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল। রূপনারায়ণের দক্ষিণ সুবর্ণরেখার উত্তর ভূভাগ, উৎকলের বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ আর ছোটনাগপুরের কিয়দংশও তার অন্তর্গত ছিল। তাম্রলিপ্ত জনপদও তখন দণ্ডভুক্তি জনপদের নামেই পরিচিতি পেত।
সেই দণ্ডভুক্তি দেশ য়ুয়ান্-চোয়াঙের সময়কালে বোধকরি রাজা শশাঙ্কেরই অধীনে ছিল। এত বড় জনপদ, পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত সেখানে ‘দন্তবন মহা-বিহার’ও বর্তমান, তবু তার উল্লেখ য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে পাই না কেন!
য়ুয়ান্-চোয়াঙ তৎকালীন বঙ্গের চারটি জনপদে ভ্রমণ করেছেন ―‘পুন্-ন-ফ-টন্-ল’ (পুণ্ড্রবর্ধন), ‘সন্-মো-তট’ (সমতট), ‘তন্-মো-লিহ্-তি’ (তাম্রলিপ্ত), ‘ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন’ (কর্ণসুবর্ণ)। উঁহু, আরও একটি―‘ক-চু-ওয়েন্-কি-লো’ (কজঙ্গল)!
তবে কি কজঙ্গলই বর্ধমানভুক্তি যুক্ত দণ্ডভুক্তি ? অথবা বিযুক্ত দণ্ডভুক্তি ? ‘কজঙ্গল’ প্রসঙ্গে য়ুয়ান্-চোয়াঙ নিজে বলেছেন―‘রাজ্যটি পররাষ্ট্রের অধীন, রাজধানীতে লোক ছিল না এবং লোকেরা গ্রামে এবং নগরেই বাস করত।’
আবার কজঙ্গলকে ‘রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল’ ধরলে সে তো উত্তর রাঢ় ―বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম, অজয়নদের দেশ! কেননা, ‘রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল’-এর কথা যিনি শুনিয়েছেন, তিনি তো বীরভূমের সিদ্বলগ্রামের ভূমিপুত্র ‘পণ্ডিত-মন্ত্রী ভট্টভবদেব’। উৎকলেরই মহামন্ত্রী। আর বর্ধমানভুক্তি, তাম্রলিপ্তি, দণ্ডভুক্তি তো একদা উৎকলেরই অধীন। ‘অজলা ঊষর জাঙ্গলময়’ বলে ভট্টভবদেব নিজেরই গ্রামে একটা মস্ত দিঘি খুঁড়িয়েছিলেন।
উত্তর-রাঢ় সমগ্র একদা বর্ধমানভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদান অন্য কথা বলছে, বিহারের পূর্বপ্রান্তস্থ রাজমহলের নিকটবর্তী ‘কজঙ্গল’। ছয়শত একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধন এই কজঙ্গল থেকেই নাকি তাঁর বিজয়াভিযান চালিয়েছিলেন উড়িষ্যাতে।
এসব নিয়ে অনেক গল্পও আছে। হর্ষবর্ধন উড়িষ্যার কোঙ্গোদ, অধুনা গঞ্জাম, জয় করে দু বছর পরে কজঙ্গলে পৌঁছে য়ুয়ান্-চোয়াঙের কামরূপ যাবার কথা শুনে ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়েছিলেন।
তাঁকে নাকি তার সঙ্গেই বাস করতে বলেছিলেন হর্ষবর্ধন। য়ুয়ান্-চোয়াঙ শোনেননি। কামরূপ অধিপতি ভাস্করবর্মার কাছে অনুরোধ গেল তাঁকে তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠাতে।
উত্তরে ভাস্করবর্মা য়ুয়ান্-চোয়াঙকে ফেরত তো দিলেনই না, তদুপরি দূত মারফৎ বলে পাঠালেন, ‘তার মস্তক দিতে পারেন, কিন্তু য়ুয়ান্-চোয়াঙকে ফেরত দিতে পারবেন না।’
অতঃপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হর্ষবর্ধন আদেশ পাঠালেন ভাস্করবর্মার কাছে, ‘বেশ আপনার মুণ্ডুই পাঠিয়ে দিন। এই দূত সেটা যেন অবিলম্বে এখানে নিয়ে আসতে পারে।’
অগত্যা অবস্থা বেগতিক দেখে ভাস্করবর্মা স্বয়ং কুড়ি হাজার হস্তী ও তিরিশ হাজার নৌকা নিয়ে গঙ্গাপথে য়ুয়ান্-চোয়াঙকে সঙ্গে করে কজঙ্গলে এসেছিলেন। তখন ভাস্করবর্মা হর্ষের অনুগত-মিত্রই ছিলেন। ক মাস দু জনে কজঙ্গলে কাটিয়েছিলেনও বেশ!
দিব্যাবদান যদি মানতেই হয় তবে তো কজঙ্গল রাজমহল পাহাড়ের নিকটেই। গঙ্গার পশ্চিমে। শুধু কজঙ্গল কেন, রাঢ়, কঙ্কগ্রাম, কর্বট, সুহ্ম, বর্ধমান-ভুক্তি, তাম্রলিপ্তি, দণ্ডভুক্তিও তো গঙ্গার পশ্চিমে!
গঙ্গা বেয়ে রাজমহলের তেলিগড়ি-সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্তের ভিতর দিয়েই তো গঙ্গার পশ্চিমে আসা। আসা কজঙ্গলে, বর্ধমানভুক্তি-দণ্ডভুক্তিতে, আসা তাম্রলিপ্তিতে!
য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে কজঙ্গল আলবাৎ আছে। কিন্তু বর্ধমানভুক্তি-দণ্ডভুক্তির কোনও উল্লেখ দেখি না। আমার তো মনে হয় বর্ধমানভুক্তি-দণ্ডভুক্তিই ‘কজঙ্গল’। সেখান থেকে রাজমহল আর কতটুকুই বা দূর! ফারাক্কা থেকে হাত বাড়ালেই তো রাজমহল!
ইতিহাসে যতই তর্ক-বিতর্ক থাক কজঙ্গল নিয়ে, আমার আগ্রহ যতটা না কজঙ্গল, তার থেকেও বেশি আমাদের ঘরের ধারে সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত দণ্ডভুক্তি-দন্তভূমি-দান্তন বা দাঁতন নিয়ে।
নৌকার নাউড়িয়া বড়োডাঙার হংসী বধুক একবার তার ‘নৌকাবিলাস’ যাত্রায় সত্যি সত্যিই আমাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল দাঁতনে। পুরাকালের সে-সমৃদ্ধি কি আর আছে!
কাতা ধারে ধারে কতক বাঁশঝাড়, চিমনির ধোঁয়া উদ্রেককারী ইটভাটা, ধীবরদের গৃহসংলগ্ন বাঁশের বেড়ার গায়ে রৌদ্রে মেলে দেওয়া মাছধরার ‘বেড়-জাল’ ‘বেঁহুদি জাল’ ‘সারানি জাল’।
জালুয়া কৈবর্তের ন্যাঙটো-পোঁদো ছেলে তাতা বালির উপর সেদিন এঁকে বেঁকে হিসু করতে করতে এসে নদীজলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেখাদেখি তার পিছনে আরও ‘কৎগা’ কৎগা ন্যাঙটো-পোঁদো! তাই নিয়ে ‘নৌকাবিলাস’-এর নৌকায় বসে আমাতে-হংসীতে জব্বর হাসির গপ্পো হয়েছিল।
কী-ই ছিল আর কী হয়েছে! দণ্ডভুক্তি তো একসময়, বোধকরি সপ্তম শতকে, এতটাই সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাম্রলিপ্তি জনপদও তার আওতায় থেকে তার নামেই পরিচিতি পেত।
হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের আমলেও তার রমরমা বেশি বৈ কম ছিল না। সপ্তম শতকেই গৌড়রাজ তথা কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের অধীন ছিল দণ্ডভুক্তি। শশাঙ্কের আমলের, আনুমানিক ছ শ খ্রি. থেকে ছ শ পঁচিশ খ্রি., পাওয়া তাম্রশাসনগুলিতে শশাঙ্কের নাম, ‘মহাপ্রতিহার’ শুভকীর্তি, ‘সামন্ত’ সোমদত্তের নাম, এমনকি তার কার্যালয় বা অধিকরণগুলোর নামও পাওয়া যাচ্ছে।
‘দাঁতন’ নামের মূলে দুটি কিংবদন্তি আছে। তবে তা ইতিহাসও বটে। ‘দাঠাবংশ’ বৌদ্ধগ্রন্থে ‘ক্ষেম’ নামের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা থেকে একটি দন্ত কুড়িয়ে পান, যা কিনা বুদ্ধের দন্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।
সেই দন্ত তিনি কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে দেন। সমাদরে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করেন ব্রহ্মদত্ত। স্থানটির সেই হেতু নামকরণ করা হয় ‘দন্তপুর’।
দন্তপুর যে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মস্থান রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে তো ইতিহাস! দেখা যাচ্ছে, ‘কার্তাকৃতিক- কুমারামাত্যরাজানক’ বিজয়বর্মা দক্ষিণ-মেদিনীপুর অঞ্চলে অবস্থিত দণ্ডভুক্তির ‘উপরিক’ ছিলেন, তখন ‘আর্য- অবলোকিতেশ্বরাধ্যাসিত বোধিপদ্রক-মহাপ্রহারের বিহার’ নির্মাণের জন্য মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে দান হিসেবে ‘শ্বেতবালিকাগ্রাম’টি কিনে নেওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছেন মহাসামন্ত মহারাজ অচ্যুত। আর, শ্বেতবালিকা গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ‘শ্বেতবালিকাবীথি’র অন্তর্গত।
এ কথা গোপচন্দ্রের ফরিদপুর শাসন থেকে জানা যাচ্ছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন বাঙলায় তখন গোপচন্দ্র। তাঁর অধীন দণ্ডভুক্তিও। সময়টা পাঁচ শো ঊনসত্তর। তারপরই তো শশাঙ্ক!
যা হোক, সেই ব্রহ্মদত্ত বংশের নৃপতি শিবগুহ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভক্ত। পরে তিনি বৌদ্ধ হন। তাতে রাজ্যের ব্রাহ্মণ্যেরা রুষ্ট হয়ে পাটলিপুত্ররাজের শরণাপন্ন হলেন। পাটলিপুত্ররাজ বুদ্ধদন্তসহ শিবগুহকে বন্দি করে নিয়ে এলেন পাটলিপুত্রে।
কিন্তু, অতঃপর রাজ্যে দৈবের বশে অঘটনের পর অঘটন! ভীতসন্ত্রস্ত পাটলিপুত্ররাজ বুদ্ধদন্তসহ শিবগুহকে ফের ফেরত পাঠালেন দন্তপুরে। পরবর্তী সময়ে, পাটলিপুত্রাধিপতির মৃত্যুর পরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জনৈক রাজসেনাপতি শিবগুহকে হত্যা করেন।
তখন দন্তপুরের রাজকুমারী হেমবালা এবং রাজমাতা উজ্জয়িনী ছদ্মবেশে বুদ্ধদন্ত নিয়ে তাম্রলিপ্তের পথে সিংহলে পালিয়ে যান। সিংহলরাজ মেঘবাহন মন্দির নির্মাণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে দন্তটির প্রতিষ্ঠা করেন।
সিংহলে আজও আছে ‘দেবানামপ্রিয়’ তিস্য নির্মিত সেই দন্তমন্দির। ফা-হিয়েন নিজে সে-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।
তবে তর্ক আছে পণ্ডিতমহলে। দাঁতনই কী ‘দন্তপুর’ ? রোমক পণ্ডিত প্লিনি, কানিংহামের মতে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রীই দন্তপুর নগর। ফার্গুসনের মতে আবার পুরীই নাকি দন্তপুর।
আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর মত হলো―দাঁতনই দন্তপুর। কেননা, তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে করিঙ্গপত্তন রাজমহেন্দ্রী আর দাঁতনের দূরত্ব বিবেচনা করলে দাঁতনই ধর্তব্য।
পুরী কিংবা রাজমহেন্দ্রী, যা-ই হোক, পুরীবন্দর দিয়েই দন্তটি প্রেরিত হওয়ার কথা। তা নয়, ‘দাঠাবংশ’-এ পরিষ্কার কথিত আছে―তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়েছিল।
আবারও বলা হয়, ওড়িশা যাবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে দাঁতনকাঠিতে দাঁত মেজেছিলেন বলেই স্থাননাম ‘দাঁতন’। সে হতেই পারে, সেও তো ইতিহাস। তবে এ তো এই সেদিন পঞ্চদশ শতকের কথা। আর দন্তপুর তো যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও আগে!
যেভাবেই হিসাব করা যাক না কেন, দন্তপুর-দণ্ডভুক্তি-দাঁতন যে বহু পুরাতন স্থান―সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী। ফা-হিয়েন য়ুয়ান্-চোয়াঙের আমলেও সেখানে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে দান করার নিমিত্ত শ্বেতবালিকা গ্রামটি ক্রয় করাই তার যথোপযুক্ত প্রমাণ।
চালকবিহীন বর্তমানের গো-শকটটি তবে কি সেই সার্থবাহ গো-শকটের চিরাচরিত পথেই পরিভ্রমণে চলেছে ? হয়তো পথিমধ্যে কোথাও দেখা মিললেও মিলতে পারে ‘বৃহৎছত্তিবন্না’ ‘ক্ষুদ্র ছত্তিবন্না’ ‘বল্লিকন্দর’ ‘কুম্ভারপদ্রক’ ‘বাল্লাহিটঠা’ ‘সিদ্ধল’ ‘শ্বেতবালিকা’ ‘দণ্ডভুক্তি’ গ্রাম ও নগরাদি।
এতদ্ অঞ্চল ব্যতীত ধ-আসন-আঁটারি-চুরচু-ডকা-ভাদু-ইক্ষু- সর্ষপ-মধুকঃ বা মহুয়া-গুবাক-সহকার-পনস-পান-নাড়িয়েল বৃক্ষ, তদুপরি লবণ ও মৎস্য―আর কোথায় পাওয়া যাবে!
সমুদ্রের লবণাক্ত জল, উত্তাল ঢেউয়ের আন্দোলনে তাড়িত হয়ে খাঁড়িতে, খালে-বিলে-জমিনে জমা জল জ্বাল দিয়ে এমন লবণই বা তৈরি করবে কে ?
নদীপথের দুই ধারে পথিক যত পথই পরিক্রমা করবে, এদিক-ওদিক দুই দিকে দৃষ্টি ফেলবে, ততই তার চোখে পড়বে পল্লীতে পল্লীতে গৃহস্থের ঘরের চালে বেড়ার গায়ে উঠানে দুই খুঁটিতে রজ্জুযুক্ত হয়ে শুষ্ক হচ্ছে জালুয়াদের মাছ ধরার জাল!
নাকে আসবেই আসবে শুকা বা শুঁটকিমাছের গন্ধ। এত, এ-ত্ত পুঁটিমাছ রাতভোর জালে পড়েছে, কত আর খাবে কত আর সাই-পড়শিদের মধ্যে দানছত্র করবে, কত আর বেচবে, অবশিষ্টাংশ তো উনুনের মাথায় খইচালায় শুকাবে!
মাছের আঁশযুক্ত মেলে দেওয়া ‘বেড়াজাল’ ‘বেঁহুদি জাল’ ‘সারানি জাল’ ‘জগৎবেড় জাল’ ‘ভাসানি জাল’ ‘ঝুলিজাল’ ‘চার-গোড়িয়া-জাল’ ‘মাথা-ফাবড়ি-জাল’-এর আঁশটে গন্ধ, তদুপরি শুকামাছের ভুর ভুর গন্ধ―‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!’
সেই দেশের ভিতর দিয়েই কি চলেছে বর্তমান চালকবিহীন গো-শকট ? ওই ওই তো, একটা সুবিশাল পুষ্করিণী যার জলের ধারে কলমি-শুশনি ‘লহ লহ’ করছে। ডাহুক, জলপিপি উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ওই, ওই তো একটা কাদাখোঁচা একবার এদিক একবার ওদিক, একবার উঁচু একবার নিচু, ঢেউখেলানো ভাবে উড়তে উড়তে ‘চিক-চিক চিকা-চিকা-চিকা’ রবে মুহুর্মুহু ডেকে চলেছে।
গঞ্জটির মাঝামাঝি একটা ঈষৎ প্রশস্ত জোটিকা বা খাল বয়ে গিয়েছে পশ্চিম থেকে পুবে, পুবে পুবে, বুঝিবা বড় নদীর সমান্তরালে। খালের ধারে ধারে বিরাজিত একটি-দুটি পর্কটি বা পাকুড়গাছ, পিপ্পলী গাছ। বিশেষত ডুমুরগাছ।
উপস্থিত জোটিকার ঘাটে বাঁধা জালুয়াদের মাছ ধরার জেলেডিঙি ‘পাটিয়া’। যেন এইমাত্র জাল টেনে ঘরে ফিরল মাঝি। পায়ের ফেলে যাওয়া চাপে পাটিয়ার পাছা এখনও নড়ছে! কোত্থেকে একটা কাক এসে ঈষৎ দুলতে লাগল।
ঘরে ফেরার সময় মৎস্যানন্দে জালুয়া কি কোনও গীত গাইতে গাইতে আসছিল ? এহেন গীত―
‘হেদে হে নাগর চতুর-শেখর
সবারে করিবে পার।
যাহা চাহ দিব ও-পার হইলে
তোমার শুধিব ধার।।
মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী
যে হয় উচিত দিয়ে।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাব ত ও-পার হয়ে ॥’
না না, চতুর্থ-সপ্তম শতকে যখন ফা-হিয়েন য়ুয়ান্-চোয়াঙ এসেছিলেন এখানে, এতদ্ অঞ্চলে তখন মাঝি মাল্লারা এ ভাষা পাবে কী করে ? এ তো চণ্ডীদাসের আমলের কথা, এই সেদিনকার! তখন তবে কী ভাষায় কথা বলত এখানকার মানুষ ? এইরকম কী―
‘তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্ন মনে পার হয়িব ছোট নাঅ খানী ॥
একেঁ একেঁ পার যাইব যাইব মথুরা।
সহ্মাই চড়িলে নাঅ না সহিব ভরা ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে ।
সহ্মা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥’
উঁহু, তাও না। এ তো বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর পদ। তবে আমাদের পাশের গ্রামের ‘হাটুয়া’ জনমানুষরা অনেকটা এই ভাষাতেই কথা বলে। যেমন ‘নৌকাবিলাস’-এর গীতে ―
‘সোবু সখীকু পারঅ করাইতে
নিমু আনা আনা।
শ্রীরাধাকু পারঅ করাইতে
নিমু কানর সোনা ॥ আ গো’
৯
অবশেষে গো-শকটটি আপনা-আপনিই এসে দাঁড়াল একটি পোড়ো মন্দিরের সন্নিকটে। গঞ্জের সীমানা-চৌহদ্দি শেষ হতে তখনও বাকি বোধকরি।
পোড়ো মন্দিরই তো বটে! নাকি আবাসগৃহ ? না না, ওই তো মন্দিরের একাধিক চূড়া দৃশ্যমান। সাত, সতেরো না পঁচিশ চূড়া ? এমনটি কোথায় যেন দেখেছি!
পরিত্যক্ত রাজবাড়ির কোনও রাসমঞ্চ কী ? ভিতরে ঢুকলেই দেখা মিলবে একাধিক কক্ষযুক্ত অন্দরমহলের ? নাচমহল ? ঘুঙুরমহল ? খিলান ?
রাসমঞ্চটি কী সাত, সতেরো না পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট ? কতক তো ভেঙে হেলে পড়েছে! আচমকা ভদভদিয়ে একঝাঁক পায়রা বেরিয়ে এল। ডানা ফেটিয়ে উড়ে চলল আকাশে। পায়রা তো নয়, যেন পারাবত। ঈষৎ স্থূলকায়া।
কত ঝুরকা, ঝোরোকা! ভালো কথায় গবাক্ষ। কত ‘পিঁড়া’, কত
বারান্দা! ভালো কথায় অলিন্দ। কত আঁকাজোকা, টেরাকোটা কত! তবে অধিকাংশই ভগ্নপ্রায়। কিছু লেখাজোকাও খোদিত আছে দেখছি। যেমনটা সচরাচর দেখি মন্দিরগাত্রে, জমিদারবাটীতে, হরিমন্দিরে, তুলসীচৌরায়।
এই যেমন―
‘ শ্রীশ্রী’ পঃ শ্রীমহে
দধিপাব শ চন্দ্র রায়
ন চন্দ্র জী সন ১২৯৭
উ স্বহায় সাল সাঙ্গ
সকাব্দ ১৮১২’
না না, বাংলা কেন হবে, এ যেন অন্য হরফ, অন্যরকম। দেবনাগরী কী ?
‘আবাসবাটী যৎউত্তরশ্যাম
গোপশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্বিভাগে।
কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ
সা মেদিনীনাম পুরী শুভেয়ম ॥’
উঁহু, দেবনাগরী তো এ নয়। রোহিণী হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাই শ্রীযুক্ত বাবু হিমাংশুশেখর ত্রিপাঠীর নিকট ‘নরঃ নরৌঃ নরাঃ’ মুখস্ত ক’রে যৎকিঞ্চিৎ হলেও সংস্কৃতের পাঠ তো নিয়েইছি! তবে কী ‘ব্রাহ্মীলিপি’ ?
নাকি মৌর্যযুগে ব্রাহ্মীলিপি সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। অশোকের অনুশাসন ব্রাহ্মলিপিতেই লেখা হতো। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পরে তা বিবর্তিত হয় প্রদেশ থেকে প্রদেশে। হয়তো ব্রাহ্মীও নয়, মাগধী অপভ্রংশ। বাংলা ভাষা ও লিপির প্রপিতামহেরা ?
ধরেই নিচ্ছি পোড়ো মন্দির, রাজগৃহ কী সামন্তবাটীটি গুপ্তোত্তর পালযুগেই নির্মিত। ততদিনে ‘তন্-মো-লিহ্-তি’ বা তাম্রলিপ্তির দিন শেষ। কিন্তু ‘তণ্ডবুত্তি’ বা দণ্ডভুক্তির গৌরবসূর্য মধ্যাহ্ন গগনে জ্বলজ্বল করছে! তাম্রলিপ্তি তো তাম্রলিপ্তি, উৎকল, এমনকি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলও তার অধিগত।
এহেন সময়কালে দণ্ডভুক্তি বা দাঁতনের সন্নিকটে এই গঞ্জে যেখানে হালিক-জালিক কৈবর্তরা, পণ্ডাসুর বা পঁড়াসুর তথা মহিষাসুরের পূজাকারী ইক্ষুচাষিরা, ‘ক্ষেত্রকরান্’ ‘কর্ষকান্’ ‘কৃষকান্’ ইত্যাদি গোত্রধারী মানুষেরা বসবাস করত, সেখানে এই গৃহও যে নির্মিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!
তাছাড়া ভূমি দান-বিক্রয়, গৃহনির্মাণার্থে রাজা-রাজড়া, উপরিক, প্রতি-হার-মহাপ্রতিহাররা এই বলে বিজ্ঞপ্তিও যে জারি করেছেন―
‘এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক―
রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি―
ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপালিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌস্―
সাধসাধনিক-দূত-খোল-গমাগমিকা-ভিত্বরমান-হস্ত্যশ্ব―
গোমহিষাজীবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক―
শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদায়ুক্তক-বিনিয়ুক্তকাদি-রাজপাদ―
পোজীবি-নোহন্যাংশ্চা-কীর্তিতান-চাটভট-জাতীয়ান্―
যথাকালধ্যাসিনো-জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর―
দাশগ্রামিকাদি-বিষয়-ব্যবহারিণঃ-সকরাণান্-প্রতিবাসিনঃ―
ক্ষেত্রকরাংশ্চ-ব্রাহ্মণ-মাননাপৃর্বকং-যথার্হং-মানয়তি
বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ ॥’
গৃহগাত্রে খোদিত অক্ষর-বৃত্তান্ত তবে কি পালি ভাষায় লিখিত ? হতেও পারে। হয়তো ভগ্নপ্রায় পোড়োবাড়িটা কোনও বৌদ্ধ সংঘারামই বটে। থ্রি-ফোরের ইতিহাস পড়াইস্তক জেনে আসছি চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, য়ুয়ান্-চোয়াঙের কথা।
তাঁরা কেউ কেউ তাম্রলিপ্তি-দণ্ডভুক্তিতে একাধিক বৎসরকাল বসবাসও করেছিলেন। দশটা-বাইশটা বৌদ্ধ সংঘারামও দেখেছিলেন। সেখানে শিক্ষার্থে বসবাসকারী দুশো-সাতশো বৌদ্ধভিক্ষুকেও চাক্ষুষ করেছিলেন। এই পোড়ো গৃহ সেরকম কোনও একটা সংঘারামও হতে পারে।
সেনযুগে যেমন তেমন, পালযুগে বৌদ্ধধর্মের রমরমা খুব কম ছিল না। ধর্মপাল, দ্বিতীয় গোপাল, মহীপাল, নয়পাল, রামপালের মতো পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি রচিত হয়েছিল।
মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর, পণ্ডিত শীলভদ্রও তো এই সময়কালেই বিদ্যমান ছিলেন! তার পরে পরেই ‘চর্যাগীতি’ বা ‘চর্যাগান’। লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কুক্কুরী-পাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ। তাঁদেরই রচিত―
‘কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠ কাল ।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান ॥’
ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পোড়ো সংঘারামগাত্রে নিশ্চয় ‘ত্রিশরণ’ মন্ত্রই খোদিত আছে―
‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’
‘ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি’
‘সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি’
যা হোক, এক্কাগাড়ি অর্থাৎ এক বলদের গো-শকট এহেন পোড়ো বাড়ির সন্নিকটে আমাকে নামিয়ে দিয়ে অসমাপ্ত গঞ্জের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলো। তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে!
বেলা বুঝি দ্বিপ্রহর। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এতক্ষণে কাতর বোধ হচ্ছে। সেই কখন খেয়েছি, মায়ের হাতের রান্না! এত বড় গঞ্জ, আড়ে-বহরে যে কত! তাও একটা লোক দেখি না।
ভগ্নপ্রায় সংঘারামের মতো গোটা গ্রামটাও মনুষ্যবিবর্জিত, পোড়ো নাকি ? তা তো মনে হয় না। কিয়ৎক্ষণ আগেও নধর গতর কতক তো উড়ে উঠল আকাশে, ওই তো এখনও সঞ্চরমাণ!
উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কাক-চিল, সামুদ্রিক পাখি। ঘুরপাক খাচ্ছিল চড়ৈ-চটি। নলখাগড়ার দঁকে ঘাপটি মেরে বসেছিল ‘মাছরাঁকা’। তার মানে মাছরাঙা। সেও তো দেখেছি একটু আগে।
তবে ? তার বেলা ?
১০
এতক্ষণে মনে পড়ল একটা অদৃশ্য শিকল, যাকে বলে ঝিঁজরি, আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বেঁধে অদৃশ্য লোকগুলোই আমাকে টেনে এনেছে সুবর্ণরেখা নদীর মশানির দহের জলতলে, জলের গভীরে।
জলতল ছেড়ে তারপরে এই ডাঙায়, ডাঙা-ডুঙোড় ভূ-ভাগে। কতকটা চেনা, কতকটা অচেনা ভূখণ্ডে। পুরুষের যেমন পূর্বপুরুষ, তেমনি এ ভূ-ভাগও যেন আমাদের রামেশ্বর ডাঙা, পাড়িয়ার বিল, মহিষাসুর দঁক, গোঠটাঁড়ের মাঠেরই পূর্বপুরুষ।
সামান্য হৃষ্টপুষ্ট, চৌদ্দ পুরুষকে পরপর দাঁড় করালেই তফাৎটা যেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। কাকগুলো যেন বড় বেশি কালো, পারাবতগুলোও ঈষৎ স্থূলকায়া, চড়ৈ-চটিও বেশ পুচ্ছওয়ালা।
গো-শকটের এক্কায় থাকাকালীন পায়ের ঝিঁজরির উপস্থিতি ততটা টেরই পাইনি। এখন টান পড়ল। সেই অদৃশ্য হাত যেন আবার টানতে শুরু করেছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই পোড়োবাড়িটার দিকে।
মশানির দহের জলের ঝাঁজি বা শ্যাওলা এখনও যেন লটকে আছে পায়ে! মা-কাকিমারা, দাদু-ঠাকুমারা নিছকই ভয় দেখানোর জন্য হয়তো বলেছিলেন, ‘যাস না, ওরে যাস না, মশানির দহের জলে অত ঝাঁপাঝাঁপি করিস না রে! একবার যদি জলের ঝাঁজি পায়ে আটকায়, নিশুতি রাতে লোহার ঝিঁজরি হয়ে তোকে টেনে নিয়ে যাবে একেবারে জলের তলায়।’
আর তাই কীনা, হবি তো হ, সত্যি হয়ে গেল আমার বেলায়! ঝিঁজরি বেঁধে কেউ না কেউ টানছে, স্পষ্টতই টের পাচ্ছি। অথচ ধারেকাছে কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।
শুধুই পোড়োবাড়িটা। নাকি ওদন্তপুরী-নালন্দার মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন মহাবিহার মহাগ্রন্থাগার মহাসঙ্ঘারাম ?
বলা হয়, নাকি বক্তিয়ার খলজী সব ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন শশাঙ্ক। তবে য়ুয়ান্-চোয়াঙ বলেছিলেন, বৌদ্ধবৈরী শশাঙ্ক বোধিদ্রুম কর্তন করেছেন। নালন্দা ধ্বংস করেননি। কেননা তারপরেও নালন্দা অটুট ছিল।
আসলে এর মূলে হয়তো সেই মহাযান ও হীনযানদের দ্বন্দ্ব। রাঢ় তথা আমাদের এতদ্ অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ আজীবক, শ্রমণরা ধর্ম প্রচারের হেতু একদা ঘুরে বেড়াতেন। তবে তাঁদের প্রচারিত ধর্মে এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার তেমন কিছু হেরফের ঘটেনি। বরং উল্টোটাই হয়েছে।
যার ফলে তাঁদের স্বীয় ধর্মে এসেছিল শৈথিল্য। মহাযান তো মহাযান, হীনযানদের মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র জাদুবিদ্যা ডাকিনীবিদ্যা ঝাড়ফুঁক পিশাচসাধনা, হেন-তেন আরও অনেক কিছু ঢুকে পড়েছিল। নাথ, যুগীদের আবির্ভাব ঘটল। সৃষ্টি হলো মন্ত্রযানী বজ্রযানী কালচক্রযানীদের।
বলা বাহুল্য, সুদূর উড়িষ্যা থেকে তাম্রলিপ্ত অবধি বিস্তৃত বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামে কালচক্রযানীদেরই আধিক্য। কালচক্রযানী সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে মীননাথ, শবরীপাদ তো এতদ্ অঞ্চলেরই মানুষ। কেউ ছিলেন ধীবর, কেউ বা শবর।
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কাঁথি অঞ্চলে এহেন কাপালিকদেরই দর্শন পেয়েছিলেন। তাঁদেরই জনৈক কাপালিক পরোপকারী নবকুমারকে, যিনি কীনা পরের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁকে বধার্থে অপহরণ করেছিলেন।
কোন ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসছি ‘অঁড়গা-ধরা’ অর্থাৎ ছেলেধরা তথা কাপালিকরা তন্ত্রসিদ্ধির জন্য নরবলি দেন। পুকুর-পুষ্করিণী খোঁড়া হয়েছে, জল আসছে না। চল্লিশ ফুট কুয়ো খোঁড়া হলো, জল উঠছে না। মজবুত করে বাঁধ তৈরি হলো, তবু পুনঃপুনঃ ভেঙে যাচ্ছে। তন্ত্রসাধক সিদ্ধাই বললেন, ‘নরবলি চাই!’
এইভাবে কত যে নরবলি দেওয়া হতো! মীননাথ, শবরীপাদের মতোই অনেক ধীবর, শবর, ডোম্বী, চণ্ডালী, রজকিনীরা সেযুগে সিদ্ধাই ছিলেন। তাঁরা তুক-গুণ ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র জানতেন।
কেন, ‘বেহুলা-লখিন্দর’ পালায় নেতা ধোপানী কি কম বড় সিদ্ধাই বা কাপালিক ছিলেন ? এক থাপ্পড়ে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে ফের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। অধিকন্তু বেহুলাকে হদিস দিয়েছিলেন স্বর্গের।
আমাদের ঘরের ধারেই পিতলকাঁঠি গ্রাম। সেখানকার বড়ামচণ্ডীর থানের সিদ্ধাই বা দেয়াশীরা লোধাশবর। শুধু কী পিতলকাঁঠি, গুপ্তমণি থানের সিদ্ধাইও তো লোধাশবর! নরবলি না হোক, পিতলকাঁঠিতে বড়ামচণ্ডীর পূজায় এখনও তো মহিষ বলি হয়। হয় না ?
তবে কি এই পোড়োবাড়িটা হীনযানী বজ্রযানী কালচক্রযানী সিদ্ধাই কী কাপালিকদের আখড়া বা আবাসস্থল ? ডাকিনীবিদ্যা জাদুবিদ্যার চর্চা হয় এখানে ? বলিদানের ‘অর্গলা’ বা হাড়িকাঠ আছে ?
আমার মা-কাকিমারা কেন, তামাম তল্লাটই তো জানে, মশানির দহে ‘অর্গলা ভূত’ আছে! জলের তলায় অর্গলা ভূতের ‘অর্গলা’ অর্থাৎ হাড়িকাঠ আছে। ঝিঁজরি বেঁধে ধরে আনা মানুষকে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া হয়।
মৃত নালন্দা কি ওদন্তপুরীর ধ্বংসস্তূপের মতো অত বৃহদাকার না হোক, তবু তো আচিরে-প্রাচীরে এটাও কম বৃহৎ নয়। তবে কি এখানকার আবাসিকরাই ‘অর্গলা ভূত’-এর হাড়িকাঠের বলিদার ? বলিদানের উদ্দেশ্যেই কি অপহরণ করা হয়েছে আমাকে ?
পরক্ষণেই মনে হলো, ধুৎ! এসব কী ভাবছি সিদ্ধাইরা, আজকাল না হোক সেকালে, যাঁরা অত সুন্দর সুন্দর পদ লিখেছেন, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে কত পদ মুখস্ত করেছি―
‘ভব নই গহন
গম্ভীর বেগে বাঁহি
দু আন্তে চিথিল
মাঝে ন থাঁয়ি ॥’
কিংবা, ওই যে―
‘উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসয়ি সবরীবালী―’
তাঁরাও আবার কাপালিক ? তাঁরাও আবার বলিদার ? এ হতে পারে না। বুকে-মনে জোর এনে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। যদিও ঝিঁজরির টান ততটা প্রবল ছিল না।
না থাকারই কথা। কেননা, তাঁরা তো বুঝেই গিয়েছেন, পাখি আটকা পড়েছে খাঁচায়। পালানোর আর কোনও পথ নেই।
আমাদের গ্রামের প্রতাপ রানাও এমনটা করে। বনডাহির ধারে কুরথি কলাইয়ের ক্ষেতির আড়ালে ফাঁদ পেতে গুঁড়ুর বা গুড়গুড়ি পাখি ধরে। খাঁচার পাখিটা খাঁচার ভিতরে থেকে আপন খেয়ালে ডাকতেই থাকে, ডাকতেই থাকে―
গু-ড়্-ড়্-ড়্-ড়্-ড়্-ড়্―
বনের পাখিটাও এক পা দু পা করে আসতে থাকে―আসতে থাকে ―
খাঁচার দরজা খোলা। খোলাই থাকে। খাঁচার দরজা স্প্রিংয়ে ভর করে মাটিতে পোঁতা। ঘরের পাখি যেমনকার তেমনই বন্দি থাকে খাঁচায়। ঘর-বাহির করে। এক পা-দু পা-তিন পা-চার পা-অতঃপর বনের পাখি খাঁচার দরজায় পা রাখা মাত্রই দরজা উঠে যায় ঝপাং করে! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বনের পাখি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।
প্রতাপ কিন্তু ধীরস্থির থাকে। বিচলিত হয় না এতটুকুও পাখি ধরার জন্য। তার পরিবর্তে সে কুরথি কলাইয়ের খেতির উপর বসে থেকে দাঁতে ঘাস কুটে। কী কুরথির দানা চিবায়। কুরথি খেতিতে কাজ করা লোকেদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যায়। কারণ, সে তো জানেই পাখি আটকা পড়েছে খাঁচায়।
আমারও পালাবার পথ নেই। পথ নেই, পথ নেই।
অথচ একটা সাদামাটা আর পাঁচটা গঞ্জের মতোই গঞ্জ। গাছপালা আছে, পাখ-পাখালি আছে। ওই, ওই তো ঝাঁকের পারাবতগুলি উড়ে ঘুরে ফিরে আসছে আবার! এই এই, পোড়ো বাড়িটার ছাদে বসল বসল করেও বসল না!
কোথাও কোনও কাঁটাতার নেই। প্রহরায় বন্দুক হাতে মুখোশধারী কোনও দুষ্কৃতী নেই। দৃশ্যত বন্ধনকারী ঝিঁজরিও নেই। তবু, তবু।
ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে দু পা তুলে কাণ্ডজ্ঞানহীন তালজ্ঞানহীন প্রায় নৃত্যই শুরু করলাম। তা থৈ তা থৈ। তা তা থৈ তা তা থৈ―এ নৃত্য কেউ দেখছে কী দেখছে না, জানি না। নৃত্য তো জানিও না! ওই বড়জোর স্কুলে এ. সি. সি ক্যাডার হিসাবে ‘সা-ব-ধা-ন’ ‘বি-শ্রা-ম’ ‘ক-দ- ম তো-ড়’।
কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। সেই অদৃশ্য ঝিঁজরির টান। টানছে তো টানছেই, নিশির ডাকের মতো। বলিপ্রদত্ত আমিও যেন এগিয়ে চলেছি। ভূতে ধরা আর কাকে বলে ?
ওই, ওই। ওই তো হাট করে খুলে গেল ভগ্নস্তূপ, কী পোড়োবাড়ি কী মৃত বৌদ্ধ সংঘারামের সিং-দরোজা।
১১
গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই কে যেন মৃদুস্বরে বলে উঠল, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?
কে ? কে বলল এ কথা ? কণ্ঠস্বর ভারী পরিচিত বোধ হচ্ছিল। তবে কি পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ তথা পোড়োবাড়ি বা সংঘারাম জনমানবশূন্য নয় ?
কিন্তু কই ? চারদিকে খুব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকেই দেখতে পেলাম না ? তবে কি কণ্ঠস্বর কুহেলিকা ‘মায়ামাত্র’ ?
একেকটা মুহূর্ত আসে। আসেই, যখন বোধশক্তি সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। চারপাশে জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তখন আর কিছু করার থাকে না। আমার এখনকার অবস্থা যেন তদ্রƒপ, তথৈবচ।
পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে এ তো বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নারীচরিত্র ‘কপালকুণ্ডলা’র কণ্ঠস্বর! ভ্রম, অলীক স্বপ্নমাত্র! তবু যা হোক নবকুমারের কপালকুণ্ডলা ছিল।
ছিল, ছিল। ‘মামনুসর’ বলে সেই যে তান্ত্রিক কাপালিক নবকুমারকে বধার্থে কুটিরমধ্যে আটকে রেখেছিলেন, কপালকুণ্ডলা না থাকলে কে তাঁকে খড়্গাঘাত থেকে বাঁচাতেন ?
কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রেম-পরিণয়ও হয়েছিল। উপন্যাস তো এরকমই বলে! আমার কোনও কপালকুণ্ডলা নেই, প্রেম-পরিণয় তো দূরঅস্ত্।
তবে এক-আধটুকু ভালবাসাবাসি হয়েছিল বৈকি, যখন থ্রি-ফোরে পড়ি। কার যেন একটা এইরকমই হুবহু কবিতা পড়েছিলাম―
আমাদের ফ্রি প্রাইমারি মরি মরি কীরূপ ধরেছে হেরি
দেয়ালে এখনও লেখা ― ‘নলিনী + কুসুমকুমারী’
এখানে ওখানে কালি হাতে মসি মুখে মসি
বাছা তুই পড়ে এলি ― কুণ্ডুদের অলি-মলি
ছেঁড়া বই জীর্ণ রাফখাতা করবলী গাছের পাতা
ভাঙা উড্ পেনসিলের সীস্ ― অঙ্কে একশোয় উনিশ
মহামতি লম্বোদর গিরি এখনও করেন ‘টিচারি’
লালমোহন সিং ― শান্তবালাকে খায় ‘কিস্’
বলে কীনা ‘ আমি শুক তুই শারী তোদের আজ কী তরকারি
আমাদের শুশনি পাতা ‘―সারি সারি ছেঁড়া ছাতা’
ছোট ছোট খোকা খুকু ভয়ে প্রাণ ধুকু ধুকু
তবু সাজিয়া গুজিয়া ― জিলিপি বোঁদে নিদেন ‘গুজিয়া’
রোল কলের সময় এখনও বলতেই হয়
‘জয়হিন্দ’ ‘স্বাধীন ভারত’―রামচিমটি নতুবা নাকখৎ
স্ট্যান্ড আপ অন দী বেঞ্চ নীলডাউন হাঁটুর তলায় খেঁচ্
পনেরই আগস্ট ― নিমপাতা আমসার রঙিন কাগজ
‘অ-য়ের পিছনে আঁকড়ি খুইয়েছিস সোনার মাকড়ি
ঘরে চল আজ তোর হবে’―ধরেছে কদমকুঁড়ি সবে
আমাদের ফ্রি প্রাইমারি মরি মরি কীরূপ ধরেছে হেরি
দেয়ালে এখনও লেখা ― ‘ভোট + আদমসুমারি’
কিন্তু সে-কবিতায় ‘নলিনী + কুসুমকুমারী’ কী আর ছিল ? ছিল না, ছিল না। ছেলের নাম ও মেয়ের নাম―অন্য কিছু ছিল। আমি তার উপর বেলের আঠা লাগিয়ে পরিষ্কার কাগজ সেঁটে কালি দিয়ে মুক্তাক্ষরে লিখে রেখেছিলাম―‘নলিনী + কুসুমকুমারী’ কুসুমকুমারী বাগালদের মেয়ে। ‘নলিনী + কুসুমকুমারী’―এই ফর্মুলা অত কী আর বুঝত! প্রেমট্রেম নয়, সে ভালবাসত ‘গুটি’ খেলতে। গুটি অর্থাৎ নুড়ি― সেই যে এ-হাতে সে-হাতে নুড়ি নিয়ে লোফালুফি খেলা―‘এ-ক-ম দু-ক-ম টিলিঙ ঠয়া’― তারপর তো তার বিয়ে হয়ে গেল বেশ ঘটা করে সেই কোন নাবালক বয়সে দূর দেশে ওড়িশা মুলুকে! সে আর এখানে কোথায় যে পরিত্রাতার ভূমিকায় সহসা অবতীর্ণ হয়ে কর্ণকুহরে মৃদুস্বরে শোনাবে―‘পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?’
হয়তো বা সে এখন তার রসুঁইশালে জুরুথুবু হয়ে বসে মাটির ‘ত্যালান’-এ কুরথির ডালে শুকনা লঙ্কার ফোড়ন দিয়ে মনে আনছে, মনে আনছে―‘সোউ যে নলিন নামর গুট্যে ছুয়া থিলা, সে মোর বইঅর পাতায় পাতায় কাগজ সাঁটি কিছু লিখি থিলা―ই গো কিছি কি, গুট্যে হেঁয়ালি―’ নলিনী + কুসুমকুমারী―হয়তো বাকি জীবনটা সে এই হেঁয়ালির ‘মানতি’ খুঁজে যাবে, সেইক আর এখানে এসে এই পোড়োবাড়ি থেকে বহির্গমনের বা পলায়নের পথ জানিয়ে দেবে! যেমনটা করেছিলেন কপালকুণ্ডলা―
‘কোথা যাইতেছ ? যাইও না।
ফিরিয়া যাও―পলায়ন কর।’
তদুপরি, কাপালিক যখন নবকুমারকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে সমুদ্রবালিতে ফেলে রেখে নরবলির জন্য পূজায় ব্যাপৃত হলেন, পূজাশেষে বলিদানের খড়্গের সন্ধানে দূরস্থানে গমন করলেন, তখন যেমন কপালকুণ্ডলা অভয় দিয়ে নবকুমারকে শুনিয়েছিলেন ―
‘ চুপ! কথা কহিও না―
খড়্গ আমারই কাছে―চুরি
করিয়া রাখিয়াছি ―’
অধিকন্তু নবকুমারের হাত-পায়ের বাঁধন খড়্গ দিয়েই ছেদন করে তাঁকে মুক্তির পথ দেখিয়ে বলেছিলেন―
‘পলায়ন কর; আমার পশ্চাতে
আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি ―’
তেমনটা কি আর পারবে ? পারবে কুসুমকুমারী ? আমার এই পায়ের ঝিঁজরি কেটে আমাকে এই কারাগার থেকে, এই ‘অর্গলা’ থেকে মুক্তি দিতে ?
সাধ্য কী কুসুমকুমারী তা পারে! এক্ষণে কোথায় কুসুমকুমারী আর কোথায় বা আমি ? হায় কুসুমকুমারী! হায় ‘নলিনী + কুসুমকুমারী!’
এখনও যে পায়ের ঝিঁজরি টেনেই চলেছে! টেনেই চলেছে, টেনেই চলেছে। এ কী গৃহ ? না, গুহা ?
গৃহই। ওই তো―সারি সারি ‘ঝুরকা’। যাকে বলে গবাক্ষ। গবাক্ষ-দণ্ডের ফাঁক-ফোকর দিয়ে মধ্যাহ্ন-সূর্যের রৌদ্র এসে পড়েছে ইতস্তত। আলো যেন বরফি কাটছে। চক্রা-বক্রা।
আলো-ছায়া তো নয়, ‘আলো-ছাঁয়রা’। আলো বাতাস। আহ্! এই তো জীবন! গবাক্ষদণ্ডের ফাঁকফোকর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া আসছে।
হাওয়াই তো। ঝুরকার পার্শ্বস্থিত দেয়ালগাত্রে ঊর্ণনাভ যে তন্তুজাল বয়ন ও বিস্তার করেছে―তা যেন ওই হাওয়াতেই দোদুল্যমান। দুল দুল দুলছে। দুলছে, কিন্তু ছিঁড়ে পড়ছে না।
একটার পর একটা ঝুরকা। তার মানে, একেকটা ঝুরকাবিশিষ্ট কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ। একদা কারা ছিলেন এই সমস্ত প্রকোষ্ঠে, এক্ষণে কারাই বা এখানে বাস করেন―কই, কাউকেই তো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না!
গিনতি শুরু করেছিলাম―রামে রাম, দুই-তিন-চার-পাঁচ- ছয়-সাত―আচমকা গুলিয়ে গেল। কোত্থেকে একঝাঁক চামচিকে না তার বাদুড় ঝটাপটি করে উড়ে এসে সবকিছুকেই ঘুলিয়ে দিয়ে ভদভদিয়ে বেরিয়ে গেল।
মনে হলো, কে যেন পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খবরদারি করে তাড়িয়ে দিচ্ছে ―‘হে-ই হু-স্ হু-স্ হু-স্―’ কে ? কে ? কে ?
১২
কই ? কেউ তো নেই।
ঝুরকার বাহিরে দৃশ্যমান―ওই, ওই তো―জল ছিল্ ছিল্ পুষ্করিণী। চারধারে তার কেয়া বনঝাড়। এমন, এমনতরো পুকুর-পুষ্করিণী তো আমাদের তল্লাটে হামেশাই দেখা যায়! উদাহরণ স্বরূপ―চিনিবাসের গাড়িয়া। চিনিবাস তো নয়, ভালো নাম শ্রীনিবাস। বড়োডাঙা গ্রামের দঁড়পাট মহাজনদের ‘গড়িয়া’। সেই বলে না―‘গড়িয়া আড়িরে শ্বেত মান্দার’। অর্থাৎ পুকুরপাড়ে শ্বেত মান্দারগাছ―রামেশ্বর ডাঙার ‘কুঁড়পুকুর’ বা কুণ্ডুপুকুর। কুঁড়পুকুরের পাড়ে গাজনের সময় ‘বারুণী’র মেলা বসে। শশা কাঁকুড় তরমুজ শাঁকআলু ঢেলে বিক্রি হয়। শাঁকআলু তো নয়, কেশর আলু। বোলতার পেটের মতো নাকে নোলক পরা চাষিদের মেয়ে সারা রাত ধরে কেশর বেচে ক্লান্ত হয়ে একসময় কেশর আলুর গাদাতেই ঘুমে ঢলে পড়ে।
যেমনটা, ‘সেথা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।’ চৈত্রসংক্রান্তির শেষ রাতে যখন চেলা-চামুণ্ডা-পাণ্ডা পরিবৃত হয়ে প্রধান পুরোহিত ‘গয়লা-ভার-কাঁধে’ সুবর্ণরেখার জলে তার সামান্য পিতলের ঘটিদুটি ভরাতে যান, বা ঘটিদুটি জলে ভরতি করে ভার-কাঁধে অতিশয় ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাপুস থুপুস করে হেঁটে আসেন, তখনও তার ঘুম ভাঙে না।
ঘুম ভাঙে না। ঘুম ভাঙে না ।
জলে শিরশিরানি ওঠে। নদীজলে কী পুষ্করিণীর জলে। কাক-চিল খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেলে এক রকম, শিকারি জেলের ছায়া পড়লে এক রকম, নদীর কাতাধারে কী পুষ্করিণীর পাড়ে ঝুর ঝুর বালি ঝরে পড়লে এক রকম।
চরতে বেরিয়ে ঝাঁক-বাঁধা-মাছ জলে বিলি কেটে কেটে এগোচ্ছে, অনুকূলে নয় প্রতিকূলে, এগোচ্ছে তো এগোচ্ছে। হঠাৎ কেমন চাক ভেঙে ছিন ছাতুর! ভয়ার্ত জলচরগুলো মুহূর্তেই হাওয়া!
আর তাতেই জলে শিরশিরানি ওঠে। জলের শিরা-উপশিরা দেখা যায়। কুঞ্চন অকুঞ্চনে জলসিঁড়ি তৈরি হয়। এমনটা হামেশাই ঘটে।
কাক-চিল জালুয়া-মালুয়া বালি ঝরঝরানি থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। ওই, ওই তো গবাক্ষের বাহিরে পুষ্করিণীর জলে বাও নেই, বাতাস নেই আচমকা জল-শিরশিরানি, জলসিঁড়ি তৈরি হলো।
গবাক্ষের পর গবাক্ষ। পেরিয়ে যাচ্ছি একের পর এক। ঝপাং করে কেউ যেন ঝাঁপ দিল পুষ্করিণীর জলে! চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ রাখলাম গবাক্ষে।
―কই, কেউ তো নেই!
অথচ পুষ্করিণীতে পরিষ্কার আলোড়ন উঠেছে। জল আলোড়িত হতে হতে জলাশয়ের কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে।
আর আমরা তো জানিই, ‘একটি স্থির জলাশয়ে যদি ঢিল ফেলা যায় তবে ঢিল যেখানে জলস্পর্শ করে সেখানে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আলোড়ন ওই জায়গাতেই আবদ্ধ থাকে না, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে সমস্ত জলাশয়েই আলোড়ন বিস্তৃত হয়ে যায়।’
পদার্থবিজ্ঞানে একেই তো বলে ‘তরঙ্গ । জলসিড়ি ধানসিড়িও তো এভাবেই রচিত হয়। ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে―’
ধানসিড়ি নদী না হোক, ধানখেত। ধানের খেতেও হাওয়া দোলা দিলে এমনিতরো তরঙ্গের অভিঘাত তৈরি হয়। পাকা ধানের শীষগুলো কেমন দোল তুলে ধাপে ধাপে ধানসিঁড়ি রচনা করে। অথচ ধানগাছগুলো কোথাও একেবারে চলে যায় না। স্থির অবস্থানকে মধ্যে রেখে শুধু উপর-নিচ পর্যায় গতিতে দুলতে থাকে।
দুলতে থাকে, দুলতে থাকে।
আর এভাবেই কখন যে কী করে ভাবের ঘোরে তৈরি হয়ে যায় ধানসিড়ি জলসিড়ি!
কতবার যে হাতেনাতে প্রমাণ করেছি ―‘কোনও তরঙ্গবাহী সুতোরী বিন্দুতে ‘নতি’, ওইবিন্দুতে কণার গতিবেগ ও তরঙ্গবেগের অনুপাতের সমান।’
অঙ্ক করেছি―‘পজিটিভ-অভিমুখে গতিশীল একটি সরল দোলগতির তরঙ্গের বিস্তার ৫পস, গতিবেগ ৪০পস/ং এবং কম্পাঙ্ক ৬০; মূলবিন্দু থেকে ৪০পস দূরবর্তী একটি কণার ঃ=২ং সময়ে সরণ, গতিবেগ এবং ত্বরণ নির্ণয় কর।’
সে যা হোক, জলাশয়ে এত বড় তরঙ্গ তোলা বস্তুটি তরঙ্গ তুলেই কোথায় বা অদৃশ্য হলো! তবে সে কি ডুব-সাঁতারে আছে ? ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার, ব্রেস্ট স্ট্রোক, ফ্রি স্টাইল, বাটার ফ্লাই, ব্যাক স্ট্রোক―
ডুব-সাঁতার―এই ডুব মারলো তো, ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরেই চলেছে ঘুরেই চলেছে, ঘুরেই চলেছে, জলের তলায় নাক টিপে দম আটকে আর কতক্ষণ বা থাকা যায়―ওই, ওই ভুস করে খইচালার মতো ভেসে উঠল কালো মাথা!
আমিও উৎকন্ঠায় অধীর আগ্রহে তরঙ্গায়িত জলাশয়ের জলবিজকুড়ির অপেক্ষায় তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি―
সাঁতারু যেদিকে যায় তার যাত্রা বরাবর জলের উপরিতলে গুঁড়ি গুঁড়ি বুদ্বুদের কণা, জলবিজকুড়ি ভেসে ওঠে। তেমন কিছু ভেসে উঠছে কি ?
কই, না তো!
অবশ্য চোখ খুলে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার উপায়ন্তর কি আর আছে! মশানির দহের ‘অর্গলা ভূত’-এর অদৃশ্য পায়ের ঝিঁজরি তো অনবরত টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে।
লোকে বলে, ‘পায়ের তলায় সর্ষে’। তার মানে ভ্রমণের চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই। সর্ষেদানার আকার-অবয়ব যে গোলাকার! সমতল মাটিতে পড়লে সে আর থামতে জানে না, গড়াতেই থাকে, গড়াতেই থাকে। তার উপর পা পড়লে যার পা সেও তো গড়াবেই―
আমার অবস্থাও, বলা বাহুল্যই, তদ্রূপ। পায়ের তলায় সর্ষে না থাক, লোহার ‘জিঞ্জলি’। তাও আবার দৃশ্য নয়, অদৃশ্য। অদৃশ্য ঝিঁজরির টানেই কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে―
পরিত্যক্ত পোড়ো বৌদ্ধ সংঘারামই ধরব। সেই কোন থ্রি-ফোর থেকেই তো পড়ে ইতিহাসে পড়ে আসছি―‘গৌতম বুদ্ধ কে ছিলেন ? গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের নাম কি ? নালন্দা ও তক্ষশীলা কী জন্য বিখ্যাত ?’
শুধু কি তক্ষশীলা নালন্দা ? কর্ণসুবর্ণ রঙ্গভিত্তি সংঘারাম, তাম্রলিপ্ত সংঘারাম, জগদ্দল বিহার, পুণ্ড্রবর্ধন বিহার, বরাহ বিহার, বিক্রমপুরী বিহার, শীলবর্ষ বিহার, সোমপুরী বিহার, ত্রৈকূটক বিহার, দেবীকোট বিহার, আরও যে কত!
শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, আচার্য অদ্বয়বজ্র, উধিলিপা, ভিক্ষুনী মেখলা, বন-রত্ন, অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র, লীলাবজ্র, বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত, ধর্মাকর, সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ, তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ, বোধিবর্মা, আচার্য প্রজ্ঞাবর্মা, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান্-চোয়াঙ, ইৎসিঙ।
কত যে বড় বড় পণ্ডিত, আচার্য, সিদ্ধাচার্যরা এই সমস্ত বৌদ্ধবিহার―মহাবিহারে বসবাস করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কত যে সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ, তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ, সারসংগ্রহ রচনা করেছেন!
ফা-হিয়েন, য়ুয়ান্-চোয়াঙ, ইৎসিঙ, মহাস্থবির তাম্রলিপ্তবাসী কালিকের মতো কত যে ভিক্ষু আর থেরীরা এই সমস্ত সংঘারামগুলোয় কাঠ কী সেজের আলোয় অধ্যয়ন করতেন!
কক্ষে কক্ষে পায়রা-পারাবতের মতো ‘বকম’ ‘বকম’ কলরব উঠত। দশটা-বাইশটা শুধু নয়, কোথাও কোথাও পঞ্চাশ-ষাট, এমনকি শতাধিক সংঘারামের রমরমা! পাঁচ শো-ছ শো শুধু নয়, হাজার হাজার আজীবক-শ্রমণ-ভিক্ষু ও থেরীদের উপস্থিতি।
আজ বাঙালি কবির কবিতায় সে সমস্তই ‘সকরুণ স্মৃতি’―
‘হিমালয় নামমাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিম টিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
―তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতের
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে;
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!
ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরও এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
―ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই!’
১৩
কক্ষের পর কক্ষ। কত যে কক্ষ পার হয়ে এলাম! গণনা শুরু করেছিলাম বটে, অকস্মাৎ দাপাদাপি-ঝাঁপাঝাঁপিতে কখন যে গুলিয়ে গেল! মনে পড়ে ঊনচত্বারিংশতম কক্ষ পর্যন্ত গণনা করেছিলাম ―
ঊনচত্বারিংশ ? অ্যাঁ, তার মানে তো ঊনচল্লিশ! কথায় কথায় সংস্কৃতের এত টানটোন আসছে কেন ?
শ্রীশ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ এক্ষণে তর্জমা করে যে, এগূণ-চত্তালীস, একোনচত্বারিংশৎ সংখ্যক। আর ‘ঊন’ তো কতই শুনেছি! ‘কার্তিকের ঊন জলে। খনা বলে দুন ফলে ॥’ কিংবা, ‘ঊন ভাতে দুন বল। ভরা ভাতে রসাতল ॥’
অর্থাৎ, কার্তিক মাসের অল্প জলেও দ্বিগুণ ফসল ফলে। কিঞ্চিৎ অল্প আহারেও শরীরে দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হয়।
ধু-উ-র! কীসব ভাবছি! যাকে মশানির দহের ‘অর্গলা ভূত’-এর ঝিঁজরি বাধাছাঁদা করে নিয়ে এসেছে, যে কীনা বলিপ্রদত্ত―তার এ সময়ে এসব ব্যাসকূট-শ্লোককূট, ইত্যাদি কূটকচালি নিয়ে ভাবনাচিন্তা কি আর মানায় ?
মানায় না, মানায় না।
মনে তো হয়, এসব কক্ষে শিক্ষার্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই একদা বসবাস করতেন। ঝিঁজরির অদম্য টানে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাবার পথে নাবালকের মতো দেয়ালগাত্রে হাত থাবড়াচ্ছি, কী যেন ঝুর্ ঝুর্ করে ঝরে পড়ছে হাতের থাবড়ায়।
‘স্ট্যাকো’র গুঁড়ো কি ? পড়েছি বটে সংঘারাম কী বৌদ্ধবিহার, মহাবিহার-এর বহির্দেয়াল ‘স্ট্যাকো’র প্রলেপ দেওয়া। যেমনটা নালন্দা মহাবিহারে এখনও দেখা যায়।
একটু ছাড়া ছাড়াই দেয়ালে কুলুঙ্গি। একটা তো নয়, অজস্র। আমাদের ঘরের মাটির দেয়ালে একটাই কুলুঙ্গি আছে বটে। মা প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বেলে গলায় শাড়ির আঁচলা জড়িয়ে কাকে যেন নমঃ করে।
‘স্ট্যাকো’ তার মানে চুনের পলেস্তরা। চুন বা অন্য কোনও যৌগ। যা দিয়ে মূর্তি গড়া হতো। মূর্তির গায়ে দেয়ালে দেয়ালে নানারকম কারুকার্য করা হতো। কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে বসানো হতো মূর্তি।
ছায়াচ্ছন্ন ঈষৎ অন্ধকারময় ফেলে আসা কক্ষের কুলুঙ্গিগুলোতে কোনও মূর্তি ছিল কীনা―এতক্ষণ লক্ষ করিনি। এবার সতর্ক হলাম―দেখিই না, কোনও বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর কী গৌতমবুদ্ধের মূর্তি দেখতে পাই কীনা। কোথাও খোদিত আছে কী না―‘ওঁ মণি পদ্মে হুঁ’―
তিব্বতীরা নাকি এখনও এই মন্ত্র জপ করবার জন্য পথেঘাটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে একপ্রকার ‘কল’ বা প্রার্থনাচক্র বসিয়েছেন। কল ঘুরোলেই ওই জপমন্ত্র ‘ওঁ মণি পদ্মে হুঁ’ ঘুরতে থাকবে। ঘুরতে থাকবে। আর, যতবার ঘুরবে, যত বেশিবার ঘুরবে, তত বেশি পুণ্য।
একবার হয়েছিল কি, এই নিয়ে তো মহাধুন্ধুমার কাণ্ড! জনৈক লামা প্রার্থনাযন্ত্র ঘুরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরছিল। যন্ত্রের ঘূর্ণন তখনও অব্যাহত। হঠাৎ আরেকজন লামা তৎক্ষণাৎ এসে চাকা ঘুরিয়ে দিল তার দিকে।
পূর্বতন লামা ফের অকুস্থলে এসে বর্তমান লামার চাকাকে বন্ধ করে নিজের স্বপক্ষে চক্রযান ঘুরিয়ে নিল। গালাগালি থেকে মারামারি উপক্রম হলো।
এ বলে, ‘আমি প্রথম ঘুরিয়েছি। তুমি আমার চাকায় ঘূর্ণন শেষ হওয়ার আগেই কেন হাত দিয়েছো ?’ ও বলে, ‘আমার ঘুরন্ত চাকা তুমি এসে কোন সাহসে বন্ধ করেছো ?’
অবশেষে এক বৃদ্ধ লামা এসে পুণ্যার্থীদের কলহের অবসান ঘটান। পুণ্যার্থীদের হয়ে স্বহস্তে চাকা ঘুরিয়ে যার যত সংখ্যক পুণ্য তাকে তা পাইয়ে দেন। পুণ্য অর্জন করে পুণ্যেচ্ছুক ব্যক্তিদ্বয় নিশ্চিন্তে যে যার গৃহে গমন করে।
সেই ‘ওঁ মণি পদ্মে হুঁ’ প্রার্থনামন্ত্রটি কোনও দেয়ালগাত্রে কী কুলুঙ্গিতে খোদিত আছে কীনা―খুঁজে চলেছি, খুঁজেই চলেছি।
হঠাৎ চোখে পড়ল একটা মূর্তি, কুলুঙ্গিতে যেন ধরছে না! তলায় টেরা-কোটার প্রদীপ একটা। মায়ের মাটির প্রদীপের থেকেও বৃহৎ, সুবৃহৎ।
হাতে ‘স্ট্যাকো’র রঙ লেগেছিল দেয়ালগাত্রে হাত বুলিয়ে। রঙ কী আর, চুন বা কুইক লাইমের সঙ্গে জিপসাম অর্থাৎ বালি মিশিয়ে তার প্রলেপ দেওয়া। গেঁড়ি-গুগলি-শামুক আর ঝিনুক পুড়িয়ে ‘কলিচুন’ তো চুনাভাটিতে চুনাবুড়িরা এখনও করে।
কিন্তু মূর্তির গায়ে হাত বোলালাম। একবার, দুবার, তিন-তিনবার। তেমন কোনও রঙ বা যৌগ হাতের তালুতে উঠে এল না। তবে কি মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত ? পাথর দিয়ে গড়া ?
হবেও বা। বইয়েই পড়েছি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার বা সংঘারামগুলোয় স্থানীয় পোড়ামাটির ভাস্কর্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল আমদানিকৃত মুগনি আর শিস্ট পাথরের মূর্তি। কুবের, জাঙ্গুলী, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর আর বোধিসত্ত্বের মূর্তি। নানাবিধ নকশা করা ইট!
কিয়ৎক্ষণ পরে আলো-আঁধারি যৎসামান্য দূরীভূত হলে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম―মূর্তিটি মস্তকবিহীন! তার মাথা নেই!
মাথা নেই, মাথা নেই।
অতঃপর সারিবদ্ধ একাধিক কুলুঙ্গিতে মস্তকবিহীন মূর্তিই দেখা গেল। শুধু কী মস্তক, কারওর হাত ভেঙেছে কারওর বা পা। কাটা গেছে কান, ভাঙা পড়েছে নাক।
একের পর এক যত সব ভাঙাচোরা মূর্তি। বিশেষ করে মাথা-ভাঙা, মাথা-মুণ্ডুহীন। কতক পদ্মাসনা, পদ্মোপবিষ্ট। কতক দণ্ডায়মান, দণ্ডায়মানা।
এমন একটা দেখেছি বটে ইতিহাসের পাতায়। কী যেন নাম, কী যেন―
হ্যাঁ, কনিষ্ক। গলাকাটা সম্রাট। পরনে গলা থেকে পা পর্যন্ত আলখাল্লা। পায়ে ভারী গামবুট। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে কৃপাণ―
যা হোক, আর কোনও সন্দেহ নেই পোড়োগৃহটি বৌদ্ধবিহার বা সংঘারামই হবে। মূর্তিগুলি গৌতম বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, বোধিসত্ত্বেরই বটে। মুণ্ডুহীন কিছু মূর্তি তো মনে হয় লক্ষ্মী, গণেশেরও।
কোনও কোনও কুলুঙ্গিতে মূর্তি নেই, কেবল প্রস্তরফলক। ত্রিরত্ন, ধর্মচক্র, হস্তী, ব্যাঘ্র, নাগমূর্তি, মকরমূর্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন চুন, চুনাপাথর, মার্বেল পাথর, হাড়ের গুঁড়ো আর অসাধারণ এক ‘চিট’-এর মিশেল দিয়ে সব তৈরি!
কিন্তু প্রায় সবই তো কবন্ধ, মস্তকবিহীন। ভাঙা। হন্তারক কালাপাহাড়ের মতো কেউ যেন তরবারির প্রকোপে ছেদ করেছে অগণিত মুণ্ড। কথা বলতে চায়, হায়! মুখ নাই তার, কথা বলবে কী!
‘বিস্মৃত যত নীরব কাহিনি
স্তম্ভিত হয়ে রও―
ভাষা দাও তারে, হে মৌন অতীত,
কথা কও, কথা কও।’
একদা বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, বিদ্যাধর, কিন্নর-কিন্নরী, কুবের, বরুণ, মঞ্জুশ্রী, গন্ধর্বের মস্তকবিহীন ভাঙাচোরা মূর্তি দেখে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় যেন খেদ প্রকাশ করে বলেছেন―‘পুতুলগুলোও আধুনিক হিন্দুর মতো অঙ্গহীন হইয়া আছে।’
বটেই তো!
‘বসিত রাজেন্দ্র যথা স্বর্ণসিংহাসনে,
ফুকারে শৃগাল তথা বিকট নিঃস্বনে।
লুপ্ত গৌড়, সমতট, কর্মান্তের চিহ্ন,
কোথা হরিকেল কোথা কর্ণসুবর্ণ!
পথে পথে রাজধানী―ফুলের বাগান,
এ তো নহে বঙ্গ―এ যে বঙ্গের শ্মশান।’
এ কথা তো সত্যি, সত্যিই। হাজার মুখে বলতেই হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস যা, তা বৌদ্ধযুগেরই ইতিহাস। সংস্কৃতি যেটুকু, তা বৌদ্ধযুগেরই সংস্কৃতি। মাটি খুঁড়লেই হিন্দুস্তরের দু হাত নিচেই বৌদ্ধস্তর―গাঁইতি-শাবলের ঠোকাঠুকিতে বেরিয়ে আসবে কী, বেরিয়ে আসছে―হয় বৌদ্ধ সংঘারাম নয় বৌদ্ধ মহাবিহারের ভগ্নস্তূপ। ‘স্ট্যাকো’র কাজ করা গৃহপ্রাঙ্গণ, কারুকার্যময় ইটে তৈরি কুলুঙ্গির পর কুলুঙ্গি―আর পুতুলগুলো। লোকেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, মানুষীবুদ্ধ… কুবের, বরুণ, শিব, সূর্য, গন্ধর্ব … জাঙ্গুলী, মঞ্জুশ্রী, সিদ্ধাচার্য তিলোপা, সিদ্ধাচার্য নাড়োপা―পুতুল, পুতুল।
প্রথম প্রথম, বিশেষ করে অশোকের আমলে এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তারিত হয়েছিল স্তূপপূজা। ফলত সারনাথ, সাঁচিস্তূপ। কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধও চাইতেন না তাঁর মূর্তিপূজা হোক। তবু এত পুতুল এল কী করে ?
বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় চারশো বছর পরে সম্রাট কনিষ্কের আমলেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তাঁর রাজত্বেই বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ‘মহাযান’ ও ‘হীনযান’-এ বিভক্ত হন। মহাযানীরাই গান্ধার শিল্পের অনুকরণে বুদ্ধের মূর্তি গড়া শুরু করেন। অবশ্য হীনযানীরা প্রথম প্রথম মূর্তি গড়া পরিহার করতেন।
মূর্তি গড়তে গড়তে ‘আদিবুদ্ধ’ প্রথমে তিন ভাগ, ‘ধ্যানীবুদ্ধ’ ‘বোধিসত্ত্ব’ আর ‘মানুষী বুদ্ধ’, তারপর তাঁরা নিজেরাই আবারও পাঁচ ভাগ―
বুদ্ধ ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছেন। বেড়েই চলেছেন, বেড়েই চলেছেন। ওদিকে তখনও স্বমহিমায় বিরাজিত ‘ব্রাহ্মণ্য ধর্ম’, ভারতবর্ষে তাহলে কী করছিল ? অপরাপর যুক্ত শৈবরা, শাক্ত আর তান্ত্রিকেরা ?
বৌদ্ধ ধর্মের বাড়বৃদ্ধি যখন এতটাই, তখন তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল কী করে ? কী ভাবে ? ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ? মুসলমানী আক্রমণে ?
মূর্তিগুলোর শিরñেদ হলো। তাদের হাড়গোড় ভেঙে পড়ল। সেই সব খণ্ডিত মস্তকের স্তূপ, সংঘারাম, বিহার, মহাবিহারের ভগ্নস্তূপ রসাতলে চলে গেল ।
উঁহু, কতকটা উপরোক্ত কারণেও বটে, কতকটা স্বখাত সলিলে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে ক্রমশ মিশতে গিয়ে, মতের আদান প্রদান করতে করতে, একসময় লীন হয়ে গিয়েছে উভয়ত।
আর, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয়রা তো লোকভোলানো তন্ত্রমন্ত্রে, ‘ব্ল্যাক-ম্যাজিক’-এ সবিশেষ পটু! শীঘ্রই তাঁরা ধ্যানীবুদ্ধকে যোগাসনারূঢ় মহাদেব বানিয়ে ফেললেন। শুধু কী মহাদেব, একে একে আসতে লাগল শক্তি, উমা, জয়া, চণ্ডী মহাকালী খড়্গহস্তা কপালিনী, কপালমালা অজিতা, অপরিজিতা মার্তৃকা, খট্টাঙ্গা বজ্রহস্তা মহারূপা―
তদুপরি ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিনী, ভৈরবী। তাদের সাধনার জন্য লেখা হলো ‘সাধনমালা’, তাতে সাধনমন্ত্র, ‘বজ্রযোগিনী’ ‘কুরুকুল্লা’ ‘বজ্র-বারাহী’ ‘মহামায়ূরী’ ‘মহাপ্রতিসরা’ ইত্যাদি ইত্যাদি ডাকিনী-যোগিনীর ধ্যান-মন্ত্র।
রীতিমতো মূর্তি গড়ে ‘গুহ্যপূজা’ও শুরু হলো। ততদিনে কী হীনযান কী মহাযানঠউভয়ে মিলে সহজযান, সহজিয়া। ভিতরে ভিতরে লণ্ডভণ্ড হয়ে চলল।
এ যেন ‘পরশুরাম’ বিরচিত ‘ভুশণ্ডীর মাঠে’র আড়াধাড়া। ‘পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে―’
সেখানে পানতুয়ার শাঁসের মতো ডাকিনীকে দেখে শিবু ওরফে পেনেটির শিবু ভট্টাচার্য যেই একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল―
‘আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।’
সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্র কণ্ঠে শব্দ উঠিল।
‘চা রা রা রা রা রা
আর ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগলুকে বিটিয়া
কেকরাসে সাদিয়া হো কেকরাসে হো-ও-ও-ও―’
এই পোড়ো সংঘারাম কী বৌদ্ধবিহার অদ্য মধ্যাহ্নেই যেন সেই ‘ভুশণ্ডীর মাঠে’র আকার-প্রকার ধারণ করেছে!
১৪
‘ভুশণ্ডীর মাঠে’র সঙ্গে কোনও গতিকে তুলনা টানলেও এখানকার রকমসকম একটু আলাদা প্রকৃতির।
আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনোওল বাবলার গাছপালা থাকলেও এখানকার মানুষজন, কী শরীরী কী অশরীরী, কেউই এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। সবাই যেন ‘ইনভিজিবল’।
মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য হলেও তবু তো পিটুলিবিলের ধারে শ্যাওড়াগাছের পেত্নী পোলো-হাতে মাছ ধরতে যায়। শাঁকচুন্নী একটা গামছা পরে একটা গামছা মাথায় দিয়ে এলো চুলে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাতের হাঁড়ি থেকে গোবর-গোলা-জল ছড়ায়।
ক্ষীরি-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় ডাকিনী খেজুরের ডাল দিয়ে রোয়াক ঝাঁট দেয়। কারিয়া পিরেতকে ডাকলেই তালগাছের মাথা থেকে সড়াক করে নেমে এসে বলে, ‘গোড় লাগি বরমদেওজী।’
তদুপরি হিজলিতে নেমকের গোমস্তা কালিদাসের ভায়রাভাই নদের চাঁদ মল্লিক ওরফে নাদু মল্লিকের কণ্ঠে পেট বাজিয়ে চৌতাল শোনা যায়―ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক―
কিন্তু এখানে, এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে তো লোকজন একটাও দেখি না! অথচ আস্ত না হোক ভাঙাচোরা একটা বাড়ি। ‘চি-চি-ঙ্ ফাঁ-ক’-এর মতো একটা দরজা, অবারিতও বটে।
কক্ষের পর কক্ষ। গবাক্ষ ও কুলুঙ্গি। পারাবত কুহরে, চর্মচটকা-বাদুড়ার মাঝেমধ্যে ঝটপটানিও আছে। রৌদ্র উঠেছে, গাছের পাতায় হি লি হি লি গি লি গি লি করে সে-রৌদ্র ছলবলাচ্ছে। হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।
পুষ্করিণীর জলে যেন মধ্যাহ্নে সূর্যসহ রৌদ্রেরও ছায়া পড়েছে। আকাশে চক্রাকারে উড়েঘুরে বেড়াচ্ছে চিল। ‘ভু-ই-চু-ঙ’ আওয়াজ করে একটা পাখি তো এইমাত্র কোত্থেকে উড়ে এসে পুষ্করিণীর জল ছুঁয়ে আবার উড়ে গেল কোথায়! ডাক শুনে বোধ হলো―‘ঢ্যাপচু’।
তার মানে ফিঙে পাখি। ফিঙেই।
পোড়োবাড়িটার অন্দরে, অকুস্থলে, দেয়ালগাত্রে, কুলুঙ্গিতে এইসব মুণ্ডুহীন মূর্তি, তথাকথিত ‘পুতুলগুলো’―‘কথা কও কথা কও’ বলে হাজার চেঁচালেও তারা বুঝি আর কখনও কথা বলবে না! কোনও কালে বলেওনি।
এসব কত যুগ আগের! গত জন্মের। হয়তো বৌদ্ধদের, বৌদ্ধ শিল্পীদের দ্বারাই নির্মিত। এখন হাড়-গোড়-ভাঙা ‘দ’ হয়ে পড়ে আছে। মরা, মৃতই।
এত কিছু দেখে ইতিহাস-পুরুষেরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সব বৌদ্ধ ছিলেন। কমবেশি তামাম বাঙলাই ছিল বৌদ্ধদের চারণক্ষেত্র।
সে যা হোক, পোড়োবাড়িটা তথা বৌদ্ধসংঘারাম বা বৌদ্ধবিহারের ভিতরটা যখন মরা মরা, তখন বাহিরে গনগনে আঁচের মতোই জীবন! ওই, ওই তো পুষ্করিণী-জলে বিলি কাটছে মৃদুমন্দ হাওয়া―
গুচ্ছ গুচ্ছ ছেয়ে আছে শুশনির দঙ্গল, ছেয়ে তো নয় যেন জলাশয়ের ধারে ধারে ভেসে বেড়াচ্ছে। তেমন আর বিলম্ব কই ? হয়তো আমাদেরই গ্রাম থেকে এক্ষুনি চলে আসবে সোমবারি-কাঁদরিরা। ‘টুপা’ ভরে তুলে নিয়ে যাবে শুশনিশাক।
যেতে যেতে শাক তোলা নিয়ে হয়তো দু কলি গানও শুনিয়ে যাবে তারা―
‘শাক তুললম লতা লতা মাছ রাঁধলম গেঁতা লো। বিটি ছাইলার দূরে বেহা কাঁদিছে অন্তর লো ॥’
গাঁতি-জাল ফাবড়ি-জাল নিয়ে মাছ ধরতে নেমে পড়বে বিপিন আর সুরেশ বিশুইয়ের দল। জল ঘোলা করে ছাড়বে বেলা আড় অব্দি। মাছও উঠবে তেমন―রুই, মিরগেল, কালবোউশ, বাটা, খয়রা―
ফের জলে কে যেন ঝপাং করে ঝাঁপ দিল―দেখিই তো দেখি! ঝোরকার দিকে তড়িদ্বেগে দৌড়ে ঝুঁকে পড়েছিলাম, ‘অর্গলা ভূত’-এর ঝিঁজরি হ্যাঁচকা টান মারল। তবু এর মধ্যেই জলে যেন এবার বুজকুড়ি কাটতেও দেখে ফেললাম।
কিন্তু সে কই ? সে, সে-ই―জলে যে ঝপাং করে ‘ডাইভ’ মারল! সে কি এই পোড়োবাড়িটার উঁচু ছাদ থেকেই লাফ দিল ? জলাশয়ের জল তো মনে হয় পোড়াবাড়িটার তল ছুঁয়েই আছে।
এতক্ষণ পরে আমার রাগ হলো। রাগ বলতে রাগ, ভয়ানক রাগ―সেই কখন রাতে খেয়েছি! আমাদের নিজের ঘর হলে খিদের জ্বালায় এতক্ষণে মাকে কত যে জ্বালাতন করতাম! ‘খেতে দাও মা, খেতে দাও!’
মা বলত, ‘দাঁড়া বাছা, এই তো সবে তরকারিটা বসিয়েছি!’ বলেই বাঁশের ফুঁক-নলিতে উনুনে ফুঁ দিত মা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ তার লাল হয়ে উঠত।
জিজ্ঞাসা করতাম, ‘কী তরকারি মা ? কী তরকারি ?’ উত্তরে মা হয়তো বলল, কুড়কুড়িয়া ছাতু কি বাঁশকরোল। আহা, ডুমো ডুমো ডুমুরের মতো এক ধরনের ছত্রাক। ব্যাঙের ছাতা। বালিতে কুড়্ কুড়্ করে ফোটে বলেই ‘কুড়কুড়িয়া’। কাঁচায় ভেঙে নখে টিপে তার কালো না না হোক সাদা শাঁসটুকুই কত খেয়েছি!
আর ‘বাঁশকরোল’―মাংসের মসল্লা দিয়ে যদি রাঁধো, খেতে একেবারে খাসির মাংস! বাঁশকরোল, তার মানে নতুন বাঁশের কলি। বাঁশের পোঙ বা চারা। তাই খেতে দলমার হাতি পর্যন্ত আসে লাইন দিয়ে! গুরাসাঁওতালের ‘ঘুসুর’ বা শূওর তো গজামুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে ভেঙে তসরপাৎ করে দেয়!
যা হোক লোভে পড়ে বলতাম, ‘বেশ মা, বেশ। তাহলে তো একবার নয়, দুবার খাব। ভাত চাট্টি বেশিই খাব মা। কিন্তু যাহোক-তাহোক দিয়ে এখন কিছু তো দাও মা!’
কপট রাগ দেখিয়ে মা হয়তো বলল, ‘হা-ঘরে ছেলে কোথাকার! যা, ‘বাড়ি’ থেকে কটা ঝিঙা তুলে আন জলদি!’ তন্মুহূর্তেই দৌড়ে গিয়ে ‘বাড়ি’ অর্থাৎ ঘরের পিছনের বাগান থেকে ছিঁড়ে আনলাম একটি-কি-দুটি ঝিঙা।
তারপর তো ঝিঙাঝোল আর ভাত। তরিবৎ করে ঝিঙাদুটি চুলহার আগুনে ধুড়সে নিয়ে সামান্য নুন-লঙ্কা-তেল দিয়ে মা আমার চটকাত। চটকালেই পোড়া ঝিঙা রসস্থ হয় । তাই ঝিঙাঝোল।
মায়ের হাতের ঝিঙাঝোল আর ভাত! যেমন তেমন খাদ্য তো নয়, একেবারে ‘অম্রুতো’! এই পোড়োবাড়িটার অন্দরে ঝিঁজরির টানাটানি সত্ত্বেও খিদের জ্বালায় আর ঝিঙাঝোল-ভাতের কথা মনে পড়ায় জিভে জল এসে যাবে না আমার ?
তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্য জনপদের অলক্ষ্য জনমানুষদের উদ্দেশ্যেই তড়পে উঠে চিৎকার করে বলি, ‘এই যে খেতে দেওয়ার মুরোদ নাই কিল মারার গোঁসাইরা! তোমরা শুনছ কি ? আমার খিদে পেয়েছে, ভয়ানক খিদে! ঝিঁজরি টানছ, যত পারো টানো। তা বলে খেতে দেবে তো!
আমার চিৎকার-চেঁচামেচিতে ফের কতক বাদুড়া-চর্মচটকার ওড়াউড়ি শুরু হলো। পারাবতগুলোর ভদভদানি, কতক ডানা ফেটিয়ে বাইরে বেরিয়েও গেল। কিন্তু আমার কথায় শরীরী অশরীরী কেউই যেন কর্ণপাত করল না! যথা পূর্বং তথা পরং, ঝিঁজরি ঝিঁজরির মতোই চলতে লাগল।
‘মামনুসর’ বলে কাপালিক নবকুমারকে পশ্চাতে অনুসরণ করতে বললে, ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর নবকুমার নিমরাজি হয়েও পশ্চাদভাগে গমন করতে করতে বলেছিল, ‘প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন।’
নবকুমার তবু তো বলেছিল বটে। হায়, আমি তো ‘―সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে, ভীষণ-দর্শন মূর্তি’―তেমন কোনও কাপালিকেরও সন্ধান এ পর্যন্ত পেলাম না! ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবেদন অতঃপর কার কাছেই বা রাখব ?
অগত্যা ঝিঁজরির মন্থর টানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে খাদ্য না জুটুক, নানাবিধ খাদ্যের কথাই মনের ভিতর উপর্যুপরি আসতে লাগল ।
প্রথমেই আমাদের গ্রামের নিত্যানন্দ বেহেরার কথা মনে এল। তাঁর বয়স আশির উপরে হবে বৈ কম হবে না। গ্রামে কারওর বিবাহের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে কী শ্রাদ্ধশান্তির ‘আঁশপালনা’য় মৌখিক বা চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ থাক বা না থাক, নিত্যানন্দ কাঁশকুটের কানাভারী একটা গহীরা বাটি কী তাটিয়া সঙ্গে নিয়ে আগেভাগে উপস্থিত থাকবেই থাকবে।
পরিবেশনকারীরা হাতা ভরে এক অবর্ণনীয় দ্রুততার সঙ্গে মাংসের ঝোল-ব্যঞ্জন যাহোক তাহোক করে ভাতের উপরিভাগেই ঢেলে দিতে চাইলে দু হাত আড়াআড়ি পেতে মানা করবেই করবে নিত্যানন্দ। মাংসের জ্যুস-ব্যঞ্জন দিতে হয় দিক তারা তার নিজের ঘর থেকে আনা তাটিয়া বা বাটিতে। তা না হলে কব্জি ডুবিয়ে তরিবৎ করে ভোজ খাওয়া আর কাকে বলে!
মনে আসছে ভজহরির ছেলেটার ভোর ভোর পেট ভরে খাসি মাংস আর ভাত খাওয়ার কথা। একদিন হয়েছিল কি, চারদিকে পাতলা ফিনফিনে কুয়াশা। ঝুনঝুনি গাছগুলোর ডগায় ডগায় সপ সপে শিশিরজল। তার ভিতর দিয়ে, তার ভিতর দিয়ে আমাদের ভজহরির ছেলেটা দখিনসোলের সোঁতার দিকে এগুচ্ছে তো এগুচ্ছে।
ভালো করে সকাল হয়নি তখনও। ভজহরি ও তার পরিবার ঘুমোচ্ছে। দড়ি-টানা হাফ-পেন্টুল, গায়ে চারহাতি ময়লা চাদর। বয়স বড়জোর বছর আট, ভজহরির ছেলেটা।
দখিনসোলের সোঁতায় ন্যাড়াবিলে যত্রতত্র ডোবায় ঝিরঝিরে জল তখন। সে সময় হি-হি করা শীতে সোঁতার দিকে ছেলেটার হেঁটে যাবার হেতু অনুমান করা সহজ বৈকি।
কিন্তু না, হাফ-পেন্টুল ময়লা চাদর আচমকা বাঁক নিল দক্ষিণে। সে দেখতে পেয়েছে একটা কিছু। আনকোরা নতুন মেটে হাঁড়ির মুখে বসা কতক কাক ভদভদিয়ে উড়ে উঠল চারদিকে।
উড়ে উঠল বটে, তবে একেবারে ছেড়ে গেল না জায়গাটা। ঘুরে ঘুরে মাথার উপর উড়তে লাগল, ততক্ষণে ভজহরির ছেলেটা হাঁড়ির মুখ দেখছে উবু হয়ে। হাঁড়ির ভিতর ঝরঝরে শুকনো ভাত, হলুদ মশলামাখা খাসি মাংসের তরকারি!
আহ্লাদে স্তম্ভিত হয়ে গেল হাফ-পেন্টুল, খানিকক্ষণ মুখ হাঁ করেই থাকল ছেলেটা। তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে, ‘ হিঁ-ই-ই-ই বাবা! এত ভোরে এ-ত্ত মাংসভাত মাঠের মধ্যি কে রেখে গেল ? কে ? ?
ব্যস! বাবু হয়ে বসে ভজহরির ছেলেটা হাঁড়ির ভিতর ডানহাতটা সটান ঢুকিয়ে দিল। এতক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে আরও কাছে নেমে এল ক্ষুধাতুর কাকগুলোও। খাড়া খাড়া চুলে ভরতি হাফ-পেন্টুলের মাথাটায় খুবলে দেয় আর কী!
ওসব গ্রাহ্য করল না ও। পরম নিশ্চিন্তে ভোজনপর্ব সমাধা করল। সোঁতার দিকে যাওয়া আর হলো না, ভারী পেট নিয়ে ভজহরির ছেলেটা ফিরে আসছে।
ঘুম থেকে উঠে অ্যানামেলের ঘটিতে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিল ভজহরি, ধুয়ে পোস্তঢুলির জোগাড় দেখবে ভাবছিল।
ফলের বীজ থেকে পোস্ত, ফলের গায়ের আঠা থেকে আফিম আর শুকনো ফলের খোল জলে ফুটিয়ে পোস্তঢুলির রস! র-চায়ের মতো দেখতে, চিনিসহ সেবনে একপ্রকার ঢুলু ঢুলু নেশা হয়।
ভজহরি সেই নেশার তরে উনুনের ধার ঘেঁষে কুঁকড়ে বসে পড়ল। তখন জল আর পোস্তফলের খোল ফুটছিল বুগ বুগ করে উনুনে। ময়লা চাদর, হাফ-পেন্টুল―হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকল ভজহরির ছেলেটা।
ডানহাতের তর্জনী মুখে পুরে চুষতে চুষতে বলল, ‘বাপ, মাঠের মধ্যি এত ভোরে এ-ত্ত মাংসভাত কে রেখে গেল বল দেখি ?’
খানিক থম মেরে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল ভজহরি। তারপর বলল, কেন ? তুই কি খেয়েছিস ?
‘হুঁ-উম!’ ছেলেটার চোখদুটো আহ্লাদে বুজে এল।
ওদিকে ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে ভজহরি, পোস্তঢুলির নেশা টুটে গেছে তার।
‘হায়! হায়!! কী সব্বোনাশ করেছিস, হা-ঘরে হতচ্ছাড়া বাঁদর!’
কাকে খাচ্ছিল, না হয় সে খেয়েছে―এর মধ্যে অপরাধটা কোথায় ? বুঝতে না পেরে ছেলেটা কেঁদে ফেলল হুড়ুস করে।
তার কান্না দেখে বাপের চোখেও জল, কপাল চাপড়ে সে বলতে থাকল, ‘শেষে তুই কী না মরা মানুষের ভাত খেলি! হারু বেহেরার ‘আঁশপালনা’-র মাংসভাত কাল মাঠের মধ্যি দে গেছিল হারুর জন্য―আর তুই অভাগা খেয়ে ফেললি ?’
‘বাঁচবি না, আর তোকে বাঁচানো গেল না রে! এখন যে কী-ই ওষুধ দিই তোকে!’ আতঙ্কিত ভজহরি অস্থিরতায় ছটফট করল। মৃত হারু বেহেরার ‘আশপালনা’র দিন হারুকে উৎসর্গ করা ভাতমাংস এখন ছেলেটার পেটের ভিতর! মরা মানুষের ভাত জ্যান্ত মানুষের পেটে পড়লে মানুষ কি আর বাঁচে!
অতএব মরে যাবার ভাবনায় ভজহরির ছেলেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলে, ‘একটা কিছু অষুধ এনে তুই আমাকে দে বাপ!’
তার উত্তরে ভজহরি বলেছিল, ‘সার্থক ওঝার আখড়ায় চ শিগগির, দেরি করলে আর তোকে বাঁচানো যাবে নারে!’
বলেই দু চোখে জল ভজহরি ছেলেকে কাঁধে তুলে পড়ি-কি-মরি দৌড়েছিল সার্থক ওঝার আখড়ার দিকে।
ভজহরির ছেলেটার মৃত মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করা ‘আশপালনা’র মাংস-ভাত গোগ্রাসে গলাধঃকরণের দৃশ্যটা এ সময় ভারী মনে পড়ছে। রাখো তোমার ‘আঁশপালনা’র ছুঁৎমার্গতা! এখন হাতের কাছে তাই যদি পেতাম, আহা! আমিই কি আর ছেড়ে দিতাম ?
খাই খাই। ‘খাই খাই’ কবিতার কথাও মনে আতা-যাতা করছিল। ‘খাই খাই’ ॥ কবি সুকুমার রায় ॥ এই বলে জোড়হস্তে দণ্ডবৎ করে কবিতাটা কতই না আবৃত্তি করেছি ―
‘খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে ―
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যতকিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব,―থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যতকিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে ―
ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার ‘ঙাপ্পি’তে বাপ্ রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কিযে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।’
এত খাওয়া-খাওয়ির মধ্যেও একটা হাসির কথা এই ‘আবৃত্তি’র প্রসঙ্গে মনে এল! তখন আমাদের ফ্রি প্রাইমারির থ্রি-ফোরের ছাত্রছাত্রীরা ‘খাই খাই’-এর মতো লম্বা লম্বা কবিতাই আবৃত্তি করত।
শনিবার শনিবার ‘বড়দা’ অর্থাৎ হেডস্যার ইস্কুলে আবৃত্তি ধরত। ওয়ান-টুয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি না করলেও মন দিয়ে সেসব শুনত। আবৃত্তি শুনতে শুনতে তাদের চোখগুলি হয়ে উঠত বড় আর ড্যাবা ড্যাবা। অত্যধিক মনোযোগ হেতু অসাবধানতাবশত তাদের মুখ থেকে লালা ঝরত।
‘খাই খাই’-ই হচ্ছিল। শেষ হতে না হতেই ক্লাস টু-এর একটি ছেলে আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করল। আমরা থ্রি- ফোররা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আরে এ যে অ-ভ-য় চ- র-ণ! মোঃ চঁদর পুর। অর্থাৎ রামচন্দ্রপুর।
―‘কী ব্যাপার অভয় ? উঠে দাঁড়ালে যে ?’
বড়দার জিজ্ঞাসা।
অভয় হাত জোড় করে বলল, ‘একটা আবৃত্তি করব!’
বড়দা ভারী উল্লসিত হয়ে টেবিল চাপড়ে অভয়কে অভয় দিয়ে বললেন, ‘এই তো চাই-ই! ছোটদের মধ্য থেকেও উৎসাহিত হয়ে কেউ যদি আবৃত্তি করতে চায়’―বাঃ বেশ বেশ! অভয় শুরু করো!
প্রথমটায় অভয় থতমত খেল। তারপর শরীর মৃদুমন্দ দোলাতে দোলাতে রুদ্ধশ্বাসে বলে চলল―
‘অ থ অথ ক র কর চ র চর ধ ন অন
ই হ ইহ খ ল খল ছ ল ছল ন খ নখ
ঈ শ ঈশ গ ণ গণ জ ল জল ন ত নত
ঋ ণ ঋণ গ ত গত ত ট তট ―’
বড়দাও হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকলেন। অতঃপর চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘অভয়! থামো থামো! ওহে এ যে পদ্য নহে, গদ্য ―’
কিন্তু থামতে বললেই অভয় থামবে কেন ? সে যে শেষ পর্যন্ত বলে তবেই ছাড়বে―‘ ন র নর এ ক এক ঘ ন ঘন দ শ দশ প ট পট।’
থামল বটে অভয়। কিন্তু ততক্ষণে সারা ইস্কুলঘরে হাসির কলরোল আছড়ে পড়েছে। বড়দাও না হেসে থাকতে পারলেন না। এই পোড়োবাড়িটায়, সংঘারাম কী বৌদ্ধবিহারের ভগ্নস্তূপে একপেট খিদে নিয়ে আমিও মনে মনে হেসে একশেষ হলাম।
শ্রীশ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ তর্জমা করে যে ‘একশেষ, একের শেষ অর্থাৎ যাহাতে এক বিভক্তিস্বরূপ শব্দসমূহের একমাত্র শব্দ শেষ থাকে, অন্য শব্দ নিবৃত্ত হয়।’
১৫
ভাত, ভাত, ভাত। কবে কোন যুগ থেকে ভাত খেয়ে আসছি আমরা! আমাদের গ্রামের সাঁওতালরা অবশ্য ভাতকে ভাত বলে না, বলে ‘দাকা’ ।
একসময় কত সাঁওতালী ‘ঠার’ মুখস্থ করেছি! ভাত খা―‘দাকা জম্ মে’। আমি ভাত খেয়েছি―‘দাকা এং জম্ আকাদা। আমরা ভাত খেয়েছি―‘আলেদ দাকা লে জম্ আকাদা’।
প্রবাদ আছে―‘টাকা খান বৌহু, দাকা খান কৌহু’। মানে ? মানে হলো―ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কত রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইন সাঁওতালী করেছি! আজি ঝর ঝর মুখর―‘তেহেন ঝিপির ঝিপির জাপুট’। তুমি কোন কাননের ফুল―‘নাম দো নোকা বাগারেন বাহা’―
আজ ‘অর্গলা ভূত’-এর হাড়িকাঠের দিকে ঝিঁজরির টানে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি, তখনও এসব কথা মনে আসছে!
কী ব্রাহ্মণ্য যুগ, জৈন যুগ, বৌদ্ধ যুগ―সব যুগেই কৃষিকাজই ছিল প্রধান কাজ, ভাতই তো ছিল প্রধান খাদ্য। হাল-লাঙল-বলদ কৃষিকাজের প্রধান উপকরণ। সঙ্গে খনার বচন। এই যেমন―‘যদি বর্ষে মকরে। ধান ফলে টিকরে ॥’ ‘কার্তিকের ঊন জলে। দুনো ধান খনা বলে ॥’ ‘যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥’
তাছাড়া শিবই তো কৃষিকাজের দেবতা। আবার নিজেও একজন দরিদ্রতম চাষি। ‘কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন।’ একটাই গুণ আছে বটে―বড়ই অলস। স্ত্রী দুর্গা তাঁকে ঠেলে ঠেলে জমিতে নামান। পুকুরধারের জমিতে পঞ্চশস্য অর্থাৎ ধান, সরষে, তুলো, যব আর তিলের চাষ করান। কখনও কখনও সব্জি।
চর্যাপদেই তো আছে ‘ভাত’-এর কথা―
‘টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥’
গুহ্য অর্থ যা-ই হোক, সরল কথা তো এই―টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত থাকে না, প্রায়ই উপোস করতে হয়। এখানে ভাত না পাওয়া গেলেও অন্যত্র তরকারি বা ষোড়শ ব্যঞ্জনের ছড়াছড়ি―
‘ওগগরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খাই পুনবন্তা ॥’
রম্ভা বা কলাপাতায় ভাত, গাওয়া ঘি, দুধ, মৌরলা মাছ আর নালিতা শাকের তরকারি। স্ত্রী বেড়ে দিচ্ছে আর ভাগ্যবান স্বামী খাচ্ছে। এরকম দৃশ্যও তো দেখা গিয়েছে।
তাছাড়া শুধু মৌরলা মাছ, আরও যে কত কী!
‘রোহিত মাগুর পাবদা তপসী চিতল ।
ভেউস বাউস কই জিওল কাতল ॥
ইলিশা খলিশা বাইস গোলসা কোড়াল ।
চাঁদা বাচা চিংড়ি চেলা বাতাসি বোয়াল ॥’
হরিণের মাংস, ছাগের মাংস, গণ্ডারের মাংস, গো-মহিষাদির মাংস তো ছিলই। তদুপরি ময়ূর, কুক্কুট, নানাবিধ পাখির মাংস।
ভাত তো ভাত, একটু ফ্যানের জন্য এই তো সেদিন মানুষের কী হাহাকার! ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর। কলকাতার রাস্তায় ‘একটু ফ্যান দেবে গো’ ‘একটু ফ্যান দেবে গো’ বলে উপোসি মানুষের সে কী আর্তচিৎকার!
কলকাতা যেমন তেমন, দুর্ভিক্ষের কবল থেকে আমাদের মেদিনীপুরকে বাঁচাতে কাগজে কাগজে কি কম লেখালেখি হয়েছিল ? একটা কাগজের রিপোর্ট :
‘মেদিনীপুরকে বাঁচাইতে এক হও’
গতবছর মেদিনীপুর জেলায় ৫০ হাজার লোক অনাহার ও
মহামারীতে মরিয়াছে। তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া
মহিষাদল প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার লোকের একমাত্র
সম্বল ছিল লঙ্গরখানা। শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়া,
শতকরা ৩০ জন কলেরা ও বসন্তে এবং শতকরা ৬০ জন
রোগে ভুগিয়াছে। গত বছরের এই অবস্থা সামলাইয়া না
উঠিতেই আবার মেদিনীপুরে অনাহার দেখা দিয়াছে। বীজধান
ও বলদের অভাবে এবার ৩০ ভাগ আউসের জমিতে ফসল
হয় নাই। আমনধান যা হইয়াছিল, তারও অধিকাংশ মহাজনের
ঘরে। বর্তমানে শতকরা ১০ জন কৃষকের ঘরে ধান একেবারে
নাই। পাঁশকুড়া থানার ১৫ নং ইউনিয়নে একটি গ্রামে
১০০ ঘরের মধ্যে ৩৫ ঘরে কোনও খাবার নাই। কলাগাছিয়া
গ্রামে শতকরা ৫০ জন না খাইয়া আছে। শতকরা ৫০ জনের
বস্ত্র নাই। ইহার উপর বসন্ত, ম্যালেরিয়া আবার ছড়াইতেছে।
দুধের অভাবে শিশুমৃত্যু বাড়িতেছে।’
ভাত তো ভাত, এখন ভাতের ফ্যানটুকু হলেও মন্দ হতো না! বিড় বিড় করে যেন বললামও, ‘একটু ফ্যান দেবে গো!’ ‘একটু ফ্যান দেবে গো!’
কেউ শুনল না। কেউই না। এই ভগ্নপ্রায় গৃহে আছেটাই বা কে, যে আমার কথায় কর্ণপাত করবে! আছে তো কতক ঘর-ঘর কুলুঙ্গি, তায় মাথাভাঙা হাড়গোড়হীন কতক অবয়ব। মূর্তি বললে মূর্তি।
আর আছে―চর্মচটকা বাদুড়া―বাদুড় চামচিকা। কতক কবুতর পায়রা। আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে তারাই ‘কঁহরাচ্ছে’। মাঝে মাঝে ডানা ফেটিয়ে সাঁক করে উড়ে যাচ্ছে। ইতস্তত উড়ে-ঘুরে আবারও ফিরে আসছে।
তবু তো তারা আছে। আছে, আছে। নচেৎ পোড়োবাড়িটাকে আরওই হতকুচ্ছিৎ ‘মরা’ ‘মরা’ লাগত। মনে মনে ভাবতে না ভাবতেই পারাবতসকল ফের একবার ভদভদিয়ে উড়ে উঠল।
অতিরিক্ত ভদকানিতে গায়ে গায়ে ডানা ঝটপটানিতে একটা পায়রার পালক খসে ঘুরে ঘুরে নিচে পড়ল। নিচু হয়ে পালকটা কুড়িয়ে নিলাম। পালকই তো ?
হ্যাঁ, পায়রার পালকই বটে। তবে আকারে ঈষৎ ‘পুরুষ্ট’ ও বড়। এরকমটা কতই দেখেছি! কেননা, আমাদের মাটির বাড়ির ‘দাঁতিয়া’য় পায়রার বাসা বাঁধবার নিমিত্ত কত যে পোড়ামাটির হাঁড়ি টাঙানো থাকতো, এখনও আছে।
তাছাড়া, আমাদের মা-কাকিমারা এই পায়রার পালক দিয়েই তো তিলের তেল, দুধের ঘি নিষ্কাশন করে―সে এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়!
গ্রামের মাথায় জঙ্গলের ধারে ‘ডাহি’ জমিনে, এমনকি টাঁড়ে-টিকরে লাটকে-লাট ‘খসা’র চাষ হয়। খসা, যাকে বলে তিল। চৈত্র-বৈশাখে তিল বোনা হয় আর শ্রাবণ-ভাদ্রে সে তিলগাছে ফুল এসে যায়।
‘তিলফুল জিনি নাসা’―পুরাণ-মহাভারতে রমণীয় নাসিকাকে তিলফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শ্রাবণ-ভাদ্রে ডাহি-ডুংরিতে লাটকে-লাট তিলজমিনে যখন তিলফুল ফুটে ‘আলা’ হয়ে যায়, তার চারধারে কত যে রঙিন প্রজাপতি উড়েঘুরে বেড়ায়! প্রজাপতি তো নয়, আমরা বলি ‘পতনি’।
অবশেষে খসা বা তিল পেকে খসার বন হাওয়ায় ঝুন ঝুন করে। খসা কেটে খসা ঝাড়া হয়। আছড়ে পাছড়ে খসাকে ধুলাবালি মুক্ত করা হয়। তারপর তো শুরু হয় মা-কাকিমাদের হাতের কারসাজি―
বালির খোলায় ভাজো রে! জলে ধুয়ে খোসা ছাড়াও রে! কালো তিল খোসা ছাড়ালেই ধবধবে সাদা। অতঃপর তো গরম জলে ফেলে উসুম উসুম সেদ্ধ করা।
কথায় বলে না―‘তেলে-জলে মিশ খায় না ?’ সত্যিই তো, জল পড়ে থাকে নিচে, তেল জলের উপরিতলে ভাসে। তা তো কথার কথা শুধু নয়, পিছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।
জলে মিশে না কোনও তেল বা তরলের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপরই তেল বা তরলের ভেসে থাকা নির্ভর করে।
এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটা অঙ্কের কথা তো এখনই মনে পড়ছে―
একটি ট-নলে কিছু জল আছে। এক
বাহুতে জলের সঙ্গে মিশে না এমন একটি
তরল ঢালা হইল যাহাতে অন্য বাহুর জলতল
তরল স্তম্ভ ফ উচ্চতায় থাকে; কিন্তু প্রথম
বাহুর জলতল ইতিমধ্যে খ দূরত্বে নামিয়া
গিয়াছে। জল এবং তরলের ঘনত্ব ছ১ এবং
ছ২ হইলে প্রমাণ কর :
ছ২ ( ২খ +ফ )= ২ছ১খ
ডায়াগ্রামটাও এইরকম :
উরধমৎধস ভরম. ১
সে যা হোক, মা-কাকিমারা তো এসব কিছু বোঝেও না। তারা তাদের মতো সাময়িকভাবে উসুম উসুম জ্বাল দেওয়ার উনুনের পাশে পায়রার পালক হাতে নিয়ে বসে যায়।
তারপর তো ক্রমাগত উসুম উসুম ধোঁয়া-ওঠা পোড়ামাটির খোলায় পায়রার পালক চোবানো আর তেলে ভেজা সপসপে পালক হাত মসকে গাড়ু বা তৈলাধারে নিঙড়ানো!
ভারী একঘেয়ে তৈল কী ঘি নিষ্কাশন পদ্ধতি! একঘেঁয়ে বলতে একঘেয়ে, কতদিন দেখেছি মা-কাকিমারা উনুনের ধারে বসে পালক নিঙড়াতে নিঙড়াতে তন্দ্রাবশত ঢুলছে।
ঘিয়ের পালক হলে তো কথাই নেই, আমাদের পোষা বিড়াল জানকী কী সারদা ঘুমন্ত মা-কাকিমাদের হাত ফসকে পড়ে যাওয়া ঘিয়ে ভেজা পালকটা চেটেপুটে দেখত―ঘিয়ে ঠিকঠাক পাক ধরেছে কীনা!
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীর আফিংখোর মার্জার হলে আরও এককাঠি উপরে উঠে গাড়ুর সবটুকু ঘৃত নিঃশেষ করে গোঁফ মুচড়ে উদগার তুলে হয়তো মন্তব্য করত, ‘কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।’ আর নয়তো, ‘উর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি।’
পালকটা হাতে পেয়ে যেমন যেমন মা-কাকিমাদের তৈল ও ঘি নিষ্কাশনের কথা এল, তেমন তেমন এই হা-অন্ন হা-অন্ন সময়ে ‘পালক’ নিয়ে একটা ‘পদ্য’র কথাও মনে এল।
চেঁচিয়ে তাই মুখস্থ বলতে লাগলাম―
‘কী একটা পালক খুঁজতে খুঁজতে লোকটা এদিক দিয়ে চলে গেল
তার চরণচিহ্ন ছায়ায় পড়ে না, চরণচিহ্ন মাটিতে পড়ে না
সে নিশ্চিহ্ন হেঁটে গেল
সূর্যের সব আলো তাকে ঝলসে দগ্ধাতে পারল না
পৃথিবীর সব ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সমুদ্র ধোয়াবে পা
অরণ্যে একটাও দেবদারু না জন্মালে আকাশ দেবে ছায়া
ছায়া বরফের মতো মৃত্যুর মতো দূর থেকে আর্দ্র হয়ে আসে―
এ তথ্য সে জেনে গেছে, জেনে চলে গেছে
পালক সন্ধানে
কী একটা পালক সে রোজ খোঁজে, রোজ, সারাক্ষণ’
চেঁচালাম, জোরসে চেঁচালাম! কিন্তু কেউই তা শুনল না। অগত্যা পায়রার পালকটাকে নিশান করে যাহোক তাহোক ভাবে মেঝেয় পুঁতে রেখে এখানেই গ্যাঁট হয়ে ‘অনশন’-এ বসে পড়লাম।
যতই টানো, মারো ধরো, অদৃশ্য ঝিঁজরির কসরত-কেরামতি দেখাও―
খেতে না দিলে আর এক পা-ও নড়ছি না! এক চুলও না!
ততক্ষণে মধ্যাহ্ন সূর্যও পশ্চিমে হেলে পড়েছে। পুষ্করিণীর জলে তার ছায়াবিম্ব, সূর্যের আলো জলে বিলি কাটছে।
বাঁদিকে আরেকটা কুঠরিঘর, কে জানে কত নম্বর! কী যেন অস্পষ্ট লেখাও রয়েছে! একশত ছয় কী ? একশত ছয়কে সংস্কৃততে বলে, ‘ষড়ধিকং শতম্’ আর পালিতে ? আ
পালিতে তো শতকিয়াকে এইরকমই বলে―‘পঠমো’ ‘দুতিযো’ ‘ততিযো’―
‘পঠমো বগগো’ ‘দুতিযো বগগো’ ‘তিতিযো বগগো’―
আচমকা কানে এল, কে যেন বিড়বিড় করে বলছে―
‘ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥’
‘কে ? কে বলল এ কথা ?’ অনশনে বসে আমার মুখ দিয়েই কি উচ্চারিত হলো এ কথা ? ‘এখানে এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, আমার চামড়া, হাড় ও মাংস ক্ষয় হোক, আমি ‘বুদ্ধত্ব’ লাভ না করে উঠছি না!’
কিন্তু না। আমার কথা কেন হবে, এ কথা তো নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষের নিচেয় যোগাসনে বসে বোধিলাভের আশায় সিদ্ধার্থই বলেছিলেন।
এখন এই তো আবারও শুনলাম―‘দ্বিতীয় প্রহরবেলা অতীত হইলে আহার করিবে, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন অনুচিৎ, রৌপ্য ও সুবর্ণ গ্রহণ নিষিদ্ধ।’
‘কে ? কে ?’ প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। চারধার তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কেউ থাকলে তো উত্তর দেবে ? কেউই নেই। কেউই নেই। কিছুক্ষণ পরেই নধর-গতর একটা টিকটিকি, যাকে আমরা বলি ‘ক্যাঁকলাস’, কুঠরিঘর থেকে ধীরে-সুস্থে নির্গত হলো।
দ্বারকক্ষে পেট-তাবুড় দিয়ে কয়েক পলক আমারই দিকে নেত্রপাত করে তার তাবড় মাথাটা বারকতক নাড়ল। তারপর আমারই পাশ দিয়ে আমাকে গ্রাহ্য না করে দ্রুতগতিতে কোথায় হারিয়ে গেল।
ডানা ফেটিয়ে পায়রাগুলো এ সময় আবারও ফিরে আসছে ―ওই তো, ওই!
১৬
তবে কি এই ‘এক শত ছয়’ নম্বর কক্ষেই আমার গতি হলো ? আপাতত অবস্থা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আর কেউ ঝিঁজরি ধরে টানাটানিও করছে না। পা দুটোয় হাত বুলিয়ে দেখছি―আহা রে! অদৃশ্য ঝিঁজরির রজ্জুবন্ধনের ছাপছোপ আর বুঝি লেশমাত্র নেই!
এখন আমি―মুক্ত , মুক্ত, মুক্ত―
ঈষৎ ঝুঁকে ঘাড় গলিয়ে কক্ষের ভিতরের পরিসর মাপছি আর দেখি কি―ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে! তার মানে মুক্ত নই আমি, ফের বন্দি হলাম কক্ষের অন্দরেই।
রাগ, স্বাভাবিক কারণেই রাগ হলো, ভয়ানক রাগ। খিদের জ্বালায় এমনিতেই রাগে জ্বলছিলাম। তার উপর আচমকা দড়াম করে ঝাঁপ বন্ধ হলো। রাগও বেড়ে দাঁড়াল দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ!
দমাদ্দম! দমাদ্দম! দরজায় লাথি কষালাম একের পর এক। দরজা এই ভাঙে কি সেই ভাঙে! তবু কারও কোনও ভ্রƒক্ষেপই নেই। কেউ আছে যে দৌড়ে এসে মানা করবে ? আরে, কেউ যদি না-ই থাকে তবে দরজা বন্ধ করলই বা কে ?
তাহলে কি, যা কিছু ঘটে চলেছে সবটাই সেই ‘ইনভিজিবল’ হাতের কাজ ? তারই হাতেরই কারসাজি ? যে আমাকে নিশুতি রাতে ঝিঁজরির টানে ঘর থেকে টেনে এনেছে মশানির দহে নিশির টানের মতো, রাতভর দহের জলে ডুবিয়ে রেখেছে, তারপর তো গো-শকটে এতদূর―
তাছাড়া আশপাশ, চতুর্পাশ দেখে তো মনে হয় না কোথাও উল্টাপাল্টা অঘটন কিছু ঘটে চলেছে। অগত্যা রুদ্ধদ্বার কক্ষের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঝুরকায় খানিক চোখ রাখলাম।
অপরাহ্ণের আলো এসে গৃহের অভ্যন্তরে ইকিড় মিকিড় খেলা খেলছে। আর সে-আলোয় দেখা যাচ্ছে―পোঁটলায় বাঁধা কতক কাপড়চোপড় ঘরের এক কোণে স্তূপীকৃত করে রাখা আছে।
এসব বস্ত্রাদি, কাপড়চোপড়, তোষক-বিছানা কার ? মনে মনে ভাবলাম―কার আবার ? কক্ষের যে হকদার, তার। হয়তো সে কোথাও কাজে গিয়েছে। সন্ধ্যা হব হব সময়ে কী সন্ধ্যা উত্তীর্ণকালে বাসায় ফিরবে।
এসেই কর্মক্লান্ত শরীরে বিছানা পেতে একটু গড়িয়ে নেবে হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। উঠেই হাত-মুখ ধুয়ে আসবে পুষ্করিণীর জলে, চাই কি পুষ্করিণীর জলে ঝপাং করে একডুব-দুইডুব-তিনডুবও দিয়ে আসবে।
কিন্তু, তারপর ? তারপর ? তারপর তো খাওয়া ? কী খাবে ? ধারেকাছে কোথাও কি কোনও পান্থশালা, আহারাগার, হোটেলমোটেল আছে ? যৌথপাক কি রন্ধনশালা ?
যৌথ রন্ধনশালার কথায় মনে পড়ল আমাদের ইস্কুল হোস্টেলের রাঁধুনি টুনিঠাকুরের কথা। টুনিঠাকুর আদতে শ্রীনবকুমার চক্রবর্তী। মোকাম শ্রীশ্রী-রামেশ্বরজীউর মন্দির সংলগ্ন দেউলবাড় গ্রাম।
হোস্টেলে প্রায় দুই শতাধিক বোর্ডার। তাদের দিবারাত্র কলরোল কল-নিনাদে মাটির দেয়াল টিনের ছাউনি তিনতলা বাড়ি অষ্টপ্রহর গমগম করে। তারা যখন উচ্চৈঃস্বরে ভূগোল-ইতিহাস-ইংরাজি-বাংলা, ইত্যাদি পাঠ মুখস্থ করে, তখন যেন ‘কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুলকুল’ বা, সহস্রাধিক পায়রা-পারাবতের বকমবকম ডাককেও হার মানায়।
কিন্তু ওই তারাই আবার আহারের ঘণ্টা পড়লে স্ব স্ব কাঁসকুটের থালা, এনামেলের বাসন হাতে টুনিঠাকুরের তথা ইস্কুল হোস্টেলের সুবৃহৎ রন্ধনশালার সমুখে দণ্ডায়মান হলে, দাপুটে রসুইকরের উচ্চবাচ্যে তাদের গলায় আর স্বর ফোটে না!
কী আর তরকারি ? ওই বড়জোর কাঁকুড়ের ছ্যাঁচড়া, ভেঁড়ী কি বৈতালের ঘণ্টা। তবে হ্যাঁ, কাঁচা লাউয়ের শাঁস বেমালুম বাদ দিয়ে কেবল তার চোপা নিয়েই যে ‘লাউয়ের চুপি’র রেসিপি―তার তুলনা ভূ-ভারতে নেই।
কাজে কাজেই রন্ধনশালা যেমনটা বড়, আড়ে-বহরে পঞ্চাশ বাই একশো কি সওয়া শো ফুট, তেমনি পাঁচ-ফুটিয়া শ্রীনবকুমার চক্রবর্তীর হাইটও বড় কম নয়!
ছেঁড়া কাঁথা, তোষক-বিছানার মালিক যেই হোক, আপাতত তাই পেতে খানিক গড়িয়ে নিলাম। ঝুরকা দিয়ে অপরাহ্ণিক সূর্যের রোমাঞ্চকর আলো গায়ে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।
একপেট খিদে সত্ত্বেও ঘুম এসে যাচ্ছিল অচিরেই। ঘুমই তো! সেই ‘আয় ঘুম যায় ঘুম বাগদীপাড়া দিয়ে। বাগদীদের ছেলে ঘুমোলো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।’
আমাদের গ্রামের পাশেই বড়ডাঙা গ্রামে কয়েকঘর বাগদী বসতি আছে। তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উদারডাঙায় কত লাল-নীল-হলুদ কাচের গুলি খেলেছি! বাঈধর নামের ছেলেটার হাতের টিপ ছিল এককথায় অসাধারণ! প্রায় সবগুলিই সে একাই জিতে নিত।
সে নিক। তা বলে তাদের পাড়াতেই ঘুমের এত আতা-যাতা কেন ? কই, কেউ তো কখনও বলে না বামুনপাড়া, কায়স্থপাড়ার কথা! নিদেনপক্ষে সদগোপ কি মহাজনপাড়ার কথা! তবে কি একটা কিছু ষড়যন্ত্র আছে ঘুম পাড়িয়ে রাখার বাগদীদের ?
হবেও বা। যা হোক ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন কোথাও একটা বাজনা বেজে উঠল। সেই একটানা পূজার ঘণ্টাধ্বনি। জলের তলায় কতবার যে শুনেছি!
কিন্তু এ যে বলিদানের ঢাকের বাদ্যি! ‘ড্যাং ড্যাং ড্যা ড্যাং ড্যাং!’ আমাদের গ্রামের ‘গরাম থান’-এ গরাম পূজায় কি ‘শীতলা থান’-এ শীতলা পূজায় পাঁঠা বলিদানের প্রাক্কালে এমনটা হামেশাই বাজতে শুনেছি।
বলিদানের আগে নিরীহ গোবেচারী ছাগ খুঁটোয় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও জিভ লম্বিত করে মুখের কাছে জড়ো করা বট-অশ্বত্থের পাতা, চিরোল চিরোল শালপাতা, মনের সুখে চিবোয়, চিবোতে থাকে।
সে তো আর জানে না এই জীবনে এই তার শেষ খাওয়া! শেষ আহার। এমনকি বলিদার যখন গলার রজ্জু ধরে সজোরে টানতে টানতে নিয়ে যায় হাড়িকাঠের দিকে, সে তখনও বিপরীত পার্শ্বে ঘাড় বেঁকিয়ে লকলকে জিভ আরওই লম্বা করে শেষ পাতাটুকুও খাবলে খেতে চায়।
তার পিছনের পা দুটো টেনে ধরে, ঘাড় যতটা পারা যায় লম্বা করে অর্গলে পুরে যখন হাড়িকাঠের আংটা খড়াং করে আটকে দেয়, তখনও ছাগ ঘুণাক্ষরেও টের পায় না লোকগুলো তাকে নিয়ে কী করতে চায়।
এমনকি খাঁড়াটা গলার উপর ঝপাং করে এসে পড়ার আগ-মুহূর্তেও সে তার কানদুটি ঝটপট করে, চোখদুটো গুলির মতো বড় করে তোলে, গলাটা কোন ক্রমে টেনেটুনে ছাড়িয়ে নিয়ে পাতা খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে, জিভটাও কিঞ্চিৎ বেরিয়ে আসে।
সেই ‘ড্যাং ড্যাং ড্যা-ড্যাং ড্যাং’ বলিদানের বাজনাটা অনর্গল বেজে চলেছে, বেজেই চলেছে। বলি কি হয়ে গেল ? না, হতে চলেছে ? ছাগবলি না নরবলি ?
যদিও ধারণা করা হচ্ছিল মন্ত্রযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী কী হীনযানী বৌদ্ধদেরই আবাসস্থল এই পোড়োগৃহটি, তাঁরাই উৎসবাদিতে মেতে উঠে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে ঢাকঢোল বাজাচ্ছে, কিন্তু অদ্যাবধি চর্মচক্ষে একটাও তো লোক দেখি না। অথচ মনে তো হচ্ছে―আছে, আছে। সবকিছুই আছে।
বিছানায় যে শুয়েছিল, এই উঠে চলে গিয়েছে, তার শরীরের ওম যেন এখনও লেগে রয়েছে!
ষোড়শ প্রচারে পূজা বোধকরি এতক্ষণে শেষ হলো। বাজনার ‘কাঁই না না’ ‘কাঁই না না’ শব্দধ্বনিও আর শোনা যাচ্ছে না। এক্ষণে পূজা শেষে হয়তো প্রসাদ বিতরণের পালাও শুরু হয়েছে।
প্রসাদের কথায় হুদ হুদ করে মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রামের হরিমন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায়, তৎসহ অন্যান্য উৎসবাদিতে ‘চিড়া-ভোগ’ প্রস্তুতিকরণের কথা।
পূর্বদিগন্ত আলোয় আলোময় করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, মৃদঙ্গে চাঁটি পড়েছে―‘ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা ॥ না তিন তিন তা। তেটে ধিন ধিন ধা ॥’
অমনি ঘর-ঘর ঝকঝকে কাঁসার থালায় ধবধবে চিঁড়া, গুড়, বাতাসা, দুধ, নারকেল, পাকারম্ভাসহ নানাবিধ পূজা-উপাচার এসে গেল। সঙ্গে গুলাজ ফুলের মালা, জ্বলন্ত প্রদীপ!
জলদে কীর্তন চলত খোল-করতাল-কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে― ‘ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ ॥’
পুরোহিত নারায়ণ দাশঠাকুর উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্যের এক-তৃতীয়াংশ নিজের গাঁটরিতে বেঁধে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ পিতলের বড় হাঁড়ায় তাহুত করে মেখে ভোগ তৈরি করতেন। চিঁড়া-ভোগের গন্ধে তখন চারধার ম ম করে উঠত।
কীর্তনেও ‘ভরা’ উঠত―‘হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥’ মৃদঙ্গে বোল ফুটত―‘ঝে নে ঝা গে না তে নে তা খি টি। ঝা ঝিনি ঝা ঝা ঝা খিটি তা খি তা―’
অতঃপর শুরু হতো প্রসাদ বিতরণ। মুঠো মুঠো চিঁড়া-ভোগ―আহ্! পাকা-রম্ভা-গুড়-দুধে মাখামাখি সে-চিঁড়া, চিঁড়া তো নয়, ‘অম্রুতো’! তার উপরে গোঁজা থাকত আস্ত পাঁচ-দশটা বাতাসা!
শুধু কী চিড়া-ভোগ, পৌষসংক্রান্তি অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির সকালে হরিমন্দির বা হরিবাসরে পূজাশেষে বিতরণ করা হত ‘মকরভোগ’। আতপচাল, গুড়, দুধ, নারকেল, রাঙাআলু আর ছাল-ছাড়ানো-আখের টুকরো। ছোটরা খেত বলে বাদ দেওয়া হত ভাঙ বা সিদ্ধি।
সেই ‘চিঁড়া-ভোগ’ ‘মকরভোগ’-এর গন্ধ যেন এই খিদের মুখে ‘মহকে’ উঠছে নাকে! ‘ছ্যা-অ্যাং ছ্যাং-চ্যাং’ করে এরা কি শুধু পূজাচারের নামে খোল-কত্তালই বাজাবে ? চিড়াভোগ, মকরভোগ,―কোনও ভোগই কি দেবে না ?
বৈদিক পূজার্চনার চল ছিল, এখনও আছে। তাবলে বৌদ্ধদেরও কি ‘দেবপূজা’র প্রচলন আছে ? না বোধহয়। বুদ্ধই তাঁদের দেবতা। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব। ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি―ধর্মং শরণং গচ্ছামি―সংঘং শরণং গচ্ছামি―’
তবে যে ঢাক-ঢোল-বাদ্য ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাও একসময় বেজেছিল বটে―ওই যখন তাঁদের মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্র এসে পড়ল। খড়্গহস্তা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা বজ্রহস্তা, ডাকিনী-পযাগিনী, ইত্যাদির পূজার্চনা শুরু হলো। পাঁঠাবলি, এমনকি নরবলিও হতে লাগল।
একটু আগে―জানি, জানি―যে বাদ্যধ্বনি আমার কর্ণকুহরে শ্রুতিগোচর হচ্ছিল―তা তাঁদেরই । তাঁদেরই। ‘চিঁড়াভোগ’ ‘মকরভোগ’ ‘ক্ষীরিভোগ’―তাঁরা আর পাবেন কোথায়!
রাগে, দুঃখে ও অভিমানে বিছানায় ফের গড়িয়ে পড়লাম। বেলা আড় হয়ে গেছে সেই কখন! এখনও আহারের সংস্থান হলো না!
ভিক্ষুরা নাকি একাহারী। সারা দিন ভিক্ষা করে খায়! সারা দিন ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হয়, ‘পর্যোহ্নে’ তাই নাকি একত্রে রান্না করে খায়! ‘মাগন’ থেকে এখনও কি কেউ ফিরল না!
এঁরা কোন ভিক্ষু ? গৃহী ভিক্ষু না জাত ভিক্ষু ? শুনেছি একশ্রেণির ভিক্ষুরা নাকি গুহ্যসিদ্ধির জন্য মাছ-মাংস-মদ সবই খান―‘হস্তীমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্―’
আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো―এই পোড়োগৃহ, পরিত্যক্ত আবাসন―তাঁদের, তাঁদেরই। সেই সমস্ত ভূতপ্রেতের উপাসকদের। যাঁদের পাল্লায় পড়ে আজ আমি পর্যুদস্ত ও নাস্তানাবুদ হচ্ছি। এখন আর রাগ নয়, কেমন যেন একটা অসহায়তা―তবু, তবু বলব রোমাঞ্চকর বোধ হচ্ছে―দেখিই না, দেখি―কী হয়―পার্শ্বস্থিত পুষ্করিণীর জলেও এতক্ষণে অপরাহ্ণের রং ধরেছে। রাঙা রৌদ্রের মলিন ছায়া নেমেছে জলে। জল ক্রমে বাতাসে তরঙ্গায়িত হতে হতে আলোড়ন পরিশেষে কিনারায় মৃদুমন্দ শব্দে উপর্যুপরি আছড়ে পড়ছে।
ছোট ছোট পাখি-জলপিপি-কাদাখোঁচা-পানকৌটি-ডাহুক- ফুটকি মাছরাঙারা―পুষ্করিণীর ধারে ধারে অগভীর ঝাঁজি-জলে যাহোক তাহোক করে ডানা ফেটিয়ে গা ধুচ্ছে। অবগাহন শেষে পরিপাটি হয়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার আগে আগেই ঝোপে ঝাড়ে তাদের বাসায় ঢুকবে।
বাসায় ঢোকার আগ-মুহূর্তে বাসার মুখে উড়েঘুরে তারা ডাকতে থাকবে মুহুর্মুহু, যেন বা ‘ধর্মের ডাক’ দেবে―‘কেউ যদি বহিরাগত বা শত্রুপক্ষের লোক আমার বাসায় ঢুকে থাকো, আমি ‘চেতাবনী’ দিচ্ছি―তুমি বেরিয়ে এসো!’
পাখপাখালির বাসায় সাপখোপ তো হামেশাই ঢুকে থাকে! পাখিদের চিল-চিৎকারে হয়তো বেরিয়েও আসে। পাখির ডাকের সেই ‘চেতাবনী’ এই কক্ষের একশো ছয়তম ঘরে শুয়ে থেকেও শুনতে পাচ্ছি।
তবে কি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এল ? ‘পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল ॥’ কিংবা, ‘পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে জেগে।’ সন্ধ্যায়-প্রভাতে―ওই দুবারই! পাখির ডাকে ফুলও ফোটে।
আমাদের খলা-খামারের ধারে খেতিবাড়িতে তো বেলা থাকতে থাকতেই ঝিঙামাচানে রদোবদো করে স-ব ঝিঙাফুল ফুটে যায়!
এই পোড়ো গৃহের খেতিবাড়িতে লাউমাচান কি ঝিঙামাচান নেই ? সেখানে ভোরে কি সাঁঝবেলায় রদোবদো করে লাউফুল কী ঝিঙাফুল ফোটে না ? পাখি তো আছেই। ওই তো ওই―
পারাবতগুলো গলা ফুলিয়ে ‘কঁহরাচ্ছে’! তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ডাক তো নয়, যেন টুলো পণ্ডিতের পাঠশালায় ‘ব্যাকরণ কৌমুদি’র ধাতুরূপ শব্দরূপ মুখস্থ করছে!
মনে হয় একটা পারাবত অধ্যাপকসুলভ গমগমে গলায় শিক্ষা দিচ্ছে―‘ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সর্ব-মত্যন্তগর্হিতম্। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ ।’
কে যেন দরজায় করাঘাত করল। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম―
‘কে ? কে-এ-এ-এ ?’
কোনও উত্তর এল না। আর কোনও করাঘাতও শোনা গেল না। তবে অনুমান হলো―এই পোড়োগৃহ যদি সংঘই হয়, তাহলে মাধুকরী থেকে ভিক্ষুদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল বুঝি সমুপস্থিত!
যে কক্ষে আমার আপাতত অবস্থান, যার বিছানায় সাময়িক শুয়ে আছি, অনাহারক্লিষ্ট শরীরেও সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অপরাহ্ণ শেষের আমেজটুকু উপভোগ করছি―সেই কি দরজায় করাঘাত করেছিল ?
হবেও বা। তার লণ্ডভণ্ড বিছানার দিকে চোখ রাখলাম। খাটিয়া-তক্তপোষ―কিছুই নেই। মেঝেতেই খেজুরপাতার পাটিয়া বা চাটাই পাতা। কোথায় যেন পড়েছিলাম―
‘অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্।
শালপত্রে চ ভোজনম্ ॥
শয়নম্ খর্জ্জুরী পত্রে।
ঝাড়খণ্ডৌ বিধিয়তে ॥’
অর্থাৎ, মাটির ভাঁড়ে জল পান করা, শালের পাতায় খাওয়া, খেজুরপাতার পাটিয়াতে শোওয়া―এই ছিল ঝারিখণ্ডবাসীদের বিধিলিপি। তবে কি এই অঞ্চল ঝারিখণ্ডের ? না, কজঙ্গল-দণ্ডভুক্তির ?
বৈষ্ণব শাস্ত্রকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন―
‘মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥’
ঝারিখণ্ড ―‘অরণ্য পর্বতাবৃতং দেশং ঝারিখণ্ভ খ্যাতং।’ প্রাচীন কালের রাঢ়া বা লাঢ়া, রাঢ়ভূমি। রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গলভূমি। আলেকজান্ডারের সময়কালের গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারাঢ়। আর অশোকের অটবীরাজ্য। পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল। ধর্ম প্রচারের জন্য এখানেই এসেছিলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব ও শ্রী-চৈতন্য।
একটা লোকায়ত গানেই আছে―‘খেজুর-মেজুর খাঞে বুড়ীর পেট ফাঁপিল’। সত্যি সত্যিই এ তল্লাটে বুনো খেজুরগাছের আধিক্য। প্রায় ঘরে ঘরেই খেজুরপাতার পাটিয়া। এখানেও একটা ছেঁড়াখোঁড়া পাটিয়া দেখলাম। তবে, গদি-তোষক-বালিশ-পাশবালিশের চিহ্নমাত্র নেই। কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথা অবশ্য আছে।
ভিক্ষুদের ব্যবহৃত কষানো বা ছাপানো রক্তরঙা ধুতি-চাদর তো নেই ?―নেই, নেই―
কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘোরতর সন্দেহ! পোড়োবাড়িটা― যার মধ্যে ঈষৎ স্থূলকায়া পারাবতগুলো সংস্কৃত টোল খুলে বসেছিল, ‘কঁহরাচ্ছিল’―আছে তো ঠিক ? আছে তো ?
কিছুক্ষণ আগে পুষ্করিণী তটে যে সমস্ত স্নানরতা পাখিদের হর্ষোৎফুল্ল কলরব শোনা যাচ্ছিল―তারা বাসায় ঠিকঠাক ফিরল কি ?
যে গো-শকট একটা আস্ত গ্রাম পরিক্রমা শেষে―যে গ্রামটির অবস্থিতি মনে হচ্ছিল নিম্নশায়ী জলাভূমিতে, যার একধারে অনেকগুলি নৌযোগ, নৌঘাট, যে ঘাটে ছোট-বড় নৌকো বাঁধা, যে গ্রামের নাম হলেও হতে পারে ‘বলিকন্দর’ ‘বাল্লহিটঠা’ ‘ব্যাঘ্রতটী’ ‘খেদিবল্লী’ ‘কন্তেড়দক’ ‘নাদভদক’ ‘কুক্কুট’ কী ‘বিলকীন্দক’―সেই গ্রাম, সেই গো-শকট, সেই মহেঞ্জদাড়োর ষাঁড়―সত্যি সত্যিই ছিল তো ?
সবকিছুই কেমন যেন মরা মরা, পাংশুটে ভাব।
অকস্মাৎ দেখি―দরজাটা ঈষৎ নড়ে উঠল। যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক হলো। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে একে একে ঢুকে এল―শালপাতার থালায় ‘চিঁড়াভোগ’―‘মকরভোগ’―মাটির গাড়ুতে জল―
১৭
শুধুই কি শালপাতায় চিঁড়াভোগ, মকরভোগ আর মাটির পাত্রে জলপান ? না, এ তো গেল ঠাকুরপূজার প্রসাদ। ‘প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ―’
সিদ্ধিপ্রসাদ, ক্ষীর, মালা, প্রসাদান্ন, গুরুর ভুক্তাবশেষ, ইত্যাদি। ‘যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া―’। তারপরই তো মহাভক্ষণ!
আহা! কী-ই না খেলাম! ভাত তো ভাত, ‘কুড়কুড়িয়া’ ছাতুর তরকারি, ‘বাঁশকরোল’-এর মাংস, মায় মিহিদানার মতো কাঁচা কাঁকড়ার ডিম আর পোস্ত-পোড়ার মতো ‘কুরকুট-পোড়া’―
সেই যে ডিমওয়ালা লাল লাল ডেঁয়ো-পিঁপড়ে! সাদা ভাতের মতো ডিম। নোড়া দিয়ে শিলে বেঁটে সামান্য নুন মাখিয়ে পোস্তপোড়ার মতো কাঁচা শাল-পাতায় মুড়ে আগুনে ‘ধুড়সে’ নেওয়া!
বাংলাভাষার খবরের কাগজগুলো তো হামেশাই খবর পরিবেশন করে :
‘মেদিনীপুরের অনাহারক্লিষ্ট লোধারা
পিঁপড়ের ডিম ভক্ষণ করিয়া উদর―
পূর্তি করে।’
বাবু রে! বনে-ঝাড়ে ‘কুরকুট-পটম’ অর্থাৎ ডিমওয়ালা লাল লাল ডেঁয়ো পিঁপড়ের পোঁটলা দেখলে আমাদেরও জিভে জল আসে যে!
তা বলে এই পোড়োগৃহের, ‘লা সিট্টা ইনভিজিবিলি’, অলক্ষ্য জনপদের মানুষজনও এই সমস্ত আহার্য খায় নাকি ? খায় খায়, নচেৎ সংগ্রহ করল কী করে! নাকি আমাকেই তুষ্ট করতে!
যাঁদের কথা ভাবছি, তাঁরা যদি এঁরাই হন, তবে তো তাঁদের ‘সংঘ-ভোজন’ও আছে। আমাকে তাহলে একা একা নিরালায় বসিয়ে এত সব আহার্য খেতে দিলেনই বা কেন ?
ভিন্ন জাতগোত্রের, তদুপরি আগন্তুক বলে ? নাকি ‘দ্বিজত্ব’-এর মতো এখনও গোত্রান্তর হয়নি, তাই ?
শুনেছি, সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ির উপর উবু হয়ে বসে তাঁরা খান। দুটো পিঁড়ি, অর্থাৎ দুজনের মাঝখানে অন্তত একফুট জায়গা ফাঁকা থাকে। তা বলে ব্রাহ্মণদের মতো ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। পঙক্তি ভোজন হলেও যার পাতে যখন যেমন পড়ে, তাই তাঁরা হাপুস হুপুস শুরু করে দেন খেতে।
একবার তো নাকি প্রায় তের হাজার ‘পাত’ পড়েছিল একসঙ্গে! তখন আর সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ি কোথায়! চাদর বিছিয়ে খাওয়া! একসুতোও ফাঁক নেই, চাদরের উপর চাদর―এ যেন সেই এক ‘আরব্য উপন্যাস’-এর ‘গালিচা’!
―‘গালিচাটা এমন ত কিছু বেশি সুন্দর
নয় যে, ত্রিশহাজার টাকা দাম হাঁকছ ?’
ফেরিওয়ালা হোসেনকে বণিক মনে করিয়া
বলিল, ‘মশাই এই দামটাই অসম্ভব বোধ
হচ্ছে ? তাহলে একথা শুনলে না-জানি কি
বলবেন যে নগদ ত্রিশহাজার টাকা হাতে না
পেয়ে গালিচা ছাড়া বারণ!’
হোসেন বলিলেন, ‘তবে নিশ্চয় এর কোনও
গুপ্ত গুণ আছে।’
ফেরিওয়ালা বলিল, ‘আপনি ঠিক ধরেছেন
ত! এ গালিচায় বসে যে যেখানে যেতে চায়
তখনি সেখানে যেতে পারে।’
সেই চাদরটাও যেন তাই। ভাত তরকারি পরোটা লুচি―মূলা সিদ্ধ, ডাল―চাদরে একের পর এক পড়ছে তো পড়ছেই। আর তাঁরা খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। ছোঁয়াছুঁয়ি নেই, আগে পড়া পিছে পড়ার বাছ-বিচারও নেই।
শুধু কী খাদ্য, চাদরে উড়ে এসে জুড়ে বসছিল―ট্যাঁকের কড়ি, এলাচ, লবঙ্গ, চাল, সুপারি। খাদ্য তো জুটলই, সঙ্গে আবার জুটল চাদর-গোটানো কিছু নগদানগদি, যজমানদের দেওয়া দানসামগ্রী!
যা হোক, অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো। বাইরের আলো নিভে এল। শুধু দিকচক্রবালে অস্তগামী সূর্যের লাল আভাটুকু মন্দের ভালো এখনও জেগে থাকল। জেগে আছে, কিন্তু সেটুকুই বা আর কতক্ষণ! এই নিভল বলে!
তবে এবারই ঠিক বোঝা যাবে―এই পোড়োগৃহে অদৃশ্য মানুষজনেরা আদৌ বসবাস করে কীনা। প্রতিটা কক্ষে ভাঙাচোরা দীপাধার বা কুলুঙ্গি দেখেছি বটে, এই, এই তো এঘরেও একটি বর্তমান।
এক্ষণে দেখার―‘যেন দীপে দীপ জ্বলে।’ কিংবা, ‘আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো’।
যদিও এখন ঝুঁজকো অন্ধকার, আলো ক্রমে কমে আসছে। এই সময়টায় আমাদের গ্রামে হলে―গোঠ থেকে গরুগুলো গোহালে ফিরেছে, জরিলাল তাদের ‘তাড়’-এ ভাতের ফেন আর খড়ের কুচি গুলে ‘জাবনা’ দিচ্ছে, মা-কাকিমারা মশা আর ডাঁশ তাড়াতে ধুনো জ্বেলে ধোঁয়া দেওয়ার উদযোগ নিচ্ছে!
ছোটকাকিমা খলা-খামারে তুলসীচৌরায় প্রদীপ জ্বেলে গলায় শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ‘সঞ্ঝা’ দিল। চল্লা-পাকুড়-আশ-শ্যাওড়ার ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে হিজল-বিঝল তারাদের ভিতর থেকে সাঁঝতারাটিকে গড় করল।
নকুলজেঠু দাওয়ায় বসে ‘ঢেরা’ ঘুরিয়ে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল। তার সাদা চুল সাদা দাড়ি সাদা ভ্রƒ শনের ভুরভুরে আঁশে আরওই সাদা হচ্ছিল। ঝুঁজকো অন্ধকারে আর কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। ঢেরা তাই বন্ধ রাখল।
সরকারি পাতকোতলায় ঘড়রি ঘুরিয়ে জল তোলার হিড়িক পড়ে গেছে বউড়িদের মধ্যে। বেলা যে পড়ে যাচ্ছে! কুয়োর ভিতর দড়ি-বালতির ‘ধাস’ ‘ধাস’ আওয়াজ। গুঞ্জন চরমে উঠেছে।
এসবই ‘ঝুঁজকোব্যালা’র আখ্যান-উপাখ্যান। সন্ধ্যা হয়ে আসা আর ঊষার প্রাক্কাল। এই মুহূর্তের অন্ধকারই তো ঝুঁজকো অন্ধকার।
কিন্তু এহেন পোড়োগৃহে যেন কোনও নিয়মকানুনের বালাই নেই! এই তো এখনই কে যেন একপোঁচ কালি ঢেলে দিল চারধারে। ‘কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।’
এতক্ষণে ভয়ই ধরল আমার। মসিকৃষ্ণ অন্ধকারে কারা যেন ভিতরে ও বাইরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। কে সে ? কারা তারা ?
ঝিলের জলও তরঙ্গ তুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে। জলোচ্ছ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পারাবতগুলোও হঠাৎ হঠাৎ ভদকে উঠে ডানা ফেটিয়ে উড়ে গেল বাইরে। এই ঘনঘোর অন্ধকারেও তারা আকাশে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
আশ্চর্য! তার মধ্যেও কেউ কি এ সময় খঞ্জনী বাজিয়ে এই ‘বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনী’তে গান ধরল ? নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গই বা আর থাকল কী করে ? এ যে ‘কোলাহলতাড়িত বাতক্ষুব্ধ’!
খঞ্জনী না করতাল ? করতালধ্বনি ? ‘চ খ চ খ তালধ্বনি করতালে।’ কে যেন গাইছে―
‘মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়ো ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
মু জগ বাহির নই ছার ॥’
স্পষ্ট শুনছি। আরে, এ তো বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্তন! এ পদ ক-ত শুনেছি! আমাদের গ্রামের উপান্তে ‘নুয়াসাহি’ বলে আরেকটা গ্রাম আছে। সে-গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত হলেও চারুবোষ্টুমী ও তার পরিবার সেখানে বাস করেন। জাতিতে তাঁরা বৈষ্ণব।
রোজদিন সন্ধ্যায় তাঁদের ‘আখড়া’ বসে। ‘অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে। গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে ॥ ‘―এই বলে বন্দনা করে তাঁরা ‘হরিনাম সংকীর্তন’ শুরু করেন।
চারুর মেয়ে গিরিবালা। যেন শ্রীরাধিকা। কীর্তনের আখর, পাঠ কিছুই জানি না, বুঝি না। তবু তার কণ্ঠে গাওয়া কীর্তন আর সেই শ্রীখোলের বোল, ‘গুড় গুড় গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তেত্তা― খিটিতা খিতা তেত্তা তেত্তা’ যেন কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে যেত!
কান খাড়া করে সজাগ হলাম। কেউ কি খঞ্জনী বাজিয়ে গিরিবালার গাওয়া সেই গানটাই গাইছে এখন ? ওই যে ―
‘ও শারী তুই দে গো সাড়া ―
সুখের নিশি হলো সারা―ও শারী তুই দে গো সাড়া―
নইলে শারী হবে সারা, যদি শাশুড়ি ননদী দেখে তারা
ও শারী সব হবে সারা ॥’
না না, কোথায় কী! এ তো শুভঙ্করের ‘আর্য্যা’। কেউ ‘শিশুবোধক’ থেকে বিড় বিড় করে মুখস্ত বলছে। ‘সের কসা’।
‘তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাবে।
ওঙ্কারনাথ প্রতি মণ হইলে সের কত লবে ॥
আনা প্রতি কত হবে গণ্ডায় কত লবে।
কড়া প্রতি কি ধরিবে স্থির করিতে হবে ॥
ইহার নিয়ম কিছু শুন শিশুগণে।
টাকায় অষ্ট গণ্ডা সেরে লইবে যতনে ॥’
পরক্ষণেই মনে হলো, উঁহু, ‘সের কসা’ তো নয়, কে বা কারা সেই ‘গোপাল ধনিয়া’ ও বুদ্ধদেবের কথামৃত পাঠ করছে―
‘ধনিয়া গোপো :
অন্ধ কম কসা ন বিজ্জরে
কচ্ছে রূঢ়তিনে চরন্তি গাবো
বুটিটম্ পি সহেয়্যুম্ আগতম্
অথ চে পত্থয়সি পবস্ স ॥’
ধনিয়া ॥ অন্ধক মশা থেকে ছাড়া পেয়ে গরুগুলো
তৃণাচ্ছন্ন চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি
আসুক, দেখার দরকার নেই। যত চাও পাবে,
বৃষ্টি হতে দাও এখন।
একটার উপর আরেকটা! কথা সব চাপা পড়ে যাচ্ছে! কী যে হচ্ছে―কিছুই বুঝতে পারছি না। আদৌ কিছু হচ্ছে কি ?
নাকি ভ্রম ? না মতিভ্রম ?
১৮
দীপাধার। ভাঙাচোরা দীপাধার দেখেছি বটে।
‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ লেখে যে, ‘দীপ পুং, যাহা দীপ্তি পায় বা গৃহাদি দীপিত করে; জলদবর্ত্তি, প্রদীপ।’
কিন্তু সে দীপ বা প্রদীপ জ্বলে কীসে, তার তো কোথাও উল্লেখ দেখিনা। ‘পঞ্চতন্ত্র’-এ আছে―
‘ণৃপদীপো ধনস্নেহং প্রজাভ্যঃ সংহরন্নপি ।
অন্তরস্থৈগুর্ণৈঃ শুভ্রৈলর্ক্ষ্যতে নৈব কেনচিৎ ॥’
ণৃপ-দীপের কথা আলাদা। দরকার হলে প্রজার চর্বি দিয়েও রাজার আলো জ্বলতে পারে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে পাওয়া মাটির ফলকে দীপাধার, পুস্তকাধারের প্রতিকৃতি আছে। তা বলে তৈল, ঘৃত, ইত্যাদি তৈজস ?
ঘিয়ের কথা তো আছেই! আছে না―‘ওগগরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা―’ ? ঘিয়ের প্রদীপ তো এখনও বর্তমান! তাছাড়া নাড়িয়েল, কুসুম, কচড়া, নিম, রেড়ী, তিল, তিসি, সরিষা থেকেও তেল হত। এখনও হয়।
গন্ধতেল মাখানো চকচকে কেশদাম, তাই নিয়ে মাথার উপর ‘শিখণ্ড’ বা চূড়াবাঁধা, তাতে আবার ফুলের মালা গোঁজা, কানে নবশশিকলার মতো ঝকঝকে তালপাতার ‘কর্ণাভরণ’ বা কানপাশা।
‘সদুক্তিকর্ণামৃত’য়েই তো আছে―
‘দবাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়ো কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্ ।
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃনৈগন্ধর্তৈলৈঃ শিখণ্ডঃ ॥
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং ।
বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম ॥’
রেড়ির তেলের কথা তো এই সেদিনও পড়েছি শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’-এ।
‘সেদিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত
বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা
ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ
হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে।
সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত
বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের
সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।’
রেড়ি। তার মানে তো ভেরেণ্ডা গাছের ফল থেকে তৈরি তেল! মশাল বা মোশাল বোধকরি ততোধিক প্রাচীন। কাঠিতে জড়ানো তেলমাখা ন্যাকড়ার বাতিবিশেষ।
‘মোশাল ধরিল বীরগণ’। কিংবা, ‘থাবায় থাবায়, মশাল নিবায়’।―সে না হয় হলো, কিন্তু মশালের তেলই বা কীসের তেল ? এই পোড়োগৃহের কি সংঘারামের ভাঙাচোরা দীপাধারেই বা রেড়ির না ঘিয়ের মশাল জ্বলে উঠবে―সেইটা এখন দেখার!
পল, দণ্ড, মুহূর্তের পর মূহূর্ত কেটে যাচ্ছে, ইত্যবসরে অন্ধকারাত্মক রাত্রি আরওই যেন ঘনসন্নিবিষ্ট হয়েছে। চোখের সামনে হাতের আঙ্গুল তুলে তুলে দেখছি―দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না।
ঝুম ঝুম করে কোথাও অন্ধকারে নূপুর বাজছে। কে যেন নাচছে, কে যেন গাইছে! ত্রিতাল, ছোট-খেয়াল। গান-টানের আমি কিছু বুঝি না। তবু শুনতে পাচ্ছি―
‘আব না করো মূসে রার কাহ্নাইয়া
ছোড় না মোহে কর কর বাতি
চালি যাত সব যমূনা তটপর
রোকো না মোকো শ্যাম কাহ্নাইয়া ॥’
এ কিরে বাবা! কখনও বিদ্যাপতি কখনও রাধারতি! তার উপর তমিস্রাঘন নিñিদ্র অন্ধকার। বাতিহীন, বাতিহীন। সবকিছুই কেমন যেন ঘুলিয়ে দিচ্ছে। পোড়োবাড়ি, না তার হানাবাড়ি ? সংঘারাম, না তার ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও রাজপ্রাসাদ ?
‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এ পড়েছি বটে। সেই যে সেই―
‘…সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া
শুনিতে পাইলাম কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া, বুক ফাটিয়া
ফাটিয়া কাঁদিতেছে―যেন আমার খাটের নিচে, এই বৃহৎ
প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের
ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, ‘তুমি আমাকে
উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও―কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল
স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া, তুমি আমাকে ঘোড়ায়
তুলিয়া, তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর
দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের
সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার
করো।’
সেই রাত্রে সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কন কি আর বাজেনি ? সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক―আমাদের এ দেশেও সেরকম রাজপ্রাসাদ তথা রাজা-রাজড়া বড়ো কম ছিল না। মহাভারতের যুগ থেকেই তো তাম্রলিপ্ত রাজবংশ―ময়ূরবংশীয় ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ।
তস্য তস্য পরবর্তী কৈবর্ত রাজারা―কালুভুঁইয়া, জঙ্গলভুঁইয়া। শুধু কী তাম্রলিপ্ত বা তমলুক, কাশীজোড়া, চন্দ্রকোণা, নাড়াজোল, মহিষাদল, চিল্কিগড়, কর্ণগড়, নারায়ণগড়, চন্দ্রকেতুগড়―আরও কত ক-ত যে গড়, রাজ্য, রাজবাড়ি! তারপরেও শক-হূনদল-পাঠান-মোগল!
মালজেঠিয়া নামের একটি গড় ছিল। এই তো কাছেই। ‘মালঝাটা গড় বন্দ মহলা রু´িণী। ১৬ শো রাখাল খেয়ে সেজেছে ডাকিনী ॥’ গড়ের অদূরবর্তী একটি গো-চারণের প্রান্তর ছিল। প্রান্তরের মধ্যস্থিত একটি পুরাতন প্রস্তর ছিল।
প্রাচীন প্রস্তর, বোধকরি মাকড়াপাথরই হবে, আর এ জাতীয় পাথর পড়ে থাকলে যা হয়―ক্লান্তশ্রান্ত রাখাল বালকেরা বসে দু দণ্ড বিশ্রাম করে। চাই কি, গরুগুলিকে নিশ্চিন্তে চরতে দিয়ে পাথরের উপর গামছা পেতে খানিক ঘুমিয়েও নেয়।
দৈবাৎ একদিন রুণ্ডু-উরুণ্ডু গরু-বাগালদের মধ্যে ভক্তিভাবের উদয় হলো। তারা পাথরটিকে জলে ধুয়ে-পুছে দেবীজ্ঞানে পুজোও শুরু করে দিল। তবে সব কিছুই খেলাচ্ছলে। হা-ডু-ডু, ছো কিৎ কিৎ তো নয়―পুজো করতে হলে ব্রাহ্মণ চাই, ক্ষৌরকার চাই, ঢাকী-বাজনদার চাই, বলিদার চাই―
সাকুল্যে ষোলজন। তাদের মধ্যেই কেউ ব্রাহ্মণ সাজল, কেউ ক্ষৌরকার। কেউ আবার নকল ঢাকী সেজে ‘ডু-ডু-ম্’ ‘ডু-ডু-ম্’ করে বাজাতে লাগল। বলিদারও সাজল, কিন্তু বলি কোথায় ?
কিন্তু আসল কী আর, নকল নকল। গরু-বাগালদের খেলা―খেলাই তো! অবশেষে দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ জনই ‘বলি’ সাজল। শুরু হলো পুজো―‘অং বং চং’ ‘অং বং চং’ করে মন্ত্রও উচ্চারিত হলো। ভক্তিসহকারে বাজনাও বাজতে থাকল―‘ডু-ডু-ম্ ডু- ম্!’ ‘ডু-ডু- ম্ ডু-ম্!’
পূজা শেষ হলো। এবার বলিদান―নরবলি! কনিষ্ঠতম গো-রাখালটি অনিচ্ছুক পুং ছাগের মতো ‘অর্গলা’য় অর্থাৎ যূপকাষ্ঠে মাথা রাখল। বলিদার বা হন্তারক বাগালছেলেটি একটি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে আলতোভাবে খড়্গাঘাত করল তার ঘাড়ে!
আর কী আশ্চর্য! কী হৃদয়বিদারক মর্মন্তুদ কাণ্ড! আলতোভাবে শুষ্ক কাষ্ঠাঘাতেই গো-রাখালটির মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে গেল, রক্ত ছিনছাতুর হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ল।
এহেন অদ্ভুতুড়ে দৃশ্য দেখামাত্রই বাকি বাগালরা ভয়ে-ত্রাসে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। গরুগুলো ‘হাম্বা’ ‘হাম্বা’ রবে কীসব বলতে বলতে ঘরে ফিরল।
সন্ধ্যা সমাগত হলো। তবু গো-রাখালরা ফিরল না দেখে ‘গিরিহা’ বা গৃহস্বামীরা ‘ভাতুয়া’দের খোঁজে গো-চারণে গেল।―খোঁজ―খোঁজ―গোচারণের মাঠে পৌঁছে তারা দেখল―নেই, নেই। কোনও গো-বাগালই সেখানে নেই। কেবল একজনেরই ধড়-মুণ্ড আলাদা হয়ে পড়ে আছে। আর রক্তে লাল হয়ে আছে জায়গাটা।
এ খবর শোনামাত্রই চারধারের গাঁ-গঞ্জ থেকে ধাঁ ধাঁ করে লোকজন দস্তুরমতো আসতে লাগল। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তারাও হাহাকার করে উঠল। গো-চারণের মাঠ, লাটাপাটা, মায় বন-প্রান্তরও যেন হাহাকারে ভরে গেল। তারাও দমকে দমকে কাঁদছে―কাঁদছে অঝোরঝরে―
‘কাঁসা-ভাঙা পেতল-ভাঙা সবই জোড়া যায়।
মানুষ ম-র-লে আর নাইকো জোড়া যায় ॥’
কিন্তু গৃহে ফিরে গৃহস্থরা দেখল―যেমনকার তেমন! সবই তো ঠিক আছে। সমস্ত বাগালরাই তো ঘরে ফিরেছে! পোড়ামাটির ‘তাড়’-এ তারা জাবনা গুলে ওই তো গরুগুলোকে খেতে দিচ্ছে।
এমনকি গোচারণের মাঠে তারা যে গো-রাখালটির ধড়-মুণ্ড আলাদা আলাদা দেখে এসেছিল―সেও তো এখন তার ‘গিরিহানীর নির্দেশমতো গোহালে ঘুঁটে পুড়িয়ে ধোঁয়া দিচ্ছে!
এমন অলৌকিক কিত্তিকাণ্ড তথা ‘কাটা মুণ্ড জোড়া লাগা’-র ঘটনাটা অবশেষে কানে গেল মালজেঠিয়া গড়ের রাজা রুক্মের। তিনি দেবীজ্ঞানে পাথরটির প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখলেন ‘দেবী রু´িণী’। আর গোচারণের মাঠ হলো ‘রাখালদ্বীপা’।
আজও সে রাখালদ্বীপা আছে, আছে সেই পাষাণ প্রতিমা। তবে সে রাজাও নেই, সেসব দিনও আর নেই! দেবীর কাছে নরবলি দিতে না পারায় রাজাকেই নাকি দিতে হয়েছিল আত্মবলিদান!
এমনি কত শত কাহিনি যে গুমরে গুমরে কাঁদে গুমাইগড়, রু´িণী কুণ্ড, শোণিত কুঠিতে! গাংড়ার বনবাশুলী, দধিবামন জীউর মন্দির, সিঁদুরটিকার মঠে! সেই বলে না―
‘ঞযবৎব যধঢ়ঢ়বহ সড়ৎব ঃযরহমং
ওহ যবধাবহ ধহফ বধৎঃয, ঐড়ৎধপরড়,
ঞযধহ ধৎব ৎবঢ়ড়ৎঃবফ রহ ুড়ঁৎ হবংিঢ়ধঢ়বৎং.’
অকস্মাৎ আলো জ্বলে উঠল। দীপাধারে দীপ না, মশাল জ্বলল ? বন্ধ দ্বারের অভ্যন্তরে থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। তবু দ্বারের নিম্নতলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যে আলো, আলো না বলাই ভালো, যেটুকু আলোর আভাস এল তাতে করে এটুকু বলাই চলে―আলো জ্বলছে!
তদুপরি কোলাহল উঠেছে। তার মানে, লোকজন আছে। আছে, আছে। লোকজন না থাকলে কোলাহল কোত্থেকে আসে ? মনুষ্য না থাকলে আলোই বা জ্বলে কী করে ? তাছাড়া, অতসব খাবারদাবার―
আমি অতঃপর ভারী তদগত হয়ে মনুষ্য কোলাহল শুনতে সচেষ্ট হলাম। শোনা যাচ্ছে কী, সমস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে কী―‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি ?’
বারে বারেই বা এমনটা কেন হবে ? আশপাশে দাঁতনে, মোগলমারিতে সদ্য সদ্য মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে বলেই কি সেই ‘তাঁহাদের’ কথাই স্মরণে আসছে বেশি করে ?
হবেও বা। নচেৎ তাঁরা তো অহিংসার পূজারী, এসব হিংস্র কাজে জড়াবেন কেন ? তাছাড়া, একটু আগেই তো অন্যরকম―যেমন ‘পদাবলী’ গিরিবালার ‘বালক-সংগীত’, মায় শুভঙ্করের আর্য্যা ‘সের কসা’, এমনকি ‘আর না করো মুসে রার কাহ্নাইয়া’ রাধারতিও শুনছিলাম।
হঠাৎ দরজা খুলে গেল হাট করে! কে যেন দীপাধারে একটা জ্বলন্ত দীপও রেখে গেল! তার শিখায় এখন ১০৬ নম্বর দাগামারা ঘর আলোয় আলোকিত। আমি ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম―
‘কে ? কে ? কে তুমি ?’
যেতে যেতে পিছন ফিরে সে যেন মুচকি হাসল। কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হলো, কেমন যেন―ঠিকঠাক দেখেছি তো ?
উঠে গিয়ে আবারও যে খুঁটিয়ে দেখব―তারও সর-অবসরটুকু পাওয়া ভারী দুষ্কর হলো। কেননা তন্মুহূর্তেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল ধড়াস্ করে!
আলো ছিল না। ঘরভরতি অন্ধকার। হঠাৎ আলো এসে সবকিছুকেই ধাঁধিয়ে দিল, ঝলসে দিল। আমার চোখদুটিও তেমনটা হয়ে থাকবে বোধকরি। তাই কী দেখতে কী দেখে ফেলেছি মাথামুণ্ডহীন!
সময় সময় এমনটা হয়। আমাদের জাহাজকানার জঙ্গলেই তো হয়। হয় না ? হঠাৎ হঠাৎই ঝলসে ওঠে জাহাজের কানা!
বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে শ্রীমন্ত সওদাগর তো সমুদ্রবক্ষেই আচমকা দর্শন করেছিলেন ‘কমলে কামিপী’―কমলে আসীনা কামিনীরূপিনী চণ্ডী! ‘বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।’ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই কবিতা―
‘কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালীদহে। বসি বামা শতদল-দলে
( নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহারি।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।’
‘মনসামঙ্গল’-এই তো আছে। চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা তৈরি হলো, নাম তার ‘মধুকর’। মধুকর কালীদহের জলে ভাসান শুরু করবে―তার আগে ‘কলীদহের বালিচরে কত তাল জল’―পরিমাপ করতে হবে। ডাক পড়ল ‘ডুবারু’দের। কে কতক্ষণ জলের তলায় একডুবে থাকতে পারে।
চাঁদ সওদাগরের সামনে তাই নিয়ে অভিজ্ঞতার বাখান। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ! রীতিমতো কমপিটিশন, কমপিটিশন! গঙ্গা, বোনা, জয়, রামেশ্বর, তোতারাম, সিতা, জিতা―সব বাঘা বাঘা মাঝির দল!
গঙ্গা বোলে ‘মহাশয়, করি নিবেদন।
এক ডুবে থাকিতে পারি দিবস কত্তন ॥’
বোনা মাঝি বোলে আমি জগাই-সন্তান।
‘এক ডুবে ছয়মাস থাকে কোন বস্তুজ্ঞান ॥’
আসি জয় মহাশয় বোলে, ‘নাহি হীন।
এক ডুবে বৎসর কাটাই বরং চারিদিন ॥’
রামেশ্বর মাঝি বলে সুদামের জ্যাঠা।
‘ডুব দিয়া তলায় না পড়ি যেন লৌহভাটা ॥’
‘তোতারাম কিঙ্কর দুলাল জয়হরি।
আমরা, একডুবে থাকিতে পারি ছয়মাস বৎসরি ॥’
সিতা জিতা বোলে, ‘শুন, পাহাড়ি।
এক ডুবে জনম কাটে লেখাজোখা কি ॥’
আরে! জলের তলায় এক ডুবে আমিও তো ছিলাম একরাত্রি অর্ধেক দিবস। যেখানে গঙ্গামাঝির মতো মাঝির এক ডুব-স্থিতিকাল বড়জোর একটা দিবস।
যা হোক, যা দেখেছি তা নিজেরই ভ্রম বলে মনে করলাম। দীপাধারের দীপের আলোয় অতঃপর ধাতস্থ হয়ে আবারও ঘরের চারধারটা দেখতে লাগলাম। সেই পোঁটলায় বাঁধা কতক কাপড়চোপড়, ছেঁড়া কানি, তোষক-বিছানা―
দেখতে দেখতে কেন জানি আবারও মনে হলো―এই পোড়োবাড়ি তাঁদেরই, সেই সমস্ত শিক্ষার্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণেরই। সেই স্টাকো, সেই ভাঙাচোরা মূর্তি―
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। মাধুকরীর ভিক্ষান্ন থেকে প্রস্তুত আহার্যও গৃহীত হয়েছে। দীপাধারে দীপও জ্বলেছে। এবার তো―‘ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।’
হয়তো এক্ষুনি বৌদ্ধ শিক্ষার্থী ভিক্ষুরা দীপাধারের আলোয় অধ্যয়ন শুরু করবে। কেউ পড়বে ‘সুত্তপিটক’ কেউ বা ‘বিনয়পিটক’ আর কেউ ‘অভিধর্ম-পিটক’। আবাসন গৃহ, অলিন্দ, কক্ষ, দ্বার, গবাক্ষ মায় উঠোন পাঠোচ্চারণে নিনাদিত হবে―‘উচ্চ উঠাঅন বিমলঘরা, তরুণী ঘরিণী বিনঅপরা’―সহসা বন্ধ দরজা আবারও খুলে গেল! কে যেন কক্ষে ফের হুটমুট প্রবেশ করল। মনে হলো, ১০৬তম কক্ষটি তাঁরই, তাঁরই। মাথায় পরা ‘হেলমেট’-এর মতোই কী একটা মাথা থেকে খুলে বিছানার উপর ছুড়ে ফেলল, অবিকল গৃহ- কর্তার মেজাজেই।
এবার লোকটাকে সামনাসামনি পরিষ্কার দেখলাম―স্পষ্টতই ‘মাথামুণ্ডুহীন’―
ওদিকে এই সময়ই যুগপৎ শুনতে পাচ্ছি―না না, ‘সুত্তপিটক’ কি ‘বিনয়-পিটক’ নয়, কেউ কোথাও যেন ‘টাকার খৎ লিখিবার ধারা’ সুর করে মুখস্ত করছে―
‘মহামহিম শ্রীযুক্ত রামজয় চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু ॥
লিখিতং শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ কস্য কর্জ্জপত্রমিদং
কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে মবলগে কোং
সিক্কা ৩২ বত্রিশ টাকা কর্জ্জ করিলাম ইহার সুদ
ফিঃ টাকায় মাসিক দস্তুর দরমাহ দিব টাকার
ওয়াদা মাহ চৈত্র সুদসমেত…’
১৯
আগেও বলেছি, এরকম মাথামুণ্ডহীন একটা ছবি দেখেছি থ্রি-ফোরের ইতিহাস বইয়ে। গলাসুদ্ধ মাথাটাই নেই।
শুধু কি ঘাড়-মাথা ? হাতও তো ছিল না বোধকরি। অবশিষ্ট অবয়ব জুড়ে বোতাম-লাগানো সেই একটা মোটা ও মস্ত আলখাল্লা। তাঁর বিষয়ে কত প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করেছি :
‘ প্র:। কুষাণ কারা ?
উ:। মধ্য এশিয়ার এক পরাক্রমশালী
যাযাবর জাতি ‘ইউচি’। তাঁরাই কুষাণ।
প্রঃ:। কুষাণদের মধ্যে খ্যাতিমান সম্রাট
কে ছিলেন ?
উ:। কণিষ্ক।
প্র:। তিনি কখন রাজা হন ? তাঁর রাজধানী
কোথায় ছিল ?
উ:। কণিষ্ক ৭৮ খ্র্রিস্টাব্দে রাজা হন। তাঁর
রাজধানী ছিল পুরুষপুর।
প্র:। কণিষ্কের ধর্মমত কি ছিল ?
উ:। কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ।
প্র:। তাঁর সভাকবির নাম কি ?
উ:। অশ্বঘোষ।
প্র:। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন ?
উ:। বুদ্ধচরিত।’
মথুরার নিকট তাঁর একটি কবন্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। ‘কবন্ধ >কন্ধ > কন্ধ +কাটা’। অর্থাৎ মাথাকাটা, মস্তকবিহীন। হয়তো কোনও কারণবশত সম্রাট কণিষ্কের আস্ত মূর্তিটার মাথাটাই খোয়া গিয়েছিল এই সংঘারাম বা ভগ্নগৃহে রক্ষিত যত সব মাথা-ভাঙা, মাথামুণ্ডহীন মূর্তিদের মতো!
তাও ভালো। স্কন্ধকাটা বা কন্ধকাটা ‘কবন্ধ ভূত’ হলে তো মুশকিল। নাকি সপ্তকাণ্ড রামায়ণে উল্লেখ আছে―যুদ্ধক্ষেত্রে এক অযুত গজ, এক নিযুত অশ্ব, একশত পঞ্চাশ রথী আর দশ কোটি পদাতিক সৈন্য হতাহত হলে একটা ‘কবন্ধ’ তৈরি হয়।
‘কবন্ধ’―মাথামুণ্ডহীন, কেবল ধড়বিশিষ্ট এক ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা। ‘চলেন চলেন’ বলে এরা সামনে এসে ডাকে না। পথিককে পিছন থেকে আবাহন করে, ‘আয়েন আয়েন!’
সাড়া দিয়ে পথচারী যদি বেভুলে পিছন ফিরে তাকায়, মুহূর্তেই সে কবন্ধ তার ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। আর, তা দেখে পথচারী মূর্ছিত হয়ে পড়লে তবে তো কেল্লা ফতে!
অজ্ঞান পথচারীর বুকের উপর উঠে রক্ত শোষণ করে নেয় কবন্ধ। ‘পহলমেট’―খোলা কবন্ধরূপী আমার সমুখে দণ্ডায়মান এই আগন্তুকও কি সেই গোত্রের ? সেই তন্ত্রের ?
কই, লোকটাকে দেখে তেমনটা তো বোধ হচ্ছে না! গৃহকর্তার মেজাজ দেখালেও উল্টে কেমন যেন চেনা চেনা, নিরীহ, গোবেচারীই লাগছে তাকে। উপরন্তু বিছানায় ফেলে রাখা ‘পহলমেট’টা যথাস্থানে জুড়ে নিলে ফের যে-পেক-সেই।
মানুষ, মানুষ।
ভেল্কি নাকি ? মাদারির খেল ? ‘কী মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।’ এমনটাও শুনেছি বটে আমাদের গ্রামের গুনিনের গুনিন রাজা গুনিন বালকা সাঁওতালের মুখে!
বড়ই শ্রদ্ধাস্পদ সাঁওতালী-পুরাণ-বিশারদ আমাদের গ্রামের এই বালক তথা বাল্কা সাঁওতাল। একদিন সকাল সকাল আমি দোয়াতে কালির বড়ি গুলে বাঁশের কলম দিয়ে হাতের লেখা অর্থাৎ হস্তাক্ষর চর্চা করছি―
‘ সন্দীপনী মুনির পাঠশালা।
তবে হলধর হরি, মনে মহা খেদ করি
গেলা যথা জনক জননী।
প্রণমিয়া করপুটে, দাণ্ডাইয়া সন্নিকটে,
কহিতে লাগিলা যদুমণি ॥
পণ্ডিত সভার মাঝ, পাইলাম বড় লাজ
বিদ্যাহীন জন কেন বাঁচে।
সন্দীপনী মুনিবর, অবন্তীনগরে ঘর,
বিদ্যা শিক্ষা করি তাঁর কাছে ॥’
আর আমার মা আমারই কাছে বসে বোধকরি আড়চোখে মুক্তার মতো হস্তাক্ষর সন্দর্শনে যারপরনাই প্রীত হয়ে কাটারি দিয়ে বাঁশের কঞ্চি চাঁচছে একমনে। সরু সরু বাঁশের খুঁচি, যা দিয়ে বালির খলায় চাল বা মুড়ি ভাজা যায়।
আচমকা সেখানে কী কাজে যেন বালকা সাঁওতাল উপস্থিত। পরনে একটা কৌপীনমাত্র। মাথায় ঘোমটা টেনে শশব্যস্ত হয়ে মা বসার জন্য বাবুইদড়ির ‘মাচিয়া’টা এগিয়ে দিল।
মাচিয়াটা টেনে বসতে বসতে বালকা বললেন―
‘হেঁ গড়ম, তা’লে―’
‘কী ?’
‘মাথার খুলিটা খুলি ইবার ?’
বলে কী লোকটা! খুলি আবার খোলা যায় ?
‘নাট-বল্টু দিয়ে আঁটা বুঝি ? বাইকবালার হেলমেট নাকি ?’
‘এই ত! বল্লে তুঁই বিশাস করবি নাই―ওঃ মোঃ―’
বলেই বালকা দু হাত দিয়ে মোচড়াতে লাগলেন আপনার মাথার খুলিটা। মা আর আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। গুনিনের গুনিন রাজা গুনিন বলে কথা―খুলেও ফেলতে পারেন মাথার খুপরিটা!!
না, খুললেন না। তবে সখেদে বললেন―
‘খুলত গড়ম, আগের যুগ হৈলে আলবাৎ খুলে যেত পটাং করে। এই যুগে ত্যামন আর সুবিস্তা কই ? কোথায় ? নাই, নাই। সবটাই আমাদের কপালের দোষ বাবু, জাতের বজ্জাতি।’
‘কী রকম ?’
বাঁশের খুঁচি-ছাড়ানো পড়ে থাকল একধারে, মা উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল। তার উত্তরে বালকা গুনিন সৃষ্টিকর্তা ‘ঠাকুরবাবা’র জরপ শুরু করলেন। বিমানবিহারী সূর্যদেবই সাঁওতালদের ‘ঠাকুরবাবা’―
‘ সিন চান্দো সেওয়া কাতে
বাহা মান্দার মূলিং রহয়লেদা―’
মান্দারমূলী ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম ‘সিন চান্দো’ বা সূর্যদেবের পূজার জন্য―সাঁওতালদের আদি বাসস্থান নাকি ছিল ‘হি হি ড়ি-পি পি ড়ি’ ও ‘চায়-চম্পা’। পিপিড়ি, তার মানে প্রজাপতি আর চায়-চম্পা তো ফুলের গাছ। হিহিড়ি পিপিড়ি আর চায়-চম্পা রাজ্যে সাঁওতালরা কিস্কু রাজাদের রাজত্বে নাকি বেশ সুখেই বসবাস করছিল।
‘সুখ বলতে সুখ! সুখের অধিপতি, সীমা-চৌহদ্দি ছিল না। বা-ঙা―’
দু হাত মেলে ধরে বালকা গুনিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন―
‘এই যে তুঁই বাঁশ না খাগের কলম দিঞে আজ লেখালিখি কচ্ছিস, সেকাল হৈলে কষ্ট করে তোকে আর লিখতেই হতো নাই। ঠাকুরবাবার কিরপায় কাগজে দাগা বুলানো মাত্রেই চড় চড় করে লেখা হঞে যেত।
‘ধানগাছে ধান ফলত নাই, ফলত ঢেঁকি-ছাঁটা-চালের ল্যাখেন চাল। তুলা-গাছে তুলা হত নাই, সরাসরি কাপড় ফলত। নানা রঙের শাড়ি-ধুতি- লুগা―
ঠাকুরবাবার দয়ায় বলতে গেলে মানুষকে খাটতে খুটতেও হতো নাই। মাগলেই হাতের কাছে―অমুক-ঢেঁক্-ফালনা-তুসকা― খাবারদাবার―সবকিছুই এসে যেত।
দু চোখ বড় বড় করে বলেন কী ?’
‘তা’লে আর বলছি কী!’ বলেই মাথার উকুন বাছার গল্প তুললেন বালকা। এমনিতেই কারওর মাথার উকুন বাছতে হলে আজকাল আরেকজন লোকের দরকার। একা একা তো আর নিজের মাথার উকুন বাছা যায় না!
মাথার চুলে বিলি কেটে কেটে চুলের গোড়ায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা উকুনটাকে ধরে দু হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখে টিপে পুটুস করে মারা। ঝঞ্জাটের কাজ―সে তো আর একার দ্বারা হয় না।
কিন্তু ‘ঠাকুরবাবা’র কৃপায় এককালে নাকি একা একাই উকুন-বাছা হতো। কী করে ? কেন মাথার খুলিটা টুক করে খুলে হাতে নিয়ে ইচ্ছামতো উকুন বেছে ফের ‘হেলমেট’-এর কায়দায় মাথায় বসিয়ে নেওয়া―কী গড়ম, বহুৎ সুবিস্তা না ? আরও শুনবি―‘মেঘপাতাল’টাও ছিল হাতের নাগালের মধ্যে, বলতে কি হাত দিয়ে ছোঁয়াও যেত―’
মেঘপাতাল! তার মানে তো আকাশ। আকাশ, আকাশ। দূর, বহুদূর। তাও কী না ছোঁয়া যেত হাত বাড়িয়ে ?
হঁ হঁ। সেই আছে না,―‘তুলব ফুল গাঁথব মালা আমরা দুজনে’―মেঘ-পাতালের তারাফুল হাত দিয়ে খুশিমতো ছেঁড়ো, মালা গাঁথো, গলায় পরো আর নাচো―‘তাঁহা রেতা না না তারনা ―তাঁহা রেতা না না তারনা―‘মা অতঃপর জিজ্ঞাসা করল―‘তা এমনটা কেন বন্ধ হয়ে গেল, বাবা ?’ বালকা বললেন―‘অই যে বললম―আমাদের কপালের দোষ!’ আমাদের জাতের বজ্জাতি! এক সান্তাল মেয়েমানুষ মাঠে ‘জলঘাট’ করতে বসে গাছ থেকে চাল তুলে মুখে পুরে আক্কুটির মতো গসা গসা খাচ্ছিল―তাই দেখে রাগ হয়ে গেল ঠাকুরবাবার―রাগ তো হওয়ারই কথা!
পূর্বপুরুষরা, ঠাকুর্দার বাপ-ঠাকুর্দারা, পই পই করে বলত―ঘরদুয়ার সাফ-সুতরো রাখিস, খাবারদাবারের ‘আঁইঠা-পাতা’ ঘরের ছামুতে ফেলিস নাই ফেলিস নাই! ঠাকুরবাবা মেঘপাতাল থেকে নেমে এসে রোজ রাতের বেলা সান্তালদের ঘরসংসার দেখতে চান স্বচক্ষে―দেখতে এসে যদি―
আর সত্যি সত্যিই, পড়বি ত পড়, উড়বি ত উড়―খাবারদাবারের ‘আঁইঠা-শালপাতা’ বাতাসে পৎ পৎ করে উড়তে উড়তে―লাগবি ত লাগ―একেবারে স্বয়ং ঠাকুরবাবার চোখে-মুখে!!
―রাগ হবেক নাই ঠাকুরবাবার ?
―হৈলও তাই! তাই! ভয়ঙ্কর রাগে ঠাকুরবাবা ধরতি থেকে এক হ্যাঁচকায় মেঘপাতালটাকে তুলে নিয়ে গেল উপরে। ধানগাছেও আর চাল ফলল নাই। কাপাসগাছেও আর কাপড় ধরল নাই। সেই থেকে মাথার খুলিটাও আর খুলল নাই―ইসক্রুটাও টাইট হঞে গেল বরাবরের তরে! তোকে আর কী বলব, গড়ম- কবেকার কথা। আতান্তরে পড়ে আজ যাদের এখন সমুখে দেখছি―তাদেরও মাথার খুলির স্ক্রুর ঢিলা-টাইটের ব্যাপার আছে নাকি ?
২০
‘মাথামুণ্ডহীন’ লোকটা কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে! তার জিনিস সে খুঁজতেই পারে। তাতে আমারই বা কী বলার আছে!
কিন্তু আমার মাথার মধ্যে সহসা একটা চিন্তার উদ্রেক হলো―লোকটা কি রাতে আমার সঙ্গে এই এক বিছানায় রাত কাটাবে ? নাকি যা খুঁজতে এসেছে, তা পেয়ে গেলে অন্যত্র চলে যাবে ?
কে জানে সে কী করবে! আপাতত সে হাণ্ডুলমাণ্ডুল হয়ে জিনিসটা ঢুঁড়ে চলেছে। খুলিটা তো খোলা অবস্থায় বিছানাতেই রাখা আছে। তাহলে এত কিছু সে দেখতে পাচ্ছে কী করে ?
না না। চোখ-মুখ তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। শুধুমাত্র খাপে-খাপ খুলিটাই যা খোলা। অবিকল আমাদের গ্রামের বালকা সাঁওতালের বলা ‘বিনতী-কাহনি’টার মতো।
লোকটার পরনে লুঙ্গির মতো ‘চীবর’ই হবে। গেরুয়া গেরুয়া দেখতে, ‘কাষায়’ কী ? গায়েও একই রঙের ফতুয়া, ‘চৌবন্দি’ কী ? দীপাধারের আলোয় তো ভিক্ষু-ভিক্ষু লাগছে।
বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। হয়তো ভিক্ষু, তবে এখনও শিক্ষার্থী। তাহলে এই গৃহ, গৃহবাসী সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যা ভাবছি ―তা বোধকরি ঠিক।
তবে তার সঙ্গে আমার এখনও কোনও কথা হলো না। সে তো আসা ইস্তক ব্যস্ত―কী যেন ঢুঁড়ে চলেছে! তাছাড়া ‘মাথামুণ্ডহীন’ একটা লোকের সঙ্গে আগ-বাড়িয়ে কী কথাই বা বলা যায়!
উপরন্তু ওই যে বললাম―একটা চিন্তা, কথায় আছে ‘খেতে পেলে শুতে চায়’―আলাপ জমে গেলে সে যদি আর উঠতেই না চায় ? এখানেই শুতে চায় ?
তার বেলা ?
অতএব যা বলবার―ওই আগে বলুক। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ তার কার্যকলাপ ও গতিবিধি লক্ষ করতে থাকি। অন্যথায় কক্ষের গবাক্ষ পথে চোখ রেখে রাতের পুষ্করিণী দেখি―‘গগন গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া―’ সত্যি সত্যিই রাতের পুষ্করিণী অপরূপা হয়ে উঠেছে! তারাদল নিয়ে নভোমণ্ডল জলে নেমে পড়েছে। তারাগুলি জলে পড়ে গুলিয়ে না গিয়ে ড্যাবা ড্যাবা অজস্র চোখে যেন তাকিয়ে রয়েছে।
তাকিয়ে আছে এই পোড়োবাড়িটার দিকেই। বাড়ির প্রতিটা কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে দীপাধারের আলোও যেন ক্রমে ক্রমে নেমে পড়েছে জলে!
আর, এখনকার নদীধারের গ্রাম লাউদহ নৈহাট কাঁটাপাল কুলবনী থুরিয়া মলম না হোক, তখনকার করঞ্জ ঘাঘরকাট্টি তালবাটী বটগোহালী গোবিন্দকেলি বলিকন্দর দণ্ডভুক্তি কি শ্বেতবালিকা নামের কোনও না কোনও গ্রামের কেউ না কেউ কী এহেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণকালে যেতে যেতে পথিমধ্যে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে এদৃশ্য অবশ্য অবশ্য দেখছেই।
যেমনটা আমাদের নদী-সেপারের বড়-ইস্কুলের ডুলুঙ নদীতটস্থ হোস্টেলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণকালে প্রায় তিন শতাধিক ‘বোর্ডার’-এর হেরিকেন-প্রজ্জলনের মাধ্যমে সচরাচর ঘটে থাকে।
বিশেষ করে রগড়া-হরিপুরা গ্রামের সেদিক থেকে সায়ংকালে যখন কোনও হাটুরে, গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমনকারী পদযাত্রী, চলতে চলতে ডুলুঙ নদীর তীরে সহসা উপস্থিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে―রোহিণী চৌধুরানী রু´িণীদেবী হাইস্কুল হোস্টেল বাড়ির কম-সে-কম পঞ্চাশ-ষাটটা ‘ঝুরকা’ দিয়ে নলাকারে আলোর শীষ এসে লেগেছে ‘ডোলঙ্গ’ তথা ডুলুঙ নদীর জলে―
তখন, থমকে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে এ দৃশ্য সে দেখবেই দেখবে! উপরন্তু তার কোনও পুত্র কি নিকট আত্মীয় হোস্টেলে থাকলে এক ফাঁকে তার কাছে সত্বর গিয়ে দেখাও করে আসবে এই বলে―
―বাবু রে! এই যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। তাই আর কী! সব দিক কুশল তো ? পয়সাকড়ি ?
এতক্ষণে লেপ-তোষক হাটকে-পাটকে লোকটাও যেন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে। মাথামুণ্ডহীন লোকটা!! যা খুঁজছিল―তা কি সে পেয়ে গেছে ? নাকি এখনও খোঁজাখুঁজি বাকি আছে তার ?
হ্যাঁ, আমারই কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছিল। তবু যদি বিছানায় ফেলে রাখা নিজের খুলিটা মাথায় চাপিয়ে খোঁজাখুঁজি করত লোকটা!
আস্ত একটা মানুষ তো নয় লোকটা, আদতে একজন ‘ই ন্ ক ম্ প্লি ট্ ম্যা ন’। তবে বোর্ডিংয়ের সব কটা বোর্ডারেরই কি এই একই অবস্থা ? মাথামুণ্ডহীন দশা ?
না, না। লোকটা আমার মনের কথা বোধকরি বুঝতে পেরেছিল। তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে খুলিটা হাতে নিয়ে খাপে খাপ স্ক্রু-টাইট করে মাথায় পরে নিল।
তাকে দেখেই অনেকটা মনে হলো―বুঝি বা দেউলবাড় গ্রামের ফকিরমোহন চক্রবর্তী। না না, বরঞ্চ মিল আছে রামচন্দ্রপুরের চারুচন্দ্র হাটুইয়ের। উঁহু, উঁহু। তাও না। কিছুটা হলেও এক দেখতে―নুয়াসাহি গ্রামের সুধীর সীট।
যা হোক লোকটা তো বিছানার তলা থেকে হাতড়ে বের করে আনল লাল শালুতে মোড়া কী একটা হাতে-লেখা পুঁথি। দীপাধারের আলোয় সেটা মেলে ধরল।
তাই দেখে ফের আমি যারপরনাই বিরক্ত হচ্ছি―এই রে! লোকটা আর তাহলে এ ঘর ছেড়ে যাচ্ছে না ? রাতটা তার সঙ্গেই কাটাতে হবে আমাকে ?
এক্ষণে পুঁথি খুলে সে কী আর পাঠ করবে―এই বড়জোর ‘ত্রিশরণ মন্ত্র’ ― ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’ ‘ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি’ ‘সংঘং শরণং গচ্ছামি’―
না, না। কান খাড়া করে শুনলাম―পালিও না, সংস্কৃতও না, পরিষ্কার বাংলা। বাংলাই পড়ছে লোকটা। আ মরি বাংলা ভাষা―
‘থলরেণু ঘুচাইয়া যুবতী রূপবতী।
সরস গোময় রসে স্থান কৈল শুদ্ধি ॥
সুগন্ধি চন্দন রসে রচিল দেহালি।
আরোপিল শ্বেতধান্য হেমঘট বারি ॥
ঘটে চূতডাল দিল কণ্ঠে ফুলমাল।
স্থাপিল কুঞ্জরমুখ দেবার কুমার ॥’
শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল―বুঝি বা কোনও পূজা-আরাধনার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে। ‘থলরেণু ঘুচাইয়া’―(চমৎকার প্রয়োগ!) তারমানে তো পূজাস্থলের ধুলাধুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে―
নাচদুয়ারতক আঙিনাময় গোবর লেপে, শুদ্ধ করে, তদুপরি জলভরা হেমঘট বসিয়ে, ধান-আমডাল-সপুষ্প-সচন্দন দিয়ে বেদীমঞ্চ সাজিয়ে, চাক-ঘাঘর-নুপূর-শঙ্খ-মাদল বাজিয়ে―
এ তবে কার পূজা ? কার আরাধনা ? এতক্ষণ, এতদিন ধরে জলেস্থলে যে বাদ্য-বাজনা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল―সে কি তবে এই ? আরও কতকটা শুনে সন্দেহের মেঘ বুঝি কেটে গেল!
‘তুমি মাহেশ্বরী বাশুলী খেচরী
দানবদলনী ভীমা।
গদিনী খড়্গনিী চাপিনী শূলিনী
যার তনু নাহি সীমা ।।
সিন্ধু জলদেবী লোক ভয়ঙ্করী
নাসিকা দিঘল খর্ব্বা ।
প্রচুর হাসিনী দেবতা-জননী
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ॥’
বাশুলী ? বাশুলী খেচরী ? হ্যাঁ, আমাদের ওদিকটায় বাশুলী দেবীর ‘থান’ আছে বটে। লাউদহয় যেমন আছে ‘ভুলাসনি’ দেবীর মাথা-কাটা মূর্তি, তেমনি আছে কালরুইয়ে ‘বাশুলীর থান’ ।
কোথাও কোথাও মনসাদেবীই বাশুলী। ত্রিনয়নী, বড় বড় চোখ। সেহেতু ‘বিশাল লোচনী’ বা ‘বিশালাক্ষী’ও তিনি।
কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা। কখনও মা কালীর মতো গলায় নরমুণ্ড-মালা। কখনও এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে বরাভয়। আবার রঙ্কিনী, ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গেও তাঁর যোগসাজশ আছে।
কিন্তু এদের সঙ্গে তাঁর কী ? কে এই লোকটা ? যদি আমার অনুমানই ঠিক হয়―তবে সে এই সন্ধ্যা উত্তীর্ণকালে দীপাধারের আলোয় ‘অর্হতে নমঃ’ বা ‘নাম-মিও-হো-রেঙ্গে-কিও’ অর্থাৎ ‘কার্য ও কারণের এই পদ্মসূত্রকে অভিবাদন’ এই বলে তথাগতকে ভরসন্ধ্যায় স্মরণ ও প্রণাম করবে―
তা নয়, পাঁচালির সুরে কী পড়ে চলেছে লোকটা ? কিছুক্ষণ আগে এই লোকটাই কি বিদ্যাপতির পদ আওড়াচ্ছিল, ‘মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়’ ?
এই লোকটাই কি সেই কীর্তনটাও গাইছিল, ‘ও শারী তুই দে গো সাড়া’ ? কীর্তন ছেড়ে মুখস্থ করছিল শুভঙ্করের আর্য্যা―‘তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাবে। তঙ্কা প্রতি মণ হইলে সের কত লবে’ ?
পাগল নাকি ‘কখনও মাথাওয়ালা কখনও মাথামুণ্ডহীন’ এই লোকটা ? এই পোড়োবাড়িটায় একা একাই সে নানাবিধ উৎপাত করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ? ধারেকাছে আর কেউ নেই বুঝি ?
বাইরে বেরিয়ে এই রাতেই চারধারটা একবার সরেজমিনে দেখে আসা মনস্থ করলাম। কিন্তু দরজা তো বন্ধ! কে জানে ঠেলাঠেলি করলে আবার খুলবে কীনা!
‘আলীবাবা ও চল্লিশজন দস্যু’ গল্পের ‘সিসেম্, দরজা খোল’ ‘সিসেম্, দরজা বন্ধ কর’-এর মতো ‘চিচিং ফাঁক’ ‘চিচিং ফাঁক’ বলে চিৎকার করতে হবে ? নাকি তার জন্য আলাদা কোনও ফুসমন্তর আছে ?
তার আগে লোকটার সঙ্গে আলাপ করা দরকার। একসঙ্গে রাত কাটাতে গেলে আলাপ-আলোচনা তো করতেই হবে। কিন্তু লোকটা যে থামেই না, থামেই না। পুঁথি পাঠ করেই চলেছে, করেই চলেছে―
‘যে তোমার পদ সেবে অভিমত কর্ম্ম লভে
ক্ষিতি তার জনম সফল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে সরসমঙ্গল ॥ ’
ভণিতা হলো। ‘শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে বিরচিয়ে সরসমঙ্গল’― প্রশ্ন, কোন মুকুন্দ ? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কী ? ‘সরসমঙ্গল’ তবে কী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ?
যাই হোক, ভণিতা তো শেষ হলো। এইবার যদি লোকটা থামে! থামলও। লাল-শালুতে পুঁথিটা ফের বাঁধাছাঁদার উদ্যোগ নিলে সেই মুহূর্তে আমিও তাকে ‘দাদা’ বলেই সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলাম―
―‘এই যে দাদা, এতক্ষণ ধরে কী পুঁথি পড়লেন জানতে পারি কী ?’
ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখল আমাকে। যেন ঘরে আরেকজন কেউ আছে―জানতেই পারেনি সে।
কার্যত কোনও উত্তরই দিল না সে। যেমনকার তেমন পুঁথিটা বাঁধাছাঁদা করতেই থাকল।
আমি আবারও চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম―
―‘দাদা, দাদা! কী পুঁথি পাঠ করা হলো―জানতে বড়ই কৌতূহল হয়। দয়া করে যদি বলেন―‘বলল না। নিষ্ঠা সহকারে বাঁধাছাঁদা সেরে পুঁথিটা ফের বিছানার তলায় গুঁজে রেখে মাথার খুলিটা খুলে হাতে নিয়ে বেরিয়েও গেল।
দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে।
এতকাল পরে তবু একটা লোক এসেছিল বটে। মাথামুণ্ডহীন। দেখাও হলো বিলক্ষণ। কিন্তু কোনও কথা হলো না। হয়তো এখনও আমার ‘গোত্রান্তর’ হয়নি বলে।
২১
লোকটা গেল। আর আমিও ‘না না’ করে বিছানার তলা থেকে লাল শালুর পোঁটলাটা খুঁজে টেনে বের করলাম।
তালপাতার পুঁথি তো নয় এটা। মোটা তুলট কাগজে কপি করা পুঁথি। চাল-পোড়া কালিতে ঝরঝরে লেখা।
একটা নয়, দু-দুটো পুঁথি। ‘বাশুলীমঙ্গল গীত’ আর ‘ব্যবস্থাসর্বস্ব’। ‘বাশুলী-মঙ্গল গীত’-এর রচয়িতা ‘কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র’।
‘ব্যবস্থাসর্বস্ব’-র লেখকের নাম তো দেখতে পাচ্ছি না। বোধকরি পুঁথিটা অসম্পূর্ণ। তবে ‘প্রতিজ্ঞা’ নাম দিয়ে গোড়াতেই কিছু কথা উদ্ধৃতি আছে―
‘বর্তমানকালে সদ্বিদ্য পণ্ডিতের প্রায়ই দিন
দিন বিরলতা হইয়া উঠিতেছে, কেহই স্বজাতীয়
শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক নহেন। তন্নিমিত্ত বৈদিক
গৃহস্থদিগের ধর্ম্মকর্ম্মাদির নিরন্তর বিঘ্ন ঘটিতেছে।
বিশেষতঃ প্রাচীন প্রাচীন পণ্ডিতেরা অর্থলোলুপ
হইয়া আপন আপন পুত্রপৌত্রদিগকে বিজাতীয় বিদ্যা
শিক্ষা করাইবার জন্য সম্পূর্ণ যত্নবান হইয়াছেন।
তন্মধ্যে যদিও কথঞ্চিৎ কোন কোন ব্যক্তির
স্বশাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন আছে বটে কিন্তু সে যত্নলতিকা
কোনক্রমে ফলবতী হয় না, যেহেতু সুচারু নিয়মে
বিদ্যাশিক্ষা করা হয় নাই, সম্প্রতিঝ যে সকল সম্ভ্রান্ত
বিদ্যালয় প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে যে প্রণালীতে শিক্ষা―
দান হইতেছে, যে স্থলে ব্যাকরণের বিপন্নতা, সে স্থলে
ধর্মশাস্ত্রের যত আলোচনা হইবে তাহা কে না উপলব্ধি
করিতে পারিবে!…’
উপরোক্ত ‘বাশুলীমঙ্গলগীত’ ও ‘প্রতিজ্ঞা’ থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লোকটা বাশুলীমন্দিরের ‘দেহুরি’ বা পুরোহিতই হবেন। আর ধারেকাছে কেন, এই পোড়োগ… হেরই অভ্যন্তরে কোথাও হয়তো বাশুলীদেবীর মন্দির আছে।
সুবর্ণরেখা নদীধারের গ্রাম কালরুইয়ে বন্ধুবর কালীপদ হাটুইয়ের বাড়ি গিয়ে তাদের গ্রামের বাশুলীর থান দেখে এসেছি বটে। তা বলে মহিষাদল রাজবাড়ির অধীনস্থ নন্দীগ্রামে হলদি নদীর ধারে বাশুলীচকে কখনও যাইনি!
শুনেছি বাশুলীচকে শ্রীশ্রী বাশুলীদেবীর মস্ত মন্দির আছে। আর সমুদ্র উপকূলবর্তী মহিষাদল তো দস্তুরমতো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ! একদা সাগরসঙ্গমে গিয়ে ফিরতি-পথে বাশুলীর মন্দিরে পূজা দেওয়াও নাকি ছিল অবশ্য কর্তব্য। সেখানে নরবলিও হতো।
মহিষাকৃতি দ্বীপই মহিষাদল। তাছাড়াও তৎকালীন বনেজঙ্গলে বুনোমোষ―। আবার কেউ বলেন, মাহিষ্যদের আদি বাসভূমি। তাই মহিষাদল।
বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মনুসংহিতা বলছে―ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্যমাতা-জাত সন্তানই কৈবর্ত। আবার কখনও তাদের পিতা নিষাদ, মাতা আয়োগব।
যা হোক, কৈবর্তদের আবার দুটি ভাগ―হালিক কৈবর্ত আর জালিক কৈবর্ত। যাঁরা হাল বা চাষ করেন তাঁরা ‘দাস’ বা চাষি কৈবর্ত। তথা মাহিষ্য। আর যাঁরা জাল ফেলে মাছ ধরেন, নৌকা চালান―তাঁরা ‘কেবট্ট’ বা আদি কৈবর্ত তথা ধীবর।
এতদ অঞ্চলে―তমলুক, বালিসীতা, তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতুবপুর―একদা ছিল মাহিষ্যদের সর্বময় রাজ্য। মহিষাদল-নন্দীগ্রাম-গুমগড়ও তারই অন্তর্গত।
এই গুমগড়েই ব্রাহ্মণদের মেয়ে সেজে একদা এক ধীবরের গৃহে বাস করছিলেন বিশাললোচনী বাশুলী। ধীবরকে ‘বাবা’, ধীবরপত্নীকে ‘মা’ পাতিয়েছিলেন।
দেবীর কৃপায় লক্ষ্মীলাভ ও ধনে-মানে প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছিল ধীবরের। দরিদ্র ধীবর কোথায় বিলেঝিলে মাছ ধরে বেড়াবেন, তা নয়―
এহেন সংবাদ কানে পৌঁছাতে সময় লাগল না মহিষাদল রাজাধিরাজেরও। তৎক্ষণাৎ আদেশ হলো―কন্যাটিকে সাদরে রাজগৃহে নিয়ে আসার।
সত্বর ধীবরগৃহে পৌঁছাল রাজ-শিবিকা। পালকি বা ডুলি। কিন্তু কোথায় কী, ততক্ষণে বাশুলী তো প্রস্তরীভূত শিলা!
কুপিত হলেন মহারাজা। ততোধিক কুপিত হয়ে প্রস্তরখণ্ডটিকে সমুদ্রবক্ষে ছুঁড়ে দিলেন ধীবর।
অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হলেন এলাকারই জনৈক ব্রাহ্মণ। সমুদ্রে নেমে উদ্ধার করে আনলেন প্রস্তরীভূত দেবীকে। স্বপ্নমোতাবেক তাঁকে ‘থাপনা’ করলেন সেই জায়গায়, পরবর্তীকালে যে জায়গার নামই হবে ‘বাশুলীর চক’।
বাশুলীর চক, বাশুলীর চক।
ধীবরের ধন হাতছাড়া হয়ে গেল কীনা ব্র্রাহ্মণের কাছে! তদুপরি মহিষা-রাজরানি দেবীর নিত্য পূজার্চনা ও ভোগদ্রব্যাদির জন্য দান-খয়রাত করে দিলেন এক সুবিস্তৃত নিষ্করভূমি।
কালক্রমে সতের শো পঁয়ষট্টিতে দেওয়ানি সনদ পেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আর রাতারাতি জায়গাটা হয়ে দাঁড়াল নুন তৈরি ও ব্যবসার পটভূমি।
দারোগা, হাবিলদার, চৌকিদার, জেলাদার, আদলদার, সেপাই-শান্ত্রী, দেশি-বিদেশি কত রকম বেতনভুক কর্মচারী। তাঁদের উপস্থিতিতে গম গম করতে লাগল ‘বাশুলীর চক’।
তাঁদেরই কেউ কেউ তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাসী বজ্রযানী-সহজযানীরা মদ-মাংসে পূজা দিতে লাগলেন বাশুলীর। এ দেবী তো তাঁদেরই―‘বাচ্ছলী’ বলে ‘চর্যাপদ’-এ এক দেবী ছিলেন না ?
উপরন্তু তাঁদের সঙ্গে এসে জুটলেন সাগর-সঙ্গম-ফেরত তীর্থযাত্রীরা। নাঙা সন্ন্যাসী আর কাপালিকরাও। ‘বাচ্ছলী’ই বাশুলী। কোথাও কোথাও বা বিশালাক্ষী।
তাছাড়া পদাবলীর কবি দ্বিজচণ্ডীদাস তো শালতোড়া গ্রামে এক জ্যান্ত ‘ডাকিনী’ বাশুলীকেও দেখেছিলেন!
আসলে এই ডাকিনীও এক যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি ‘বাসুলী’ বা নিত্যা নামের দেবীর সেবিকা। ভক্তরা তাঁকেও ‘বাসুলী’ বলত―
‘শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥’
কথিত আছে যে, এই ‘ডাকিনী বাসুলী’ই দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বলেছিলেন―বিশাললোচনী বাসুলী ওরফে বিশালাক্ষী প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে তন্ত্রমন্ত্র-সংস্কৃত শ্লোক শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দেবীর ইচ্ছা―তুমি তাঁকে প্রেমরসের গীত শোনাও―
‘চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহার চাপড়ে নিঁদ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল শুরু ॥’
আর চণ্ডীদাস নিজেও তো তন্ত্রযানী সহজিয়া সাধক। দেবী ‘বাসুলী’র একান্ত সেবক।
তবে ওই যে―ধীবরের ধন হাতছাড়া হয়ে গেল কীনা ব্র্রাহ্মণের কাছে। তবু তবু, মূলত বনজঙ্গলজীবী ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের হাতেই ‘বাশুলী’ বেশি বেশি পূজা পান।
কোথাও কোথাও তিনি ঘোড়ামুখী। কোথাও মনুষ্যরূপী। কোথাও বা শুধুই মুণ্ডুধারী। আর কোথাও কেবল পাথরের ঢেলা―
‘পুরীর বাশুলীর মুখ অশ্বের মুখের মতো।
সংবাদ নিয়া জানিলাম, ইঁহার নাম ‘ঘোড়ামুহ
বাশুলী’ কেওটসাহী পাড়ায় কেওট শ্রেণি এঁর
পূজা করেন… চৈত্র-বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা রাত্রে
নরনারী মিলিয়া নৃত্যগীত সহকারে এঁর মূর্তি
লইয়া নগর প্রদক্ষিণ করে… দেবীর উদ্দেশ্যে
আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত ফেলা হয়।’
আবার―
‘জগন্নাথের নবকলেবর অনুষ্ঠানে পুরীস্থ
বাসেলী দেবীকে পূজা করিয়া দয়িতাপতিগণ
তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে।’
‘কেওট’ শ্রেণি তো ‘কেবট্ট’ বা কৈবর্তই। আর দয়িতাপতিগণ অরণ্যচারী ‘শবর’। যেহেতু শবরকন্যা ‘নোলিতা’র পানিগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যা ব্রাহ্মণ। তাই পুরীর ব্রাহ্মণপাণ্ডারা আত্মীয়তা স্বীকার করে নিয়ে শবরদের ‘দয়িতাপতিগণ’ বলে সম্বোধন করেন।
সেই দয়িতাপতিগণ অর্থাৎ শবররাই পুরীতে ‘বাসেলীদেবী’র পূজার্চনা করেন। জগন্নাথদেবের অদূরে উত্তর-পশ্চিমে বাশুলীসাহীতে নাকি ‘বাসেলীদেবী’র মূর্তিও আছে মনুষ্যাকার।
দু নম্বর পুঁথিটাও নেড়ে চেড়ে দেখছি। ‘প্রতিজ্ঞা’ আর কি―পুরোহিতের সন্তান কেন পুরোহিত হচ্ছে না তজ্জনিত আক্ষেপ ও সেহেতু ‘একরারনামা’ করা―
‘বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসীদিগের বিস্তর হিতসাধন,
প্রতি গ্রামে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য নাই, হঠাৎ
কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে পণ্ডিতের অণ্বেষণ করিতে
গ্রামান্তরে যাইতে হয়, যদি নিকটস্থ গ্রামে পণ্ডিতের সাক্ষাৎ
না হয়, তবে সহসা তৎকর্ম্ম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা এবং
এরূপ অনেক গ্রামে অনেক কর্ম্মও পণ্ড হইয়া গিয়াছে,
সুতরাং…’
অনুভব করি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা এই পুঁথি―
প্রসাদে অনেক তৈলবট দিয়া পুঁথিখানিকে আত্মসাৎ করিয়া
রাখিলে বিস্তর উপকার দর্শিবে”
‘ব্যবস্থাসর্বস্ব’―এর ব্যবস্থাই বা কী ?―প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, অশৌচ ব্যবস্থা, তিথিকৃত্য ব্যবস্থা, দায়ভাগ ব্যবস্থা―ইত্যাদি, ইত্যাদি।
আর ‘তৈলবট’ ?
এক্ষণে ফের শ্রীশ্রীহরিচরণ শর্ম্মা বিরচিত ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এর শরণ নিতে হয়। ‘তৈলবট বি ব্যবস্থাপত্রের মূল্যস্বরূপ স্মার্ত্ত পণ্ডিতের প্রাপ্য অর্থ। [পূর্ব্বে ব্যবস্থার মূল্যস্বরূপ তৈল ও বট (কড়ি) দেওয়ার নিয়ম ছিল; সেইহেতু ‘তৈলবট’।]
তার মানে তেল-কড়ি। ফেলো কড়ি মাখো তেল―সেই আর কি! তদুপরি ‘ব্যবস্থাসর্বস্ব’-এর সূচিপত্রে কতক ক্ষেত্রে ‘ভেরি ভেরি ইমপ্যরটেন্ট’-এর মতো দাগা বুলানো। এই যেমন―
মুণ্ডন ব্যবস্থা। যজ্ঞোপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্তং। বিদ্যাপুস্তক চৌর্য্য জন্য মূকরোগ প্রায়শ্চিত্তং―
তিন-তিনবার দাগা-বুলানো ‘বিদ্যাপুস্তক চৌর্য্য জন্য মূকরোগ প্রায়শ্চিত্তং’ বিষয়টি পাতা খুলে দেখতে ভারী কৌতূহল হলো। কেননা―এর-তার বইয়ে কতই তো লেখা দেখি―‘এই বই যে করিবেক চুরি’ খুলে দেখলাম―
‘যথা। বিদ্যাপুস্তকহারী চ কিল মূকঃ প্রজায়তে ।
ন্যায়েতিহাসং দদাৎ স ব্রাহ্মণ্যায় সদক্ষিণং ॥
অস্যার্থঃ । জন্মান্তরে বিদ্যাপুস্তক চৌর ব্যক্তির তৎপাপ
চিহ্নরূপ মূক অর্থাৎ অস্পষ্ট বাক্য হয় তাহার
প্রায়শ্চিত্ত ন্যায় কিম্বা ইতিহাস পুস্তক লেখাইয়া
দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে।’
ভারী তো কঠিন প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাপনা! বই-চুরির পাপহেতু মূক হলে বা কথা বলায় আড়ষ্টতা দেখা দিলে আস্ত একটা ‘ন্যায়’ কী ‘ইতিহাস’ লিখিয়ে দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে!
পাছে বইচুরির পাপে পড়ে যাই তাই পুঁথিদুটি লালশালুতে বেঁধে তড়িঘড়ি ফের যেমনকার তেমন বিছানার তলায় ঢুকিয়ে রাখলাম।
এতক্ষণে দরজা খুলে লোকটাও পুনরায় ঘরে ঢুকল। তবে এবার সে একলা নয়, সঙ্গে আরও একজন।
২২
দুজনেই ‘হেলমেট’ তথা মাথার খুলি খুলে প্রথমেই তো ছুড়ে ফেলল বিছানায়। আমার চোখের সামনে এখন দু-দুটো মাথামুণ্ডুহীন মানুষ!
দু-দুটোই বা বলি কেন, এতক্ষণে ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, এই ভগ্নপ্রায় গৃহটির সমস্ত আবাসিকেরই মাথার খুলি ছিপি-আঁটা। যখন খুশি খোলা-পরা যায়।
দ্বিতীয় লোকটির পরনেও গেরুয়া ‘চীবর’। তবে ঠিক ‘চীবর’ কীনা জানি না―অনেকটা আমাদের ‘উড়া’ বা গাজনের ‘ভক্তা’দের গেরুয়া-ছোপানো পোশাকের মতো। যা তারা উৎসবের আগে প্রায় মাসাধিক কাল ‘হাঁকড়’-এর সময়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে থাকে। দু নম্বর লোকটা তুলনায় কিঞ্চিৎ ছোটই। বয়ঃক্রম বড়জোর পঁচিশ-টচিশ। বোধকরি সহকারী পুরুত-টুরুত হবে।
আমি গবাক্ষে দাঁড়িয়ে ফের পুষ্করিণীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অন্ধকারে ওই শুধু আলোর ফোকাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু অগত্যা তাকিয়ে থাকলাম।
লোকদুটি আমার উপস্থিতিকে আদৌ গ্রাহ্য না করে নিজেদের ভিতর কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। কী কথা, ব্যাঙের মাথা―উৎকর্ণ হয়ে শুনছি―
কী বললি ? বাড়চুনফলি ?
আদি নিবাস ?
হঁ, আইজ্ঞা।
কোন পরগনণা ?
সুজামুঠা।
জুনপুটের সন্নিকটে কী ?
বড়জোর তিন পোয়া-তিন ক্রোশ, আইজ্ঞা।
বৃত্তি ?
মৎস্যজীবী, আইঙ্গা।
জানি, জানি। বাঁশের খুঁটায় কুলজানের বেড় দিয়ে মাছধরা―
হঁ, আইজ্ঞা। হুড়মুড় করে মাছ নিয়ে জোয়ারের জল ঢুকে আসে। আর―
জানি, জানি। ভাটার জল সরলেই ‘কতুগ্গা’ ‘কতুগ্গা’ মাছ!
কী বললেন ? ‘কতুগ্গা’ মাছ ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত কত মাছ ।
তার মানে আপনিও কি সুজামুঠা ?
না না। বালিসীতা-পাঁচখালি। নরঘাট থেকে আধাক্রোশ।
নরঘাট! বলেন কী আইজ্ঞা।
হুঁ, সেই ‘নরের হাট’। হলদি নদীর ধারে। এককালে যেখানে নর ও নারী ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বসত।
বলেন কী আইজ্ঞা ?
তবে আর বলছি কী! মগ, মগের মুল্লুকের নাম শোনা আছে ?
হঁ, আইজ্ঞা।
কাউখালি, হলদি, হুগলি, রূপনারায়ণ―ওই সমস্ত নদী দিয়েই ওই মগ জলদস্যুরা হানা দিত। সাধে কি আর নদীগুলোর নাম হয়ে গিয়েছিল ‘ডাকাতে নদী’।
আইজ্ঞা।
সেই সময়টায় নদীধারে, নদীঘাটে গা ধুতে, মাছ ধরতে আসা মাইয়া-মাইপোদের দেখতে পেলেই ছেঁকে তুলত নৌকায়। চালান করে দিত মগরাজপুরে―
বলেন কী আইজ্ঞা ?
শুধু কি মগ-হার্মাদরা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ-কর্মচারীরাও মহিলাদের জোরজবরদস্তি করে গোরাসন্তান ধারণে যেমন খুশি ব্যবহার করত। গোরা-বাচ্চা নিয়েই তো খেজুরীর ‘সাহেবনগর’।
কুনোরকম কেউ বাধা দিত না আইজ্ঞা ?
দিত বৈকি। জমিদারদের লেঠেলবাহিনী ছিল―‘সরবোলা’। নদীধারে বড় বড় গাছে লুকিয়ে থাকত তারা। হার্মাদদের নৌকা আসতে দেখলেই শাঁখে ফুঁ দিত। শঙ্খধ্বনি শুনেই মাইয়া-মাইপোদের লুকিয়ে পড়ত।
হঁ, আইজ্ঞা।
তার-উপর গুমগড় কী চক্রবেড়িয়া গড়ের জমিদারদের ছিল ‘রণতরী’। ওড়িয়া পুঁথিতে লেখা আছে―
‘ময়ূরপঙ্খী জলযান, গড়ন কৈলে পঞ্চখান।
ভাসায়ে তাকু গঙ্গাজলে, দমন কলে মগদলে ॥’
তাছাড়াও মগ তাড়াতে মোগল বাদশারা হেথা-হোথা হুগলি কী হলদি নদীধারে গড়, দুর্গও বানিয়েছিল।
আর ওই যে বললেন ‘নরের হাট’ আইজ্ঞা ?
হুঁ, ‘নরের হাট’। মগ-ফিরিঙ্গিরা বেছে বেছে শুধু যে মাইয়া-মাইপোদের ধরে নিয়ে নৌকায় তুলত, এমনটাও নয়। খেত-খামারে কাজে লাগা মুনিশ-মাহিন্দর, রাস্তায় ঘাটে হেঁটে-চলে বেড়ানো তাগড়াই জোয়ানদেরও টেনে-হিঁচড়ে নৌকায় চাপাত।
কেউ কুনোরকম টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করত না, আইজ্ঞা ?
টেণ্ডাই-মেণ্ডাই ? তবে আর মগের মুল্লুক কাকে বলে ? তখন তো পুরোদমে চলছে ক্রীতদাস প্রথা। কেনো আর বেচো, হাটে-বাজারে। চালান করে দাও গোয়া কী সিংহলে। পর্তুগিজ-ওলন্দাজদের বাজারে।
মাঝরাস্তায় কেউ কেটে পড়ত না, আইজ্ঞা ?
পালাবে কী! একে তো বন্দুকের নল। তার উপর হাতের তালু ফুটো করে দড়ি গলিয়ে নৌকায় বাঁধা। আর পালাবেই বা কেন ? পেটের দায়ে তো বিক্রি হয়ে গেছে তারা!
বলেন কী আইজ্ঞা ?
হুঁ, নদী-সেপার থেকে যাত্রী নিয়ে নাউড়িয়া যেমন এপারে নৌকার ‘ভরা’ নিয়ে আসে, তেমনি আসত নৌকায় করে ‘চালানী’ মাইয়া-মাইপোদের ‘ভরা’। হাঁস-মুরগিদের মতো গাদাগাদি করে চালান হয়ে যেত হাটে―
কোথায়-কুনমা হাট বসত, আইজ্ঞা ?
কোথায় না, চারুবিটিয়া। তমলুক, আর ‘নরের হাটরু’ ত নরঘাট।
আইজ্ঞা।
চণ্ডীপুর, ভগবানপুর, ময়না, মহিষাদল, ঈশ্বরদহ জালপাই, মৈসালি জালপাই, চুনাখালি, তেরপেখ্যা, বাঘডোবা জালপাই, টেংরাখালি, দ্বিতীয় খণ্ড জালপাই, বাশুলীচক, শ্রীপতিগঞ্জ, হোড়খালি, খাগদা জালপাই―এসব গ্রামের নাম শোনা আছে ?
কিছি কিছি, আইজ্ঞা।
গ্রাম-কে-গ্রাম―সে তাম্রলিপ্ত পরগনণাই হোক আর বালিসীতাই হোক―প্রায় সব তো হালিক আর জালিক কৈবর্তদের বসবাস। হাল আর জাল নিয়েই কারবার।
মশায়ের পূর্ব-পেশা, আইজ্ঞা ?
যথা পূর্বং তথা পরং। আগেও যা এখনও তাই। শ্রীশ্রী বাশুলীদেবীর পূজাপাঠ।
অনুমান হয় আইজ্ঞা, জাতি― ?
কৈবর্ত।
হঁ গ, বলুন না! আমহর বি ‘জালি খাদাল’, কেঁওট আইজ্ঞা। ছোট মুখে বড় কথা―একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ?
বল না। কী কথা ?
আমাদের জাতটার নাকি কোনও পুরোহিত ছিল না। বাঙলার রাজা বল্লাল সেনই এক হাড়ির গলায় পৈতা দি করি তাকু আমারমেনকার পুরোহিত করথান ?
যত সব আফুয়া কথা। হাড়ি-মুচি-ডোম জানি না―তবে জানি বল্লাল সেনই যে আমাদের ‘জাত’-এ তুলেছিলেন―সেটা কতক কতক জানা আছে।
আইজ্ঞা, বলুন না!
তবে শুন। জানিস তো বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। বিবাহের পরে পরেই রাজকার্যাদিহেতু তাঁকে থাকতে হতো দূর বিদেশে। সূর্যদ্বীপের সূর্যনগরে। এদিকে বিরহকাতর পুত্রবধূ পত্র লিখলেন স্বামী লক্ষ্মণকে ।
হঁ, আইজ্ঞা।
সে পত্রে বিরহের কথা লিখিতং ছিল―
‘পতত বিরতঃ বারি নৃত্যান্তি শিথিনো মুদা ।
অদ্যকান্তঃ কৃতাস্তোবা দুঃখ শান্তি করিষ্যতি ॥’
তা বাদে, আইজ্ঞা ?
পড়বি তো পড়, সে পত্র পড়ল গিয়ে বল্লাল সেনের হাতে। পত্র পড়ে শ্বশুর বল্লাল সেন বুঝতে পারলেন পুত্রবধূর অন্তরবেদনার কথা। তৎক্ষণাৎ রাজা ঘোষণা করলেন―
কী আইজ্ঞা ?
সূর্যাস্তের আগে যে বা যারা লক্ষ্মণকে সূর্যদ্বীপ থেকে সত্বর নিয়ে আসতে পারবে―তাকে বা তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।
কী পুরস্কার, আইজ্ঞা ? অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা ?
না না। শুন না! ঘোষণা শোনামাত্রই জালিক কৈবর্তরা তো ‘পাটিয়া’ ‘ভাউলিয়া’ নিয়ে শুরু করে দিল ‘নাউ-দৌড়ানি’।
হঁ, আইজ্ঞা। বাইচ প্রতিযোগিতা। ‘ভাউলিয়া’ আর ‘পাটিয়া’ বাইতে বাইতে সৌউ ‘দেওয়ান-ভাবনা’ পালার গানটা গাইথিলান কী―
‘উড়িয়া যাও রে বনের পাংখী
খবর দিও তারে।
তোমার সুনাই লইয়া যায়
দেওয়ান ভাবনার ঘরে ॥’
হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান তো হচ্ছিলই। উপরন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই ধীবর-জালুয়ারা মহা আনন্দে সূর্যদ্বীপ থেকে পাল তোলা ‘পাটিয়া’ কী ‘ভাউলিয়া’য় ‘নাউ-দৌড়ানি’ খেলে লক্ষ্মণকে এনে দিল তাঁর বউয়ের কাছে, বল্লালের কাছে।
তা’পরে আইজ্ঞা ?
রাজা বল্লাল সেন মহাখুশি। দিলেন তো দিলেন, তাবৎ সূর্যদ্বীপটাই দান করে দিলেন ধীবরদের। আর জাতটাকেও তুলে দিলেন উপরে―
শুধু কী সূর্যদ্বীপ, তমলুক-বালিসীতা-তুর্কা-সুজামুঠা-কুতুবপুরও তো আমাদেরই ছিল, আইজ্ঞা ?
ছিল মানে, এসব রাজ্যের রাজা ও রাজপুরোহিত তো আমরাই! তাছাড়া কেন্দ্রভূমি তো আমাদের। কৈবর্ত বীর ‘দিব্বোক’ তস্য ভ্রাতা ‘রুদোক’ তস্য পুত্র ‘ভীম’―সবাই তো বরেন্দ্রভূমের রাজা। তমলুকের ময়ূরধ্বজ বংশ, ময়নাগড়ের বাহুবলীন্দ্র বংশ, তুর্কাগড়ের গজেন্দ্র মহাপাত্র বংশের বংশধররা তো এখনও আছেন।
আপুন কুন দিয়ার পূজারি রহিথান ?
বাশুলীচকের নাম তো জানা আছে বললি―সেই চকের শ্রীশ্রী বাশুলীদেবী মন্দিরের।
নাম আইজ্ঞা ?
শ্রীযুত বুদ্ধেশ্বর লায়া। ‘নম্বর দেবী ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী। কুমতিনাশিনী সুখসমৃদ্ধিদায়িনী ॥’ নমঃ শ্রীশ্রী বাশুলীয়ৈ নমঃ।
নমঃ আইজ্ঞা!
তোর নামটা তো বললি না ?
আইজ্ঞা, লম্বোদর দলাই। মোকাম বাড়চুনফলি।
দলাই, এতক্ষণে কী বুঝলি ?
আইজ্ঞা, যা বুঝার। আসলে কৈবর্ত জাতটা বীরের জাত।
শুধু কি বীরের জাত! নৌকা বানাতে ও চালাতেও ওস্তাদ। রামায়ণের এক জায়গায় আছে―
‘নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাংশতংশতম্ ।
সন্নদ্ধানাং তথা য়ূনাং তিষ্ঠত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥’
হঁ, আইজ্ঞা।
যন্ত্রের নৌকা বা কলের জাহাজ বানাবার কথা তো মহাভারতেও আছে―
‘সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্ ।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈবির্ব্বশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম ॥’
ভারী খটোমটো, আইজ্ঞা।
আরে না। শুন না! পাণ্ডবরা বারণাবত নগর থেকে বনে এলেন। মা-কুন্তীসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে পারাপারের জন্য নদীর জল মাপছেন পাণ্ডবেরা।
হঁ, আইজ্ঞা।
তখনই নৌকাটা এল। মনোমারুতগামিনী যন্ত্রপতাকাশালিনী (যন্ত্রচালিত ও পালযুক্ত) বাতসহা নৌকা। হাতজোড় করে ধীবর লোকটি জানাল―
“হে মহানুভব! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর আপনাদিগকে
কহিয়া দিয়াছেন যে, ‘তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধন
ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে।’
―হে মহাত্মন্! এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার
দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহে এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে
পারিবেন।”
বলেন কী আইজ্ঞা ? মহাভারতের যুগেও যন্ত্রচালিত ট্রলার ভুটভুটি ?
ছিল বৈকি। এই তো শুনলি মহর্ষি বেদব্যাসের স্বহস্ত লিখিত শ্লোক-‘সর্ব-বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং।’ আরও কী যেন জানতে চাইছিলি, দলাই ?
কালকের পাঠকক্ষের পাঠক্রমটা, আইজ্ঞা।
ও হো, ওই যে―
‘দী কনস্ট্রাকশন অব্ দী শিপ্ মাস্ট বী সাচ্ দ্যাট্
হার জেনরল্ স্ট্রাকচারাল স্ট্রেংথ উইল বি
স্যাফিসিয়েন্ট ফর দী ফ্রী বোর্ডস্ টু বি অ্যাসাইন্ড।
দী ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব দী শিপ মাস্ট
বী সাচ্ দ্যাট্ হার স্ট্যাবিলিটি ইন্ অল্ প্রোব্যাবল্
লোডিং কনডিশন ইজ স্যাফিসিয়েন্ট ফর দী ফ্রী
বোর্ডস্ অ্যাসাইন্ড।
ডিসপ্লেসমেন্ট ঝড
ফর্মূলা =…
৪ দ্ধ ঞচঈ
হোয়ার ঞচঈ ইজ্ দী টনস্ পার সেন্টিমিটার
ইম্যারসন্ অ্যাট দী ওয়াটারলাইন, অ্যান্ড ডিস-
প্লেসমেন্ট ইজ্ ইন্ টনস্।’
কিছি কী বুঝা গেলা, দলাই ?
হঁ, আইজ্ঞা। যেমতি কলকাতার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের হাওড়া-শালিখার ‘ক্যালিডনিয়ন ডক-ইয়ার্ড’-এর ‘নক্সা জাহাজ’। আমানকার পাটিয়া, ভড়, ভাউলিয়া, ট্রলারনু উঁচা―
২৩
লোকদুটি দরজা হাট করে খুলে রেখে কথা কইতে কইতেই স্থানান্তরে অন্তর্হিত হলো। আর আমি অগাধ বিস্ময়ে তাদের যাত্রাপথের দিকে বেবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভাবছি―
এরা কারা ? কারা ? দেখতে তো বড়জোর আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম বড়োডাঙা কী চঁদরপুরের ‘হাটুয়া’ জনমানুষ নাউড়িয়া মনাবধুক নচেৎ আখের গুড় প্রস্তুতকারক গুড়িয়া সরো বেহারার মতো।
কিন্তু তুখোড় মুখে যে রোহিণী চৌধুরানী রু´িণীদেবী হাইস্কুলের দোর্দণ্ড প্রতাপ হেডমাস্টার শ্রীউমেশচন্দ্র দে, ট্রিপল্ এম. এ মহাশয়ের মতোই ‘বোম্বাস্টিক’ ইংরাজি বলে!
কখনও সংস্কৃত―
কখনও কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র বিরচিত ‘বাশুলীমঙ্গল’ গীত আউড়ায়। আবার কখনও নেহাতই ‘হাটুয়া’ ভাষায় জাহাজ তৈরির ফর্মুলা শোনায়।
এবম্বিধ কাণ্ডকারখানা ও কেরামতি দেখাতে দেখাতে কখন যে হুট করে মাথার খুলিটাও খুলে ফেলল! ফের ক’ মিনিট বাদে ইচ্ছামতো খাপে-খাপ লটকেও নিল।
কোনও অসুবিধাই হলো না।
তা না হয় হলো। তা বলে এই পোড়োগৃহেই বা কেন ? আগামীকালের পাঠ-কক্ষের ‘পাঠ’টাই বা কী ?
দেখে শুনে মনে তো হয়―জাহাজ তৈরি বা মেরামতির কোনও কারখানা বা কামারশালা আছে এখানে। বিশেষ করে কলকাতার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের হাওড়া-শালিখার ‘ক্যালিডনিয়ন ডক-ইয়ার্ড’-এর ‘নক্সা জাহাজ’য়ের কথা যখন তুলল।
বলাই বাহুল্য, দেখতে এদের আদার বেপারী মনে হলেও আদতে বুঝি জাহাজের কারবারিই বটে।
তার উপর বল্লাল সেন-লক্ষ্মণ সেনের ইতিহাসও জানে দেখছি।
জাহাজ তৈরির কলকব্জা কোন বই থেকে ‘কোট’ করছে―তা ধরতে না পারলেও, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের ‘পদার্থ বিজ্ঞান’ পড়া থাকায় ‘জাহাজ জলে ভাসে কেন’―তার কলকব্জা আমারও যৎকিঞ্চিৎ জানা বৈকি।
সেই তো একই ব্যাপার―
একটুকরো লোহা জলে পড়লেই ডুবে যায়।
অথচ লোহার তৈরি অতবড় জাহাজ ডোবে না কেন ?
এখানেও আর্কিমিডিসের সেই একই ভাসন-নীতি।
‘কোনও বস্তুকে স্থির তরলে আংশিক অথবা পূর্ণ নিমজ্জিত
রাখিলে ঐ বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস হয় এবং এই হ্রাস
বস্তুটি যে আয়তনের তরল স্থানচ্যুত করে তাহার ওজনের
সমান।’
জাহাজ জলে ভাসার কারণও তাই―জাহাজের তলদেশ কড়াইয়ের মতো চ্যাপ্টা। সে কারণে যথেষ্ট পরিমাণ জলও অপসারণ করতে পারে। সেই অপসারিত জলের পরিমাণ জাহাজের ওজনের সমান।
জাহাজ তাই ভাসে, ডোবে না।
ধরা যাক, কোনও জাহাজ যদি ৮০,০০০ কিগ্রা জল অপসারণ করতে পারে, তবে নিজের ভর, মালপত্র ও প্যাসেঞ্জার সহ ৮০,০০০ কিগ্রা ওজনের জাহাজও জলে ভাসতে পারবে।
প্রশ্ন আসে―[১] নদীজলে সাঁতার কাটার চাইতে
সমুদ্রজলে সাঁতার কাটা সহজ কেন ? [২] সমুদ্রজল
হইতে নদীজলে আসিলে জাহাজ ডোবে কেন ?
সেটাও আবার নির্ভর করে জলের ঘনত্বের উপর। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ঘনত্বের চেয়ে নদীর পরিষ্কার জলের ঘনত্ব কম। তাই প্লবতাও কম।
সেহেতু নদীজলে জাহাজের বেশি অংশটাই ডুবে যায়। তার উপর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদী কি সমুদ্র হলে তো কথাই নেই। নদীর খাঁড়িতে ঢুকেও জাহাজডুবি ঘটে।
যেমনটা ঘটেছিল আমাদেরই গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত থুরিয়ার মহিষাসুর ‘দঁক’-এ।
ওই যে ‘তপোসা’ আর ‘পালেকাথ’ নামের দুই ওড়িয়া সওদাগরের জাহাজ ‘আদজেত্তা’ বন্দর থেকে ‘সুয়োমা’ অর্থাৎ ‘সুহ্ম’ দেশে যাবার পথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের জোয়ার ও বাত্যাতাড়িত হয়ে ঢুকে পড়েছিল সুবর্ণরেখার খাঁড়িতে। শুধু ঢুকে পড়াই নয়, আছড়ে ভেঙে পড়েছিল আমাদেরই গ্রামের মহিষাসুর ‘দঁক’-এ।
সেই তো ডুবে গেল। অচেনা অজানা বীজদানা, নাকি আরও কীসব নিয়ে মাটি চাপা পড়ল। ‘বালিপোত’ হলো।
তারপর তো তার উপর নানাবিধ গাছ জন্মালো। অর্জুন, পাকুড়, শাল, মহুল, ডুমুর, শিমুল নয়―অজানা অচেনা সব বীরুৎ বৃক্ষ!
সেই থেকে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে, ফিন-ফোঁটা-জ্যোৎস্নাধারায়, এমন কী নিকষকালো অন্ধকারেও দিন-ক্ষণ-মুহূর্ত দেখে ঝলসে উঠতে লাগল―উঠতে লাগল কী, এখনও ঝলসে ওঠে ভেঙে পড়া ডুবে যাওয়া সেই জাহাজের কানা!
সেই বলে না―
‘কে দেখেছে ? কে দেখেছে ?’
‘দাদা দেখেছে। দাদার হাতে কলম ছিল ছুড়ে মেরেছে।’
দাদা-দিদি কীনা জানি না―যেই দেখেছে সেই নাকি উন্মাদ ও বিবাগী হয়ে দেশান্তরী হয়েছে।
তবে এখন আর স-সাগরা সে সুবর্ণরেখাও নেই, সুবর্ণরেখায় সে জোয়ারও আসে না, সে ভাটাও পড়ে না। জাহাজই বা কোথায় ?
আছে তো বড়জোর কটা ডোঙা-ডুঙি ভেলা-ভেউরি পাটিয়া-পানসী। তাও তো শীত পড়তে না পড়তেই নদীর জল একহাঁটু!
তখন নাউড়িয়া মনা বধুকের নৌকা, জালুয়া ঝাড়েশ্বর কী মাধব পানীর মাছ মারার পাটা, গুড়ের কারবারি সরো বেহারার পাটিয়া, পানসী, ভাউলিয়া, ডোঙাডুঙি, বাছাড়ি, জালিবোট―
সব, সব তো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে নদীর বালিতে। হয় মেরামতি কাজের জন্য নয় রং মাখাতে।
বুদ্ধেশ্বর লায়া, লম্বোদর দলাই―না জানি এরা কারা ? কোন দিয়া বা দিগরের ? বলল তো বাশুলীর চক, বাড়চুনফলির!
বোধকরি এদের ‘দ্বিজত্ব প্রাপ্তি’ বা শুদ্ধিকরণ ঘটে গিয়েছে, আমার এখনও সেসব ঘটেনি। তাই হয় তো এরা আমাকে চিনতে পারছে না, বা চিনেও না চেনার ভান করছে।
কোনও রকম কথাই কেউ আমাকে বলছে না। অথচ নিজেদের ভিতর খুলি থাকল কী থাকল না―কোনও কিছুতেই কথা তাদের আটকাচ্ছে না। অনর্গল তো বকেই চলেছে!
হালচাল, কথাবার্তা শুনে এতক্ষণে বোধগম্য হতে কিছু বাকি নেই আমার―নির্ঘাত কোনও জরুরি কাজে নিযুক্ত আছে তারা।
কোনও ঠিকাদার তাদের ধরে এনে নিযুক্ত করেছে। আর কাজটাও কঠিনস্য কঠিন বটে। যার দরুন ‘পাঠ’ নিতে হচ্ছে নিয়মিত। বুঝতে অসুবিধা নেই―সে ‘পাঠ’ অবশ্যই জাহাজ তৈরি বা মেরামতি সংক্রান্ত।
আগামীকাল সকালের পাঠকক্ষের পাঠ্যসূচির বহর দেখে তো ওইরকমই বোধ হচ্ছে। ‘ঞযব পড়হংঃৎঁপঃরড়হ ড়ভ ঃযব ংযরঢ় সঁংঃ নব ংঁপয ঃযধঃ যবৎ মবহবৎধষ ংঃৎঁপঃঁৎধষ ংঃৎবহমঃয―’
কিন্তু কল-কারখানার কুলি-কামিনদের বস্তি, শিক্ষানবিশীদের ‘সেল’, শ্রমিকদের কোয়ার্টার ‘খিলান ধাওড়া’, হাজারীবাবু- লোডিংবাবু-তংখাবাবুদের হাতায় বা খাতায় তো আর এক-দুজন থাকে না, থাকে তো বুদ্ধদেব লায়া, লম্বোদর দলাইয়ের মতো আরও একশ, দুশ―
হাট-খোলা দরজা দিয়ে বিনা বাধায় তো নিষ্ক্রান্ত হলাম―ঘুরে বেড়িয়ে দেখিই না এই পোড়োবাড়িটার আনাচে কানাচে বুদ্ধদেব-লম্বোদরদের মতো আর কেউ কোথাও আছে কীনা।
কুহররত পায়রা-পারাবত বাদুড়-চর্মচটিকার ভদভদানি তো শুনেছি একবার নয়, একাধিকবার!
নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই একরাশ খোলামেলা হাওয়া যেন আমাকে সমাদরে গ্রাস করল। দরজাটাও খোলা থাকল। পায়েও অদৃশ্য ঝিঁজরির টান আর তেমন অনুভূত হলো না।
এই রে! মুক্তি কি তবে এসে গেল ? এপাশ ওপাশ পা ছোড়াছুড়ি করেও দেখলাম বারকতক―কই ? কেউ তো অদৃশ্য ঝিঁজরি ধরেও টানছে না আর ?
মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! খানকতক পায়রা ভদভদিয়ে উড়ে এসে মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। মুক্তির স্বাদ যেন তারাও পেয়ে গেছে আমার মতো।
একদিকে পায়রার ভদকানি, আরেক দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ধুলামন্দির’ কবিতাটা আমার মুখে ‘শতজল ঝর্নার মতো উৎসারিত’ ও উচ্চারিত হতে লাগল।
কাকে যে চেঁচিয়ে জোরে জোরে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি―
‘ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে!
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে―দেবতা নাই ঘরে ॥
… … …
মুক্তি ? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!’
কক্ষ থেকে কক্ষান্তরের পাশ দিয়ে, যেমনটা অদৃশ্য ঝিঁজরি আমাকে টেনে এনেছিল সকালের দিকে, তারও চেয়ে জোরে, আরও জোরে দৌড়াচ্ছি।
কোথাও রুদ্ধদ্বার, কোথাও বা অবারিত। দীপাধারে আলো জ্বলছে, কোথাও বা নির্বাপিত। কিন্তু বুদ্ধেশ্বর লায়া আর লম্বোদর দলাইয়ের মতো মাথামুণ্ডহীন লোকজন তো আর দুটো দেখি না।
অথচ কতই না কোলাহল-কলরব শুনছি―
টিকে গুড়াখু দিবু ?
কেনে, তোর ডিবার কী হেলা ?
কঁঠে যে রাখনু! মনে পড়েটেনি রে!
হায় দ্যাক্! মোর ত আকবর গুড়াখু। মাজি পারবু ত ?
ম’লা! ‘ন দবু ধন, কহিবু দিব্যবচন’।
আচ্ছা, নে তাইনে―
‘ছাই ছাড়,
গুড় কাড়।
ছাই মোর হাতে
গু তোর দাঁতে।’
এই রে! এরা আবার কারা ? জোড়ায় জোড়ায় যেন বসে গেছে গুড়াখু-হাতে দাঁত মাজতে ঝিলের ধারে। এমনটা দেখেছি বটে আমাদের ইস্কুল হোস্টেলে, ডুলুং নদীর ধারে।
ইস্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ল কী পড়ল না, বইখাতা হাতে হোস্টেলের বোর্ডাররা যে যার ঘরে পৌঁছাল কী পৌঁছাল না, তামাকের গন্ধে তো ভরে উঠল ডুলুঙের পাড়!
উঁহু, তামাক-তম্বাকু-তামুক-তামাকু কী আর, গুড়াখু―গুড়াখু, গুড়াখু। নামটাতেই কেমন একটা ওড়িয়া মাদকতা আছে।
না হলে বোর্ডাররা, শুধু কী বোর্ডাররা, আশপাশের গ্রামের লোকেরাও ডান হাতের তর্জনীর ডগায় আফিমের গুলিসদৃশ গুড়াখুর মাজন বা মাঞ্জন লটকে নিয়ে বেলাবেলি এসে যায় ডুলুঙের তীরে।
‘কালিন্দীসলিলকান্তিকলেবর কৃতকুসুমাবলী বেশ!’ অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে মুখ করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যায় সার সার।
তারপর ক্রমান্বয়ে ডাহিনে ও বামে
তারপর ক্রমান্বয়ে ডাহিনে ও বামে চালিত হতে থাকে, হতেই থাকে হতেই থাকে তাদের গুড়াখুরঞ্জিত আঙ্গুল।
গুড়াখুর গুলি ক্ষয়িত হতে থাকে, হতেই থাকে হতেই থাকে, তবু ভুলেও বেমক্কা আলটপকা খসে পড়ে না আফিমনন্দিত তর্জনীধৃত গুড়াখুর গুলি!
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। ঝপ করে রাত্রি নেমে আসে। কেউ কেউ তখনও বসে থাকে, বসেই থাকে।
ইস্কুল হোস্টেলের বোর্ডাররা তো রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে গুড়াখু আঙ্গুলে লটকে আবারও একবার এসে যায় নদীধারে।
ডুলুঙ নদী-সেপারে আখুবিলে তখন ফিঙা ডাকে, রট রট করে শিয়াল আখু ভাঙে।
কিন্তু এই পোড়োগৃহের পুষ্করিণীর পাড়ে এখন জোড়ায় জোড়ায় বসে গুড়াখু হাতে নিয়ে ‘রাতালাপ’ করছে কারা ?
পুষ্করিণীর রাত্রিজলে তাদের ছায়া পড়েছে কী ?
দেখিই তো!
২৪
প্রত্যুষে, জল থেকে নিষ্ক্রমণের পরে, ডাঙায় উঠে মহেঞ্জোদাড়ীয় গো-শকটে চড়ে বাস্তুভিটা, মাঝেমধ্যে খিলক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষিভূমি সমন্বিত এক বৃহদাকার গঞ্জের ভিতর দিয়ে যখন এই পোড়োগৃহে আনীত হলাম, তখন বলা বাহুল্য―
না এই গৃহে, না গঞ্জে, না রাস্তায় ঘাটে তো একটাও লোক দেখি না। তবে জলভ্রমি ডাঙার মানুষ, ঘরের মানুষ যে এইমাত্র জোটিকা বা খালের ঘাটে ডোঙাডুঙি পাটিয়া বেঁধে ঘরে ফিরল, তার পায়ের চাপে সদ্য বাঁধা ডোঙা-ডুঙি পাটিয়া যে যৎসামান্য এখনও নড়ছে, টলমল করছে―তা অবশ্যই টের পেয়েছিলাম।
আম্রতলে, কানঠাড়ী ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পেতে কেউ না কেউ নিদ্রা যাচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ উঠে যাওয়ায় তার পেটে পিঠে দড়ির ছাপ নির্ঘাত লেগে থাকবে, যেন হাঁক দিলেই সে বাইরে আসবে আর তার দেহে দড়ির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাবে।
রৌদ্রে, দড়িতে কী তারে, মেলে দেওয়া শাড়ি-সায়া-সেমিজ গামছা-লুঙ্গি এতক্ষণ দিব্য শুকোচ্ছিল, কে যেন টান মেরে এক ঝটকায় কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেছে, হ্যাঁচকা-টানে কাপড় শুকাবার তার যে তরঙ্গ তুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝনঝন করে, তখনও কাঁপছে, নাচছে, ওঠানামা করছে―তাও তো স্ব-চক্ষে দেখেছিলাম বটে।
আর―
পুষ্করিণীর জলের ধারে কলমি-শুশনি লহ লহ করছে, জলপিপি উড়েঘুরে বেড়াচ্ছে, কাদাখোঁচা চিক চিক চিকা-চিকা-চিকা রবে মুহুর্মুহু ডাকছে―
এই পোড়োগৃহ বা সংঘারাম থেকেই তো কত পায়রা-পারাবত বাদুড় চর্মচটিকা ভদভদিয়ে ডানা ফেটিয়ে উড়ে গেল, আবারও ফিরে এল―সেসবও তো একসময় দেখেছি! এবার তো কী ঘরে কী বাইরে সশরীরে মানুষ দেখছি। মানুষ, মানুষ।
তবে কীনা মাথামুণ্ডহীন মানুষ। এখন যারা পুষ্করিণীর পাড়ে জোড়ায় জোড়ায় বসে গুড়াখু মাজছে, মাজতে মাজতে দিব্য কথা বলে চলেছে, কথা বলতে বলতে হয়তো ফের হেলমেটের মতো মুণ্ডুটা গলিয়ে নিচ্ছে।
এখন দেখতে হবে পুষ্করিণীর রাত্রিজলে তাদের ছায়া পড়েছে কী না! আচ্ছা, ছায়া দেখার কথা উঠল কেন ? তবে কি তারা অশরীরী ? প্রেতাত্মা ?
প্রেতাত্মাদের ছায়া পড়ে না। ছায়া পড়ে না ডাইনিদেরও। মা-কাকিমারাই তো এবম্বিধ বলত।
আমাদের গ্রাম বাছুরখোয়াড়ে যে কজন স্ত্রীলোক ‘ডাইনি’ বলে এ পর্যন্ত বিবেচিত হয়ে আসছে, যেমন ধরো ফাটাদার বুড়া―
মুখের চেহারা, শরীরের চেহারা―কুঁচকে মুচকে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে যাওয়া, চোখদুটিও মার্বেল-গুলি, বিড়ালাক্ষী, লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটা।
দৈবাৎ পথিমধ্যে কোথাও দেখা হয়ে গেলে খনখনে গলায় আগ-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করা, নচেৎ ফটাস করে থুতনি ধরে চুমু খাওয়া―‘কী গো স্যাঙাৎ, কুন বাটিয়া যাবা ?’
আমি থতমত খেয়ে বলি―
‘এই তো―একটু এদিকে ―’
পরক্ষণেই তার শরীরের ছায়া খুঁজি―ছায়া, ছায়া―হয়তো অপরাহ্ণ, পড়ন্ত বেলায় দীর্ঘ ছায়া পড়েছে তার। ছায়া পড়েছে তার লম্বা লাঠিটারও।
দশরথের বউ। কতই বা বয়স তার! বড়জোর ছোটকাকির সমান সমান। সুঠাম ও সুন্দর দেহ। মাগুর মাছের মতোই গায়ের রং। তেমনি খলবলি।
লোকে তো বলে―সে নাকি ডাইনি! যে সে ডাইনি নয়, পাক্কা ডাইনি। রাতভিত দশরথের অজান্তে সে নাকি ঘরের ‘বাহির’ হয়ে যায়।
নাকি আর আর ডাইনিদের সঙ্গে বনধারে কী বনের ভিতরে ‘চরতে’ যায়। চরতে চরতে গরুছাগলরা যেমন ঘাস, বনের লতাপাতা খায়, ডাইনিরা খায় গু।
গু, গু।
দেহ উল্টে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে জিভে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে তারা উলঙ্গ হয়ে চরে। সে সময় কারও সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয় যদি তো সে মরে।
রাত না পোহাতেই তার মরণ! ডাইনি বা ডাইনিরা চেটেপুটে খেয়ে নেয় তার কলজেটা। এমন এমন যে দশরথের বউ সেও সময় সময় বড় আদর করে আমাকে ডাকে―
‘আয়! আয় না রে ললিন! গাছের আমটা, কলাটা খেয়ে যা!’
রৌদ্রে, পরনে নীল খুরদা শাড়ি, মাথায় এক হাত রেখে আরেক হাত দিয়ে সে-হাতের আঙ্গুলগুলো ধরা, খলা-খামারে দাঁড়িয়ে মনোহরণ ভঙ্গিতে সে ডাকে। ভারী লোভাতুর সে-ডাক!
ডাক শোনামাত্রই আমি তার শরীরের ছায়া খুঁজি―ছায়া, ছায়া―‘ছায়া ঈশ্বরীর মতো’। কোথাও পাই না। মধ্যাহ্ন-সূর্য যে তখন মাথার উপর! ছায়াও ছোট হতে হতে মিশে গিয়েছে দেহে।
রাত্রে, এই পোড়োগৃহ কী সংঘারামের পশ্চাতে পুষ্করিণীর জলে তামাকু-মাঞ্জনকারী এই সমস্ত মাথামুণ্ডহীন লোকেদের ছায়া পড়েছে কী না―
তা দেখার দরুন নিজে নিজেই একটা সবিশেষ উদ্যোগও নিলাম। এধার ওধার ইতস্তত ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করছি―উঁহু, দেখা কী যায়!
জলাশয়ের আবদ্ধ জলে জ্যোৎস্নাধারায় মৃদুমন্দ সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হতে হতে তা যেন ভেঙেচুরে একশা হয়ে যাচ্ছে। আর নয়ত মাথামুণ্ডুহীনদের ছায়া বা ছায়াহীনতা অতদূর জলাশয়ের জলের তল পাচ্ছে না।
অথচ পোড়ো বাড়িটার শতাধিক গবাক্ষবাহিত দীপাধারের আলো তো ঠিক জল ছুঁয়ে ফেলছে!
ছায়ার হদিস পাই বা না পাই, কান পাতলাম গুড়াখু-মাঞ্জনকারীদের কথালাপ শুনতে―কে কী বলছে, কী সব বলাবলি করছে!
তারা যে ডুলুঙ নদীতীরবর্তী রোহিণী চৌধুরানী রুক্মিণীদেবী হাইস্কুল হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রদের মতোই পুষ্করিণীর তটে বসে গুড়াখু মাজছে―তারই বা খোঁজ পেলাম কী করে ?
আরে বাবা, একে তো ‘আকবর গুড়াখু’র নাম শুনলাম, তার উপর তার গন্ধ। গন্ধে যে পুষ্করিণীর সারা পাড় ম ম করছে! রোহিণী হাইস্কুল হোস্টেলের বোর্ডার হিসাবে আমিও যে কম-বেশি ভুক্তভোগী, ওই রকমই নেশাখোর।
গন্ধ শুঁকেই বোধ হচ্ছে তর্জনীর ডগা তামাকু রঞ্জিত করে তাদের সঙ্গে আমিও বসে যাই! তাদের দলে ভিড়ে আমিও কথায় কথায় রাজা-উজির মারি। যেমনটা আফিংখোর কমলাকান্ত।
ক্লাস নাইন-টেনেই তো পড়েছি―
আমি শয়নগৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া,
হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্
মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে―দেয়ালের
উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার
প্রস্তুত হয় নাই―এইজন্য হুঁকাহাতে, নিমীলিত
লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি
নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে
পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ
হইল, ‘মেও!’
চাহিয়া দেখিলাম―হঠাৎ কিছু বুঝিতে
পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন
হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট
আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে,
পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে,
ডিউকমহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার
দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার
দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত
লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, ‘মেও!’
তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম
যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন
আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা
নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন
ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই।
এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত
হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার
অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ‘মেও!’
দুটিই মাদক জাতীয়। নেশার দ্রব্য। একটা খাওয়ার, আরেকটা মাজার। গুড়াখু মাঞ্জনে দাঁত মাজতে মাজতেও একরকম নেশা হয়, মাথা ঘুরে যায়।
ঘোরের মাথায় লোকে তখন কত কী ভাবে! কত কী অনর্গল বকে যায়! উৎকর্ণ হয়ে শুনছি, কে কী বলছে। যেমনটা শুনছিলাম বুদ্ধেশ্বর লায়া আর বাড়চুনফলির দালাইয়ের কথোপকথনের মধ্যে।
সার বুঝেছিলাম―তারা এই আশপাশের মানুষজন, আদার বেপারি হলেও জাহাজের কারবার করে।
নচেৎ ‘কনস্ট্রাকশন অব্ দী শিপ্’ নিয়ে মাথা ঘামায় ? অমন ইংরাজিতে চোখা চোখা কথা বলে ? তারপর এই তো গুঁড়াখু-আকবর গুড়াখু-নিয়ে ঘরের ধারের ‘হাটুয়া’ ভাষায়―
কী যেন, কী যেন বলল―
‘ছাই ছাড়
গুড় কাড়।
ছাই মোর হাতে
গু তোর দাঁতে ॥’
এমনটা কত শুনেছি হাটুয়াদের গ্রাম বড়োডাঙার ছা-ছুয়াদের মুখে!
‘ওলো ওলো শাঁখা হাতি!
তোর কাঁখে পো না নাতি ?
এঙ্কর বাপো যাঙ্কর শ্বশুর
তাঙ্কর বাপো আমার শ্বশুর।’
তবে কি তারা ‘হাটুয়া গ্রাম’ বড়োডাঙা, চঁদরপুর, থুরিয়া, মলম, ঝরিয়া, কলমাপুখুরিয়া, লাউদহ, কালরুই, ঢেরাছাড়া কী কুলবনীর লোক ?
নদীধারের লোক ? নদীর মানুষ ? ডিঙি-ডোঙা- পাটিয়া-ভেলা- ভেউরি-জালিবোট-লৌকা-পানসী, এমনকি জাহাজ নিয়েও তারা কারবার করে ?
বাশুলীচকের বুদ্ধদেব লায়া আর বাড়চুনফলির লম্বোদর দলাইয়ের কথাবার্তায় তো এতক্ষণ কলকাতার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের হাওড়া-শালিখার ‘ক্যালিডনিয়ন ডক-ইয়ার্ড’-এর ‘নক্সা জাহাজ’য়ের প্রসঙ্গও উঠে আসছিল!
পুষ্করিণীর পাড় থেকে গুড়াখুমাঞ্জনকারী একজোড়া এইমাত্তর উঠে এসে আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের দুজনের একজন পরিষ্কার চাঁদের আলোয় কী একটা পুস্তক পড়ছিল―
‘ভোর চারটে থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে
বেলা প্রায় দুপুর আন্দাজ সাগরদ্বীপে এসে
পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরে একখানি পানসী
নৌকা এল, …বেলা দুটোর সময় আমরা
সকলে মিলে পানসীতে করে কলকাতা অভি-
মুখে যাত্রা করলাম। পানসীতে যেতে আমার
আপত্তি ছিল, কারণ বাঙলাদেশের এই বিচিত্র
নৌকাটি এমনভাবে তৈরি যে তারমধ্যে সোজা
হয়ে বসা যায় না, অথবা রোদবৃষ্টি থেকে
নিজেকে রক্ষা করা যায় না। এমনকি পা ঝুলিয়ে
একটু আরাম করে বসাও সম্ভব নয়। তবু
পানসীর অভিনবত্বের জন্য এই অসুবিধাটুকু
আমাদের সয়ে গেল। ছ-জন ‘কালা আদমী’
খুব জোরে জোরে দাঁড় বাইছিল, পানসীও
চলছিল র্ত র্ত করে দুরন্ত বেগে।’
চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম―দুজন মাথামুণ্ডহীন মানুষ। তাদের মাথার খুলিগুলো হেলমেটের মতো হাতেই ধরা।
২৫
কী পড়ছিল তারা ? কোন পুস্তক ? যে পুস্তকে লেখা আছে ‘কালা আদমীদের’ কথা ?
‘কালা আদমী’ তো আমাদেরই বলত ইংরেজরা। ব্ল্যাক। নেটিভ। মনে হয় পুস্তকটি কোনও ইংরেজ সাহেবসুবোর জলপথে ‘ভ্রমণ কাহিনি’ই হবে।
যখন উল্লেখ শুনি সাগর, সাগরদ্বীপ, পানসী, দাঁড়িমাঝিদের কথা। আর পুস্তকে যতরকম ভেলা-ভেউরি ডোঙাডুঙি পাটিয়া, এমনকি ময়ূরপঙ্খী, হাঙ্গরমুখী, রণতরী, ভ্রমণতরীর ছবি দেখেছি―দাঁড়-হাতে পাল-হাতে তাদের চালকরা, দাঁড়ি- মাঝিরা মাথায় পাগড়ি বাঁধা, খালি গা―সবাই তো ‘কালা আদমী’!
কেন ? আমাদের বড়োডাঙার শিমুলতলীর ঘাটে সুবর্ণরেখা নদীতে হংসী নাউড়িয়ার পানসির দাঁড়িমাঝিদেরও তো পোড়া আঙরার মতো ভুসভুসে কালো গায়ের রং। কালো না ?
কালো, কালো। ‘কালা আদমী’।
‘কালা আদমী’―আর তো বলে ক্রীতদাসদের! একসময় পৃথিবীর কোথায় না দাসপ্রথা বা দাসব্যবসা প্রচলিত ছিল! দরদাম করেই কালো তথা প্রান্তিক মানুষদের ক্রয়বিক্রয় হতো।
ইতিহাস তো বলে অত বড় গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্য-সভ্যতাটাই নাকি দাসনির্ভর। গবাদি পশুর মতোই অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী ছিল ক্রীতদাসরা।
অতদূর কেন ? এই তো একটু আগে বাশুলীচকের বুদ্ধেশ্বর লায়া আর বাড়চুনফলির লম্বোদর দলাইয়ের কথোপকথনের মধ্যেই তো উঠে আসছিল ‘নরের হাট’ তথা নরঘাটে মানুষ কেনাবেচার গল্প।
‘নরের হাটে’ আমাদের মতো ‘কালা আদমীদের’ কিনে মাইয়া-মাইপো বাছ-বিচার না করে এক পানসিতে গাদাগাদি করে ঠেসে হাঁসমুরগির মতো চালান করে দিত গোয়া কী সিংহলে ওলন্দাজ-পর্তুগিজদের বাজারে।
তারপর তো তাদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার! এহেন দাসরাও যে একসময় বিদ্রোহ করে উঠবে―তাতে আর কী আছে অবাক হওয়ার ?
রোমে ‘দাসবিদ্রোহ’র কথা আমরা তো নিচু ক্লাসের ইতিহাস বইয়েই পড়েছি―
“প্রশ্ন : রোমে দাসদের অবস্থা কিরূপ ছিল ?
স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রোমান দাসদের
বিদ্রোহের কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
উত্তর : রোমের অধিবাসীদের একটা বড় অংশই
ছিল ক্রীতদাস। তাদের নাগরিক অধিকারই
ছিল না। তারা ছিল কেনা গোলাম। প্রভুদের
একচেটিয়া সম্পত্তি। তাদেরই খেতখামারে
চাষাবাদের কাজ করত। রাস্তাঘাট তৈরি
থেকে যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ তারাই করত।
কাজ, খাবার আর শাস্তি―এই যেন তাদের
বরাদ্দ ছিল! শাস্তি মানে বেকসুর চাবকানো
থেকে মানসিক পীড়ন আর হত্যা। ফলত
ক্রীতদাসরা মাঝেমাঝেই বিদ্রোহ করত। দাস
বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য―
‘স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ’। থ্রেসীয় বন্দি স্পার্টাকাসের
নেতৃত্বে লক্ষাধিক দাস দুবছর কাল ধরে রোমকে
নাস্তানাবুদ করে রোমের পতন প্রায় আসন্ন
করেছিল―”
যাত্রাদলের নায়ক শান্তিগোপাল অভিনীত ‘স্পার্টাকাস’ যাত্রাপালাও তো দেখেছি! ‘টমকাকার কুটির’ও পড়েছি―
টম, হ্যারি, এলিজা, জর্জ হ্যারিস, ক্রো, হ্যাগার, জন, বেন, সাউল, অ্যালবার্ট, ফিনিয়াস, মাইকেল, রোজা―কতসব নিগ্রো ক্রীতদাসদের নাম!
তারা তো কালোই। সব ‘কালা আদমী’।
‘কালা আদমী’দের পুস্তক পড়তে পড়তে একজোড়া চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরে পরেই পুষ্করিণীর জলে হাত-মুখ প্রক্ষালনের পরিচিত আওয়াজ উঠল।
কারা যেন ‘কুলকুচা―মুখে বদ্ধ ও আলোড়িত জলের শব্দ’ ‘কুল, কুলকুল’ এবং জলত্যাগের শব্দ ‘কুচ্’―কুলকুচো’ করল। (বি: দ্র: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’) ।
পরক্ষণেই যথা পূর্বং আমারই পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুজনের একজন অপর একজনকে ‘আগো’ সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করে ―
‘আগো শুনছনি ?
অষ্ট হাঁটু ষোল চরণ,
মাছ ধরতে গেলা লাল্টুলাল।
শুকলা ভুঁইর জাল পাতি গি,
মাছ ধরলা চিলকাল ॥’
নারীকণ্ঠ। উত্তরে পুরুষটি বলল―
‘হ, ছালিয়ার মা। শুনি থায়। সে তো গুট্যে ‘ধাঁধা’। যার উত্তর হেলা―মাকড়শা’।
‘না গো। ধাঁধা না। সত্যি সত্যিই আজ মুই নদীরু ‘সতীবাঁধা’ মাছ ধরলি দুপহরকু। চানাচুনা মাছ। অউ সঞ্ঝাবেলা রাঁধমু। খাইগি দেখহ।’
ভালা হিলা। চানাচুনা ‘সতীবাঁধা’ খাইগি আজ রাতকু মুই ‘উকা’য় যামু। বড় বড় ডাঁটিয়াল মাছ ধরবা।
নারী-পুরুষ। বোধকরি স্বামী-স্ত্রী। তবে এরাও কি এই পোড়োগৃহে তথা সংঘারামে থাকে ?
সংঘারামে কি ভিক্ষুনীরাও থাকে ? আগে আগে ছিল না, পরে পরে ‘চল’ ছিল সবকিছুরই। কেন ? অম্বপালী-বিশাখা-সুজাতারা ছিল না ?
ছিল, ছিল। তা বলে―‘ছালিয়ার মা, ছালিয়ার বাপ’―এরা তবে কারা ? ‘সতীবাঁধা’ ‘উকা’য় মাছ ধরার কথা বলে ? লোকগুলোও যেন একরকম চেনা, তাদের মুখের ভাষাটাও চেনা-চেনা লাগে।
এরাও এই পোড়োগৃহে কী সংঘারামের অন্দরে থাকে ? নাকি ওই অদূরবর্তী গঞ্জে ? কী ভেবে তাদের পিছু পিছুই হাঁটতে লাগলাম।
তারা বেশ তো ‘সতীবাঁধা’ তার মানে চানাচুনো মাছ ধরার কথা, ‘উকা’য় বড় বড় মাছ ধরতে রাত্রিবেলা নিষ্ক্রমণের কথাও বলছিল।
বর্ষাকালের নদী শুখা মরশুমে এসে ছিঁড়ে যায়। স-মাছ স-জলজ উদ্ভিদ, ঝাঁজি-শ্যাওলা নিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ফালিগুলো নদীর মূলধারা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়, হতে থাকে।
অতঃপর ছেঁড়া ছেঁড়া জলাধারগুলি স্থানীয় মেছো মেছুনীদের নজরে ও অধিকারে আসে। তারা তার-উপর তাদের শ্যেনদৃষ্টি ফেলে রাখে।
মাঝেমধ্যেই অকুস্থলে হাজির হয়ে আয়নার মতো স্বচ্ছ জলে চাক বেঁধে ছোট ছোট মাছেদের খেলা দেখে।
মেছুনীরা সময় সময় হাতের তালি বাজায় আর মন দিয়ে দেখে―কেমন র্স র্স ক’রে চানাচুনো মাছগুলো ঝাঁজি-শ্যাওলার ‘দঁক’-এ চকিতে লুকিয়ে পড়ে।
সময় সুযোগমতো তারা জলাধারগুলিকে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে বিভক্ত করে। যে যার সে তার। যাকে বলে ‘সতীবাঁধ’।
একদিন কিছুটা জল ছেঁচেও নেয়। তারপর তার সঙ্গে গুড়মন গাছের রস নিঙড়ে মিশিয়ে দেয়।
গুড়মন গাছ হলো একপ্রকার মাদক গাছ। ছোট ছোট এক-দেড় হাত উঁচু, ঝাঁপুড় ঝুপুড় গাছ। ধনিয়া ফলের মতো তার ফল।
চটকে মটকে রস নিঙড়ে জলে গুলে দিলেই হলো! ছোট ছোট জ্যান্ত জলে সঞ্চরমান মাছগুলো আফিমখোরের মতো ত্বরিতে পেট উল্টে জলের উপর ভেসে উঠবে।
তখন ঝুলিজাল দিয়ে ছাঁকো রে, খলুইয়ে মুঠো মুঠো করে ভরো রে। ধরা মাছ নিয়ে হাটে-বাজারে যাও রে, কচু-মানকচুর পাতায় ‘খালি খালি’ করে ‘সতীবাঁধা মাছ’ বেচো রে!
ছালিয়ার মা হয়তো এভাবেই ‘সতীবাঁধা’ মাছ ধরে এনেছে। আজ রাত্রে তাহুত করে রেঁধে ছালিয়ার বাপকে খাওয়াবে। খেয়ে দেয়ে ছালিয়ার বাপ যাবে রাতভোর ‘উকো’য় মাছ ধরতে।
‘উকা’―সে আরেক প্রকার মাছ ধরার ‘কল’। ভরা নদীতে সে খুব জুতের হয় না, হয় মরা নদীতে অর্থাৎ শীত-হেমন্তের নদীতে।
সে সময় স্রোতটাও খুব বেশি থাকে না। ঝিরঝিরে, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জল। জ্যোৎস্না রাতের চেয়ে অন্ধকার রাতই যেন ‘উকা’র পক্ষে অনুকূল। তা বলে তেমন আঁধার রাত কী আর! সেই যে সেই ‘আঁধারের রূপ’―‘বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনী―সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।’
না, না। যেমন তেমন আঁধার রাত হলেও হয়। বৃহদাকার ‘পাটিয়া’, ‘পানসি’ না হলেও চলে। দরকার শুধু একটা ডোঙাডুঙি আর হ্যাজাক লাইট। অন্যথায় হাই-ব্যাটারির টর্চ।
উঁহু, আরও একটা জিনিসের দরকার হয়। একটা ঝকঝকে ধারালো অস্ত্র, ঝকঝকে তরবারি। যা দিয়ে এক কোপে একটা আস্ত মাছের ধড়-মুণ্ডু আলাদা করা যায়।
ওইরকমই আলো-অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তালডোঙায় চড়ে হংসী নাউড়িয়ার সঙ্গে কতদিন গিয়েছি অঝোরঝর অন্ধকারে ‘উকা’য় মাছ ধরতে সুবর্ণরেখায়।
মাথায় ‘ঘোঙ’। উপরন্তু একটা ছেঁড়া ছাতাও থাকে তালডোঙায়। পরনে খেটো গামছা। কোনও মতে টেনেটুনে মালকোঁচার মতো খুঁটটা কোমরে গোঁজা।
খালি গা, ছেঁড়া-ফাটা ফতুয়াটা ভাঁজ করে কাঁধেই ফেলে রাখা। এই হলো আমাদের গ্রামের শিমুলতলী ঘাটের বরাবরের হংসী নাউড়িয়া।
নাউড়িয়ার পোয়ের সঙ্গে নদীজলে ‘উকা’য় চলেছি। চলেছি তো চলেছি, চুপচাপ।
কেবলই ওঠা-পড়া জলের ঢেউ-তরঙ্গ, উড়াল ঘূর্ণির জলোচ্ছ্বাস। মাঝেমাঝে মাথার উপর। দু-একটা রাতচরার চক্কর। তাদের ‘ট্র্যাঁ ট্র্যাঁ ‘ কলরব।
লগিতে ঠেস মেরে ভোঙা আটকে হংসী নাউড়িয়া হাত উঁচিয়ে ঘাড় লম্বা করে হঠাৎই বলে উঠল―
‘টিপা-লাইটে জলদি করি ফুকাস ফ্যালো বেহেরার পুআ। মাছের চক লৌকায় যাবরনাস্তি ঠেল মারেটে।’
অথচ তালডোঙায় ওঠাইস্তক হংসী নাউড়িয়ারই নিষেধ ছিল নদীতে টর্চ-লাইটের আলো না ফেলার।
না হলে এতক্ষণ ধরে কম ইচ্ছা তো হয়নি পাঁচ-সেল-ব্যাটারির টর্চের আলোয় ফোকাস ফেলে রাতের নদীর হাবভাব দেখার।
কেমন করে নদীবক্ষে স্থানে স্থানে নদীজল হঠাৎ হঠাৎ পাক খায়। ঘূর্ণি তোলে। যাকে বলে ‘ঊরাল ঘূর্ণি’।
ঘূর্ণিতে পড়ে মাছের চক ঘুরপাক খাচ্ছে। মাছ এসে যারপর নাই নৌকার গায়ে ঠুকরে দিচ্ছে। তাই এতক্ষণে নদীজলে টর্চের আলো ফেলতে বলছে হংসী।
আলো ফেললামও। আর দেখি কি―
শয়ে শয়ে মাছ! শুধু মাথাটুকু উঁচিয়ে কব্ কব্ আওয়াজ দিচ্ছে। শরীরের গতিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কী মাছ ওগুলো ?
পাঁচ-সেল টর্চের আলোয় মাছগুলো স্থিরচিত্র। নড়েও না চড়েও না। কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থম মেরে আছে।
‘কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম,
হাতে দিলাম মাকু,
ভ্যা কর তো বাপু।’
এ যে কিছুই করে না। মাথা উঁচিয়ে শুধুই ভেসে থাকে। হাঁকাড় দিয়ে উঠল হংসী নাউড়িয়া―
‘করোটো কী বেহেরার পুআ ? কোপ মারো! কোপ মারো! মারি দু ফাঁক করি দও, ধড়-মুণ্ড আলাদা আলাদা! উকায় মাছ মারতে আসি অত কাতর হিনে চলে ?’
এই হলো ‘উকা’। ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে আলো ফেলতে হবে জলে। আলোর তাড়সে মাছের দশা হবে ‘ন যযৌ ন তস্তৌ’। তৎক্ষণাৎ তরবারির কোপে করে ফেল দু টুকরো।
তারপর কাটা মাথা কাটা ধড় জলের উপর ভেসে উঠলে যত পারো ছাঁকো রে! খলুইয়ে ভরো রে!
‘সতীবাঁধা’ আর ‘উকা’য় মাছ ধরার কথা শুনে আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো―এরা নির্ঘাত গাঁ-ঘরের, আমাদের গাঁ-ধারের লোক।
মনে হতেই আমি তাদের পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়াচ্ছি। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছিল। হাওয়ার বেগ এক্ষণে আরওই বেড়ে গেল।
সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ