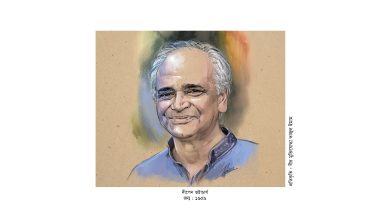প্রচ্ছদ রচনা : স্বাধীনতা দিবস ২০২৪ : ইসহাক খানের মহাকাব্যিক স্মৃতিগদ্য আমার মুক্তিযুদ্ধ : সরকার আবদুল মান্নান

প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনা থাকে, জাতিগত অস্তিত্বের মূলে যার বুনিয়াদ। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এমন একটি তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে ধারণ করার মতো ঘটনা হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতি কোনওদিন স্বাধীন ছিল না, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বাঙালি জাতি কোনও কালেই পায়নি। শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন ভোগ করা ছিল বাঙালি জাতির অনিবার্য নিয়তি। ইতিহাসের নানা সময়ে নানা জাতি, নানা শক্তি ও অপশক্তি বাঙালি জাতিকে শোষণ করেছে, নিপীড়ন-নির্যাতন করেছে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ভিন্ন এক পটভূমি রচিত হতে থাকে। প্রথমে দেশভাগ এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আর তার মূলে নিহিত থাকে স্বাধীনতার অঙ্কুর।
১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খোকা নামে এক শিশু এবং পরে যিনি শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সর্বশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে এক মহীরুহ রূপ ধারণ করেন। তাঁর স্বপ্নের মধ্যে আস্তে আস্তে দানা বাধঁতে থাকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিমা। তিনি এবং তার অসংখ্য সহযোদ্ধাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে একসময় স্বাধীনতার ডাক আসে। তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাদেরই একজন ইসহাক খান।
১৩৬২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ইসহাক খান জন্মগ্রহণ করেন সিরাজগঞ্জের কানসোনা নামক গ্রামে। কানে সোনা―কানসোনা, নারীপ্রতিমা, সৃষ্টির আধার। আমরা দেখতে পাই, সেই শৈশব থেকে ইসহাক খানের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিবিড়ভাবে কাজ করতে থাকে। ফলে মাত্র দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন তার নাটক ঢেউয়ের দোলা দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চস্থ হয়। এ এক বিরল ঘটনা। এরপর জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছেন তিনি। জীবনের সেই যাত্রা পথে ইসহাক খান লেখালেখির মধ্যেই নিজেকে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট রেখেছেন। যে সন্তানের একটিমাত্র গ্রন্থ প্রকাশের পর পিতা আপনজনদের কাছে লেখক হিসেবে ছেলের পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন, সেই ছেলের লেখক হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং সরকারি চাকরির সোনার হরিণ ছেড়ে দিয়ে হলেও তিনি যে সর্বক্ষণ সৃষ্টির প্রেরণায় নিমজ্জিত থাকতে চাইবেন, তা আর বিচিত্র কী!। নিরন্তরভাবে লিখতে হবে তাঁকে। আজ অবধি লেখাই তার বেঁচে থাকার আয়ুধ। তিনি গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন এবং লিখেছেন অসংখ্য নাটক। তিনি গল্পে আর উপন্যাসে খুব স্পর্শকাতর, খুব কোমল-করুণ ও পেলক শব্দের জাল বুনে বুনে রচনা করেন তাঁর আখ্যানের জগৎ। যারা তাঁর পাঠক, তারা নিশ্চয়ই জানেন, ইসহাক খানের গল্পের স্রোতে একবার যদি কেউ পা রাখেন, তাকে যেতে হয় শেষ অবধি। তাঁর গল্প, তাঁর উপন্যাস শেষ না করে ওঠা যায় না। ইসহাক খানের আখ্যানের জগৎ এমন কেন ? কোন রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর বয়ানের শৃঙ্খলার মধ্যে ? এই রহস্য আর রহস্যময়তা আর কিছু নয়―জীবনের প্রতি তাঁর অসামান্য মমত্ববোধ।
জীবন তো এক তৃষ্ণাতুর রাজহংস। জলে অবগাহন ছাড়া কে মেটায় তার অনিঃশেষ সেই তৃষ্ণা ? একজন সৃষ্টিশীল মানুষও নিরন্তর তৃষ্ণাকাতর থাকেন। এই তৃষ্ণা হলো সৃষ্টির ভেতরে নিজেকে উজাড় করে উন্মোচন করার তৃষ্ণা। ইসহাক খান তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই অফুরন্ত তৃষ্ণার বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর লেখা পাঠ করে আমরা মনের, মননের, বোধ ও বুদ্ধির তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সাঁতার কাটি। এই সাঁতার কাটার আনন্দ অপরিসীম।
যে রহস্যময়তা আর মমতার আখ্যান তিনি রচনা করেন এবং ভাষার ভেতরে জীবনের প্রতি যে গভীর আস্থাবোধ ও ভালোবাসাবোধ তিনি এঁকে চলেন, তার আকর্ষণ, তার আবেদন, তার চোরা টান আমরা কেউ উপেক্ষা করতে পারি না। সেই ইসহাক খান রচনা করেছেন তার যুদ্ধদিনের গল্পের ব্যক্তিগত ইতিহাস, যার নাম আমার মুক্তিযুদ্ধ।
ইতিহাসতত্ত্ব বা হিস্টোরিওগ্রাফি বলে একটি কথা আছে। এর মানে হলো, ইতিহাস লেখার প্রয়োগ-পদ্ধতি, মানুষ, স্থান-কাল ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ইসহাক খানের আমার মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসতত্ত্ব বা হিস্টেরিওগ্রফির দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের কোনও বই নয়; সে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়ও এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। কেননা, তিনি তাঁর অজ্ঞাত ইতিহাসের কোনও বিষয় নিয়ে, কোনও বাস্তবতা নিয়ে বা কোনও ঘটনা নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেননি। এ ক্ষেত্রে বরং তিনি নিজেই ইতিহাস, নিজেই ইতিহাসের নায়ক। তিনি আধার এবং তিনিই আধেয়। জাতীয় জীবনের সেই মহা সন্ধিক্ষণে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের তিনি সান্ত্রি, তিনি যোদ্ধা। ফলে অনিবার্যভাবেই ইতিহাসতত্ত্বের কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি হাঁটেননি। তিনি হেঁটেছেন একজন শিল্পীর পথে, একজন শিল্পীর করণকৌশলে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই আমার মুক্তিযুদ্ধ ব্যক্তিগত ইতিহাসগ্রন্থ, ব্যক্তিগত স্মৃতিগদ্য। কিন্তু ইতিহাস কি কখনও ব্যক্তিগত হয় ? হয়, যদি ব্যক্তি নিজেই ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠেন। ইসহাক খান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ এবং ইতিহাস। ফলে যে দৃষ্টিকোণ থেকে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যে জীবনবিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, অনুভব করেছেন, তার হৃদয় নিংড়ানো আলেখ্য হয়ে উঠেছে আমার মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক গ্রন্থটি।
ইসহাক খান লিখেছেন :
আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার জীবন এক একটি ইতিহাস। তাদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক-অনেক যুদ্ধের গল্প আছে। একই চিত্র আমরা ক’জন একসঙ্গে দেখেছি। তারপরও দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর তাৎপর্য এক নয়, আলাদা আলাদা। আমি লিখেছি আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ। অন্যের দেখার সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে। এইজন্যে আমার লেখার নাম দিয়েছি আমার মুক্তিযুদ্ধ। যদি কোন বন্ধুর দেখার সঙ্গে আমার দেখার পার্থক্য ঘটে যায় সেটা হবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি। অন্য বন্ধুর যদি আলাদা কোন গল্প থাকে নিঃসন্দেহে তিনি তার দেখা গল্প লিখবেন। আমি তাকে অগ্রিম স্বাগত জানাচ্ছি। আমি চাই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা তার যুদ্ধের স্মৃতিচারণ লিখে যাক। সবই আগামী দিনের ইতিহাস। [পৃ. ভূমিকা]
ইসাক খানের এই বক্তব্যের মধ্যে ইতিহাসের কিছু ন্যায়সূত্র নিহিত আছে। প্রথমত, ইতিহাসতত্ত্ব বলে কোনও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকাণ্ড নেই। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে কোনও প্রপঞ্চ নয়। তৃতীয়ত, ইতিহাস ব্যক্তির আলোকে নৈর্ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আলোকে ব্যক্তিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ইতিহাস বহুবিচিত্র মাত্রা ও মাত্রান্তরের পাঠ নিশ্চিত করে। আমার মুক্তিযুদ্ধ মূলত ইতিহাসতত্ত্বের এই নতুন পটভূমিতে রচিত। শুরুটা একটু খেয়াল করি :
কথা ছিল সূর্য ওঠার আগে আমরা বাড়ি থেকে বেরোব। আমরা মানে, আমি, রফিকুল আলম, গোলাম মোস্তফা, জহুরুল হক খান, আব্দুর রাজ্জাক, সরকার আলী আসগর ও আসাদুজ্জামান খোকন ।
আমাদের পরিকল্পনা ছিল অন্ধকার থাকতে থাকতে লোক জানাজানি হওয়ার আগে আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ব। তা হলো না। আমাদের সঙ্গে যারা পরে যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার করেছে, তারাই নানাভাবে গড়িমসি করছিল। যেতেও চায় আবার মনে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার মাকে নিয়ে। মা কোনওভাবে জেনে গেলে আমার যুদ্ধে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমার মা অনেকগুলো সন্তানহারা একজন দুঃখী মা। আমাকে নিয়েই তাঁর পৃথিবী। সেই আমি মৃত্যুর সামনে বুক পেতে দিতে যাচ্ছি―এ কথা জানলে আমার দুঃখিনী মা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। মাথা ঘুরে ঠাস করে পড়ে যাবেন। আর না হলে এমন করুণ নাটকীয় দৃশ্যের জন্ম দেবেন যা দেখে আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।
এই নিয়ে আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছিল। আমি বারবার তাড়া দিচ্ছিলাম। গ্রাম থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে যেন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। অনেক পরে বেরিয়ে এল বন্ধু আলী আসগর। তার হাতে তেলের শিশি। আসগার মাকে মিথ্যে বলেছে। বলেছে বাজারে যাবে। বাজারে যাবে শুনে আসগারের মা হাতে তেলের শিশি ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘ঘরে এক ফোঁটা কেরোসিন তেল নেই। তেল না আনলে রাতে অন্ধকারে খেতে হবে।’
আমরা আমাদের মা-বাবা পরিবার আত্মীয়স্বজনকে অন্ধকারে রেখে আলো আনতে পথে বেরোলাম। [পৃ. ৯]
উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যটি লক্ষ্য করার মতো। ইসহাক খান লিখেছেন, ‘আমরা আমাদের মা-বাবা পরিবার আত্মীয়স্বজনকে অন্ধকারে রেখে আলো আনতে পথে বেরোলাম।’ এই বক্তব্যটুকুর ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের পুরো ইতিহাস মূর্তমান হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালের নয় মাস জুড়ে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আত্মত্যাগের যে অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি আলোকিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়। আর তার জন্য দরকার ছিল স্বাধীনতা। সুতরাং এই বক্তব্য আমাদের মহিমামণ্ডিত ইতিহাসের একমাত্র দর্শন। ইসহাক খান এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যে অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেছেন তার প্রতিটি উপাদানের মধ্যে নিহিত আছে মুক্তির আলোকিত আখ্যান। এবং একই সঙ্গে এই হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সূচনালগ্নের চিরপরিচিত এক মিথ।
যদি বলা হয়, ইতিহাসের সঙ্গে গল্পের এবং আখ্যানের ব্যবধান কতটুকু ? তাহলে তার উত্তরে একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তির মুখোমুখি হতে হবে, আর তা হলো, ইতিহাস মূলত জীবনেরই ব্যাখ্যা এবং সেই জীবন ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর। কিন্তু রাজরাজড়াদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জয়-পরাজয়ের যে ইতিহাস এতদিন রচিত হয়ে এসেছে, সেই ধারণা থেকে এখন ইতিহাসতত্ত্ব নতুন এক যাত্রাপথে হাঁটতে শুরু করেছে, আর তা হলো ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের পাঠ অন্বেষণ, যে ব্যক্তিমানুষ একই সঙ্গে সামাজিক ও সামগ্রিক। ইসহাক খানের আমার মুক্তিযুদ্ধ নামক গ্রন্থ থেকে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হলো, সেখানে আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের একটি প্রগাঢ় ইতিহাস পেয়ে যাই, যে ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের আবেগ, অনুভূতি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হৃদয়ের রক্তক্ষরণ আর বিচিত্র অনুভবপুঞ্জ নিবিড়ভাবে জড়িত।
ঐতিহাসিক বাস্তবতার পটভূমিতে স্মৃতিগদ্য রচনা করার পেছনে বেশ ঝুঁকি থাকে। প্রথমত হলো, বাস্তবতার অনুপুঙ্খ বিবরণ সততার সঙ্গে তুলে ধরার প্রবণতা; দ্বিতীয়ত, সত্যের মূলগত ভিত্তিগুলোকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তোলার চেষ্টা; তৃতীয়ত, স্থান, কাল ও সময়ের ঐক্য বিধানের প্রবণতা এবং সর্বোপরি নিজের দিকে আলো ফেলার সহজাত প্রবৃত্তি। এই বিষয়গুলো ইতিহাসভিত্তিক স্মৃতিগদ্য লেখার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। ইসহাক খান আমার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থে এক ধরনের সহজাত শক্তিতে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে উতরে গেছেন। তিনি নিজের দিকে যেটুকু আলো ফেলেছেন তা সময়ের পটভূমিতে ছিল অনিবার্য। এর মধ্যে কোথাও মনে হয়নি যে, তিনি এই গ্রন্থের প্রোটাগনিস্ট বা নায়ক। অধিকন্তু সর্বদাই মনে হয়, আর দশজন সহযোদ্ধার মতো তিনিও যুদ্ধদিনের পটভূমিতে প্রবলভাবে বাস্তব, এই বাস্তবতার বিবরণ তার লেখার মধ্যে এতটাই নিরপেক্ষ, নির্মোহ সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে যে, কয়েকটি উদাহরণ দিই :
এক
হলঙ্গা এক ধরনের দেশি অস্ত্র। বাঁশের মাথা চোখা করে তৈরি এই অস্ত্রকে আমরা স্থানীয়রা বলি হলঙ্গা। হাড়িভাঙা গ্রামের কয়েকজন লেঠেল মালকোঁচা মেরে কোমরে গামছা বেঁধে হলঙ্গা নিয়ে ট্রেনিং দিতে আসত। তারা নানা রকম শারীরিক কসরত দেখাত। এমনভাবে তারা হলঙ্গা নিয়ে কসরত করত, মনে হতো সামনাসামনি পাকিস্তানি আর্মি পেলে এখনই ফটাস করে গেঁথে ফেলবে। কিন্তু সেটা যে অবাস্তব ও হাস্যকর, বোঝা গেল ২৪ এপ্রিল করতোয়া ব্রিজে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে।
এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ এলাকা শত্রুমুক্ত ছিল। আমরা নিরাপদেই সময় পার করতাম। পাকিস্তানি আর্মি উত্তরবঙ্গে আসার একমাত্র রাস্তা নদীপথ, যমুনা পেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। তারা আরিচা ঘাট থেকে গানবোট এবং ফেরি নিয়ে নগরবাড়ী ঘাটের দিকে আসতে থাকলে তৎকালীন সিরাজগঞ্জের এসডিও শামসুদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেয়। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মির ভারী অস্ত্রের সামনে মুক্তিযোদ্ধারা বেশি দিন টিকতে না পেরে পিছু হটে বাঘাবাড়ি ঘাটে এসে পজিশন নেয়। সেখানেও তারা টিকতে না পেরে পজিশন উইথড্র করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি আর্মি সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। অগত্যা মুক্তিযোদ্ধারা উল্লাপাড়া থেকে দেড় মাইল পূর্বে করতোয়া ব্রিজের কাছে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা ব্রিজের কাছে রেল উপড়ে ফেলে তারপর ব্রিজের পূর্বে শাজাহানপুর গ্রামের নানা স্থানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নেয়। এই দৃশ্য দেখতে আমি মোস্তফা, জহুরুল, আসগার, রাজ্জাক, সুকুর মামু, খোকন, মিন্টুসহ আরও কয়েকজন কানসোনা থেকে দুই মাইল হেঁটে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে শাজাহানপুর গ্রামে ছুটে আসি। [পৃ.২৮]
দুই
অনেকক্ষণ কেটে গেল। গ্রেনেড বিস্ফোরণ হচ্ছে না। আমাদের টেনশন বাড়ছে। আমাদের গেরিলাযোদ্ধারা কি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে গেছে ? গ্রেনেড বিস্ফোরণ হচ্ছে না কেন ?
আমাদের অস্থিরতা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তাহলে কি আমাদের পরিকল্পনা মার খেয়ে যুদ্ধে আমরা হেরে যাব ? আমাদের এলোমেলো ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বিকট শব্দে পরপর কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলে আমরা জয় বাংলা বলে গগনবিদারী হুংকার দিয়ে উঠলাম। আনন্দে আমাদের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্রমাগত আরও গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতে থাকে। আর এদিকে পাকিস্তানিদের মরণ চিৎকার শুরু হয়ে যায়। তারা চেঁচিয়ে আল্লাহর নাম করে তাঁর সাহায্য চাচ্ছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোরআনের সুরা পাঠ করছে। আমাদের একজন চেঁচিয়ে বলল, ‘ওই কুত্তারা, আল্লাহ্ কি তোদের একলার ? আমাদের না ?’ ওদের মরণ চিৎকার আমাদের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়।
ভোর হচ্ছে। চারপাশ ফর্সা হচ্ছে। আলো ফুটছে। ওদের তখন গোলাগুলি থেমে গেছে। আমরা টার্গেট করে ফায়ার করে যাচ্ছি। গুলি লেগে ওদের কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ছে। সে দৃশ্য আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা তখনও জয় বাংলা বলে ক্রমাগত গর্জন করে যাচ্ছি।
এই সময় ওরা অস্ত্র উঁচিয়ে স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়ায়। আত্মসমর্পণ করে। আমরা তখন অস্ত্র বাগিয়ে চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলি। [পৃ. ১২৫]
তিন
স্টেনগান কাঁধে নিয়ে আমরা মুক্ত পরিবেশে আনন্দে গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রান্ধুনীবাড়ি থেকে কানসোনা গ্রামের দূরত্ব ২০-২৫ মাইল। এই দূর মোটেও দূর মনে হচ্ছিল না। হাসি-ঠাট্টায় কখন যে আমরা বাড়ি এসে পৌঁছলাম নিজেরাই বুঝে উঠতে পারলাম না। বাড়ি আসার পর ভীষণ আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলো। সবাই ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করতে লাগলেন। আনন্দে কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন। তাদের সবার মুখে এক কথা, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, আমরা বিজয়ের বেশে ফিরে এসেছি। আমাদের জন্য তারা গর্বিত।[পৃ. ১৭৭]
বাড়িতে আসার পর শুরু হলো আমাকে নিয়ে মায়ের পাগলামি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করল। কিছুতেই সে আমাকে ছাড়ছে না। ছাড়লে যদি আমি চলে যাই ? তাকে যত বলি যুদ্ধ শেষ। সে বলে, বিশ্বাস কি ? তুমি তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছিলা। যদি আবার যাও ? বললাম তো আর যাব না। তবু সে বিশ্বাস করে না। […] বালিশের পাশে রাখা স্টেনগান নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আমার ছোট ভাই নাজমুল। ও তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। বললাম, ‘কী করছিস ?’
ও বললো, ‘এই অস্ত্রের নাম কী ভাই ?’
বললাম, ‘স্টেনগান’। ‘কীভাবে ফায়ার করে ?’
‘ট্রিগারে চাপ দিলে গুলি বেরিয়ে যায়। নাজমুল ট্রিগারে চাপ দিচ্ছিল। ব্যারেল আমার দিকে তাক করা। আমি চটজলদি ধাক্কা দিয়ে ব্যারেল ওপরে তুলতেই দ্রাম করে গুলি টিনের চালা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। আমার ছোট ভাই ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অস্ত্র ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি হতভম্ব মুখে বসে আছি। [পৃ. ১৭৮-১৭৯]
চার
জানুয়ারির ৯ তারিখ সন্ধ্যায় আকস্মিক আমরা সুখবরটা পেলাম। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এখন বিমানে লন্ডনের পথে। এই খবরে গোটা ক্যাম্প, গোটা শহর, গোটা দেশ একসঙ্গে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সারা শহর মিছিলে মিছিলে সয়লাব। আমরাও আনন্দ মিছিল বের করলাম । মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে আবার আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম। নেতার মুক্তির আনন্দে ভেতরটা কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। আনন্দে উত্তেজনায় কেবলই টগবগ করে ফুটছিল। বিজয়ের চেয়ে বেশি আনন্দ এসে হৃদয়ে দোলা দিচ্ছিল। […] পরদিন দুপুরের পর থেকে রেডিও ঘিরে আমরা বসে আছি। রেডিওতে ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন সাংবাদিক আবৃত্তিকার কামাল লোহানী। তিনি যখন বলছিলেন বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান বাংলার আকাশে দেখা গেছে। আকাশে বিমান চক্কর দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান বাংলার মাটি স্পর্শ করবে। তাঁর এই বর্ণনা আমাদের বাকরুদ্ধ এবং ভীষণ আবেগী করে তোলে।
তারপর তিনি যখন বলেন, এইমাত্র বিমান বাংলার মাটি স্পর্শ করেছে।
তখন আমরা আপনা থেকে সবাই জয় বাংলা বলে ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। আশপাশের বাসাবাড়ি থেকে জয় বাংলা ধ্বনি ভেসে আসছিল। বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করা হলো। কামাল লোহানী এমনভাবে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন যেন চোখের সামনে বঙ্গবন্ধুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
এবার তাঁকে নিয়ে গাড়িবহর ছুটলো রেসকোর্স ময়দানের দিকে। সেখানে লাখ লাখ মানুষ ভোর থেকে প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছে।
পনেরো মিনিটের পথ আসতে দুই ঘণ্টা লেগে গেল। পথে পথে বাঁধভাঙা মানুষের ঢল, বারবার থেমে যাচ্ছিল গাড়িবহর। তারপর তিনি সরাসরি মঞ্চে উঠে জনতার সামনে হাত নেড়ে তাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন। বক্তৃতার সময় তিনি আবেগে কেঁদে ফেললেন। তাঁর সেই ভালোবাসার কান্না আমাদেরও সংক্রামিত করে। আমাদেরও চোখ ভিজে আসতে লাগল। বঙ্গবন্ধু কান্নাভেজা কণ্ঠে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, ‘বিশ্বকবি, আপনি বলেছিলেন’, ‘সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।’ আপনার কথা ভুল প্রমাণ করেছে আমার সোনার ছেলেরা। তারা মানুষ হয়েছে। তারা বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে। আপনি আসুন, দেখে যান। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন।’
সে রাতে আমরা হই হুল্লোড় আর আনন্দ করে কাটালাম। নেতা এসে গেছে। আমাদের আর কোনও চিন্তা নেই।
কদিন যেতে না যেতে আমাদের আনন্দ ফিকে হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু আমাদের অস্ত্র জমা দিয়ে আগের পেশায় ফিরে গিয়ে যার যার অবস্থান থেকে দেশ গড়ার আহ্বান জানালেন। খুবই যৌক্তিক আহ্বান। কিন্তু সমস্যা বাধলো যে সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধের আগে দিনমজুর ছিল তারা কীভাবে যুদ্ধ শেষে আবার পরের বাড়ি দিনমজুরি করবে ? এ ছাড়া বড় সমস্যা বঙ্গবন্ধু এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।
[…] বেশি মন খারাপ হয় অস্ত্র সরানোর ঘটনা দেখে। অতিরিক্ত যে অস্ত্রগুলো আমরা রাজাকার মিলিটারি মেরে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলো জমা না দেওয়ার কূটকৌশল লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে খুব হতাশ হলাম। গভীর রাতে বাড়তি অস্ত্রগুলো চরাঞ্চলে রেখে আসা হলো। এই ব্যাপারটা সহযোদ্ধা মলয় আমাকে প্রথম জানায়। আমি পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভীষণ আহত বোধ করি। আমার তখনই মনে হতে থাকে এই অস্ত্র দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হবে। পরবর্তী সময়ে তাই হয়েছে। […] জানুয়ারির শেষের দিকে একদিন সিরাজগঞ্জ কোর্ট এলাকায় গিয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অস্ত্র জমা দিলাম। পেলাম অস্ত্র জমা দেওয়ার রসিদ। দেড়শ টাকা, একটি সাদা কম্বল আর জেনারেল ওসমানীর স্বাক্ষর করা একটি সার্টিফিকেট। […] কদিন পর একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লাম। এতটাই হতাশ হলাম যে আমার জীবনটাই পাল্টে গেল। এক বন্ধুর হাতে দেখলাম জেনারেল ওসমানীর স্বাক্ষর করা সেই সার্টিফিকেট। যে সার্টিফিকেট আমাদের দেওয়া হয়েছে। হুবহু একই। আমার সেই বন্ধু যুদ্ধ করেনি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা ধরনের বিরূপ কটাক্ষ করেছে আমাদের সামনে। তার হাতে তার নামে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কীভাবে পেলি ?’বললো, ‘কীভাবে পেলাম সেটা বলা যাবে না। তবে কারও দরকার থাকলে বলতে পারিস, ব্যবস্থা করা যাবে।’ ওর কথা শুনে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি। একরাশ হতাশা আমাকে চিবিয়ে খেতে থাকে। এমন ভয়ংকর অনিয়ম আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। রাগে দুঃখে ক্ষোভে নিজের সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে নর্দমায় ফেলে দিলাম। বেদনার ভারী দীর্ঘশ্বাস নেমে গেল বুক চুঁইয়ে। এসব কী হচ্ছে ? কেন হচ্ছে ? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। [পৃ. ১৮৮-১৯২]
আমার মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে গ্রন্থটি পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ মুক্তিযুদ্ধ এক মহাকাব্যিক জীবনাখ্যান। এই জীবনাখ্যানের প্রায় প্রতিটি উপাদান নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস লেখা যেতে পারে, রচনা করা যেতে পারে হাজার হাজার পৃষ্ঠার আখ্যানকাব্য, লেখা যেতে পারে মহাকাব্যিক নাটক। কিন্তু ইসহাক খান মাত্র ৩৬টি এপিসোডের ১৯২ পৃষ্ঠার একটি ছোট সৃষ্টিকর্মের ভেতরে এই মহাকাব্যিক জীবনাখ্যানের প্রায় সবটুকুই তুলে ধরেছেন খুব সহজ-সুন্দর শৈল্পিক ভঙ্গিতে। তিনি কোথাও কোনও সন-তারিখের আশ্রয় নেননি। তথ্যে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি তাঁর গ্রন্থটিকে। অত্যন্ত ছোট―সর্বোচ্চ চার-পাঁচ পৃষ্ঠার এপিসোডগুলোতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব কটি মাত্রা ও মাত্রান্তর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিবরণ তিনি তুলে ধরেননি, অধিকন্তু বিজয়-পরবর্তী অন্য এক জীবনাকাক্সক্ষার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে আমার মনে হয়েছে যে, পুরো বইটি যদি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা যেত, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু সেটা উচিত নয়, শোভন নয় এবং সম্ভবও নয়। সুতরাং আমি শুধু কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে ইসহাক খানের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছি। এই পরিচয়ের ভেতর দিয়ে ইসহাক খানের শিল্প-সৃষ্টির প্রতি আমার আগ্রহ, কৌতূহল ও তৃষ্ণা অনেক দূর বেড়ে গেল। জয়তু ইসহাক খান।
লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক