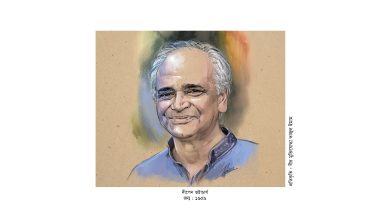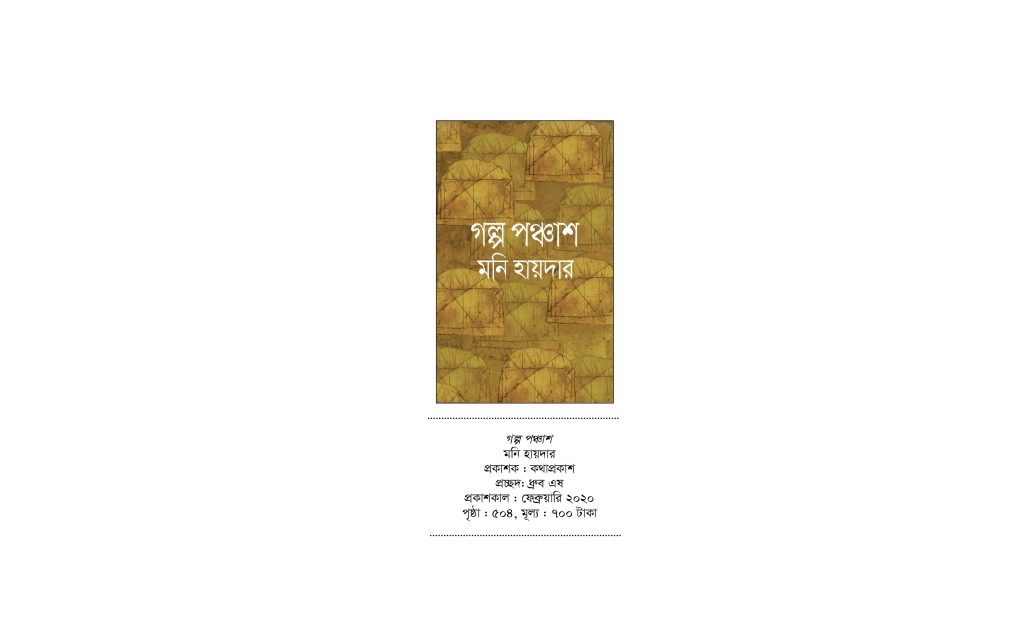

নব্বই দশকের গল্পের একটা প্রধান প্রবণতা অতিরিক্ত ভনিতা। গল্প পড়তে গেলে মনে হয় কোনও প্রবন্ধ পাঠ করছি। অকারণ নিরীক্ষা করতে গিয়ে অনেককেই কলম থামাতে হয়েছে। মনি হায়দারের গল্পে ভনিতা নেই, তাই গল্পগুলো বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। মনি হায়দারের গল্প পড়ার সময় মনে হয় পাশে বসে কেউ গল্প করছে। পাশে বসে গল্প করার সময় যেমন হাত নড়ে, চোখ নড়ে, গলার স্বর উঠানামা করে, হঠাৎ উত্তেজনা ও চাপা আবেগ প্রকাশ পায়―মনি হায়দারের গল্পগুলোও সেরকম, গল্পকারের শারীরিক উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। প্রকৃত গল্পকারের সার্থকতা এখানেই।
কী বললেন ? অফিসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ?
জি স্যার, ঘাড় চুলকে কণ্ঠ নামিয়ে জবাব দেয় হাবিব আহমেদ। বুঝতেই পারছেন, স্যার, সবাই আমার কলিগ। ওদের বিরুদ্ধে আপনার সঙ্গে গোপন কাজ করছি আমি। আমাকে যেন ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার করা না হয়, একটু দেখবেন প্লিজ স্যার।
টেবিলের উপরের পেপারওয়েট নাড়াতে নাড়াতে জবাব দেয় ডেপুটি ডিরেক্টর মুন্সি আহসান কবির, এই অফিসের কোথায়, কখন কী হয় আমি সব জানি। আপনি চিন্তা করবেন না হাবিব। আমি সব ব্যাটাকে ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করছি। আমাকে তো চেনে না। জনপ্রশাসন সচিব ইকরামুল হক আমার ব্যাচ মেট। একটা ফোন করলেই কর্ম সাবাড়। কিন্তু আমি ক্ষমতা দেখাতে চাই না। সেটাকে ওরা আমার দুর্বলতা মনে করছে, না ? মোটা কালো গর্দান সামনে এনে স্লো ভলিউমে জিজ্ঞেস করে মুন্সি, বলুন তো আমার বিরুদ্ধে কে বেশি ঘোঁট পাকায় ?
একটি সরকারি অফিসের চিত্র গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন গল্পকার। পড়ছেন আপনি কিন্ত মনে হবে গল্পকার নিজেই আপনাকে বলছে গল্পটা। অফিসের ডিডি অযথাই সবার ওপর ছড়ি ঘোরায়। সবাইকে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চায়। কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে তরুণ অফিসার অনন্য মামুন। অন্যদেরও বোঝাতে চায় আমরা কেন তার ভেড়া হয়ে থাকব ? কিন্তু, মুন্সি আহসান কবিরের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে সাহস করে না। যদি তাদের চাকরি চলে যায়, যদি তাদের বদলি করে দেওয়া হয় বান্দরবান! লোকগুলোকে ওর কাছে গিনিপিগ মনে হয়। গল্পকারের ভাষায়, ‘সবাই মানুষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে বহন করছে হীনম্মন্যতার দাসত্ব। দুশো বছরের ব্রিটিশ গোলামি, চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি গোলামি আমাদের সকলের অস্থি, মজ্জা আর মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। মামুন আরও ভাবে―আমার সামনে এই যে কোট স্যুট টাই আর শাড়ি পরিহিত মানুষগুলো বসে আছে, প্রত্যেকে মননে খুব নিম্নশ্রেণির প্রাণী।’
মামুন একদিন আবিষ্কার করে মুন্সি আহসান কবিরের কোনও ক্ষমতাই নেই। কথায় কথায় তিনি যেসব মন্ত্রী, সচিবের ভয় দেখান সেসব বাকওয়াজ। মুন্সি আহসান কবির আসলে বিকারগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ। এরকম বিকারগ্রস্ত অসংখ্য মানুষই আমাদের অফিসগুলোতে থাকে, আর পুরো অফিসকে জাহান্নাম বানিয়ে তোলে। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার সময় আমি এরকম কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। গল্পটা পড়তে গেলে মনে হয় এ আমাদের পরিচিত গল্প, পাশে বসে কোনও বন্ধু তার অফিসের গল্প করছে।
কথাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত গল্প পঞ্চাশ বইয়ের নবম গল্প শূন্য মানুষের যাত্রা থেকে পাঠক আপনাদের জানালাম, গল্পের আখ্যান।
‘আবদুল মতীনের ছয় পর্ব’ গল্পটা ভয়াবহ। শুরু হয়েছে স্বাভাবিক গতিতেই। ‘আমাদের আবদুল মতিন বরাবরই ব্যতিক্রম। অথবা বলা যায় ব্যতিক্রম হওয়া, ব্যতিক্রম থাকাটাই পছন্দ, হবি। প্রসঙ্গক্রমে মতিন বলে, সমাজের আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে একটু আলাদা থাকা ভালো। তর্কে তর্ক বাড়ে। সে পথে না গিয়ে বন্ধুরা ওর যুক্তি মেনে নেয়।’ মেনে নিয়েছে মিতাও।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে মিতার সঙ্গে মতিনের বন্ধুত্ব হয়, প্রেম হয়। ব্যতিক্রমী মতিনের প্রতি মিতা আকৃষ্ট হয়। প্রেমপর্যায়ে অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মতিন মিতার সঙ্গে শারীরিকভাবে বেশি অগ্রসর হয় না। কিছু মূল্যবোধ সে ধরে রাখতে চেয়েছিল। মতিনের কথায়, ‘মূল্যবোধ মানেই শাশ্বত একটা বিষয়। যে মানুষের ভেতর শাশ্বত সত্য নেই―সে তো মানুষই নয়।’
লেখাপড়া শেষ করার পর চাকরি নিয়ে ঢাকার বাইরে চলে যায় মতিন। শুরু হয় কর্মব্যস্ত জীবন। ছুটির দিনেও কাজ থাকে। ফলে ঢাকায় যেতে পারে না। চিঠিতে দুজনেরই আকুতি ফুটে ওঠে। রাত জেগে অনেক চিঠি লিখে মিতাকে মতিন। কিন্তু, সব চিঠি পোস্ট করে না। তাহলে মিতা আরও পাগল হয়ে যাবে। ছয় মাস পর হঠাৎ মিতার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যায়। মতিন ঢাকায় এসে জানতে পারে মিতার বিয়ে হয়েছে। মতিন পরদিনই কর্মস্থলে ফিরে যায়। ছয়পর্বে বিভক্ত এ-গল্পের পঞ্চম পর্বে দেখা যায় মতিন প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠেছে। তিন বছর পর হঠাৎ একদিন মিতাকে সে অপহরণ করে। মিতাকে শারীরিকভাবে পেতে চায় মতিন। মিতা নিজেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে।
‘প্লিজ, মতিন আমার একটা কথা শুনো প্লিজ।
বলো। মিতাকে বুক থেকে নামায়। খাঁখাঁ নগ্ন কাঁধে মতিনের ডান হাত।
আমার পেটে বাচ্চা―
তাতে আমার কি ?
আমাকে দয়া করো। অমি তোমার কাছে দয়া প্রার্থনা করছি। আমার সংসার ভেঙে কি লাভ তোমার ? নিষ্পাপ শিশুটিকে বাঁচতে দাও―মতিনের দুটি পায়ের উপর আছড়ে পড়ে মিতা―আমি যদি তোমার বোন হতাম―মিতা, পায়ের ওপর থেকে তোলে বাহুর ওপর মতিন, তোমার সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ―শেষ। আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড়। এসো এতদিন পর তোমার শরীরের গোপন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি। মিতার সারা শরীর কাঁপে ভয়ে বেদনায় ভবিষ্যৎ সর্বনাশের প্রেক্ষিতে। মতিন সাক্ষাৎ জানোয়ার। মিতা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারায়। মতিন মিতাকে অপলক চোখে দেখতে থাকে।’
গল্পটি এখানেই শেষ করে দিলে ভালো হতো। কিন্তু, লেখক পর্ব ছয়ে মতিন চরিত্রটির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এটা পাঠকের প্রতি এক প্রকার অনাস্থা। এবং এই অনাস্থা তৈরি হয় লেখকের নিজের প্রতি অনাস্থা থেকেই। অবশ্যই এটা একেক লেখকের বৈশিষ্ট্য, যে তিনি যেভাবে খুশি লিখবেন। পাঠক গ্রহণ করলে করবেন না করলে নাই। কিন্তু, একজন সমালোচককে এ-নিয়ে দু-চার কথা বলতেই হয়। সমালোচক তো আর স্রেফ পাঠক নন। তাহলে তার এ-নিয়ে কথা বলারই প্রয়োজন হতো না।
কিছু গল্প বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আহীর আলমের বাম পা, আসুন―আমরা আবদুল খালেকের একটা ছবি আঁকি, গৃহপালিত চিড়িয়াখানা গড়ে উঠবার প্রণালি, জিহ্বার মিছিল, তিমিরেরও তিমির, গ্রামে একটি কাঁচা রাস্তা যখন পাকা হয়, ঘাসকন্যা, খোয়াজ খিজির, কচানদীর অট্টহাসি, ন্যাড়া একটি বৃক্ষ, সোনায় খাঁচায় আবিদ হাসান, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি গল্পগুলো জীবন ও জগৎকে নানামাত্রিকতায় দেখবার গভীর এবং চেতনাগত প্রয়াস আছে গল্পকারের।
বইয়ের প্রথম গল্প ‘আহীর আলমের বাম পা’। বছর দশেক আগে আহীর আলম কোমরে একটা ব্যথা পায়। মতিঝিলের একটা অফিসে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শব্দ উৎপাদন হলো, মঝচ। খুব পাত্তা দিলেন না তিনি। এটাকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। শৈশব থেকে এই চল্লিশ বছর ওই রকম কত মঝচ শব্দ উঠেছে কোমর থেকে, কি হয়েছে ?
কিন্তু, এই সামান্য ব্যথা তাকে আস্তে আস্তে কাবু করে ফেলে। প্রায়ই ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। ডাক্তার বলেন একটু সাবধানে চলাফেরা করার জন্য। কিন্তু, বোহেমিয়ান, বেখেয়ালি আহীর আলম ডাক্তারের সাবধান বাণী খুব বেশি পাত্তা দেন না। যেখানে সেখানে ঘুরতে চলে যান। এক পর্যায়ে প্রায় বাঁকা হয়ে তিনি ডাক্তারের কাছে আসেন। ডাক্তার এমআরআই করতে দেন। এমআরআই রিপোর্ট দেখে বলেন, মেরুদণ্ডের একটা ডিস্ক সরে গেছে, সেটাকে অপারেশন করে ঠিক করতে হবে। প্রথমে দশদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে বললেও কার্যত থাকতে হয় আঠাশ দিন। দ্বিতীয়বার আবার অপারেশন করতে হয়। এর মধ্যে টাকা-পয়সা বেরিয়ে যায় জলের মতো। নিম্নমধ্যবিত্ত আহীর আলমের মাথায় হাত। হাসপাতালে পড়ে থাকার সময় কারও সান্নিধ্যও পান না। না পরিবারের না কোনও বন্ধুর। বাসায় আসার পর আরও একলা হয়ে যান। ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেন বাইরের মানুষের হাঁটাচলা। মানুষ যে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে এটাই তাকে অবাক করে দেয়। পিঠের ব্যথাটা সেরে গেলেও বাঁ পাটা তাকে খুব ভোগাচ্ছে। থেরাপি নিয়েও সেটা সারছে না। সব সময় কেমন ভার ভার, অবশ অবশ। একদিন হঠাৎ আহীর আলমের মনে হয় তিনি যে কতদিন বাইরে যান না, বাইরের পৃথিবীটা এখন কেমন আছে ? পত্রিকা কিনতে যান না, মুদির দোকানে যান না, কেউ কি জানতে চেয়েছে সেই মানুষটি আর আসছে না কেন! আহীর আলম জীবনের প্রবল এক নিঃসঙ্গতা ও অর্থহীনতায় আক্রান্ত হন। গল্পের শেষটা ভয়াবহ। সেটা আমি আর এখানে বলব না।
পঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে সবচেয়ে অসামান্য মনে হয়েছে ‘তিমিরেরও তিমির’ গল্পটি। সুলতান মৌলভি ছিলেন গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তি। খুবই পরহেজগার মানুষ। মসজিদে নামাজ পড়িয়ে সংসার চালান। ভদ্র, সুশোভন, মার্জিত শান্ত মানুষটির জীবনে হঠাৎ নেমে আসে অন্ধকার। লাইলি নামের একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মেয়েটির বয়স মাত্র দশ-এগারো। এর আগে সুলতান মৌলভির এক বুজুর্গি কথায় গ্রামের মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ এ কি প্রস্তাব! মুরব্বিরা কেউ কেউ রাজি হলেও বেঁকে বসে স্বয়ং লাইলির মা। ‘বুজুর্গ হউক, আলেম হউক, মৌলভি সুলতান ক্যা হের বাপে আহুক, আমি আমার এই ছোট্ট মাইয়ারে ওই ঘাটের মড়ার কাছে বিয়া দিমু না’, লাইলির মা শক্ত প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।
কিন্তু, সুলতান মৌলভি এখন নানা উছিলায় লাইলিকে দেখতে চায়। মজনুর মতো পাগল তার অবস্থা। গ্রামের মানুষের অবস্থা আক্কেল গুড়ুম। একদিন লাইলির মা সুলতান মৌলভির গায়ে গরম ফেন মারে। কোঁকাতে কোঁকাতে রাস্তায় এসে সুলতান একজনের কাছে বিড়ি চায়। জহিরের চোখ কপালে। গ্রামের এক শিক্ষিত ছেলে ঘোষণা করে সুলতান মৌলভি আসলে পাগল হইয়া গেছে।
সুলতান মৌলভির নাম আস্তে আস্তে সুলতান পাগল হয়ে যায়। এক সময় গ্রামের বউ-ঝিদের পেছনে ঘোরা শুরু করে। খাল থেকে পানি নিয়ে আসার সময় সানজিদা নামের এক মেয়েকে জোরে করে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। সানজিদার দেবর তখন মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফিরছিল। অবস্থা দেখে সে যা বোঝার বুঝে ফেলে। হাতের লাঠি দিয়ে সুলতান পাগলকে আচ্ছামতো পেটায়। ‘সুলতান পাগলা কালুর কথার প্রতি উত্তরে যা করে, তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। তাকেও কয়েকজনে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে পরনের লুঙ্গি তুলে লিঙ্গ বের করে প্রবলবেগে নাড়াতে থাকে আর বলতে থাকে, তুই করবি আমার চ্যাটটা। তুই করবি আমার এই লম্বা চ্যাটটা।’
সুলতান পাগলা বাড়ি না গিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। পরদিন গ্রামে ফিরে আসে চূড়ান্ত পাগল হয়ে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে। তাকে বাড়িতে এনে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। গভীর রাতে দরজা খুলে স্বামীকে দেখেন আছিয়া বেগম। মানুষটা খালি গায়ে শুয়ে আছে মাটির ওপর। খুব অসামান্য দক্ষতায় গল্পকার মনি হায়দার শেষ দৃশ্যগুলো এঁকেছেন। শিকল বাঁধা অবস্থাতেই সুলতান পাগলা নিজের মেয়েকে একদিন খুব মারধর করে। হাসপাতাল থেকে আসার তিন মাস পর মেয়েটি মারা যায়। অনেক চিকিৎসার পরেও সুলতান পাগলা আর ভালো হয়নি। বাড়ির পেছনে আম গাছটির সঙ্গে শিকল দিয়ে তাকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখা হয়। ছেলেরাও তাকে আর দেখে না। কিন্তু, স্ত্রী আছিয়া বেগম এক মুহূর্ত স্বামীর এ দুর্দশার কথা ভুলতে পারেন না। একুশ-বাইশ বছরের সংসার তার। কীসের দোষে, কীসের অভিশাপে এমন হলো! বিয়ের পর থেকেই দেখতেন স্বামী রাত জেগে জিকির করতেন, সেই জিকির যে এই তিমিরের তীরে নিয়ে আসবে কে জানতো!
মনি হায়দারের গল্প সরাসরি পাঠকদের সঙ্গেই সম্পর্ক তৈরি করেছে। মাঝখানে কোনও আঁতেল ইন্টেলেকচুয়াল সমালোচক দরকার হয়নি। নিজের গল্প লেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখক ছোট্ট একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, ‘বনেদি একটি প্রকাশনা থেকে গত দু বছর ধরে আমার গল্পের বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম বছর জিহ্বার মিছিল প্রকাশিত হবার পর মেলার মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশক আমাকে বললেন, জানতাম কথাসাহিত্যিকেরা উদার হয়। কিন্তু আমার ভুল ভাঙল। আপনার বই প্রকাশ করায় আপনার ঘনিষ্ঠ লেখকবন্ধু এসে আপত্তি জানায়, আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে মনি হায়দারের গল্পের বই প্রকাশ করলেন কেন ?
প্রকাশক উত্তরে জানান, উনি অনেক দিন ধরে লিখছেন। গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত…। আমি গল্প পড়েছি, বেশ ভালো গল্প লিখেন মনি হায়দার।
কিন্তু আমাদের সঙ্গে যায় না।
আমি প্রকাশকের কাছে সতীর্থ বন্ধুর নাম জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, সব সময়ে আপনারা একসঙ্গে আড্ডা দেন। নাম বলা যাবে না।’
মনি হায়দার লিখেছেন, ‘গল্প যদি না লিখতাম, আমি কি আমার সতীর্থ গল্পকার, সে যেই হোক, আমি কি গল্পের এমন আখ্যানে এমন ক্যারেকটার পেতাম ? নিশ্চয়ই না।’ মনি হায়দারের জীবনটিই গল্প।
‘কচানদীর অট্টহাসি’ বড় মর্মান্তিক গল্প। ‘অনেক দিন পর বাড়ি আসে আবু ওসমান। ঢাকায় একটা পত্রিকায় মফস্সল সম্পাদক হিসেবে কাজ করে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর নিজেই সম্পাদনা করে কিন্তু বাড়ি আসার সময় পায় না। অবশ্য গ্রামে থাকার মধ্যে আছে এক চাচা। বহু বছর পর সেই চাচাকেই দেখতে আসা। লঞ্চঘাট থেকে সন্ধ্যানাগাদ চাচার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় আবু ওসমান। বন্ধুদের কাছেই শোনে আবু ওসমান, চাচার আর বাড়ি নাই, কচানদীর ভাঙনে বাড়ি এখন নদীর মাঝে জলের স্রোতে―এখন বেড়িবাঁধের ওপর দুই-তিনটি খুপরি নিয়ে কোনওভাবে থাকে। আবু ওসমানকে দেখে চাচা জয়নাল কেঁদে বুক ভাসান। চাচার অবস্থা দেখে আবু ওসমানের মনে হয় না-আসাই ভালো ছিল। এমন দুরাস্থা চোখে দেখা যায় না। অথচ কিছু করারও তো নেই। হঠাৎ কান খাড়া করল আবু ওসমান। পাশের ছোট রান্নাঘরে কথা চলছে চাচা জয়নাল আর চাচি আসমা খাতুনের।
‘কী খাওয়াবে ভাতিজাকে ? চাচি জিজ্ঞেস করে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জয়নালের উত্তর―সেটাই তো ভাবছি। একমাত্র ভাইয়ের ছেলে কতদিন পরে এসেছে।…’
ভাতিজাকে খাওয়ানোর জন্য অনেক ভেবে চাচা শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বের করে। আসার সময় তিন প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। এক প্যাকেট এর মধ্যেই বাচ্চাদের খাওয়ানো হয়ে গেছে। আর দু প্যাকেট মিষ্টি চাচা গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে বাজারে রওয়ানা হন, মিষ্টি তো এনেছে আবু আবুলের দোকান থেকে, তাকে বলেকয়ে যদি এক কেজি মিষ্টি ফেরত দেওয়া যায়, তাহলে তো তার দাম ষাট-সত্তর টাকা ফেরত পাবেন, সেই টাকা দিয়ে আবুর জন্য মাছ-তরকারি আনবেন। সব শুনে আবু ওসমান আর সহ্য করতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বেড়িবাঁধের খুপরি ঘরগুলো অতিক্রম করে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ায়। সামান্য দূরে কচানদীর পানি চিকচিক করে হাসছে। আবু ওসমানের মনে হচ্ছে নদীর পানি অট্টহাসি দিচ্ছে। স্থির থাকতে পারল না আবু ওসমান―প্যান্টের জিপার খুলে নদীর বুকে তীব্রগতিতে প্রস্রাব করতে লাগল।
নদীভাঙন বাংলাদেশের প্রকৃতির খামখেয়ালীর খেলা। এই খেলায় বাংলার নদীপাড়ের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। বলা যায়, ফকিরে পরিণত হয় নদীর ভাঙনে। গল্পকারেরা নদীভাঙনের প্রতিবেশ নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন কিন্তু মনি হায়দারের কচানদীর অট্টহাসি, আমার ধারণা সব গল্পকে ছাড়িয়ে গেছে, নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে।
‘ঘাসকন্যা’ মনি হায়দারের গল্প পঞ্চাশ বইয়ের আর একটি গল্প, যা পাঠককে অলৌকিক অভিজ্ঞতা দেয়। ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ঘাস কেটে পরিষ্কার করে নতুন করে ঘাস লাগানো হচ্ছে। সেই ঘাস লাগানোয় যুক্ত হয় জরিনা। জরিনার দুলাভাই এই কাজে নিয়ে আসে। মেয়েটা কাজে যেমন পটু, তেমন পটু কথায়ও। আগে থেকে যারা ঘাস লাগাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে গল্প করে আর ঘাস লাগায়। গল্প করতে করতে জরিনা জানায়, ছোটবেলায় তার যৌনাঙ্গ দিয়ে জোঁক ঢুকেছিল, যখন আলুশাক তুলছিল বাড়ির উঠানে। ওর চিৎকারে মা এসে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে ভেতর থেকে জোঁক টেনে বের করে আনে। মহিলারা অবাক হয়ে শোনে, মজা পায় জরিনা। বলে, আমার শরীরের মধ্যে এহনও জোঁকের আনাগোনা টের পাই।
ঘাস লাগানোর কন্টাক্ট্রর চিনটুর সঙ্গে লেনেদেনর বোঝাপাড়া করে একদিন জরিনার দুলাভাই জরিনাকে পৌঁছে দেয় চিনটুর বাসায়। এবার গল্পকার মনি হায়দারের ম্যাজিক―‘বলে কী মাগী! চিনটুকে ভয় পায় না ? দ্যাখ মাগি, ভয় কাকে বলে―পলকমাত্র, চিনটু প্রবিষ্ট হতে না হতেই জরিনার জোঁক প্রবেশের সুরঙ্গ তীব্র ঝংকারে খুলে যায়। অসম্ভব ক্রোধে ট্যাপের নলের মতো বের হয়ে আসতে থাকে টাটকা রক্ত, টাটকা রক্তের সঙ্গে শত শত ছোট ছোট চিনা জোঁক, আর সবুজ টুকরো টুকরো ঘাস। রক্তে ঘাসে আর জোঁকে চিনটুর শরীর লেপ্টে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব চিনটু। বিস্মিত চিনটু। জরিনাকে ছেড়ে দ্রুত সরে আসে রুমের একপাশে। কী হচ্ছে এসব ? কোত্থেকে আসছে এত সব জোঁক রক্ত আর সবুজ টাটকা ঘাস ? জরিনার ছোট চকমকে শরীর কাঠামোয় এসব আসবে কোত্থেকে ? জরিনা একইভাবে শুয়ে আছে বিছানার ওপর। দুদিকে ছড়ানো দুটি নধর চকচকে থাই, দুই থাইয়ের মাঝখান থেকে বেরুচ্ছে প্রবলবেগে টাটকা রক্ত, জোঁক আর ঘাস। ক্রমশ গতি বাড়ছে ঘাস, রক্ত আর জোঁকের। ভয়াবহ দৃশ্য। পাশবিক দৃশ্য।… দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্তাক্ত হচ্ছে চিনটু। রুমটার অর্ধেক প্রায় ভরে গেছে রক্তে, জোঁকে আর ঘাসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে চিনটুর।’
‘ঘাসকন্যা’ গল্পের আখ্যানে গল্পকার কী বলতে চেয়েছেন ? কী বার্তা দিয়েছেন―যে কোনও পাঠক নিজের মতো করে ব্যাখা করে নিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয়েছে, বিশাল প্রতিরোধের গল্প ‘ঘাসকন্যা’।
মনি হায়দার কেবল গল্পই লেখেন না, গল্পের কলকবজায় সমাজের সর্বনাশের ছিদ্র কুঠুরিও উন্মোচন করেন। বুঝিয়ে দিতে চান―আমরা যে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস করতে চাই―ক্ষমতা, চরিত্রহীনতা, অমানবিকতার মধ্যে বাস করছি। লেখক বা গল্পকার বার্তাই দিতে পারেন নিরন্তর লেখার ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গল্পে গল্পে মনি হায়দার সেই ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে যাচ্ছেন। গল্প পঞ্চাশ বইয়ের পঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতির ভূগোল, রাজাকারদের প্রতিষ্ঠাকরণ, বাংলাদশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত, বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র, ব্যক্তির সুখ ও সর্বনাশ, সমাজের ক্ষত ও লাবণ্যর করুণা দারুণ দক্ষতায় শব্দছেনি দিয়ে একটু একটু করে সংহত সন্ধানে তুলে এনেছেন গল্পকার মনি হায়দার।
প্রত্যেক লেখক বা গল্পকার বা কথাকারের নির্দিষ্ট কিছু প্রিয় বা নির্দেশিত শিল্পসুর থাকে, যেখানে তিনি নিজেকে নিবেদন করে, গোরখোদকের মতো খুঁড়ে খুঁড়ে তৃপ্তি পান। কথাশিল্পী মনি হায়দারের গল্প খুঁড়ে তৃপ্তির জায়গা―মূলত মানুষ, মানুষের অন্তঃভূমির অন্তহীন দূরত্ব, মানুষের বিপরীতে মানুষের তীর নিক্ষেপ, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং লালিত্য প্রেম। আর একটা বিষয়, গ্রাম। বাংলাদেশ মানে গ্রাম। কিন্তু শহরের নাগরিক বনে যাবার পর আমরা গ্রাম, ফেলে আসা চাতাল উঠান বন্ধু খাল মেঠো পথ ভুলে যাই। কিন্তু মনি হায়দার গল্পে গল্পে ফেলে আসা সেই গ্রাম, গ্রামের চরিত্র আর মাঠ গভীর মমতার সঙ্গে তুলে আনেন। কচানদী―মনি হায়দারের আবাল্যর সঙ্গী। অনেক গল্পে কচানদী, ভাণ্ডারিয়া উপজেলা, পিরোজপুর জেলা, বরিশাল শহর আর মানচিত্র প্রায় শরীরের জামার মতো তুলে আনেন, আবেগ আর স্মৃতির মূর্ছনায়। সবচেয়ে যেটা আমাকে বেশি আকর্ষণ করে মনি হায়দারের―সেটা, যখন তিনি বলেন, আমি লিখতেই ঢাকা শহরে এসেছি, লেখা ছাড়া কিছুই পারি না, তখন আমি এ পর্যন্ত লেখা মনি হায়দারের সাড়ে তিনশো ছোটগল্পের কাছে আনত হই। প্রাণিত হই। কথাসাহিত্যসাধনার এমন সাধক এই সময়ে আমাদের মধ্যে আছেন, ভেবে গৌরববোধ করি।
লেখক : প্রাবন্ধিক