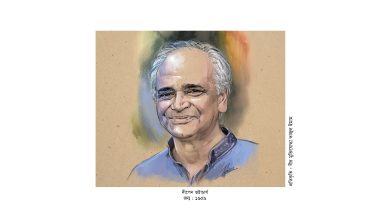ষাটের দশক : দেখি নাই কভু দেখি নাই : মফিদুল হক
আবার পড়ি : মফিদুল হকের প্রবন্ধ

মাত্র একটি দশকে কোনও জাতি যখন পাড়ি দেয় দীর্ঘ পথ, বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে জীবনের নতুন বিন্যাস খুঁজে নিতে উদগ্রীব হয়, কাঁধের ওপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে থাকে, বন্দি মানুষ স্বপ্ন দেখে মুক্ত মানুষ হওয়ার, শৃঙ্খলিত সমাজ হয়ে উঠতে চায় অবাধ স্বাধীনতার সমাজ, তখন সেই পরিবর্তমান দশক নিয়ে বিশ্লেষণী লেখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তনে থাকে নাটকীয়তার দিক, সেটাকে আমরা সচরাচর বলি রাষ্ট্রবিপ্লব, সেই বিপ্লবকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় দিনক্ষণ ধরে চিহ্নিত করা যায়, মূল ঘটনা ও নায়কদের শনাক্ত করে বিশ্লেষণে নামা যায়, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তেমনটা ভাবার অবকাশ কম। সমাজ রাতারাতি বদলে যায় না, ইতিহাস এখানে কাজ করে অলক্ষ্যে, তত গোপনে হয়তো নয়, তবে অনেক সময় অভ্যস্ত ভাবনার ঠুলি-আঁটা চোখে বুঝতে পারা যায় না কোনও ঘটনা কিংবা পদক্ষেপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, কিন্তু পরে বদলে যায় যখন অনেক কিছু, তখন আমাদের দৃষ্টিসীমায় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় পরিবর্তনের অবয়ব ও কার্যকারণ। আমরা বুঝতে পারি সে-এক আশ্চর্য সময় এসেছিল আমাদের জীবনে, যখন নিবিড় অন্ধকারেও ফুটে উঠছিল আলোর ইশারা এবং বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রয়াস ও ছোট-বড় নানা ঘটনা মিলিয়ে দেশ ক্রমে যেন তৈরি হয়ে উঠছিল বড় ধরনের পরিবর্তনের জন্য, তারপর যখন ডাক এল ইতিহাসের পালাবদলের, কী প্রবলভাবেই না বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই দায় মেটাতে! এভাবেই তো আমরা চিহ্নিত করতে পারি ষাটের দশককে।
অথচ দশকের শুরুটা ছিল একেবারেই তমসাচ্ছন্ন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ করা হয়, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা, বন্ধ হয় রাজনৈতিক দলের সকল কার্যক্রম এবং অগ্রণী রাজনীতিবিদদের অনেককে এবডো আইনের অধীনে অভিযুক্ত করে তাঁদের রাজনীতি করবার অধিকার হরণ করা হয়। সেনাবাহিনী এক শক্ত শাসন প্রবর্তন করেছিল এবং স্নায়ুযুদ্ধ পীড়িত বিশ্ব পটভূমিকায় বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সেনাশাসন পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে চলছিল নানাভাবে। ফলে ষাটের দশকের সূচনায় পাকিস্তানে ত্রাতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। ইতিমধ্যে তিনি বেসরকারি লেবাস পড়বার আয়োজনও শুরু করেছিলেন। কেননা সামরিক আইন বা বে-আইন যে বেশিদিন একনাগাড়ে চলতে পারে না, সেটা শাসকেরা ভালোই বোঝেন। পাকিস্তানের ৮০,০০০ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে কেবল তাঁদের দেওয়া হলো ভোটাধিকার এবং মৌলিক গণতন্ত্রী নামে পরিচিত আইয়ুবের পোষ্য এই পুত্ররা দেশবাসীর পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে, এমন কামনা ছিল লৌহশাসক রাষ্ট্রপ্রধানের মনে।
ষাটের দশক তাই শুরু হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্রের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করবার নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সামরিক শাসন শিথিল কিংবা বিলোপ করে শক্ত শাসন কীভাবে অব্যাহত রাখা যায় সেটা সমরকর্তাদের জন্য ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই কাজে তারা যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিলো তা বেশ লক্ষণীয়। আইয়ুবের ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল তাঁর মিলিটারি শাসনকে মানুষ, বুঝে হোক না বুঝে হোক, উল্লাসভরে স্বাগত জানিয়েছিল। ফলে সমরকর্তাদের হাতে খেলবার মতো তাস ছিল অনেক, আর আদর্শগতভাবে তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রে তুরুপের তাস হিসেবে তো সবসময়েই রয়েছে ধর্মকে ব্যবহারের সুযোগ। গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করে নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আইয়ুব খান বেছে নিলেন অভিনব পন্থা, নাগরিক অধিকারে আঘাত হানবার জন্য হাতে পরে নিলেন ভেলভেটের দস্তানা, ব্যবস্থা করলেন আস্থা ভোটের। আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী তথা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের দিয়ে তিনি আস্থা ভোট নিলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর পদাধিকার বিষয়ে রায় দেওয়ার জন্য। যে পদ তিনি অধিকার করেছেন কারও রায়ের তোয়াক্কা না করে এবার সেই পদকে বৈধ করার জন্য সর্বজনীন নয়, তাঁরই নির্ধারিত পদ্ধতি মান্য করে নির্বাচিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে হাজির হলেন ভোটের জন্য। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ অনুষ্ঠিত এই ভোটাভুটিতে দেখা যায় ৯৫.৬ শতাংশ ভোট পড়েছে অনুমোদনের পক্ষে। এর অন্যথা হওয়ার কোনও উপায় ছিল না, কেননা ক্ষমতাবানদের মতে অধিকাংশ জনগণ তো অবোধ, নিরক্ষর তো বটেই, তাই তাদের পক্ষে কথা বলতে পারেন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ব্যক্তিরা। এমন একটি অভিনব ‘গণতান্ত্রিক’ ধারণা শাসকদের জন্য খুব যুৎসই প্রমাণিত হয়, একে জনগণের রায় হিসেবে চিত্রিত করার জন্য জোর প্রচারণা চলতে থাকে। ফলে আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিকাশ এই অভিনব গণতন্ত্রের পথ ধরেই অগ্রসর হতে থাকে। ‘এক মানুষ এক ভোট’-এর বদলে ‘লক্ষ মানুষ এক ভোট’-এর নীতি চমৎকার এক নিয়ন্ত্রণযোগ্য গণতন্ত্রের সম্ভাবনা মেলে ধরে। সেটা সোনার পাথরবাটি গড়বার প্রয়াস কিনা, নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে কিনা, সেসব প্রশ্ন তখন আর উত্থিত হয়নি, বরং ষাটের দশকের গোড়ায় আইয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রের গুণকীর্তনে পত্রপত্রিকা সয়লাব হয়ে পড়েছিল।
আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ‘জনগণের রায়’ অর্জন করেছেন ভেবে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ পেয়েছিলেন। এবারে শাসকগোষ্ঠীর বড় দায়িত্ব হলো দেশকে তাদের চিন্তানুকূল সাংবিধানিক শাসনের পথে ফিরিয়ে আনা। ইতোমধ্যে রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট হেয় করতে সক্ষম হয়েছে সামরিক সরকার, তারাই যেন পাক-পাকিস্তানের সকল দুর্গতির জন্য দায়ী, আর তাই তাদের দ্বারা প্রণীত ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, বরং দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দরকার স্বীয় তাহজিব-তমদ্দুন ও বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত নতুন শাসনতন্ত্র, যা হবে সামরিক শাসনের পরিবর্তিত রূপ।
এবার আসে সেই পালা। গঠিত হয় বিচারপতির সভাপতিত্বে শাসনতান্ত্রিক কমিশন। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনের পক্ষে মত প্রকাশ করে আইয়ুব এক অভিনব যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় মাত্র একটি লোক কোনওরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়া পূর্ণ দায়িত্বসহ জনসাধারণের সর্বোত্তম স্বার্থে সরকার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এভাবে একজন মানুষের ওপর সর্বজনের ভার চাপিয়ে প্রায় রাজতন্ত্রসুলভ রাষ্ট্রপতি শাসিত সাংবিধানিক কাঠামোর প্রস্তাব করতে সেনাপ্রধানের চোখের পাতা বিন্দুমাত্র কাঁপেনি, কেননা সেই একজন মানুষ তো তিনি স্বয়ং। এই ছিল ষাটের দশকের শুরু।
ষাটের দশকের গোড়ায় বাধাবন্ধনহীনভাবে পাকিস্তান অগ্রসর হতে শুরু করল এক নিয়ন্ত্রিত পীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে। ১৯৪৭ সালে এই অভিনব দেশের যাত্রা শুরুর পর থেকে দেশটি কোনও শাসনতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, এবার ভিন্নভাবে সেই স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। এক লৌহমানবের শাসনে পাকিস্তান পাবে স্থিতিশীলতা, ঘটাবে উন্নয়ন এমনই ছিল লক্ষণ ও লক্ষ্য। তবে জাতির বিকাশের উপযোগী পথ শনাক্তকরণে ছিল ভ্রান্তি এবং লক্ষ্য ছিল ভুল, আর তাই পাকিস্তানের এই নবযাত্রা তাকে চোরাবালির দিকেই ঠেলে দিল। তবে সেসব তো অনেক পরের কথা, তখন ছিল ভিন্ন এক সময়, ভিন্ন এক পরিস্থিতি।
২.
শাসকেরা তাদের পছন্দসই যে-পথ বেছে নিক না কেন ইতিহাসের আছে কিছু অভিঘাত যা কারও পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। ষাটের দশকের সূচনায় পাকিস্তান যখন ছকবাঁধা পথ ধরে এগুচ্ছে তখন ১৯৬১ সালে সামনে এসে দাঁড়াল মহত্তম বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী। মহৎ এক কবির জন্মশতবর্ষ নিয়ে উৎসবে মেতে উঠবে সেই জাতি, রাষ্ট্র তাতে জোগাবে সহায়তা, সেটা নিয়ে কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের এই রাষ্ট্রটি দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্র, আর কবি হচ্ছেন অমুসলিম, আদতে ব্রাহ্ম কিংবা বলা যায় প্রচলিত ধর্মানুসারী নন। ফলে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী হয়ে উঠল অভিনব পাকিস্তানের জন্য অভিনব সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা, যারা প্রায় সর্বাংশে বাঙালি, তাদের পাকিস্তানি করবার যে আয়োজন সাতচল্লিশ সাল থেকে চলছে সেখানে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী তো বাঙালিত্বের জয়জয়কার গাইবে, ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের মুসলিম জাতিত্বের তাহলে কী হবে ?
একদিকে যুক্তি, আরেক দিকে মূঢ়তা এবং পাকিস্তান মূঢ়তার পথই বেছে নিল। তবে শাসকেরা সঙ্কীর্ণতার কূপমণ্ডূক পথ বেছে নিলেও সমাজ, কিংবা সমাজের সবাই তো আর সেই পথ অনুসরণ করেন না। মিলন ও উদারতার জয়গান করবার মতো মানুষ সবসময় মেলে, আর তাঁদেরই উদ্যোগে ঢাকায় বিশাল আয়োজনে উদযাপিত হলো রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী, শাসকগোষ্ঠীর ভ্রƒকুটি উপেক্ষা করে গঠিত হয়েছিল দুটি নাগরিক কমিটি, নেতৃত্বে প্রবীণেরা রইলেও এর একটিতে প্রধানত ছিলেন সঙ্গীত-সংস্কৃতির মানুষেরা, আরেকটিতে জড়ো হয়েছিলেন তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা। আমরা দেখতে পাই এই দুই কমিটির মানুষেরাই ষাটের দশকের সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে পরে রেখেছিলেন স্থায়ী ও গভীর প্রভাবসম্পন্ন অবদান এবং তাঁদের যাত্রাবিন্দু ছিল ঐ পঁচিশে বৈশাখ। তমসাচ্ছন্নকালে তাদের সেই প্রয়াস আকারে বিশাল না হলেও তাৎপর্য ছিল বিপুল।
পাক-শাসকেরা যে বিকৃত ভাবনা অবলম্বন করেছিলেন তা তাদেরকে টেনে নিয়েছিল বিকৃত অবস্থানের দিকে। ছোট একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৬০ সালে ঢাকাস্থ মার্কিন কনসুলার অফিসে রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন আর্চার ব্লাড। সপরিবারে তিনি অবস্থান করছিলেন ঢাকায় এবং অন্য কূটনীতিক পরিবারের সঙ্গে মিলে তাঁরা সখের নাটক মঞ্চায়ন ও আরও বিভিন্ন ধরনের বিনোদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তোপখানা রোডের ছোট্ট অথচ সাজানো-গোছানো ইউসিস মিলনায়তনে তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন জন স্টাইনবেকের অফ মাইস অ্যান্ড মেন নাটক। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপস্থিত হলে তাঁরা কবির ডাকঘর নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি নেন এবং সুধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ব্লাডের দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা শিরিন ব্লাড। স্মর্তব্য, ইতিহাসের পরিক্রমণায় এই আর্চার ব্লাডই সত্তর সালে আবার এসেছিলেন ঢাকার কনসাল জেনারেল হয়ে এবং একাত্তরের গণহত্যার বিরুদ্ধে ভূমিকা নিতে মার্কিন প্রশাসনকে বারংবার তাগিদ দিয়ে নিক্সন-কিসিঞ্জারের বিরাগভাজন হন তিনি। ব্লাড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :
‘ইউসিস (মার্কিন তথ্য কেন্দ্র) প্রস্তাব করেছিল যে, মহান বাঙালি কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সহায়তা হিসেবে তাঁর একটি নাটক আমরা মঞ্চায়ন করতে পারি। বাংলাভাষীদের কাছে ঠাকুরের স্থান ইংরেজিভাষীদের কাছে শেকসপিয়রের সমতুল্য। মঞ্চায়নের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল দা পোস্ট অফিস নামক একাঙ্ক নাটক এবং ইংরেজিতে তা মঞ্চস্থ হয়েছিল। শিরিন অভিনয় করেছিল গ্রামের এক বালিকার ভূমিকায় এবং, আমার পক্ষে বলা যদি শোভন হয়, শাড়িতে সজ্জিতা হয়ে তাকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব।’
ব্লাড আরও জানিয়েছেন, ঢাকায় সোৎসাহী বিশাল এক বাঙালি দর্শকমণ্ডলীর সামনে পরিবেশিত হয় নাটক। এরপর উত্তরের পথ পাড়ি দিয়ে নাটক পৌঁছয় ময়মনসিংহ। সেখানে দর্শক ছিল আরও বেশি। হঠাৎ, কোনও কারণ না দেখিয়েই, পূর্ব পাকিস্তানের সরকার নোটিশ জারি করে নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেয়।
রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালন নিছক এক সাহিত্য-সংস্কৃতি উৎসব ছিল না, এর পটভূমিকায় ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রদর্শনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যা বলপূর্বক ঘুচিয়ে দেয়ার চেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী যেন সফলতার আমেজ অনুভব করতে পারছিলেন। তবে তার চাইতেও বড় সত্য হলো বাঙালির জাতীয়তাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক বিকাশের যে ধারাটি রাজনৈতিকভাবে পরাভূত হয়েছিল তার সাংস্কৃতিক চেতনার পরাভব না মানা শক্তি এই উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্ফূরিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জাতিসত্তার উন্মেষ ও সংহতি ঘটিয়ে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠান ঘটায়। এই রাজনৈতিক শক্তি নানা দোদুল্যমানতা ও আপোষের পরিচয় দিলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন করে এবং সর্ব-পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জোরদার অংশীদারিত্ব তুলে ধরে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের দুর্বলতা ও জটিলতা সত্ত্বেও পাকিস্তান সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ধারায় নিজেকে স্থাপন করবে এবং দেশটিতে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে―এটা হয়ে পড়েছিল স্বতঃসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হলো তা নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র স্বার্থবাদী চক্রের আধিপত্য থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করবে, এমনই যখন প্রত্যাশা তখন বিভিন্ন অজুহাতে জারি করা হয় সামরিক শাসন। পাকিস্তানকে সাংবিধানিক শাসনের পথ থেকে চ্যুত করে ভিন্ন এক পথে চালিত করার জন্যই ছিল এত সব আয়োজন। সেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এক চরম অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা হয়, কারাগার ভরে ওঠে রাজবন্দিতে, সবরকম রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হয়ে পড়ে সীমিত এবং পাশাপাশি চলছিল পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার উপযোগী এক সাংবিধানিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে দেশে কোনও প্রতিবাদের সুযোগ ছিল না, প্রতিবাদ সংগঠনের শক্তি ও উপায় রাজনৈতিক দলগুলোর ছিল না।
সামরিক শাসনের শাসরুদ্ধকর সেই পরিবেশের ভয়াবহ দিক ছিল উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতি ব্যাপক মানুষের এক ধরনের নিস্পৃহ সমর্থন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তুলতে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা মানুষের মধ্যে যে বীতশ্রদ্ধ ভাব সঞ্চার করেছিল তার সুফল বর্তেছিল সামরিক শাসকদের ওপর। অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই অংশকে কেন্দ্রশাসিত ধর্মভিত্তিক একক রাষ্ট্রে পরিণত করার আয়োজন নানা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিল। পাকিস্তানের বহুজাতিক বাস্তবতা ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার পটভূমিকায় ফেডারেল ব্যবস্থা কিছুটা হলেও কার্যকর রাষ্ট্র জন্ম দিতে পারত; কিন্তু বিভিন্ন জাতিসত্তার সেই অধিকার মেনে নিলে তো মুসলমান জাতিতত্ত্ব আর হালে পানি পায় না। পূর্ববঙ্গের ওপর ঔপনিবেশিক ধাঁচের যে শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার ফলে পূর্ববঙ্গের রফতানি আয় জমা হতো কেন্দ্রে এবং কেন্দ্র তা বাঁটোয়ারা করে দিত মুসলিম জাতির বিভিন্ন অংশে, যার বড় ভাগটা যেত সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিমাংশে। সেই বাস্তবতা ডেকে এনেছিল আঞ্চলিক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের আয়ের সুবিধা নিচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। তাই মুসলিম জাতিসত্তার বুলি পশ্চিমী শাসকদের জন্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিশেষ ফলপ্রদ, সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করেছিল সামরিক শাসন; কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কঠিন কাজটি কিছুতেই তারা সমাধা করে উঠতে পারছিল না। বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার অস্বীকার করতে গিয়ে তারা বিপদ ডেকে এনেছিল। ভাষা আন্দোলনের অভিঘাতে সেখান থেকে কিছুটা পিছিয়ে এলেও সেই প্রচেষ্টা থেকে শাসকগোষ্ঠী কখনও সরে আসেনি। তাদের এইসব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক সৃজনমুখর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ছিল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালন উৎসব, যদিও সরব কোনও প্রতিবাদী আয়োজন সেটা ছিল না, ছিল আপন সত্তায় বিশ্বাসী গাঢ় উচ্চারণ।
শতবর্ষ আয়োজনে সুফিয়া কামাল, বিচারপতি এস. এম. মুরশেদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, কাজী মোতাহার হোসেন, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একদল তরুণ ছাত্র যাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মনজুরে মওলা, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রশীদ হায়দার, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ। ষাটের দশকের নবীন সাহিত্যান্দোলনে যাঁরা নানাভাবে সক্রিয় হবেন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় সোচ্চার হবেন তাঁরা এভাবেই বুঝি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনেও দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে বিশাল এই উৎসব কর্মকাণ্ড বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তা ও শক্তিময়তার যে বোধ সঞ্চার করে তাকে সৃজনশীলভাবে বহমান রাখার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুধাবন করেন কেউ কেউ। উৎসব পালন শেষে সুফিয়া কামালের পৌরহিত্যে ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন ও আরও গুণিজনের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো ছায়ানট, সঙ্গীতশিক্ষার বিদ্যায়তন চালু করে যে ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার ক্রমবিবর্তন তো বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে।
তবে এসব তো বীজ বপনের কাহিনি, এর পাশাপাশি জাতিসত্তাকে আড়ষ্ট ও পঙ্গু করবার আয়োজনও ছিল জোরদার। ঢাকা জেলা পরিষদে আয়োজিত এক সভায় গোলাম আযম, মওলানা মহিউদ্দিন প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমি ও বেতারকেন্দ্রকে ‘বিজাতীয় সঙ্গীত- সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত’ করার আহ্বান জানান। সভা ছোট হতে পারে, বৃহত্তর সমাজ এই অর্বাচীন আহ্বান সহজে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ঘৃণা ও সংঘাতের বিষবৃক্ষে জল ঢালার প্রক্রিয়াও যে অব্যাহত ছিল সেটা লক্ষ করবার বিষয়।
পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের এই বিষবৃক্ষ নানাভাবে ডালপালা জারিত করে চলছিল। সামরিক শাসনে উদার প্রগতিমনা চিন্তার ওপর যে বাধা আরোপিত হয়েছিল সেটাও আদায় করে নিয়েছিল মূল্য। পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যে থেকে আপসের পথে নিজেদের জন্য সঙ্কীর্ণ ঠাঁই করে নেওয়ার চিন্তাও অনেকের মনে বাসা বেঁধেছিল। বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও চর্চা কারও মানসে যে উদার সংস্কৃতিবোধ জন্ম দেয় তার ফলে পাকিস্তানি কূপমণ্ডূকতার সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়; কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে তাঁরা একটি আপসের পরিসর তৈরি করতে সচেষ্ট হন। এমন মানুষদের কেউ কেউ রবীন্দ্রশতবর্ষের আয়োজনেও শরিক ছিলেন, যেমন ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, শতবর্ষের ভাষণে তিনি বলেছিলেন :
‘পাকিস্তানবাদী হিসেবে আমরা একটি আলাদা জাতি… কিন্তু ভাষার দিক থেকে অন্য কোনও জাতির সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে বলেই আমাদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুদ্র হতে পারে, এ কথাটা সহজে গ্রহণ করা মুশকিল। আমাদের মনে যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কোনও সংশয় না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকবে কেন ?’
ফলত বোঝা যায়, নানা ধারা-উপধারায় বিভক্ত ছিল সমাজ, দ্বিজাতিতত্ত্বের সোৎসাহী সমর্থক মৌলবাদী গোষ্ঠী এক কাল্পনিক জাতিসত্তা গড়তে অবাস্তব ও অসম্ভবের ফর্দ দাখিল করে চলছিল, তারা সচেষ্ট ছিল সাম্প্রদায়িক চিন্তার কলুষে বিষভাণ্ড পূর্ণ করে তুলতে। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একটি বড় অংশ ঐ কূপমণ্ডূক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতে না পারলেও তার সঙ্গে তথাকথিত পাকিস্তানি জাতিসত্তার অলীক অবাস্তবতার একটি যোগসূত্র রচনার অসার প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেছিলেন। আর ছিল সেই গোষ্ঠী যারা জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক উৎস-সন্ধানী এবং সেই উৎস থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে পথ চলতে উদগ্রীব। ষাটের প্রবীণ ও নবীন দুইয়েরই দেখা আমরা পাই আমরা এই শেষোক্ত প্ল্যাটফর্মে, রবীন্দ্র জয়ন্তীর সুবাদে।
দেশ কোন পথে এগুবে সেটা বোঝা না গেলেও তিনটি ভিন্ন পথের রেখা যেন শনাক্তযোগ্য হয়ে উঠেছিল।
৩.
পূর্ববঙ্গের অসাম্প্রদায়িক উদারবাদী মানস দানা বাঁধবার জন্য খুঁজে ফিরছিল নানা অবলম্বন। এর একদিকে ছিল যৌথ কর্মপ্রয়াস, আরেক দিকে ছিল সৃজনশীল প্রকাশের ব্যক্তিক আকুতি। উভয় ক্ষেত্রেই পাকিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাধা, যেমন যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, তেমনি একক সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নে। ফলে এই দুই প্রবণতা দুটো সমান্তরাল রেললাইন কেবল হয়ে থাকেনি, মাঝে-মধ্যে দুইয়ের সম্মিলনও ঘটছিল। এই সম্মিলনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে যে ক্ষেত্রটি পূর্ববাংলায় তৈরি হয়েছিল তা হলো ছাত্র-তরুণদের বুকের রক্তঢালা বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এবং সেই স্মৃতিবহ শহিদ মিনার।
তবে তার আগে এটা বিবেচনায় নেওয়া দরকার ষাটের দশকের সমাজের শিল্পচেতনা কীভাবে এবং কোন চরিত্র নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে যেটা বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার তা হলো, শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাহিত্য ছিল মুখ্য ভূমিকায় এবং পুরনো কোনও কোনও মাধ্যম তার প্রভাব ও মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলতে বসেছিল, যেমন নাটক। নাটকের ওপর বড় আঘাত নেমে এসেছিল দেশভাগের ফলে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মফসসল শহর ও ঢাকায় সামাজিকভাবে নাট্যচর্চার যে জোরদার অবস্থান ছিল তা হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ও ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসারে ক্রমেই সঙ্কুচিত ও ক্ষীণতোয়া হতে থাকে। সামাজিক নাট্যচর্চার ধারা থেকে যুগের পালাবদল সূচিত হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তার বলিষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখি ড্রামা সার্কেল-এর অলৌকিক উত্থানে। উল্লেখ্য, ড্রামা সার্কেল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে নিবেদন করেছিল রক্তকরবীর অসাধারণ প্রযোজনা। ষাটের দশকে তাদের অন্য প্রযোজনার মধ্যে ছিল সপ্তশূরের থিবি আক্রমণ কিংবা দাঁতোর মৃত্যুর মতো ক্লাসিক ও আধুনিক নাটক। কিন্তু ড্রামা সার্কেল বুঝি ছিল লাস্ট অব দি মহিক্যানস, অতীত নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় নতুন শিল্পধারণায় উদ্বুদ্ধ একক প্রতিষ্ঠান, তারা নিজেরা যেমন টিকে থাকতে পারেনি পাকিস্তানি বদ্ধ ও বৈরী সমাজে, তেমনি কোনও ধারাবাহিকতাও রেখে যেতে পারেনি। ড্রামা সার্কেল থেকে আর্ত বেদনার মতো নিবেদিত হয়েছিল সাঈদ আহমদের কালবেলা, পাকিস্তানি পর্বে সেটাই বুঝি তাদের শেষ নাটক, আঁধার-পীড়িত বেলায় জীবনের অর্থহীনতায় পীড়িত সংবেদনশীল শিল্পীর বেদনার অ্যাবসার্ড আলেখ্য।
কোন শিল্পরূপে সমাজ কখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সেটা বোধহয় এক জটিল জিজ্ঞাসা। তা না হলে প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্র এমন মহান জাগরণ কীভাবে সূচিত করতে পারল! এর একটি পূর্ব-ইতিহাস অবশ্য রয়েছে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ববঙ্গে ক্ষমতায় এলে শহিদ মিনার নির্মাণের পাশাপাশি চলচ্চিত্র স্টুডিও স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই নতুন সুবিধা গ্রহণের জন্য এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভা এগিয়ে আসে এবং নানামুখী কাহিনি অবলম্বন করে সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়। দেশব্যাপী যেসব প্রেক্ষাগৃহ ছিল তাদের এযাবৎ নির্ভর করতে হতো ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র এবং লাহোরে নির্মিত বাজারি উর্দু ছায়াছবির ওপর। ঢাকায় নির্মিত শিল্পসম্মত ও পরিচ্ছন্ন বাণিজ্যিক ছায়াছবি সেখানে এক নতুন হাওয়া বয়ে আনল। লাহোর এতকাল যাবৎ যা করতে ব্যর্থ হয়েছে ঢাকা সামান্য সুযোগেই সেই শিল্পসত্তার উদ্ভাসন ঘটায়। এই প্রতিভাবান নির্মাতাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান, মহিউদ্দিন, সুভাষ দত্ত, আলমগীর কবীর, সাদেক খান, সালাহউদ্দিন ও আরও অনেককে। তাঁরা যেমন সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন (নদী ও নারী, আনোয়ারা, সূর্যস্নান) তেমনি নিজস্ব কাহিনি নিয়ে তৈরি করেছেন বাস্তবজীবনভিত্তিক ছায়াছবি (কখনও আসেনি, কাচের দেয়াল, সুতরাং), নিরীক্ষামূলক ছবি নির্মাণেও ব্রতী হয়েছেন (রাজা এল শহরে, সোনার কাজল) ইত্যাদি। ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা ছায়াছবির ইতিহাস বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ষাটের দশককে মাতিয়ে তুলেছিল। যৌথ শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাণে বিভিন্ন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ছিল জাতিসত্তার শক্তিময়তার এক প্রধান দিক। বাঙালির জাতিসত্তা সংহতকরণে চলচ্চিত্রের এই ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়।
তবে বাঙালির জায়মান শিল্পতাগিদ প্রকাশের অনুপম পথ খুঁজে পেয়েছিল সাহিত্যে এবং ষাটের কবি-সাহিত্যিকরা তাদের জীবনদৃষ্টি, শিল্পপ্রকরণ, শৈলী সবকিছুতে নানা বিভিন্নতা ও পার্থক্য সত্ত্বেও যেন সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন বাঙালি সত্তার জয়গান। অথবা বলা যায় জাতিসত্তার একটি অর্কেস্ট্রাবাদন যেন আমরা শুনতে পাই যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পযন্ত্র আলাদা আলাদা তান তুলে এক সম্মিলিত সুরের জন্ম দিয়েছিল।
ষাটের দশকের যে জাগরণী প্রয়াস সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধলো সেখানে এটাও লক্ষণীয় সাহিত্য-আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক ছিল না, বরং বলা যায় রাজনীতি থেকে যোজন-দূরবর্তী ছিল তাদের অবস্থান। কিন্তু জীবনের উপলব্ধি ও আকুতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা যে নতুন ভাষারূপ ও শিল্পশৈলী তৈরি করতে চাইলেন সেটা তাদের তাগিদকে জাতির আকুতির সঙ্গে একাকার করে ফেলেছিল। পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বজাত কূপমণ্ডূকতা থেকে জাতি চাইছিল মুক্তি, আর তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা বিদ্রোহ করেছিলেন অগ্রজদের অশিল্পজনোচিত বন্ধ্যা সাহিত্যপ্রয়াসের বিরুদ্ধে, সবরকম ফিলিস্তিনি মনোভাব ভেঙে চুরমার করে তারা মানবিক অভিজ্ঞতার সমগ্রতাকে ধারণ করতে চাইছিলেন। তাই তাঁদের অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে হয়নি, তারা চরিত্রগতভাবে উদার ও আন্তর্জাতিক, সাম্প্রদায়িক চিন্তার কলুষ তাদের মনে রেখাপাত করেনি, (কারও কারও ক্ষেত্রে মনে হয় অন্তত সেই ষাটের দশকে করেনি), তাঁদের আধুনিকতা সবরকম রাষ্ট্রসীমা অগ্রাহ্য করেছিল, তাই উপমহাদেশের বিভাজনকে তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হতে দেননি একান্ত স্বভাবগতভাবেই। তুলনায় পঞ্চাশের কবিরা ছিলেন অনেক বেশি রাজনীতি-সংলগ্ন ও সমাজ-সচেতন। হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বামপন্থি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কারাবন্দি হয়েছেন তখনকার লেখকদের অনেকে, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, শহীদ সাবের প্রমুখ কারাগারে বসে লিখেছিলেন উল্লেখযোগ্য রচনা। ষাটের কবি-সাহিত্যিকদের এমনি ধরনের প্রত্যক্ষ কোনও যোগ ছিল না রাজনীতির সঙ্গে; কিন্তু জাতীয় জাগরণের মানস তারা ধারণ করেছিলেন ভিন্নভাবে এবং এখানেই বোধহয় তাদের বিশিষ্টতা।
ষাটের দশকের সাহিত্যের স্পন্দন অনুভব করার জন্য দুটি সাহিত্য পত্রিকার সহায় আমাদের নিতে হবে, এর একটি সিকান্দর আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিকতাদুষ্ট ক্ষুদ্র বলয়, যা পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার অনুকূল, তাকে রুচি ও মননের বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দিতে পালন করে তাৎপর্যময় ভূমিকা। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার সমকাল কবিতা সংখ্যা তৎকালীন পরিবেষ্টনে ছিল প্রায় কল্পনাতীত এক কাজ। সংখ্যাটির সূচনা প্রবন্ধ ‘বন্দি-বিবেক সমাজ ও কবিমানস’ রচনা করেছিলেন আবদুল গণি হাজারী, তিনি তৎকালীন সমাজমানসকে প্রতিফলিত করে লেখেন, ‘আমি যে কবির কথা ভাবি সে হলো আধুনিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, শিক্ষিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত এবং তীক্ষè সংবেদনশীল অথচ বিশ্লেষণী মনের মালিক। এইসব মিলিয়ে তার সমাজচৈতন্য রচিত, তার সামাজিক কর্তব্যবোধ বিবেক সংহত। এমন এক কবি যখন সৃষ্টিশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তার কবিতায় আমরা সমাজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাই।’
এক নতুন কবিকুলের আগমনের পদধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছিলেন আবদুল গণি হাজারি কিংবা বলা যায় সমকাল-গোষ্ঠী। এই কবিরা আধুনিক জীবনবোধ থেকে শিল্পচর্চায় ব্রতী হবেন এবং অগ্রসর মননশীলতায় প্রাণিত ও তাড়িত হয়ে যে নতুন সাহিত্য রচনা করবেন তাতে শোনা যাবে সমাজের হৃৎস্পন্দন। এমন কবিদের জন্য বাঁধাধরা কোনও পথ নেই, পথে নেমেই তাঁরা খুঁজে নেন পথের রেখা। আর এই নতুনের সন্ধানে নানাভাবে পথ হাতড়ে ফিরছিলেন তরুণ লেখকদের দল। বুদ্ধদেব বসু যখন অনুবাদ করলেন শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা, তরুণেরা যেন পেল এক নতুন পথের সন্ধান; কিন্তু উনিশ শতকের বোদলেয়ার তো আর বিশ শতকের টগবগে তরুণের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারেন না, তা ক্লেদজ কুসুমের আবেদন যা-ই হোক। তরুণদের একটি অবলম্বন হলো পশ্চিমের হালফিল সাহিত্যান্দোলন, পশ্চিমও তখন কাঁপতে শুরু করেছিল রাগী তরুণদের পথ বেয়ে আসা বিট জেনারেশনের বেপরোয়া উদ্দামতায়। ততখানি উদ্দাম হতে না পারলেও প্রচলভাঙার আকুতিতে বঙ্গীয় তরুণেরাও কম যাননি। পশ্চিম বাংলায় যে হাংরি জেনারেশন উদ্ভূত হয় পূর্বে তা স্যাড জেনারেশনের প্রতীক ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের ভিন্নতর পরিবেশে যে-তরুণেরা প্রবল জীবনক্ষুধায় অধীর, পূর্বের পাকিস্তানি বাস্তবতায় তাঁরা কিছুটা বিষণ্ন নিশ্চয়ই, যতটা না হাংরি, তার চেয়ে বেশি স্যাড। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত বুলেটিনে ইংরেজিতে তাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের বক্তব্য, দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হওয়ার আকুতিও বোধহয় ভাষা বিবেচনায় নিহিত ছিল, লিখেছিলেন : ‘আমরা কি চাই… কিছু না, কিছু না, এই হারামির সমাজ থেকে আমরা কিছু প্রত্যাশা করি না।… আমরা শ্রান্ত, বিরক্ত, ক্লান্ত এবং বিষণ্ন।’ অনতিতরুণ রফিক আজাদ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রশান্ত ঘোষাল, আসাদ চৌধুরী, বুলবুল খান মাহবুব প্রমুখ।
ষাটের তরুণেরা লেখার নতুন বিষয় ও প্রকরণ যেমন খুঁজছিলেন, তেমনি নিজেদের জন্য পত্রিকা প্রকাশেও অধীর হয়েছেন। তাদের প্রকাশিত স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক, প্রতিধ্বনি, সমস্বর এসবই অত্যন্ত কৃশকায় সঙ্কলন, আকারে সামর্থ্যরে সীমানা প্রকাশ করলেও চিন্তার বৈভব ছিল ষোলো আনা। তবে ষাটের এই তরুণদের সাহিত্য পত্রিকার ছত্রতলে একত্র করে এক সাহিত্যান্দোলনের জন্ম দেওয়া এবং সাহিত্যের নতুন বাঁক নেওয়ার যুগান্তকারী কাজটি সম্পন্ন হয়েছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত কণ্ঠস্বর-এর প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল :
‘যারা সাহিত্যের সন্নিষ্ঠ প্রেমিক, যারা/ শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত,/ শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা/ উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত,/ অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী,/ যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, অশ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত,/ যারা পঙ্গু, অহঙ্কারী,/ যৌনতাস্পৃষ্ট/ কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা।’
স্যাড জেনারেশনের উদ্ধত ভাব এখানে কিছুটা নমনীয়, তার বদলে রয়েছে সেই জেদি আত্মসচেতন ভাবটিকে শিল্পশোভনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা, আছে চমক দেওয়ার প্রবণতাও। এ-সমস্ত কিছুকে আমরা এক কথায় বলতে পারি যুগ-লক্ষণ।
৪.
যুগ-লক্ষণ নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে চললেও, কালের রথকে রুদ্ধ কিংবা পথভ্রষ্ট করার রাষ্ট্রিক আয়োজনও তো কম ছিল না। এরই এক নিষ্ঠুর প্রকাশ ঘটলো ১৯৬৪ সালে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। পূর্ববঙ্গের সমাজে সম্প্রীতির যে শক্তি সেটা হয়তো দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি রুখে দাঁড়াতে পারবে এমন ভরসা খানখান হয়ে গেল এই বীভৎস দাঙ্গায়। কাশ্মীরে হযরতবাল মসজিদে রক্ষিত মহানবীর কেশ কে বা কারা হরণ করেছে এমন গুজবের ভিত্তিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তানে। ঢাকায় ভয়াবহ কতক রক্তপাত ঘটে, প্রায় ক্ষেত্রেই একপেশে, সাভার ও আরও কিছু এলাকায় চরম নৃশংসতার অবতারণা হয়। দাঙ্গাবাজদের রুখতে গিয়ে নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে ছুরির আঘাতে জীবন হারালেন আমীর হোসেন চৌধুরী, রোকেয়ার আত্মীয় এবং প্রগতিবাদী লেখক। এই দাঙ্গা পাকিস্তানি শাসকদের নতুনভাবে মদদ জোগায়, হিন্দু ও মুসলমানের অমোচনীয় ফারাক বিষয়ে তাদের কথাই বুঝি সত্যি, হানাহানি ও সংঘর্ষ ছাড়া এই দুই ধর্মগোষ্ঠী বুঝি শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না, পৃথক রাষ্ট্র করে যদি রেহাই না মেলে তবে পার্থক্যকরণ এখন আরও বাড়াতে হবে।
দাঙ্গায় কণ্ঠস্বর গোষ্ঠীর সদস্য সেবাব্রত চৌধুরী দেবব্রত চৌধুরীর পরিবার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরে আরও অনেক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে তাঁরাও দেশত্যাগে বাধ্য হন। এই দাঙ্গা পূর্ববঙ্গের সমাজবন্ধনে যে বিষময়তার সঞ্চার করে তা অনেক গভীরে জারিত হয়। অন্যদিকে দাঙ্গার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসে। ‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’ শীর্ষক অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোতে। শেখ মুজিব, সুফিয়া কামাল থেকে নবীন শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী নানা মত ও পথের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু মানুষ দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনায় ব্রতী হন। তবে যেটা লক্ষণীয় ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার অভিঘাত সমকালীন তরুণদের রচনায় তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। পাকিস্তানি, সেন্সরশিপ হয়তো প্রকাশের সুযোগ সঙ্কুচিত করেছিল; কিন্তু অন্তরের বেদনা ও ক্ষোভ প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়েও তো শিল্পে মূর্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বরং পঞ্চাশের লেখক-সাংবাদিকরা ছিলেন অনেক এগিয়ে।
দাঙ্গা ব্যাপক মানুষের মনে কী গভীর ছায়াপাত ফেলে, বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মানসে, সেটা বোঝার মতো সংবেদনশীলতার অভাব এখানে লক্ষণীয়। এটা বাংলাদেশের সুবিধাপ্রাপ্ত মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনচেতনার একটি ঘাটতির দিক, যা আজও মোচন করা সম্ভব হয়নি, বরং আরও গভীর হয়েছে কিনা সেটাই জিজ্ঞাসা। স্যাড জেনারেশনের বুলেটিনে প্রশান্ত ঘোষাল লিখেছিলেন নিবন্ধ, ইংরেজিতে, ‘চম্পাবতী : এ ক্যাথারসিস অব পেন্ট আপ প্যাশনস’। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে মিলে তিনি ছিলেন নবীনদের জায়মান সাহিত্যান্দোলনের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন : ‘জগন্নাথ হলের ১৫০ নম্বর রুমে প্রশান্ত থাকতো। ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পথ ধরেই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে ষাটের তরুণ লেখকেরা প্রথমবারের মতো একত্র হয় ওর রুমে। ওখানেই জন্ম নেয় আন্দোলনের অস্ফুট প্রাথমিক রূপরেখা।… মুন্সিগঞ্জে প্রশান্ত আর আমি যখন আমাদের অবিশ্রান্ত কবিতা-আবৃত্তি আর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে দিন কাটাচ্ছি তখন আমরা ভাবতেও পারিনি, ষাটের দশকের তরুণ লেখকদের যে-বিশাল সংঘ অচিরেই দানা বাঁধতে যাচ্ছে, আমরা আমাদের অজান্তে, আমাদের আত্মিক নৈকট্যের ভেতর দিয়ে আসলে সেই সংঘের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছি।’
কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে প্রশান্ত সেই সাহিত্যের কাফেলা থেকে ছিটকে পড়েন। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এমন নিভৃতে চলে যান যে আন্দোলনের নিকটসঙ্গীরাও তাঁর মনের বেদনা বুঝতে ব্যর্থ হন, সংবেদনশীলতা নিয়ে বিবেচনায় অসমর্থ হন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এই নিভৃতচারিতার একটি রোমান্টিক ভাষ্য প্রদান করে লিখেছেন :
‘কিন্তু এর পর হঠাৎ করেই সেই ভূমিকা থেকে ওর নিঃশব্দ প্রস্থান। এতদিনের পরিচিত বন্ধুবান্ধব, মধ্যরাতের রাজপথ, সাহিত্যের উত্তেজনার ঝাঁঝালো জগৎ―সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায় প্রশান্ত। সাংসারিকতার আবর্তে প্রায় মৌমাছির মতো প্রোথিত হয়ে যায়। কোনও অভিমান বা মতান্তর থেকে নয়, একা-একা প্রায় অকারণেই বিদায় নিয়ে যায় ও। এই বিদায় যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভ্রƒক্ষেপহীন। এরপর আমাদের পনেরো বছরের উত্তাল হল্লার জগতে ভুল করে একবারের জন্যও উঁকি দিতে আসেনি প্রশান্ত। গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর মুন্সিগঞ্জ থেকে নিয়মিত যাতায়াত করে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে সাংবাদিকতা করেছে; কিন্তু ভুলেও পুরনো কারও ব্যাপারে কোনও খোঁজ খবর করেনি। যেন এই উদ্দাম জগতের কেউ ছিল না ও কোনওদিন। কারও প্রতি প্রতিজ্ঞা বা দায় থাকারও কোনও কথা ছিল না। এমন কি বছর-কয়েক আগে যখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ষাটের দশকের সাহিত্য-সৈনিকদের পুনর্মিলনীর উদ্যোগ নেয়া হলো তখন সেই অন্তরঙ্গ মধুর স্মৃতিবাহী সমাবেশে যে-একমাত্র মানুষটি যোগদানের সুযোগকে অবলীলায় তাচ্ছিল্য করেছে সে তো এই প্রশান্ত ঘোষালই।’
কিন্তু প্রশান্ত ঘোষালের সরব উপস্থিতি ও অভিমানী প্রস্থানের মাঝখানে যে রয়েছে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বেদনা, অপমান ও দুঃখবোধ তার পরিমাপ কে করবে! সাথীদের অসংবেদনশীলতাও কি তাঁর এই দুঃখবহ প্রস্থানের পেছনে কোনও অবদান রেখেছে ? কে জানে, কেই-বা তা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারবে, তবে স্যাড জেনারেশনের এই কবি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রবংশের বিষণ্নতম সদস্য হয়ে আছেন, একাকী বয়ে চলেছেন গোটা জাতির অসদাচরণের বেদনার ভার।
৫.
১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর ভারত প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে মুসলিম রাজ্য পাকিস্তান কোনওভাবেই গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রশ্নে ফয়সালা করতে পারে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সামন্ত ভূস্বামী ও ভারত থেকে আগত মোহাজের পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে, আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীতেও তাদের ছিল গরিষ্ঠতা। ফলে শুরু থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল বিশেষ এক গোষ্ঠীর হাতে এবং এই নিয়ন্ত্রণের সুবিধা ভোগ করে নব্যধনপতি শ্রেণির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে, যারা ছিল প্রায় সর্বাংশে পশ্চিম পাকিস্তানি। জনসংখ্যা বিচারে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বাঙালিদের ছিল সংখ্যাধিক্য, ফলে যে কোনও রকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাঙালিরা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে। এই বাস্তবতা এড়াতে নানা ধরনের উদ্ভট ফরমুলা দাঁড় করাবার চেষ্টা চালাচ্ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। দেশভাগের পরপর পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় তার জের ধরে উভয় দেশের সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে জনবিনিময় নামে বিশ শতকের এক চরম নিষ্ঠুর জন-উচ্ছেদ নীতি, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের ট্রাকে-বাসে-ট্রেনে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভারতে আর পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের পাকিস্তানে। এই বেদনাময় বাস্তবতার রূপকার সাদাত হাসান মান্টো হৃদয়চেরা অসাধারণ কতক ছোটগল্প লিখেছেন; অপার বেদনায় খাক হয়ে পানাসক্তিতে খুঁজেছেন শান্তি, এভাবে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যান অচিরেই।

দেশভাগের সময় বাংলা তুলনামূলকভাবে ছিল শান্ত। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতায় অবস্থান করছিলেন মহাত্মা গান্ধী, তিনি ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে দিনটিতে পালন করেন অনশন। এর সঙ্গে আরও নানা কারণ মিলে বাংলায় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার রাশ টেনে ধরা সম্ভব হয়; কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক বিভাজন একই সমাজের মানুষের মধ্যে স্থায়ী এক বিভাজন রেখা টানতে উদ্যত হয়। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আদর্শগতভাবেই হিন্দু-মুসলমানের এই বিভাজনের বিরোধী এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের বিপরীতে ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতিসত্তার অখণ্ডতা ও সম্প্রীতির পরিচয় তুলে ধরে। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতিসত্তার জাগরণের ছিল বিশেষ তাৎপর্য। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ভয়াবহতা পূর্ববঙ্গের এই সম্প্রীতির আবহের ওপর বিরাট আঘাত হানে। বিপুলসংখ্যক অমুসলিমের দেশত্যাগ সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দেশের জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভাজন ও হিংসা এবং এর বিপরীতে জাতিচেতনার অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির বাণী―এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল পাকিস্তান।
১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক ঐতিহাসিক আপোসরফা করে পাকিস্তানের জন্য শাসনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ উন্মুক্ত করেন। এই আপসের মূল ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় সংসদ গঠনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জনসংখ্যার নিরিখে নয়, সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে আসন বণ্টন, তথা প্যারিটির নীতি গ্রহণ। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করে ডিসপ্যারিটির ভিত্তিতে যে ফয়সালা তাকে প্যারিটি নীতি আখ্যায়িত করার মধ্যে আজব দেশে এলিসের উপাদান রয়েছে। এই নীতি প্রবর্তনের স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক সংসদ ও প্রদেশ ব্যবস্থা বাতিল করে গঠন করা হয় ‘এক ইউনিট’। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী এক ঢিলে অনেক পাখি বধ করলেন এবং এভাবে পাকিস্তানে পাঞ্জাবি চক্রের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করে তুলতে চাইলেন। এই আপসের পথে এগিয়েও সোহরাওয়ার্দী শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হলেও সেই সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন আর দেশে অনুষ্ঠিত হলো না, ১৯৫৮ সালে নেমে এল সামরিক শাসন।
মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এবার আইয়ুব খান অগ্রসর হন মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। এই অপচেষ্টার পথের বাধা অপসারণের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে গ্রেফতার করা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে, যা ছিল পাকিস্তানে কোনওরকম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে সমরশাসকদের ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতামদমত্ততার প্রকাশ। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর করাচির বাসভবন থেকে ভোররাতে গ্রেফতার করে আই.জির গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। সরকারিভাবে বলা হয়, তিনি পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে পাকিস্তানবিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর কন্যা আখতার সোলায়মান ও বড় ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন। শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলে শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধজন, বিষ্ণু দে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের বন্ধু, ভারতের এককালের অগ্রণী শিল্পসমালোচক, যামিনী রায় বিশেষজ্ঞ। অবিভক্ত বাংলার পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী, সফল ব্যারিস্টার, গণতন্ত্রপ্রাণ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের জন্য বড় সম্পদ বিবেচিত হতে পারতেন। পত্রিকার খবরে জানা যায়, কারাগারে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত রেকর্ড প্লেয়ার ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কয়েকটি রেকর্ড সঙ্গে নিয়ে যান। অক্ষম ভ্রাতা নীরবে দেখলেন তাঁর রাজনীতিবিদ ভাইয়ের অবমাননা আর যিনি ছিলেন অবিভক্ত ভারতের সবচেয়ে সম্মানীয় বাঙালি মুসলিম তিনি দেখলেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রক্ষমতার বর্বর আস্ফালন। শিল্পরুচি ও বৈদগ্ধ্য, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার যে পাকিস্তানে অচল সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের ঘটনা সেই বাস্তবও মেলে ধরেছিল।
স্থূলবুদ্ধি সামরিক শাসনের জাঁতাকল থেকে দেশের মানুষের উদ্ধার পাওয়ার পথ যে প্রায় রুদ্ধ সেটা ষাটের দশক নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। কেবল ছাত্রসমাজের মধ্যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ মাঝে-মধ্যে উদগীরিত হয়ে প্রকাশ করছিল দেশের প্রাণ একেবারে মরে যায়নি। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার আঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠলো ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর, যুদ্ধকালে অন্ধ ভারত-বিরোধিতার যে তথাকথিত দেশপ্রেমিক জিগির তোলা হয় তা সকল নাগরিককে যেন জিম্মি করে তুলল। পাকিস্তানি যুদ্ধবাজদের তালে তাল মেলাতে হলো সবাইকে, না হলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নিগ্রহ বরণ করতে হয়। যুদ্ধ-উন্মাদনা শাসকগোষ্ঠীকে দেশপ্রেমের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজগুলো সম্পাদনে তারা অগ্রসর হয়। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করা হয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য যাঁরাই সামাজিক নেতৃত্বের দাবিদার তাঁদের স্থান হয় কয়েদখানায়, হিন্দু ব্যবসায়ী কিংবা ভূসম্পত্তির মালিকদের একেবারে মৌলিক মানবিক অধিকার অস্বীকার করে গৃহীত হয় ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’, সরকার তাদের সম্পদ অধিগ্রহণের একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণ করে। ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগের সকল পথ রুদ্ধ করা হয়, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ভারতীয় ছায়াছবি আমদানি অথবা প্রদর্শন, ভারতীয় বইপত্রের প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয়, দেশ বা অমৃতের মতো সাপ্তাহিকও ঢাকায় অপ্রাপ্য হয়ে ওঠে, বইপত্রের তো কোনও প্রশ্নই নেই। এক বিকৃত বিকলাঙ্গ অনুদার ও কূপমণ্ডূক সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সর্বপ্লাবী হয়ে ওঠে।
এই পটভূমিকায় গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন ৬-দফা দাবিনামা, এককেন্দ্রিক পীড়নমূলক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপরীতে বহুকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েমের দাবি, যেখানে জাতিসত্তার অধিকার পাবে নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি। এরপর দ্রুত দেশ এগোতে থাকে মুখোমুখি মোকাবিলার পরিস্থিতির দিকে। সরকার যতই তার আঁটুনি দৃঢ় করতে চায় ততই ফস্কা হয়ে পড়ে গেড়ো। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার শুরু করেও আইয়ুব পার পেলেন না, গণ-আন্দোলনের তোড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে হয় তাঁকে। মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিব জনগণ দ্বারা বরিত হন ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে, তাঁর নেতৃত্বে এককাট্টা হয়ে দাঁড়ায় গোটা দেশের মানুষ। পূর্ববঙ্গ প্রস্তুত হয়ে ওঠে যে কোনও মূল্যে তার অধিকার আদায়ের দৃঢ়পণ সংগ্রামে, যে সংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেয় ১৯৭১ সালে এসে এবং অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে উদ্ভব হয় গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।
৬.
ষাটের দশকের এই যে রাজনৈতিক পালাবদল, তার সমান্তরালে চলছিল সাহিত্য ও শিল্পজগতে পরিবর্তনের দোলা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যের একদিকে ছিল শিল্প-সাহিত্য চর্চার পরিধির বিস্তার, অপরদিকে ছিল আন্তর্জাতিক ভাবজগতের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন। আইয়ুবের পীড়নমূলক শাসনের পাশাপাশি বিদেশি সাহায্যধন্য পাকিস্তানে চলছিল নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এর সুফল ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী ভোগ করলেও তা চুঁইয়ে এসে অন্যদের পাতেও কিছুটা প্রসাদ ঢালছিল। এছাড়া মৌলিক গণতন্ত্রীদের জন্য চালু হয়েছিল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, যেটা গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিৎ অর্থনৈতিক সচলতা ঘটিয়েছিল। পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্তের এক ধরনের বিকাশ ঘটছিল এবং এই মধ্যবিত্তের নবীন সন্তানেরা ধর্মপরিচয়ের বৃত্তে নিজেদের সীমিত রাখতে চাইছিল না, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আকাশের দিকেও হাত বাড়িয়েছিল। বাড়ছিল শিক্ষার সুযোগ, সেই সঙ্গে প্রসারিত হচ্ছিল শিল্প-সাহিত্যচর্চার গণ্ডি। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতিক জাগরণের মন্ত্র বয়ে আনত, চলত একুশে ঘিরে সংকলন প্রকাশের আয়োজন। ছাত্র-তরুণ, পাড়া-মহল্লার যুবক-যুবা কতজনই না কতভাবে যুক্ত হতো লেখা ও প্রকাশের কাজে। এই প্রক্রিয়া আবার পাঠকমহলকেও প্রসারিত করছিল, বাড়ছিল সাহিত্য পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক। জীবনানন্দ দাশকে নতুন করে ফিরে পেল বাংলার কবিতাপ্রেমীরা, সৈয়দ আলী আহসানের আমার পূর্ববাংলা দেশবন্দনার সমার্থক হয়ে ওঠে, এমন কি প্রায় অচেনা কবি ওমর আলীও পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেন ‘এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি’ কাব্যগ্রন্থের সুবাদে। দেশাত্মার সন্ধান কবিদের জন্য এক বিশেষ আরাধ্য হয়ে উঠতে থাকে, আধুনিকতা ও নাগরিকবোধ যে বিচ্ছিন্নতার উপাদান বহন করত সেটা নাকচ করে ষাটের ঘটনাধারা দেশের দাবি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, শামসুর রাহমান মিছিলে শরিক হওয়ার বিস্ময়াবিষ্ট ভাব নিয়ে লিখেন, ‘আমরা এখানে কেন/ এখানে কী কাজ আমাদের,’ আল মাহমুদ লেখেন অনুপম সনেটমালা, শহীদ কাদরী জয়গান গান হরতালের। এভাবেই হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হয় যুগের দাবি, পাল্টে দেয় কবিকণ্ঠ।
বিশ্বজুড়ে তখন তারুণ্যের পদপাত প্রবল হয়ে উঠছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল পশ্চিম দুনিয়ায় গণ-আন্দোলনের নতুন এক ধারা তৈরি করছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল চে গুয়েভারার বিপ্লব প্রয়াস, বিটনিকদের জ্বলজ্বলে বিভিন্ন সেøাগান, মেক লাভ নট ওয়ার, নবীন গায়ক-গায়িকার দল হ্যামিলনের বংশীবাদক হয়ে তরুণদের মাতিয়ে তুলছিলেন। নিউ ইয়র্কে ছাত্ররা দখল করে নিলো কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড ডিবেটিং ক্লাবে তারিক আলী শাপান্ত করছেন পুঁজিবাদের, আমেরিকার কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যুদ্ধ-বিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হলো ছাত্র―এসব ঘটনা আলোড়ন তুলছিল দুনিয়া জুড়ে। ‘১৯৬৮ সালে প্যারিসের যুব বিদ্রোহ তো দেখিয়ে দিলো নতুন এক পৃথিবীর জাগরণ আর কোনও স্বপ্নকল্পনা নয়। পাকিস্তান চেয়েছিল ভারত বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গবাসীর কোনও রকম সাংস্কৃতিক যোগ থাকবে না, অথচ সেই বাঙালি হাত বাড়িয়েছিল বিশ্বের দিকে। সামান্য সুযোগ অবলম্বন করে কিংবা সুযোগ তৈরি করে শুষে নিচ্ছিল দুনিয়ার যেখানে যা কিছু আছে, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। পূর্ববঙ্গের সেই মফসসলী ভাব আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, নতুন এক কসমোপলিটানিজম সবাইকে স্পর্শ করেছিল গভীরভাবে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক এই আবহের যোগ নিছক কোনও তাত্ত্বিক ব্যাপার ছিল না, এ-ছিল আত্মিক যোগসূত্র এবং টলে উঠছিল কায়েমি স্বার্থবাদী চেনা পৃথিবীটা এবং স্বপ্নের এক বিশ্ব গড়ে নিতে শুরু হয়েছিল ভুবনব্যাপী বিস্তৃত এক জয়যাত্রা, যেখানে নেই রাষ্ট্রের ফারাক, নেই জাতি থেকে জাতিতে, মানুষ থেকে মানুষে পার্থক্য, সবাই মিলে যেন গাইছিল নতুন এক পৃথিবীর গান।
সেই আশ্চর্য দশক একবারই এসেছিল আমাদের জীবনে এবং ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিভাজন পীড়ন ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে জর্জরিত পাকিস্তানি দর্শন। ষাটের দশকের উদার মানবিক সম্প্রীতির বিশ্বচেতনা সকল বদ্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার অবসান রচনা করেছিল। আর তাই তো সত্তরের গোড়ায় সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশের অমন উজ্জ্বল অভ্যুদয়।