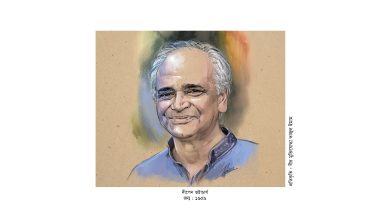মফিদুল হকের সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা : লালনকে কে বাঁচাবে : মাহবুবুল হক
মফিদুল হকের সাহিত্যকর্ম : আলোচনা
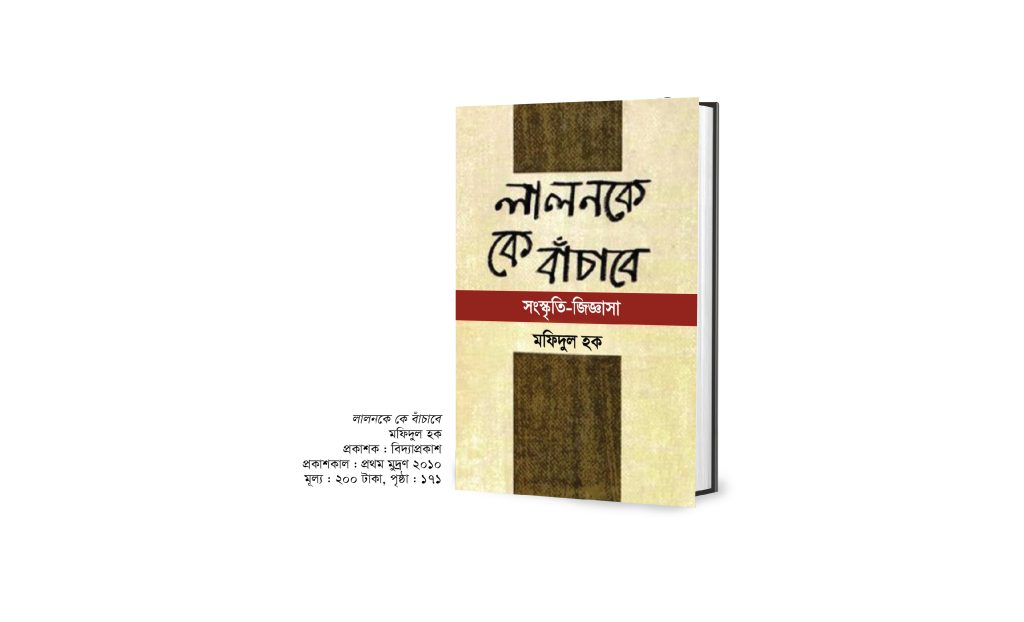
মফিদুল হকের লালনকে কে বাঁচাবে সংস্কৃতি-ভাবনাবিষয়ক বই। এতে সংকলিত হয়েছে সংস্কৃতিবিষয়ক ২৩টি প্রবন্ধ। লেখক জানিয়েছেন অধিকাংশ প্রবন্ধই রচিত হয়েছে উনিশ শো নব্বইয়ের দশকে। প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র হলেও সেগুলির মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। এসব প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংস্কৃৃতির একটা চিত্র ও একটা পথরেখা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।
গ্রন্থের শুরুতেই সন্নিবেশিত হয়েছে লোকসংস্কৃতিবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ : ‘লালনকে কে বাঁচাবে’, ‘কবি ও কবিয়াল’ এবং ‘ফোকলোর ও মুক্তিযুদ্ধ’।
প্রথম প্রবন্ধটিই হচ্ছে গ্রন্থের নামপ্রবন্ধ ‘লালনকে কে বাঁচাবে’। এই প্রবন্ধে মফিদুল হক বাউল সাধনাকে ঘিরে একপেশে মন্তব্য ও অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আহমদ শরীফ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ লেখক-বুদ্ধিজীবী অভিজাত নাগরিক অবস্থান থেকে বাউলদের দর্শন, সাধনা ও সংগীত সম্পর্কে যে অনভিপ্রেত মন্তব্য করেছেন প্রবন্ধটিতে তার অসংকোচ সমালোচনা করতে পিছপা হননি তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেছেন বাউলের অসাম্প্রদায়িক সাধনাকে ন্যাক্কারজনকভাবে ইসলামিকরণ তথা সাম্প্রদায়িকীকরণের দুঃখজনক তথ্য। এর সূচনা সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বশংবদ তল্পিবাহক ও অর্ধশিক্ষিত গভর্নর মোনেম খানের হাতে। তিনিই পদক্ষেপ নেন লালন সাঁইকে লালন শাহ, লালনের আখড়াকে লালনের মাজার হিসেবে ইসলামিকরণের। একই সঙ্গে লালনের সমাধিপ্রাঙ্গণে একতলা ঘর করে দিয়ে সেখানে জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্ব জারি করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে লোকসাহিত্য কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে করা হয় লালন একাডেমি। এভাবে রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত থাবা বিস্তার ঘটে লালনের আখড়া ও সমাধিতে। আর তারই ধারাবাহিকতায় এখন চলছে লালন মেলার নামে অর্থের বিনিময়ে স্টল বরাদ্দ। লেখক এই অবস্থার অবসান কামনা করেন। তিনি চান বাউলসাধনা যেন মাজারব্যবসা থেকে মুক্ত থাকে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ঘেরাটোপে যেন হারিয়ে না যায় বাউলদের সহজিয়া সাধনা।
‘কবি ও কবিয়াল’ প্রবন্ধে মফিদুল হক তাঁর লোকসংস্কৃতি-সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক বৈশ্বিক পটভূমিতে নাগরিক শিক্ষিত কবির কাব্যচর্চার তুলনায় গ্রাম্য অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের কাব্যচর্চাকে উপেক্ষা করার মনোভাবকে সমালোচনা করেছেন। কবিগান যে বাংলার লোকায়ত জীবনধারা থেকে উৎসারিত প্রাণশক্তিময় সংগীতধারা, সে বিষয়ে গভীর প্রত্যয় রয়েছে তাঁর। তাই কবিগানকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখার পেছনে তিনি এক ধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, এ দেশে জমিদার শ্রেণির আনুকূল্যে ধ্রুপদী সংগীতের বিকাশ ঘটলেও কবিগানের প্রসারের পেছনে ছিল সাধারণ জনগণের ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে কবিগানের বিবর্তন ও ভূমিকা সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কবিগানে একসময় অশ্লীলতার প্রভাব থাকলেও উনিশ শো চল্লিশের দশকে কবিগান খিস্তি-খেউড়-তরজার অশ্লীলতা পরিত্যাগ করে প্রগতিচেতনার নানা বিষয়কে ধারণ ও প্রচার করেছে। যোগসূত্র ঘটিয়েছে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার। তিনি আরও লক্ষ করেছেন, বাম রাজনীতির ভাটার টানে কবিগানের ঘরানা লুপ্তপ্রায় হতে চলেছে। এই সংকট মোকাবিলায় পথ অনুসন্ধান করা তিনি জরুরি বলে মনে করেন। কবি ও কবিয়াল যে সম আসন দাবি করতে পারেন সেটা অনুধাবন করে কবিগানের বিকাশের জন্য পথ তৈরির কাজে এগিয়ে আসার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই রচনায়।
‘ফোকলোর ও মুক্তিযুদ্ধ’ প্রবন্ধে লেখক ফোকলোর চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে ফোকলোর কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও তার চেতনাকে ধারণ করেছে তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। উপস্থাপন করেছেন কিছু উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত চারটি পথুয়া কবিতার পরিচয় তুলে ধরে এই অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, ফোকলোরের জগতে অনুসন্ধান চালালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে। তিনি মনে করেন, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা হলে তার পরিচয় লাভের জন্যে ফোকলোরের শরণাপন্ন হওয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
বাঙালির বিনোদনমূলক লোকসংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যাত্রা। এ গ্রন্থে যাত্রা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এগুলি হলো : ‘বাংলাদেশে যাত্রাচর্চা : পটভূমি ও পথপরিক্রমা’, ‘যাত্রাদল : গঠনকাঠামো ও শিল্পশক্তি’, ‘মুক্তিযুদ্ধে যাত্রাশিল্পী’। ‘বাংলাদেশে যাত্রাচর্চা : পটভূমি ও পথপরিক্রমা’ প্রবন্ধে যাত্রার উৎসমূল, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবের প্রেক্ষাপটে সামাজিক অবস্থান ও শিল্পধারায় যাত্রা ও যাত্রাশিল্পীদের লক্ষণীয় পরিবর্তন, নতুন সমাজবাস্তবতায় দেশজ নাট্যরীতিতে যাত্রার অবস্থা ও ভূমিকা, তার দুর্বলতা ও শক্তি, সংকট ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলায় যাত্রাশিল্পের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা আলোচনা সূত্রে লেখক শ্রী চৈতন্যদেবের সময়ে নাম সংকীর্তন ও কৃষ্ণ আরাধনার সূত্রে নাট্যগীতি হিসেবে যাত্রার উদ্ভব, আঠারো শতকে কৃষ্ণযাত্রা এবং রামযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে যাত্রায় পৌরাণিক উপাদানের প্রাধান্য, উনিশ শতকের বিশের দশকে ধর্মীয় অনুষঙ্গবিহীন মানবিক প্রেম-উপাখ্যান ভিত্তিক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অভিনয়, নতুন গড়ে ওঠা নগর কেন্দ্র বিত্তবানদের গৃহাঙ্গণ-কেন্দ্রিক যাত্রাশিল্পের প্রসার, উনিশ শতকের মধ্যভাগে যাত্রায় ধর্মাশ্রয়িতার চেয়ে লোকাশ্রয়িতার প্রাধান্য, বিশ শতকে শহরাঞ্চল ছেড়ে গ্রামবাংলায় যাত্রার বিস্তার, লোকরঞ্জক ভূমিকা পালনের সূত্রে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়সহ নানা বিষয়-বৈচিত্র্যকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ, পোশাকে ও বাদ্যযন্ত্রে নতুনত্বের সঞ্চার ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও সামাজিক স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও লোকজীবনের সঙ্গে গভীর সংশ্লিষ্টতা যাত্রাশিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের অভিঘাতে যাত্রাশিল্পী ও পালাকাররা দেশত্যাগ করলেও পূর্ব বাংলায় যাত্রাশিল্প বড় রকমের বিপর্যয়ে পড়েনি। পাকিস্তানি আমলে অনেকগুলি জেলায় সংগঠিত যাত্রাদল গড়ে ওঠে। ষাটের দশক থেকে যাত্রাদলে মুসলিম শিল্পীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যাত্রাশিল্পের নতুন বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। একাত্তর সালে বাংলাদেশে যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। সত্তরের দশকের মধ্যভাগে সে সংখ্যা দাঁড়ায় একশো। ১৯৮৭-৮৮ সালে দুইশো ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এর পর এ দেশে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং প্রশাসনের বৈরী মনোভাবের কারণে দ্রুত যাত্রাদলের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯২ সালে সরকার ফরমান জারি করে যাত্রাভিনয়ের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। এর ফলে যাত্রাশিল্পের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা চরম সংকটের মুখে পড়ে। এই অবস্থায় যাত্রার মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ থেকে লেখক সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
শহর থেকে নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও আড়াই শো বছর ধরে যাত্রাশিল্প যে আমাদের সমাজজীবনে সজীব ও সক্রিয় সেই দিকটি বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে ‘যাত্রাদল : গঠনকাঠামো ও শিল্পশক্তি’ প্রবন্ধে। লেখক মনে করেন, নানা বাধাবিঘ্ন মোকাবিলা করে, যন্ত্রযুগের সামাজিক পরিবর্তন ও দেশবিভাগের বিপর্যয়কে সামলে নিয়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও যে যাত্রাশিল্প তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তার বড় কারণ লোকজীবনের সঙ্গে তার যোগ এবং যাত্রাশিল্পের পেছনে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। গ্রামীণ সমাজে যাত্রাশিল্প পেয়েছে উৎসবের মর্যাদা। তা শিল্প হিসেবে অর্জন করেছে ব্যাপক লোকপ্রিয়তা। এর মাধ্যমেই যাত্রাশিল্প পেয়েছে তার প্রাণশক্তি।
লেখক বাংলার যাত্রাশিল্পকে ইউরোপের ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের সমগোত্রীয় করে দেখেছেন। প্রসঙ্গত তিনি যাত্রাদলে প্রযোজক বা অধিকারীর ভূমিকা, গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে এর কার্যক্রম, লোকসমাজে শিল্পরস দিয়ে মাতিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যাত্রার ক্ষমতা, যাত্রাদলে নারী-পুরুষ শিল্পীদের নিরন্তর যুক্ত হওয়াকে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলে মনে করেন। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে সব বাধা অপসারণ এবং প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি।
লেখকের যাত্রাশিল্প বিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে ‘মুক্তিযুদ্ধে যাত্রাশিল্পী’। এই প্রবন্ধে লেখক মুক্তিযুদ্ধে যাত্রাশিল্পীদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। খ্যাতনামা যাত্রানট অমলেন্দু বিশ্বাস আলোড়ন তুলেছিলেন ‘গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা’ শীর্ষক পালা মঞ্চস্থ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অন্যান্য শিল্পশাখার মতো যাত্রাশিল্পীরাও লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন। অনেক যাত্রাশিল্পী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে প্রবন্ধে। যেসব যাত্রাশিল্পী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের কথাও স্মরণ করা হয়েছে।
এ গ্রন্থে সংকলিত তিনটি প্রবন্ধের বিষয় নাটক ও নাট্যাভিনয়। ‘বাংলা মঞ্চনাটক : যাত্রাকালের ট্রাজেডি’, ‘নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যসংস্কৃতি’ ও ‘নীরবতার শিল্পরূপ : মাইম’।
‘বাংলা মঞ্চনাটক : যাত্রাকালের ট্রাজেডি’ প্রবন্ধে বাংলা মঞ্চনাটকের দুই শো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই দীর্ঘ কালপর্বের নাট্যচর্চার মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো মফিদুল হক তুলে ধরেছেন সংক্ষিপ্ত রূপরেখায়। সেই সূত্রে বাংলা নাট্যচর্চার ঐতিহাসিক পথযাত্রা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, ১৭৯৫ সালে রুশ ভাগ্যান্বেষী গেরাসিম লিয়েভেদিয়েফ যে অনূদিত বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন তাতে ছিল বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। সে যুগে যখন সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে নেটিভ বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল না, সে সময়ে বাংলা অনুবাদে নাটক মঞ্চায়ন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, বাংলা রীতিতে মঞ্চসজ্জা ও বাংলা গানের সুর যোজনার ভেতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এরপর ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজদের ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল অনুকরণপ্রিয় বাঙালি নব্য বাবু গোষ্ঠী। এর বিপরীতে শিক্ষিত উদারভাবাপন্ন আর একটি গোষ্ঠী ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছিল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও আধুনিক শিক্ষায় সমুন্নত হয়ে। এই উভয় গোষ্ঠী প্রথম দিকে ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বেঙ্গলি থিয়েটারের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু থিয়েটার। এর ফলে বাঙালি জাতিসত্তার জায়গায় প্রাধান্য পায় ধর্মসত্তা। বাঙালির নাট্যচর্চায় ইংরেজি রীতির প্রাধান্যের মধ্যে ১৮৩৫-এ বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় ছিল ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নব্যশিক্ষিত বাঙালির চোখে তা অসংস্কৃত আচার ও অশ্লীল ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হলেও এর ভেতর দিয়ে উপনিবেশবিরোধী মানসিকতার কিছুটা প্রকাশ ঘটে। বাংলা নাট্যচর্চা বেগবান হয়ে ওঠে ১৮৫৭ সালে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল সর্বস্ব অভিনয়ের মাধ্যমে। শুরু হয় গৃহ নাট্যশালাকেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়। এরপর বাংলা নাট্যাভিনয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া থিয়েটারকে কেন্দ্র করে এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্য অবদানে। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নীলদর্পণ নাটক ও বেশ কিছু প্রহসনের অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কারের প্রত্যাশা প্রধান হয়ে ওঠে। তাতে উপনিবেশবিরোধী চেতনা ও জাতীয় মুক্তির আকুতির স্ফুরণ ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে নাটকের ওপর ব্রিটিশ রাজের খড়গ নেমে এলে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে নাট্যচর্চা শুরু হয়। প্রতিবাদী নাটক রচনার পথ বন্ধ হয়ে গেলে রুদ্ধ মনের আকুতি অবলম্বন খুঁজে নেয় রূপক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটকে। সেই সঙ্গে অবলম্বন হয় বাণিজ্যিক নাটক। নাট্যকার এই প্রবন্ধে এভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, বাংলাদেশে বাঙালির স্বাভাবিক নাট্যচর্চার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল উপনিবেশবাদ।
‘নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যসংস্কৃতি’ প্রবন্ধে বাংলা নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনার একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে তথ্যঋদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন ১৮৫০-এর দশকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক প্রকাশনার ভেতর দিয়ে বাংলা নাট্যগ্রন্থের প্রকাশনা শুরু হলেও তার অনেক আগে থেকে জনপ্রিয় নাট্যধারা প্রকাশনার জগতে জায়গা করে নিয়েছিল। এই জনপ্রিয় নাট্যধারার উৎস ছিল লোকজীবন। বটতলার প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত এই প্রকাশনা ছিল নব্যশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবিত এলিট গোষ্ঠীর বিশেষত হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে। বটতলার প্রকাশনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে ছিল হিন্দু-মুসলিম অংশীদারিত্ব। প্রকাশনার মান উন্নত না হলেও এই ধারার নাটকের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপক সাধারণের মধ্যে। সেখান থেকে প্রকাশিত নাটক ছিল অনেক রংদার এবং তাতে ছিল আদিরসের প্রাবল্য। মঞ্চায়ন এগুলির লক্ষ্য ছিল না, বরং লক্ষ্য ছিল পাঠক পরিতৃপ্তি, তথা জনচিত্ত জয়ের বাসনা। এই প্রবন্ধে এ ধরনের অনেক নাটকের উল্লেখ করে এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
‘নীরবতার শিল্পরূপ : মাইম’ প্রবন্ধে মূকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। লেখক মনে করেন মাইম নিছক শব্দহীন নাটক নয়, শব্দের অভাবকে কেবল শরীরী ব্যঞ্জনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নয়, তা হচ্ছে শরীরের ভাষা, শরীরের সৌন্দর্য, শরীরের গান।
লালনকে কে বাঁচাবে গ্রন্থে চলচ্চিত্র নিয়ে আছে তিনটি প্রবন্ধ। এগুলি হলো : ‘চলচ্চিত্রের শতবর্ষ : প্রসঙ্গ হীরালাল সেন’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র’, ‘আগন্তুক’ : পরিচালকের জীবনদর্শন’।
‘চলচ্চিত্রের শতবর্ষ : প্রসঙ্গ হীরালাল সেন’ প্রবন্ধে বাংলা তথা উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ হীরালাল সেনের চলচ্চিত্র-জীবন ও নাট্য-সংসর্গ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। লেখকের ধারণা এ দেশে ঔপনিবেশিক মানসিকতা তাঁর প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি করেছিল, যা প্রকারান্তরে তাঁকে বিস্মৃত চরিত্রে পরিণত করেছে। সে দায় মোচনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এই প্রবন্ধে তাঁদের কথা স্মরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে হীরালাল সেনের জীবন ও কর্মের ওপর।
রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টতার নানা দিক নিয়ে তথ্যবহুল প্রবন্ধ হচ্ছে ‘রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র’। প্রবন্ধটিতে নির্বাক ও সবাক যুগের চলচ্চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনার যোগসূত্র অনুসন্ধান করেছেন লেখক। নির্বাক যুগে আমরা পাই মস্কোর চলচ্চিত্র কর্মীদের সঙ্গে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকের কথা, সেখানকার চলচ্চিত্র দর্শনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বতীর্থ কবিতার শরীরে চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রনাথ রচিত বিচারক, দালিয়া ও নৌকাডুবি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির কথা। সবাক যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর কথাও এ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। সেগুলি হচ্ছে : নটীর পূজা, চিরকুমার সভা, গোরা, চোখের বালি, শোধবোধ, শেষ রক্ষা, দৃষ্টিদান, যোগাযোগ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ক্ষুধিত পাষাণ, তিনকন্যা ও চারুলতা।
‘আগন্তুক’ : পরিচালকের জীবনদর্শন’ প্রবন্ধে মফিদুল হক সত্যজিৎ রায়ের শেষ চলচ্চিত্র আগন্তুক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এই চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় নির্মমভাবে উন্মোচন করেছেন সভ্যতার আড়ম্বর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও আকাশচুম্বী দালানের দম্ভ ও জীবনের অজস্র উপকরণের মধ্যে থাকা মানুষের মমতাহীন যান্ত্রিকতা, শূন্যতাবোধ ও হৃদয়হীনতা।
লালনকে কে বাঁচাবে গ্রন্থের প্রথমে লোকসংস্কৃতি নিয়ে যে আলোচনা আছে তারই সম্প্রসারণ লক্ষ করা যাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর আলোচনার মধ্যে। এ গ্রন্থে সংস্কৃতির কয়েকটি দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন মফিদুল হক। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হচ্ছে : ‘বটবৃক্ষের সংস্কৃতি : সংস্কৃতির বটবৃক্ষ’, ‘সাংস্কৃতিক সত্তা ও আমাদের ভবিষ্যৎ’ ও ‘সংস্কৃতির রক্তস্নাত অভিযাত্রা’।
‘বটবৃক্ষের সংস্কৃতি : সংস্কৃতির বটবৃক্ষ’ প্রবন্ধে মফিদুল হক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মিতা ও সুরসংগতির আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টার দিকটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তিনি বাংলাদেশে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন, বাংলা একাডেমি কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে ছায়ানটের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বায়নের যুগে ভোগবাদী সংস্কৃতির দাপটের মুখে বটবৃক্ষের সংস্কৃতিকে রক্ষা ও লালন করে সংস্কৃতির বটবৃক্ষের বিকাশ ঘটাতে হবে।
‘সাংস্কৃতিক সত্তা ও আমাদের ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তার মূলগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ নির্দেশ করেছেন লেখক। স্পষ্ট করে বলেছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার বিকাশের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তার বিরোধী শক্তি এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছে বারবার। জাতিসত্তার ওপর বারবার পীড়নমূলক আঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশ উদার অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী রাষ্ট্র গঠনের পথ থেকে পিছিয়ে যায়নি। নবতর শক্তিতে মোকাবিলা করেছে হিংসাত্মক মৌলবাদের উত্থানকে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বারবার সশস্ত্র হামলা ও আঘাত সত্ত্বেও নিরুদ্যম হয়নি সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা। অন্যদিকে বিশ্বায়নের ডামাডোলে আরোপিত বিনোদনের সংস্কৃতির প্রবল বিস্তারকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতিকে। লেখক জানেন, সংস্কৃতির শক্তিতেই বাংলাদেশের জন্ম। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, সংস্কৃতির শক্তিতেই বাঙালি জাতিসত্তা অটল পায়ে আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে যাবে।
‘সংস্কৃতির রক্তস্নাত অভিযাত্রা’ প্রবন্ধে মফিদুল হক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক বাতাবরণের মধ্যে পূর্ববাংলায় ষাটের দশকে যে সাংস্কৃতিক লড়াই শুরু হয়েছিল তা ধর্মভাবাপন্ন পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক জোশকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। সেই জোশকে বাঁচাতে গিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী হাতে তুলে নেয় মারণাস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতির ওপর। সামিল হয় বুদ্ধিজীবী হত্যায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক শক্তি জয়লাভ করে। লেখক বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে দেখিয়েছেন পাকিস্তানি আমলে ঢাকা ও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম ও কাগমারীতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন, প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন, ছায়ানট ও উদীচীর মতো সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা ইত্যাদির ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীন দেশেও বাঙালির সংস্কৃতিকে হত্যা করার জন্যে নিষ্ঠুর হামলা চলেছে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে। তা সত্ত্বেও বাঙালির সংস্কৃতি অটল। কারণ তার যোগ এ দেশের মাটির সঙ্গে।
এ গ্রন্থের শেষ দিকে ভাষা নিয়ে আছে চারটি প্রবন্ধ। এগুলি হচ্ছে : ‘ভাষা নিয়ে খিস্তি-খেউড়’, ‘ভাষা ও জাতিসত্তা’, ‘সম্প্রচারের ভাষা : সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট’ ও ‘বিশ্বায়ন ও ভাষার সংকট’।
‘ভাষা নিয়ে খিস্তি-খেউড়’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় মারাত্মক বুলি মিশ্রণের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক। অনেকের মতো তিনিও লক্ষ্য করছেন তথাকথিত আধুুনিক শিক্ষার নামে এক শ্রেণির লোকের মধ্যে দেখা দিয়েছে বাংলা ভাষাকে অচল মুদ্রার মতো পরিত্যাগের প্রবণতা। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজি শব্দ, কখনও কখনও হিন্দি। পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের নামে ভোগবাদী জীবন-দর্শনের দিকে সুপরিকল্পিতভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের। অন্যদিকে উগ্র ও খণ্ডিত জাতীয়তাবাদী একটি ক্ষুদ্র মহল বাংলা ভাষায় আঞ্চলিকতা ঢুকিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। এইসব প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার ওপর লেখক জোর দিয়েছেন এ প্রবন্ধে।
‘ভাষা ও জাতিসত্তা’ প্রবন্ধে লেখক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ভাষা জাতিসত্তা নির্মাণ করে। ভাষার মাধ্যমেই জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধন রচিত হয়। ভাষা নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণার আলোকে লেখক এই প্রবন্ধে বিশ্বে ভাষার উদ্ভব ও বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি সতর্কভাবে লক্ষ করছেন বাজার অর্থনীতির সর্বগ্রাসিতা ভাষাকে ঠেলে দিচ্ছে অরাজক পরিস্থিতির দিকে।
বাংলাদেশে বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের ভাষার পালাবদলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে ‘সম্প্রচারের ভাষা : সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট’ প্রবন্ধে। পাকিস্তানি আমলে এ দেশের বেতার ও টিভি সম্প্রচারে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটানোর অপপ্রয়াস চলেছিল। তা সত্ত্বেও তা সফল না হবার অন্যতম কারণ সম্প্রচারের ভাষাকে সাধারণ শ্রোতার উপযোগী রাখার দায়বদ্ধতা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সম্প্রচারে পাকিস্তান আরোপিত মেকি ভাষার পরাজয় ঘটে। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে সম্প্রচারে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যাপক গুরুত্ব পায়। তাকে নস্যাৎ করা হয় রক্তাক্ত আঘাত হেনে। সামরিক স্বৈরশাসকদের হাতে ‘বাংলাদেশ বেতার’ হয়ে যায় ‘রেডিও বাংলাদেশ’। সম্প্রচারে ধর্র্মচেতনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ষড়যন্ত্র চলে। বর্তমানে সম্প্রচার চলছে সেটেলাইট টিভি ও অসংখ্য বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে। তাতে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার প্রমিত মান রক্ষিত হচ্ছে না। নানা ভাষাভঙ্গি ও বৈভাষিক শব্দের মিশেল ঘটছে সম্প্রচারের ভাষায়। তবে এর বিপরীত চিত্রের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখক। সম্প্রচারের ভাষায় এবং নাটকে ও আবৃত্তিতে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের একটা সচেতন প্রয়াসও চলছে তরুণদের মধ্যে। প্রমিত উচ্চারণ নিয়ে অনেক প্রশিক্ষণও হচ্ছে। ভাষাকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করার এই প্রয়াস লেখককে আশাবাদী করে তুলেছে।
এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ ‘বিশ্বায়ন ও ভাষার সংকট’। প্রবন্ধের শিরোনামে ভাষার সংকট কথাটা থাকলেও প্রবন্ধে লেখক সার্বিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের কথা মাথায় রেখেছেন। বিশ্বায়নের প্রভাব চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছেন, বিশ্বায়নের মাধ্যমে দেশে দেশে সমাজজীবনে এসেছে প্রযুক্তিগত নতুন বিনোদন স্রোত। তার লক্ষ্য পরিভোগপ্রবণ সমাজ গড়ে তোলা। ভাষা ও সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য নিয়ে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ বিশ্বায়ন তা ঘুচিয়ে দিয়ে তৈরি করতে চাইছে ছাঁচে ঢালা মানুষ ও সমাজ। এর পরিণতি না বুঝে আমরা অবলীলায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছি এ স্রোতে। লেখক এ ক্ষেত্রে সচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের। তিনি মনে করেন, আগ্রাসী বিশ্বায়নকে মোকাবিলায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে জাতীয় জাগরণের মাধ্যমে।
এই গ্রন্থের লেখক মফিদুল হক ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ষাটের দশক থেকে শুরু করে অর্ধশতকেরও বেশি সময় তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতির জোয়ার-ভাটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও সক্রিয় থেকে। সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠক হিসেবেই তিনি নিরন্তর এ বিষয়ে লিখে চলেছেন। সে দিক থেকে এসব প্রবন্ধ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও গভীর ভাবনার ফসল।
এসব প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। চিহ্নিত করেছেন তার বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও সম্ভাবনার দিক। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন বাঙালির সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার পথে করণীয়গুলি। বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালির ঐতিহ্যিক সম্পদ লোকসংস্কৃতি রক্ষা ও লালনের ওপর।
এ বই বার বার অতীতের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়, তা এইজন্য যে অতীতের নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস থেকে আমরা যেন গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগুতে পারি। লালনকে কে বাঁচাবে―এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন ভূমিকাকেই প্রত্যাশা করেছেন তিনি।
ঢাকা থেকে বিদ্যাপ্রকাশ প্রকাশিত মফিদুল হক রচিত লালনকে কে বাঁচাবে (২০১০) বইটি সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গী বইয়ের মতো। সেই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা বই হিসেবেও বিবেচ্য।
লেখক : বাংলা একাডেমি ও
একুশে পদকপ্রাপ্ত, প্রাবন্ধিক, গবেষক