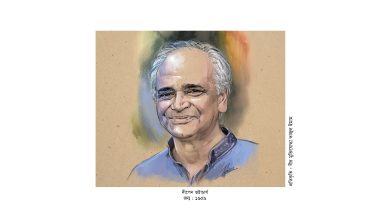প্রবন্ধ
বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য অতুলনীয়। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে সর্বকালের সেরা শিল্পীদের একজন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এটিও মনে রাখতে হবে, মননশীলতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের তুলনা তিনি নিজেই। প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা সহজে মেলে না। রবীন্দ্রনাথের রেনেসাঁস চেতনা ক্ষুরধার রূপ লাভ করেছে প্রবন্ধ সাহিত্যে।
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তাঁদের অপূর্ব প্রতিভাগুণে বাংলা গদ্যের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। তাঁদের তুলনায় স্বল্প আলোচিত অক্ষয়কুমার দত্তের অবদানও অনস্বীকার্য। তবে তাঁদের কারও হাতেই প্রবন্ধ যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। প্রবন্ধকে সাহিত্যের মর্যাদা দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধ সেই প্রথম প্রসাদগুণে সম্পন্ন ও রসের স্পর্শে রসমণ্ডিত হলো। বঙ্কিমের উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা প্রবন্ধ সার্থকতম রূপ পেল। কবি রবীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সমান কৃতিত্বের অধিকারী। অতুল গুপ্ত বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের গদ্য মহাকবির গদ্য কিন্তু ভুলেও পদ্যগন্ধী নয়।’ কথাটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। যুক্তি ও প্রসাদগুণের মিশেলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের মহামূল্যবান সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের রেনেসাঁস-চেতনার দ্যুতিতে অতুলনীয় শক্তিধর হয়ে ওঠেছে তাঁর প্রবন্ধ।
রেনেসাঁসের মানবতাবাদের কেন্দ্রীয় সত্য হচ্ছে মানুষ। ঈশ^র নয়, দেবদেবী নয়, অলৌকিক আধ্যাত্মিক কোনও বাস্তবাতিরিক্ত সত্তা নয়, স্পষ্ট মানুষ। মানুষের বিশে^ সবাই মানবিক, সমস্ত কিছুরই মাপকাঠি মানুষ, সেই যেমন বহুকাল আগে গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছিলেন। এই মানুষ কোনও আদর্শায়িত বা কাল্পনিক ভাব―সত্তা নয়, এ মানুষ আমাদের পরিচিত ইতিহাসের বাস্তব মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ। মানুষ অফুরন্ত সম্ভাবনার আকর, প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তা-ই। এই সম্ভাবনার সর্বাঙ্গীণ বিকাশেই মানুষের সার্থকতা। বুদ্ধিই এই সার্থকতালাভের প্রধান―বলা যায় একমাত্র পথ। বুদ্ধি অর্থ জ্ঞানের অনুশীলন, বিজ্ঞানের অনুশীলন, জিজ্ঞাসার জাগরণ, অন্তহীন অনুসন্ধান। যেহেতু বাস্তবাতিরিক্ত বা ইহজীবনের বাইরের কোনও তত্ত্ব মানুষের পক্ষে সত্য নয়, যেহেতু ইহজীবনের সত্য মানুষের সত্য―সেই হেতু বাস্তব জীবনের মধ্যেই মানুষের বিকাশ সত্য হয়, জীবনের আনন্দময় সম্ভোগেই মানুষ সার্থক হয়। বৈরাগ্যসাধনে মানুষের মুক্তি নয়, জীবনসম্ভোগেই মানুষ মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদ লাভ করে।
মুক্তি বা স্বাধীনতা, জীবনের সম্ভোগ বা ইহজাগতিকতা এবং সবার কেন্দ্রে মানুষ বা ব্যক্তি, এই হলো রেনেসাঁসি হিউম্যানিজমের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার মূল কথাও তাই―মানুষ। সর্বমানব এবং ব্যক্তিমানব, দুই-ই। প্রত্যেক ব্যক্তি অনন্য, প্রত্যেক অনন্য ব্যক্তিকে নিয়েই সর্বমানব। বাস্তবজীবনের অসংখ্য সম্পর্কের মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ। তারই নাম মুক্তি। তারই পথ যুক্তি। ব্যক্তির বিকাশ তথা মুক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যুক্তি ও জীবনাসক্তির। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেও এর পরিচয় মেলে।
মনুষ্যত্ব আর মুক্তি বা আত্মকর্তৃত্বকে রবীন্দ্রনাথ একবারে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই, সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বের পক্ষে ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ প্রবন্ধে তিনি সব থেকে জোরালো যে যুক্তি দিয়েছিলেন, তাহলো এই―
মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে ওই একই প্রবন্ধে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন―
… আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই।
… বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন… বিশ^প্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চ ললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূরে ভবিষ্যতের শিখাচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাতরাগিনী বাজিতেছে।
রেনেসাঁস বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনও প্রবন্ধ রচনা করেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে একাধিক রচনায় রেনেসাঁস সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি অব্যর্থভাবে রেনেসাঁসের প্রভাব চিহ্নিত করেছেন। ‘কালান্তর’ প্রবন্ধে বলেছেন :
একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলন্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না দিয়ে থাকতেই পারে না―এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।
বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব- ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেখানেই সে অধিকার করেছে। কীসের জোরে ? সত্যসন্ধানের সততায়।
… য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ^প্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা আর এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনও শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনও চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনও বিশেষ শ্রেণির বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।
ভারতবর্ষে রেনেসাঁসের প্রভাবকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধে লিখছেন :
য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এরূপ ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির উপর অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এরূপ ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।
… সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলি প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানস সৃষ্টি, সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।
রেনেসাঁসের মূলকথা জীবনবাদী মানবিকতা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মে জীবনবাদী মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করে তিনি মানবমুখিন জীবনচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন। ‘মানুষের ধর্ম’ রচনা থেকে উদ্ধৃতাংশটুকুকে তাঁর জীবনদর্শন বললে অত্যুক্তি করা হয় না―আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্তকে কখনওই ছাড়াতে পারে না।… মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন।
প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা আত্মজ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করলেন প্রতিবেশীকে জানার ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা। মানব অস্তিত্বের স্বার্থেই এই প্রয়োজনকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কথায় মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার কারণেই তার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে। সামাজিক সহযোগিতা সেই সহযোগিতারই সম্প্রসারণ যার উপর ব্যক্তির জীবন নির্ভর করে থাকে। ‘পল্লীপ্রকৃতি’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন―কোনও সন্ন্যাসী যদি বলেন যে, বিশে^র সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সংকুচিত করতে হবে তাহলে গোড়ায় মানুষের হাত দুটোই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্যন্তই যায়। সে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে; বলে, ‘ সংসারের সঙ্গে আমার কোনও ব্যবহারই নেই, আমি মুক্ত।
শাস্ত্রের অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেছিলেন রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ। লোকাচার ও কুসংস্কারকে পরাভূত করেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। নতুন জ্ঞান ও নতুন আদর্শ স্বাগত জানাতে না পারলে যুগের চেয়ে পিছিয়ে যেতে হয়। প্রগতির সাধক রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে ‘সমুদ্র যাত্রা’ প্রবন্ধে―স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।… লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না।… আমাদের কি নিজের কোনও শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনও দোষের সঞ্চার হয়… তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনও নিষেধ-বিধি ছিল কি না।… দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।… আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়ছে।… মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ… নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ^াস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে।… ইংরেজি শিক্ষাতে কেবল যতটুকু কেরানিগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না। এও কি কখনও সম্ভব হয়।
‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।’ অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যকে তিনি কখনওই সমর্থন করেননি। যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে তিনি সত্যকে যাচাই করেছেন। এই যুক্তিনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছেন রেনেসাঁস থেকে। মানুষে মানুষে বিভেদ ও ঘৃণা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সোচ্চার তিনি। ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধে প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন :
তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনও বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনওদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।
রেনেসাঁস তথা পাশ্চাত্যের প্রভাব ও আবহমান ভারতবর্ষের দ্বন্দ্বের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহ্য বিসর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। রেনেসাঁসের স্পর্শে ঐতিহ্যের নবায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ―আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্য জগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসে আছি।… মনে করিয়াছিলাম এই পাশ্চাত্ত্য মন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা-বিজেতার ভেদ থাকিবে না… ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি কীসের জন্য… ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটি যদি আমরা বরণ করিয়া লই তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।
বিশে^র সঙ্গে ভারতবর্ষকে যুক্ত করার সাধনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতি শুধু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে না। বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সামনে যেতে হয়। ‘হিন্দু বিশ^বিদ্যালয়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ―আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকেই যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স¦াতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনও মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে।
রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মন বিশ্বাস করে যে মানুষকে ঘৃণা করার কোনও বিধান কোনও শাস্ত্রে নেই। কোনও শাস্ত্রে যদি সেই বিধান থাকে তবে সে শাস্ত্র দিয়ে কোনও কল্যাণ হবে না। মানুষকে ঘৃণা করে, অপমান করে কখনও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। ‘কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে ধর্মের নামে যারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, বিভেদ ও রক্তপাত ঘটায় তারা প্রকৃত ধার্মিক নন। তারা ধর্মতন্ত্রের অনুসারী। ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত―ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে।… ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তাারিত নিয়মাবলি যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিন বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয় চৌদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটা দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।’
নিজের ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি কঠিন সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হয়ে শাস্ত্রীয় মত ও বাহ্যিক আচারকে প্রাধান্য দেয় তবে এটি চরম বিপর্যয় তৈরি করে। এমন চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের রচনাতেও। টলস্টয় ধর্মের তিনটি দিকের কথা বলেছিলেন―ঊংংবহঃরধষং ড়ভ জবষরমরড়হ (ধর্মের মূল মর্ম), চযরষড়ংড়ঢ়যু ড়ভ জবষরমরড়হ (ধর্মের দর্শন), জরঃঁধষং ড়ভ জবষরমরড়হ (ধর্মের আচার)। রবীন্দ্রনাথ কথিত ‘অন্তরের জিনিস’ টলস্টয়ের ভাষায় ধর্মের মূল মর্ম। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মর্ম অভিন্ন। পার্থক্য শুধু দর্শনে ও আচারে। মর্মের অভিন্নতা সত্ত্বেও যুগে যুগে এক শ্রেণির মানুষ অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রাণহরণ ও সম্পদ বিনষ্ট করেছে।
প্রকৃত ধার্মিক ধর্মকে ধারণ করেন, ধর্মতন্ত্রকে নয়। ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য যদি আমাদের বোধগম্য হয় তবে ধর্মের নামে হানাহানি বা উগ্রবাদের বিস্তার লাভ সম্ভব নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর এর ঢেউ প্রভাবিত করে তৎকালীন বাংলার সমাজমানসকে। রবীন্দ্রনাথ এর বাইরে ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায় যোগ দেয়নি। এ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ ছিল। কিন্তু মুসলমানদের এই আচরণে রবীন্দ্রনাথ কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেননি। ‘লোকহিত’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন―যে কারণেই হোক সেদিন স্বদেশি নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল। সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাক শুরু করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই; আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না।… বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্ন-বস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনও দিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।
বিস্মিত হতে হয় রবীন্দ্রনাথের তীক্ষè দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে। সাম্প্রতিক ভারতে গোহত্যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা উগ্ররূপ ধারণ করেছে। গোহত্যার অভিযোগে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কোনও কোনও স্থানে। এই পাশবিক প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের যুগেও ছিল। এই মূঢ়তার প্রতিবাদ করে ‘ছোট ও বড়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :
বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয় তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনও কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনও নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচার প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরও একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিত সাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া ওঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।
দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য রবীন্দ্রনাথের এই আশা পূরণ হয়নি।
ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের যে পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছিলেন, সেই পার্থক্য যুগে যুগে আরও স্পষ্ট হয়েছে। ধর্মকে বুঝতে না পারার অক্ষমতা থেকেই ধর্মতন্ত্রের অনুসারী হয়ে ওঠে মানুষ। ধর্মতন্ত্র ধর্মের মৌলনীতিরই বিরোধী। আচারসর্বস্বতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভেদের দেয়াল গড়ে তুলেছে―এটি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলসূত্রটি তিনি যেভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন সেভাবে অন্য কেউ পারেননি। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল কারণটি রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাক্সিক্ষত সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেনি। সেতুবন্ধন গড়ে তোলার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা অপরিহার্য। বাংলার রেনেসাঁস কাক্সিক্ষত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি দুই সম্প্রদায়ের অসম বিকাশের কারণে। এই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ―আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মানশিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।
…আমরা মুসলমানকে যখন আহ¦ান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক একদিন পরস্পরের যর্থাথ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।
বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম সীমাবদ্ধতা এই যে বৃহৎ সম্প্রদায় মুসলমান সেই রেনেসাঁসের আলোকস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। রেনেসাঁসের পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমানের আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘পাবনা অভিভাষণ’ এ তিনি বলেন―চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নেই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনওমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না… যে রাজপ্রাসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।… ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে-সহিষ্ণুতা, যে-সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।… জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।
রেনেসাঁসের মানবতাবাদ সব শ্রেণির মানুষকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। সেই ঐক্যের আহবান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে :
আমাদের দেশেও একটু নাড়া দিলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি ? একত্র সংগঠনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।… কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত করো, যে, দেশের উচ্চ ও নীচ , হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।
নির্মোহভাবে নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুসলমান ও সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন সময়ে অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে ডাকার সুবিধাবাদী নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। স্পষ্টভাষী রবীন্দ্রনাথ ‘সদুপায়’ প্রবন্ধে বলেন―আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম।… ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনও প্রমাণ কোনও দিন দিই নাই… এমন অবস্থায় ‘ভাই’ শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না… জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া ‘মা’ শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি… দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই।
হিন্দু রিভ্যাইভ্যালিস্ট ও মুসলিম রিভ্যাইভ্যালিস্টরা যখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করছে তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। ‘কোট চাপকান’ প্রবন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ―এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনও মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।
… আমাদের ভারতবর্ষের সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, নৃত্য, গীত ও রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনওটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে।
বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের রিভ্যাইভ্যালিস্ট দ্বারা কণ্টকিত হয়েছিল। সেই কাঁটা অপসারণ করে রেনেসাঁসকে কাক্সিক্ষত গন্তব্যে পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবেই বাংলার রেনেসাসেঁর ফলবতী ধারাকে দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা করেন তিনি।
মনুষ্যত্ব তথা মানবধর্মকে সবার উপরে ঠাঁই দিয়েছিল রেনেসাঁস। মানবধর্মকে রবীন্দ্রনাথও সর্বাগ্রে বিবেচনা করেছেন। ‘মানুষের ধর্ম’ বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন―আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সে পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে।… আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।
ধর্মের সত্য রূপের যারা সন্ধান করেছেন তারা সকলেই যুগে যুগে, দেশে দেশে একই কথা বলেছেন। তারা সকলেই ধর্মকে শাস্ত্র এবং আচারসর্বস্বতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে সর্বমানবের কল্যাণময় পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, পৌরাণিক যুগের কৃষ্ণ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম পুরোহিত-শাসিত শাস্ত্রসিদ্ধ বিধানের অমোঘতা মেনে নেয়নি। তিনি ধর্মের আবেদন আর্য-অনার্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য বিস্তৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাখাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পুরাকাহিনি এ কথাই প্রমাণ করে। যে ধর্মের মধ্যমণি হিসেবে কৃষ্ণ বিরাজ করেছেন সে ধর্ম-মূলত ছিল অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আশ্রয়স্থল। পরবর্তীকালে, ঐতিহাসিক যুগে গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন ধর্মীয় চেতনাকে সকল মানুষের জন্য কল্যাণমুখী করে তুলতে। যিশু খ্রিস্টও একই পথে তাঁর প্রচারিত ধর্ম পরিচালনা করেছেন। ‘খৃস্ট’ রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন―… মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলেছিলেন, বলি নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।
‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’―চণ্ডীদাসের উচ্চারণকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রবল আস্থা ছিল মনুষ্যত্বের শক্তির প্রতি। গৌতম বুদ্ধের প্রতি তিনি শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন মনুষ্যত্বের শক্তিকে বুদ্ধ মহীয়ান করেছিলেন বলেই। ‘মন্দির’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি― ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।… মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।
ভারত বহু ধর্ম, জাতি ও ভাষার দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিজেপি এক জাতি, এক ধর্মের ভারত গড়ে তোলার শূন্যগর্ভ তত্ত্ব উপস্থাপন করে যাচ্ছে। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের সময়েও ছিল। তিনি এই প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ভারতের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, সামাজিক ভেদাভেদ ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো―আজকের দিনে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নানাবিধ যে সকল জাতি বাস করিতেছে তাহাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ সত্তাকেই ভারতীয় নেশন বলা যাইতে পারে। অতএব ন্যাশনাল বিদ্যালয় তাহাকেই বলা যায় যেখানে শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলন সাধনের দ্বারা এই নানা জাতি নানা সম্প্রদায় আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করে।
ধর্মের নামে বিভাজন ও রক্তপাতকে বরাবরই ঘৃণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ‘ধর্ম ও জড়তা’ রচনায় লিখলেন―আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি! তাইতো দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারছে। এই কি হলো ধর্মের চেহারা ? এই মোহমুক্ত ধর্মবিভীষিকার চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।
ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্ঠা উপমহাদেশের পুরাতন ক্ষত। এখনও এ ক্ষত সারেনি। এর উপশমের বিধান প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ ‘কালান্তর’ প্রবন্ধে দিয়েছেন যা এ যুগেও প্রাসঙ্গিক―ধর্মের মিলেই যে দেশ মানুষকে মিলায়, সে দেশ হতভাগ্য।
ধর্মান্ধতা ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন ন্যায়বোধ ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে। সংকীর্ণ জনমত উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ মুক্তচিন্তা ও স্বচ্ছ বিবেককে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের বাইরে তাঁর কোনও দেবতা নেই। মনুষ্যত্বের অবমাননা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। শুধু কবি নন, একজন সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় তিনি কথা বলেছেন। মনুষ্যত্বকে যে তিনি সবার উপরে ঠাঁই দিয়েছেন এর উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। ‘প্রাচ্যসমাজ’ প্রবন্ধে তিনি বলেন―য়ুরোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এসিয়াতে তাহা নাই।…তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙ্গিয়া আসে, পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপর স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।… যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন বুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক।
যুক্তিবোধের সর্বজনীনতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। বাইরের চেহারায় ও গড়নে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, একের সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অন্যের সঙ্গে মেলে না, এমনকি ভিন্ন পরিবেশের কারণে বিভিন্ন জনের আবেগগত প্রক্রিয়াও আলাদা হয়। ভিন্নতাকে অতিক্রম করে মানুষ সম্মিলিত হয় তখনই যখন সে যুক্তিবোধসম্পন্ন, কারণ প্রকৃতিগতভাবেই যুক্তি ব্যাপারটি সর্বজনীন এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকাশ ভিন্নতাকে তা অতিক্রম করে থাকে। ব্যক্তিমানুষ বা জনগণ যুক্তিবোধের সর্বজনীনতায় যতটুকু পৌঁছায় ঠিক ততটুকু বিরাটত্ব সে অর্জন করতে পারে। যুক্তি দ্বারা চালিত না হলে ব্যক্তিমানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ঘটনার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হতো। যুক্তিবোধই পারে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অগণ্য দাবির ভিতর থেকে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে। রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তিবোধের দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাস্বর হয়ে উঠেছে।
রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদের ভিত্তি―তাঁর মানুষ সম্পর্কিত ধারণায়, যাকে বলা যায় তাঁর মানবপ্রত্যয়। তাঁর যুক্তিবাদ যে একপেশে হয়ে উঠতে পারেনি সেও এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্ব সমগ্রতায় তত্ত্ব, তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সামনে মানুষের যে রূপটি উজ্জ্বল হয়ে আছে তা হলো জ্ঞানে কর্মে অনুভবে পূর্ণ মনুষ্যত্বের রূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রাচীন ভারতের মহত্ত্ব¡ কোনও প্রকার মানসিক প্রতিকূলতা ব্যতিরেকেই সত্যানুসন্ধানে নিহিত ছিল। যুক্তিতে বিশ^াস হারানোর ফলে সেই মহত্ত্ব খর্ব হয়। ‘স্বদেশি সমাজ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ―এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে―আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে।… ভারতে ‘সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি―কী জলময় সমুদ্র, কী জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশে^র, দাঁড়াইলাম পল্লিতে।
রেনেসাঁসের অন্যতম অবদান বিজ্ঞানমনস্কতা। রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানচেতনার অনুশীলন করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক পথিকৃৎ গ্রন্থ ‘বিশ^পরিচয়’ তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ^াসের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আধুনিক, উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ মতামত তুলে ধরেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘শিক্ষা’ সংকলনে বললেন―বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ^ররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি পদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশে^র সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।
শিক্ষাজীবনের শুরুতেই বিজ্ঞানশিক্ষার কথা জোর দিয়ে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ― শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।
মাত্র একটি বাক্যে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’র বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন―বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।
সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা যে চিঠিটি ‘বিশ^পরিচয়ের’ ভূমিকা, তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন―আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধকরি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফোরিত হয়ে যেত।…
তারপর বয়স আরও বেড়ে উঠল।… সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছতার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি।…
… জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পানিবিজ্ঞান কেবলই এই দুই বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।
এর পরেই রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলেছেন, তা তাঁর জীবনদর্শনকে বোঝার পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আত্মবিশ^াসের সঙ্গে বলেছেন যে, এভাবে নিষ্ঠা সহকারে বিজ্ঞান পাঠের ফলে―অন্ধবিশ^াসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।
আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অভাবে যে চিত্তদৈন্য ঘটে, বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। এ কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কত অসম্পূর্ণ এ কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন নানা উপলক্ষে। এখানেও তিনি সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন―বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।
এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু তথ্যের কথা বলছেন না, বলছেন বিজ্ঞানের নিজস্ব সংস্কৃতির কথা। এই সংস্কৃতির প্রাথমিক কথাই হল ঔৎসুক্য, সমস্ত বিশ^সংসার সম্বন্ধে অপরিসীম ঔৎসুক্য। আর সেই ঔৎসুক্য যখন তৃপ্ত হয় সার্থক হয়, তখনই জিজ্ঞাসুর মনে রসের সঞ্চার হয়। বিজ্ঞানকে যাঁরা শুধু তথ্যের সমাহার বলে ভাবেন, তাঁরা তার প্রেরণার উৎসটাকেই জানেন না। বিজ্ঞানচর্চার অন্তিম সার্থকতা আসে একধরনের সৌন্দর্যের উপলব্ধি থেকেই। অর্থ নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, যথার্থ বিজ্ঞানের পুরস্কার হল সেই সৌন্দর্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে দেখেছেন শক্তিরূপে, যন্ত্ররূপে নয়।
বিজ্ঞানচর্চা মানুষকে প্রশ্নপ্রবণ ও পরীক্ষাপ্রবণ করে। আরও বড় কথা, জীবনদৃষ্টিকে ঋজু ও নির্ভীক করে―মানুষকে আত্মশক্তিতে বিশ^াসী করে। এই আত্মশক্তিতে আস্থা মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ। সুদূর অতীত থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে মানুষ আত্মশক্তিতে―কোনো অলৌকিক শক্তিতে নয়, দৈব নয়, গুরুতে নয়, সোজাসুজি আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে উঠছে। মানুষের অগ্রগতির এটি প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। বলাবাহুল্য এটি রেনেসাঁসেরই বৈশিষ্ট্য।
বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠার মানে হলো যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা। সবার উপরে বুদ্ধি সত্য, সবার উপরে যুক্তি সত্য, সবার উপরে পরীক্ষা সত্য―এই হলো বিজ্ঞানমুখিতার মূল মন্ত্র। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেখানে লোকের যুক্তিবাদিতা ক্রমশ কমতে থাকতে থাকে, আত্মশক্তিতে আস্থা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ক্রমশ আত্মশক্তিতে আস্থাশীল হয়েছেন, ক্রমশ আপোষহীনভাবে যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রগতিশীলতার অন্যতম লক্ষণ এই যে বার্ধক্যের চিরায়ত পশ্চাদ্গমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী হলেই যে মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। রবীন্দ্রনাথের কালে এবং এযুগেও এমন ডিগ্রিধারী রয়েছে যারা বিজ্ঞানের মোড়কে অন্ধ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছে। তাদের উদ্দেশে ‘শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন―… সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের মনের যোগ হয়নি। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রিধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্তলে; তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ^াস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।
‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন―… মানুষের সব চেয়ে বড় স্বভাব হলো মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী।
…জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব।
রেনেসাঁস প্রত্যয় যুগিয়েছিল মানুষের অনন্য সম্ভাবনা সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথও আস্থা রেখেছেন মানুষের শক্তিতে। ‘সৃষ্টি’ প্রবন্ধে তাঁর স্পর্ধিত উচ্চারণ―মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো মানুষ সৃষ্টিকর্তা।
রবীন্দ্রনাথের তীক্ষè বিজ্ঞানচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে যেখানে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান সম্পর্কে তিনি সারগর্ভ মন্তব্য করেছেন―‘জগদীশ আজ বিশ^কে যা দিচ্চেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডুক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চ্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্যদর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েছে।’
রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা লক্ষ্য করে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে বলেছিলেন―তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।
এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাকপতি রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে―রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একাধারে অপার্থিব রসানুভূতি ও বস্তুতন্ত্র বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়; সেই জন্যই তাঁহার রচনা ও আলোচনা উভয়ই কল্পনা ও বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল।… গণিত, ফলিতবিজ্ঞান, দ্যুলোকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব… সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য ও সংস্কৃতিপূত চিত্তের উপযোগী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাঁহার আছে। তাঁহার মধ্যে রসসৃষ্টির অপরিহার্য্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলে, এই মন লইয়া রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন বড় দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হইতে পারিতেন।
বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তির অনুশীলন দ্বারা গত শতাব্দীতে তুরস্কে নবজাগরণ ঘটেছিল। মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে গিয়ে তুরস্কের এই পরিবর্তন দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাগত জানিয়েছেন রেনেসাঁসের দীপ্তিকে। ‘পারস্যে’ গ্রন্থে লিখেছেন―নব তুরস্ক একদিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর এক দিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে-বাহিরে। কামাল পাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধূনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন… পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন সকলের আগে করা চাই।
রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তবে প্রবল ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। সেই চেতনা ছিল জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণের পক্ষে।তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। আজীবন তাঁর অবস্থান ছিল সাম্যের পক্ষে। রাশিয়ায় গিয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। রাশিয়ার জাগরণকে তিনি রেনেসাঁস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। রাশিয়ার সমস্ত সাফল্যের মূলে তিনি দেখেছেন শিক্ষাকে―আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হলো শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত-ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে (রাশিয়ায়) সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।
মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূলে হলো তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ…। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম―জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি…।
… মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আপন সম্পদকে কড়াক্কড় করে আটে-ঘাটে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা-অর্থাৎ ধন কোনও একজায়গায় একান্ত বাঁধা থাকবে এটা বিশ^নিয়মের বিরুদ্ধ। রাশিয়ায় সোভিয়েট কথাটা বুঝচে। তারা ব্যক্তিগত লোভের থেকে ধনকে মুক্ত করতে চায়। যদি পারে তাহলেই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তারা সত্য করে পাবে।
… তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরও যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা―অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে।
রবীন্দ্রনাথ যেভাবে যুক্তি দিয়ে সাম্যের কথা বলেছেন, গণমুক্তির কথা বলেছেন, যে রকম সর্বান্তঃকরণে ধনতন্ত্র-বিরোধী, শোষণ-বিরোধী ও সভ্যতার ভিত্তি-বদলের কথা বলেছেন, সকল সমস্যার একেবারে মূল ঘেঁষে সমাধান করার কথা বলেছেন, তাতে তাঁকে সাম্যবাদী না বলার কোনও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ ধনতন্ত্রবিরোধী, শোষণবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। অর্থনৈতিক সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য সামাজিক সাম্য―শিক্ষার সাম্য, সুযোগের সাম্য, সর্বপ্রকার সাম্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত কাম্য―এখানে তাঁর সমর্থন সম্পূর্ণ শর্তহীন। তিনি জানেন, অসাম্য মানবমুক্তির প্রতিবন্ধক। দানবের সঙ্গে যে সংগ্রামের প্রয়োজন আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। এই সংগ্রামের জন্যে যারা প্রস্তুত হচ্ছে ঘরে ঘরে, নগরে প্রান্তরে, হাটে-ঘাটে-পথে, কারখানায়- খামারে, দেশে-দেশান্তরে তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক। তাদের সক্রিয় সমর্থক তিনি। তাই রাশিয়ার সঙ্গে কবি এত একাত্ম হতে পেরেছেন। রাশিয়া ভ্রমণকে উল্লেখ করেছেন তীর্থদর্শন হিসেবে। অভিভূত কবির অভিব্যক্তি―
রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনও দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।…
মস্কোর পথে চলেছি। আমার মনে হয় মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে ঐ পথে।
ধর্মহীনতার অজুহাত তুলে যারা রাশিয়ায় নিন্দা করে তাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন―অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনওখানে আছে ?
বাংলার রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বুঝেছিলেন, সেভাবে আর কেউ বুঝেছিলেন কিনা সংশয় রয়েছে। রেনেসাঁসের উৎপত্তি নগরে। কিন্তু নগর থেকে পল্লি পর্যন্ত যদি এর ব্যাপ্তি না ঘটে তবে সেই রেনেসাঁস খণ্ডিত থেকে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন চিন্তা। সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষদের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধে বলেছেন―… যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পর্শ অন্ধকারের ব্যবধান।
ভারতবর্ষ পল্লিপ্রধান দেশ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রামে-গাঁথা দেশ। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মানুষমুখী দেশপ্রেমকে পল্লিমুখী দেশপ্রেমও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ দেশের নেতৃস্থানীয় চিন্তাশীল সকলকে আহ্বান করে তাদের দৃষ্টি পল্লি-অভিমুখী করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র তাঁর গ্রাম, ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে গ্রামকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ‘স্বদেশী সমাজ’ এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে―ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান দেশ নয়, সমাজপ্রধান দেশ। দেশকে ধারণ রক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব চিরকালই সমাজের। সেই গ্রাম সমাজকে সংগঠিত করে নিতে হবে।
আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি-আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি।
সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে কখনও দেশের অগ্রগতি হতে পারেনা। বুলিসর্বস্ব দেশপ্রেমের ফাঁকিকে যথার্থই চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘পল্লীসেবা’ প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন―মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে বলি ছোটলোক; সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোট।
… দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছে অথচ আমাদের এক দেশ নয়।
‘ছিন্নপত্রাবলী’তে দরিদ্র চাষীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সহমর্মিতার পরিচয় স্পষ্ট―… আমার এই দরিদ্র চাষি প্রজাগুলো দেখলে আমার ভারি মায়া করে―এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো―নিরুপায়―তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনওমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে―যদি একবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড় নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।
রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ অর্থ দেশের মানুষ। তাদের অধিকাংশই অনশনক্লিষ্ট রুগ্ণ ও অশিক্ষিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনা অর্থই দারিদ্রের ভাবনা, অশিক্ষার ভাবনা, স্বাস্থ্যহীনতার ভাবনা। এই ভাবনারই পরিণতি শ্রীনিকেতনের কর্মোদ্যম, পল্লিসংগঠন বিভাগের প্রতিষ্ঠা। এই ভাবনারই পরিণতি কুটিরশিল্পের উদ্যেগ, কারুকলার উদ্যোগ, উন্নততর কৃষি, পল্লিতে পল্লিতে সীমিত শিল্পায়নের প্রয়াস। এই ভাবনারই পরিণতি গ্রামজীবনে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। সব থেকে বড় পরিণতি-সমবায়! এসব উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের পরনির্ভরশীল করতে চাননি, তাদের মধ্যে জাগরণ ও আত্মবিশ^াস তৈরি করতে চেয়েছেন।
আজ সমবায় আন্দোলন সকলের সুপরিচিত আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ যে সময় সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, অক্লান্তভাবে সমবায়নীতির প্রচার করেছেন, সে সময় সমবায় সম্পর্কে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি অগ্রগামী চিন্তা করেছেন। সমবায় কেবল অর্থনৈতিক সংগঠন বা উৎপাদন-বণ্টনের সংগঠন নয়, তার মর্মগত সত্যটির ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ। সমবায়ের শক্তি মিলনের শক্তি, সহযোগিতার শক্তি।
কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রামকে বেছে নেয়ার প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন―দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার এই গ্রামের কাজে। শিক্ষা-সংস্কার এবং পল্লিসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।
জীবনের শেষ জন্মদিনে ‘সভ্যতার সংকট’ নামে একটি অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধ তখন চলমান। মানবজাতির ঐক্যের সাধক রবীন্দ্রনাথ স্বার্থলোলুপ রাষ্ট্রসমূহের হিংস্রতায় ক্ষুব্ধ। তবে হতাশ হননি, আশায় বুক বেঁধেছেন। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় আশাবাদী ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন―মানুষের প্রতি বিশ^াস হারানো পাপ, সে বিশ^াস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।
মানুষের অসীম সম্ভাবনায় বিশ^াস স্থাপন রেনেসাঁস চেতনার মূল কথা। সমগ্র পৃথিবীকে নিজের দেশ বলে জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সমস্ত মানবজাতিকে আপন ভেবেছিলেন। আশাবাদী হয়েছিলেন মানব ইতিহাসের আসন্ন সম্ভাবনাময় যুগ সম্পর্কে। রেনেসাঁসি প্রত্যয়কে ধারণ করেছিলেন বলেই তিনি মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনায় বিশ^াসী ছিলেন, বিশ^াস করতেন সব মানুষ মূলত এক জাতি অর্থাৎ মানবসভ্যতার ঐক্যে ছিল তাঁর গভীর বিশ^াস। এই চেতনা থেকেই তিনি মানুষের অগ্রগতিতে বিশ^াসী। তিনি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যকে মূল্যবান মনে করেন, প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে অনন্য মনে করেন। একই সঙ্গে তিনি ভাবতে পারেন, পৃথিবীই একমাত্র দেশ এবং মানুষ হচ্ছে একমাত্র নেশন। জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের রেনেসাঁস ভাবনার দীপ্তিমান প্রকাশ ঘটেছে―সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।… পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জেনেছি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্ব পৃথিবীর হাওয়া উঠেছে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিত। এইখানে রামমোহন রায় সর্বজনীন ধর্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন―সেই প্রভাতের আলোকেই বাংলাদেশের নবজাগরণের উষালোক। সেই আলোকে যে বিশে^র সুর বেজেছে সেই সুরই আমাদের সুর―সেই সুরই মানব ইতিহাসের আসন্ন ভাবীযুগের সুর।…
লেখক : প্রাবন্ধিক