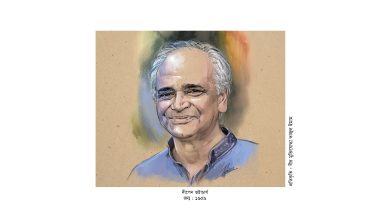প্রবন্ধ
প্রাককথন
ইমদাদুল হক মিলনের জন্ম ১৯৫৫ সালে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভেঙে তৈরি হলো ভারত ও পাকিস্তান। সে পাকিস্তানের দুটি অংশ, পূর্ব ও পশ্চিম। সুদীর্ঘ হাজার বছরেরও অধিক যে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, স্বাধীনতা তথা দেশভাগের ফলে তাতে চিড় ধরল অনেকটাই। সাধারণ মানুষ যেমন তেমনি বহু শিল্পী-সাহিত্যিক বাধ্য হলেন নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে। শওকত ওসমান, আনিসুজ্জামান, হাসান আজিজুল হক আশ্রয় নিলেন পূর্ব বাংলায় আর পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বুধজন।
সংস্কৃতির অঙ্গনে, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতা ধারণ করে আসছিল ঐতিহ্যের পরম্পরা, উত্তরাধিকার। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হবার সুবাদে কলকাতা সাংস্কৃতিক উন্নতির চূড়ায় উঠতে পেরেছিল। তবে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ১৯ ও ২০ শতকে নিতান্ত নগণ্য নয়। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক, নীলদর্পণ। একই সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘস্থায়ী ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা।
এতৎসত্ত্বেও ১৯৩৫ সাল থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় স্থান পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন যেমন পশ্চিমবঙ্গের কবিরা তেমনি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী প্রমুখ। ১৯৫৩ সাল থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাস পত্রিকা পূর্ববঙ্গের কবিদের যথেষ্ট ও যথাযথ প্রশ্রয় দিয়েছে।
কবিতা ও কৃত্তিবাস ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হতো, যাদের দরজা পূর্ববঙ্গের কবিদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। পত্রিকাগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন ছিল দৈনিক আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক দেশ তেমন ছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা, আলোক সরকার সম্পাদিত শতভিষা ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গ থেকেও ১৯৪৭ এবং তার পরবর্তীসময় নতুন কবি-সাহিত্যিকদের আহ্বান জানাল চট্টগ্রাম থেকে মাহবুবুল হক সম্পাদিত সীমান্ত, অভিযান (১৯৫৪), মেঘনা (১৯৫৭), অগত্যা (১৯৪৯), উত্তরণ (১৯৫৮), দিলরুবা (এখানেই আব্দুল গাফফার চৌধুরীর চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল)।
১৯৫৭। ইমদাদুল হক মিলনের বয়স যখন দুবছর, ঠিক সেসময় পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে উচ্চাকাক্সক্ষী পত্রিকা ‘সমকাল’ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সিকানদার আবু জাফর। স্বাধীনতা-পরবর্তী পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকার ইতিহাসে একদিকে যেমন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত কণ্ঠস্বর, রফিক আজাদÑআব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত স্বাক্ষর দিশারীর ভূমিকা পালন করেছিল, কলকাতা থেকে এ সময় তাঁর বাস ও পত্রিকা সওগাত উঠিয়ে এনে ঢাকায় থিতু হন মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন। বলা বাহুল্য, তাঁর পত্রিকা পূর্ববঙ্গের ৫, ৬ ও ৭-এর দশকের কবি-সাহিত্যিকদের যেমন ছিল সূতিকাগার তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গের সাহিত্যকে গতিজাড্য দিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। এরই পাশাপাশি ১৯৫৬ সালে যখন বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলো, সেখান থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রিকা তৎকালীন লেখকদের প্রিয় আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।
ইমদাদুল হক মিলন যেহেতু কথাসাহিত্যিক, একদা পূর্ববঙ্গ এবং ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতি বিহঙ্গাবলোকন জরুরি। আমরা কেবল পূর্ববঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় রচিত বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিও এক্ষেত্রে মনোযোগী হতে চাই। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর কালপর্বে পশ্চিমবঙ্গে গদ্যসাহিত্য যে মূল্যবান ফসল ফলিয়েছে, তার তুলনায় পূর্ববঙ্গের অবদান নানা কারণেই ছিল সীমাবদ্ধ জলে অবরুদ্ধ। ঐতিহাসিকভাবে মনে করা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব। যেমন টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল (মতান্তরে হানা ক্যাথারিন ম্যালেনস-এর ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’) এর মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের পথচলা, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ এক্ষেত্রে খ্যাতিচিহ্নিত। সেই থেকে প্রায় দেড়শো বছর ধরে বাংলা গল্প-উপন্যাস লেখকদের যে মেধাতালিকা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতাদেবী, কমলকুমার মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মাত্র কয়েকটি নাম। একদা বাংলা কথাসাহিত্যিকরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে অবস্থান করেও বিভা ছড়িয়ে গেছেন। যেমন মুজঃফরপুরে বসে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিয়ায় সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা ভাগলপুরে বনফুল। বাংলার বাইরে ত্রিপুরাতেও ছিল এবং এখনও রয়েছে কবিতা ও গল্প- উপন্যাসের স্রোতধারা। ত্রিপুরায় গদ্যকারদের মধ্যে ১৯৪৭ পরবর্তী উল্লেখযোগ্যরা হলেন বিমল চৌধুরী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, বিমল সাহা, মানস দেববর্মন, কালিপদ চক্রবর্তী, প্রদীপ সরকার, অরুণোদয় সাহা প্রমুখ।

১৯৪৭ পরবর্তীসময়ে পূর্ববঙ্গে কবিতা যত দ্রুত সাহিত্যের অঙ্গন দখল করে ছিল, বলা বাহুল্য কথাসাহিত্য তা পারেনি। পাশাপাশি একথাও সত্য যে কবি জসীমউদ্দীন লিখেছিলেন বোবা কাহিনী-র মতো উপন্যাস বা এমন কি মূর্তজা বশীর লিখেছেন আলট্রা-মেরিন উপন্যাস। তবে এই সময়কালে কথাসাহিত্য হীরকদীপ্ত করে রেখেছেন আবু ইসহাক তাঁর সূর্যদীঘল বাড়ি এবং সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর লাল সালু উপন্যাস দুটির মাধ্যমে। বাংলাদেশের কথা সাহিত্য: প্রাক-মিলন পর্ব।
পূর্ববঙ্গের সৃজনশীল কথাসাহিত্যের কতগুলো প্রস্থান তথা শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করা যায়। এদের মধ্যে একটি হলো ইসলামি ধারা। অপর ধারাটি মার্কসবাদী তথা সাম্যবাদী ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই ধারার লেখকদের মধ্যে সত্যেন সেন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ অগ্রগণ্য। অপর ধারাটি সদ্য স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা লেখকদের রচনায় রঞ্জিত। এঁদের মধ্যে আছেন শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবু রুশদ।
এঁদের মধ্যে অনেকেই ১৯৪৭-এর আগে থেকেই লেখার জগতে আসেন। উল্লিখিত লেখদের প্রায় সকলের মধ্যেই ছিল দেশি-বিদেশি সাহিত্যপাঠের ব্যাপক অভিজ্ঞতা। নদীমাতৃক বাংলাদেশের যে বিপুল বৈচিত্র্য, তা এসব লেখকের গল্পে-উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা উঠে এলো, যা বাংলা সাহিত্যে এতকাল ছিল না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে গহর বা তাঁর ‘মহেশ’ গল্পে গফুর বা রবীন্দ্রনাথের ‘একটি মুসলমানীর গল্প’ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে হোসেন মিয়া ব্যতিক্রম মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করে দুর্গেশনন্দিনী বা রাজসিংহ উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র থাকলেও সেসব চরিত্র প্রাচীন কালের। সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধি তারা নয়।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের লেখকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে নিয়ে এলেন বাঙালি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা ধর্মে মুসলমান, তাদের হৃৎস্পন্দন। এর ফলে এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অন্তর ও বাহির পাঠকের গোচরে এল। বাংলা সাহিত্যের চারণভূমি সীমিত সবুজ-এর ফলে দিগন্তপ্লাবী হলো। আরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যযোগ্য বিষয় তাহলো শহর ও বিশেষ করে গ্রাম-গ্রামান্তরে আমজনতার মধ্যে হাট, মাঠে বাজারে, বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, পীরের মাজার আর বৌদ্ধ সংঘারামে যেসব সংখ্যাহীন শব্দ ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দ তাঁদের লেখায় তুলে আনা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংকলিত ‘আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ যে অজস্র শব্দ ধারণ করেছে তাতে গল্প উপন্যাসে ঠাঁই দিয়ে তাঁরা শব্দগুলো বাংলা ভাষার অবধারিত অলংকারে পরিণত করেছেন।
নদীর পর নদী, এই নিয়ে বাংলাদেশের অনন্যতা। পূর্বে চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও কুয়াকাটার সমুদ্র, মধুপুর, বান্দরবান ও খাগরাছড়ির অরণ্য একদিকে, অন্যদিকে বাংলার সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মহাস্থানগড় পাহাড়পুর লালমাঈ উয়ারি-বটেশ্বর-বিক্রমপুরের ঐতিহ্যে অবগাহন করে আছে যে বাংলাদেশ, তার হৃদয়ের বার্তা বাংলাদেশের কথা তাদের কাব্যের রচনায় উঠে এসেছে। শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন, সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত, সেলিনা হোসেনের নীল ময়ূরের যৌবন, মোহিত কামালের লুইপার কালসাপ ইত্যাদি রচনায় যেমন পাই ‘মা-যা ছিলেন’ তেমনি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই, হাসান আজিজুল হকের আগুনপাখি অথবা শওকত ওসমানের জাহান্নাম হইতে বিদায় উপন্যাসে পাই ‘মা-যা হইয়াছেন’।
বাংলাদেশের কবিতা ও নাটক যতটা সফল হয়েছিল, গোড়ায় গল্প উপন্যাস ততটা হতে পারেনি। তবু এরই মধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সফল প্রসূন হিসেবে গণ্য করা চলে হাসান হাফিজুর রহমানের আর একটি মৃত্যু, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি তুলসীগাছের কাহিনী, শাহেদ আলীর জিব্রাইলের ডানা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিরুদ্দেশযাত্রা, হাসান আজিজুল হকের শকুন।
এবারে আমরা দেখার চেষ্টা করব, ইমদাদুল হক মিলন তাঁর কথাসাহিত্যে বাংলা গল্প-উপন্যাসের দিগন্তে কী অভিপ্রায় নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর রচনাবলির সামূহিক বার্তা। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে তাঁর গল্পলেখকরূপে আবির্ভাব এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করব, ছোটগল্পকার মিলন শুরু থেকেই কতখানি পাঠকের অভিনিবেশের দাবি রাখেন। তাঁর গল্পে যে নিজস্ব গঠনরীতি রয়েছে, রয়েছে গল্প বুননের পারিপাট্য ও মুনশিয়ানা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সামঞ্জস্যরক্ষা―এসব মিলিয়ে মিলনের ছোটগল্প যে অনন্যতা অর্জন করেছে, তার স্বরূপ উন্মোচন করব আমরা।
খেলোয়াড় : একটি আন্তর্পাঠ
‘খেলোয়াড়’ গল্পটি ১৯৭৬ সালে লেখা, লেখকের বয়স যখন মাত্র ২১ বছর। প্রতিতুলনায় আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকার রূপে আবির্ভাব ৩০ বছর বয়সে। যে সময়ে তাঁর হাতে ‘দেনাপাওনা’, ‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘পোস্টমাস্টার’ ইত্যাদি গল্প একের পর এক প্রকাশিত হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসি লেখক মোপাসাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প ‘নেকলেস’ রচিত হয় লেখকের যথেষ্ট পরিণত বয়সে। পাশাপাশি সমারসেট মমের বিখ্যাত গল্প ‘দি লোটাস ইটার’ লেখা হয়েছিল তাঁর মধ্যবয়সে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, মোপাসাঁ অথবা মমের সঙ্গে মিলনের গল্পের প্রতিতুলনা অবান্তর। তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, রচনার পরিপক্বতা এবং অনুপুঙ্খতার বিচারে মিলন এখানে অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। গল্পটি বীরু নামে এক সাধারণ ফুটবল খেলোয়াড়ের অসাধারণ জীবন-আখ্যান। বীরু এক নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার স্বপ্ন একজন বড় ফুটবলার হওয়া। নিতান্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে হলেও যে বড় ফুটবল প্লেয়ার হওয়া যায়, এমন কি হতদরিদ্র অবস্থা থেকেও পেলের মতো বড় বিশ্বখ্যাত ফুটবলার হওয়া সম্ভব, তা আমরা জানি।
বীরুর দারিদ্র্য এতটা তীব্র ছিল না। তার বাবার এমনকি ইচ্ছা ছিল তাকে ডাক্তার বানাবার। সেজন্য ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছিল সে, যদিও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ না থাকায় সে পরপর তিনবার ইন্টারমিডিয়েটে ফেল করে। ফলে তার ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না। আসলে বীরুর প্রতিভা বিকশিত হতে পারে ফুটবলেই, এটা বীরু ভালো করেই জানত। তাই বীরুর স্বীকারোক্তি―‘ফখরুল স্যার অঙ্ক করিয়ে যেতেন, আমি সেই অঙ্কের পরিবর্তে খাতায় দেখতাম উদাস একটা মাঠের ছবি। বাইশ জন প্লেয়ার ফুটবল খেলছে সেই মাঠে। এই সুন্দর বিকেলে আমি ফখরুল স্যারের কাছে বন্দি হয়ে আছি আর সবাই খেলছে, আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত।’ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা আর চৌতিরিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে তেইশ বছরের বীরু তার বাবামায়ের সাত ছেলেমেয়ের একজন। চারশো সত্তর টাকা মাইনের কম্পাউন্ডার বাবা সংসারের হাল সামলাতে হিমসিম। তাদের বাস তিরিশ ফুট বাই বিশফুট সাইজের স্যাঁতসেঁতে একটিমাত্র ঘরে। বীরুর মা ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সংসারের কাজে ডুবে থাকেন। সব মিলিয়ে গল্পটিতে এক চূড়ান্ত বিধুর মর্মান্তিক আবহ পরিবাহিত। সবদিক থেকে নেতির কবচে আবৃত বীরু তার পরিবারসহ পতনোন্মুখ এক খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে । অতঃ কিম ?
এইখানে গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত কবি সমালোচক টিএস এলিয়টের শরণাপন্ন হব, The critic must perform his laboratory work well. এলিয়ট Laboratory বলতে যা বুঝিয়েছেন তাহলো আবেগতাড়িত না হয়ে বুদ্ধিমত্তাকে (যা তাঁর মস্তিস্কের রসায়নাগারে জমা থাকে) প্রাধান্য দেওয়া। আমাদের আলোচ্য গল্পে অতঃপর আমরা সেভাবেই অগ্রসর হব।
‘খেলোয়াড়’ গল্পটি শুরু হয় বীরুর মাঠে ক্রীড়ারত অবস্থায়। বল নিয়ে পেনাল্টি সীমানার দিকে ধাবিত হওয়ার সময় সে বাধা পায় বিপরীত দিকের স্টপার নাসিমের কাছ থেকে। কিন্তু নাসিমের বাধাকে তুচ্ছ করে ডান পায়ের তীব্র শটে গোল দেয় বীরু। বীরু, নাসিম, পেনাল্টি সীমানা, স্টপার ইত্যাদি আপাত নিরীহ শব্দগুলোর পিছনে যে গূঢ় অভিপ্রায়, সেখানে আমাদের অন্তিমে আসতে হবে। আপাতত আমাদের কানে বাজছে হামিদ ভাইয়ের ভরা গলার ধারাবিবরণী। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র তিন-চার মিনিট আগে বীরুর দেওয়া গোলে সে সমর্থকদের করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে খেলার মাঠ।
খেলা শেষ। একমাত্র গোল করে বীরু আজ মাঠের একমাত্র বীর। কিন্তু খেলার মধ্যে কখন যে বীরুর ডানপায়ের পাতায় মৃদু ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, বীরু তা টের পায় খেলাশেষে। আজ তাকে মারেনি কেউ তবু ব্যথা। ক্লাব সেক্রেটারি রঞ্জু তাই বীরুকে রাতে ক্লাবে থেকে যেতে বলে, ‘রাতে হেভি চলবে’।
কিন্তু বীরুর রাতে ক্লাবে থাকার উপায় নেই। বাবার বারণ, ‘খেলাধুলা জিনিসটাই খারাপ। তার ওপর ক্লাবে থাকলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।’ বীরুর বাবা যথার্থই একজন মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধি। প্রচলিত মূল্যবোধ, সাতটি সন্তান এবং একটি যন্ত্রের মতো পরিশ্রমী স্ত্রী নিয়ে তার যে দুরূহ জীবন অঙ্গ, সেখানে কতগুলো সরলরৈখিক আর স্থির ধ্যানধারণা রয়েছে। এযুগের ছেলে বীরু, যে কি না উনিশশো একষট্টি সালের স্টাইলে চুল কাটে, তার সঙ্গে তার বাবার মূল্যবোধের ফারাক থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। বীরুর কাছে তার বাবা একজন ব্যর্থ মানুষ, যে কি না সারা জীবন বজলু ডাক্তারের কম্পাউন্ডার হয়ে কাটিয়ে গেল। দুই সময়কালের, দুই প্রজন্মের, দুই জন মানুষের জীবনের চলচ্ছবি লেখক এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
ম্যাক্সিম গোর্কির ‘লোয়ার ডেপথ’ নাটকের নিচুতলার মানুষ বীরুর বাবা, যার মালিকানায় রয়েছে একটি ছাতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলা যায়, ‘জরিমানা দেওয়া মাইনের মতো, বহু ছিদ্র তার।’ He who knows, does not speak. He who speaks, does not know.―Lao Tse বিখ্যাত চিনা দার্শনিক লাও ৎসে-কথিত বাক্যটির নিহিতার্থ এখানেই যে, আমাদের বোধ, চিন্তনক্রিয়া, সাধারণত সমান্তরালে থাকে না। আলোচ্য গল্পে মিলন ব্যক্তিমানুষের এই দ্বৈতসত্তা বড় নিপুণভাবে এঁকেছেন। এ গল্পে বীরু সবদিক থেকেই একটি বিধুর চরিত্র। তার খেলোয়াড় হওয়ার ইচ্ছে অথচ বাড়ীর বৈরী পরিবেশ তাকে তা হতে দেয় না। খেলায় তার গোলেই দল জেতে কিন্তু সে নিজে আহত হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়। তার বন্ধু ইউসুফ তাকে সিগারেট সাধে। বীরু সাধারণত স্মোক করে না কারণ সে জানে ‘প্লেয়ারদের সিগারেট খেতে নেই।’ তাছাড়াও সিগারেট না খাওয়ার পেছনে বীরুর একটি গহিন কারণ রয়েছে। সমগ্র গল্পটির ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে এর নিহিতার্থ। গল্পটির মূল ট্রাজেডি এখানেই ।
গল্পটি গড়তে পড়তে বিখ্যাত মার্কিন লেখক জন স্টাইনবেক-এর অনুরূপ একটি গল্প মনে পড়ে, যে গল্পের নায়ক একজন মুষ্টিযোদ্ধা। পুষ্টিকর ভরপেট খাদ্যের অভাবে খেলার প্রতিপক্ষের কাছে সে নির্মমভাবে হেরে যায়। তার হার-জনিত বেদনা বহন করতে করতে পরাজিত সেই নায়ক যখন শোক ও ক্ষুধা ভুলতে বেশ্যালয়ে যায়, সেখানে বেশ্যাকে পূর্ণ মূল্য না দিতে পাবার জন্য তার সঙ্গে আংশিক সঙ্গম করার পরিহাসেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়।
‘খেলোয়াড়’ গল্পে যে বিধুরতা, এরিস্টটলের ভাষায় তা Complex Tragedz. এই Tragedz-র একদিকে রয়েছে বীরুর খেলোয়াড় জীবনের বিড়ম্বনা, অন্যদিকে ‘সেই মেয়ে’।
ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রামে সে মেয়ের বাড়ি নয় কিন্তু তার জন্যই বীরুর কালিচরণ সাহা রোড থেকে শুরু করে সতীশ সরকার রোড হয়ে লোহারপুল বাঁয়ে রেখে ভাট্টিখানা হয়ে সোজা ডিস্টিলারি রোড, ধুপখোলা মাঠের চারদিকে ঘুরে দীননাথ সেন রোড ধরে মিলব্যারাক মাঠপর্যন্ত প্রতিদিন দৌড়। মেয়েটির পরনে ঢাকাই শাড়ি নয়, বীরু তার বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় বা কল্পনায় দেখে, তার রুমে জ্বলছে নীল ডিমলাইট। আর খুব ধীর লয়ে বাজছে ভারি সুন্দর একটা মিউজিক। কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু…
বীরুর এই ভাবনার সঙ্গে লেখক মিলন অপরূপভাবে জুড়ে দেন একটি নান্দনিক কোলাজ। ডিম লাইটের আলো যখন সঙ্গত করছে মিউজিকের সঙ্গে চোখ ও কানের সেই যুগলবন্দি। তৃতীয় একটি মাত্রা এনে দেয় বিরিয়ানির ঘ্রাণ ২৭৭৩ আস্বাদনের চতুর্বাত্রিক অনুভূতি। লেখক কেবল এ গল্পেই নয়, তাঁর অন্যান্য গল্প উপন্যাসেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের চমৎকৃতি দেখিয়েছেন। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে একে বলা হয় বর্ণিকাভঙ্গ। এ নিয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করব।
আমরা Complex Tragedz বলেছি এই কারণেই, যে বীরুর জীবনের নেতিবাচকতা বহুমাত্রিক ও জটিল। একদিকে সে ও তার পরিবার দারিদ্র্যপীড়িত, অন্যদিকে বীরুর সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক অসহজ ও শ্রদ্ধাসাধ্য নয়। অন্যদিকে খেলা ভালোবাসলেও খেলোয়াড় জীবনে যে নানা প্রতিকূলতা আসতে পারে, যেমন আজকে তার ডান পায়ের চোট (আমাদের মনে পড়বে বিখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ এইচজি ওয়েলস একদা ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়। শরীরে আঘাত লাগায় তিনি চিরতরে খেলা ছেড়ে দেন)। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বীরুর পরিবারের মা-বাবা-ভাই-বোনের সঙ্গে তার সম্পর্কের শিথিলতা। সর্বোপরি বীরুর মতো তেইশ বছরের একটি যুবকের নিজস্ব গান্ধর্ব স্বপ্ন আর কল্পনার মানসপর্যটন, গল্পের অন্তিমে যে স্বপ্নের অরুন্তুদ সমাধি হয়েছে আমরা দেখতে পাই।
বীরুর পিতা বীরুর কাছে একজন ব্যর্থ মানুষ। গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে বীরু তার পিতা সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও তার এই মানসিকতা যে একরৈখিক নয়, আমরা তার প্রমাণ পাই যখন যন্ত্রণাকাতর বীরুকে নিরাময়ের জন্য তার কম্পাউন্ডার বাবা নিজে ইঞ্জেকশন দেয়। বীরুর সে সময়কার উপলব্ধিতে পিতার প্রতি তার অনুকম্পা জেগে ওঠে। বীরু অনুভব করে, ‘বাবার মুখটা ভেঙে গেছে। দেখে আমার বুকটা ক্যামন করে।’ বীরুর এই যে পিতা সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তন, এবং তারই পাশাপাশি বীরুকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন, আর তার দিদিকে ভালো ঘরে বিয়ে দেবার সংকল্প যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত, সে জন্য বীরুর পিতার প্রতি সহমর্মী হওয়ার ঘটনাটি বীরুচরিত্রের মানবিক হয়ে ওঠার সম্ভ্রান্ত সোপান, ফলে গল্পটি নিঃসন্দেহে মহত্তর মাত্রা অর্জন করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।
পায়ের ব্যথা থেকে সেরে উঠতে দিন পাঁচেক সময় লাগে। এই পাঁচ দিন জগৎ সংসার অপরিবর্তিত থাকলেও বীরুর আহ্নিক গতি অর্থাৎ প্রতিদিনকার সাইকেল চালনা ও দৌড়ানো রুটিন মাফিক হতে পারেনি। বিপরীতক্রমে বীরুর স্বপ্নের নারীর প্রতি আগ্রহ-উদ্গ্রীব মানসিকতা চক্রবুদ্ধি হারে বাড়ছিল। পাঠক হিসেবে আমরা এই ভেবে কৌতুক বোধ করি, তেইশ বছরের বীরু তার মানসিকতা নিয়ে ধরা দিচ্ছে গল্পের লেখক ইমদাদুল হক মিলনের কাছে, যাঁর বয়স তখন একুশ!
এ পর্যন্ত গল্পটি নিয়ে আমাদের যে অবলোকন ও আলোকপাত, তাকে আমরা এখন ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যেতে চাই। গল্পটির প্রকৃত তাৎপর্য ও সেই সঙ্গে গল্পকারের প্রকৃত এষণা যার ফলে উন্মোচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ জন্য কয়েকটি তথ্য আমাদের মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত বীরু ও তার পরিবার বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। দ্বিতীয়ত বীরুর খেলার জগতের পরিচিতরা সকলে মুসলমান। এবং তৃতীয়ত, গল্পটির রচনাকাল উনিশশো ছিয়াত্তর ।
খেলোয়াড় : বিবেচনাসমূহ
গল্পটির রচনাকাল আমাদের মনোযোগ দাবি করে। ১৯৭৬ সালটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা বাংলাদেশকে পৃথিবীতে একটি সম্ভ্রান্ত আর পদবিতে তুলে ধরেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাক্সিক্ষত ফলটি সাপলুডু খেলার মতোই নিম্নগামী ও পশ্চাদায়িত করে ফেলল। ‘খেলোয়াড়’ এই দুঃসময়ের ছবিকে পরোক্ষভাবে হলেও তুলে ধরেছে মিলনের ছোটগল্পে, এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করি, যা বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও বাঙালি মুসলমান লেখকের লেখায় পাই না। মিলন তাঁর গল্পের পর গল্পে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সুখদুঃখ বেদনার কথা গভীর সহমর্মিতা এবং অন্তঃস্থ নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে এঁকেছেন। আমাদের আলোচ্য গল্পের বীরু, তার বাবা মা এবং বোনের আচরণে তারা অন্তরে ও বাইরে হিন্দু লেবাস পরে আছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বীরুদের বাড়িতে কালীমূর্তি, বীরুর ‘পানি’ না বলে ‘জল’ বলা, তাদের হিন্দু বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকা, এসব হিন্দু অনুষঙ্গ গল্পটিতে সলমাাচুমকির মতো জড়িয়ে আছে। এসব হিন্দু আবহ বনাম বীরুর প্রতিদিনের জীবনে হামিদ ভাই, নাসিম, রঞ্জু, আফসান, নয়ীম, বজলু, ইউসুফ প্রমুখের সঙ্গে তার সহবাস হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কের আসলেই যে একটি প্রকৃত চিত্র, লেখক তা গল্পের অছিলায় অনায়াসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে লেখককে আলাদা করে কুর্নিশ জানাতে হয়।
সাধারণভাবে আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে হিন্দু- মুসলমানকে গড়পরতা বিদ্বেষপূর্ণভাবে দেখানো হয়। কিন্তু তা যে প্রকৃত চিত্র নয়, তার প্রমাণ বাংলাদেশের ইতিহাসে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। বিখ্যাত কবি জসীমউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনী উৎসর্গ করেছিলেন যে মুসলমান ভদ্রলোককে, তিনি ৪৬-এর দাঙ্গায় হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানদের হাতে নিহত হন। বঙ্গবন্ধুকেও জীবনে নানা পর্যায়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে আন্দোলনে দেখা গেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী রণেশ দাশগুপ্তের যখন বয়সজনিত কলকাতায় মৃত্যু হয়, তাঁর মৃতদেহ শত প্রতিকূলতা পার করে বাংলাদেশের আর এক বরেণ্য পুরুষ জনাব হাসান ইমাম ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। তা ভাবলে আমরা নতজানু হয়ে আমরা এই বিশ্বাসে স্থির না থেকে পারি না যে, এ উপমহাদেশের প্রকৃত ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের দেয়াল তোলার ইতিহাস নয়, তার চেয়ে অধিক―সেতু রচনার ইতিহাস। বর্তমান গল্পে মিলন হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটিকে ফ্রিজিং পয়েন্টেরও নিচে থেকে পাঠকের প্রায় অজ্ঞাতসারে প্রস্ফুটিত করেছেন। লেখকের রচনাচাতুর্যের এটি এক প্রশংসনীয় দিক।
এ গল্পে বীরুর একটি প্রেমের কাহিনিও সমান্তরালভাবে লেখক বুনে দিয়েছেন। ২৩ বছরের এক সুঠাম যুবকের জীবনে প্রেম ভালোবাসার আগ্নেয়তা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রেমে সাফল্য লাভের চেয়ে ব্যর্থতার পরিমাণ জগতের সর্বযুগের ইতিহাসে প্রবল। তাই দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, লায়লি মজনুর যেমন তেমনি বাস্তবজীবনেও ব্যর্থ প্রেমের পরিমাণ জলধিপ্রতিম। তাই এরিস্টটলের মতন নন্দনতাত্ত্বিক ট্রাজেডিকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ বলেছেন। ইংরেজ কবি শেলি বলেছেন: We pine for what is not আর আমাদের ঘরের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।’
বীরু যা চেয়েছে তা পায়নি, এবং তার বিষাদগাথা অল্প আঁচড়ে মিলন এমন করে তুলে ধরেছেন, যা রোমিও জুলিয়েট, শিরি ফরহাদ, ‘নকশি কাঁথার মাঠ’-এর সাজু ও রুপার ট্রাজেডির সমধর্মী হয়ে দেখা দেয়। যে মেয়েটির জন্য বীরু বারবার রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, নীল শাড়ি পরা, নীল পাতলা আলোয় আলোকিত ঘর, গ্যারেজে নীল গাড়ি―এসব মিলিয়ে যে নীলের স্নিগ্ধতা, তারই সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আরেকটি বর্ণের আবির্ভাব ঘটান মিলন, মেয়েটির বাড়ির সামনে লাল রঙের হোন্ডা। তাতে আরোহী রাজপুত্রের মতো এক যুবক। নীল ও লালের এই যে কন্ট্রাস্ট বা স্ববিরোধিতা, ভারতীয় আলংকারিকেরা একে আখ্যায়িত করেছেন বর্ণিকাভঙ্গ বলে। রঙের মাধ্যমে চরিত্র ও ঘটনার গভীর মাত্রা বোঝাতে দেশি-বিদেশি সমস্ত লেখকেরাই রঙের আশ্রয় নেন। জীবনানন্দ যখন লেখেন, ‘নীল মৃত্যু উজাগর’ তখন নীল রঙ অসীম ও রহস্যময়তার অন্তর্গত করে দেখা হয়। বা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চোখে, ‘মৃত্যুর বরণ নীল’। ও. হেনরির বিখ্যাত গল্প The Gift of the Magi-তে আমরা দেখি, বড়দিনের আগের রাতে স্বামী জিমকে উপহার দেবার মতো স্ত্রী ডেলার সামান্য ২ ডলারও হাতে নেই। সে সময় সোফায় বসে সে ধূসর রঙের জানালার ওপারে ধূসর রঙের দেয়ালের উপরে ধূসর রঙের একটি বেড়াল দেখতে পায়। এই ধূসরতা তার ধূসর মনেরই সমরেখ।
ঠিক তেমনি বীরুর কাছেও লালরঙের হোন্ডা একটি Red alert―রক্তিম সংকেত। এছাড়াও আছে বাইক আরোহীর অঙ্গে নানা রঙের বাহার, কালো প্যান্ট, সাদার উপরে চকরাবকরা শার্ট, গলায় সোনার চেইন এবং তদুপরি হাতে সিগারেট। অর্থাৎ বীরুর পক্ষে যা ‘শ্বেত সন্ত্রাস’!
‘দেখে আমি সব ভুলে তাকিয়ে থাকি। ঘোর লেগে যায়।’ এ ঘোরলাগা পরিণত হয় নিতান্তই মনের বিনাশে। সেই বাইক-আরোহী দোতলা থেকে নেমে আসা মেয়েটিকে তার বাইকে উঠিয়ে নেয়। লেখক যেন কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরের মতোই বীরুকে দেখান, মেয়েটির পায়ে নীল চটি। কিন্তু চটিপরিহিতা মেয়েটিকে দেখে বীরু স্বগতোক্তি করতেই পারত, ‘আজ সুরবালা আমার কেহই নহে।’ বদলে বীরুর বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সামনের মাঠটিকে সে কুয়াশাময় দেখতে পায়। এ কুয়াশা বর্ণিকাভঙ্গের অব্যর্থ চমৎকৃতি হয়ে আসে। এখানেই শেষ নয় কেননা ছোটগল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ‘শেষ হয়ে না হইল শেষ।’
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. শেলির এই আপ্তবাক্যটি মিলনের বর্তমান গল্পটি সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত হতে দেখা যায়। তার প্রেমিকাকে নিয়ে যাবতীয় স্বপ্ন মুহূর্তেই আয়নার মতো খান খান হয়ে যায় মেয়েটিকে প্রেমিকের বাইকে উঠতে দেখে। আশা, ও একই সঙ্গে আশাহীনতার যুগলবন্দি বীরুর মনের ঘটাকাশে, পটাকাশে। বীরুর হৃদয়ে চলে শোক ও নন্দনের যুগপৎ মৈথুন। মেয়েটিকে দেখে বীরুর দৈবী অনুভূতি, ‘ঈশ্বর এত সুন্দর মানুষও তৈরি করেছেন পৃথিবীতে!’ বীরুর মানসিকতাকে উশকে দিতে লেখক বীরুর চোখ দিয়ে অধিকন্তু অবলোকন করাচ্ছেন, ‘তার হাসিতে আমি দেখতে পাই, এই মাত্র মনোরম আলোয় ভরে গেল পৃথিবী।’ মেয়েটির শারীর-সৌন্দর্য বীরুর চেতনাকেও বলাধান করেছে, তাই বীরুর অঙ্গেও ‘শততরঙ্গে ডেকেছে বান।’ মেয়েটির পায়ের দিকে তাকিয়ে বীরু তার পায়ে নীল স্যান্ডেল পরা দেখতে পায়। অমনি বৈষ্ণবকবিতার একটি চরণ আমাদের হৃদয়ে আছড়ে পড়ে, ‘চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি পরান সহিত মোর।’ বর্ণিকাভঙ্গের অন্য এক মাত্রা আনা হলো বীরুর দৃষ্টিতে মেয়েটির পায়ের খানিকটা উপরে উঠে আসা শাড়ির অবকাশ দিয়ে। তার গাত্রবর্ণ দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, আহ্ পায়ের রং কী তার! পাকা শারিকলার মতো। অপলক তাকিয়ে থাকি।’
বীরুর উপলব্ধিতে মেয়েটির শরীরের যে শুভ্রতা, সেই শ্বেতবর্ণ হলো সাতটি রঙের সমাহার। ‘বেনিয়াসহকলা’ যখন একটি মাত্র রঙে পরিণত হয় তখন তা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। বীরুর খুঁড়িয়ে হাঁটা, বাঁ গালের কাছে ফেঁসে যাওয়া পাঞ্জাবি, শৈশবে বার্লির সঙ্গে চালের আটা গুলে খাওয়ার যাবতীয় দীনতার নেতিমালা ভেদ করে এই যে সাত রং সপ্তসুরের মূর্ছনায় অনুভব করা, এখানেই বীরু আমাদের কাছে ‘নন্দনের এনেছে সংবাদ।’
এই আলোকিত পর্বের পরমুহূর্তেই লেখকের নিষ্ঠুর প্রকল্প, বারান্দা থেকে গেটে এসে দাঁড়ানো একটি এলসেশিয়ান কুকুর। মোটরবাইকে আরোহী সুদর্শন যুবক এবং সেই অনামা মেয়েটি (এ গল্পে ছোট-বড়-মাঝারি, সব চরিত্রেরই নাম রয়েছে কিন্তু বীরুর মানসীই একমাত্র নামহীন। মেয়েটির এই নামহীনতা লেখকেরই স্বকীয় অভিপ্রায়। পাঠকের পক্ষেও মেয়েটিকে বনলতা, নীরা বা মাধবী ভাববার অবকাশ এর মাধ্যমে তৈরি করে দেওয়া হলো) এবং খানিক দূরে বীরু। মধ্যখানে কুকুরের অশুভ ব্যারিকেড, যা এভারেস্টসদৃশ। ছুটে আসা কুকুরটিকে বীরুর কল্পনায়িকা যখন আদুরে গুডবাই জানায়, মেয়েটির হাত তখন যুবকের কোমর জড়িয়ে ধরা, বীরু তখন নিজের অজান্তেই ‘গুডবাই’ বলে ওঠে। বীরুর অবচেতনে মনে হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে আল বিদা বলার তীক্ষè, তীব্র, নিয়তিতাড়িত, অবশ্যম্ভাবী আর নির্ভুল লগ্ন উপস্থিত। আয়রনি বা পরিহাস এখানেই যে, মেয়েটির গুডবাই প্রকৃত অর্থে ছিল তার পোষা কুকুরটির সঙ্গে গতানুগতিক খুনসুটি। কিন্তু বীরু মেয়েটির ‘গুডবাই’ উচ্চারণ তার প্রতি চূড়ান্ত ঘোষণা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। আর এভাবে বীরুর মনে যে মতিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন, তাতে মেয়েটির প্রতি লেখকের নির্বিরোধ দায়মুক্তির প্রশ্রয় রয়েছে।
এর পরের দু-এক মুহূর্ত চিত্রকল্পময়। যেন চলচ্চিত্রের কামেরা প্যান করিয়ে লেখক চার-পাঁচ জন বৃদ্ধকে বীরুর পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যান। এঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত চেহারার। এঁদের হাতের লাঠিগুলোও দামি। কুকুর, রেড অ্যালার্ট-প্রতিম লাল হোন্ডা আর গুডবাইয়ের অনতিপরের এই সম্ভ্রান্ততা-নির্মাণের চমৎকৃতি আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। গল্পটি যেখানে শেষ হয়েও শেষ হয় না, তার মহাসন্ধিক্ষণ এটি, নৈরাশ্য থেকে আশার আলোয় উত্তরণের রহঃবৎ ৎবমহঁস বা মধ্যপর্ব । এই কারণেই গল্পটি ট্রাজেডি না হয়ে কেবল যে আশাবাদী হয়ে উঠেছে তাই নয়, বরং সময়ের বার্তা এনে দিয়ে অবিনাশী ও শাশ্বত সমাচার এনে দিয়েছে। বীরু কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠে স্যান্ডেল খুলে রেখে, লুঙ্গি কাছা মেরে মাঠে নেমে পড়ে। ডান পায়ে তার বেদনার তখনো পুরোপুরি উপশম হয়নি। তবু সে দৌড় শুরু করে।
বীরুর এই দৌড় শুরু করার মধ্য দিয়ে একদিকে জীবনকে তিল তিল মরণেও ভালোবাসতে শেখানো হয়েছে, অন্যদিকে উনিশশো পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু-হত্যা (পনেরই আগস্ট), জেলহত্যা (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৫), বাংলাদেশে দুঃশাসনপর্ব, এসব বিধুর ইতিহাসের জ্বালামুখ থেকে উচ্ছত ভিসুভিয়াস, ‘গ্রহরান্ডের, পাশ ফেরা’ বনাম এসব সামগ্রিক অপহ্নবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অভীপ্সাই কি আভাসিত হয়নি গল্পটিতে ?
আমাদের বিশ্বাস তা হয়েছে। বীরুর মতো সংখ্যাহীন তারুণ্যের পদাঘাতেই ফিরে আসবে অর্জিত স্বাধীনতার প্রকৃত সাফল্য। এক অস্থির ও নাজুক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে একুশ বছরের গল্পকার মিলন বীরুর মধ্য দিয়ে নিজের স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। বীরুর বাড়িতে তিন বছর ধরে পোষা টিয়া পাখিটি যেমন প্রচ্ছন্ন আশাবাদ হয়ে দেখা দেয়, যে পাখিকে বীরুর বিষণ্ন বাবাও মানবিকতা দেখিয়ে খাবার খাওয়ায়। গল্পে ছোট ছোট এই রকম ডিটেইলিং উজ্জ্বল স্বর্ণরেণুর মতো ফুটে থাকে।
গল্পটির মাহাত্ম্য রয়েছে আরও। লেখক গল্পটিতে পুরানো ঢাকার ভূগোল মেলে ধরেছেন। সেই সূত্রে আমরা কালিচরণ সাহা রোড, সতীশ সরকার রোড, ভাট্টিখানা, ডিস্টিলারি রোড, ধূপখোলা মাঠ, লোহারপুল, দীবানাথ সেন রোড, মিল ব্যারাক অনায়াসে পরিক্রমা করে আসতে পারি। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন রাঢবঙ্গ, টমাস হার্ডির যেমন ঊংংবী, মিলনের তেমনি একদিকে বিক্রমপুর ও অন্যদিকে পুরানো ঢাকা তাঁর গদ্য রচনার প্রধান ও মূল চারণভূমি। তার সঙ্গে উঠে আসে সময়ের নানান অনুষঙ্গ এবং সেই সঙ্গে মোক্ষম কিছু চিত্রকল্প, যেগুলো গল্পের প্রসাদগুণ বাড়িয়ে দেয়। বর্তমান গল্পে এ রকম দু-একটি মুক্তার দানার মরতা চিত্রকল্প কেমন ঝলসে উঠেছে তা দেখা যাক :
* বলটা চড়ুই পাখির মতো মধ্যমাঠে নাচানাচি করছে।
প্রতিপক্ষের কামালকে দেখি গুলতির মতো ছুটে আসছে।
* কানের কাছে প্যান পোন করে রাষ্ট্রীয় মশা। ৮ লোহারপুল মসজিদে তখন আজানের শব্দ।
* ফুরফুরে একটা হাওয়া আছে, পাতলা বার্লির মতো আলো ফুটো করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাগানে কত যে ফুল ফুলের মতো ফুটে আছে! বারান্দায় একটা অ্যালসেশিয়ান, গ্যারেজে একটা নীল গাড়ি।
* গেটের সামনে লাল হোন্ডায় বসে আছে রাজপুত্রের মতো এক যুবক। তার হাসিতে আমি দেখতে পাই, এইমাত্র মনোরম আলোয় ভরে গেল পৃথিবী। দূরাগত শব্দের মতো হামিদ* ভাইয়ের ভরাট গলা।
* বাংলাদেশের বিখ্যাত ক্রীড়াভাষ্যকার
খেলোয়াড় : পরিশিষ্ট বচন
লেখকের অভিপ্রায়। যেকোনও মহৎ রচনার পেছনে লেখকের থাকে বিশেষ অভিপ্রায়। একটি লেখা অভিপ্রায়হীন হলে তা শিল্পের বিচারে খারিজ হয়ে যায়। আমরা এখন গল্পটির পেছনে লেখকের অভিপ্রায়, এষণা, বার্তা ও মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব।
প্রথমেই আমরা গল্পের নায়ক বীরুর নামকরণের প্রতি আগ্রহান্বিত। একটি সার্থক রচনায় চরিত্রের নামকরণ, বা রচনার নামকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ গল্পটির নামকরণে একটি বিশেষ অভিপ্রায় রয়ে গেছে। হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবের অপর নাম মহেশ। শরৎচন্দ্রের গল্পটিতে যে প্রোটাগনিস্ট বা প্রধান চরিত্র, সেই গফুর হলো মুসলমান আর মহেশ হলো একটি বলদ, যা কি না শিব বা মহেশ বা মহাদেবের বাহন। গোরু বলদের সঙ্গে একজন মুসলমানের সাধারণ সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের। অথচ গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই, মহেশের সঙ্গে গফুরের নিবিড় মানবিক সম্পর্ক। অন্যদিকে গফুর যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ জমিদার মহেশের প্রতি নির্মম। গল্পটির নামকরণ এখানেই সার্থক ও মোক্ষম। অনুরূপভাবে বিভূতিভূষণের একটি গল্পে গ্রামের এক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলা তার অপূর্ব স্নেহে বেঁধে রাখেন গ্রামের এক যুবককে, যে তার কাছে স্নেহের ‘গোপাল’। গল্পের শেষে সেই হতদরিদ্র বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার কাফন কিনে দেয় গোপাল। গোপাল নামটির সার্থকতা ও পরিকীর্ণ ব্যঞ্জনা এখানেই যে, নামটির মধ্যে নিহিত আছে হিন্দুদের অন্য এক সেরা দেবতা, কৃষ্ণ। আমরা অতঃপর বৃদ্ধার ‘গোপাল’ ডাকটির পেছনে মূল কারিগর বিভূতিভূষণের আশ্চর্য এষণটি টের পাই। তেমনি বীরু। অর্থাৎ বীর। বীরুর গল্পটিতে বীরুর যে সামগ্রিক অবস্থিতি, প্রতিপক্ষকে গোল দেওয়া, পায়ের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করা, প্রেমের ব্যর্থতায় নিজেকে দেবদাসসুলভ হতে না দিয়ে প্রকৃত খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে আবার দৌড় শুরু করা, এরই নাম বীরত্ব তথা বীরুত্ব। গোলদাতা বীরু দলকে জেতায়, যে বীরুর কোন বুটজুতা নেই, আছে ‘এনক্লেট’।
আমরা দেখেছি, মিলনের গল্পে পুরনো ঢাকা তার অলিগলিসমেত বাঙ্গময় হয়ে ওঠে। গল্পের প্রয়োজনে এখানে লেখক পুরানো ঢাকার রাস্তাঘাট, মাঠময়দান, গলিঘুঁজিজ নিয়ে এসেছেন। গল্পটিতে এর ফলে একটি স্বতন্ত্র আবহসুর বেজে উঠেছে। গল্প-উপন্যাসের প্রয়োজনে স্থান ও কালকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা লেখককে নিতে হয়। এ জন্যই দেখি গল্পকে বাস্তবভিত্তিক করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘একরাত্রি’ গল্পকে নোয়াখালির প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিলনের গল্পটিতে পুরনো ঢাকা (যদিও বীরুর বাবার কানি দু-এক জমির সূত্রে বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে) অবধারিতভাবে কাক্সিক্ষত ছিল একাধিক কারণে। তার মধ্যে অন্যতম হলো হায়ার খেলতে গিয়ে পঞ্চাশ একশো টাকা উপার্জন অথবা তার পায়ের যন্ত্রণা দেখতে এসে রঞ্জুদার তাকে তিনশো টাকা দিয়ে সাহায্য করা। ঢাকার প্রেক্ষাপট ছাড়া এটা বাস্তবভিত্তিক হতো না। ১৯৭৬ সালের ঢাকাই এই টাকা বরাদ্দ দিতে পারত। তাছাড়া বীরুর একটি উক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, রাজধানীতে থাকার সুবাদেই তার এহেন প্রতীতি জন্মানো সম্ভব, ‘একাত্তরের পর থেকে আমাদের জেনারেশনের ছেলেদের লম্বা চুল রাখা চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কখনও রাখিনি।’ বেশভূষা ও গতরে হালফিল স্টাইল রাজধানীতেই প্রথমে দেখা দেয়, যা পরে গ্রাম ও মফস্সলে ছড়ায়। তাই গেন্ডারিয়া স্কুল, ঢাকা স্টেডিয়াম ইত্যাদি অনুষঙ্গ গল্পটিকে বাস্তবানুগ করতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। আবার ঢাকায় বাস করেও যে বিজলির আলো নয়, তাদের রাতের অন্ধকার দূর করে নির্ভেজাল হ্যারিকেন, এই বেদনার্ত সত্যটিও নিশ্বঃসিত বেদনার মতো আমাদের বিদ্ধ করে। ইলেকট্রিসিটি নেই, অতএব বীরুর ‘মা বসে বসে পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটিকে বাতাস করছেন।’ অবাক হয়ে আমরা ভাবতে বসি, ঢাকা শহর বনাম বীরুদের অর্থনৈতিক দীনতাকে এত নিপুণভাবে কী করে প্রতি পদক্ষেপে দক্ষ শল্যবিদের মতোই শবব্যবচ্ছেদ করে লেখক জীবনের প্রারম্ভেই এতখানি গভীরভাবে অঙ্কন করতে পারলেন! মহৎ লেখকের লক্ষণ এখানেই। আর এ হেন ডিটেইলিং বা অনুপুঙ্খতা আমাদের এই একটিমাত্র গল্পপাঠেই মিলনভক্ত করে তোলে।
আসলে গল্প বা উপন্যাস নির্মিত হয় বাস্তব ও কল্পনার যথার্থ মিশ্রণে। একে বাস্তবানুগ করতে লেখকের যে মনীষা, তা ব্যয়িত হয় অন্যান্য জিনিসের মতো ডিটেইলিংয়ের যথার্থ প্রয়োগে। আমরা বিভূতিভূষণের গল্প ‘যাত্রাবদল’ এ দেখি, কাহিনির সময় শীতকাল। গল্পের প্রধান চরিত্রের সহসা স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে ট্রেনযাত্রার মাঝপথে। স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রামের জমির উপর দিয়ে। শ্মশানযাত্রীদের পায়ে বিধঁছে সদ্য আমন ধান কেটে নেবার পর যে গোড়া জেগে থাকে, তার রুক্ষতায় অর্থাৎ আমন ধান কেটে নেবার বাস্তবতায় গল্পটিকে মুড়ে ফেলা হলো। আবার সদ্য বিপত্নিক ব্যক্তিটি স্ত্রীর শবদাহ শেষে যখন অচেনা এক বাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রিত তার শিশুপুত্রটির কাছে যায়, তখন সে দেখে, শিশুটি আপন মনে একটি কমলালেবু খাচ্ছে। কমলালেবু এখানে শীতকালের অনবদ্য ডিটেইলিং হিসেবে এসে গল্পটিকে বাস্তবতাদানে ভূমিকা নিয়েছে।
মিলনের গল্পটিতেও দেখি, খেলার পরে ব্যথাহত বীরু তার বন্ধু নয়নকে সাইকেলটা গস্ত করে দিয়ে নিজে তার মোজা ও জার্সি বহন করে হাঁটতে থাকে। মোজা ও জার্সি যে ঘামে ভেজা ছিল, লেখক তা উল্লেখ করতে ভোলেন না। ভেজা, কেননা দীর্ঘক্ষণের খেলা সেগুলো স্বেদাক্ত করবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা কি চমৎকার ডিটেইলিংয়ের উদাহরণ নয় ?
প্রসঙ্গত এখানে প্রতিতুলনা হিসাবে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা The Solitary Reaper না এনে পারছি না। কবিতাটিতে একটি মেয়ে ফসল কাটছে আর একই সঙ্গে Melancholy Strains শোকগীতি গাইছে। আপাতভাবে ফসল কাটার সঙ্গে যুক্ত হতে পারত মেয়েটির কণ্ঠে উচ্চারিত কোনও আনন্দসংগীত। কিন্তু মেয়েটির কণ্ঠে মর্সিয়ার এই কাজরিগাথা কেন? আমরা আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করলে এহেন রুদালির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। মেয়েটি পাকা ফসল কাটতে গিয়ে হৃদয়ঙ্গম করছে যে তার জীবনের লাবণ্য ও সুধাও একদিন এই পাকা ফসলের মতোই পরিণতি পাবে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ফসল তোলার সময় চিরায়ত নবান্নের গান নয়, মেয়েটির কণ্ঠে উঠে এল Swan’s Song অথবা হংসপাদিকার গান, বৈষ্ণবকবিদের রচনায় ‘প্রেম বৈচিত্য’ নামে যা খ্যাত।
শেষকথা
গল্পটির বিশদ আলোচনার মাধ্যমে আমরা এমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ইমদাদুল হক মিলনের এ খেলোয়াড়ও বাংলা সাহিত্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা হিসেবে তাঁর মেধা অনুযায়ী যথার্থ স্বীকৃতি পায়নি। তাহলে কি বর্তমান সমালোচকের গল্পটি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও ব্যাখ্যা অতিরঞ্জিত এবং ভ্রান্ত ? তা যে নয়, গল্পটির চুলচেরা বিশ্লেষণে তা পরিস্ফুট হয়েছে নিঃসন্দেহে এবং সুনিশ্চিতভাবে। তবু গল্পটি উপেক্ষিত থেকে গেল কেন ?
আসলে এর পেছনে কয়েকটি কারণ সক্রিয়।
প্রথমত, কোনও সৃজনশীল লেখা বা যেকোনও শিল্পকর্ম, যেমন সংগীত, চিত্রকর্ম, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সমালোচকদের কাছ থেকে মূল্যায়ন দাবি করে। কেবল একজন সমালোচক নয়, কোনও একটি শিল্পকর্ম একাধিক সমালোচক তাঁদের বৈদগ্ধ্য ও অর্জিত প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিচার করে থাকেবেন। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, চেখভ অথবা লু শুন-এর রচনা যুগে যুগে সমালোচিত হতে হতে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অপরিত্যাজ্য হয়ে উঠেছে। সমালোচকের দৃষ্টিপাতে বহু লেখকের রচনা অপরিহার্য পাঠ হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখি, জগদীশ গুপ্ত বা সোমেন চন্দ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শহীদুল জহিরের লেখা মূলত সমালোচকদের হাত ধরেই পাঠকের কাছে অন্তিমে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য যখন রচিত হত, যেমন বাণভট্টের ‘কাদম্বরী,’ মাঘ-রচিত ‘শিশুপালবধ,’ সেই গ্রন্থগুলোর সামগ্রিক আলোচনার প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে, হ্যাঁ, বিস্ময়কর হলেও, প্রতিটি শব্দকে বিশ্লেষণ করে সেই শব্দ বা গোটা বাক্যের গুণ বিচার করা হতো। একে বলা হতো ‘টীকা’। যে গ্রন্থের টীকাকার যত বেশি, স্বাভাবিকভাবেই সে গ্রন্থটি তত বেশি সাহিত্যগুণসম্পন্ন বলে অবধারিতভাবেই বিবেচিত হতো। এভাবে সুবিপুল বেদের ভাষ্য লেখেন সায়ন, মহাভারতের ভাষ্য বা টীকা লেখেন নীলকণ্ঠ। কালিদাসের মেঘদূত, যা সমগ্র বিশ্বে আদৃত ও অগণিত ভাষায় অনুদিত, তার টীকা লেখা হয়েছে শতাধিক ভাষ্যকারের দ্বারা।
কিন্তু আজ পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের হার বহুগুণ বেড়ে গেলেও সাহিত্য-সমালোচকের দীনতা আমাদের বেদনাহত করে। সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা হয় দেদার কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ধারা ক্রমশ ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বহু প্রতিভাধর ব্যক্তিই সাহিত্য সমালোচনাও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই ধারা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল কিন্তু এ যুগে এসে সাহিত্য বহুলাংশে হয়ে পড়েছে পৃষ্ঠপোষকতানির্ভর।
তাছাড়া সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আর একটি দুঃখজনক ঘটনা হলো, নতুন লেখকদের সম্পর্কে সম্পাদকদের অমনোযোগ, উপেক্ষা আর তুষ্ণীস্তাব ও অবমূল্যায়ন। এটা অবশ্য আদিতেও ছিল, যে জন্য কালিদাস তাঁর ‘শকুন্তলা’ নাটকের একটি চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, কোনও কিছু নতুন হলেই তা অপাঙ্ক্তেয় হয় না। যাঁরা যথার্থ রসগ্রাহী তাঁরা নতুনকে যথার্থ বিচারের মাপকাঠিতে ফেলেই মূল্যায়ন করে থাকেন।
আজকে ইমাদুল হক মিলন বাংলা ভাষার জননন্দিত কথাকার। তাঁর লেখা যেমন দেশে বিদেশে পঠিত হয় তেমনি তাঁর রচিত কাহিনি নিয়ে নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সাহিত্যরচনার জন্য দেশি-বিদেশি বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর যথার্থ স্থান কোথায়, কোন কোন দিক থেকে তাঁর রচনা বিশিষ্ট ও অনন্য, তার বিশ্লেষণ অদ্যাপি অপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে।

‘খেলোয়াড়’ গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা কথাকার মিলনের রচনাধারার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের প্রয়াস নিলাম । আমরা একে একে তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করব, মিলন সার্বিকভাবে একজন গদ্যশিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কোন অবস্থানে রয়েছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হতে চলেছে। এই সময়ে তাঁর রচনার মূল্যায়নের যথার্থ সুযোগ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। ইমদাদুল হকের ছোটগল্প : প্রবণতাসমূহ।
ইমদাদুল হক কুড়ি একুশ বছর বয়স থেকেই ছোটগল্পরচয়িতা হিসেবে তাঁর পরিচয়ের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প ‘বন্ধু’ রচিত হয়েছিল। আমাদের মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথের ‘করুণা’, শরৎচন্দ্রের দেবদাস এবং মানিক বদ্যোপাধ্যায়ের অতসীমামী ঐ বয়সেইর রচনা। মিলনের প্রথম উপন্যাস যাবজ্জীবন লেখা হয় তাঁর মাত্র একুশ বছর বয়সে। অতএব বলা চলে, সাহিত্যের অঙ্গনে মিলনের আত্মপ্রকাশ বেশ অল্প বয়সেই।
মিলনের জন্ম তখনকার পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাসের এক বেপথু সময়ে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বুড়ো খোকার ভারত ভেঙে দুটি রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে নিয়ে এল ছিন্নমস্তা দেশভাগ, স্বাধীনতা। সবচেয়ে তাজ্জব, উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই অংশ কেটে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো, সেই রাষ্ট্রের এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের দূরত্ব দেড় হাজার কিলোমিটার! গোড়া থেকেই পাকিস্তান ছিল এক আজগুবি রাষ্ট্র। ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ।
তেতো ও বিস্বাদপূর্ণ হয়ে উঠল অচিরেই। শুরু হলো পশ্চিমাদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতার আসা এবং অচিরেই সেই সরকারকে পাকিস্তানি শোষকদের নাকচ করে দেওয়া, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের মার্শাল ল জারি, এসব টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন পূর্ববঙ্গ অতিবাহিত করছিল, ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে মিলনের জন্ম। মিলনের শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো কেটেছে বাংলাদেশের উত্তাল রাজনীতির আবর্তে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের ভয়াবহ বন্যা ও নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ Operation Searchlight তথা ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশে গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ, ও অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মলাভ, ইতিহাসের একের পর এক যাত্রাপথের যুগপৎ আনন্দগান ও ব্যথার দান অতিক্রম করতে করতে বাংলাদেশ নামক একটি স্বপ্নের ভূখণ্ড নির্মিত হয়েছিল মিলনের কৈশোর ও তারুণ্যকাল জুড়ে।
এরপরে ঘটল ইতিহাসের ছন্দপতন। ইতিহাসের দেবী ক্লিও বড় নিষ্ঠুর ও ছলনাময়ী। তাই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিকে তাঁর স্বপ্ন আর সাধ নিয়ে যখন তিলে তিলে গড়ে তুলছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সেই সময়ে নেমে এল ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বছর না ঘুরতেই জাতির পিতার রক্তাক্তদেহ ভূলুণ্ঠিত হলো বিপথগামী সামরিক নেতাদের হঠকারিতায়। বঙ্গবন্ধুহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম রাজনৈতিক ট্রাজেডি। কেননা জুলিয়াস সিজার, আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ নিহত হয়েছিলেন এককভাবে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু নিহত হন স্ত্রী পুত্র-পুত্রবধূসহ আরও পরিজনসমেত। এর ফলে কালের চিরচঞ্চল গতি ব্যাহত হলো দীর্ঘদিন।
মিলন এই দুঃসময়ের ও দুঃশাসনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন তাঁর জীবন আর জাহান্নামের আগুনে বসে পুষ্পের হাসির মতই ফুটিয়ে তুলেছেন একটির পর একটি গল্পের পারিজাতকুসুম।
মিলন ছোটদের জন্য লেখা দিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। তিনিই সম্ভবত একজন ব্যতিক্রমী লেখক, যিনি কখনও কবিতাচর্চা করেননি, যেমন তাঁর অগ্রজ কবি রফিক আজাদ নিষ্ঠাসহকারে কেবল কবিতাই লিখেছিলেন, কবিতাচর্চা- ব্রতপালনের অনুশীলনে গদ্যরচনাকে নিতান্ত বিঘ্ন বিবেচনা করেছিলেন বলে।
ইমদাদুল হক মিলনের গল্পাবলি পাঠ করতে গিয়ে তাঁর রচনাশৈলী ও গাল্পিকসত্তার পরিচয় মেলে। আমরা মিলনের গল্পগ্রন্থ ‘দেশভাগের পর’ নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে সেগুলো বিশ্লেষণ করায় প্রয়াসী হব।
লেখক : কবি, কথাশিল্পী, সাহিত্যবিশ্লেষক