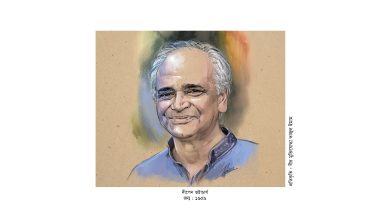ছোটগল্পের দিকনির্দেশক : হাসান আজিজুল হক : আব্দুল বারী
জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি : হাসান আজিজুল হক
হাসান আজিজুল হক বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় এক মহীরুহ। বাংলাদেশের ছোটগল্পের দিকনির্দেশকও বলা যায়। ১৯৬০ সালে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত ‘সমকাল’ পত্রিকায় ‘শকুন’ নামক সিগনেচার গল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর সজীব উপস্থিতি। অবশ্য তিনি কৈশোর জীবন থেকেই লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। মহারাণী কাশীশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলে রাজা সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর আগমন উপলক্ষে একটি সংবর্ধনা পত্র রচনা ও পাঠ করেন (সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী হলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর বংশধর)। রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। মুর্শিদাবাদ তো বটেই পাশের বর্ধমান জেলাতেও বেশকিছু বিদ্যালয় নিজ নামে এবং রাণীর নামে স্থাপন করে গেছেন। বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) মহারাণী কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় ও রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় নামে দুটি বিদ্যালয় আছে। বেলডাঙ্গাতে (মুর্শিদাবাদ) কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দ সুন্দরী হাই স্কুল রাজা মনীন্দ্র চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা। তবে বহরমপুরের মহারাণী কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় এবং লেখক যে মহারাণী কাশীশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন দুটি আলাদা)।
সূচনা লগ্নে ১৯৫৬ সালে নাসির উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত ‘মুকুল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘মাটি ও মানুষ’ এবং বিএল কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় ‘লাঠি’ ও অন্য একটি কলেজ বার্ষিকীতে ‘পাষাণ-বেদী’ নামক একটি গল্প। এগুলো বাদ দিয়ে ১৯৬০ সাল থেকে ধরলে দীর্ঘ একষট্টি বছর একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন আর বাংলা সাহিত্যকে তাঁর অনবদ্য চিন্তার ফসল উপহার দিয়েছেন।
ছয়ের দশক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবন নির্মাণের সময় পর্ব। এই পর্বে কিছু লেখক যে ধারা সাহিত্যে বেঁধে দিয়েছিলেন আজও সেই ধারা বহমান। বলা যায়, সেই রাজপথেই তরুণেরা তাদের বিজয়রথ চালিয়ে চলেছেন। সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ বা নতুন দিগন্তের উন্মোচন খুব বেশি চোখে পড়ে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের নবযুগের সূচনা লগ্নের পথ দেখিয়েছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কায়েস আহমেদ, সুব্রত বড়ুয়া, সেলিনা হোসেন, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, দিলওয়ার হোসেন, রশিদ হায়দার, রিজিয়া রহমান প্রমুখ। ছয় দশকের বিশিষ্ট কথাকার হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পের নির্মাণকৌশল নিয়ে কিছু আলোচনা রাখব।
হাসান আজিজুল হকের জন্ম ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে। যেটা মধ্য রাঢ় বলা যায়। মধ্য রাঢ় থেকে তিনি ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে পড়াশোনার জন্য যান। পরে বাংলাদেশে স্থিত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বাকি জীবন এখানেই কাটিয়ে দেন।
রাঢ় থেকে যে জীবন তিনি অন্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন সারা জীবন তার থেকে নব নব সৃষ্টি তিনি করে গেছেন। দেখা জীবন, জগত, প্রকৃতি এই ছিল লেখার মূল উপজীব্য। জায়গা জমি মানুষ ছিল তাঁর গল্পের মূল বিষয়। তিনি সারা জীবন ধরে তাঁর গল্পে মানুষকে খুঁজেছেন, মানুষের জীবন খুঁজেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন মানুষ দেখব, মানুষের গ্লানি দেখব না, তা হয় না। আসলে সমগ্র মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। আর তাঁর দেখার চোখ ছিল আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর গল্প লেখার কৌশল ছিল আলাদা। তাঁর গল্পে সৌন্দর্যবোধের চেয়ে বাস্তব বোধ, কঠোরতা, জীবনের গ্লানিময় দিকের উপস্থিতি অনেক বেশি। উপন্যাস, গল্পে জীবনের এই কর্কশ দিক উপস্থাপন করেছেন।
আসলে তাঁর গল্প লেখার সময় কালকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলেই বুঝতে পারব কেন তাঁর গল্পের নির্মাণ এমন। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প বা উপন্যাস একরৈখিক নয়, বহু কৌণিক। বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে তিনি সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, ধর্ম, জীবন, প্রকৃতি, মানুষকে দেখেছেন। আর তাদের নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে তাঁর জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে ভাঙন, অর্থনৈতিক মন্দা, দারিদ্র্য― তিনি সেই ছোট বয়সে চোখ মেলেই দেখতে পেয়েছিলেন। ৫২’র ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশের জন্ম দিচ্ছে। সেই ৫২ পরবর্তীসময়ে তিনি বাংলাদেশে পা রেখেছেন (১৯৫৪)। সে এক এক উত্তাল সময়। বাংলাদেশ আধা-ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি চায়। মানুষ নির্মাণ করতে চাই নিজেদের স্বদেশ। স্বদেশের স্বপ্নমাখা চোখ। সেই উত্তাল সময়ে তিনি ব্রজলাল কলেজে পড়তে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন ছাত্র আন্দোলনে। ব্যক্তিজীবনে রাজনীতি করতে গিয়ে খানসেনাদের (পাঞ্জাবি) হাতে তিনি একটি স্টেশনে মারও খেয়েছিলেন। হয়তো সেদিন পাঞ্জাবি পুলিশের দল লেখককে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারত কিন্তু দেয়নি। সে যেমন হাসান আজিজুল হকের সৌভাগ্য তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও সৌভাগ্য বলা যায়।

তাঁর চোখে এক নতুন দেশের স্বপ্ন, নতুন ভোরের স্বপ্ন। ফলে লেখকের জীবন গড়ে উঠছে এক কঠোর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। ভাঙাচোরা বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করে এক নবতর রূপে দেখতে চাইছেন। সে সময় তিনি খুব কাছ থেকে দেখলেন ধর্মকে হাতিয়ার করে কিভাবে একশ্রেণির মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। শুধু ধর্মকে শিখণ্ডী করে তারা মানুষ মারছে। একটা দেশকে শোষণ করছে। তার অর্থনীতিকে শুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই উত্তাল সময়, অপমানিত মানবতা তাঁর কলমের উঠে এসেছে। ফলে তাঁর গল্পে অন্য মাত্রা যোগ হয়েছে। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে এক অন্য জীবন, এক অন্য জগত। তিনি যে গল্পের (জননী, খনন, তৃষ্ণা, মন তার শঙ্খিনী, মা মেয়ের সংসার, হেমাপ্যাথি অ্যালাপ্যাথি, জীবন ঘষে আগুন, পাতালে হাসপাতালে, নামহীন গোত্রহীন, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, খোঁজ, আমৃত্যু আজীবন, পরবাস, শকুন প্রভৃতি) চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন আমরা যদি সে চরিত্রগুলো একটু একটু করে ভাঙি তাহলে দেখব সেসব চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে অবহেলিত বাংলাদেশ, বিপন্ন সময়, ক্ষয়িষ্ণু বাংলাদেশের কঙ্কাল।
তিনি চাইতেন সাহিত্যে উঠে আসুক একটা গোটা মানুষ। সেখানে স্বপ্ন থাক, স্বপ্নভঙ্গের আর্তনাদ থাক। সবকিছু নিয়ে সমগ্র মানুষকে তিনি সাহিত্যে তুলে আনতে চেয়েছেন।
আমরা তাঁর গল্পে নারী চরিত্রের যে উপস্থিতি দেখতে পাই তা অন্যমাত্রার নারী। তাঁর ‘মা মেয়ের সংসার’ ‘জননী’ কিংবা ‘বিধবাদের কথা’ গল্পগুলিতে নারী চরিত্র ভিন্নমাত্রায় উপস্থিত। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন প্রেম তাঁর জীবনে এসেছিল একবার। নবম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে এবং পরবর্তীকালে তিনিই গৃহিণী। ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই মহিলাই সঙ্গ দিয়ে গেছেন কথাকারকে। আর অন্য নারীর প্রতি তাঁর তেমন আসক্তি আমরা খুঁজে পাইনি।
তিনি বলেছেন জীবনের চাপে প্রেম বিষয়টি তাঁর গল্পে কম এসেছে। এখানে জীবনের চাপ বলতে রূঢ় বাস্তবকে বুঝিয়েছেন। তা শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনে নয় সমাজ জীবনেও। আসলে তাঁর গল্প উপন্যাসে নারী বলতে মা-খালা- ফুফুদের যে মহীয়সী রূপ সেটাকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাদের চোখ দিয়েই জীবন, জগত, সংসার দেখিয়েছেন। তাদের চোখের জিজ্ঞাসা গুলি ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের পাতায়। আর দেখেছেন নারী-জীবনের অবক্ষয়। ‘মা মেয়ের সংসার’ গল্পে মেয়েটি বাঘ খুঁজতে চেয়েছে। কারণ তার উপর যে অত্যাচার হয়েছে, যে গ্লানি তার জীবনে এসেছে তার থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। এই অনুভূতি জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার তীব্র যন্ত্রণাকে বাঘ খোঁজার প্রতীকে গল্পকার উপস্থাপিত করেছেন। নারী জীবনের এমন হাহাকার আরও অনেক গল্পে ফুটে উঠতে দেখা যায়। ‘বিধবাদের কথা’ তার অন্যতম।
ব্যক্তি হাসান আজিজুল হককে বুঝতে হলে তার ‘উঁকি দিয়ে দিগন্ত’, ‘চালচিত্রের খুঁটিনাটি’, ‘স্মৃতি কহন’ গ্রন্থগুলো পাঠ করতে হয়। এই গ্রন্থগুলোতে যাপিত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। রাঢ়বঙ্গের যে জীবন কথা তা নিয়ে তিনি বেশকিছু গল্পে লিখেছেন (জীবন ঘষে আগুন)। দেশভাগ, মানুষের মহাপ্রস্থান, জীবনের এক অনিশ্চিত যাত্রা বারবার তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। গল্পটি নিয়ে প্রচুর কথা লেখা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ১০০ বছরে যা লেখা হয়েছে সেই সমস্ত গল্পের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ দশটি গল্প বেছে নিতে বললে ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ তাতে অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারে। দেখা ঘটনাকে দীর্ঘদিন তিনি অন্তরে লালন করে তার থেকে শিল্পের নির্যাস রূপে গল্পটি তিনি লিখেছেন। দেশভাগ পরবর্তী যন্ত্রণার বিভিন্ন স্তরগুলো দীর্ঘদিন পরে গল্পের আকারে ফুটিয়ে তোলেন। গল্পটি তৎক্ষণাৎ লিখলে হয়তো এমন শিল্পসম্মত সাহিত্য হয়ে উঠত কি না বলা কঠিন। (১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ মাঝে প্রায় ১৮-২০ বছরের ব্যবধান)। আসলে হাসান আজিজুল হকের লেখার ধরনটাই এমন। তৎক্ষণাৎ কোনও ঘটনা লিখে ফেলা নয়। সময় ধরে, সময় নিয়ে সেই ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে শিল্পসম্মত উপস্থাপন করা। এটা হাসান আজিজুল হকের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার ছোট গল্পে প্রচুর ছোট ছোট কাজ থাকে, যেগুলো পাঠককে ভাবায়। গল্পের একটানা বর্ণনা নয়, সেই বর্ণনার মাঝে সামান্য ছোট ছোট আঁচড়ে তাকে আরও বর্ণময় আরও ভাব গভীরতায় পৌঁছে দেওয়া। সকলের পক্ষে এমন সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব নয়। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পে খালের পাড়ে রেড়িওর গান বন্ধ করা কথাটি না বলে কণিকার গলা টিপে দেওয়া এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন যা অন্যমাত্রা যোগায়। গল্পটির আলোচনা থাক। ‘শকুন’ গল্পটি নিয়ে কিছু কথা লিখি।
‘শকুন’ গল্পটির সূচনা হয়েছে এক প্রদোষকালে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পোড়োবাড়ির প্রাঙ্গণ। সেখানে কিছু ছেলে খেলাধুলা করছে। হঠাৎ বড় তেঁতুল গাছের মাথা থেকে একটা সজিব অন্ধকার নেমে আসে। ছুটে যায়। এই যে একতাল সজীব অন্ধকার এই শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সময়কাল অর্থাৎ অবহেলিত বাংলাদেশকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। পোড়ো বাড়ি। বিভাগোত্তর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য পরিবার আশ্রয় ফেলে ছুটে গেছে জীবনের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। তাদের ফেলে যাওয়া বাড়ি হয়ে ওঠে পোড়া বাড়ি। এ যেন বাংলাদেশের এক অন্যরূপ। বাংলাদেশ যেন তখন ওয়েস্টল্যান্ড। অন্য দিক থেকেও মানুষ এসেছে। বাংলাদেশে নিরন্তর মানুষের যাত্রা চলছে। এই অবহেললিত সময় পর্বটা পোড়ো বাড়ি আর সজীব আঁধারের উপমায় অদ্ভুত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। শকুন চিরদিন মৃত্যুর প্রতীক। অশুভর প্রতীক।
শকুনটি নিয়ে ছেলেরা খেলতে শুরু করে। এটা নিছক খেলা নয়। আসলে মনের মধ্যে জমে থাকা দীর্ঘদিনের রাগ দুঃখ বেদনা, কিছুটা হতাশার বহিঃপ্রকাশ। শকুনিটি ধরে কী করবি? ছেলেরা বলেছে কিছু করব না। খেলব। এই যে খেলতে চাওয়া এটা নিছক খেলতে চাওয়া নয়। কিছুটা যেন প্রতিহিংসা, প্রতিবাদ চরিতার্থ করা। পালক ছিঁড়ে নেওয়ার মধ্যেই তার প্রকাশ। ছেলেরা শকুনটি কখনও মোড়ল শকুন, কখনও মোল্লা শকুনি বলে সম্বোধন করেছে। মোল্লা, মোড়ল শাসিত বাংলার সমাজ এই গল্পের মধ্যে এক অপূর্ব প্রতীকে ফুটে উঠছে। সমাজের অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিকগুলো চিহ্নিত করছেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়, ইঙ্গিতে। মোল্লা শাসিত সমাজ বলতে পশ্চিম পাকিস্তানি মানুষদের যে নিরন্তর অত্যাচার তার কথা বলতে চেয়েছেন। শকুনটি কখনও হয়ে উঠছে সুদখোর অঘোর বোষ্টমী। আবার কখনও অত্যাচারী হামবুর বাপ। একই প্রাণী তার কত রূপ, কতভাবে প্রতীকায়িত হচ্ছে। আর সবগুলোতেই ফুটে উঠছে অবহেলিত, অত্যাচারিত বাংলাদেশ। এ এক অদ্ভুত গল্প। গল্পের শেষে শকুনটি মারা গেছে। তার পাশে পড়ে আছে উগরানো কিছু গলা মাংস আর একটি সদ্যোজাত মানব সন্তান। এক অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখি। একটা সদ্যোজাত মানব সন্তান তার পাশে মৃত্যুদূত শকুনি। মৃত্যুর আগে শকুনটি ঠুকরিয়ে দিয়েছে মানব সন্তানের পেট। সন্তানটি কাদু শেখের বিধবা বোনের অবৈধ সন্তান।
আসলে গল্পটিতে তিনি সময়কে, সময়ের গ্রন্থিগুলো, বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের অবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন। একুশ বছরের এক তরুণ এই গল্পে যে অসম্ভব পরিণতি দেখিয়েছিলেন তা পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছিল। অচিরেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে একটা সুনিশ্চিত স্থান হতে চলেছে তার আভাস সাহিত্য পাঠকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। কখনওই তিনি নিছক গল্প বলে যাননি। গল্পের ভেতর ভেতর নির্মাণ কাজও চালিয়ে গেছেন। তাই তাঁর গল্পের সংখ্যা কম। সৃষ্টির বিপুলতা নেই (বোধহয় মাত্র নয় বা দশটি গল্পগ্রন্থ)। স্বল্প সৃষ্টি যেন মণি-মাণিক্যের মত উজ্জ্বল।
হাসান আজিজুল হকের এক একটি গল্প একেক রকম। তার ভাষা ও নির্মাণশৈলীও ভিন্ন। একটি গল্পের গদ্যের সঙ্গে অন্য গল্পের গদ্যের অনেক ফারাক লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। শব্দ নিয়ে অসম্ভব কাজ করতে পারতেন। জীবনানন্দ দাশ যেমন একই শব্দ একই কবিতায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে পাঠকের মনে এক অপূর্ব আবেশ তৈরি করতে পারতেন, এক অপূর্ব চিত্রকল্প নির্মাণ করতে পারতেন, আজিজুল সাহেবও তেমনি শব্দগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে গল্পের এক অপূর্ব সৌকর্য নির্মাণ করতে পারতেন। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ বা ‘শকুন’ গল্পের যে ভাষা ‘হেমাপ্যাথি অ্যালাপ্যাথি’ গল্পের ভাষা ঠিক তেমনটি নয়। এ গল্পের ভাষা সরস, চলমান। পাঠক মনে এক অদ্ভুত চঞ্চলতা, একটা আবেগি স্রোত তৈরি করে। হোঁচট খেতে হয় না। বরঞ্চ এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়। ভাবনার জটিলতার চেয়ে সরল অনুভূতিটাই বেশি। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ বা ‘শকুন’ গল্পের ভাষা অনেক সুচিন্তিতভাবে নির্মাণ করা। প্রতিটি শব্দ, উপমা কথাকারের গভীর চিন্তার ফসল। যেন টেরাকোটার কাজ। প্রতিটা জায়গা জ্যামিতিক মাপে সূক্ষ্মভাবে নির্মাণ করা।
লেখক : কথাসাহিত্যিক
কলকাতা থেকে