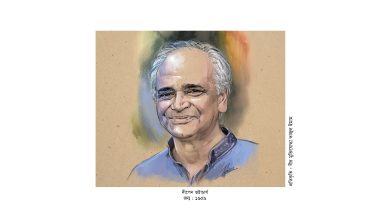এগারোতম পর্ব
মুকুলের কেতাবি নাম আইয়ুব উদ্দিন চৌধুরী। এই চৌধুরী সাহেব আমাকে সম্পাদক বানিয়ে দিলেন। বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসের কথা। দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। দেশের সর্বত্র বইছে আনন্দের বন্যা। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে আগেই গ্রামে চলে গিয়েছিল মুকুলদের পরিবার। লক্ষ্মীবাজারের মুখে এক রুমের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রেস করেছেন মুকুলের বাবা। বড়ছেলের নামে প্রেসের নাম ‘মুকুল প্রেস’। একটা ট্র্যাডেল মেশিন। একজন মেশিন ম্যান প্লাস কম্পোজিটার। ছোট ছোট জব ওয়ার্ক করা হয় প্রেসে। যেমন ভিজিটিং কার্ড, বিয়ের কার্ড, প্যাড ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর মুকুলদের পরিবার আর ঢাকায় আসেনি। মুকুলদের আলাদা কোনও বাসাও নেই তখন। মুকুলকে নিয়ে ওর বাবা থাকেন প্রেসেই। প্রেসের পিছন দিকটায় একটি চৌকি পাতা হয়েছে। হাত দুয়েক জায়গা আছে চলাফেরা করার। সামনের দিক থেকে যাতে চোখে না পড়ে সেজন্য একটা বেড়া দেওয়া হয়েছে। ওখানে বাপ ছেলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, মুকুলের পড়ার ব্যবস্থা। একটা স্টোভে কখনও মুকুল নিজে কখনও তার বাবা রান্না করেন। মুকুলের বাবা গ্রামের বাড়িতে গেলে প্রতিরাতেই আমি গিয়ে মুকুলের সঙ্গে থাকতাম। স্বাধীনতার পরের প্রথম ব্যাচে আমরা এসএসসি পরীক্ষা দেব। তখনও পরীক্ষার ডেট ঘোষণা করা হয়নি। তবে আমাদের ব্যাচের কয়েক বন্ধু আমরা ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত। রেজাল্ট সবসময় আমরা ভালো করতাম।
প্রেসে ঢোকার মুখে পশ্চিম পাশের দেয়ালের সঙ্গে ছোট্ট টেবিলে মুকুলের বাবার বসার ব্যবস্থা। ওই আমলের কালো ফোন আছে। বাবা বাড়িতে গেলে মুকুল চেয়ারটায় বসত। আমরা বন্ধুরা আড্ডা দিতে গিয়েও বসতাম। কেটলিতে করে মুকুলদের একমাত্র কর্মচারিটি দুআনা-চার আনার চা আনত। তাই ভাগ করে খেতাম। কত এমন রাত কেটেছে, আমার খাওয়া হয়নি। গত অক্টোবরে আব্বা মারা গেছেন। সংসার প্রায় অচল। পেটের খিদে নিয়ে মুকুলদের প্রেসে ঘুমাতে গেছি। আমার মুখ দেখে মুকুল বুঝেছে রাতের খাওয়া হয়নি। স্টোভ জ্বেলে ভাত বসিয়েছে। ভাতের মধ্যেই চারটা আলু আর দুটো ডিম সিদ্ধ করতে দিয়েছে। হয়তো দুপুরের একটু ডাল ছিল। ওই দিয়ে আমরা দুজন গভীর আনন্দ নিয়ে রাতের খাবার সারলাম। তারপর দুই বন্ধুর হাসি গল্পে রাত ধীরে ধীরে গভীর হলো। ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনেই।
মুকুল অত্যন্ত দুষ্টু বুদ্ধির ছেলে। সারাক্ষণ নানা রকম দুষ্টুমি নিয়ে আছে। কথায় চালচলনে কাজে দুষ্টের শিরোমণি। কথায় কথায় অদ্ভুত সব শব্দ ব্যবহার করত। যেমন : ‘ইসটিকুলুসটু’। যেসব শব্দের কোনও মানে হয় না। কোথায় যে পেত ওসব শব্দ বা কেমন করে যে বানাতো! মুকুল ছাড়া কেউ জানে না। সেই জীবনের বহু বহু বছর পর বিটিভিতে নাটক করতে গেছি। প্রডিওসার ফখরুল আবেদিন দুলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। মুকুলের চেয়ে শখানেক গুণ বেশি দুষ্টু দুলাল। নির্বিকারভাবে এমন সব ঠাট্টা মশকরা আর মজার মজার কথা বলত, তার কোনও তুলনা হয় না। দুলালের মুখে ‘ইসটিকুলুসটি’ শব্দটা শুনলাম। ওটা সে যৌনকর্ম অর্থে ব্যবহার করত। তো গ্রামে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ইনফরমার হিসেবে কাজ করেছে মুকুল। ওর খুব প্রিয়বন্ধু ছিল বজলু। সাতাত্তর সালে বজলুর সঙ্গে সে জার্মানিতে গিয়েছিল। জীবন কাটিয়ে দিল সে দেশেই।
মুকুল এদিক-ওদিক খুব ফোন করত। আমরা বন্ধুরাও মুকুলের বাবা না থাকলে গিয়ে ফোন করি। ফোনে বান্ধবী জোগাড়ের চেষ্টা করি। দুয়েকজন বান্ধবী হয়েছেও। সময় বুঝে পালিয়ে পালিয়ে তাদের ফোন করতে হয়। মুকুল এ ব্যাপারে দরাজ দিল। ফোন করতে খুবই উৎসাহ দেয়। মাস শেষের বিল দেখে ওর বাবা বুঝে গেলেন ফোনটা মুকুল একটু বেশিই ব্যবহার করছে। প্রেসের বাইরে গেলেই ফোনে তালা লাগিয়ে যান। চাবি তাঁর কাছে। গ্রামের বাড়িতে গেলেও একই কাজ করেন। মুকুল কেমন কেমন করে যেন ওই তালা বন্ধ ফোনেই রিসিভারটা হাতে নিয়ে ক্র্যাডেলে খটখট করে তিনটা চাপ দিল। অর্থাৎ থ্রি। এভাবে সে ফোন ব্যবহার করত। আমি গিয়ে হয়তো একটা নাম্বার বলেছি মুকুল ওই কায়দায় ফোন করে দিল। ঠিকই ওপাশ থেকে ফোন ধরল যাকে চেয়েছি সে। মাস শেষে বিল দেখে মুকুলের বাবা অবাক হতেন। বিল কেন বেশি এল ? কিছুতেই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারতেন না।
মুকুলদের প্রেসটা ভালোই চলত। ওই অতটুকু প্রেসের আয়ে মুকুলদের বেশ বড় পরিবারটি ভালোই চলত। কোনও কোনও রাতে এমনও হয়েছে খেয়েদেয়ে আমি আর মুকুল ঘুমিয়ে পড়েছি প্রেসের চৌকিতে। অদূরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাডেল মেশিন। তার পাশেই টাইপের বক্সগুলো। বক্সের সামনে টুল। একপাশে ডাঁই করা কাঠের কালো হয়ে যাওয়া গ্যালি। রাত হয়তো বারোটা সাড়ে বারোটা। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। মুকুল, মুকুল দরজা খোল।
মুকুলের বাবা এসেছেন। মানিকগঞ্জ থেকে লঞ্চে অথবা বাসে এসেছেন। আসতে রাত হয়ে গেছে। পথে খেয়ে নিয়েছেন। তারপর ওই ছোট চৌকিতে আমরা তিনজন গাদাগাদি করে শুয়েছি। মুকুলের বাবা খুব সজ্জন মানুষ ছিলেন। তাঁকে আমি কখনও হাসতে দেখিনি। তবে বিরক্ত হতেও দেখিনি কখনও। ছেলের বন্ধুদের খুবই আদর করতেন। বিশেষ করে আমাকে। কথা তেমন বলতেন না। মুখ দেখে বোঝা যেত আমাকে তিনি পছন্দ করেন।
মুকুল খুবই স্মার্ট ছিল। ট্র্যাডেল মেশিনটা চালাতে পারত। টাইপ বসিয়ে বসিয়ে কম্পোজ করতে পারত। গ্যালিতে কম্পোজ করা টাইপ বেঁধে মেশিনে পরিমাণ মতো কালি লাগিয়ে ছাপার কাজটাও সে পারত। ওদের ওই মেশিনম্যান প্লাস কম্পোজিটারকে দেখে দেখে শিখে নিয়েছিল।
বাহাত্তর সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে বাবার সঙ্গে ঢাকায় এল মুকুল। আমরা পুরনো বন্ধুরা একত্র হয়ে খুবই হইচই করলাম। মোহাম্মদ আলী বুলু, মানবেন্দ্র, মুকুল, আমি মানবেন্দ্রদের বাড়িতে মিলিত হয়ে স্বাধীনতার আনন্দ উদ্যাপন করলাম। কয়েকদিন পর মুকুলের বাবা মুকুলকে রেখে আবার বাড়িতে গেলেন। জানুয়ারির মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। আমি গিয়ে মুকুলের সঙ্গে প্রেসে ঘুমাই। শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধু গল্প করছি। মুকুল বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।
কী আইডিয়া ?
তুই আর আমি মিলে একটা একুশের সংকলন বের করব। তুই সম্পাদক, আমি নির্বাহী সম্পাদক। দুই ফর্মার পাঁচশো পত্রিকা ছাপব। সবকিছু মিলিয়ে দুই আড়াইশো টাকা খরচ হবে।
টাকাটা আসবে কোত্থেকে ?
ওটা তুই আমার উপর ছেড়ে দে। আমাদের কম্পোজিটার আর আমি মিলে ফাঁকে ফাঁকে কম্পোজ করে ফেলব। প্রেসে অন্যদের কাজের কয়েক রিম হোয়াইট প্রিন্ট কাগজ আছে। ক্রাউন সাইজের কাগজ। ওখান থেকে এক রিম মেরে দেব। কাভারের ডিজাইন ও ব্লক আমি করিয়ে আনব। ওই দুই ফর্মার মধ্যে কাভারটাও থাকবে। আমি জানি কোথা থেকে কী করতে হয়। তুই লেখাগুলো জোগাড় করে ফেল। বাকি চিন্তা আমার।
আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তোর বাবা যদি জানতে পারেন ?
বাবা জানতে পারবেন না। এখনও প্রেসে কাজটাজ শুরু হয়নি। বাড়ি থেকে বাবার ফিরতে দেরি হবে। এই ফাঁকে কাজটা সেরে ফেলব। কাগজ আর ছাপা তো আমাদের এইখানেই। ডিজাইন আর ব্লকের টাকা বাকি রাখব। একটা পয়সাও আমাদের লাগবে না। পত্রিকা বিক্রি করে ব্লক ডিজাইনের টাকা দিয়ে দিব। তুই একটা নাম ঠিক কর।
তারপরও আমার ভয় যায় না। সংকলন যদি বিক্রি না হয় ?
হবে, হবে। তুই আর আমি বিশে ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকেই স্টেডিয়ামের ওদিক গিয়ে সংকলন বিক্রি শুরু করব। কোনও নির্ধারিত দাম থাকবে না। যে যা দেয়। এত চিন্তা ভাবনা না করে তোকে যা বললাম তুই সেই কাজটা শুরু কর। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ জোগাড় কর। সংকলনের নাম ঠিক কর। কাল থেকেই শুরু কর।
আমি কোথা থেকে, কার কাছ থেকে লেখা আনব কিছুই জানি না। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রতিবছরই নানা রকমের সংকলন প্রকাশিত হয়। বিশে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকেই সেসব সংকলন গুলিস্তান, স্টেডিয়াম, নিউমার্কেট, ঢাকা ইউনির্ভাসিটি, বাংলা একাডেমি এলাকা আর শহিদ মিনার ওদিককার এলাকায় ঘুরে ঘুরে ছেলেমেয়েরা বিক্রি করে। তখনকার দিনে ওরকম সংকলনের প্রচলন ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই ধীরে ধীরে সংকলন প্রকাশের ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও অনেকগুলো বছর পর্যন্ত প্রচলনটা ছিল। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে উধাও হয়ে গেল, আমরা কেউ টেরও পেলাম না।
আমি তখন গেন্ডারিয়ার রজনী চৌধুরী রোডে থাকি। বাড়িটির ঠিক উল্টোদিকে থাকেন ফুটবলের বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার হামিদ ভাই। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ভাবিও খুব ভালোবাসতেন আমাদের। মানুষের জন্য এত টান খুব কম দম্পতিরই আমি দেখেছি।
হামিদ ভাইদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিককার বাড়িটি ছিল সালেহদের বাড়ি। সালেহ আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে। ওদের বাড়ির নিচতলায় থাকেন মাহমুদ শফিক নামে এক যুবক। শফিক বোধহয় তার খালা বা ফুফু বা মামা বা চাচা এরকম কারও পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। কবিতাপ্রেমী যুবক। লেখেন বাম হাতে। হাতের লেখা খুব সুন্দর। প্রতিদিন পাঁচ-দশটা করে কবিতা লেখেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতা পড়ে পড়ে শোনান। সেসব কবিতার বেশির ভাগেরই অর্থ বুঝি না। তবু খুব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করি।
ছেলেবেলা থেকে বই পড়ার অভ্যাস হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদ্দিন, সুকান্ত―এসব কবির কবিতা পাঠ্যবইতে পড়েছি। সেসব শফিকের কবিতার মতো দুর্বোধ্য মনে হয়নি। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছেন। এখন জগন্নাথে বাংলায় ভর্তি হবেন। একদিন কথাটা শফিককে বললামও। আপনার কবিতা খুব কঠিন লাগে। বুঝতে পারি না।
শফিক বললেন, আধুনিক কবিতা এমনই হয়। সে খুবই চাঁছাছোলা যুবক। বললেন, কবিতা বেশি না পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন না। আধুনিক কবিরা আমার মতোই কবিতা লেখেন।
আধুনিক কবিদের সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। কারা আধুনিক আমি তাও জানি না। তবে শফিককে আমার বিরাট প্রতিভাবান মনে হয়েছে। আমি গিয়ে শফিককে ধরলাম। সংকলনের কথাটি বললাম। তিনি চট করেই একটা নাম দিয়ে দিলেন। ‘কম্পাস’। সংকলনের নাম কেন কম্পাস আমি তা বুঝতেই পারলাম না। জ্যামিতি বক্সে কম্পাস দেখেছি। ওই কাঠখোট্টা জিনিসটার সঙ্গে সাহিত্য সংকলনের কী সম্পর্ক হতে পারে আমার মাথায়ই এল না। তবে শফিক দিয়েছেন। তিনি আধুনিক কবি। নামটাই নিয়ে নিলাম।
এখন লেখা!
এই সমস্যার সমাধানও শফিকই করে দিলেন। বললেন, আমার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ চলেন। ওখানে আমার বন্ধু আছে, মুজিবুল হক কবীর। ওর বাবা লেখক সিরাজুল হক। কবীর নিজেও কবিতা লেখে। ওদের একটা মাসিক পত্রিকাও আছে, নাম কালের পাতা। অনেক লেখকের সঙ্গে কবীরের পরিচয় আছে। সে আপনাকে লেখা জোগাড় করে দেবে। ওর বাবার একটা গল্পও আপনি পাবেন।
সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, সংকলনটি শুধু গল্প দিয়ে সাজালে কেমন হয় ? অর্থাৎ গল্প সংকলন। আমার গল্প পড়তে ভালো লাগে। সুতরাং গল্পের সংকলনই করব।
গেলাম নারায়ণগঞ্জের কবীরদের বাসায়। টিনের লম্বা ঘর। খালের ধারে বাড়ি। এখন আর এলাকাটা চিনবার উপায় নেই। না গ্রাম না শহর। জায়গাটির নাম বাবুরাইল। দুপুরের পরপর গেছি। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লম্বামতন একজন মানুষ দরজার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তিনি সিরাজুল হক। কবীরের বাবা। সেই প্রথম আমি একজন সম্পাদককে দেখলাম। সম্পাদক ও লেখক। তখন কে জানতো, সেদিনকার সেই বিকেলের তেতাল্লিশ বছর পর কালের কণ্ঠ নামে একটি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় দৈনিকের সম্পাদক হব আমি। একটানা সাড়ে দশ বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করব। বছর খানেক গ্যাপ দিয়ে দেশের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের সেই কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হব।
কবীর মুহূর্তেই আমাকে আপন করে নিল। তার বাবার লেখা জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব নিল আর তার পরিচিত তরুণ গল্পকার বুলবুল চৌধুরীর কাছে পাঠাল আমাকে। বুলবুল পুরান ঢাকাতেই থাকেন। বাংলাবাজার থেকে একটি সিনেমার মাসিক পত্রিকা বের হয় জোনাকী নামে। বুলবুল সেই পত্রিকায় কাজ করেন। এক বিকেলে গেলাম তাঁর কাছে। বইয়ের দোকানের মতো ঘরে জোনাকী পত্রিকা’র অফিস। সামনের টেবিলে বসে বুলবুল চৌধুরী প্রুফ দেখছেন। আমার চেয়ে বছর সাতেকের বড় হবেন। লম্বা লালচে চুল। চোখে মোটা কাচের চশমা। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। চেহারা উপজাতিদের মতো। বেশ একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেন। আমাকে চা খাওয়ালেন। সিগারেট সাধলেন। আমি তখনও সিগারেট ধরিনি। চা-টা খুব আগ্রহ নিয়ে খেলাম। বুলবুল নিজে তো গল্প দিলেনই, সিরাজুল ইসলাম নামে আরেক তরুণের গল্পও জোগাড় করে দিলেন। শেখ আবদুল হাকিমের গল্প জোগাড় করে দিলেন। পাঁচটা না সাতটা গল্প নিয়ে সংকলনটা বেরিয়ে গেল। মুকুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা ম্যানেজ করল। উনিশশো বাহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারির তিন-চার দিন আগেই সংকলন রেডি। বিশ ফেব্রুয়ারি দুপুরের পর থেকে সংকলনের বোঝা কাঁধের ঝোলায় ঝুলিয়ে আর বুকের কাছে ধরা একগাদা, আমি চলে গেলাম স্টেডিয়ামের দিকে। মুকুল গেল বাংলা একাডেমির দিকে। আমাদের দুজনার হাতে দুটো মাঝারি সাইজের তখনকার দিনের গুঁড়ো দুধ অস্টার মিল্কের কৌটা। মুখ ঝালাই করা। তার মাঝখানে মাটির ব্যাংকের মতো খানিকটা কাটা। আমরা কোনও দাম চাইব না সংকলনের। যার যা ইচ্ছে এই কৌটায় ফেলে দেবেন। আমার মনে আছে স্টেডিয়ামের ওদিকটার এক ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক গুনে গুনে পাঁচটা এক টাকার কয়েন ফেলে দিলেন একটা সংকলনের বিনিময়ে। আমি তো মহাখুশি। তখনকার পাঁচ টাকা মানে বিশাল ব্যাপার। রাত দশটা পর্যন্ত গুলিস্তান, স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম ওসব এলাকায় ঘুরে ঘুরে সংকলন যা সঙ্গে নিয়েছিলাম, শখানেকের মতো হবে, সবই বিক্রি করে ফেললাম। রাত সাড়ে দশটার দিকে মুকুলদের প্রেসের ওখানে এসেছি। আজ আর কাল দুবন্ধু একসঙ্গে তো থাকবই। কারণ কাল একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ভোরবেলা প্রভাতফেরি বেরোবে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। সবাই ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গাইতে গাইতে মিছিল করে যাবে শহিদ মিনারে। লক্ষ্মীবাজার এলাকার প্রভাতফেরিতে ঢুকবে মুকুল। আমি ঢুকব গেন্ডারিয়ায়। হেঁটে হেঁটে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গাইতে গাইতে শহিদ মিনারে যাব। ফাঁকে ফাঁকে সংকলন বিক্রি করব।
মুকুল তখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি প্রেসের সামনে বসে আছি। মিনিট দশ পনেরো পর সে এল। মুখ উজ্জ্বল করা হাসি। ‘সব সংকলন বিক্রি কইরা ফালাইছি রে, ‘বদেস্টিক’।’ ‘বদেস্টিক’ শব্দটা সে ‘বদ’ অর্থে আদর করে ব্যবহার করত। যখন কোনও কাজ সফলভাবে শেষ করত তখন ওসব উদ্ভট শব্দ সে কেলানো হাসির সঙ্গে বন্ধুদের উপহার দিত। তারপর হাতের কৌটাটা নাড়াল মুকুল। খালি ঝোলাটা দেখাল। আমি হাসিমুখে বললাম, আমার গুলোও সব শেষ। পরদিন দুপুরের মধ্যে প্রায় সব পত্রিকা আমরা শেষ করে ফেললাম। বোধহয় গোটা পঞ্চাশেক অবশিষ্ট ছিল। ওই নিয়ে বিকেলে আবার গেলাম শহিদ মিনারে। টুকটাক সংকলন বিক্রি হচ্ছে। মুকুল একদিকে, আমি আরেকদিকে। সময় দেওয়া আছে। ওই সময়ে ঢাকা মেডিক্যালের গেটের সামনে আমি আগে গেলে আমি দাঁড়াব। মুকুল আগে গেলে মুকুল আমার জন্য দাঁড়াবে। দুজন একসঙ্গে প্রেসে ফিরে যাব।
সেই রাতে প্রেসে ফিরে যার যার হাতের কৌটা ছুড়ি দিয়ে খুললাম। প্রেসের চৌকিতে বসে টাকা-পয়সা গুনে আমরা আনন্দে প্রায় ফেটে পড়েছি। চারশো আশি টাকা দুজনে বিক্রি করেছি। সব খরচ বাদ দিয়ে আড়াইশো টাকার মতো লাভ হয়েছে। মুহূর্তে দুই বন্ধু তা ভাগ করে পকেটে পুরে ফেললাম। এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমি তার আগে কোনও দিন চোখেই দেখিনি। আনন্দে রাতে আমার আর ঘুম হয় না। মুকুল দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে।
সেবারের একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদ মিনারে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সঙ্গে আরও তিন যুবক। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। বুলবুল আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকেই তখনকার তুখোড় তরুণ লেখক। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল ইসলাম ও ফিউরি খন্দকার। পরবর্তীকালে বুলবুলকে নিয়ে এই চারজন লেখক আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়বন্ধু হয়ে ওঠে। বুলবুল আর সুকান্তের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয় আপনি আপনি। ফিউরির সঙ্গে তুমি। সিরাজের সঙ্গে তুই।
তারপর ধীরে ধীরে গল্প উপন্যাসের জগতে ঢুকেছিলাম আমি। দুজন কবি ও সম্পাদক মাথায় হাত রেখে আমার জীবন বদলে দিলেন। একজন দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক আবুল হাসনাত। আমার প্রিয় হাসনাত ভাই। তিনি কবিতা লিখতেন মাহমুদ আল জামান নামে। আরেকজন কবি রফিক আজাদ। তিনি তখন বাংলা একাডেমির উত্তরাধিকার পত্রিকার সম্পাদক।
এখন তাঁদের কথা বলি।
নবাবপুরের মাঝামাঝি পশ্চিম দিককার এক রাস্তায় মানসী সিনেমা হল। মানসী হলের নাম তখন ছিল ‘নিশাত’। এই হলের ঠিক উল্টোদিকে লোহার বিশাল একটা গেট, টিনশেডের দৈনিক সংবাদ অফিস। যতদূর মনে পড়ে, তখন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ কিছুটা শুরু হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের কথা। তখন দুটো দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা অত্যন্ত জমজমাট। একটি দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতা, আরেকটি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী। দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন কবি আহসান হাবীব। আর দৈনিক সংবাদেরটা আবুল হাসনাত। তিনিও কবি। শুধু কবি বলা ভুল হবে। তিনি সব রকমের লেখাই লিখেছেন। ছোটদের উপন্যাস, শিল্পকলা নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণা ও আত্মজৈবনিক রচনা। কিন্তু আবুল হাসনাত নামে তিনি লিখতেন না। লিখতেন মাহমুদ আল জামান নামে।
যে সময়কার কথা বলছি, তখনও হাসনাত ভাই সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই প্রায় জানি না। শুধু জানি, তিনি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক। তাঁর পাতায় লেখার জন্য দেশের খ্যাতিমান সব লেখক অপেক্ষা করেন। আর তরুণ লেখকরা মনে করেন, দৈনিক বাংলার কবি আহসান হাবীব এবং দৈনিক সংবাদের হাসনাত ভাইয়ের হাত দিয়ে লেখা ছাপা হলে সেই লেখককে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। অন্য সব পত্রিকা তাঁকে মর্যাদার চোখে দেখবে।
আমার বন্ধু সিরাজুল ইসলাম তখন তরুণ গল্পকার হিসেবে বিখ্যাত। দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতায় নিয়মিত তাঁর লেখা ছাপা হয়। দৈনিক সংবাদেও হয়। সিরাজের বন্ধু শিল্পী কাজী হাসান হাবিব। সিরাজের মাধ্যমে আমারও বন্ধুত্ব হয়েছে হাবিবের সঙ্গে। হাবিবকে ঘিরে যুক্ত হয়েছে আমাদের আরও দুই বন্ধু। মোহাম্মদ জুবায়ের ও ফিরোজ সারোয়ার। এই পাঁচজনের একটি দল হয়েছি আমরা। তখন সাহিত্য পাতা প্রকাশিত হতো রবিবার ছুটির দিনে। হাবিব সরকারি চাকরি করত। সরকারি প্রকাশনা বিভাগে ইলাস্ট্রেশন মেকআপ ইত্যাদির কাজ। সেক্রেটারিয়েটের উত্তর দিককার লম্বা একটি একতলা ঘরে তার অফিস। চারদিকে ইটের দেয়াল, ওপরে ভারী টিনের চালা। হাবিবের সেই অফিসেও আমরা আড্ডা দিতে যেতাম। কবি কাজী রোজীও এখানে কাজ করতেন। তবে সপ্তাহের যে দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম দিনটি ছিল শনিবার। সরকারি চাকরির পাশাপাশি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতায় পার্টটাইম কাজ করত হাবিব। অসামান্য ছবি আঁকার হাত হাবিবের। তার প্রতিটি ইলাস্ট্রেশন দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম। অসামান্য লেটারিং আমাদের চোখে লেগে থাকত।
শনিবার দুপুরের পর হাবিব চলে আসত সংবাদ অফিসে। টেবিলে মাথা গুঁজে বসে গল্প পড়ত। সেই গল্পের ইলাস্ট্রেশন করত। চারটা-পাঁচটার দিকে সিরাজ, জুবায়ের, সারোয়ার আর আমি গিয়ে উপস্থিত হতাম। হাবিবের টেবিল ঘিরে আমরা চারজন। ফুকফুক করে সিগারেট টানছি আর চা খাচ্ছি। হাবিবের এক হাতে সিগারেট। সেই হাতের কাছে চায়ের কাপ। এক চুমুক চা খাচ্ছে আর একটান সিগারেট । অন্য হাতে কোনও গল্পের ইলাস্ট্রেশন করছে। সাহিত্য পাতা মেকআপ করছে কখনও কখনও। ফাঁকে ফাঁকে আড্ডাও ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একজন গুরুগম্ভীর মানুষ এসে মৃদু স্বরে দু-একটা কথা বলে যাচ্ছেন হাবিবকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে অতি বিনয়ী ও ভদ্রকণ্ঠে হয়তো বললেন, ‘কেমন আছেন ?’ তারপরই চলে গেলেন নিজের কাজে। মানুষটি আবুল হাসনাত। আমাদের প্রিয় হাসনাত ভাই। তিনি আমাদের ব্যাপক প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আমরা চার বন্ধুই লিখি। ছবি আঁকার পাশাপাশি হাবিব কবিতা লেখে। দু-চারটি গল্পও লিখেছে। তার ‘পরিস্থিতি’ নামে একটি গল্পের কথা আমার মনে আছে। সারোয়ার খুব সুন্দর একটি গল্প লিখেছিল। গল্পের নাম ‘একা’। হাবিবের ইলাস্ট্রেশনটি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। সিরাজ, জুবায়েরের গল্প, আমার কত গল্প যে হাসনাত ভাইয়ের হাত দিয়ে ছাপা হয়েছে! বলতে দ্বিধা নেই, হাসনাত ভাই না থাকলে ইমদাদুল হক মিলন নামে কোনও লেখকই হতো না। হাসনাত ভাইয়ের পর আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন কবি রফিক আজাদ। এই দুজন মানুষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই।
তখন নানা ধরনের হালকা চালের প্রেমের গল্প, কিঞ্চিৎ রগরগে গল্প লিখে আমি বেশ নিন্দিত। পাশাপাশি গ্রামনির্ভর কিছু গল্প লিখে বা প্রথম উপন্যাস যাবজ্জীবন রফিক আজাদ যখন বাংলা একাডেমির উত্তরাধিকার পত্রিকায় ছাপতে শুরু করলেন তখন কিছু বড় লেখক কবি আমার ওই লেখাগুলো পছন্দও করতে লাগলেন। আমার ওপর দিয়ে তখন দুটি স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একদিকে নিন্দামন্দ, অন্যদিকে কিছুটা প্রশংসা। এই অবস্থায় হাসনাত ভাই আমাকে নিয়ে একটা বোমা ফাটালেন। তিনি নিয়মিত আমার গল্প ছাপছিলেন। মাঝে মাঝে গল্পের নানা দিক নিয়ে আমাকে অল্প কথায় বোঝাতেন। বোমাটা ফাটালেন দৈনিক সংবাদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অসামান্য একটি সংকলন প্রকাশিত হল সেই সংকলনে আমার একটি গল্প ছেপে। আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হাসনাত ভাই খুব পছন্দ করতেন। ওই সংকলনে সুকান্তের ছোট্ট একটি উপন্যাস ছাপা হল। নাম ‘দেশ গেরামের মনিষ্যি’। লেখাটি ভারি চমৎকার। পাশাপাশি তরুণতর গল্পকার হিসেবে একমাত্র আমারই একটি গল্প ছাপলেন। গল্পের নাম ‘রাজা বদমাশ’।
অন্য কারও লেখা নিয়ে কোনও কথা নেই, আমার গল্প নিয়ে অনেকে কথা তুললেন। বিশেষ করে আমার বয়সি কিছু তরুণ লেখক। আমার লেখা হাসনাত ভাইয়ের হাত দিয়ে ওরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলনে ছাপা হয়েছে, এটা তাঁরা মেনেই নিতে পারছেন না। হাসনাত ভাইকে নানা রকমভাবে সে কথা তাঁরা বলতে লাগলেন। হাসনাত ভাই চিরকাল কম কথার মানুষ। অভিযোগ শুধু শুনে যাচ্ছিলেন। একদিন বিরক্ত হয়ে এক তরুণ লেখককে বললেন, ‘ওরকম একটি গল্প লিখে নিয়ে আসুন। বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ছেপে দেব।’
আমাদের পাঁচজনের দলটি ভেঙে হাবিব চলে গেল। ক্যান্সার আক্রমণ করেছিল তাকে। ধানমন্ডির এক ক্লিনিকে চিকিৎসা চলছে। গেছি হাবিবকে দেখতে। তার বিছানার পাশে বসে আছেন হাসনাত ভাই। যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাবিব। সহ্য করতে না পেরে আমি বারান্দায় এসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। খানিক পর এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন হাসনাত ভাই। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কোনও কথা বললেন না। চোখ মুছতে মুছতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন।
হাবিব চলে যাওয়ার বেশকিছু বছর পর চলে গেল জুবায়ের। একটা সময় সে চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। ডালাসে থাকত। একবার আমি গিয়ে জুবায়েরের ওখানে দিন বিশেক ছিলাম। আমাদের ফেলে আসা জীবনের কত আনন্দময় স্মৃতির কথা যে দুই বন্ধুর মধ্যে হতো! জুবায়েরও আক্রান্ত হয়েছিল ক্যান্সারে। যখনই নিজেদের নিয়ে আমরা কথা বলতাম, দলটির মধ্যে নিঃশব্দে এসে ঢুকে যেতেন হাসনাত ভাই। আমাদের লেখালেখির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন মানুষটি। আমাদের মাথার ওপর বটবৃক্ষের ছায়ার মতো ছিল তাঁর স্নেহমাখা হাতখানি।
এই হাসনাত ভাইয়ের সঙ্গে খুবই বাজে একটা আচরণ করলাম আমি। ১৯৭৯ সালের কথা। জীবনের প্রথম সাংবাদিকতার কাজ করছি রফিক আজাদের সঙ্গে। পত্রিকাটির নাম সাপ্তাহিক রোববার। হাসনাত ভাই অসামান্য একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা করতেন তখন। ডিমাই সাইজের পত্রিকাটির নাম ছিল গণসাহিত্য। দেশের বড় লেখকেরা লেখেন সেখানে। হাসনাত ভাই আমার কাছে গল্প চাইলেন। অন্য জায়গায় ছাপা হওয়া একটি পুরনো গল্প হাসনাত ভাইকে দিয়ে দিলাম। একবারও ভাবলাম না, পুরনো লেখা গণসাহিত্যে কখনও ছাপা হয় না। হাসনাত ভাইকে বুঝতেও দিলাম না কিছু। তিনি সরল মনে গল্পটি ছাপলেন। ছাপা হওয়ার পর আমার চালাকিটা ধরা পড়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাসনাত ভাই এলেন রোববার অফিসে। রোববার অফিসটা ছিল ইত্তেফাকের তিনতলায়। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আমাকে ডেকে নিলেন বারান্দায়। আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি হাসনাত ভাইয়ের সামনে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এটা আপনি কী করেছেন ? আমাকে এরকম লজ্জার মধ্যে ফেললেন ?
হাসনাত ভাইয়ের লজ্জা যেন আমার ওপর এসে ভর করল। মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতেই পারি না। একসময় মাথা নিচু করেই বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে হাসনাত ভাই।
হাসনাত ভাই আর কোনও কথাই বললেন না। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে যেমন ঢুকেছিলেন, সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, হাসনাত ভাইয়ের দরজাটি আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেল।
ধারণাটি যে কত বড় ভুল, বুঝলাম মাস দুয়েক পর। রোববার অফিসে ফোন করে হাসনাত ভাই আমাকে চাইলেন, ধরলাম, বললেন, সংবাদের জন্য আগামী সপ্তাহে একটি গল্প দিতে হবে। আমার বুকের পাথর নেমে গেল।
বিভিন্ন আড্ডায় অনুষ্ঠানে হাসনাত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর স্নেহমাখা হাসিটি আমার জন্য আছেই। দেখা হলেই এক ফাঁকে জানতে চাইবেন সিরাজ, সারোয়ারের কথা। হঠাৎ হঠাৎ আসবে হাবিব প্রসঙ্গ। জুবায়েরের প্রসঙ্গ। তাঁর চোখে সে সময় বিষণ্নতা খেলা করে যেত।
ঢাকা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে দেখা। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে কালি ও কলম নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বেরোবে। প্রথম সংখ্যা থেকে আমরা দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপব। কলকাতা থেকে লিখবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলাদেশ থেকে আপনি। কাল থেকেই লেখা শুরু করুন।
দুই বছর ধরে কালি ও কলম এ লিখলাম দেশভাগের পটভূমিতে পর উপন্যাসটি। সময়মতো কিস্তি দিতে পারতাম না। কিন্তু হাসনাত ভাই কখনওই রাগ করতেন না। মায়াবী গলায় বোঝাতেন, পত্রিকাটি তো সময়মতো বের করতে হবে। দেরি করলে ঝামেলায় পড়ব।
আহা রে, লেখালেখির জন্য কত কষ্ট হাসনাত ভাইকে আমি দিয়েছি!
কালি ও কলম সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন হলো। বিচারকমণ্ডলীতে নিয়মিতই আমাকে রাখতে লাগলেন হাসনাত ভাই। পুরস্কার প্রদানের এক অনুষ্ঠানে সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে আমিও অতিথি। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কর্ণধার আমার অতিপ্রিয় আবুল খায়ের লিটু ভাই আছেন। লুভা নাহিদ আছেন আর আছেন সবার প্রিয় আনিসুজ্জামান স্যার। সেই অনুষ্ঠানে হাসনাত ভাইয়ের স্নেহের ছায়ায় কিভাবে বেড়ে উঠেছি আমি সেসব কথা কিছুটা বললাম। নিজের প্রশংসা বা কৃতিত্বের কথা শুনলে এতটাই আড়ষ্ট হতেন হাসনাত ভাই, মুখ তুলে কারও দিকে তাকাতেই পারতেন না। অনুষ্ঠান শেষে এক ফাঁকে আমাকে শুধু বললেন, ‘এত কিছু বলতে হয় নাকি!’
এই হাসনাত ভাই নিঃশব্দে আমাদের ছেড়ে গেলেন। খবরটা আমাকে প্রথমে দিলেন কবি তারিক সুজাত। আমি জানালাম কবি কামাল চৌধুরীকে। কয়েক বছর ধরে কবি মাহবুব সাদিক ও আমার বন্ধু অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের সঙ্গে কালি ও কলম সাহিত্য পুরস্কারে বিচারক থাকি আমি। ব্যবস্থাটি হাসনাত ভাই করেছেন। তাঁর চলে যাওয়ার দিন মাহবুব সাদিক ফোন করলেন। ফোনের দুই প্রান্তে আমরা দুজন দু-একটি কথা বলে নিঃশব্দ হয়ে থাকলাম। বিশ্বজিতের সঙ্গে ফোনেও একই অবস্থা। কালের কণ্ঠে আমার সঙ্গে কাজ করে জাকারিয়া জামান। অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, আমি অনেককে বলেছি আজ মিলন ভাইয়ের মন খুবই খারাপ থাকবে। তাঁর অতিপ্রিয় হাসনাত ভাই চলে গেছেন। আমার দীর্ঘদিনের সহকারী মোহাম্মদ শাহীন। বিভিন্ন সময় হাসনাত ভাইয়ের কাছে আমার লেখা নিয়ে সে গেছে। আমাকে না পেলে অনেক সময় শাহীনকে ফোন করতেন হাসনাত ভাই। তাঁর চলে যাওয়ার কথা শুনে ধপ করে বসে পড়ল শাহীন। মৃদু কণ্ঠে বলল, হাসনাত স্যার ছিলেন সোনার মানুষ। এই জীবনে এরকম মানুষ আর দেখব না।
শাহীনের কথা শুনে আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমাদের সোনার মানুষটি চলে গেছেন। কোথায় পাব তারে!
একজন কবিকে নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছিলাম। কবির নাম রফিক আজাদ। উপন্যাসের নাম দুঃখ কষ্ট। রফিক আজাদের কবিতা থেকেই রাখা হয়েছিল নামটি।
‘পাখি উড়ে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে কঠিন মাটিতে।
এই ভেবে কষ্ট পেয়েছিলে’
’৭৮ সালের কথা। আমি তখন রফিক আজাদের প্রেমে মগ্ন। তাঁর একেকটা কবিতা বেরোয়, আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই। চব্বিশ ঘণ্টার আঠার ঘণ্টায়ই কাটাই রফিক আজাদের সঙ্গে। তিনি আমাকে আদর করে ডাকেন ‘বেটা’ আমি ডাকি রফিক ভাই।
ইত্তেফাক ভবন থেকে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বেরোবার তোড়জোড় চলছে। কাগজের নাম রোববার। আমি জগন্নাথ কলেজে অনার্স শেষক্লাসে পড়ছি। বিষয়, অর্থনীতি। রফিক ভাই বাংলা একাডেমিতে কাজ করেন। বাংলা একাডেমির মাসিক সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাধিকার-এর সম্পাদক। কিন্তু সেই কাজ তাঁর ভালো লাগছে না। যখন তখন অফিস ফাঁকি দিচ্ছেন। দুপুর কাটাচ্ছেন সাকুরা গ্রিন কিংবা অন্যকোনও ‘বারে’। দুপুরের পর চলে যাচ্ছেন ইত্তেফাক ভবনে। রাহাত খান তাঁর বন্ধু। রোববার পত্রিকার সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রফিক আজাদকে। বাংলা একাডেমির চাকরি রেখেই রোববার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। নিজের নাম উহ্য রেখে রোববারের কাজ করবেন। সকাল থেকে দুপুর অবধি বাংলা একাডেমিতে, দুপুরের পর থেকে ‘রোববার’। আমার অনার্স পরীক্ষার বিশেষ বাকি নেই। ইকোনোমিকস মাথায় উঠে গেছে। সকালবেলা আমি গিয়ে হাজির হই বাংলা একাডেমিতে, রফিক আজাদের টেবিলের সামনে বসে কাপের পর কাপ চা খাই, একটার পর একটা সিগারেট খাই। পকেটে টাকা পয়সা থাকলে রফিক ভাইকে নিয়ে দুপুরের মুখে মুখে চলে যাই কোনও বার কাম রেস্টুরেন্টে। সেখানে পানাহার করে ইত্তেফাক ভবন, রোববার অফিস। জীবনের প্রথম চাকরি হলো রোববারে। জুনিয়র রিপোর্টার বা এইরকম কিছু। বেতন চারশো টাকা।
টাকা পয়সা নিয়ে কে ভাবে ? রফিক আজাদের সঙ্গে থাকতে পারছি, কাজ করতে পারছি এটাই তো বিশাল ব্যাপার!
এসবের বছর দুয়েক আগে রফিক আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।
বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক তখন বিচিত্রা। বিচিত্রায় আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম ‘না সজনী’। সেই সময়কার যুবক যুবতীদের নিয়ে লেখা একটু অন্য ধরনের প্রেমের গল্প। রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নাম নেওয়া হয়েছে। চারদিকে ভালো একটা সাড়া পড়েছে। আমি গেছি বাংলা একাডেমিতে। দোতলার একটা রুমে রশিদ হায়দার সেলিনা হোসেন আর রফিক আজাদ বসেন। রশিদ হায়দার আমার পরিচিত। তাঁর ছোট ভাই জাহিদ হায়দার আমার বন্ধু। ওদের চতুর্থ ভাই দাউদ হায়দারের জন্য পরিবারটি খুবই বিখ্যাত। সবাই লেখালেখি করেন। রশিদ হায়দার গল্প উপন্যাস লেখেন। আমি তাঁর টেবিলের সামনে বসে আছি। পাশের টেবিলে মাথাগুঁজে কাগজপত্র ঘাটছেন সেলিনা হোসেন। বাংলা একাডেমির ছোটদের মাসিক পত্রিকা ধান শালিকের দেশ সম্পাদনা করেন। আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাননি। একটু দূরে কোণের দিককার টেবিলে বসে আছেন রফিক আজাদ। আমি তাঁকে চেহারায় চিনি। কুস্তিগিরদের মতো চেহারা। বেটে, তাগড়া জোয়ান। হাতাকাটা টিশার্ট পরেন, গলায় চেন, হাতে বালা। নাকের তলায় ইয়া গোঁফ, হাতে সারাক্ষণই সিগারেট । বিচিত্রা তাঁকে নিয়ে কভারস্টোরি করেছিল।
কাছ থেকে রফিক আজাদকে কখনও দেখিনি। রশিদ হায়দারের টেবিলে বসে আড়চোখে দেখছি। সাদা রংয়ের হাতাকাটা টাইট টিশার্ট পরা। গলায় মোটা চেন, একহাতে তামার বালা, অন্যহাতে সিগারেট। উত্তরাধিকার পত্রিকার কপি দেখছেন। সামনে চায়ের কাপ।
এসময় একটা মজার ঘটনা ঘটল।
হাতের কাজ ফেলে চায়ে চুমুক দিলেন রফিক আজাদ। রশিদ হায়দারকে বললেন, ওই রশিদ, বিচিত্রায় এ সপ্তাহে একটা ছেলে গল্প লেখছে, ইমদাদুল হক মিলন নাম, তুই চিনস ?
রশিদ ভাই হাসলেন। এই তো আমার সামনে বইসা আছে।
রফিক আজাদ আমার দিকে তাকালেন। ওই মিয়া, এইদিকে আসো।
আমার তখন বুকটা কেমন ধুকধুক করছে। বিচিত্রায় আমার লেখা ছাপা হয়েছে সেই খবর রাখেন রফিক আজাদ ? আমাকে ডাকছেন তাঁর টেবিলে! যে কবি আমাদের হিরো, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব ?
রফিক আজাদ জাঁদরেল মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সহকারী ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারী।
আমার চেহারা কিছুটা রফিক আজাদ টাইপ। পরনে জিন্স, ফুলসিøভ শার্টের হাতা গুটানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়া মোচ। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রফিক আজাদ বললেন, বসো।
বসার পর বললেন, তোমার গল্পটা আমি পড়ছি। একটা কাজ করো, উত্তরাধিকারের জন্য গল্প দেও। কবে দিতে পারবা ?
সপ্তাখানেক।
ঠিক আছে। চা খাইবা ?
না।
আরে খাও মিয়া।
চা আনালেন। আমি তখনও কিছুটা আরষ্ট। চা খেয়ে উঠে আসছি, রফিক ভাই আমার পিছু পিছু এলেন। রুম থেকে বেরিয়ে বললেন, ওই মিয়া, একশো টাকা দিয়া যাও।
আমি হতভম্ব। বলে কী ? এইমাত্র পরিচয়, এইমাত্রই ধার!
আমার পকেটে তখন টাকা থাকে। বড়ভাইয়ের কনস্ট্রাকশন বিজনেস আমি খানিকটা দেখি। ইকোনোমিকস পড়া, উন্মাদের মতো লেখালেখি, একটি বালিকার সঙ্গে প্রেম, এতকিছুর ফাঁকে বড়ভাইর বিজনেসও দেখি। পকেটে সবসময় ডানহিলের প্যাকেট। ডানহিল দামি সিগারেট। ওই সিগারেট দেখেই রফিক ভাই বুঝে গিয়েছিলেন আমার পকেটে টাকা আছে। ডানহিল সিগারেট তাঁকে অফারও করেছিলাম। তিনি যেন অতিশয় দয়া করে সিগারেটটা নিলেন। দু-তিনটা টান দিয়ে বললেন, ধুরো মিয়া, এইটা কী সিগারেট খাও ? ভাতের মতন লাগে।
মানিব্যাগ থেকে খুবই বিনয়ের সঙ্গে একশো টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। মনে মনে ভাবছি, আমাকে কি ধোর (মক্কেল) ভাবল নাকি ? লেখার সঙ্গে একশো টাকাও চাইল ?
কিন্তু রফিক আজাদের জন্য গল্প লিখতে বসে ভালো রকম ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। বিক্রমপুর অঞ্চলের একটা গ্রামের বাজার, বাজারের মানুষজন, সার্কাসের জোকাড়, হতশ্রী এক বেশ্যা, একজন হিন্দু কম্পাউন্ডার, একজন পাগল আর নিয়তির মতো একটি সাপ এইসব নিয়ে লিখতে শুরু করেছি। লেখা তরতর করে এগুচ্ছে। প্রচলিত গদ্যের ভেতরে ভেতরে নির্বিচারে ব্যবহার করে যাচ্ছি বিক্রমপুরের আঞ্চলিক শব্দ। সপ্তাহখানেক লেখার পর দেখি ফুলস্কেপ কাগজের চব্বিশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে কিন্তু লেখা শেষ হয়নি। শেষ কী, মনে হচ্ছে যেন একটি চ্যাপ্টার মাত্র শেষ হয়েছে।
আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।
রফিক ভাই এক সপ্তাহের টাইম দিয়েছেন, উত্তরাধিকারের মতো পত্রিকায় ছাপা হবে লেখা, সেই লেখা শেষ হচ্ছে না ? খুবই অসহায়, কাতর অবস্থা। চব্বিশ পৃষ্ঠা হাতে নিয়ে গেলাম বাংলা একাডেমিতে! রফিক ভাই খুশি। লেখা আনছো ? দেও।
দিলাম। তিনি চোখ বুলাতে লাগলেন। ’৭৬ সালের কথা। আমার হাতের লেখা তখন পরিষ্কার, গোটা গোটা। শিশুরাও পড়তে পারবে। তখন কম্পিউটার কম্পোজের নামই আসেনি পৃথিবীতে, সাবেকি টাইপ রাইটারে টাইপ করানো বেশ খরচের ব্যাপার। জেরোস্ক মেশিনও সর্বত্র পাওয়া যায় না। জেরোস্কের চেয়ে ফটোকপি শব্দটা বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত। আমি ফটোকপি করার কথাও ভাবিনি।
রফিক ভাই লেখা দেখছেন, ভয়ে ভয়ে বললাম, রফিক ভাই, লেখাটা শেষ হয়নি।
তিনি চমকালেন। কী কও মিয়া! শেষ হয় নাই মানে ?
শেষ করতে পারিনি। লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে।
রফিক ভাই চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। তখন তিনি বেদম সিগারেট খান। একটার আগুন থেকে আরেকটা ধরান। আমি অপরাধীর মতো মুখ করে বসে আছি। সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে আবার লেখাটায় চোখ বুলালেন তিনি। তারপর বললেন, ঠিক আছে। লেখাটা আগে আমি পড়ি। একসপ্তাহ পরে আইসা খবর নিও।
গেছি একসপ্তাহ পর। রফিক ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার লেখাটা পড়ছি। এই লেখা তুমি জোর কইরা ছোট করার চেষ্টা করবা না। লেখা যেইভাবে আগায়, আগাইব। যতবড় হয় হইব। আমি এই লেখা ছাপব।
আঠারো মাস ধরে সেই লেখা উত্তরাধিকারে ছেপে গেলেন রফিক ভাই। আমার প্রথম উপন্যাস যাবজ্জীবন লেখা হলো এইভাবে। ওই আঠারো মাসে বিখ্যাত হয়ে গেলাম আমি। সাহিত্যের মেধাবী পাঠক, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জনৈক ইমদাদুল হক মিলনের ব্যাপারে একটু নড়েচড়ে বসলেন, উৎসাহী হয়ে উঠলেন।
যাবজ্জীবন লেখার সময় দিনের পর দিন রফিক ভাই আমাকে সাহিত্য বুঝিয়েছেন, বাংলা বানান শিখিয়েছেন। তখন আমি এত ভুলভাল লিখি। সাহিত্যের পড়াশোনাটা একদম নেই। রফিক ভাই লেখকদের নাম বলেন আর আমি সেসব লেখকের লেখা খুঁজে খুঁজে পড়ি। দিনে দিনে সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে গেল, রফিক ভাইই আমার ধ্যান জ্ঞান প্রেম। রাতেও গিয়ে কখনও কখনও তাঁর বাড়িতে থাকি।
তারপর এল রোববারের কাল।
পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে, জামালপুরে একটা সাহিত্য সম্মেলনের দাওয়াত পেলেন রফিক ভাই। আমাকে বললেন, ওই মিয়া, যাইবানি ?
আমি তো একপায়ে খাড়া। রফিক ভাইর সঙ্গে থাকতে পারা মানে সবচাইতে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে থাকা। রফিক ভাইয়ের চালচলন, কথাবার্তা, গলা ফাটিয়ে হাসা, পোশাক আশাক সব কিছুরই আমি মহাভক্ত হয়ে গেছি। তখন পর্যন্ত তিনি আমার সবচাইতে প্রিয় চরিত্র।
ব্যাগ কাঁধে রফিক ভাইর সঙ্গে বাসে চড়লাম।
এসবের কিছুদিন আগে রফিক আজাদের বিখ্যাত কবিতার বই চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া বেরিয়েছে। কী বই, কী একেকখানা কবিতা! বাংলাদেশের তরুণ কবি, কবি যশপ্রার্থী এবং কবিতার পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই বইয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ অসম্ভবের পায়ে থেকেই তিনি পাঠকপ্রিয়, দ্বিতীয় গ্রন্থ সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে তাঁকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া বাংলাদেশের কাব্যজগৎ কাঁপিয়ে দিল।
আমি সেই কবির সহযাত্রী হয়েছি, এরচেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে!
জামালপুরে আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হল সরকারি এক খামারবাড়ির বাংলোয়। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া রাত। আমাদের পানের ব্যবস্থা ছিল না। বাংলোর বারান্দায় বসে সিগারেট খাই দুজনে। সামনে বিশাল সূর্যমুখীর মাঠ। মাঠের কোণে একটা চাপকল। চাঁদের আলো সরাসরি পড়েছে সূর্যমুখীর মাঠে। কী যে অপূর্ব লাগছে! চারদিকে ঝিঁঝিপোকার ডাক, ফুলের গন্ধ নিয়ে আদুরে একটা হাওয়া কোত্থেকে বয়ে আসে কে জানে। একটা রাতপাখি ডানায় জ্যোৎস্না ভেঙে মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। রফিক আজাদের কী হয় জানি না, আমার ভেতরে তৈরি হয় আশ্চর্য এক ঘোর। আশ্চর্য এক তৃষ্ণা যেন ফাটিয়ে দিতে চায় বুক। আমার ইচ্ছে করে চাপকলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, জ্যোৎস্নায় গড়া এক যুবতী তার মায়াবী হাতে চেপে দিক চাপকল। আঁজলা ভরে জলপান করি আমি। আজন্মের তৃষ্ণা মেটাই।
রফিক আজাদেরও বুঝি তখন আমার মতোই অবস্থা। তাঁর ভেতরও তৈরি হয়েছে ঘোর। সেই আশ্চর্য জ্যোৎস্না রাতে আমি, তারপর, একজন কবির ভেতরকার আরেকজন কবিকে জেগে উঠতে দেখি। একজন মানুষের ভেতরকার আরেকজন মানুষকে জেগে উঠতে দেখি। যে কবি থাকেন অন্তরালে, যে মানুষ থাকে অন্তরালে, সমগ্রজীবনে এক দুবারের বেশি তার দেখা পায় না অন্যকেউ। রফিক ভাই তাঁর জীবনের কথা বললেন, কবিতার কথা বললেন। অকালে হারিয়ে যাওয়া তাঁর প্রিয় বোনটির কথা বললেন। আর বললেন সেই মেয়ের কথা। কবিতায় লিখেছিলেন ‘ওপারে লায়লার লালবাড়ি’।
কে এই লায়লা ?
কোন্ সে দুরন্ত প্রেমিক নদী সাঁতরে যায় লায়লার লালবাড়িতে ?
জামালপুর থেকে ফিরে এসে রফিক আজাদকে নিয়ে, আমাকে নিয়ে উপন্যাস লিখলাম দুঃখ কষ্ট। উপন্যাসের প্রতিটি চ্যাপ্টার শুরু হল রফিক আজাদের কবিতার লাইন দিয়ে। একটি লাইন ‘দেয়ালে দেয়ালে, অনিবার্য অন্ধকারে’।
রোববার বেরোবার আট দশমাস পর আমি জার্মানিতে চলে গেলাম। জার্মানি তখন দুটো দেশ। আমি গেলাম পশ্চিম জার্মানিতে। বন শহরে আমার কয়েকজন বন্ধু ছিল। প্রথমে গিয়ে তাদের কাছে উঠলাম। দিন বিশেক বনে থেকে চলে গেলাম স্টুটগার্টে। স্টুটগার্টে কয়েকমাস থেকে চলে গেলাম পাশের ছোট্ট শহর সিনডেলফিনগেনে। এই শহরটিকে বলা হয় মার্সিডিস সিটি। কারণ বিখ্যাত মার্সিডিসবেঞ্জের মূল কারখানা এই শহরে।
জার্মানিতে গিয়েছিলাম রোজগারের আশায়। টাকা রোজগার করে জীবন বদলাব। হয়নি। প্রবাস জীবন আমি সহ্য করতে পারিনি। আমাদের দেশের নিম্নস্তরের শ্রমিকের কাজ ছাড়া কোনও কাজে পয়সা নেই। ওইসব কাজ আমি করতে পারছিলাম না। তাছাড়া দেশে রয়ে গেছে কত প্রিয়মানুষ, কত প্রিয়জন, তাদের ছেড়ে আছি। আমার মন পড়ে থাকত দেশে, সেইসব প্রিয় মানুষের কাছে। মা ভাইবোন তো আছেই, যুবতী হয়ে ওঠা প্রেমিকাটি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, লেখালেখি করে একটা জায়গা তৈরি করেছিলাম সেই জায়গাটি আছে আর আছেন রফিক আজাদ। আমি সবাইকে চিঠি লিখি। সবাই আমাকে চিঠি লেখে। রফিক ভাইকে চিঠি লিখি কিন্তু তাঁর চিঠির কোনও জবাব আসে না। দশ বারোটি চিঠি লেখার পর তাঁর একটা চিঠি পেলাম। চিঠির দুটো লাইন এখনও মনে আছে, ‘গদ্য লেখার ভয়ে আমি কাউকে চিঠি লিখি না। কিন্তু মনে মনে প্রতিদিন তোমাকে অনেক চিঠি লিখি। তুমি কেমন আছো, মিলন ?’
মনে আছে লাইনটি পড়ে আমি শিশুর মতো কেঁদেছিলাম!
জার্মানি থেকে ফিরে এলাম দুবছর পর। যেদিন ফিরলাম, রফিক ভাইর সঙ্গে দেখা হল তার পরদিন। আমাকে দেখে কী যে খুশি হলেন! সেদিনই বেতন পেয়েছেন, বেতনের পুরো টাকাটা আমাকে নিয়ে দামি মদ খেয়ে শেষ করে দিলেন। একটা মাস কী করে সংসার চলবে একবারও ভাবলেন না।
আবার আগের জীবনে ফিরে এলাম আমি। রোববারে নতুন করে চাকরি হল। ইত্তেফাক ভবনের সামনে ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেল এক পথচারী। পুরো শরীর ঠিক আছে শুধু মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে ট্রাকের চাকা। মাথাটা চ্যাপ্টা হয়ে রাস্তার সঙ্গে মিশে গেছে। ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে পুলিশের টাকা পয়সার সম্পর্ক। ট্রাফিক পুলিশের হাতে মোটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি একটা রিপোর্ট লিখলাম রোববারে। পুলিশ সম্পর্কে একটা আপত্তিকর মন্তব্য করে ফেললাম। লাইনটির ওপর ‘ছিপি’ লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হল পত্রিকা। ছিপি তুলে পুলিশরা সেই লাইন পড়ল এবং দেশের সব পুলিশ ক্ষেপে গেল। ’৮৩ সালের কথা। পুলিশের ঊর্ধ্বতন একজন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, তিনি লেখক। রফিক আজাদ যখন টাঙ্গাইলের করোটিয়া কলেজের বাংলার লেকচারার তখন তাঁর ছাত্র ছিল আরেফিন বাদল। বাদল ভাইর সঙ্গে মোসলেহউদ্দিন সাহেবের খুবই খাতির। বাদল ভাইকে ধরে দিনের পর দিন ছুটোছুটি করে আমাকে রক্ষা করলেন রফিক ভাই। সেই আতঙ্কের দিনে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত রফিক ভাই আমার হাতটা ধরে রেখেছেন, আমার পাশে থেকেছেন। রাতেরবেলা তাঁর বাড়িতে নিয়ে রেখেছেন আমাকে। নিজের বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও থাকলে পুলিশ যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়!
সেই লেখার অপরাধে রোববার থেকে আমার চাকরি চলে গেল। রফিক আজাদ এবং আরেফিন বাদলের চেষ্টায় মুসলেহউদ্দিন সাহেব ব্যাপারটা ম্যানেজ করলেন।
চাকরি নেই, রফিক ভাইর সঙ্গে তারপরও প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়, আগের মতোই চলছে আড্ডা হৈ চৈ, পানাহার। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর চাকরি বাকরি করব না, লেখাই হবে আমার পেশা। বাংলাদেশে তখনও পর্যন্ত শুধু লেখাকে পেশা করার সাহস পায়নি কেউ। আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়সের যুবক ইমদাদুল হক মিলন এরকম এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।
আত্মঘাতী কেন ?
তখন বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় একটা গল্প লিখলে বড়জোড় ২০ টাকা পাওয়া যায়। পত্রপত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। প্রকাশকদের পায়ে ধরলেও বই ছাপাতে চায় না। ঈদসংখ্যা বেরোয় দুতিনটা। উপন্যাস লিখলে টাকা পাওয়া যায় তিনশো থেকে পাঁচশো। তারপরও নাক উঁচু পত্রিকাগুলো তরুণ লেখকদের পাত্তা দেয় না।
আমার তখন কী যে মর্মান্তিক অবস্থা। পছন্দের মেয়েটিকে বিয়ে করেছি। সে সন্তান সম্ভবা। বড়ভাইর সংসারে থাকি, দশটা টাকা রোজগার করতে পারি না। উঠতে বসতে নানা প্রকারের অপমান। সহ্য করতে না পেরে একদিন স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার শ্বশুরপক্ষ টাকাঅলা কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন সদভাব নেই। মেয়েটি নিজের পছন্দে আমার মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করেছে, জার্মানির মতো দেশে গিয়েও যে দুটো পয়সা রোজগার করে ফিরতে পারেনি, শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া আমার নিষেধ। কিন্তু বড়ভাইর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। স্ত্রী বেচারিটি মন খারাপ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। ওর বাবা নেই, মা এবং দুভাই। সে তাদের নয়নের মণি। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মা খুবই কান্নাকাটি করলেন, ভাইরা বুকে টেনে নিল বোনকে। ওদের যৌথ পরিবার। ছয়মামা এবং একবোন বিশাল একটা বাড়ির একেক ফ্ল্যাটে থাকেন। বোন সবার বড়। সেই বোনের মেয়েটি আমার স্ত্রী। মামা-শাসিত সংসার। আমার শাশুড়ির পিঠোপিঠি ভাইটি সংসারের অধিকর্তা। তাঁর আদেশে বিশাল পরিবারটি চলে। আমার শ্বশুর অল্প বয়সে মারা যান। ব্যবসায়ী ছিলেন। টাকা পয়সা ভালোই রেখেই গেছেন। শাশুড়ি সেই টাকা বিজনেস করার জন্য ভাইকে দিয়েছেন। লঞ্চ জাহাজের ব্যবসা করে অগাধ টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেছে পরিবারটি। ভদ্রলোক যেমন টাকাঅলা তেমন রাগী। আমার মায়ের মামাতো বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। সম্পর্কে আমার খালু, অন্যদিকে স্ত্রীর বড়মামা। আমার সঙ্গে ভাগ্নির বিয়েতে তিনিই বাগড়া দিয়েছিলেন। আর তাঁর আদেশের বাইরে কিছুতেই যাবে না পরিবারটি। তবু আমাদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বিয়ের পর ওই বাড়িতে যাওয়া আমাদের নিষিদ্ধ হয়েছে। তারপরও দায়ে পড়ে স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে সেই বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। ওই যে সে নিজ থেকে গিয়েছে তাতেই পাথরটা গলে গেল। মা ভাইরা তো তাকে বুকে টেনে নিলই, মামা মামিরা, মামাতো ভাইবোনরাও নিল।
কিন্তু আমি তখনও ওই বাড়িতে ঢুকিনি। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি রাত কাটাই। দুতিনটা দিন মাত্র। শ্বশুরবাড়ির কাছে লম্বা মতন একটা ঘর ভাড়া নিলাম। ওপরে টিন চারদিকে ইটের দেওয়াল। ভাড়া সাতশো টাকা। নিজেদের বাড়ি থেকে আমার বিয়ের খাটটা, দুটো সিলিং ফ্যান আর আমার লেখার টেবিলটা নিয়ে এসেছি। তাদের প্রাসাদের মতো বাড়ির পাশে এরকম একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, স্ত্রী লজ্জায় সেই বাড়িতে আসে না। টিফিন কেরিয়ারে করে দুবেলা আমার খাবার পাঠায়। ফ্যানের হাওয়ায় ঘর ঠাণ্ডা হয় না। গরমে ঘামে ভাসতে ভাসতে আমি মাথা গুঁজে উপন্যাস লিখি।
ওই ঘরে এসে রফিক আজাদ আমাকে একদিন দেখে গেলেন। আমার দুঃখ দারিদ্র্যের জীবন, অপমানের জীবন পাত্তাই দিলেন না। অতিকষ্টে আমি একটা কেরু কোম্পানির জিনের পাইট ম্যানেজ করেছিলাম, ওই খেয়ে জীবন ও সাহিত্য নিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে চলে গেলেন। সেই ভাষণে মন এবং কব্জির জোর তৈরি হল। ভূমিপুত্র নামে একটা উপন্যাস লিখলাম, কিছু প্রেমের গল্প লিখলাম। প্রকাশকদের সঙ্গে কথা হলো প্রতিমাসে ৪/৫ ফর্মার একটা করে প্রেমের উপন্যাস লিখব, তাঁরা থোক কিছু টাকা দেবেন।
লিখতে লাগলাম। জীবন বদলাতে লাগল।
তখন সারাদিন লিখি, সন্ধ্যায় গিয়ে রফিক আজাদের সঙ্গে আড্ডা দিই। এসময় রফিক ভাইর কবিতার বই বেরোল। বইয়ের নাম ‘প্রিয় শাড়িগুলো’। বইটা আমাকে উৎসর্গ করলেন।
রফিক ভাইর সঙ্গে এদিক ওদিক সাহিত্য সম্মেলনে যাই। যশোর না খুলনায় যেন সাহিত্যের আলোচনা সভার সভাপতির হঠাৎ শখ হলো ঢাকা থেকে আগত কবি এবং ঔপন্যাসিকের চেহারা দেখবেন। তিনি এই দুজনকে কখনও দেখেননি।
আমার হাত ধরে মঞ্চে উঠলেন রফিক আজাদ। বললেন, সভাপতি সাহেব, আমাদের চেহারা দেখে আপনার ভালো লাগবে না। আমরা লিখি ভালো কিন্তু চেহারা জলদস্যুদের মতো।
ভদ্রলোক হতভম্ব।
এসব করে আমাদের দিন যায়। রফিক আজাদের দুটো বই সম্পাদনা করলাম আমি। বাছাই কবিতা এবং প্রেম ও প্রকৃতির কবিতা। ততদিনে রফিক ভাই তাঁর জীবন বদলে ফেলেছেন। হঠাৎ হঠাৎ তাঁকে কেমন অন্যমনস্ক এবং বিষণ্ন হতে দেখি। এমন মন খারাপ করা একেকটা কবিতা লেখেন,
বালক ভুল করে নেমেছে ভুল জলে
বালক পড়েছে ভুল বই
পড়েনি ব্যাকরণ, পড়েনি মূলবই।
এইসব কবিতা পড়ে আমার বুক হু হু করে, ইচ্ছে করে রফিক আজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁর হাতটি ধরে বলি, প্রিয় বালক রফিক আজাদ, আমি এখনও সেই আগের মতোই তোমার অনুরাগী।
রফিক ভাই চলে গেছেন, রয়ে গেছে তাঁর অমূল্য একেকটি কবিতা। সেই সব কবিতা কখনও পুরনো হবে না।
আনিসুজ্জামান স্যারের সঙ্গে কবে যে পরিচয়, সে কথা মনে পড়ে না। কবে যে ঘনিষ্ঠতা বা তাঁর স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় মিলল, সে কথা মনে পড়ে না। মনে হয় জন্মের পর থেকেই তিনি আমার মাথার ওপর ছিলেন। আমার দশদিক জুড়ে ছিলেন। স্যার ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। তাঁর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তনুমন জুড়িয়েছে। তাঁর মুখপানে তাকালে যে আলোর ছটা দেখা যেত সেই আলো অন্তরে গিয়ে পৌঁছাত আমার। এমন মায়াবী স্নিগ্ধ মানুষ জীবনে অনেক কম দেখেছি। মনে হয় দেখিইনি।
স্যারকে নিয়ে লিখতে বসে কত দিনকার কত কথা যে মনে পড়ছে। নূরজাহান লিখতে শুরু করলাম তিরানব্বই সালে। ‘আজকের কাগজ’ গ্রুপের সাপ্তাহিক খবরের কাগজে। স্যার সেই লেখা পড়তে শুরু করলেন। তখনও মোবাইল যুগ শুরু হয়নি। ল্যান্ডফোনে মাঝেমধ্যে ফোন করতেন। নূরজাহান নিয়ে কথা বলতেন। কথা একটাই ছিল, যেভাবে লিখছ লিখে যাও। তাড়াহুড়া কোরো না। লেখা লেখার গতিতে এগোক। ছোট করার চেষ্টা কোরো না। ভাবিও একই কথা বলতেন। কখনও কখনও খুব উচ্ছ্বসিত হতেন।
আমি স্যারের কথা মাথায় রেখে উপন্যাসটি লিখছিলাম। কলকাতার ‘আনন্দবাজার গ্রুপের’ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘আনন্দ পাবলিশার্সের’ কর্ণধার বাদল বসু আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ওই সময় তিনি একবার ঢাকায় এলেন। চারদিকে নূরজাহান নিয়ে কথা হচ্ছে শুনে বললেন, এই বই আমি ছাপব। অন্য কাউকে দেওয়ার কথা ভেবো না।
কিন্তু লেখা তো শেষ হয় না। বিক্রমপুর অঞ্চলের কত ঘটনা, কত চরিত্র! অঞ্চলের ইতিহাস আর প্রকৃতি, মানুষের জীবনযাপন প্রণালী সব কিছু এসে ভিড় করছে লেখায়। নূরজাহানের ঘটনা ঘটেছিল সিলেট অঞ্চলের কমলগঞ্জের ছাতকছড়ায়। সেই নূরজাহানকে আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম বিক্রমপুরে। ফতোয়ার শিকার নূরজাহানকে নেওয়া হয়েছিল প্রতীকী চরিত্র হিসেবে। এই নূরজাহান তো পুরো বাংলাদেশেরই। বাংলাদেশের যেকোনও অঞ্চলেই এমন অনেক নূরজাহান ধর্মীয় মৌলবাদ এবং অন্য নানা রকম সামাজিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমি বিক্রমপুরের লোক। ওই অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য সব আমার জানা। মাঠ নদী খাল গ্রীষ্ম বর্ষা আর শীত বসন্তের প্রকৃতি আমার চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে থাকে। কোন গাছের পাতা কখন রং বদলায়, তাও আমি জানি। আমি আমার চেনা পরিবেশে নূরজাহানকে নিয়ে এলাম।
কিন্তু লেখা শেষ হয় না। ওদিকে বাদলদা তাগিদ দিচ্ছেন। তাঁকে জানালাম লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে। কবে শেষ হবে বুঝতে পারছি না। ‘আনন্দ পাবলিশার্সে’র মতো প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বাদলদা। তীক্ষè বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী মানুষ। পরামর্শ দিলেন, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এনে শেষ করো। লিখে দাও ‘প্রথম পর্ব সমাপ্ত’।
বাদলদার পরামর্শ আমি নিলাম। ‘আনন্দ পাবলিশার্স’ থেকে প্রথম পর্ব বেরিয়ে গেল। মুদ্রণসংখ্যা পাঁচ হাজার। দেড়-দুই মাসের মাথায় দেশ পত্রিকায় নূরজাহানের বিজ্ঞাপন বেরোল। ‘চোখের পলকে দ্বিতীয় মুদ্রণ’। মুদ্রণসংখ্যা তিন হাজার। ‘আনন্দ পাবলিশার্স’ বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনে মুদ্রণসংখ্যা উল্লেখ করে।
আনিসুজ্জামান স্যার তখন ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে থাকেন। এক সন্ধ্যায় নূরজাহান নিয়ে গেছি তাঁর কাছে। বইটির শেষ পৃষ্ঠায় গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। কী রকম হতাশ গলায় বললেন, ‘প্রথম পর্ব সমাপ্ত’ মানে কী! লেখা শেষ করোনি ? বললাম, না স্যার। আরও বড় হবে। দ্বিতীয় পর্ব লিখতে হবে।
স্যার আর কিছু বললেন না। পরে এক ঘনিষ্ঠজনের কাছে শুনলাম, স্যার আনন্দ পুরস্কার কমিটির বিচারকদের একজন। তিনি চাইছিলেন নূরজাহান যেন আনন্দ পুরস্কার পায়। কিন্তু অসম্পূর্ণ বইয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ পুরস্কার হয় না।
আনন্দ পুরস্কার পাওয়া হলো না, কিন্তু স্যার যে নূরজাহান নিয়ে এভাবে ভেবেছিলেন তার মূল্য কম কি!
জনকণ্ঠ পত্রিকায় আমি একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখলাম। ‘অধিবাস’। দেশভাগের প্রভাব কিভাবে পড়েছিল বিক্রমপুর অঞ্চলের একটি গ্রামে! একজন হিন্দু ডাক্তার মণীন্দ্রকে ঘিরে কাহিনি। দেশভাগের প্রভাবে রাতারাতি কেমন বদলে গেছে এলাকার মানুষগুলো। মানুষ আর মানুষ থাকল না। হয় হিন্দু হয়ে গেল না হয় মুসলমান হয়ে গেল। উপন্যাসটির বক্তব্য ছিল এই রকম। নূরজাহানের মতো এই উপন্যাসেও বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। উপন্যাসটিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন স্যার। ফোনে বা দেখা হলে অধিবাস নিয়ে কথা বলতেন। ‘মাওলা ব্রাদার্স’ থেকে বইটি বেরোল। স্যারকে উৎসর্গ করলাম এই বই। বাংলা একাডেমি বইমেলায় স্যারের হাতে তুলে দিলাম। স্যার খুবই খুশি। উৎসর্গ পাতাটি খুলে দিয়ে বললেন, এখানে একটা সই করে দাও।
জীবনে ওই প্রথম সই করতে আমার হাত কাঁপছিল। এক ফাঁকে বললেন, নূরজাহানটা দ্রুত শেষ করো। এসব লেখা বেশি দিন ফেলে রাখতে হয় না।
তার পরও সাড়ে বারোশ পৃষ্ঠার নূরজাহান লিখতে আমার ১৮ বছর লেগেছিল। বাদল বসু প্রয়াত হয়েছেন। এখন আনন্দ পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রী সুবীর মিত্র। তিনি নূরজাহানের অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এবারও সেই প্রথম পর্বের মতো ঘটনা। এক হাজার রুপি দামের বইটি বছর দুয়েকের মধ্যে তিনটি সংস্করণ হলো। অখণ্ড সংস্করণ হাতে পেয়ে স্যার খুব খুশি। পড়ে কিছুদিন পর বললেন, তোমার আর কিছু না লিখলেও চলবে।
শুধু ওটুকুই। স্যারের কথায় আমার চোখে পানি এসেছিল। দিল্লির আই আইপিএম সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিল নূরজাহান। আর্থিক মূল্যে সে এক বিশাল পুরস্কার।
তারপর কত দিন কত অনুষ্ঠানে স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি তাঁর কথা। প্রতিটি মঞ্চেই তিনি সভাপতি বা প্রধান অতিথি। পরিচ্ছন্ন সুন্দর উচ্চারণে এত পরিমিতিবোধ থাকত তাঁর বক্তব্যে, শ্রোতাদের মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকত না। একটি বাড়তি শব্দও ব্যবহার করতেন না কখনও। সেই চেনা ঢোলা পায়জামা, স্যান্ডেল শু আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, ওই সামান্য পোশাকে কী অসামান্য এক ব্যক্তিত্ব! কোটি মানুষের মধ্যেও চোখে পড়ার মতো। যখনই স্যারের সামনে দাঁড়াতাম, মনে হত হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষের অনুরোধ কখনও ফেলতেন না। অনেক ছোট ছোট অনুষ্ঠানেও ঠিক গিয়ে হাজির হতেন। শুধু তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে জায়গাটার কিংবা মানুষগুলোর মিল থাকলেই সেই অনুষ্ঠানে স্যার উপস্থিত হতেন। কী অসামান্য পড়াশোনা! কী অপূর্ব জীবনদর্শনে আলোকিত একজন মানুষ!
হুমায়ূন আহমেদের ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন সমর। এক আড্ডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। তাঁর একটি কবিতা নিয়ে কথা বললেন। শুনে সুনীলদার চোখ কপালে উঠে গেল। এ কবিতাও আপনি পড়েছেন ? এ কবিতার কথাও আপনি মনে রেখেছেন ? এ তো আমি ভাবতেই পারছি না।
সমরেশ মজুমদার তো স্যারকে আনিসদা আনিসদা বলতে অজ্ঞান। জলপাইগুড়িতে স্যারকে আর ভাবিকে বেড়াতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা সমরেশদা লিখেছেনও।
তরুণদের সঙ্গে স্যার মিশতেন বন্ধুর মতো। কবি মারুফুল ইসলামকে খুব ভালোবাসতেন। অন্য প্রকাশের মাজহার কমলদের খুব ভালোবাসতেন। এ রকম কত প্রিয় তরুণ স্যারের সান্নিধ্য পেয়েছে।
বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে যখন কালি ও কলম পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলো, সম্পাদক পরিষদের উপদেষ্টা হলেন আনিসুজ্জামান স্যার। আর সম্পাদক আমাদের সবার প্রিয় হাসনাত ভাই। আবুল হাসনাত। এ আরেক তুলনাহীন মানুষ। কালি ও কলম প্রকাশের প্রস্তুতিপূর্বে ঢাকা ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্যার এবং হাসনাত ভাইও আছেন। হাসনাত ভাই আমাকে বললেন, প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা দুটো ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপব। কলকাতা থেকে লিখবেন সুনীলদা আর বাংলাদেশ থেকে আপনি। আমি একটু গাঁইগুঁই করছিলাম। কারণ লেখার কোনও প্রস্তুতি নেই। লেখা দিতে হবে দিন পনেরোর মধ্যে। ব্যাপারটা হাসনাত ভাই বুঝলেন। বুঝে ঠোঁট টিপে হাসলেন। ইশারায় আনিস স্যারকে দেখিয়ে বললেন, স্যার বলেছেন।
আমার আর নড়াচড়ার উপায় নেই। প্রায় দুই বছর ধরে লিখলাম পর উপন্যাসটি। কোনও কোনও কিস্তি লেখার সময় বেশ ফাঁকি দিতাম। স্যার প্রতিটি কিস্তিই মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। কিন্তু দুর্বল কিস্তিগুলো নিয়ে তিনি কিছু বলতেন না। ভাবিকে দিয়ে আমাকে ফোন করাতেন। ভাবি খুব নরম মাতৃসুলভ কণ্ঠে বলতেন, লেখায় আরেকটু মনোযোগী হওয়া দরকার। বুঝতাম এটা স্যারেরই কথা। বই করার সময় পর উপন্যাসের সেই দুর্বল অংশগুলো আমি নতুন করে লিখেছি।
স্যার তেমন বেশি লেখেননি। সেই কবে পড়েছি তাঁর পুরোনো বাংলা গদ্য নামের বইটি। মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট বই ‘মুনীর চৌধুরী’ পড়েছি। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়েছি তাঁর দুই পর্বে লেখা আত্মজীবনী কাল নিরবধি ও বিপুলা পৃথিবী। বিপুলা পৃথিবীর জন্য পেলেন আনন্দ পুরস্কার।
দেশে বিদেশে কত পুরস্কার পেয়েছেন স্যার। বাংলাদেশের সবগুলো জাতীয় পুরস্কার। ভারতের আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘পদ্মশ্রী’। শিক্ষাক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন। কিন্তু এসবে যেন তাঁর আসলে কিছু যেত আসত না। এত বড় মানুষটি যখন আমাদের সঙ্গে মিশতেন, মনে হত আমরা আমাদের এক সিনিয়র বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। অহংকার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। নিজের আলোয় তিনি এতখানি আলোকিত ছিলেন, সেই আলো পূর্ণিমা সন্ধ্যার মতো মোহময় করত চারদিক।
অন্যদিন পত্রিকার জন্য স্যারের একটা দীর্ঘ ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি। কোনও কোনও সন্ধ্যায় ইন্টারভিউ নিতে বসতাম হুমায়ূন আহমেদের ফ্ল্যাটে। আমার প্রশ্ন ধরে ধরে স্যার কথা বলে যাচ্ছেন। রেকর্ডার চলছে। স্যারের চারপাশ ঘিরে বসে আছি আমরা কয়েকজন। হুমায়ূন আহমেদ এবং তাঁর বন্ধুদল। আলমগীর রহমান, দুই করিম ভাই, মাজহার কমল নাসের মাসুম, মুনীর ভাই। ফাঁকে ফাঁকে খাওয়াদাওয়া চলছে। বেশ কয়েকটা সিটিং হলো এ রকম। একদিন স্যারের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারেও বসা হলো। এত বড় ইন্টারভিউ এবং এত বিষয় নিয়ে কথা, স্যার অতি সরল ভঙ্গিতে সব বলে গেলেন। অন্যদিনে সেই ইন্টারভিউ ছাপতে গিয়ে দেখা গেল, এত কথার পরও কোনও কোনও প্রসঙ্গ বাদ পড়ে গেছে। ছাপার আগেই ইন্টারভিউটা স্যার পড়লেন। তারপর এক বিকেলে এসে হাজির হলেন অন্যদিন অফিসে। অনেকটা রাত পর্যন্ত বসে কী যে মনোযোগ দিয়ে অসম্পূর্ণ জায়গাগুলো সম্পূর্ণ করলেন নিজ হাতে লিখে লিখে, স্যারের সেই একাগ্রতার দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না।
আনিসুজ্জামান স্যার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক বিশাল বটবৃক্ষ। তাঁর মায়াবী ছায়ায় আমরা স্নিগ্ধ হয়েছি। আমাদের মাথার উপরকার সেই ছায়া সরে গেছে। তবে সরে যাওয়ার পরও ছায়ার সবখানি রেশ চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে। মৃত্যু আনিসুজ্জামান স্যারকে একটুও মøান করতে পারেনি। চলে গিয়েও তিনি আসলে আমাদের মাঝে রয়েই গেছেন। কোন শক্তি তাঁকে সরায় আমাদের অন্তর থেকে!
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের রসবোধের তুলনা হয় না।
বিটিভি শুরু হলো ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। তখন নাম ছিল ‘ঢাকা টেলিভিশন’। সন্ধ্যার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা চলত। সোমবার বন্ধ থাকত। ৩১ ডিসেম্বর স্যার প্রথম অনুষ্ঠান করলেন। টেলিভিশনে তাঁকে নিয়ে গেলেন মুস্তাফা মনোয়ার। স্যার তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সবগুলো হলে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন। ডিবেট, উপস্থিত বক্তৃতা, নির্বাচিত বক্তৃতা, বাংলা ইংরেজি আবৃত্তি সবগুলোতেই চ্যাম্পিয়ন। থাকেন সায়েন্স কলেজের হোস্টেলে। মুস্তাফা মনোয়ার ও জামান আলী খান এসে সায়েন্স কলেজের হোস্টেলে হাজির। ‘আপনাকে অনুষ্ঠান করতে হবে। পরশু দিন রেকর্ডিং। কবি জসীম উদ্দীনের ইন্টারভিউ।’
জামান আলী খান পরে পাকিস্তান টেলিভিশনের এমডি হয়েছিলেন।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের টেলিভিশনযাত্রা শুরু হলো জসীম উদ্দীনের ইন্টারভিউ দিয়ে। প্রথম প্রথম স্বভাবতই খুব নার্ভাস। ধীরে ধীরে সেই অবস্থা কেটে গেল। একের পর এক অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। স্বাধীনতার পর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান শুরু করলেন। অনুষ্ঠানের নাম ‘সপ্তবর্ণা’। এই অনুষ্ঠান এমন জনপ্রিয় হলো, স্যারের রাস্তায় বেরোনো দুষ্কর। যদিও তখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন ছিল না, তবু উপস্থাপক হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। মানুষ তাঁকে দেখলেই হাসিমুখে তাকায়। কথা বলার জন্য এগিয়ে আসে। যেখানেই যান, সেখানেই দু-চারজন টিভি দর্শক ঘিরে ধরে। স্যারও ব্যাপারটা ভালোই উপভোগ করেন।
একদিন বাজারে গেছেন। বাজার করছেন। এক লোক এগিয়ে এল। ‘আপনাকে চেনা চেনা লাগে!’
স্যার ভাবলেন তাঁর ভক্ত। কথা না বলে হাসলেন।
লোকটা তাঁর দিকে তীক্ষèচোখে তাকাল। ‘আপনারে কোথায় দেখছি বলেন তো ?’
স্যারের মুখে সেই হাসি। মাত্র বলতে যাবেন, নিশ্চয় টেলিভিশনে দেখেছেন, তার আগেই লোকটি উৎফুল্ল গলায় বলল, ‘এই তো মনে পড়ছে। চিনছি আপনেরে। আপনে আমোগো মজিদের খালু।’
খুব রসিয়ে রসিয়ে এই ঘটনা বলেছেন স্যার। আমরা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছি।
ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাঁর ক্লাসে দেখা যায় ক্লাস উপচানো ছাত্র। বসার জায়গা না পেয়ে অনেকে দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার! এত ছাত্র এল কোত্থেকে ? আসলে স্যারের লেকচার শোনার জন্য অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা এসে ভিড় করেছে। ছাত্রদের কাছে এতই জনপ্রিয় হয়ে গেছেন তিনি।
‘কণ্ঠস্বর’ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি আর আমার বন্ধু সৈয়দ ইকবাল গল্প পাঠিয়েছি কণ্ঠস্বরে। সৈয়দ ইকবালের গল্পটা ছাপা হল, আমারটার খবরই নেই। পর পর দুটো গল্প ছাপা হয়ে গেল ইকবালের। ’৭৪-৭৫ সালের কথা। অন্য পত্রপত্রিকায় আমার গল্প ছাপা হয়, কণ্ঠস্বরে হয় না। লজ্জায় ব্যাপারটা চেপে গেলাম। কাউকেই কিছু বলি না। বহু বছর পর, যখন স্যারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সারা দিন ধরে চলেছে রমনার বটমূলে, অনুষ্ঠান শেষ করে স্যারকে ঘিরে আমরা কয়েকজন বসেছি আড্ডা দিতে, কথায় কথায় কণ্ঠস্বরে আমার গল্প ছাপা না হওয়ার ঘটনাটা বললাম। শুনে স্যার মজার ভঙ্গি করে বললেন, ‘ও, তুমি তাহলে একজন ব্যর্থ লেখক।’
আমরা সবাই হাসতে লাগলাম।
স্যার তাঁর কথোপকথন বইটি আমাকে উৎসর্গ করেছেন। এ আমার লেখকজীবনের এক বিশাল পুরস্কার।
এনটিভিতে একটা টক শো করেছিলাম ‘কী কথা তাহার সঙ্গে’। ১৫০ পর্বের পর আর করিনি। প্রথম অনুষ্ঠানটি করেছিলাম স্যারকে নিয়ে। আমি জানি পোশাকে, জীবনাচরণে, কর্মে আর কথায় তিনি আমাদের আদর্শ হয়ে উঠেছেন। টেলিভিশনে ‘সপ্তবর্ণা’, ‘চতুরঙ্গ’ এই দুটো নিয়মিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তো করলেনই, ফাঁকে ফাঁকে করলেন বেশ কয়েকটি ‘ঈদ আনন্দমেলা’। টিভি উপস্থাপক হিসেবে যখন জনপ্রিয়তার একেবারে তুঙ্গে, যে জনপ্রিয়তার লোভ সামলানো বাঙালির পক্ষে কঠিন, হঠাৎ করেই সেখান থেকে সরে এলেন স্যার। শুরু করলেন ‘বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র’। ’৭৮ সালের কথা। ইন্দিরা রোডের একটি বাড়িতে বই জড়ো করতে লাগলেন। বইয়ের আলোয় আলোকিত করতে শুরু করলেন ছাত্রছাত্রীদের, দেশের মানুষকে। ‘আলোকিত মানুষ চাই’ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্লোগান। দিনে দিনে ‘আলোকিত’ শব্দটি আলোকময় হয়ে উঠতে লাগল। এখন রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে দেশের শিক্ষকসমাজ, সুশীল শ্রেণি, ছাত্র অভিভাবক, সবার মুখে এই শব্দ। বক্তৃতা বিবৃতিতে, নাটকে সাহিত্যে, টক শোতে আর খবরের কাগজে কথায় কথায় আসছে ‘আলোকিত’ শব্দটি। এই শব্দের প্রকৃত জনক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।
কিছু মানুষ জন্মান কাজ করার জন্য। দেশ ও সমাজ বদলের জন্য। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তেমন একজন মানুষ। একের পর এক কাজ করে গেছেন তিনি। শিক্ষকতার মহান পেশায় ছিলেন। সেখান থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, মানুষের হাতে বই তুলে দেওয়ার ব্রত নিলেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দাঁড় করাবার জন্য কী অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করেছেন, কত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন, আমরা দেখেছি। অতি লক্কড়ঝক্কড় একটা গাড়ি ছিল। ড্রাইভার রাখার সামর্থ্য ছিল না। নিজে ড্রাইভ করতেন। ‘র্যামন ম্যাগসাইসাই’ পুরস্কার পেলেন। সেই টাকার কিছুটা খরচ করে অপেক্ষাকৃত ভালো একটা গাড়ি কিনলেন। থাকেন সেন্ট্রাল রোডের দুই বেডের ক্ষুদ্র একটি ফ্ল্যাটে। তাঁর লেখার জায়গাটি এত ছোট, ছোট্ট একটি টেবিল রাখার পর চারজন মানুষের বসার জায়গা নেই। ওইটুকু জায়গায় বসে আমরা বহুদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনেছি।
স্যার ‘বুড়িগঙ্গা বাঁচাও’ আন্দোলন করেছেন, পরিবেশ আন্দোলন করেছেন। ঢাকা যখন ডেঙ্গু আক্রান্ত হল, আমাদের নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে। স্কুলে স্কুলে গিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন আমাদের সঙ্গে। ডেঙ্গুর আবাসস্থলগুলো ধ্বংস করেছেন, মানুষকে সচেতন করেছেন। এডিস মশা কী, কোথায় বংশ বিস্তার করে, ডেঙ্গু আতঙ্ক যখন তুঙ্গে, তখন এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে চলে এল ডেঙ্গু। এখনও, এই বয়সেও তিনি কমপক্ষে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি করে দেশের জেলায় জেলায় বই পৌঁছে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের হাতে। বই পড়ো, আলোকিত মানুষ হও। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ধারণাটিও তাঁর। দেশের প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীকে বইপড়া কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। জেলায় জেলায়, স্কুলে স্কুলে বইপড়া প্রতিযোগিতা করেন। দুই দিনের অনুষ্ঠানে ১০-১২ হাজার ছেলেমেয়েকে পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যাবেলা প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হয় মোমবাতি। একসঙ্গে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার মোমবাতি। ওই দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা আসলে আলোকিত বাংলাদেশ দেখেছেন, আমাদের আগামী প্রজন্ম যাদের হাতে আগামী দিনের বাংলাদেশ, তাদের দেখেছেন।
এই মহতি কর্মের উদ্যোক্তা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে বহু বই প্রকাশিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সব বই। বিশ্বসাহিত্যের, বাংলা সাহিত্যের সেরা বইগুলো পাঠকের হাতে তুলে দেয় স্যারের প্রতিষ্ঠান। গত প্রায় ৪০ বছরে এত এত কৃতী মানুষ তৈরি হয়েছে এই কেন্দ্র ঘিরে, বাংলাদেশের যেকোনও সেক্টরে কেন্দ্রের ছেলেমেয়ে কেউ না কেউ আছেই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও আছেন স্যারের বহু কৃতী ছাত্র।
প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন স্যার। যদিও এই পুরস্কার তাঁর পাওয়া উচিত ছিল ২০-২৫ বছর আগে। ২০-২২টি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। ঢাকার ব্যস্ত জীবনে লিখতে অসুবিধা হয় বলে ঢাকার বাইরে এক তরুণ বন্ধুর বাড়িতে চলে যান। দু-চারদিন থেকে মনের মতো করে লিখে ফিরে আসেন। সংসারজীবনের দিকে কখনওই ফিরে তাকাননি।
একুশে পদক পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। সাধারণত বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পর একুশে পদক পান লেখকরা। স্যার একুশে পদক পেলেন আগে। তারপর পেলেন এশিয়ার নোবেল প্রাইজ খ্যাত র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। এই পুরস্কার পাওয়ার পর পৃথিবী বিখ্যাত সিএনএন টেলিভিশন স্যারের দীর্ঘ ইন্টারভিউ করল। খুবই জাঁদরেল এক মহিলা করলেন ইন্টারভিউ। স্যার তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে, স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে এত বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি ভাষায় ইন্টারভিউ দিলেন, পুরো পৃথিবী অবাক হয়ে এক কৃতী বাঙালিকে দেখল, তাঁর কথা শুনল।
স্যার আমাকে একদিন বলেছিলেন, ‘আমি জীবনে টাকার কথা ভেবে কোনও কাজ করিনি’। শুনে কেঁপে উঠেছিলাম। নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল স্যারের সামনে, মনে হয়েছিল আমি দাঁড়িয়ে আছি এক হিমালয়ের পায়ের কাছে। মাথা তুলে যতই ওপর দিকে তাকাই না কেন, হিমালয়ের চূড়াটা দেখতে পাই না।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার আমাদের একটি বাতিঘর। বাতিঘরের আলোয় গভীর সমুদ্রে পথ হারানো মানুষ পথের দিশা পায়। বাতিঘর আক্রান্ত হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় চারদিক। আমরা অন্ধকার চাই না। আমরা চাই আলো, আমরা চাই আলোকিত মানুষ।
যেদিন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে প্রথম দেখি সেই দিনটির কথা পরিষ্কার মনে আছে। চুয়াত্তর সালের শুরুর দিক। আমি জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। একটা দুটো লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে সাহিত্য পড়ি বেশি। ওসব নিয়েই আছি। বিকাল কাটে গেন্ডারিয়ার সীমান্ত গ্রন্থাগারে বই পড়ে। জগন্নাথে কি একটা উৎসব হচ্ছিল। নিচতলার পশ্চিম-উত্তর দিককার বিল্ডিংটার একটা বড় রুমে বাংলা বিভাগ দেয়াল ভর্তি করে রেখেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার বড় লেখক কবিদের নানা রকম উদ্ধৃতি লিখে। আমরা কয়েক বন্ধু সেই রুমে ঢুকেছি। উদ্ধৃতিগুলো পড়ছি। আমার খুব ভালো লাগছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নকশা থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা। বোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার লেখাটুকু পড়লাম। হঠাৎ একজন পেছন থেকে বললেন, কেমন লাগছে ? ফিরে তাকিয়ে দেখি রাজপুরুষের মতো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স একত্রিশ বত্রিশ। মাথাভর্তি কোঁকরানো চুল। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। চেহারায় প্রবল আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্ব। মুখের দিকে তাকালেই সমীহ জাগে। নিশ্চয়ই আমাদের কোনও শিক্ষক হবেন। বললাম, হুতোম পেঁচার নকশা সবচাইতে ভালো লাগল। তিনি হাসলেন, কেন বলতো ? আমি একটু ফাঁপরে পড়লাম। কী ব্যাখ্যা করব ? কোনও রকমে বললাম, লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম।
শুধু এটুকুই। তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন। বন্ধুরা আমাকে বলল, উনি হচ্ছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্যার। বাংলার টিচার।
ইন্টারমিডিয়েটের বাংলা ক্লাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে আমি কখনও পাইনি। আমাদের বাংলার ক্লাস তিনি নিতেন কিনা জানি না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় হলা আমি গল্প লিখছি, আর তখনকার উঠতি তরুণ লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। যেমন বুলবুল চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ফিউরি খন্দকার। বুলবুল এবং সিরাজের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সিরাজ বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। নারিন্দার স্বামীবাগে বাড়ি। সিরাজের বন্ধু হচ্ছে হেলাল। একই পাড়ায় বাড়ি। হেলাল জগন্নাথে বাংলায় অনার্স পড়ে। আমার আরেক বন্ধু নারায়ণগঞ্জের মুজিবুল হক কবীর জগন্নাথে বাংলায় পড়ে এবং কবিতা লেখে। এইসব বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা শুরুর পরেই দেখলাম তারা সবাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একাধারে ছাত্র এবং মহাভক্ত। ওরা সবাই তাকে স্যার স্যার করে। আমি ততদিনে জগন্নাথে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছি। ইলিয়াস স্যারকে হঠাৎই ভাই ডাকতে শুরু করলাম। দিনে দিনে তিনি আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন। থাকতেন বাংলা ভাষার আরেক বড় লেখক শওকত আলী স্যারের হাটখোলা রোডের বাড়ির নিচতলার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। তারপর চলে গিয়েছিলেন শওকত আলী স্যারের বাড়ি থেকে সোজা পুবদিকে রোজ গার্ডেনের কাছাকাছি একটা বাড়ির নিচতলার ফ্ল্যাটে। বেশ অনেকগুলো বছর সেই বাড়িতে তিনি ছিলেন। রাস্তা থেকে ইট বিছানো পথে উত্তর দিকে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে সেই বাড়ি। বুলবুল, সিরাজ, হেলালদের সঙ্গে মুজিবুল হক কবীর আর আরিফদের সঙ্গে ওই বাড়িতে কত বিকাল সন্ধ্যা আড্ডা দিয়েছি আমরা! ইলিয়াস ভাই বগুড়ায় গেলে সেই বাড়ি পাহারাও দিয়েছি। রাতেরবেলা দলবেঁধে থেকেছি, হইচই, করেছি। এই লেখা লিখতে বসে মনে পড়ছে সেসব দিনের কথা।
আড্ডায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তুলনা ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। চা আর পাইপ টানতেন। হা হা করে হাসতেন। অতুলনীয় রসবোধের অধিকারী। আড্ডা দেওয়ার জন্য অনেকগুলো জায়গা ছিল তাঁর। বাংলাবাজারের বিউটি বোডিং, নবাবপুরের হোটেল আরজু, গুলিস্তানের রেক্স রেস্টুরেন্ট। বন্ধুবান্ধবও ছিল প্রচুর। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, খালেদ চৌধুরী, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ। ‘গুলিস্তান’ রেস্টুরেন্টেও আড্ডা দিতেন। বুড়োভাই, বিপ্লব দাস, প্রশান্ত ঘোষাল আড্ডার সঙ্গী ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় যেমন ছাত্রদের সঙ্গেও তেমন। একসঙ্গে চা সিগারেট চলছে। হাসি ঠাট্টা মশকরা চলছে। তাঁর কে এম দাস লেনের ফ্ল্যাটেই বেশিরভাগ আড্ডা হয়েছে আমাদের। একটানা পাঁচ সাত ঘণ্টা, কখনও সারা রাত। তাঁর পড়াশোনা ব্যাপক। ইউরোপীয় সাহিত্যের পণ্ডিত বলা যায়। সব রকমের বিষয় নিয়ে আড্ডা দিতেন। সিনেমা প্রেম সংগীত সাহিত্য শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন কোনওটাই বাদ যেত না। একটা বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠিনতম মানুষ। লেখা ভালো না লাগলে সেই লেখক তাঁর যত প্রিয় মানুষই হন, কখনও তার লেখার প্রশংসা করতেন না। একটি উদাহরণ দিই। আমরা একবার তাঁকে এক লেখক সম্পর্কে ধরলাম। সেই লেখক ইলিয়াস ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ। নামটা আমি উহ্য রাখছি। কথাটা বোধহয় হেলাল তুলেছিল। সেই লেখকের নাম ধরে বলল, তিনি লেখেন কেমন ? তার লেখা আমার কেমন লাগে ? ইলিয়াস ভাই বললেন, সে মানুষ খুব ভালো। তারপর কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হেলাল আবার বলল, তার লেখা কেমন ? ইলিয়াস ভাই পাইপ টানতে টানতে বললেন, বললাম তো সে লোক খুব ভালো। তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। হেলাল নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ পর আবার বলল, বললেন না তিনি লেখেন কেমন ? ইলিয়াস ভাই খুবই সিরিয়াস মুখ করে বললেন, না না তুমি বুঝতেই পারছ না, সে লোক খুব ভালো।
আমরা হাসতে লাগলাম। বুঝে গেলাম তিনি ওই লেখকের লেখা নিয়ে কথা বলবেন না।
আমাদের হেলাল পরে আত্মহত্যা করে। তাঁর এই প্রিয় ছাত্র ও বন্ধুটিকে দোজখের ওম বইটি উৎসর্গ করেছিলেন ইলিয়াস ভাই।
১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ অন্য ঘরে অন্য স্বর। সেই বই বোদ্ধা পাঠক মহলের কলকব্জা নাড়িয়ে দিল। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সংবর্ত লিটল ম্যাগাজিনে এই বইয়ের সমালোচনা লিখলেন হাসান আজিজুল হক। তাঁর লেখায় নাম ছিল ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ’।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন খুব কম। মাত্র ২৮টি গল্প, ২টি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধ সংকলন। কিন্তু তিনি নিজেকে বলতেন ২৪ ঘণ্টার লেখক। শিক্ষকতা করছেন, পাইপ টানছেন, বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল আড্ডা দিচ্ছেন, কাঁধে ঝোলা, পরনে প্রিন্টের হাওয়াই শার্ট। সবার মধ্যে থেকেও আলাদা হয়ে গেছেন। পুরান ঢাকার প্রতিটি গলিঘুচি নিজের হাতের তালুর মতো চিনতেন। কোন গলির কী নাম তা মুখস্থ ছিল। ঢাকাইয়া ভাষাটা অসাধারণ জানতেন। এক সময় কিছুদিন গেন্ডারিয়ায় থেকেছেন। ফরিদাবাদ পোস্ট অফিসের ঠিক উল্টোদিকে ছিল তাঁর বন্ধু শাকের চৌধুরীদের বাড়ি। সেই বাড়ির নিচতলায় শাকের চৌধুরীর একটা ওষুধের দোকান ছিল। ওখানেও যেতেন কখনও কখনও আড্ডা দিতে। পঁচাত্তর সালে দৈনিক সংবাদে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। নাম চিলেকোঠায়। সাহিত্য পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সেই উপন্যাস। সরকার পরিবর্তনের পর উপন্যাসের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। এই উপন্যাসই চিলেকোঠার সেপাই নাম দিয়ে ’৮১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায়। দুই বছর ধরে লিখে সেই উপন্যাস শেষ করেছিলেন।
রোববার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল আটাত্তর সালের শেষদিকে। আমি সেখানে জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতাম। নির্বাহী সম্পাদক কবি রফিক আজাদ। ইলিয়াস ভাইয়ের বাসার কাছে ইত্তেফাক ভবনে অফিস। তিনি প্রায়ই আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন। রোববারের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সংখ্যায় লিখেছিলেন তাঁর ‘মিলির হাতে স্ট্যানগান’ গল্পটি। ঊনআশি থেকে একাশি সাল পর্যন্ত আমি ছিলাম জার্মানিতে। সেখানে বসে রোববারের ঈদ সংখ্যায় পড়লাম তাঁর ‘দুধ ভাতে উৎপাত’ গল্পটি। সেই সংখ্যায় সম্ভবত আমার কালোঘোড়া উপন্যাসটিও ছাপা হয়েছিল। কালোঘোড়া জার্মানিতে বসে লিখেছিলাম। ‘গাহে অচিন পাখি’ গল্পটিও ওখানে বসেই লেখা।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্য বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে আমি তাঁর সব লেখা পড়েছি। কোনও কোনও লেখা দু-তিনবারও পড়েছি। মনে আছে একবার খোয়াবনামা ও মার্কেজের ওয়ান হান্ড্রেট ইয়ার্স অব সলিচিউট পাশাপাশি পড়েছিলাম। পড়ে মনে হয়েছিল দুজন প্রায় একই রকমের মেধাবী লেখক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ইংরেজি কিংবা স্প্যানিশ ভাষায় জন্মালে, ফরাসি কিংবা জার্মান ভাষায় জন্মালে পৃথিবী তাঁকে মাথায় তুলে রাখত।
ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ভক্ত পাঠক প্রচুর। গায়ক কবীর সুমন প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন। খোয়াবনামা উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের টাকাটা তাঁর চিকিৎসার কাজে লেগেছিল।
ক্যান্সারের কারণে তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। ঢাকায় ফেরার পর একদিন তাঁকে দেখতে গেছি। গিয়ে বিস্মিত। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আগের মতোই আড্ডা দিচ্ছেন। শরীরে ক্যান্সার, পা কাটা পড়েছে, তোয়াক্কাই করছেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার রাতে ঘুম হয় ? নির্বিকার গলায় বললেন, হয়। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে কাটা পায়ের দিকে হাত চলে যায়। তখন ফিল করি পা-টা নেই। এমন মনের জোর হতে পারে মানুষের! কলকাতার ডাক্তাররাও তাঁর মনের জোর দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।
বাংলাবাজারে গেলে মাওলা ব্রাদার্সে বসতেন। মাহমুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। মাওলা ব্রাদার্স তাঁর প্রকাশক। ওখানে একদিন আমার সঙ্গে দেখা। আমার ভূমিপুত্র উপন্যাসটি তাঁর খুব পছন্দ ছিল। সেই প্রসঙ্গ ধরে বললেন, ‘আবোল তাবোল লিখে ভালো হাতটা নষ্ট কোরো না’।
ইলিয়াস ভাই যেদিন চলে গেলেন ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭। আমি সেদিন হুমায়ুন ফরীদির সঙ্গে কক্সবাজারে। ফরীদি সিনেমার শুটিং করে আর আমি হোটেলে বসে নাটক লেখার চেষ্টা করছি। শুটিং শেষ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসে ফরীদি। দুই বন্ধু মিলে আড্ডা দিই। ৪ জানুয়ারি দুপুরবেলা হোটেলে ফিরে এল ফরীদি। আমি অবাক। ফরীদির মুখটা বিষণ্ন। ধরা গলায় বলল, একটা দুঃসংবাদ আছে। শুনে কান্নাকাটি করিস না। ইলিয়াস ভাই চলে গেছেন। বলে নিজেই হু হু করে কাঁদতে লাগল।
বাংলা সাহিত্যের এক মহীরুƒহ মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দারুণ ভক্ত। তিনি লিখেছিলেন, ‘ইলিয়াসের পায়ের নখের যোগ্য কোনও লেখা লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম।’ খোয়াবনামা শেষ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা ছিল ইলিয়াস ভাইয়ের। তাঁর অকাল মৃত্যতে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হলো এক অমর উপন্যাস থেকে।
[চলবে]সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ