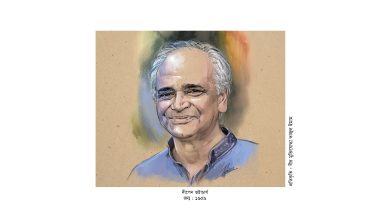১১৯তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ : রম্যজগতের অনন্য স্রষ্টা সৈয়দ মুজতবা আলী : ইয়াসমিন মাসহুদা
স্মরণাঞ্জলি
রম্যরচনাকে সরস, মার্জিত, সুকুমার ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে যিনি বিশিষ্ট হয়েছেন, তিনি হলেন বহু ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, রম্য রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী। ভ্রমণের নেশা ছিল তাঁর। দেশ-বিদেশ ঘুরে অভিজ্ঞতার যে রসদ আহরণ করেছেন তা আপন সৃজনশীলতায় তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। তাই ভ্রমণকাহিনি রচনার জন্যেও তিনি বিশিষ্ট। মুজতবা আলীর রচনাশৈলীর প্রধান আকর্ষণ গল্প বলার বৈঠকী রীতি। তাই তিনি বাংলা মজলিসি সাহিত্যের খ্যাতনামা শিল্পী হিসেবে পরিচিত।
মুজতবা আলীর জন্ম সিলেটের করিমগঞ্জে, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে। বাবা সাব-রেজিস্ট্রার সৈয়দ সিকান্দার আলী। মা আয়তুল মান্নান খাতুন। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে মুজতবার প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কেটেছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শৈশব থেকেই ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন।
একবার সরস্বতী পূজার সময়―দেশে তখন ইংরেজবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল জোয়ার। সিলেটও সেই আন্দোলনে উত্তাল। পূজা উপলক্ষে স্কুলের কিছু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো বাড়ি থেকে ফুল চুরি করে। এই দলে মুজতবা আলীও ছিলেন। এই ঘটনায় ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে তাঁর চাপরাশি ছাত্রদের বেত মারলে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। মুজতবার বাবাকে ডেকে তাঁর কাছে ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়। বাবা মুজতবাকে স্কুলে যেতে বললে তিনি কিছুতেই রাজি হন না। কেননা তিনিও ছিলেন ধর্মঘটী ছাত্রদের দলে। এরপর থেকে মুজতবা আর ঐ স্কুলে যাননি। লেখাপড়ার জন্য তিনি চলে যান শান্তিনিকেতনে। এই ঘটনার প্রায় বছর দুই আগে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এসেছিলেন। পরপর দুদিন দিয়েছিলেন বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘বাঙালির সাধনা’ এবং ‘আকাক্সক্ষা’। পনেরো বছর বয়সের কিশোর মুজতবা কবির বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে বসেন। কবির কাছে তিনি জানতে চান, আকাক্সক্ষা উচ্চ করতে হলে কী করণীয় ? কিছুদিন পর কবির পক্ষ থেকে চিঠির জবাব আসে। এটি ছিল মুজতবার কাছে অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আকাক্সক্ষা উচ্চ হতে হবে এ কথার মোটামুটি অর্থ হলো স্বার্থ যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গল ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার কী করা উচিৎ তা এত দূর থেকে বলে দেওয়া যায় না। তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।’ এই চিঠি মুজতবা আলীকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছিল।
পুত্রকে দূরে যেতে দিতে চাননি মা। তবে বাবার সমর্থন ছিল। ১৯২১ সালে মুজতবা শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলেন। দূর দেশে মায়ের জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হলো। এই ব্যাকুলতা সর্বদাই তাঁর মধ্যে বিরাজ করেছে এবং এই বেদনার রেশ তাঁর রচনায় নানাভাবে এসেছে।
মুজতবা ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম দিকের ছাত্র। শান্তিনিকেতনে প্রথম সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, ‘ওহে, তোমার মুখ থেকে তো কমলালেবুর গন্ধ বের হচ্ছে।’ এই ছোট্ট তামাশাটিও মুজতবার মনে ধরেছিল। ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুজতবা স্নাতক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত সনদ লাভ করেন। ঐ সনদের অলংকরণ করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। মুজতবা কেবল বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করেননি, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করেন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন বৃত্তিসহ। ১৯৩২ সালে ‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব’ বিষয়ে গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
মুজতবা আলীর জীবনের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল একাধিক ভাষার ওপর তাঁর দখল। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি লুসাই ভাষা শিখতে শুরু করেন। তিনি আবিষ্কার করেন লুসাই ভাষায় বাংলা বেশ কিছু শব্দের প্রতিশব্দ নেই। সেই থেকে তাঁর বিভিন্ন ভাষা নিয়ে অপার কৌতূহল। ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ানসহ মোট পনেরোটি ভাষা খুব ভালোভাবে জানতেন। শান্তিনিকেতনেই তিনি পাঁচ বছর জার্মান ভাষা শিখেছেন। অনুবাদক হিসেবে বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রয়েছে তাঁর। জানা যায়, ১৯৩৪ সালে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার অজিত বসু নিজস্ব কাজে ইউরোপ যাবার সময় দোভাষী হিসেবে মুজতবা আলীকে সঙ্গে নেন। তাঁরা ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, চেকোসেøাভাকিয়া ঘুরে ইতালির ভেনিস থেকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন। এখান থেকে ট্রেনে চেপে কায়রো যান। যদিও মিশর নিয়ে তাঁর জলে ডাঙায় রচনা লেখা হয়েছিল আরও আগে, ১৯২৯ সালে―মুম্বাই থেকে ফরাসি জাহাজ যোগে জার্মান যাবার অভিজ্ঞতা থেকে।
কাবুলের শিক্ষাদপ্তরের একজন অধিকর্তা হিসেবে মুজতবা আলীর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের শুরু। কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বরোদা কলেজ, দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বগুড়ার স্যার আজিজুল হক কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন পাটনা, কটক, কলকাতা এবং দিল্লিতে। এরপর ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং বিশ্বভারতীতে যোগ দেন।
মাত্র পনেরো বছর বয়সে মেজদাদা সৈয়দ মুর্তজা আলীর সঙ্গে মিলে কুইনিন নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সৈয়দ মুজতবা আলী নিয়মিত লিখতেন মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাম, আনন্দবাহার, দেশ, শনিবারের চিঠি, বসুমতি প্রভৃতি পত্রিকায়। ‘ওমর খৈয়াম’, ‘টেকচাঁদ’, ‘প্রিয়দর্শী’ প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনি লিখতেন।
মননশীলতা ও বৈঠকী মেজাজ মুজতবার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে এ দুয়ের সমন্বয় বিরল। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন রসিক, ভ্রমণপিপাসু। পৃথিবীর পাঠশালা ঘুরে তিনি সমৃদ্ধ হন। বোহেমিয়ান জীবনে অনুসন্ধিৎসু মন কত কী না খুঁজে ফেরে! সেসব তিনি জানেন, হৃদয়ে ধারণ করেন এবং পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। রচনায় তিনি কথা বলেন গল্পের মেজাজে। সাধারণ পরিচিত শব্দ দিয়ে কথার পিঠে কথার মালা গেঁথে তৈরি হয় পটভূমি। শব্দ দিয়ে তিনি ছবি আঁকেন। সেই ছবি পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয় ক্যানভাস আর রঙ-তুলির মিথস্ক্রিয়ায়। রাইন নদীর বর্ণনায় তিনি বলেন :
দু’দিকে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দু’পাড়ে যেন দুখানা সবুজ শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে শাড়ি দুখানা আবার খাঁটি বেনারসি। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারি, হোথায় নীল সরোবরের ঝলমলানি। যেন পাকা হাতের জরির কাজ। আর সেই শাড়ির ওপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মতো কারও কথা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদাকালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভেতর চাপা রঙের ট্রামের আসা-যাওয়া―সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব মনে হয় না।
হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধের উপস্থাপন তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তু অনুসারে প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতাও চমৎকার। অনেক সময় হাসির অন্তরালে বেদনা ও কঠিন উপলব্ধি তুলে ধরেন তিনি। সেই সঙ্গে মানবধর্মী বৈশ্বিক চেতনা এবং উদার সম্প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনাকে দেয় ভিন্ন মাত্রা। ধর্মীয় গোড়ামি নিয়ে লেখকের ভাষ্য, ‘উইলি ঠিকই বলেছে, ধর্মমাত্রই মোমবাতির আধা আলোর কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।’

মুজতবা আলীর বিভিন্ন রচনার মধ্যে রয়েছে উপন্যাস : অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শব্নম্ (১৯৬০), শহ্র-ইয়ার (১৯৬৯) ও তুলনাহীনা; ভ্রমণ সাহিত্য: দেশে বিদেশে (১৯৪৯), জলে ডাঙায় (১৯৬০), ভবঘুরে, মুসাফির, বিদেশে; রম্য রচনা ও ছোটগল্প: চাচা কাহিনি (১৯৫২), পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫৭), টুনিমেম (১৯৬৪), দ্বন্দ্বমধুর, চতুরঙ্গ, বড়বাবু, দু-হারা, সত্যপীরের কলমে, বহুবিচিত্র, ধূপছায়া। প্রবন্ধ গ্রন্থ : রাজা উজির, কত না অশ্রুজল, পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, বাংলাদেশ, উভয় বাংলা, ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য। আত্মজীবনী: দিনলিপি, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন। অনূদিত উপন্যাস: প্রেম।
বিশ শতকের শুরুতে মুজতবার উপন্যাস রচনার সূচনা। তাঁর রচিত চারটি উপন্যাসই নায়িকা-প্রধান। শব্নম্ ও শহ্র ইয়ার উপন্যাসের নায়িকা মুসলিম, অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নায়িকা ইউরোপীয় আর তুলনাহীনার নায়িকা হিন্দু। উপন্যাস পাঠে লেখকের অসাম্প্রদায়িক ও উদার চেতনাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। অবিশ্বাস্য নায়ক চরিত্র-প্রধান হলেও বাকি তিনটি উপন্যাসে নারী চরিত্র মুখ্য।
অবিশ্বাস্য উপন্যাসের মূল চরিত্র ডেভিড ওরেলি। তৎকালীন মধুগঞ্জ শহরের অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ। সুদর্শন এবং স্মার্ট। বিয়ে করে বিলেত থেকে সস্ত্রীক ফেরেন মধুগঞ্জে। স্ত্রী মেবল শিক্ষিত এবং সুন্দরী। এই দম্পতির জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। গভীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এর সূচনা, মর্মান্তিক পরিণতিতে হয়েছে এর সমাপ্তি।
শব্নম্ প্রেমের উপন্যাস। কাহিনি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। নায়িকা শব্নম্ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাহসী, দৃঢ়চেতা কন্যা সে। জন্ম প্যারিসে। তার বাবা সেনাপতি আরঙ্গজেব খান। শব্নম্ যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তার বয়স আঠার কি উনিশ। চলনে বলনে কিছুটা পশ্চিমা ধাঁচ। কিন্তু হৃদয়ে নিজ দেশের জন্য নিখাদ ভালোবাসা। সেই টানই তাঁকে দেশে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। উপন্যাসের নায়ক ও কথক মজনুন পেশায় শিক্ষক। আফগানিস্তানের পাগমান শহরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মজনুন আর শব্নমের দেখা হয়। প্রথম পরিচয়েই সপ্রতিভ এবং অপূর্ব সুন্দরী শব্নম্কে ভালোবেসে ফেলে মজনুন। স্বাধীন, মুক্তমনা শব্নম্ মজনুনের প্রেমে সাড়া দেয় এবং তারা বিয়ে করে। এদিকে বাচ্চা-ই-সাকা কাবুল আক্রমণ করলে সাকার লোকেরা শব্নম্কে ধরে নিয়ে যায়। সাকার একজন সেনাপতি শব্নমের সঙ্গে অশোভন আচরণে প্রবৃত্ত হলে শব্নম্ তার ব্যাগে থাকা বন্দুক দিয়ে সেই সেনাপতিকে গুলি করে পালিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শব্নম্কে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যায় মজনুন। শব্নমের চাচা মজনুনকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। উপন্যাসের শেষে শব্নম্ ফিরে আসে। আসে মজনুনের মানসপটে জ্যোতির্ময়ীর বেশে। এ পর্যায়ে লেখক তাঁর নায়ককে বাস্তবলোক থেকে নিয়ে যান কল্পলোকে। পঞ্চাশের দশকে রচিত এ উপন্যাসে, যখন মুসলমান নারী অন্তপুরবাসিনী, পর্দার অন্তরালে কাটে তাদের জীবন, সে সময় শব্নম্কে আধুনিক, প্রথাবিরোধী ও মুক্তমনা হিসেবে উপস্থাপন করে লেখক প্রগতিমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।
শহ্র ইয়ার উপন্যাসের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে শহ্র ইয়ার নামের একজন নারীকে কেন্দ্র করে। সে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রগতিশীল, সাহিত্যপ্রেমী এবং কিছুটা রহস্যময়ী। লেখক নিজেই উপন্যাসের নায়ক এবং কথক। লেখক-বর্ণনায় এ উপন্যাসে নায়ককে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
শহ্র ইয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। প্রধান চরিত্র শহ্র ইয়ার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অন্য মুসলিম মেয়েদের তুলনায় সব দিক থেকে আলাদা। সে নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তার ভেতর সাধারণ নারীসুলভ মানসিকতা থাকলেও চরিত্রের দৃঢ়তায় সে অনন্য। স্বামী ডাক্তার। অধিকাংশ সময় তিনি কর্মক্ষেত্র ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন। বিশাল বাড়িতে নিঃসঙ্গ শহ্র ইয়ার মুক্তি খুঁজে নেয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আর গানে। লেখকের সঙ্গে কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অন্তর্বেদনা। আভিজাত্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে বন্দি নিঃসঙ্গতায় যেন কিছুটা মুক্তি এনে দেয় লেখকের সান্নিধ্য। তার মন প্রশান্ত হয়। কেননা দুজনের রুচিতে চমৎকার মিল।
উপন্যাসের এক পর্যায়ে শহ্র ইয়ারের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন চমকে যাওয়ার মতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর তার মনকে দোলা দেয় না। নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে সে পিরের শরণাপন্ন হয়। তার মন কখনও বলে না যে, এতে শান্তি। তারপরও সে যায়। নিজের মনের সঙ্গে এ এক অদ্ভুত খেলা। লেখকের বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাঁর মনে হয়, যদি শুনতেন শহ্র ইয়ার আত্মহত্যা করেছে তাও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পিরের কাছে যাওয়া! শহ্র ইয়ার কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়, কিন্তু একটু শান্তির জন্য সে অবলম্বন খোঁজে। উপন্যাসের সমাপ্তির পথে দেখা যায় শহ্র ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা। অন্যদিকে স্বামীর উচ্চতর গবেষণার জন্য দুজনেরই সুইডেন যাওয়া স্থির হয়। শহ্র ইয়ার ফিরে পায় প্রত্যাশিত নতুন জীবন।
লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস তুলনাহীনা। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। নায়িকাপ্রধান এ উপন্যাসে নায়ক কীর্তি চৌধুরী ও নায়িকা শিপ্রা রায় রাজনীতি সচেতন। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়। পটভূমি কলকাতা, আগরতলা, শিলং এবং বাংলাদেশ। এ উপন্যাসের নায়ক কিছুটা লাজুক, শান্ত ও বিনম্র স্বভাবের। অন্যদিকে নায়িকা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বশীল ও সপ্রতিভ। বিতার্কিক হিসেবে সকলে তাকে চেনে। এক সময় দেখা যায় শিপ্রা সহজ, শান্ত স্বভাবের কীর্তি চৌধুরীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিপ্রার সান্নিধ্যে এসে নিজেকে গুটিয়ে রাখা কীর্তি হয়ে ওঠে উদ্যমী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাহসী। সে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে―যার মাধ্যমে অসীম সাহসী একজন কীর্তি চৌধুরীর পরিচয় মেলে।
প্রবন্ধ রচনায় মুজতবা আলী বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। এতে স্থান পেয়েছে মনীষীদের নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্য, মাতৃভাষা, মানবিক মূল্যবোধ, স্বদেশ, নীতিকথা, রম্যরচনা, ভ্রমণসাহিত্য প্রভৃতি। রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবপ্রেম, প্রকৃতি চেতনা, হাস্যরস তাঁর প্রবন্ধের মূল ভাববস্তু। তিনি লেখেন বৈঠকি ঢঙে, যেন সামনে বসে গল্প বলছেন। সাধু-চলিতের মিশ্রণ তাঁকে ভাবায় না। তাঁর রচনায় আছে নিসর্গ বর্ণনা ও কাব্যিক চেতনা। কোনও কোনও রচনা জুড়ে রয়েছে প্রচুর শ্রুতিমধুর কবিতা। পাঠক তাতে বিমোহিত হন। অনেক রচনা রম্য ভঙ্গিতে লেখা। তাতে হাস্যরস সৃষ্টিতে নজর কাড়ে শ্লোক ও রূপকের চমৎকার ব্যবহার। তাঁর সকল প্রবন্ধেই রয়েছে বহুমুখী মনন আর প্রজ্ঞার বিচিত্র প্রকাশ।
মুজতবা আলীর রসসাহিত্যভিত্তিক ভ্রমণকাহিনি দেশে-বিদেশে (১৯৪৯), জলে ডাঙায় (১৯৬০) ভবঘুরে, মুসাফির। এর মধ্যে দেশে-বিদেশে সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয়তা পায়। বগুড়ায় অবস্থানকালে তিনি এটি রচনা করেন। প্রথমে ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে প্রথম বই হিসেবে ছাপা হলে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং দেশে-বিদেশে সে বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। একই বছর সৈয়দ মুজতবা আলী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘নরসিংহ দাস’ পুরস্কার অর্জন করেন। আর দেশে-বিদেশে তাঁর লেখক জীবনের সেরা অর্জন বলে বিবেচিত। তাঁর অন্যান্য সম্মাননার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৬১ সালে ভারতের আনন্দ পুরস্কার এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশের একুশে পদক (মরণোত্তর)।
মুজতবা আলীর অস্তিত্বে বিশেষভাবে যিনি বিরাজমান ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। মুজতবার উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা এবং প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়―কখনও কবিতা, কখনও গান, কখনও কোনও রচনা থেকে পঙ্ক্তি―উদ্ধৃতি হিসেবে। এ থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের কতটা জুড়ে ছিলেন। কবির লেখা বহু কবিতা, প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাসের অংশ মুজতবা মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। কবিরও অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন মুজতবা। কবিগুরুর উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন :
‘তারপর তব জয়রথ
বাহিরিল ঘর্ঘরিয়া, রুধিল না সমুদ্র পর্বত
বঙ্গভূমি কেন্দ্র করি রবিরশ্মি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
দিক্ হতে দিগন্তরে, বিশ্বলোক মানিল বিস্ময়
সর্বকণ্ঠে শুনি জয় জয়।’
রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও নজরুল, মধুসূদন, সত্যেন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, পরশুরাম, কেদারনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের রচনা মুজতবা আলীকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বসাহিত্যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে শেলি, কিটস, বায়রন প্রমুখ।
১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনে যিনি সকলকে―তাঁর বন্ধুবান্ধব ও প্রিয় পাঠকদের হৃদয় হাসি ও আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন―তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন অনেক কষ্টের অনুভূতিতে ভুগে। বোহেমিয়ান জীবনে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পারিবারিক সময় কাটিয়েছেন খুবই কম। জীবন সায়াহ্নে এসে এই বেদনাবোধ তাঁকে ভীষণ আক্রান্ত করেছে। ছিল অর্থকষ্ট। টাকার অভাবে ভুগে লিখেছেন, ‘আমার বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে। মানুষ আফটার অল পশু। একটু খেতে চায়। সেই বা কোথায় ?’
১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মুজতবা আলী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীরের ডান দিক অবশ হয়ে যায়। সেই হাত দেখিয়ে তাঁর এক প্রিয়ভাজনকে বলেছিলেন, ‘জান হে। সব শেষ। আর লিখতে পারবো না।’ এটিও ছিল লেখকের জীবনে সহজে মেনে নিতে না পারা নিদারুণ কষ্ট।
মুজতবা আলীর সকল সৃষ্টির মধ্যে রম্য রচনা বাংলা সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করেছে। এমন হালকা চালে, উপভোগ্য ভাষায় বিষয়জ্ঞানসমৃদ্ধ সৃজনশীল, সরস রচনা উপস্থাপনে মুজতবা আলীর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের যেখানেই গেছেন গল্পের আসর জমিয়ে শ্রোতার হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। রম্য সাহিত্যের এই অনন্য স্রষ্টা যুগ যুগ ধরে পাঠকের কাছে বরণীয় হয়ে থাকবেন।
লেখক : প্রাবন্ধিক