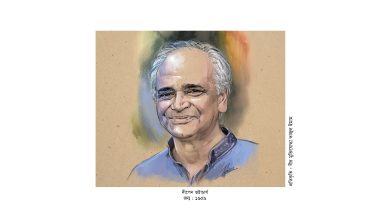শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধ : মানবর্দ্ধন পাল
ভাষা-গবেষণা ধারাবাহিক
দশম পর্ব
[প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা শব্দকে ‘ব্রহ্ম’ জ্ঞান করেছেন―শব্দ যেন ঈশ্বরতুল্য। পাশ্চাত্যের মালার্মেসহ নন্দনতাত্ত্বিক কাব্য-সমালোচকদেরও বিশ্বাস, শব্দই কবিতা। যা-ই হোক, শব্দের মাহাত্ম্য বহুবর্ণিল ও বহুমাত্রিক। বাংলা ভাষার বৃহদায়তন অভিধানগুলোর পাতায় দৃষ্টি দিলেই তা প্রতিভাত হয়। আগুনের যেমন আছে অসংখ্য গুণ তেমনই ভাষার প্রায় প্রতিটি শব্দেরও আছে অজস্র অর্থের সম্ভার। কালস্রোতে ও জীবনের প্রয়োজনে জীবন্ত ভাষায় আসে নতুন শব্দ, তা বিবর্তিতও হয়। পুরানো শব্দ অচল মুদ্রার মতো ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে মণি-কাঞ্চনরূপে ঠাঁই নেয় অভিধানের সিন্দুকে।বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমুদ্রসম―মধুসূদনের ভাষায় : ‘ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন’। বৈঠকি মেজাজে, সরস আড্ডার ভঙ্গিতে লেখা, এই ‘শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু’। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক―সবকিছু মিলিয়ে শব্দের ভেতর ও বাইরের সৌন্দর্য-সৌগন্ধ এবং অন্তর্গত আনন্দধারার ছিটেফোঁটা ভাষিকরূপ এই ‘শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু’ ধারাবাহিক।]
স্নান
ফেসবুকে কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি স্টেটাস দিয়ে শুরু করি। স্নান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : ‘স্নান করলাম’ এইটে বলা ঠিক হবে না। হঠাৎ করেই বাড়ি ফেরা পথে নামলো একেবারে আকাশভাঙা ধুম বৃষ্টি। আহা, কী সুন্দর স্বচ্ছশুদ্ধ জল! তবে এই বৃষ্টির জলধারা এড়ানো যেতো পথের পাশের কিছু বারান্দায় আরও অনেকের মতো। কিন্তু আমি সেপথে গেলাম না। আমি নিজেকে ভিজতে দিলাম শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টিজলে। যাকে বলে বৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করা। ঠিক তা-ই। গ্রীষ্মের দাবদাহে বৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণের আনন্দ যারা একবার পেয়েছেন―তারা জানেন, নারীর কাছে সমর্পণের আনন্দ কী অসীম!
বাথরুমে যারা স্নান করেন, তারা নগ্ন হন কি হন না―এই নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করেন না। এটা অভদ্রতা। আসলে ওটাই হলো স্নান। প্রকৃত স্নান করা বলতে আমি বাথরুমের স্নানটাকেই বুঝি। সেখানে পূর্ণ দেহে নিশ্চিন্ত মনে নগ্ন হওয়াটা আপনার জন্মগত অধিকার।
কদম্বতলে শ্রাবণের নবধারাজলে সবস্ত্রে গা-ভেজানোটা রবীন্দ্রনাথ স্নানের মর্যাদা দিলেও, আমি তাকে কখনও স্নান বলি না।
আমি কী বলি জানেন ? আমি বলি―‘শ্রাবণের হঠাৎ বৃষ্টিতে আমি শরীরটা ভিজিয়ে নিলাম জলে।’
নির্মলেন্দু গুণের স্নান সম্পর্কে এমন বক্তব্যে কাব্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির জাল থাকলেও দুই কবির মধ্যে রুচির পার্থক্যটিও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্নানের সময় শরীরে কাপড় থাকা বা না থাকাটা স্নানের একমাত্র শর্ত কি না, তা বিজ্ঞদের বিতর্কের বিষয়। সবস্ত্র ও নির্বস্ত্র স্নানের ভেদাভেদ যা-ই থাকুক তাতে স্নানের প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। সেসব দার্শনিক বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় : এখানেই দুই কবির মধ্যে―রবীন্দ্রনাথ ও নির্মলেন্দু―আকৃতিতে মিল থাকলেও প্রকৃতিতে পার্থক্য। কবিদের পাশ কাটিয়ে আমরা আমজনতা ‘স্নান’ বলতে কী বুঝি তা অভিধানের আলোকে জেনে নিই।
অভিধান বলে ‘স্নান’ অর্থ : * চান * নাওয়া * নাহা * অবগাহন * নিমজ্জন * ডুবন * ডুব দেওয়া * সান * গা-ভেজানো * গোসল * অবগাহ * অভিষেক * গা- ধোওয়া * অভিষেচন * গাত্রপ্রক্ষালন * গাহন * গাহ * বিগাহ * গায়ে জলঢালা * সলিলপ্রবেশ * জলপ্রবেশ * গাত্রপ্রক্ষালন। এর মধ্যে বেশকিছু শব্দ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক―অঞ্চলভেদে ব্যবহার হয়। স্নান ছাড়া অন্য তৎসম শব্দগুলো লেখ্য সাধুরূপে থাকলেও কথ্যরূপে অচল। এদেশে আরবি শব্দ ‘গোসল’ এবং পশ্চিমবঙ্গে স্নানের তদ্ভব রূপ ‘চান’ সুপ্রচলিত। ব্রজবুলি ভাষায় স্নানের কাব্যিক ও কোমল রূপ ‘সিনান’ (স্নান > সিনান > সান > চান)। ‘তুমি কোন দিনে যমুনা সিনানে গিয়াছিলা নাকি একা।’ (বড়ু চণ্ডীদাস)।
স্নানের আছে বিচিত্র প্রকারভেদ : মুক্তিস্নান, মোক্ষস্নান, তীর্থস্নান, পুণ্যস্নান, প্রাতঃস্নান, রৌদ্রস্নান, আতপস্নান, সূর্যস্নান, ধারাস্নান, বাষ্পস্নান, স্বেদনস্নান ইত্যাদি। তীর্থদর্শনে গিয়ে নিকটস্থ নদী, সরোবর বা সাগরে অবগাহনকে তীর্থস্নান বা পুণ্যস্নান বলে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের পর স্নান করতে হয়। তাকেই বলে ‘মুক্তিস্নান’। কোনও বাসনা পূর্ণ হলে যেকোনও তীর্থস্থানের জলাশয়ে স্নান করাকে বলে ‘মোক্ষস্নান’। রৌদ্রদগ্ধ প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতহীন অবস্থায় আপনি ঘেমে নেয়ে উঠেছেন―একেই বলে ‘স্বেদনস্নান’ বা ‘ঘর্মস্নান’। স্বেদ ও ঘর্ম―দুটি শব্দই তৎসম এবং অর্থ ‘ঘাম’―ঘর্ম > ঘম্ম > ঘাম। বাষ্পস্নান মানে, ভাপ দিয়ে সর্বাঙ্গ সিক্তকরণ। ইংরেজিতে একে বলে―ঠধঢ়ড়ঁৎ নধঃয. রৌদ্রস্নান বা সূর্যস্নান হলো, সূর্যকিরণে সর্বাঙ্গ তাপিত করা (ঝঁহনধঃয)। এসব স্নান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অঙ্গ। সমুদ্রতীরের রৌদ্রময় বালুকাবেলায় পাশ্চাত্যের গৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গীরা সংক্ষিপ্ত পোশাকে শুয়ে থাকে সুদীর্ঘ সময়―এরই নাম সূর্যস্নান বা রৌদ্রস্নান।
স্নান প্রাত্যহিক জীবনের একটি আবশ্যিক ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া―অন্তত বাঙালিসমাজে। শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা তো জীবনেরই অঙ্গ। তাই স্নান পুত-পবিত্রতার অন্যতম লক্ষণ। পরিচ্ছন্নতা এবং সুস্থতার জন্যে স্নানের বিকল্প নেই। স্নান মানে তো আপাদমস্তক প্রক্ষালন―আমুণ্ডুনখাগ্র ধৌতকরণ। স্নান শব্দটি সংস্কৃত বা তৎসম। এর অর্ধতৎসম রূপ ‘সিনান’। শব্দটি অনেক সময় আমরা ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহার করি! কিন্তু এটি স্নানের কোমল ও কাব্যিক রূপ। মধ্যযুগের গীতিকবি চণ্ডীদাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন এভাবে―
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
এ কাব্যবাণীর মধ্যে জীবনের গভীরতম বিষাদ লুকিয়ে আছে―হয়তো অন্তহীন দার্শনিকতাও।
স্নানের সঙ্গে হরিহর সম্পর্ক জলের। বিনা মেঘে বজ্রপাত হতে পারে, বিনি সুতোর মালা হতে পারে কিন্তু বিনা জলে স্নান হয় না―অন্তত বাঙালির জীবনে। আমার মনে হয়, স্নানের সঙ্গে জলের যেমন আন্তরিক সম্পর্ক তেমনি মানবদেহের সঙ্গে জলেরও। আমাদের শরীর অন্তরে যেমন জল চায় তেমনই বহিরঙ্গেও জল চায়। জলের চাহিদা ভেতরে-বাইরে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলের মতোই মানবদেহেও নাকি সত্তর ভাগ পানি―শরীর বিজ্ঞানীরা এমনটিই বলেন।
পৃথিবীর সব ধর্মে নিশ্চয়ই স্নানের রীতিনীতি আছে―আছে দোয়া-স্তুত্র-মন্ত্র। বাল্যকালে সনাতনধর্মের স্নানের মন্ত্রটি শিখেছিলাম। এখনও একটু মনে আছে : ‘ওঁ গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরি…।’ তবে অন্য রকম স্নানও আছে―সেটি শারীরিক নয়, মানসিক। সনাতনী শাস্ত্রে আছে―‘ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবাং সর্বাবস্থানে… বাহ্য অভ্যন্তরে শুচি।’ মন্ত্রটি বলে শরীরে জলের ছিটা দিলেই স্নান হয়ে যায়, সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়! সেটি আত্মিক শুদ্ধতা কিংবা মনের প্রশান্তিমাত্র। তাতে আত্মিক প্রশান্তি হয়তো মিলে কিন্তু দৈহিক স্বস্তি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন : ‘শীতল জলে জুড়াইলে’ কিংবা ‘এসো নীপবনে, ছায়াবীথি তলে এস, কর স্নান নবধারাজলে’―এ তো অমূলক নয়! মাতৃময়ী প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে, নৈসর্গিক কোমল-তরল স্পর্শে দেহেমনে পরিশুদ্ধ হওয়া! তাই তো বোধ করি জলের আরেক নাম জীবন। তবে একই সঙ্গে এও মনে রাখি যে, জীবনের অপর নাম জল নয়।
আমরা আগেই জেনেছি, স্নান শব্দটি সংস্কৃত―√স্না + অন = স্নান। ভারতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রে কত ধরনের স্নান যে আছে তার কোনও সীমা-সংখ্যা নেই! এ মুহূর্তে মনে পড়ছে―প্রাতঃস্নান, ঊষাস্নান, অষ্টমীস্নান, গঙ্গাস্নান, বারুণীস্নান, ত্রিবেণীস্নান, অদ্রিস্নান―আরও কত কী! তবে পৌরাণিক বিধি অনুসারে স্নান পাঁচ প্রকার : অগ্নিস্নান, বরুণস্নান, ব্রাহ্মস্নান, বায়ুস্নান ও দিব্যস্নান। এসব স্নানই পৌরাণিক এবং পুণ্যের। রবীন্দ্রনাথ বর্ষবরণের গানে লিখেছেন, ‘অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’ শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে পৌরাণিক অগ্নিস্নান ও রাবীন্দ্রিক অগ্নিস্নান হয়তো সমার্থক। তবে মনে প্রশ্ন জাগে, পাশ্চাত্যের ‘সানবাথ’ তারই নবায়ন ? প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অগণিত সাহিত্য-সাধক ‘স্নান’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি নিদর্শন :
* কে না সুতিত্থে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
(বড়ু চণ্ডীদাস, ১৪৫০)।
* স্নান করাইয়া রাজা দেহত মেলানি।
(মালাধর বসু, ১৫০০)।
* স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
(কৃষ্ণদাস, ১৫৮৮০)।
* স্নান করি সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে ফিরিলা লঙ্কারপানে…। (মধুসূদন, ১৮৬০)।
সনাতন ধর্মে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার আগে বহুবার স্নান করতে হয়। সেসবের একটির নাম অদ্রিস্নান। সনাতনীরা গঙ্গাস্নান করে পাপস্খলনের জন্যে। সেখানে পুণ্যসঞ্চয়ের চেয়ে পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যই বড়! শুনেছি, কন্যা-সম্প্রদানের পর মাতাপিতাকে না কি গঙ্গাস্নান করতে হয়! মেয়ে বিয়ে দেবার পর গঙ্গাস্নান কেন ? মেয়ে জন্ম দিয়ে কি পিতামাতা পাপ করেছে! এসব নারীবিদ্বেষী শাস্ত্রের কুসংস্কার। বাঙালির লোকজীবনে তো এমন প্রবচনও আছে : ‘শত পুত্র, এক কন্যা যদি পাত্রে পড়ে।’ শত পুত্রের চেয়েও একটিমাত্র কন্যা মহার্ঘ হয় যদি সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করা যায়। তবে তাতেও কিন্তু পুরুষতন্ত্রেরই জয়জয়কার!
শীতকালে স্নান-যে কত অঘটন ঘটায় এবং বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে তার বিবরণ আছে রবীন্দ্রনাথের ‘সামান্য ক্ষতি’ কবিতায়। যারা পড়েছেন তারা এর ভেতরের মর্মটি নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন―
বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছ সলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখিসনে
কাশীর মহিষী করুণা।
তারপর স্নানশেষে শীতার্ত সম্রাজ্ঞী শুরু করে দেন মহা বিড়ম্বনা। শীত-নিবারণের জন্যে সখীদের নির্দেশ দেন গরিবের ঘরে আগুন লাগাতে! ‘… উঁহু শীতে মরি/ সকল শরীর উঠিছে শিহরি/ জ্বেলে দে আগুন ও লো সহচরী / শীত নিবারিব অনলে।’
অনেকের কাছেই শীতকালের স্নান মানে মহাশক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা! অনেকে তো কেবল শীতকালে নয়, বারো মাসই গোসলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করেন। কিন্তু কবি নির্মলেন্দু গুণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণই অন্য রকম মানুষ। তাঁর আত্মস্মৃতি ‘আমার কণ্ঠস্বর’-এ সম্ভবত পড়েছি, তিনি পুরো শীতকালে―পৌষ-মাঘ দুমাস―একদিনও স্নান করেন না! শীতের শেষ রাত পেরিয়ে বসন্তের প্রথম দিন এলে একটা পুরো লাক্স সাবান গায়ে ঘষে নিঃশেষ করেন। শীতে বোধ করি তাঁর জলাতঙ্ক হয়! কত বিচিত্র স্বভাব মানুষের!
স্নান শব্দটির সঙ্গে ‘স্নাত’ ও ‘স্নাতক’ শব্দদুটির গভীর আন্তঃসম্পর্ক আছে : √স্না + ত = স্নাত এবং √স্না + তক/অক = স্নাতক। স্নাত মানে, স্নান করেছে এমন : ‘বাদলের জলে স্নাত বনানী।’ স্ত্রীলিঙ্গার্থে স্নাতা। আর স্নাতক শব্দের অর্থ, স্নানকারী। কিন্তু এর পৌরাণিক অর্থ : ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপন করে গার্হস্থ বা সংসারজীবনে প্রবেশকারী। তাই বৃন্দাবন দাসের লেখায় আছে : ‘শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।’ স্নাতক আবার তিন প্রকার―বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাব্রতস্নাতক। যদিও আমরা এখন জানি, গ্র্যাজুয়েশানের বাঙলায়ন হলো স্নাতক। প্রাচীন কালে, পৌরাণিক যুগে আমাদের উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহ-ভিত্তিক। সেই গুরুগৃহে বেশ কয়েক বছরের জন্যে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা গিয়ে ধর্মগ্রন্থের পাঠ নিত। সেই সঙ্গে চাষাবাদ ও পশুপালনসহ গুরুর সংসারের সমস্ত কাজকর্মই করত। শিষ্যের শিক্ষা পূর্ণ হলে গুরুদেব শুভদিন দেখে শিষ্যকে স্নান করিয়ে এনে পূজাপার্বণ করে তার শিক্ষা সমাপ্তির ঘোষণা এবং বিদায় দিতেন। পবিত্র স্নানের মাধ্যমে শিষ্যের এই শিক্ষা-সমাপ্তির বিষয় থেকে এখন ব্যাচেলার বা এৎধফঁধঃব ডিগ্রির বাংলা হয়েছে স্নাতক। আর চড়ংঃমৎধফঁধঃব মানে স্নাতকোত্তর।
স্নান নিয়ে এই সাতকাহন পাঁচালি বা প্যাঁচালের কারণ হলো সম্প্রতি (২০২০) একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক মজার সংবাদ। তা-ই এখন সংক্ষেপে বলি―
ব্রিটেনে নিবাসী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক সুন্দরী মডেল ও গায়িকা। তার নাম কামালিয়া। মহাবিত্তশালী ব্যবসায়ী মো. জহুরের স্ত্রী তিনি। তার বাইশ জন গৃহপরিচারিকা। তার হাতঘড়িটির দাম চল্লিশ লাখ এবং চশমার দাম চার লাখ টাকার বেশি। এই সুন্দরীর আছে এক অদ্ভুত সখ যা শুনলে আশ্চর্য তো হবেনই, এমনকি আঁতকেও উঠবেন! স্নানের জন্যে আমরা যে জল ব্যবহার করি তিনি তা মোটেই পছন্দ করেন না! স্নানের জন্যে তিনি প্রতিদিন লক্ষলক্ষ টাকা ব্যয় করেন! জলের পরিবর্তে তিনি স্নানে ব্যবহার করেন বিশ্বের সবচেয়ে দামি মদ শ্যাম্পেন! এজন্যে প্রতিদিন তার খরচ হয় এক কোটি টাকার বেশি! আর তার স্নানে প্রতিদিন দরকার হয় বিশ থেকে পঁচিশ বোতল শ্যাম্পেন। বিলাসিতা, সখ ও বিলাসবহুল জীবন আর কাকে বলে ?
আমাদের কামনা শুধু এটুকুই―বেঁচে থাক বাংলার নদী, পুকুর আর নলকূপের জল। বেঁচে থাক মেঘমালা, অঝোর বর্ষণ, গঙ্গোত্রী হিমবাহ আর বঙ্গোপসাগর!
জল
জল নিয়ে জলোকথা দিয়েই শুরু করা যাক। আমরা সবাই জানি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। বিজ্ঞান বলে, দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেনের পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটলে একটি জলের অণু সৃষ্টি হয়। জল স্বাদ-বর্ণহীন তরল পদার্থ―যে পাত্রে সে পাত্রের আকার ও রং ধারণ করে। জীবনধারণের জন্য জল অপরিহার্য। এজন্যই বলা হয়, জলের অপর নাম জীবন। তবে সেই জলকে অবশ্যই হতে হবে জীবাণু ও ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত এবং সুপেয়। এসব নিশ্চয়ই শিশুতোষ জ্ঞানের কথা। যেসব সবজিতে জলের আধিক্য তার মধ্যে চালকুমড়ো এবং লাউ প্রধান। মানুষ লাউ বা চালকুমড়ো নয় তবু বিজ্ঞানীরা বলেন, মানবদেহে নাকি তিন ভাগই জল। সারবস্তু মাত্র একচতুর্থাংশ। পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে মানবদেহের মেলবন্ধনটি বোধকরি এখানে! পৃথিবীর মানচিত্র এবং দেহের ভূগোল এখানে যেন একাকার।
শৈশবে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় আকিকুল স্যারের কাছে প্রায়শই শুনতাম একটি আপ্তবাক্য : ‘জলবৎ তরলং’। ক্লাসে অংকের সমাধান করতে তাঁর কাছে গেলেই তিনি নাকের ডগায় চশমা এঁটে কথাটি বলতেন। তখন না বুঝলেও এখন বুঝি, জলের তারল্যগুণ সহজ অর্থে বুঝিয়েছেন। কৈশোরে সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ নাটকটি মঞ্চায়ন করতে গিয়ে জলের বিচিত্র প্রকাশ পাই জনৈকের জবানিতে―
‘কত জল খেলাম―কলের জল, নদীর জল, ঝরণার জল, পুকুরের জল কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল―।’…
‘জলের কথা বলতেই কুয়ওর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচরকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে…’।
‘বিষ্টির জল, ডাবের জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিকজল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল…।’ জলের বিচিত্র রূপের সরস বর্ণনা আমরা পাই সুকুমার রায়ের সেই শিশুতোষ নাটকে।
বহুরূপী জলের কথা তো জানা গেল। এবার জলের স্বরূপ জেনে নিই। ‘জল’ শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত এবং পদে বিশেষ্য। সংস্কত-চর্চিত বাংলা এমন এক সমৃদ্ধ ভাষা যে ভাষায় সমার্থক শব্দ বিপুল। অশোক মুখোপাধ্যায়ের সংসদ সমার্থ শব্দকোষ থেকে জেনে নিই জলের প্রতিশব্দগুলো : বারি, সলিল, নীর, অপ, অম্বু, উদ, উদক, পয়্, অম্ভ, তোয়, পানি, উডু, সরঃ, ইরা, ইলা, পাথ, কর্বূর, সম্বর, তামর, শীতোত্তম, বরুণ, জীবন, প্রাণদ। এসব শব্দের গোটাসাতেক ছাড়া অন্যগুলো বাংলা ভাষায় অচল এবং অভিধানের পাতায় আশ্রিত।
এসব সমার্থক শব্দ ছাড়াও জলের আছে অনেক প্রকারভেদ। বিশেষণ প্রযুক্ত করে এর ভিন্নতা প্রকাশ করা হয়। যেমন―স্বচ্ছ জল, পরিষ্কার জল, নির্মল জল, টলটলে জল, ঘোলা জল, অপরিষ্কার জল, মৃদুজল, ক্ষরজল, গুরুজল, নোনাজল ইত্যাদি। এসব বিশেষায়িত জলে গুণই প্রকাশ পায়। তবে আটপৌরে বাংলায়, প্রতিদিনের কথোপকথনে সাধারণ পানি এবং জল শব্দই ব্যবহৃত হয়। তবে শব্দ দুটি উৎসমূল ও বুৎপত্তির বিচারে রক্তসম্পর্কহীন না হলেও বাঙালির সমাজমনস্তত্ত্বে সাংঘর্ষিক। আমরা শব্দদুটিতে ধর্মীয় তকমা ও সাম্প্রদায়িকতার সিলমোহর এঁটে দিয়েছি। লক্ষণীয় যে, দৈনন্দিন জীবনে হিন্দুসম্প্রদায় ব্যবহার করে ‘জল’ আর মুসলিমরা করে ‘পানি’। যদিও ধর্মভিত্তিক শব্দ থাকলেও ভাষার কোনও ধর্ম নেই তবু এ নিয়ে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে বাদানুবাদ কম হয়নি। পাকিস্তানপন্থি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা জলকে সংস্কৃত ও হিন্দুয়ানি শব্দ এবং পানিকে আরবি ও মুসলমানি শব্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও আমরা জানি, দুটোই তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। কবি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় এক বাক্যে দুটো শব্দকে মোহন মিলনে ব্যবহারের চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন―‘শহুরে পানির ফোয়ারা শোনাতো তাকে জলকিন্নরীর কত গান।’ এবার জল ও পানি শব্দের বুৎপত্তির দিকে একটু চোখ ফেরাই।
সংস্কৃত √পা ধাতু থেকে পানি শব্দের উৎপত্তি। তরল পদার্থটি পেয় বা গলাধঃকরণযোগ্য। এই √পা ধাতুর বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ তৈরি হয়। যেমন : √পা+অন = পান, পান+ই = পানি, √পা+ অনট = পানীয় (সংস্কৃত), পান+ঈয় = পানীয় (বাংলা)। এর প্রাকৃত রূপ ‘পাণিঅ’ থেকে পাণি, পাণী, পানী, পানি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শব্দটি উল্লিখিতভাবে লেখা হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে―‘যৌবন বাধে পাণির ফোটা।’ চৈতন্যভাগবতে আছে―‘আহার পাণি নিদ্রারহিত।’ ‘সেই ঝারখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।’ (কৃষ্ণদাস, ১৫৮০)। ‘জোয়ারের পানী নারীর যৌবন গেলে না ফিরিবে আর।’ (চণ্ডীমঙ্গল)। এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, সেকালে পাণি, পাণী, পানী, পানি ইত্যাদি বানান জল অর্থেই ব্যবহৃত হতো। মূলত সংস্কৃত ‘পানীয়’ শব্দ থেকেই ‘পানি’ শব্দের উদ্ভব। তাই ওপার বাংলার গঙ্গাতীর মানুষ পানিকে ‘জল’ আর এপার বাংলায় জলকে ‘পানি’ বললেও ‘পানীয়’ শব্দে কারও আপত্তি নেই। জল আমাদের জীবন আর পানি আমাদের প্রাণ।
আর ‘পাণি’ যখন হাত অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর বুৎপত্তি ভিন্ন : √পণ্+ই (ইণ্) = পাণি। যেমন বীণাপাণি, শূলপাণি, শস্ত্রপাণি, পাণিগ্রাহী ইত্যাদি। কিন্তু ‘পান’ চিবিয়ে খাবার বস্তু তাম্বুল বোঝালে তার বুৎপত্তি ভিন্ন। সংস্কৃত শব্দ ‘পর্ণ’ থেকে পান। এই ‘পর্ণ’ কিন্তু অশ্লীলতার সঙ্গে যুক্ত পর্ণ নয়। সংস্কৃতে পর্ণ মানে পত্র বা পাতা―পর্ণ> পন্ন>পান। যেমন পর্ণকুটির, পর্ণপুট, পর্ণবীথি, পর্ণমোচী। সেজন্যই শীতকালে পাতাঝরা গাছকে আমরা ‘পর্ণমোচী’ বৃক্ষ বলি। সুতরাং তরল বস্তু গলাধঃকরণ করা পানের সঙ্গে চর্ব্য বস্তু পানকে যেন আমরা গুলিয়ে না ফেলি। তবে আমরা পানও খাই, পানিও খাই। চা খাই, চকোলেটও। অর্থাৎ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আমরা একাকার করে ফেলি! এসব বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির অব্যাখ্যাত আচরণ। তবে প্রশ্ন হতে পারে ডাল কী ধরনের খাবার ? তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। তবে খাদ্য হিসেবে ডালের চরিত্র নির্ভর করবে রান্নার পদ্ধতির ওপর। পাতলা ডাল পেয়, ঘন ডাল লেহ্য আর ভাজা ডাল চর্ব্য।
বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই জল শব্দটি প্রচলিত। এর কয়েকটি নিদর্শন―
* জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে।
(বড়ু চণ্ডীদাস, ১৪৫০)।
* জলে পসি তপ করে নীল উতপল। (ঐ)।
* না ভিজয় জলেত অগ্নিত না পোড়ায়।
(আলাওল, ১৬৮০)।
* জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ।
হাসি মুখে কও না কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
(মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১৬৫০)।
* আমি তাপিত পিপাসিত/ আমায় জল দাও।
(রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডালিকা, ১৯৩৮)।
জলসহযোগে বাংলা ভাষায় সন্ধি ও সমাসযুক্ত শতশত শব্দ আছে। সেগুলোর মধ্যে সমার্থক শব্দ যেমন আছে তেমনই সাধারণের অজানা বিচিত্র অর্থযুক্ত শব্দও আছে। উল্লেখযোগ্য তেমন কয়েকটি শব্দের বিচয়ন―
★ সমার্থক শব্দ―
* জলে নেমে সাঁতার বা খেলা বিশেষ অর্থে―
জলকৃড়া, জলক্রীড়া, জলকেলি, জল ছোঁড়া।
* কল্পলোকের জলবাসী যৌবনবতী সুন্দরী অর্থে―
জলকুমারী, জলকিন্নরী, জলকন্যা, জলপরি।
* জলের ঢেউ অথে―
জলকল্লোল, জলতরঙ্গ, জললহরী।
* টিফিন বা নাস্তা অর্থে―
জল খাবার, জলপান, জলযোগ, জলপানি, জলটল।
* ভারতীয় পুরাণমতে জলের দেবতা বরুণ অর্থে―
জলপতি, জলনাথ, জলদেবতা, জলেশ্বর, জলেশ, জলাধিপ।
* মেঘ অথে―
জলদ, জলধর, জলপতি।
* পদ্মফুল অর্থে―
জলপদ্ম, জলপুষ্প, জলফুল, জলজ লিলি, জলকুমুদী, জলমৃনাল।
* আবহাওয়া অথে―
জলবায়ু, জলবাতাস, জলহাওয়া।
* গতিময় জলের ধারা অর্থে―
জলপ্রপাত, জলধারা, জলপ্রবাহ, জলধার, জলরেখা।
* মেঘের শব্দ অর্থে―
জলদগগর্জন, জলদধ্বনি, জলদমন্দ্র।
* সমুদ্র অর্থে―
জলধি, জলরাজ, জলদলপতি।
* নির্বিষ সাপ-বিশেষ―
জলডোড়া, জলঢোঁড়া, জলবোড়া।
* জলভরা হাত অর্থে―
জল-অঞ্জলি, জলগণ্ডূষ, জলপাণি।
* জলজ প্রাণী অর্থে―
জলহস্তী, জলমার্জার, জলবিড়াল, জলখাসি।
* সহজ অর্থে―
জলবৎ, জলভাত, জাউভাত।
এবার ‘জল’ শব্দযুক্ত কয়েকটি অজানা ও অল্পজানা পদের অর্থ ও উদাহরণ―
* জলকে চলা (জল আনতে যাওয়া)। ‘জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি…।’ (নজরুল)।
* জলকিন্নরী (জলে বাসকারী দেবলোকের গায়িকা)। ‘শহুরে পানির ফোয়ারা শোনাতো তাকে জলকিন্নরীর কতো গান।’ (শামসুর রাহমান, ১৯৭২)।
* জলখ্যাংরা (জলে ভিজানো ঝাঁটা)। ‘তোমার বাড়ি ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।’ (দীনবন্ধু মিত্র, ১৮৬৩)।
* জলগোজা (ফল-বিশেষ)। ‘সো জলগোজা খাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।’ (প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮৫৮)।
* জলচল (সামাজিকভাবে খাদ্যগ্রহণ)। ‘তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪১)।
* জলচুড়ি (জলতরঙ্গ বাদ্য)। ‘বাজায়ে জলচুড়ি কিঙ্কিণী।’ (নজরুল)।
* জলজান (হাইড্রোজেন গ্যাস)। ‘তিনি জলজান বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই।’ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫)।
* ‘জলটুঙি (জলাশয়ের মাঝে তৈরি ঘর)। এবার আমি নিচ্ছি ছুটি, ছুটছি এবার জলটুঙিতে।’
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯১৫)।
* জলদোষ (পেটে জল জমা রোগ)। ‘দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জলদোষ।’ (রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৮৫৪)।
* জল-নটিনি (নৃত্যময়ী বর্ষা)। ‘তরঙ্গেরই নূপুর পরে জলনটিনি আয় নেমে।’ ( নজরুল, ১৯৩৩)।
* জলমণ্ডুক (জলের ব্যাঙ)। ‘জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায় সবে করতলে।’ (কৃষ্ণদাস, ১৫৮০)।
* জলমরু (মরুতুল্য নিষ্প্রাণ জলরাশি)। ‘সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৭)।
* জলমেয়ে (স্নানরত মেয়ে)। ‘সেই জলমেয়েদের স্তন ঠাণ্ডা, শাদা, বরফের কুচির মতন।’ (জীবনানন্দ দাশ, ১৯৩৬)।
* জলবাশ ( আরবি জলু + ফারসি বশ > জলবাশ। অশ্বারোহী সৈন্য)। ‘উজবক জলবাশে ঘিরিয়াছে চারপাশে।’ (ভারতচন্দ্র, ১৭৬০)।
ইএইএ* জলাঙ্গী (নদীবিশেষ)। ‘জলাঙ্গীর ঢেউযে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।’ (জীবনানন্দ, ১৯৩২)।
জল শব্দটি নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনও কম নেই। অর্থসহ এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচন―
* জল হওয়া (রাগ প্রশমিত হওয়া, * জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয় সংকট), * জলে পড়া (বিপদে বা অপাত্রে পড়া, * জলে ফেলা (অপাত্রে দান বা অপচয়), * জলে যাওয়া (বৃথা ব্যয়), * জলের দাম (খুব সস্তা)।
নদীমাতৃক দেশ বলেই আবহমান কালের বাংলা গানে এসেছে জলের প্রসঙ্গ। এই জল কখনও জোয়ার-ভাটার, কখনও জীবন-যৌবনের প্রতীক, কখনও বিলয়-বিধ্বংসের হাহাকারে ভরা। ভারতীয়
পুরাণ ও সাহিত্য-ঐতিহ্যে গঙ্গাজল পুণ্যের, যমুনার জল প্রেমের এবং পদ্মার জল সমৃদ্ধির পতাকা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বৈষ্ণব গীতিকবিতা, পুরনো দিনের বাংলা গান, মরমি লোকসংগীত, পঞ্চকবির গীতসম্ভার ইত্যাদিতে জলের প্রসঙ্গ বিপুল ধারায় জলছলছল। তাই জলের প্রসঙ্গ আছে, এমন গানের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাবে না! প্রভাতে ও প্রদোষকালে যমুনায় বা জলাশয়ে কুলবধূদের জল আনার দৃশ্য এখন হারিয়ে গেলেও তা বাংলা গানে ও বাঙালির প্রাণে আছে চিরন্তন হয়ে। জলকে চলা রমণী এখন চোখে পড়ে না! কিন্তু আমাদের দুই মহান কবিবর তাঁদের কবিতা ও গানে তা মনে করিয়ে দেন―
‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!’
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!―রবীন্দ্রনাথ।
…
জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি
রূপ ছাপে না তার নীল শাড়ি।―নজরুল।
জল-বিষয়ক পর্বটি এমন উদ্ধৃতি-কণ্টকিত হয়ে গেল যে, পড়তে পড়তে পাঠক জলাতঙ্কে আক্রান্ত না হলেই রক্ষা! প্রাণসত্তার উৎস যে জল তা যদি প্রাণঘাতী হয় তবে বিড়ম্বনার অন্ত নেই! তাই একটু হাসির খোরাক―
এক কৃপণ সখ করে একটি আলখাল্লা বানিয়েছে। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের পর সেটি ছিঁড়ে গেলে এর ভালো অংশ দিয়ে একটি স্কার্ফ তৈরি করল। সেটিও ছিঁড়ে গেলে তার ভালো অংশটুকু দিয়ে তৈরি করল একটি রুমাল। রুমালটিও ছিঁড়ে গেলে সেটি পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে দাঁত মেজে কুলি করছে আর বলছে―আমার আলখাল্লা তৈরির হাজার টাকা আসলে জলেই গেল।
পদ্মা-বন্দনা
মহাকালের নদী পদ্মা। প্রাগৈতিহাসিক নদী পদ্মা। পৌরাণিক নদী পদ্মা। বিভিন্ন রূপে পুরাণে ভূগোলে ইতিহাসে এই নদীর অবস্থান। ইতিহাস বলে, গঙ্গোত্রী হিমবাহের অনিঃশেষ বরফগলা জলধারা থেকে এই নদীর উৎপত্তি। সুদীর্ঘ এই নদীর ভারতীয় অংশের নাম গঙ্গা। বর্তমান বাংলাদেশের বক্ষপট ভেদ করে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত এর নাম পদ্মা। ভারতীয় পুরাণমতে, অভিশাপ্ত পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য ভগীরথ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গঙ্গাকে আনার জন্য ব্রহ্মার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু গঙ্গার প্রবল স্রোতধারা ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র শিব ছাড়া অন্য দেবতার ছিল না। তাই ভগীরথ শিবকে সাধনায় তুষ্ট করলে তিনি গঙ্গাকে জটায় ধারণ করে পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন। গঙ্গার পৃথিবীতে আগমন নিয়ে পুরাণে গোটাসাতেক উপকথা আছে। এজন্য গঙ্গার আছে ভিন্ন-ভিন্ন নাম―হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু জাহ্নবী, ভাগীরথী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল―এই তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার আরেক নাম ‘ত্রিপথগা’। এই পৌরাণিক বহুরূপী গঙ্গাই বর্তমান বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশপথ থেকে পদ্মা।
শত পাপড়ি-বিশিষ্ট একটি সুপরিচিত জলজ ফুলের নাম পদ্ম। বহুবর্ণিল এই ফুলের অনেক নাম―পঙ্কজ, কোরক, নলিনী, মৃণাল, নীলোৎপল, লালপদ্ম, রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তোৎপল আরও কত কী! নীলোৎপলের সঙ্গে আবার আছে রামায়ণের রামচন্দ্রের শরৎকালে দুর্গা দেবীকে অকালবোধনের সম্পর্ক। ‘পদ্ম’ শব্দটি বাংলা সাহিত্যে মানবদেহের কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যে তুলিত হয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই―পদ্মআঁখি, পদ্মচক্ষু, পদ্মহস্ত, পদ্মপুট, পদ্মকর, পদ্মাঞ্জলি, পদ্মনাভ, পদ্মযোনি, পদ্মাসন, পাদপদ্ম ইত্যাদি।
দেবী লক্ষ্মীর অপর নামও পদ্মা। লৌকিক দেবী মনসার নামও পদ্মা ও পদ্মাবতী। ভারতীয় পুরাণ থেকে জানা যায়, ভগবান কল্কি অবতার বৃহদ্রথ-রাজকন্যা পদ্মাকে বিয়ে করেন। হিন্দিতে পদ্মকে বলে ‘পদুমা’। মধ্যযুগের কবি আলাওলের বিখ্যাত কাহিনিকাব্যের নাম ‘পদ্মাবতী’। সবই ‘পদ্ম’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত। পদ্মের সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যুক্ত হলে পদ্মা হয়। বাঙালির লৌকিক ধর্মে সাপের দেবী মনসা। মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এর মধ্যে মনসামঙ্গল অনন্য। মনসামঙ্গলের অপর নাম ‘পদ্মাপুরাণ’। মনসামঙ্গলের রচয়িতাদের মধ্যে বিজয় গুপ্তই সেরা। রামায়ণে পদ্ম নামে এক ঋষির বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, সেই পদ্মমুনির নামানুসারে হয়েছে পদ্মানদীর নাম। সেই বর্ননায় আছে―
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব মুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গড়ায় ॥…
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথের সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
খরস্রোতা পদ্মানদী ভয়ংকর কল্লোলিনী। বর্ষায় পদ্মা আরও ভয়াবহ, দুকূলপ্লাবী এবং ধ্বংসোন্মুখ। কত গ্রামগঞ্জ, নগর-বন্দর, লোকালয় ও ফসলি খেত এই কূলপ্লাবী পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়েছে, কত মাঝিমাল্লার নাও ডুবেছে, কত মানুষ অকাতরে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব নেই। তাই এই নদী নিন্দার্থে রাক্ষুসে, কূলভাঙনি, সভ্যতা- বিনাশী। কৃষ্টি ও কীর্তিকে বিধ্বস্ত করেছে বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। নদীপ্রেমিক কবি মোহাম্মদ রফিকের পদ্মাকে নিয়ে লেখা কাব্যের নাম ‘কীর্তিনাশা’। পদ্মা একাধারে প্রাণঘাতী ও প্রাণদায়িনী। এর বহু বদনাম যেমন আছে তেমনই সুনামেরও অন্ত নেই। পদ্মার অনিঃশেষ জলধারা পলিতে সমৃদ্ধ করে ফসলি জমি। তাতে আমাদের কৃষিকৃষ্টি হয়েছে উর্বর―শস্যে-সবজিতে সমৃদ্ধ। বাঙালির খাদ্য ও জীবনরক্ষার বহুবিধ উপাদান প্রকৃতির পদ্মানদী আমাদের দান করে। তাই প্রাচীনকাল থেকে নদীকে ঘিরে দুপাড়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা। তাই তো রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বাঙালিকে আকুল করে―‘তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, শীতল জলে জুড়াইলে…।’
বাঙালির জীবনে জালের মত জড়িয়ে আছে অসংখ্য নদীনালা, খাল-বিল-ঝিল, হাওড়-বাঁওড়। মাইকেল তাঁর ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় নদীকে বলেছেন, ‘দুগ্ধস্রোতারূপী জন্মভূমির স্তনে।’ রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ছোট গল্প ও কবিতায় নদী এসেছে বিচিত্র রূপে―বিশেষত পদ্মানদী। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন : ‘বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন―খুব বেশি পোষমানা নয় কিছুটা বুনোরকম, তারপরেও পরম যতনে হাত বুলিয়ে ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে।’ সৈয়দ হক কবিতায় তেরো শত নদীর গুণগান করেছেন। নদী যেমন জীবনের সঙ্গে তেমনই জড়িয়ে আছে আমাদের শিল্পসাহিত্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে। পদ্মা-মেঘনা- যমুনা-তিতাস বাঙালির জীবন ও শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। পদ্মা নিয়ে রচিত হয়েছে কত কথাসাহিত্য, কবিতা, ছবি, চলচ্চিত্র ও গান। তাতে রূপায়িত পদ্মাপাড়ের জীবনচিত্র ও মানুষের জীবন-সংগ্রাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ এবং আবু ইসহাকের ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ এর উজ্জ্বল উদাহরণ।
বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে গৌতম ঘোষের পরিচালনায় ‘পদ্মানদীর মাঝি’ চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। উপন্যাসটির আরম্ভই হয়েছে পদ্মায় ইলিশ ধরার বর্ণনা দিয়ে―‘বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ ধরার মরশুম চলিয়াছে।’ তাছাড়াও সুবোধ বসুর ‘পদ্মা প্রমত্তা নদী’, প্রমথনাথ বিশীর ‘পদ্মা’, আবু জাফর শামসুদ্দিনের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘পদ্মা মেঘনা যমুনা’ উল্লেখযোগ্য। সুবোধ বসুর উপন্যাসটি ভারতে চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে।
ইতঃপূর্বে ইলিশের প্রসঙ্গ যখন এলই তখন লিখতেই হয়, পদ্মার ইলিশের চেয়ে সুস্বাদু ইলিশ আর নেই। রূপে-গুণে-স্বাদে-গন্ধে এবং আকার-আকৃতিতে অতুলনীয়। ইলিশের স্বামীগৃহ সমুদ্র হলেও বাপের বাড়ি পদ্মানদী। এককালে বাঙালিবধূরা যেমন সন্তানসম্ভবা হলে চলে আসত পিতৃগৃহে তেমনই পোয়াতি ইলিশ চলে আসে বাপের বাড়ি পদ্মায়। বর্ষায় এসে প্রসবোত্তর শরতে আবার ফিরে যায় স্বামীগৃহ সমুদ্রে। এ যেন শারদীয় দুর্গোৎসব শেষে হিমালয়কন্যা পার্বতীর পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন। বছরে একবার চলে আসা-যাওয়ার এই আয়োজন। ভোগে ও সম্ভোগে পদ্মা তাই আমাদের প্রাণের নদী।
প্রাচীনতম বাংলা কাব্য সংকলন চর্যাপদেও পদ্মানদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভুসুক পা-এর চর্যায় যে ‘পউয়া খাল’-এর কথা আছে তা পণ্ডিতেরা পদ্মানদী বলেই ধারণা করেছেন। পদ্মা নিয়ে রচিত কবিতার কথা মনে হলেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে। যতদূর জানা যায়, পদ্মা নিয়ে তাঁর দুটো কবিতা আছে―‘পদ্মা’ এবং ‘পদ্মায়’। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন―
হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার। (পদ্মা)।
‘পদ্মায়’ শীর্ষক শিশুতোষ কবিতায় তিনি লেখেন :
আমার নৌকা বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে―
জানি নে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কবিগুরু যে পদ্মায় বহুবার যাত্রাপথে নৌভ্রমণ করেছেন তারই যেন সাক্ষ্য হয়ে আছে এই দুটি কবিতা।
পদ্মার প্রলয়ংকরী ও রুদ্রভৈরবী রূপ বর্ণনা করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘পদ্মার প্রতি’ কবিতায় লিখেছেন―
হে পদ্মা! প্রলয়ংকরী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগলভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী।
বুদ্ধদেব বসুর একটি কিশোর কবিতার নাম ‘নদীর স্বপ’। সেখানে দ্বিতীয়র চাঁদের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে পদ্মা―
আমারে চেনো না ? মোর নাম খোকা/ ছোকানো আমার বোন/ তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা/ মেঘনা-পদ্মা শোন।/… সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু/ আগে চলো পদ্মায়/ দুপুরের রোদে রুপো ঝলমল/ সাদা জল উছলায়।
বুদ্ধদেবের এই কবিতায় নদীদর্শনের শুভ উদ্বোধনই হচ্ছে পদ্মার মাধ্যমে।
কবি ফররুখ আহমদ ‘পদ্মা’ শীর্ষক সনেটে লিখেছেন―
কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু-দুরন্ত হার্মাদ
তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হয়েছে পাণ্ডুর।
…
বর্ষায় তোমার স্রোতে ভেসে গেছে সাজানো বাগান
অসংখ্য জীবন আর জীবনের অজস্র সম্ভার।
পদ্মাপাড়ের কবি জসিমউদ্দীনের অনেক কাব্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে পদ্মা―
পূর্ণিমাদের আবাস ছিল টেপাখোলার গাঁয়/ একধারে তার পদ্মানদী কলকলিয়ে যায়।
বিপ্লবের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও প্রমত্তা পদ্মার প্রলংকরী রূপ সমাজ-রূপান্তরের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছেন―হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ/ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে।
ভাটিয়ালি বাংলার ঐতিহ্যবাহী গান। নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকজীবনে ও মাঝি-মাল্লাদের দরদি কণ্ঠে গাওয়া ভাটিয়ালি গানে পদ্মা নদী রূপায়িত হয়েছে বিচিত্র ব্যঞ্জনায়। পদ্মাকে নিয়ে রচিত গানে খ্যাতিমানদের মধ্যে আছেন নজরুল, জসীমউদ্দীন, আবদুল লতিফ, আবু জাফর, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ। পদ্মা নিয়ে নজরুলের বিখ্যাত গান―‘পদ্মার ঢেউ রে
মোর শূন্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।
…
ও পদ্মা রে, ঢেউয়ে তোর ওঠায়
যেমন চাঁদের আলো
মোর বধুঁয়ার রূপ তেমনই ঝিলমিল
করে কৃষ্ণকালো।
নজরুলের এই গান এত জনপ্রিয় যে, প্রজন্মান্তরেও তা বাঙালির হৃদয়ে গেঁথে আছে।
আবদুল লতিফ-রচিত গানটি গেয়েছেন পল্লিগীতির সম্রাট আবদুল আলীম। এই জনপ্রিয় গানটির কথা―
সর্বনাশা পদ্মানদী/ তোর কাছে শুধাই/ বল আমারে তোর কি রে আর/ কূলকিনারা নাই।।/… পদ্মারে তোর তুফান দেইখা/ পরান কাঁপে ডরে/ ফেইলা আমায় মারিস না তোর/ সর্বনাশা ঝড়ে ॥
কবি জসিম উদদীনের গানে পদ্মানদীর সঙ্গে যাযাবর বেদেজীবনের কথা উঠে এসেছে। ভাসমান ও শেকড়বিহীন বেদে আত্মপরিচয় দিয়ে গানে বলছে―
ও বাবু, সেলাম বারে বার/ আমার নাম গয়া বাইদ্যা বাবু/ থাকি পদ্মার পাড়।
পদ্মার উল্লেখ আছে ভূপেন হাজারিকার মর্মস্পর্শী গানটিতে―
গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা/ আমার দুই চক্ষে দুই জলের ধারা মেঘনা-যমুনা। তাছাড়া ফরিদা পারভীনের সুললিত কণ্ঠে গাওয়া আবুজাফর-রচিত গানটিতেও পদ্মার পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতি পাখা মেলেছে―
এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা-সুরমা নদীতটে/ আমার রাখালমন গান গেয়ে যায়…।
বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধেও পদ্মানদী উঠে এসেছে আমাদের আত্মপরিচয় ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে। উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেকয়টি গণনন্দিত শ্লোগান বাঙালিকে অবলীলায় দেশমাতৃকার বেদীমূলে অকুতোভয়ে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার মধ্যে অন্যতম―‘তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা।’ তাই বলা যায়, ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা-বিকাশে পদ্মানদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
শোকাবহ আগস্ট ও বেদনাদায়ক জাতীয় শোকদিবসের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায়, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অন্নদাশঙ্কর রায়ের কালজয়ী কবিতাটির কথা। তাতেও আছে পদ্মানদীর কথা―‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল কাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান।’ এভাবেই পদ্মা হয়ে উঠেছে আমাদের প্রাণের নদী, প্রিয় নদী। পদ্মাসেতু বিনির্মাণের পর এই বিস্ময়কর সেতু নিয়েও সাম্প্রতিককালে অসংখ্য কবিতা লেখা হয়েছে। তাতে উঠে এসেছে নানামুখী কীর্তিগাথা। তবে পদ্মাসেতু নিয়ে স্মরণযোগ্য কবিতাটি লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ। কবির ‘এই স্বর্ণসেতুহার’ কবিতার উদ্ধৃতিযোগ্য কয়েকটি পঙ্ক্তি―
আমরা দুর্বার দুরন্ত পদ্মাবতীর কণ্ঠে
পরিয়ে দিয়েছি এই স্বর্ণসেতুহার।
পদ্মাসেতু তুমি আর স্বপ্ন নও, বাস্তব।
পঙ্ক্তিগুলো পড়লে আর পদ্মা সেতুর কথা ভাবলে মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদনের দত্তের ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্যের একটি পঙ্ক্তি : কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ।
[চলবে]সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ