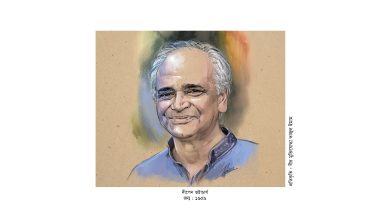বৃক্ষপ্রেমী বঙ্গবন্ধু : মোকারম হোসেন
প্রচ্ছদ রচনা : স্বাধীনতা দিবস
বঙ্গবন্ধু, এক মহিরুহের নাম
ইতিহাসের মহানায়কেরাই কেবল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে পারেন। উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারেন জীবনের পরতে পরতে। এমন মহানায়ক পাওয়া তো যেকোনও জাতির জন্যই পরম ভাগ্যের। বাঙালি জাতি হিসেবে আমরাও অনেক সৌভাগ্যবান। আমরা পেয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন প্রজ্ঞাবান সূর্যমানবকে। যাঁর জন্মই হয়েছিল জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার মহান ব্রত নিয়ে। তাঁর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছিল একদিকে যেমন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে, অন্যদিকে আবার জাতি পূনর্গঠনের কাজেও। সদ্য-স্বাধীন দেশ গড়ার কাজে তিনি সময় পেয়েছিলেন খুবই সামান্য। কিন্তু এই সামান্য সময়কেও তিনি অসামান্য করে তুলেছিলেন তাঁর সম্মোহনী জাদুতে। দূরদর্শী এই নেতা বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের মুক্তির পথ কোন দিকে। তাই আলো ফেলেছিলেন অসংখ্য উদ্দীপনা ও গঠনমূলক কজে।
তাঁর দূরদর্শী কর্মকাণ্ড থেকে বাদ যায়নি বৃক্ষরোপণের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও। আমরা এখন যা কেবল ভাবতে শুরু করেছি তা তিনি ভেবেছিলেন আরও চল্লিশ বছর আগে। এ দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বজায় রাখতে তিনি বৃক্ষ রোপণের ওপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি। তাঁর এই উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশও ঘটেছিল নানাভাবে। সদ্য স্বাধীন দেশে তিনি সবাইকে বৃক্ষপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণভবন, বঙ্গভবন ও বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে গাছ লাগিয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি গাছ আছে জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায়।

দেশের এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি ভাবেননি। কখনও কখনও উদ্ভিদ ও প্রকৃতি তাঁর ভাবনার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। যার কথ্য ও লিখিত রূপ আমরা প্রকাশনার বিভিন্ন মাধ্যমে খুঁজে পাই। কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন বইয়ে এমন অনেক আবেগঘন বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম দরদের কথা আরও গভীরভাবে অনুভব করেছেন তাঁর সুযোগ্য তনয়া শেখ হাসিনা। কারাগারের রোজনামচা বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন―
‘গাছপালা, পশুপাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। মুরগিটার মৃত্যু তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছে সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন অতি চমৎকারভাবে।’ [পৃ. ১৪]
বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এই নির্মোহ পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা অনুভব করতে পারি তাঁর উদ্ভিদ ও প্রকৃতিপ্রেম কতটা গভীর ও সংবেদনশীল ছিল। মূলত বৃক্ষপ্রেমী বঙ্গবন্ধু বইয়ে তাঁর এমন কিছু ব্যতিক্রমী বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। যা আগে কখনও এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুঁজে দেখা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বেশ কিছু গাছ এখনও বেঁচে আছে। নিজের হাতে গাছ লাগিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনায়। বলধা গার্ডেন ও ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের উন্নয়নের জন্য তিনি অর্থ বরাদ্দ দিয়েছিলেন। চা-শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি উদ্ভিদের ব্যবহার করেছেন। তাঁর শাসনামলে সবুজ বিপ্লবেরও ডাক দিয়েছিলেন তিনি।
প্রতিবছর জুন মাসে এখন বেশ উৎসবের আমেজে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। বনবিভাগের নার্সারিগুলো কম-মূল্যে চারা বিতরণ করে। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অসংখ্য বৃক্ষমেলার আয়োজন থাকে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিদিন অন্যান্য সওদাপাতির সঙ্গে দুচারটি গাছের চারাও কিনে নিয়ে যান। দেশব্যাপী এই যে বৃক্ষ আন্দোলন, বৃক্ষ সচেতনতা, তার প্রবক্তাও বঙ্গবন্ধু। মূলত তিনিই দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণকে আনুষ্ঠানিকতা দান করেন। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে শুধু জীবন ও সম্পদই নষ্ট হয়নি, দেশের বৃক্ষ ও বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা থেকে উত্তরণের জন্য, দেশকে বৃক্ষ সম্পদে আরও সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান কার্যক্রম চালু করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী প্রদান করেন :
‘বনাঞ্চলগুলোতে সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনশীল করার জন্য সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি বনাঞ্চল-বহির্ভূত এলাকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় অধিক গাছ লাগিয়ে বৃক্ষসম্পদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশে ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই বৃক্ষরোপণ অভিযানের সময় এবং পরে অধিক বৃক্ষরোপণ করে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। কেননা, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি দেশের জনপ্রতিনিধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবী ও আপামর জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিজেদের এলাকায়―স্কুল-কলেজ, কলকারখানা, রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘরের আশেপাশে যেখানেই সম্ভব মূল্যবান গাছ লাগিয়ে এবং তার পরিচর্যা করে সরকারের এ প্রচেষ্টাকে সফল করে।’

বঙ্গবন্ধুর এই গুরুত্বপূর্ণ বাণীই দেশের কোটি কোটি মানুষকে বৃক্ষ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। নতুন আঙ্গিকে বৃক্ষপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। তবে শুধু বাণীই নয়, বঙ্গবন্ধু সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে গাছের চারাও রোপণ করেন। ১৯৭২ সালে রমনা মাঠে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে জুয়াখেলা বন্ধ করে তিনি নারকেল চারা রোপণের মধ্য দিয়ে একটি উদ্যান তৈরির উদ্বোধন করে উদ্যানটির নামকরণ করেন― সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এখন নগরীর কোটি কোটি মানুষের ফুসফুস সচল রাখতে সাহায্য করছে। অথচ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে এই উদ্যানটির যে যাত্রা শুরু তা এখন অনেকটাই বিস্মৃত। তিনি সেখানে নিজ হাতে যে নারকেল গাছটি লাগিয়েছিলেন তার কোনও চিহ্ন এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। ’৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর কুচক্রী মহল তাঁর সকল কর্ম ও স্মৃতিকে আড়াল করতে বেছে নিয়েছিল ভিন্ন কৌশল। কিন্তু সত্য কখনও আড়াল করা যায় না। ইতিহাস তার আপন নিয়মেই সত্যকে বাঁচিয়ে রাখে।
প্রায় ২৩ বছর আগে, যখন বৃক্ষপ্রেমে রমনা ও সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করি তখন সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানের নারকেল গাছগুলো দেখে অনেক দিন ভেবেছি গাছগুলো কে লাগিয়েছেন। এই ভাবনা এত জোরালো হবার কারণ, কর্মসূত্রে প্রায় প্রতিদিনই একবার এই উদ্যানের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হতো। আমার উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা আমাকে নিয়ে অনেক দিন এই উদ্যানে ঘুরে ঘুরে গাছ দেখেছেন। স্বাধীনতা স্তম্ভের সুদৃশ্য নাগেশ্বরগুলো তাঁর পরিকল্পনারই একটি অংশ।
বঙ্গবন্ধু কি জানেন তাঁর উদ্যানের সেই নারকেল গাছগুলো এখন ফলবতী হয়েছে ? তাঁর নারকেলবীথির পাতায় পাতায় খেলা করে গ্রীষ্মের আলুথালু বাতাস, জোছনারাতে পাতার ফাঁকগলে নেমে আসে রুপালি আলোর ঝরনাধারা। আবার বিকেলের সোনারোদ পিছলে যেতে যেতে মায়াবী সন্ধ্যাগুলো ঘনিয়ে আসে।
সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত আরেকটি নারকেল গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি একটি নারকেল গাছের চারা রোপণ করেন। ৪৯ বছর বয়সি গাছটি এখন বেশ বড় হয়েছে। ফল ধরছে আরও কয়েক বছর আগে থেকেই। গাছটির চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছে কালো পাথরের বেদি দিয়ে। পাশে আছে বঙ্গবন্ধুর একটি আবক্ষ মূর্তিও। ১৯৭২ সালে শেখমুজিবুর রহমান খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন। তারপর মহিলা কলেজ পরিদর্শনে এসে চারাটি রোপণ করেন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি গাছ দেখা যায়। তাঁর সমাধিসৌধের পুরনো প্রবেশপথ ধরে কিছুটা আগালে টুঙ্গিপাড়া খাল থেকে একটু পশ্চিমে একটি শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটটি নতুন হলেও সংলগ্ন হিজল গাছটি শতাব্দী প্রাচীন। গাছটির ডালপালায় পরজীবী অর্কিডের রাজত্ব। এই পথে নৌকা ও বজরা যেত বাঘিয়া নদী হয়ে মধুমতীতে। বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষরা এই পথে কলকাতার সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তাঁর সমাধির অদূরে ৭০ থেকে ৮০ বছরের পুরনো একটি নারকেল গাছও আছে। বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক ভিটা লাগোয়া পুকুরপাড়ে আছে শতবর্ষী কয়েকটি হিজল। আশপাশে পুরনো আমলের কয়েকটি আমগাছও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নতুন প্রবেশপথে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কয়েকটি হিজল অবিকৃতভাবেই রাখা হয়েছে। একজন মহানায়কের সমাধিসৌধ এমনই হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধু তনয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পুরনো গাছগুলো স্বাভাবিকভাবে রেখেই সমাধিসৌধের নতুন পথ নির্মাণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বছর গোপালগঞ্জ শহরের মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ওই স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এসময় তিনি পিতা লুৎফর রহমানের সঙ্গে গোপালগঞ্জ শহরের বাড়িতে থাকতেন। বাড়ির সামনে ছিল বিরাট ফাঁকা মাঠ। পশ্চিমপাশে সরকারি পুকুর। সেখানে পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটি আমগাছ এখনও বেঁচে আছে। বঙ্গবন্ধু আমগাছটির তলায় তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গল্পগুজব ও রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি সেখানে জনসভার অনুকরণে বক্তৃতা দিতেন। আমগাছটি ছিল তাঁর প্রথম জীবনে বক্তৃতা শেখার মঞ্চ।
১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পথের পাশে, মহাসড়কের ধারে, বাড়ির আনাচে-কানাচে ও পতিত স্থানে ফলদ বৃক্ষ রোপণের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনা বর্তমান সময়ে এসে কতটা যুগপোযোগী, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি জানতেন, একটি ফলগাছ একসঙ্গে অনেক মানুষের বিচিত্র চাহিদা পুরণ করতে পারে। তা ছাড়া, ফল শুধু মানুষই খায় না, জীবজগতের বিশাল একটি অংশও ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার উদ্ভিদের জীবনচক্রের জন্যও ফল অপরিহার্য।
দেশের বৃক্ষায়ন, বৃক্ষসম্পদ রক্ষা, পরিচর্যা, গবেষণা, নান্দনিকতা, প্রচারণা, সর্বোপরি পরিবেশের সঙ্গে বনজসম্পদ এবং বৃক্ষের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে তাঁর সঠিক উপলব্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃক্ষপ্রেমী হিসেবে তিনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন বাংলার এই উর্বর পললমৃত্তিকার বুকে।
বলধা গার্ডেন
ইতিহাস নির্মাণ
১৯০৯ সাল। ঢাকা তখন রাজধানী, নতুন প্রদেশ। বিচিত্র গাছপালায় সুশোভিত করতে হবে ঢাকার পথঘাট, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এই গুরুদায়িত্ব নিয়েই তখন ঢাকায় আসেন লন্ডনের কিউ বোটানিক গার্ডেনের অন্যতম কর্মী রবার্ট লুইস প্রাউডলক। বলধার প্রকৃতিপ্রেমী জমিদার ঠিক সেই সময়েই শুরু করেন তাঁর অমর সৃষ্টি ‘সাইকি’ বাগানের কাজ। নিজেই ছিলেন সাইকির স্থপতি, শিল্পী ও উদ্ভিদবিশেষজ্ঞ। সাইকি ছিলেন গ্রিক পৌরাণিক উপাখ্যাানের প্রেমের দেবতা ‘কিউপিডের’ পরমা সুন্দরী স্ত্রীর নাম। সাইকি মানে আত্মা। যা দেবরাজ ‘জুপিটার’ কর্তৃক অমরত্ব লাভ করেছিল।
নরেন্দ্রনারায়ণ প্রায় ২৭ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৩৬ সালে সাইকি বাগানের কাজ শেষ করেন। তাতে পরিকল্পিতভাবে দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রজাতির দু®প্রাপ্য গাছের এক ঈর্ষণীয় সমাবেশ করেন। তখনকার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা ভাবলে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অসাধ্য সাধন বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি না ছিলেন স্থপতি, না উদ্ভিদবিজ্ঞানী, সুতরাং উদ্যান রচনা করতে গিয়ে তাঁকে এসব নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে। পছন্দসই গাছপালার তালিকা করে সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে দিনের পর দিন, কবে হাতে আসবে কাক্সিক্ষত উদ্ভিদটি। তারপর যথাস্থানে রোপণের পর পরিচর্যা, বাঁচানোর চেষ্টা, ফুল ফোটার পর আত্মতুষ্টি, কোনও কোনও ভিনদেশি প্রজাতির কষ্টসাধ্য অভিষেক―এসব নিয়েই দারুণ ব্যস্ত সময় কাটত তাঁর। ‘কিউপিডের’ মতোই তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন অমর সৃষ্টি সাইকিতে।
তবু অতৃপ্তি, আশা অপুরাণ
শুধু সাইকির বৃক্ষবৈচিত্র্যে তুষ্ট হতে পারেন না জমিদার, নিঃসঙ্গ সাইকির যথার্থ সঙ্গী চাই। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ১৯৩৮ সালে উত্তর পাশে আরেকটি বাগান তৈরির কাজ শুরু করেন। নাম রাখেন ‘সিবিলি’, আবারও সেই গ্রিক পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে বেছে নেওয়া সার্থক নাম। সিবিলি ছিলেন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে প্রকৃতির উর্বরতার দেবী। এ বাগানেও লাগানো হয় অসংখ্য প্রজাতির দেশি বিদেশি গাছগাছড়া। প্রথম থেকেই এখানে শুরু হয় নানা ধরনের প্রায়োগিক গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রজনন ও প্রসারণ। সিবিলির বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে পাওয়া যায় শঙ্খনদ পুকুর ও সূর্যঘড়ি। পরবর্তীকালে তৈরি করা হয় জয় হাউস। উল্লেখ্য যে, বলধা বাগান বা বলধা গার্ডেন নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দেওয়া নাম নয়। তিনি সাইকি ও সিবিলি নামে দুটো আলাদা বাগান তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে দুটো জোড়া দিয়ে সবাই বলধা গার্ডেন নামে সম্বোধন শুরু করেন। ধারণা করা হয় যে নরেন্দ্রনারায়ণ সাইকি অংশ দিয়েই বাগানে প্রবেশ করতেন। বাসস্থান বলধা হাউস ও সাইকি আলাদা করেছিলেন অনুপম গ্রিন হাউস বা ছায়াবীথি তৈরি করে। সেই গ্রিন হাউসের ভিতর তিনি মাটি ও পাথর দিয়ে বানিয়েছিলেন কৃত্রিম পাহাড় ও সুড়ঙ্গ।
যখন সিবিলির কাজ শুরু হয় তখন সারা বিশ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা। কিন্তু কাজ থামিয়ে রাখেননি তিনি। দেশ-বিদেশ থেকে আসতে থাকে গাছপালা লতাগুল্ম। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রয়োজন হয়ে পড়ে একজন যথার্থ সহকর্মীর। যুবক অমৃতলাল আচার্যই সেই প্রকৃত সহকর্মী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলধা গার্ডেনের সুখে দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন এই আপনভোলা প্রকৃতিপ্রেমি। বাবার প্রেরণাতেই তিনি মূলত বাগানের কাজে আকৃষ্ট হন। বাবা অখিলচন্দ্র শ্যামলী রমনার স্থপতি আর এল প্রাউডলকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।
শিল্পীর ভাবনা
সিবিলিতে কাজ শুরুর প্রাক্কালে মাত্র দুটি গাছ ছিল সেখানে, একটি বাদাম, অন্যটি খেজুর। যদিও শঙ্খনিধি পরিবারের এটা বাগানবাড়ি ছিল কিন্তু শঙ্খনদ পুকুর আর সূর্যঘড়ি ছাড়া আর কোনও স্থাপনা সেখানে ছিল না। ১৯৩৯ সালে শঙ্খনদ পুকুরের পশ্চিমপাড়ে, পুকুরঘাটের ঠিক উপরে নরেন্দ্রনারায়ণ নির্মাণ করেন বাগানের এক নিভৃত কক্ষ, নাম রাখেন ‘জয় হাউস’। বৈঠকখানা ও বিশ্রামাগার হিসেবেই এই কক্ষ ব্যবহৃত হতো। এ পরিকল্পিত বাগানে প্রথম লাগানো গাছ চাঁপা (সম্ভবত কনকচাঁপা)। চারাটি রোপণের জন্য তিনি অমৃত বাবুর হাতে তুলে দেন। জমিদার এভাবেই সকল কাজের দায়িত্বে অমৃত বাবুকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাতে প্রতিটি কাজেই ছিল প্রাণ।
বাগানের বহুমুখী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জমিদার ছিলেন মুক্তহস্ত। দেশ-বিদেশ থেকে শুধু গাছপালা, কলম ও বীজই আনাতেন না, সেগুলোর যত্ন-আত্মি ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিও তিনি সংগ্রহ করতেন। মূল্যবান গাছের পাতার ধুলোবালি পরিষ্কারের জন্য সেসময় টিস্যু পেপার ব্যবহৃত হতো সেখানে। এভাবেই নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্নেহমাখা, সৃজনশীল ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে সিবিলি বাগানের কাজ শেষ হয় ১৯৪০ সালে। জমিদার পরিতৃপ্তির আনন্দে বিভোর। কিন্তু এই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হয় না, আততায়ীদের হাতে নিজের একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় নিহত হলে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। এই পৃথিবীর কোনও কিছুই তাঁকে আর সান্ত্বনা দিতে পারছিল না। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ১৯৪৩ সালের ১৩ই আগস্ট তিনিও পুত্রের সহাবস্থানে চলে যান। সিবিলিতে পুত্রের পাশেই তাঁকেও সমাধিস্থ করা হয়।
বাগানের ক্রান্তিকাল
জমিদারের মৃত্যুর পরপরই স্তিমিতি হয়ে আসতে থাকে বলধাবাগানের প্রাণপ্রদীপ। শুধু অর্থানুকূল্যে নয়, তাঁর স্নেহমাখা পরিচর্যা থেকেও বঞ্চিত হয় বাগানের উদ্ভিদরাজি। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বাগানকর্মীরা হাল ছাড়েন না। কেবল প্রাণে বেঁচে থাকে অসংখ্য গাছপালা, আর এর প্রায় পুরো কৃতিত্বই অমৃতলাল আচার্যের। ১৯৪৭ সালে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হলেও বলধাগার্ডেন থেকে যায় নিভৃতে। ১৯৫১ সালে বলধাবাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের ওপর। এসময় অমৃত বাবু ও তাঁর সহকর্মীরা খেয়ে না খেয়ে, বিনা বেতনে, অর্ধবেতনে অনেকটা সন্তানের মতোই প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেন বাগানকে। তবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল বাগানটি।
বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা
১৯৬২ সালের দিকে বলধা গার্ডেন বনবিভাগের অধীনে ন্যস্ত হলে সাময়িকভাবে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এ সময় অমৃত বাবুকে বনকর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সরকারি নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায় বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ। এদিকে বাড়তে থাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দানাবাঁধতে থাকে স্বাধিকার আন্দোলন। অবশেষে স্বাধীনতা এল, শুরু হলো দেশগঠনের কাজ। এসময়ে কিছুদিন বিভাগীয় বনকর্মকর্তা হিসেবে বলধা বাগানের দায়িত্বে ছিলেন ড. মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী। আন্তরিকভাবেই তিনি বাগানের উন্নয়নে কাজ করার চেষ্টা করেন। ‘বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি’ গ্রন্থে তিনি বলধা গার্ডেনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি :
‘[…] ঢাকা শহরের উন্নয়নের তাগিদে ভূতল থেকে পাম্প করে পানি ওঠানো ও আশেপাশের খালবিল ভরে ফেলার জন্য ভূতলের পানি আশঙ্কনীয়ভাবে নেমে যায়। বিশেষ করে পুরান ঢাকার ‘ধোলাই খাল’ ভরাট করে ফেলায় অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। বলধা বাগানের আকর্ষণীয় নিদর্শন ‘শঙ্খনদ পুকুর’টি শুকিয়ে যেতে শুরু করে, আর খরা মৌসুমে এবং ভূতলের পানি নিচে নেমে যাওয়ায় তার ফলাফল বাগানের গাছপালার ওপর প্রতিফলিত হতে থাকে। বাগানে ফুলের ও ফলের অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। আর কারও চোখে পড়ুক আর না পড়ুক, আচার্যি বাবুর চোখে তা এড়ায় না কিন্তু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো ছাড়া, প্রাকৃতিক এই পরিবর্তনের মুখে তিনি কিইবা করতে পারতেন।
একটা সুযোগ এসে গেল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার। দেশ তখন কেবল স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের প্রতিও সবার দৃষ্টি পড়েছে। বলধা বাগানের প্রাকৃতিক পরিবর্তন সহজে চোখে না পড়লেও একটা জিনিস অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল-বাগানের ‘শঙ্খনদ পুকুর’ যা খরার মৌসুমে একেবারে শুকিয়ে যেতে শুরু করল। এমনকি পুকুরের তলদেশ শুকিয়ে মাটির ফাটল বেরিয়ে এল। বর্ষা মৌসুমে পানিতে পুকুর আবার ভরে উঠলেও, না থাকত তাতে জলজ উদ্ভিদ আর না থাকত তাতে কোনও মাছ বা কোনও জলজ জীব। শুকনো মৌসুম এলে আবার পুকুর শুকিয়ে তলায় শুকনো মাটিতে ফাটল বেরুতে থাকলো। এই ভাবে চলতে থাকলো কয়েক বছর ধরে।
ঠিক এই ধরনের একটা দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার বেলি রোডের বন সম্প্রসারণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উঋঙ) হিসেবে বলধা বাগানের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। আচার্যি বাবু তখন পুরোপুরিভাবে বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা হয়ে বলধা বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করছেন। বহুদিন থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন, জানতেন ও পছন্দ করতেন। আমার সৌভাগ্য হলো খুব কাছে থেকে বলধা বাগানকে দেখতে, এই বাগানের জন্য সৃজনশীল কিছু করতে এবং আচার্যি বাবুর মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রকৃতিপ্রেমিককে নিয়ে কাজ করতে। শুরু হলো বলধা বাগানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা।
খরার মৌসুমে ‘শঙ্খনদ পুকুর’টি পানি দিয়ে ভরে রাখা ও বাগানের গাছপালার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করাই হয়ে উঠল আমাদের প্রথম ও প্রধান উন্নয়ন প্রচেষ্টা। টাকার প্রয়োজন। […] ঠিক সেই সময়েই বাগানে ফুটল একটা ‘শতাব্দী ফুল’ (ঈবহঃঁৎু ভষড়বিৎ)। সুযোগ হলো রিপোর্টারদের বাগানে ডাকার।
যারা সেদিন আমার ডাকে সাড়া দিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন দৈনিক বাংলা/বিচিত্রার জনাব আহমেদ নূরে আলম ও জনাব মাহফুজ উল্লাহ, এনা’র জনাব শিহাব উদ্দীন আহমদ, বাসস-এর জনাব গাজীউর রহমান। তাঁরা শতাব্দী ফুল দেখলেন, বাগানের প্রকৃতি পরিবেশ দেখলেন ও বহু লুপ্তপ্রায় গাছপালা দেখলেন, আর দেখলেন খরায় শুকিয়ে যাওয়া ‘শঙ্খনদ পুকুর’ এবং তার মাটি ফাটা তলদেশ। তারা অভিভূত হলেন, তাঁরা আতঙ্কিত হলেন, শুরু করলেন জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁদের লেখার পালা। […] তাদের লেখায় আকৃষ্ট করল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতাদের। কাজ হয়ে গেল আমাদের।
তখন বন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। কাজের সূত্রে উনার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমাকে খুব স্নেহের চোখে তিনি দেখতেন ও আমার ওপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। পত্র-পত্রিকায় বলধা বাগানের ওপর লিখিত প্রতিবেদনগুলো দেখে উনি ডেকে পাঠালেন মিন্টু রোডে তার বাসায়। সরাসরি বললেন কেবল পত্রিকায় লিখলে তো হবে না, কি করতে হবে বলেন। একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরি করে নিয়ে আসেন, আমি চেষ্টা করে দেখব টাকা-পয়সা জোগাড়ের। দরকার হলে বঙ্গবন্ধুকেও বলব, তিনি বলধা বাগানকে খুব ভালোভাবে চেনেন ও সেখানে অনেক মিটিং করেছেন এবং এই বাগানের উন্নয়নে খুশি হবেন। স্বয়ং মন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে লেগে গেলাম একটা প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি করতে। যথারীতি তথ্য যোগালেন বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু অমৃতলাল আচার্য।
ঢাকার ডেপুটি কমিশনার তখন ছিলেন জনাব রেজাউল হায়াত। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে তাকেও জানালাম বলধা বাগানের কথা এবং বাগানটি রক্ষা করার আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা। উনি উৎসাহিত হয়ে প্লানের একটা কপি সত্বর তাঁকে দিতে বললেন। বঙ্গবন্ধু তখন প্রেসিডেন্ট। জনাব রেজাউল হায়াত ছিলেন তাঁর স্নেহভাজন। প্ল্যানটা তৈরি করার পর মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর ব্যস্ততার জন্য ধরতে পারছিলাম না। অগত্যা রেজাউল হায়াত সাহেবকেই প্ল্যানের একটা কপি দিয়ে দিলাম। এই ঘটনার মাত্র কয়দিনের মধ্যে রেজাউল হায়াত প্রেসিডেন্টের সচিব হিসেবে গণভবনে যোগদান করলেন। আর সেখানে যোগদান করার কয়দিনের মধ্যেই তাঁর টেলিফোন পেলাম গণভবনে যেতে, প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন।
কিছুটা ভয়ে, না জানি কি ঘটে এবং কিছুটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ে বলধা বাগানের অবস্থাটা তুলে ধরতে পেরেছি। কথাগুলো মনে নিয়ে ১৩ আগস্ট ১৯৭৫ (বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর মৃত্যুর ঠিক ৩২ বছর পর) হাজির হলাম গণভবনে। রেজাউল হায়াত সাহেবের কামরায় বসে থাকলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনায় আমার মতো একজন সাধারণ সরকারি কর্মকর্তার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সে দিনের মতো দেখা হলো না। নিরাশ হলাম ও কিছুটা হতাশ হয়ে বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু রেজাউল হায়াত সাহেব ছিলেন নাছোড়বান্দা। বাসায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতে টেলিফোনে খবর এল পরদিন অর্থাৎ ১৪ আগস্ট ১৯৭৫, বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২টায় আবার যেতে হবে গণভবনে।
১৪ই আগস্ট যথাসময়ে পৌছে গেলাম গণভবনে রেজাউল হায়াত সাহেবের কামরায়। ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলাম। তিনি কিছুক্ষণ পর পর কামরার বাইরে যাওয়া-আসা করছিলেন। সম্ভবত আমাদের সেদিনের প্রোগ্রাম যাতে ব্যাহত না হয় তার চেষ্টা করছিলেন। প্রায় ২টার সময় রেজাউল হায়াত সাহেবের সঙ্গে কামরায় ঢুকলেন তদানীন্তন কেবিনেট সচিব জনাব তৌফিক ইমাম, প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মনোয়ারুল ইসলাম এবং তখনকার সময়ের গোপালগঞ্জের এসডিও জনাব বদিউর রহমান। সমকালীন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে এঁদের সবাইর সঙ্গে কমবেশি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে ঢুকলাম প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কামরায়।
বঙ্গবন্ধু বসে ছিলেন চেয়ারে। টেবিলের উল্টো দিকে ডান দিকের কোনায় বসেছিলেন প্রেসিডেন্টের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি জনাব তোফায়েল আহমদ। বঙ্গবন্ধুকে আগেও কয়েকবার বেশ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তবে এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিল বেশ ভালোভাবেই তাঁর চেনা। আমার দিকে তাই তাকিয়ে রইলেন পরিচিতির জন্য। জনাব তোফায়েল আহমদ ছাড়া আমরা সবাই দাঁড়িয়েই ছিলাম। জনাব তৌফিক ইমাম যেই বললেন আমি ডিএফও অমুক। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলা শুরু করলেন যেন আমি তাঁর বহু পরিচিতদের একজন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমার প্রশংসা শুরু করলেন। সরকারি বন কর্মচারীদের ওপর তিনি যে কি পরিমাণ আস্থাশীল তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে উপস্থিত সবাইকে আমার সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না তিনি কি করে এত খবর পেলেন। যা হউক স্বয়ং রাষ্ট্রপতির মুখ থেকে আমার নিজের সম্বন্ধে এ ধরনের স্তুতিবাক্য শুনে আমার বুক ফুলে উঠল এবং আমার মন আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে উঠল। পরিচয় ও প্রশংসা পর্ব শেষ হলে নিজেই বললেন, কী হয়েছে বলধা গার্ডেনে ? কী করতে হবে বলো ?
সুযোগ পেয়ে বলা শুরু করলাম বলধা বাগানের পরিবেশের কথা, বাগানের গাছপালা, ঘরবাড়ি ও সবশেষে ‘শঙ্খনদ’ পুকুর ও বাগানে পানির অভাবের কথা। জানতে চাইলেন কি করতে হবে। সরাসরি টাকা চাইলাম আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী―প্রাথমিক পর্যায়ে তিন লক্ষ টাকা। জানালাম এর মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা লাগবে একটা গভীর নলকূপ (উববঢ় ঃঁনববিষষ) বসাতে। আমার বলা শেষ হতে না হতেই বঙ্গবন্ধু টেবিলের অপর পাশে বসা জনাব তোফায়েল আহমদকে বললেন তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদকে টেলিফোন লাগাতে। জনাব তোফায়েল আহমদ জনাব আজাদকে টেলিফোন লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দিলেন। বঙ্গবন্ধু বলধা বাগান সম্বন্ধে কিছু বলে এবং আবার আমার কিছু প্রশংসা করে কৃষিমন্ত্রীকে বলধা বাগানের জন্য একটা উববঢ় ঃঁনববিষষ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে বললেন। আলাপ শেষে বঙ্গবন্ধু জানালেন কৃষিমন্ত্রী রাজি হয়েছেন এবং আমি যেন ই.অ.উ.ঈ.-এর ঈযরবভ ঊহমরহববৎ-এর সঙ্গে দেখা করি, কৃষিমন্ত্রী তাকে বলে দেবেন। পানির ব্যবস্থার সুরাহা করে বঙ্গবন্ধু বললেন, পানির ব্যবস্থা হয়ে গেল, আর কি করতে হবে ? এখন আর কত টাকা লাগবে ?
আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, আর দুই লক্ষ টাকা দিলেই আপাতত কাজ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, এই মাত্র না বললে দেড় লক্ষ টাকা লাগবে একটা গভীর নলকূপ বসাতে। সেটা তো হয়ে গেল, এখন কেন আরও দুই লক্ষ টাকা লাগবে ? বললাম, গভীর নলকূপের পাম্প আনতে ও বসাতে আনুষঙ্গিক খরচ হবে, আর যদি কিছু বেঁচে যায় তা বলধা বাগানেরই উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে দেব। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে এবং আমার ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে সেটা পুনর্বার ব্যক্ত করে, উপস্থিত জনাব মনোয়ারুল ইসলামকে বললেন, আমাকে দুলক্ষ টাকার একটা চেক দিয়ে দিতে। মনোয়ারুল ইসলাম সাহেব ফাইন্যান্সের লোক, একটু ইতস্তত করছিলেন― কীভাবে, কীসের বিপরীতে বা কার নামে চেক দিবেন। বঙ্গবন্ধু নিজে থেকেই বলে ফেললেন―না, না, বন বিভাগের নামে নয়, চেকটা ব্যক্তিগত ওর নামে দেও, বলে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং আরও বললেন, আমি জানি এটার অপচয় হবে না।
বঙ্গবন্ধু শেষ বারের মতো বললেন, ‘জয় হাউস’টা (ঔড়-ঐড়ঁংব) ভালো করে ঠিক করো। আমি সেখানে অনেক মিটিং করেছি, ঠিক হলে আবার যাব। বঙ্গবন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে এক পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সেদিন সবার সামনে পেলাম তার জন্য মনেপ্রাণে আল্লাহতায়ালার দরগায় অশেষ শুকুর জানালাম। রেজাউল হায়াত সাহেবের কামরায় পৌঁছে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উভয়ে করমর্দন করলাম। সাফল্যের উচ্ছলতায় আমার শরীর কাঁপছিল। পানি খেলাম ও বসে থাকলাম জনাব মনোয়ারুল ইসলামের অপেক্ষায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন দুই লক্ষ টাকার চেকটা নিয়ে। দেখলাম আমার নামেই লেখা চেক। করমর্দন করে চেকটা আমার হাতে দিলেন। চেকটা হাতে নিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাত মিলালাম জনাব রেজাউল হায়াত সাহেবের সঙ্গে। সেদিনের আমাদের কৃতিত্বের পেছনে তাঁর অবদান যে ছিল অপরিসীম সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।
চেকটা শার্টের বুক পকেটে রেখে সোজা চলে এলাম বেলি রোডে আমার বাসভবনে। আমার বাবা-মা তখন আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চেকটা দেখালাম ও বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত কথাগুলো তাঁদের বললাম। তাঁরা উভয়েই ভীষণ খুশি হলেন। খেয়ে বেরিয়ে প্রথমে গেলাম প্রধান বন সংরক্ষক (ঈযরবভ ঈড়হংবৎাধঃড়ৎ ড়ভ ঋড়ৎবংঃ) জনাব আব্দুল হামিদ সাহেবের অফিসে। যদিও বন বিভাগের অজান্তে আমরা এগিয়ে যাই এই কাজে তবু খুব খুশি হলেন তিনি এবং আমাদের এই কাজে তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে উৎসাহিত করলেন। সাবধানে কাজ করে যেন সুন্দরভাবে কাজ শেষ করি, সেই উপদেশ দিলেন। প্রধান বন সংরক্ষকের দফতর থেকে বেরিয়ে গেলাম বন বিভাগের তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব রিয়াজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়িতে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ও শুনে খুব খুশি হলেন এবং ভালোভাবে টাকাটা কাজে লাগিয়ে একটা দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে তিনি উপদেশ দিলেন।
মন্ত্রী জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় গেলাম সন্ধ্যার পর। দেখলাম বাসায় একটা পারিবারিক মিলাদ হচ্ছে। ইশারায় মিলাদে বসতে বললেন। মিলাদ শেষে নিচের তলার বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে পটুয়াখালীর ডিসি ও কিশোরগঞ্জের সদ্য নিয়োজিত জেলা গভর্নর আব্দুস সাত্তার সাহেবও এলেন। সাত্তার সাহেবের সঙ্গে কথা শেষে তিনি চলে গেলে আমাকে বললেন, আমি সব জানি। এখন তো টাকা পেয়ে গেছ, কাজ করো। আমি বঙ্গবন্ধুকে তোমার কথা সব বলেছি। এবার আমার কাছে পরিষ্কার হলো বঙ্গবন্ধু আমার সম্বন্ধে কী করে জানলেন এবং কার কাছ থেকে জানলেন, কারণ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে আসার কোনও সুযোগ আমার কোনও দিন হয়নি। মন্ত্রী জনাব সেরনিয়াবাত সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমার ওপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদাহানি হবে না সেই আশ্বাস দিয়ে বাসায় ফিরলাম।
নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। যে শার্টের পকেটে চেকটা ছিল, সেটা খুলে ঝুলিয়ে রেখে, একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে শুলাম। তারপর, সে রাত্রে অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ভোর রাত্রে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল তা ব্যক্ত করার কোনও ভাষা আমার নেই। সকালে পকেট হাতড়িয়ে চেকটা বের করে বারবার দেখলাম, আর মনের কোণে বিষাদের ছায়া বারবার নেমে এল।’
বঙ্গবন্ধু জনাব মাহবুবউদ্দীনকে শেষবারের মতো বললেন, ‘জয় হাউসটা ভালো করে ঠিক করো। আমি সেখানে অনেক মিটিং করেছি, ঠিক হলে আবার যাব।’ কিন্তু বলধা গার্ডেনে আর কখনই যাওয়া হয়নি এই মহান রাষ্ট্রনায়কের। তার পরের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। জনাব মাহবুবউদ্দীনের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপচারিতার পরেরদিনই বাংলার ইতিহাসে বীভৎসতম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। দেশে নৈরাজ্যময় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। হতবিহ্বল মাহবুবউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর দেওয়া পবিত্র জামানত সেই চেকটি নিয়ে চরম এক অনিশ্চয়তায় পড়েন। সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্য হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। কিন্তু হাল ছাড়েন না তিনি। অবশেষে তিনি পুরনো চেকটি দেখিয়ে আরেকটি নতুন চেক নিয়ে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হন এবং তা দিয়েই বাগান সংস্কারের কাজ শুরু করেন। ততদিনে তাঁর দায়িত্ব বর্তায় সরকারের আরেকটি বিভাগে। বলধা গার্ডেন হয়ে পড়ে অভিবাবকহীন। এভাবে আরও অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হয়। আন্তরিকতার অভাবে কোনও উদ্যোগই তেমন সুফল বয়ে আনে না, কাটে না বাগানের দৈন্যদশা।
[বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি, ড. মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা-২০০৬]ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ও বঙ্গবন্ধু
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান (ইযধধিষ ঘধঃরড়হধষ চধৎশ) বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান। রাজধানী ঢাকা থেকে উত্তরে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে গাজীপুর সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় এই উদ্যানের অবস্থান। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭৪) অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ৫,০২২ হেক্টর জায়গা জুড়ে ভাওয়াল শালবনে এই উদ্যান গড়ে তোলে। তবে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৮২ সালে।
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে একসময় বাঘ, কালোচিতা, চিতাবাঘ, মেঘলা চিতা, হাতি, ময়ূর, মায়া হরিণ ও সম্বর হরিণ দেখা যেত। ১৯৮৫ সালে এ বনে খেঁকশিয়াল, বাঘডাস, বেজি, কাঠবিড়ালি, গুঁইসাপ ও কয়েক প্রজাতির সাপ দেখা গেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী ভাওয়াল গড়ে ৬৪ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যার মধ্যে ৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ১০ প্রজাতির উভচর ও ৩৯ প্রজাতির পাখি রয়েছে। বনবিভাগ এ বনে অজগর, ময়ূর, হরিণ ও মেছোবাঘ ছেড়েছে। এছাড়া ২০১২ সালে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ১৬টি তক্ষক ছাড়া হয়।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান মূলত ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি। এ বনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে বড় আকৃতির গাছ ১৬৭, গুল্ম ৬১, বিরুৎ ১২৭, লতান উদ্ভিদের সংখ্যা ৩৫টি। শাল, (ঝযড়ৎবধ ৎড়নঁংঃধ) এ উদ্যানের প্রধান বৃক্ষ। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে কাঁঠাল, হাড়গজা, কুম্ভী, গান্ধিগজারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিমভাবে ইউক্যালিপটাস এবং রাবার গাছেরও বৃক্ষায়ন করা হয়েছে।
ঢাকা থেকে ৪০ কিমি দূরে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে উদ্যানটি অবস্থিত। ন্যাশনাল পার্ক হিসেবেই এর পরিচিতি বেশি। এখানকার প্রধান আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে শাল-গজারির ঘন বন এবং প্রাকৃতিক মনোরম লেক। ইচ্ছে করলে লেকে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করা যায়। সময় কাটানোর জন্য রয়েছে দুটো উন্নত রেস্ট হাউজ। এই উদ্যানে প্রবেশের জন্য পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের তিনটি বড় বনভূমির মধ্যে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান একটি। এখানে রয়েছে মোট একচল্লিশটি পিকনিক স্পট। সারাদিন গাছের ছায়ায় পাতা মাড়িয়ে মর্মর শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগবে।
বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা
১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চুড়ান্ত বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হলো দেশ গঠনের কাজ। তখন ঢাকার অদূরে অবস্থিত ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আধুনিকায়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। কিন্তু কিভাবে হলো সেই কাজ। কারা ছিলেন এর নেপথ্যে। সেসব কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এই উদ্যানের বৃহৎ সংস্কার এবং নানামুখী ইতিবাচ পরিবর্তনের সঙ্গে মনে প্রাণে সম্পৃক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেদিন রচিত হয়েছিল ইতিহাসের একটি সুবর্ণ অধ্যায়। আজ আমরা গাজীপুরে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের যে অবয়ব দেখি তার পেছনেও রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর সরাসরি আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে উদ্যানটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ৯ই মে বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৩ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। ‘বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি’ গ্রন্থে ড. মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী এবিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।
‘[…] প্রকল্প শুরু করতে যে টাকার প্রয়োজন তা পেতে সময় লাগবে জানতাম। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চতম পর্যায়ে অনুমোদন একবার পেয়ে গেলে ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করার জন্য তৈরি থাকতে হবে সেটা ধরে নিয়েছিলাম। আমরা তাই প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রমের প্রস্তুতির কাজ আমাদের নীলনকশা প্রণয়নকালীন সময় থেকেই শুরু করে দিয়েছিলাম। আমার অতি ঘনিষ্ঠ একজন স্থপতি জনাব আনোয়ারুল ইসলামকে খুঁজে বের করলাম। অনু ভাই (জনাব আনোয়ারুল ইসলামের ডাকনাম) আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ও সেই সুবাদে তিনি আমার অগ্রজপ্রতীম বন্ধুও ছিলেন বটে। তিনি আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি) থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন ১৯৫৮ সালে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। কিছুদিন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করে তার ইচ্ছা হলো স্থপতি হবেন। পুরোপুরি ছাত্র হয়ে গেলেন আবার এবং আরও ৪ বছর পড়াশুনা করে স্থাপত্যবিদ্যায়ও ডিগ্রি নিয়ে নিলেন। সম্ভবত ঢাকা থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রিধারীদের প্রথম দলের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। পড়াশোনায় তাঁর ধৈর্য দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে বলতেন তিনি চেষ্টা করলে আরও ৫ বছর পড়ে এমবিবিএস ডাক্তারও হয়ে যেতে পারবেন।
যা হোক, অনু ভাইকে পেয়ে আমরা যেন হাতে আকাশ পেলাম। তাঁকে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাভাবনার কথা জানালাম। বললাম টাকা-পয়সা নেই, তবে সমর্থনের আশা আছে জাতীয় উচ্চ পর্যায় থেকে। তাই কাজ শুরু করে দিতে চাই সেই অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অনু ভাইকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা আধুনিক বিশ্রামাগারের নকশা তৈরি করে দেন। আমরা সেই নকশা বঙ্গবন্ধুর কাছে শীঘ্রই পেশ করব জানালাম। অনু ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই রাজি হয়ে গেলেন। সামান্য কয়দিনের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে বেশ কয়বার যাওয়া-আসা করলাম ভাওয়াল গড়ের আড়াইশা প্রাসাদ মৌজার সেই বনাঞ্চলে। আর এই কয়দিনেই অনু ভাই তাঁর স্থপতি মনের বিন্যাসে আমাদের চিন্তাধারা ও ভাওয়ালের শালবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয় করে এঁকে দিলেন গতানুগতিক রীতি বহির্ভূত আধুনিক বন বিশ্রামাগারের এক অনন্য সাধারণ নকশা।
[…] স্থপতি আনোয়ারুল ইসলামের এই ব্যতিক্রমধর্মী অবকাঠামো আমাদের যে কেবল অনুপ্রাণিত করল তা নয়, জনাব রেজাউল হায়াত এবং আমাদের সহযোগী সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জননেতাদেরও আকৃষ্ট করল। প্রধান বিশ্রামাগারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনু ভাই দুটা অষ্টভুজি বনভোজন কেন্দ্রের নকশাও এঁকে দেন। জনাব রেজাউল হায়াতের সঙ্গে শেষ যোগাযোগের মাত্র কয়দিনের মাথায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, স্থপতি আনোয়ারুল ইসলাম প্রণীত বিশ্রামাগারের সেই ব্যতিক্রমধর্মী নকশা, সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে আমাদের বানানো প্রস্তাবিত ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র ও প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রমে মাত্র ৩,৫০,০০০ টাকা লাগবে দেখিয়ে আমাদের তৈরি ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনটা পৌঁছে দিলাম জনাব রেজাউল হায়াত সাহেবের বাসায়।প্রকল্প প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে আমাদের বেশ সময় লাগে কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত সঠিক তথ্য এবং বিশেষ পর্যায়ে সংকলিত মানচিত্র এবং বিভিন্ন নকশার রেখাচিত্র ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণীত প্রকল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এমনিতেই জনাব রেজাউল হায়াত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন একজন নবীন ও চৌকস আমলা, তার ওপর প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত একটা আকর্ষণীয় প্রকল্প তাঁর হাতে হাতে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে গেলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে না সেই বিশ্বাস আমার ছিল।
হলোও তাই, ৯ই মে ১৯৭৪ সন্ধ্যায় জনাব রেজাউল হায়াত সাহেব এসে হাজির হলেন বেলি রোডের বন বিভাগের আমাদের বাসবভনে। আগেই বলেছি আমার সহকর্মী ও বন্ধু নুরুল আলমের সঙ্গে জনাব রেজাউল হায়াতের আত্মীয়তার সূত্র রয়েছে। নুরুল আলম থাকতেন আমার ঠিক পেছনের বাড়িতে। তিনি টেলিফোনে জানালেন রেজাউল হায়াত সাহেব এসেছেন, শুভ সংবাদ আছে, তক্ষুনি যেন তাঁর বাসায় চলে আসি। পেছনের দরজা খুলে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলাম। রেজাউল হায়াত সাহেব আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন আমাদের কাজ হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রকল্পটি অনুমোদন করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অনুদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করে দিতে।
সংবাদটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল। সেদিন ছিল ২৫ বৈশাখ। টিভিতে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান চলছিল আর ঠিক তখনই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমার ‘সোনার বাংলা’ বাজছিল। আমার মনে হলো আমরাও যেন সোনার বাংলা গড়ার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টায় আজ বিজয়ী হলাম। শুকরিয়া জানালাম আল্লাহতালার দরগায়। মনেপ্রাণে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানালাম বঙ্গবন্ধুকে। আর তাঁর প্রাপ্য ধন্যবাদ নির্ধিধায় জানালাম জনাব রেজাউল হায়াতকে, আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যের প্রারম্ভিক পর্বে তাঁর সাফল্যজনক অবদানের জন্য।
কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চেক পেয়ে গেলেন রেজাউল হায়াত সাহেব। যেহেতু চেকটি বন বিভাগের নামে ছিল না তাই কাজে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য তিনি আমাকে একটা আলাদা একাউন্ট খুলে, আমি যাতে সেই একাউন্ট পরিচালনা করতে পারি ও আলাদাভাবে তার হিসাব রাখতে পারি সেই ব্যবস্থা নিতে বললেন। তিনি ঢাকার তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব জনাব আবুল কাশেম খানকে সভাপতি করে একটা কমিটিও গঠন করে দিলেন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য। পরবর্তীকালে তিনি বদলি হয়ে গেলে নতুন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব নুরুল আহাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই কমিটিতে ঢাকার বন সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তা জনাব নুরুল আলম যার কথা আগে উল্লেখ করেছি এবং ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার এসডিও জনাব শাহরিয়ার ইকবাল ছিলেন সদস্য হিসাবে। আর আমি ছিলাম সদস্য সচিব। কয়দিন পর জনাব শাহরিয়ার ইকবাল বদলি হয়ে যান ও নতুন এসডিও জনাব ওবায়দুল মুক্তাদির তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
[…] এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে যায় যা আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়। ১৮ মে ১৯৭৪ অন্য একটা কার্যক্রম উপলক্ষে গেলাম গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সহ-সভাপতি কুষ্টিয়ার ডা. আসহাবুল হকের সভাপতিত্বে আমরা তখন পরিবেশজনিত একটা বেসরকারি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কমনওয়েলথ হিউমেন ইকোলজি কাউন্সিল (ঈড়সসড়হবিধষঃয ঐঁসধহ ঊপড়ষড়মু ঈড়ঁহপরষ-ঈঐঊঈ)-এর বাংলাদেশ অধ্যায়ের সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। বঙ্গবন্ধুকে সেই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত করাতে আমাদের একটা প্রতিনিধি দল সেদিন ডা. আসহাবুল হকের নেতৃত্বে যাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। বাংলাদেশের তিনজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. আনোয়ার হোসেন, প্রফেসার এম. আই. চৌধুরী ও ড. ইউসুফ আলী ছিলেন সেই প্রতিনিধি দলে। ড. আনোয়ার হোসেন ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি এবং প্রফেসার চৌধুরী ও ড. আলী ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। আমি যাই সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে। ঢাকায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমে কার্যরত ও কমনওয়েলথ হিউমেন ইকোলজি কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষক অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী মি. এফ. জেড. কুটেনাও সেই দলে ছিলেন আমাদের সঙ্গে।
গণভবনে কর্মরত তৎকালীন সিএসপি কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব মনোয়ারুল ইসলাম-এর লেখায়ও প্রসঙ্গটি এসেছে। তিনি লিখেছেন :
‘বঙ্গবন্ধুর এই বনায়ন পরিকল্পনার মধ্যে আমি একদিন তাঁকে বললাম, ভাওয়ালের গড়ের জঙ্গল থেকে যেভাবে শাল, গজারিগাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে, তাতে কিছুদিন পর এই বন উজাড় হয়ে যাবে। এটি রক্ষা করার একমাত্র উপায় জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা। এরপর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ঢাকার জেলা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াতকে গণভবনে ডাকলেন। প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু টাকাপয়সার ব্যবস্থা নেই। রেজাউল হায়াত শেষ পর্যন্ত পূর্ত কর্মসূচির কিছু টিন দিতে রাজি হলেন। এই টিন দিয়ে এবং বনবিভাগের কাঠ ব্যবহার করে জয়দেবপুর জাতীয় উদ্যানের অফিসঘরটি তৈরি করা হলো। সর্বমোট খরচ হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা। আমি যত বড় এলাকার প্রস্তাব করেছিলাম, অর্থাভাবে বন বিভাগ তার সবটা জাতীয় উদ্যানের আওতায় নিতে পারেনি। উদ্যানের বাইরে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ছিল যা প্রায় উজাড় হয়ে গেছে।’
[বঙ্গবন্ধু কালের সীমা ছাড়িয়ে, মনোয়ারুল ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ই মার্চ ২০১৯]লেখক : পরিবেশ বিজ্ঞানে
বাংলা একাডেমি ২০২২ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকৃতিপ্রেমী ও উদ্ভিদবিষয়ক গবেষক
আলোকচিত্র : মোকারম হোসেন