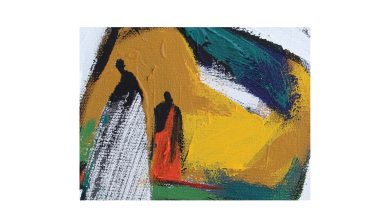শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু : সতেরোতম পর্ব : মানবর্দ্ধন পাল

ভাষা-গবেষণা ধারাবাহিক
[প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকরা শব্দকে ‘ব্রহ্ম’ জ্ঞান করেছেন―শব্দ যেন ঈশ্বরতুল্য। পাশ্চাত্যের মালার্মেসহ নন্দনতাত্ত্বিক কাব্য-সমালোচকদেরও বিশ্বাস, শব্দই কবিতা। শব্দের মাহাত্ম্য বহুবর্ণিল ও বহুমাত্রিক। বাংলা ভাষার বৃহদায়তন অভিধানগুলোর পাতায় দৃষ্টি দিলেই তা প্রতিভাত হয়। আগুনের যেমন আছে অসংখ্য গুণ, তেমনই ভাষার প্রায় প্রতিটি শব্দেরও আছে অজস্র অর্থের সম্ভার। কালস্রোতে ও জীবনের প্রয়োজনে জীবন্ত ভাষায় আসে নতুন শব্দ, তা বিবর্তিতও হয়। পুরনো শব্দ অচল মুদ্রার মতো ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে মণি-কাঞ্চনরূপে ঠাঁই নেয় অভিধানের সিন্দুকে।বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমুদ্রসম―মধুসূদনের ভাষায় : ‘ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন’। বৈঠকি মেজাজে, সরস আড্ডার ভঙ্গিতে লেখা এই ‘শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু’। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক―সবকিছু মিলিয়ে শব্দের ভেতর ও বাইরের সৌন্দর্য-সৌগন্ধ এবং অন্তর্গত আনন্দধারার ছিটেফোঁটা ভাষিক রূপ এই ‘শব্দবিন্দু আনন্দসিন্ধু’ ধারাবাহিক।]
কার
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি―
মাথা কর নত।
এ আমার পাপ এ তোমার পাপ।
―বলাকা, রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যপঙ্ক্তিতে যে ‘কার’ শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে সেটি নামপদের পরিবর্তে সর্বনাম হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে―এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই। তবে শব্দটি কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়।
শৈশবে ঠাকুরমা নির্মলাসুন্দরীর মুখে একটি ধাঁধা শুনেছি এরকম : ‘কাঁকর উদ্দিন নাম তার ক-য়েতে আকার/ পাঁঠার ঠ্যাং কাটিয়া ঠ-য়েতে আকার/ লতার প্রথম অক্ষর ল মিশাইয়া/ ইহাতে যাহা হয় তাহা/ দাও পাঠাইয়া।’ সেই বয়সে আ-কার ই-কার শিখে বানান করে পড়তে পারলেও ওই ধাঁধার উত্তর দিতে পারতাম না। কাঁঠাল প্রিয় ফল কিন্তু গ্রীষ্মকাল না-এলে ওই গাঁদাবরণ ফলের কথা মনেই আসতো না।
বাংলা ভাষায় কার-এর যে কতো কারিগরি তা বুঝেছি বড় হয়ে। বর্ণের ‘কার’ আছে, ভাষায় ‘কার’ আছে, ব্যাকরণে কার-এর নিয়ম আছে। সেসব তো বড় না-হয়ে বোঝার চেষ্টা করিনি। কৈশোরে কেবল জেনেছি, স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘কার’ বলে। কার-যে বাংলা ভাষার একটি শব্দ এবং পদের বিচারে সর্বনাম তা-ও জেনেছি কৈশোরে। কিন্তু কার-এর ভেতরে যে এতো রহস্য, তার এতো কারিগরি এবং বিচিত্রবিধ রূপ তা কখনও কল্পনাও করিনি।
স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে যে ‘কার’ তার কথাই ধরা যাক। বিষয়টি শিশুপাঠ্য তবু ধ্বনিবিজ্ঞানীদের দোহাই দিয়ে বলি, এগারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে দশটির ‘কার’ আছে। এর মধ্যে দুটির আছে হ্রস্ব রূপ [ হ্রস্ব-ই-কার ()ি ও হ্রস্ব-উ-কার (ু) ]। দুটির আছে দীর্ঘ রূপ [ দীর্ঘ-ঈ-কার (ী) ও দীর্ঘ-ঊ-কার (ূ) ]। এ-তে এ-কার ()ে। চেহারায় এ-কার ()ে এবং আ-কার (া) মিলে হয় ও-কার (াে)। বাংলা বর্ণমালায় আবার দুটি যুগ্ম স্বরধ্বনি আছে―ঐ এবং ঔ। দুটি স্বরধ্বনির মিলিত রূপ বলে তা যুগ্ম স্বর―ঐ = অই/ ওই এবং ঔ = অউ/ ওউ। দশটি কারের মধ্যে প্রথম স্বরবর্ণ অ-এর দৃশ্যত কোনও কার নেই। তবে আবার আছেও―সেই কার দৃশ্যমান নয়, অদৃশ্য। তা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে লুকানো থাকে। অ-কার শব্দে ও বানানে দেখা যায় না কিন্তু উচ্চারণে বোঝা যায়। শব্দের শেষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অ-কারটি আমরা কখনও উচ্চারণ করি, কখনও করি না। যেমন ধরুন, ‘কমল’ শব্দটি। এটি আমরা ‘কমল্’ (কমোল্) পড়তে পারি আবার ‘কম্ ল’ (কম্ লো)ও পড়তে পারি। কোনওটি অশুদ্ধ নয়। প্রথমটি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ, পরেরটি স্বরান্ত। শব্দের শেষে স্বরধ্বনির উচ্চারণ সুস্পষ্ট থাকলে তা স্বরান্ত আর স্বরের ধ্বনির উচ্চারণ উহ্য থাকলে বা অস্পষ্ট হলে তাকে বলে ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ। তবে এই উচ্চারণ-ভিন্নতায় অশুদ্ধ উচ্চারণই কেবল নয়―অর্থান্তরও হয়। ওই শব্দটির ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণে (কমল্/ কমোল্) তা বিশেষ্য পদ―একটি ফুলের নাম। আর স্বরান্ত উচ্চারণে (কম্ ল/ কম্ লো) হয়ে যায় ক্রিয়াপদ। তাই বোঝা যায়, অ-কারের লেখ্য বা দৃশ্যমান রূপ না-থাকলেও উচ্চারিত রূপ আছে। উচ্চারণভেদে অ কখনও ও হয়, আবার কখনও যথাযথ থাকে।
এবার ‘কার’ শব্দটির অর্থের রূপরূপান্তর লক্ষ করি। আভিধানিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধানে কারের আছে চারটি ভুক্তি। এগুলো নিম্নরূপ :
ক) কৃ + অ (অণ্) = কার। স্ত্রীলিঙ্গার্থে কারী। বিশেষণ পদ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে এই শব্দটির পনেরোটি অর্থ পাওয়া যায় : ১) কারক, কর্তা, অনুষ্ঠাতা। ২) নির্মাতা : স্বর্ণকার, কুম্ভকার, রূপকার। ৩) রচয়িতা, প্রণেতা, লেখক : গ্রন্থকার, নাট্যকার, সংগীতকার। ৪) পাচক। ৫) জনক, উৎপাদক। ৬) বধ্য পশু। ৭) উচ্চার্য বর্ণ। ৮) শক্তি, বল। ৯) রাজগ্রাহ্যভাগ, কর। ১০) পতি। ১১) যতি। ১২) হিমালয়। ১৩) করকাজাত জল, শিলার জল। ১৪) রতি। ১৫) তপস্যা। এগুলোর মধ্যে বেশ কটির অর্থ একালের বাংলা ভাষায় অচল, প্রয়োগ হয় না―অর্থও অধিকাংশের অজানা। তাই এই মৃতপ্রায় অর্থগুলো ফসিলরূপে বৃহদায়তন অভিধানের পাতায় আশ্রিত।
অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ‘কার’ শব্দের চারটি ভুক্তি থাকলেও তাতে শব্দার্থের পার্থক্য আছে। তাঁর মতে, কার শব্দটি সংস্কৃত কৃ ধাতু থেকে জাত। তবে ফারসি ভাষায়ও কার শব্দটি আছে। তবে বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে আরও একটি ভুক্তি পাওয়া যায়―ইংরেজি পধৎ. এগুলোর অর্থবৈচিত্র্য, ভিন্নতা এবং উৎসমুখ এরকম :
ক) কার = কার্য বা কর্ম―কারখানা, কারবার, বেকার। ২) শিল্পকর্ম―কারুকার্য, কারুকলা, কারুশিল্পী। ৩) নির্মাতা বা প্রস্তুতকারী―রূপকার স্বর্ণকার, কুম্ভকার। ৪) করণ―শব্দকরণ, জয়জয়কার, আকার, ইকার, সাকার। ৫) কার্যের বন্ধন, কর্মবিপাক, দায়―‘লোকটি এখন কারে পড়েছে।’ ৬) চেষ্টা, যত্ন, সম্বন্ধ, সংস্রব―কারগুজার, কারসাজি, কারচুপি (কারচোরি > কারচুরি > কারচুপি)। কারতূজ (কারতূস > কারতুজ > কার্তুজ)।
খ) কার = কৃ > কর > কার। হরিচরণের মতে, সম্বন্ধসূচক ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর)। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতে, প্রাকৃতে উচ্চারণ বিকারে রূপভেদ―কার > কের > কর > র। আজিকার > আজকের। কালিকার, আগেকার এদিককার, ওদিককার, সবাকার, পিছেকার, ভিতরকার, কাহাকার ইত্যাদি। এই সম্বন্ধসূচক ‘কার’কে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রত্যয় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে শব্দগুলোর বিবর্তন লক্ষণীয় : কালিকার > কালকের > কালের, আগেকার > আগের, এদিককার > এদিকের, ওদিককার > ওদিকের, সবাকার > সবার, পিছেকার > পিছের, ভিতরকার > ভিতরের, কাহাকার > কাহার > কার। প্রাকৃত ভাষায় লক্ষ করা যায়, বর্গের প্রথম ধ্বনি তৃতীয় ধ্বনিতে রূপান্তর হয় ( ক > গ)। এই নিয়মে আমাকার > আমাগোর > আমাগের > আমাগর > আমগর।
গ) কার = ইংরেজি কার্ড (পধৎফ) থেকে সৃষ্ট। বিশেষ্য পদ। অর্থ : পাকানো সুতা, পকেটঘড়ি বাঁধার সুতা, রেশমি ঘুনসি, (চশমার ফ্রেমে লাগিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখার সুতা―বর্তমান লেখক)।
ঘ) কার = কারা, জেলখানা। বিশেষ্য পদ। কারাগার, কারাবাস, কারাবন্দি ইত্যাদি।
ঙ) কার = ইংরেজি পধৎ. বিশেষ্য পদ। ইঞ্জিনচালিত গাড়ি, মোটরগাড়ি, মোটরযান।
এই কার শব্দটি বেশ মজার! এটির শেষে যেমন বিভক্তি, প্রত্যয় বা অন্য শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে যেমন যুক্ত থাকে, তেমনই এর সামনে উপসর্গও যুক্ত থাকতে পারে। এর ফলে শব্দের অর্থান্তর ঘটে এবং নতুন শব্দ গঠিত হয়। এসবের কিছু নমুনা :
কারের পূর্বে সংযুক্ত―আকার, ইকার, প্রকার, সাকার, নিরাকার, বিকার, বেকার, অনুকার, ওঙ্কার, চীৎকার, সহকার, ছড়াকার, গল্পকার, গ্রন্থকার, রচনাকার, আজিকার, সভাকার, রূপকার, অহংকার, বহিষ্কার, তিরস্কার, সাক্ষাৎকার, বলাৎকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার ইত্যাদি।
কারের শেষে সংযুক্ত―কারাগার, কারানির্যাতন, কারচুপি , কারবার, কারখানা, কারিগর, কারদানি, কারচুপি (কাপড় বা অন্য কিছুর ওপর নকশার কাজ), কারনামা, কারসাজি, কারকিত, কারকুত (কাজের নৈপুণ্য), কারকুন (জমিদারি কাজের তত্ত্বাবধায়ক), কারগুজারি (কার্যসম্পাদন) ইত্যাদি।
এবার মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের খ্যাতিমান কবি-লেখকদের রচনা থেকে কার শব্দের প্রয়োগের কয়েকটি উদ্ধৃতি চয়িত হলো :
* কার পান চুন নাঁহি খাঁও। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস)
* কার হৈলা অনুমৃতা প্রাএ। (মালাধর বসু)
* চোরে দিয়া মিয়া সাউদেরে দেয় কার। (কারাবাস অর্থে, মৈমনসিংহ গীতিকা)
* মধুসূদন সর্ম্মা কারকুন সুচরিতেষু। (ঞুঢ়বং ড়ভ ঊধৎষু ইবহমধষর চৎড়ংব নু ঝরাধ ঊধঃধনষব গরমৎধহঃ)
* নিদান নামেতে তার আছয়ে কারকুন। (জমিদারির ব্যবস্থাপক অর্থে, মৈমনসিংহ গীতিকা)
* হাতেতে কারচুপি চুড়ি পায়েতে পাশলি। (ফকির গরীবুল্লাহ)
* বলে দৈত্য, আজি তোরে পাইয়াছি কারে! (কাজের দায় অর্থে, স্বপ্ন প্রয়াণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)
* নীলের জমিতে লাঙল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো। (জমির পরিচর্যা অর্থে, নীলদর্পণ, দীনবন্ধু মিত্র)
* ধানের জমিতে যে কারকুত করিতে হয়, তার চারগুণ কারকুত নীলের জমিতে দরকার। (কাজের নৈপুণ্য অর্থে, নীলদর্পণ, দীনবন্ধু মিত্র)
* প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক? (ফলনযোগ্য জমি তৈরির কাজ অর্থে, জমিদার দর্পণ, মীর মশাররফ হোসেন)
* যেহেতু জুষ শব্দ দীর্ঘ ঊ-কার যুক্ত নহে। (সমাচার দর্পণ পত্রিকা)
* আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তার করে। (১৪০০ সাল, রবীন্দ্রনাথ)
* কারকিত করা গালিচার মত বিছিয়ে যাওয়ার কথা। (সূচিশিল্পের নকশা অর্থে, হাসান হাফিজুর রহমান)
* এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে বাসে হয়তো বা কারএ। (বিষ্ণু দে)।
* মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা। (শিল্পদ্রব্য তৈরির স্থান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)
* তাহাতে রকমে মিনার কারখানা। (কারুকাজ অর্থে, রামরাম বসু)
* মনের ভেদ মন জানে না একি কারখানা। (আশ্চর্য কাণ্ড, লালন ফকির)।
* সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী, ‘ভালোবাসা’ ‘ভালোবাসা’―
সখী, ভালোবাসা কারে কয়।
(নাট্যগীতি, ১১ নং গান, গীতবিতান)
* কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আসলে প্রাতে পুষ্প-চোর।
(নজরুলসংগীত)।
এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এবং সাধুভাষায় ‘কার’ শব্দটি বিচিত্র অর্থে প্রয়োগ করা হতো। আধুনিক যুগের সাহিত্যে আর তেমনটি হয় না। ‘কার’ এখন আমরা ব্যাকরণ, সর্বনাম পদ এবং ইংরেজি শব্দ হিসেবেই বেশি পাই। তবে ‘কার’-এর সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ যুক্ত করে এবং অন্য শব্দ সমাসবদ্ধ করে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।
বাদ
মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ।
―রবীন্দ্রনাথ।
কথার পৃষ্ঠে কথা যেমন আমরা বলি তেমনই কথার বিরুদ্ধেও কথা বলি। অমত-দ্বিমত থাকলে ভিন্নমত প্রকাশ করি। বিতর্কের প্রধান বিষয়ই হলো, কেবল ভিন্নমত নয়, বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা। সহজভাবে লিখলে বিতর্ক মানে বাদ-প্রতিবাদ। ‘বাদ’ শব্দটি আমরা কত বিচিত্র অর্থে-যে ব্যবহার করি তা ভাবলে অবাক হতে হয়! যখন বলি―বাদ দে, আর কথা বাড়াসনে―তখন ছাড় দিতে অনুরোধ করি। যখন অভিজ্ঞ কৃষক বেগুনচারা দু হাত বাদেবাদে রোপণ করতে পরামর্শ দেন তখন সেই বাদ ‘ফাঁক রাখা’ অর্থ বোঝায়। ‘আজীবন থাকে সতীনের বাদ’―এই ‘বাদ’ মানে ঝগড়াঝাঁটি। ‘দশ থেকে পাঁচ বাদ’―মানে বিয়োগ করা। আবার যখন বলা হয়, ওই পরিবারটি ‘দশের বাদ’―তখন সমাজচ্যুত বা একঘরে বোঝায়। রাজপথ প্রকম্পিত করে যখন কণ্ঠবিদীর্ণ শ্লোগান ওঠে ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’ তখন ‘বাদ’ মানে রাজনৈতিক মতবাদ বা দর্শনকে বোঝায়। আবার যখন বলা হয়, ‘বাদ-জহুর’ বা ‘বাদ-মাগরিব’ তখন নামাজের নির্দিষ্ট সময়ের পরে বা শেষে বোঝায়।
তাই ‘বাদ’ শব্দটির অর্থভিন্নতা ও বহুধা ব্যবহার বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়। এটি কখনও বাংলা আবার কখনও আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে যৌগিক মিশ্রণেও ব্যবহার হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সমাসের ভূমিকা মুখ্য। তবে মূল শব্দ ‘বাদ’-এর গঠনে আছে ‘প্রত্যয়’-এর কারুকাজ। তাই ‘বাদ’-এর উৎস-বিচারে ভুক্তি অনেক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধানে বাদ-এর পাঁচটি ভুক্তি আছে। এগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :
* বাদ = এখানে শব্দটি বিশেষণ। এর ধাতুরূপ বদ্ বা বাদি। বুৎপত্তি―বদ্ + অ/ বাদি + অ = বাদ। হরিচরণ শব্দটির অর্থ লিখেছেন : ১) কথন, ভাষণ, ২) কীর্তন, ৩) ধ্বনি, ৪) কূজন, ৫) নিন্দা, অপবাদ, ৬) বিবাদ, ৭) দোষ, (এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ―চৈতন্য চরিতামৃত) ৮) জল্প-বিতণ্ডা, ৯) তত্ত্বনির্ণয়ে কথাপ্রসঙ্গ, ১০) কথা, বাক্য, শব্দ, ১১) উক্তি, ১২) কীর্তি, ১৩) আখ্যান, ১৪) সিদ্ধান্ত, ১৫) অভিযোগ, ১৬) জনশ্রুতি, (বীরের ধনের বাদ―কবিকঙ্কণ-চণ্ডী) ১৭) প্রতিবচন, ১৮) শত্রুতা, (নাথ দরশ সুখে বিহি কৈল বাদ―বিদ্যাপতি) ১৯) যুদ্ধ, (মম সনে বাদে আয়ু শেষ হল তোর―বাইশ কবি মনসা) ২০) আড়ি, (জানিতে না বরে বাঁঝি সতীনের বাদে―কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)। লক্ষ করা যায়, প্রথম ভুক্তির বিশটি অর্থের মধ্যে হরিচরণ মাত্র পাঁচটি প্রয়োগের উদাহরণ দিয়েছেন বাংলা ভাষা থেকে―অধিকাংশ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে।
* বাদ = এটি বিশেষ্য পদ। সংস্কৃত শব্দ অপবাদ থেকে বাদ। এর অর্থগুলো নিম্নরূপ :
১) বাধ, নিষেধ, বারণ, (সঙ্কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়। চৈতন্য চরিতামৃত) ২) বাধা, বিঘ্ন (সভারে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাদ―চৈতন্য চরিতামৃত।) ৩) বিয়োগ করা, ছাড়া (মুণ্ডারি ভাষা থেকে আগত। দশ মণে এক মণ, বাদ দেও বাছাধন―শুভঙ্কর)।
* বাদ = বিশেষ্য পদ। ফারসি শব্দ ‘বরবাদ’ থেকে আগত। হিন্দি ভাষায়ও শব্দটি প্রচলিত। এর অর্থ : ১) নষ্ট, অসমাপ্ত, পণ্ড; (ঘোড়া ধরি লই জাএ যজ্ঞ হএ বাদ―অশ্বমেধ পর্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।) ২) বিফল, ব্যর্থ; (ব্রহ্ম-মন্যু-আশীর্বাদ, কালে ফলে হয় না বাদ―দাশরথি রায়ের পাঁচালি।)
* বাদ = বিশেষ্য পদ। বায়ু অর্থে।
* বাদ = ক্রিয়া বিশেষণ। অর্থ : অনন্তর, পরে, ব্যতীত, গেলে। (তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল। নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া দ্বারে ঘুচাইল খিল। ―কালিদাসী মহাভারত)।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ‘বাদ’ শব্দটির তিনটি ভুক্তি আছে। তাতে আছে :
* বাদ = বিশেষ্য পদ। বুৎপত্তি : বদ্ (বলা) + অ = বাদ। অর্থ : ১) কথন, ২) বাদ্য, ৩) বিতর্ক, ৪) নিন্দা। পরি, অপ, লোক ইত্যাদি উপসর্গযোগে বাদ শব্দটি নিন্দা অর্থে বোঝায়। যেমন―পরিবাদ, অপবাদ, লোকবাদ ইত্যাদি। প্রয়োগ : ফুলচুরি বাদ আছে সহিতেঁ না পারী। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। লোকবাদ খণ্ডিবারে বনবাস দিল তারে আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে। (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)।
* বাদ = বিশেষ্য পদ। সংস্কৃত শব্দ। অর্থ : ১) ব্যর্থ, ২) ছাড়, ৩) ছাঁট, ৪) নারকেলের ছোবড়ার দড়ি, ৫) পশ্চাৎ, পরে, অন্তর, ৬) বাকি। উদাহরণ : বাঁশটার আগার দিকে খানিকটা বাদ দিয়া কাট। কোন কিছুর বাদ রাখা ভাল না। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)।
* বাদ = বিশেষ্য পদ। সংস্কৃত শব্দ বাধ থেকে বাদ। অর্থ : বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।
ভুক্তিভেদে লক্ষ করা যায়, বাদ শব্দটি উৎস কখনও সংস্কৃত বা তৎসম আবার কখনও আরবি ও ফারসি। বাক্যে প্রয়োগের ভিন্নতার জন্য এটি পদান্তর হয়―বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে, হরিচরণ বা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে ‘বাদ’ শব্দটি অর্থ মতবাদ বা দর্শন হিসেবে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি! মান্য অভিধানগুলোর মধ্যে কেবল বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ‘মতবাদ বা থিয়োরি’ অর্থের উল্লেখ আছে। এযুগে প্রচলিত অন্যান্য অর্থের সঙ্গে মতবাদ বা দর্শন অর্থে বাদ-এর প্রচলন ব্যাপক―বিশেষত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। যেমন―ভাববাদ, বস্তুবাদ, নারীবাদ, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মরমিবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি। ফ্যাসিবাদ ইদানীং খুব আলোচিত ও বহু উচ্চারিত শব্দ। এখন আবার শোনা যাচ্ছে―পালনবাদ। এসব মতবাদের কথা যেমন রাজনৈতিক সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত তেমনই রাজপথের স্লোগানেও চীৎকৃত।
আমরা যেমন অন্যায়ের প্রতিবাদ করি তেমনি বিদেশি ভাষার লেখা অনুবাদও করি। আমরা সুকর্মের জন্য সাধুবাদ জানাই আবার নির্দোষকে অজান্তে অপবাদও দিই। আমাদের দেশে বাদানুবাদের অন্ত নেই, বাদাবাদিরও শেষ নেই―নিন্দাবাদও করি, জিন্দাবাদও দিই! আবার আইনজীবীরা আদালতে জিজ্ঞাসাবাদও করেন―যাকে আদালতি শব্দে বলা হয় ‘শাওয়াল-জবাব’। এভাবে অবিরত বাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে-থাকা যেন বাঙালি-চরিত্রের কুললক্ষণ! ‘বাদ’ শব্দের প্রাচীন অর্থ এবং প্রয়োগের কথা বাদ দিলে আমরা আধুনিক প্রয়োগসিদ্ধ যে-অর্থগুলো পাই তা ভুক্তিভেদে বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান মতে এরকম :
১) কথন, ভাষণ, উক্তি। ২) বাক্য। ৩) তর্ক, কলহ। ৪) মত, মতবাদ। ৫) যথার্থ বিচার। ৬) প্রতিবন্ধ, বাধা, বিঘ্ন। ৭) শত্রুতা, বিপক্ষতা। ৮) ছাড়, বিয়োগ। ৯) ছাঁট। ১০) ত্যাগ। ১১) পরে।
বাংলা সাহিত্যে এই ‘বাদ’ শব্দটির বহুবিচিত্র অর্থে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে সমকাল পর্যন্ত এর কয়েকটি প্রয়োগ কালানুক্রমে উল্লেখ করা হলো :
* কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে। (ঝগড়া অর্থে, বড়ু চণ্ডীদাস, ১৪৫০)।
* কেন হেন মিথ্যা বাদ হইল আচম্বিতে। (কথা অর্থে, মালাধর বসু, ১৫০০)।
* ছাগলরক্ষণে যদি তুমি কর বাদ/ তোমার জামাতা লয়্যা পড়িব প্রমাদ। (বিরোধ অর্থে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ১৬০০)।
* মনুষ্য কি বাদে পারে তার সনে। (মনোমালিন্য অর্থে, চৈতন্য ভাগবত, ১৬৫০)।
* এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সঙ্গতি। (বলল অর্থে, আলাওল, ১৬৮০)।
* নামাজ বাদেতে তবে খতিব হইয়া। (পরে অর্থে, গরীবুল্লাহ, ১৭৬৫)।
* বাদাবাদে দুইজনে বাজিল ঘোর রণ। (বাক বিতণ্ডা অর্থে, মানিকরাম,১৭৮১)।
* জেন পৌত্রিক পুর্নেহ কর্ম বাদ না হয়। (বর্জন অর্থে, ওগাস্তাঁ ওসাঁ, ১৭৮২)।
* খরচখরচা বাদে ব্যয় ভিন্ন। (ছাড়া অর্থে, প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮৫৮)।
* বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল দেখি। (বাকি আছে এমন অর্থে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৬০)।
* সাহিত্যের বাদবিরোধ এমন প্রবল ছিল না। (মতপার্থক্য অর্থে, রবীন্দ্রনাথ, ১৯০১)।
* সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাজ করাই স্বাভাবিক। (ত্যাগ অর্থে, প্রমথ চৌধুরী, ১৯১৭)।
* আমি হাফিজের মাত্র দু’টি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি। (ছাড় অর্থে, নজরুল ইসলাম, ১৯৩০)।
* যাদের নাম বাদ পড়ে গেল তাঁরা নিজগুণে আমাকে মার্জনা করবেন। (অনুল্লেখ অর্থে, বুদ্ধদেব গুহ, ১৯৭২)।
(উদাহরণগুলোর উৎস : ১) বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড ২) বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড ৩) বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড ৪) বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ৫) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের অভিধান, মোহাম্মদ হারুন রশীদ সংকলিত)।
আমরা লক্ষ করেছি, ‘বাদ’ শব্দটি কেবল দ্ব্যর্থবোধক নয়―বিচিত্র ও বহুধা অর্থের ধারক। এর সঙ্গে আগেপিছে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ করেও অর্থের বিকাশ, সংকোচ, সম্প্রসারণ ও রূপান্তর করা যায়। তবে বাদ নিয়ে বিবাদ ও বাদানুবাদ যতই থাকুক, বাংলা ভাষার প্রবাদগুলো, যা বহুকাল থেকে প্রচলিত উপদেশমূলক জ্ঞানগর্ভ বচন, তা আমাদের সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজতত্ত্বের মূল্যবান সম্পদ।
[চলবে]সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ