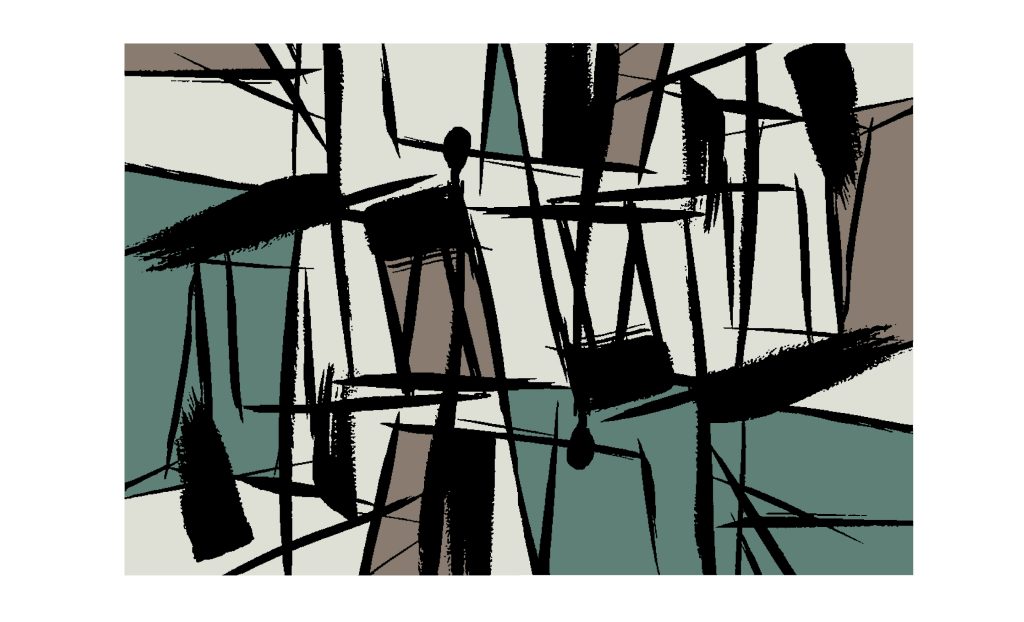
সালাম বিনিময় কিংবা ‘কেমন আছেন’ প্রশ্নে হাই-হ্যালো সামাজিকতা, ফোনে হোক অথবা সাক্ষাতে, চেনা কি অচেনা মানুষের আন্তরিক কিংবা নিছক দায়সারা―আমার জন্য বড়ই অস্বস্তি বয়ে আনে। সামাজিকতার দায় সারতে এই আছি আর কী বলি। হাসিমুখে ভালো থাকার ভান করি। মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে এড়িয়েও যাই কখনও-বা, কিন্তু প্রশ্নকর্তার ভালো-মন্দ থাকা নিয়ে তেমন কৌতূহল জাগে না। কারণ আমি নিজে ভালো নাই। অসুখের ভারে কাঁপছি সারাক্ষণ। অপরের ভালোমন্দ নিয়ে ভাবার সময় কোথায় ?
দুরারোগ্য পার্কিনসন রোগে হাতের কাঁপুনি বেড়েছে। শরীরের স্বাভাবিক চলমানতা ব্যাহত হচ্ছে। মুশকিল হলো, যারা জানে তারাও যেন ভয়ে ভয়ে রোগটাকেই জিজ্ঞেস করে, কেমন আছেন ? চেনাজানাদের মধ্যে যারা আমার এই কালব্যাধি পিডি সম্পর্কে অজ্ঞ এখনও, তাদের দাঁত কেলানো ‘কেমন আছেন’ আরও চওড়া হয়। জবাবে অজ্ঞ কৌতূহলীদের কম্পিত হাতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, মুখেও বলি―ভালো নাই রে ভাই।
পার্কিনসন তো আর সর্দিকাশির মতো মামুলি অসুখ নয়। অনেকে জীবনে প্রথম দেখার বিস্ময় নিয়ে আগাম সহানুভূতি দেখাতে আন্তরিকতার সঙ্গে জানতে চায়, ‘কী হইছে! হাতটা এমন কাঁপছে কেন ?’
আমি অসুখের বয়ান শোনাতে চাই না। বরং হাসিমুখে বলি, ‘ভূমিকম্প শুরু হইছে। আমার মনে হয়, ভূমিকম্পে এবার সব ধ্বংস হবে।’
কুশল জানতে চাওয়া স্বজন-বিজনের সহানুভূতি উদ্বেল হলে কিছু সুখ বোধ করি। শুধু হাত নয়, রোগের প্রকোপে আমার গোটা শরীর প্রায়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। কথা বলতে গেলে অনেক সময় মুখ বেঁকে যায়। ইচ্ছে করেও মুখ বেঁকিয়ে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে সুস্থদের সহানুভূতি আদায়ে ভয় দেখাই, আবার পাগলের অভিনয় করে হাসাতেও চেষ্টা করি কখনও-বা। যারা আমার অস্বাভাবিক শরীর ও কথাবার্তায় বেশি উদ্বিগ্ন হয়, কম্পিত হাত চেপে ধরে পাশে দাঁড়ায়, তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ‘ভয় নাই। এই ভূমিকম্পে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি ও আমার পরিবার ধ্বংস হব। হাত চেপে ধরলেও পিডির থরহরি কম্প থামবে না ভাই! কাঁপতে কাঁপতেই যেদিন মরে যাব, সেদিন শান্ত স্বাভাবিক হব।’
আমাকে দেখতে এসে আমার এরকম কথাবার্তা শুনে ছোট বোনটি তার প্রিয় মেজভাইকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল।
আসলে ভূমিকম্পের সঙ্গে নিজের অসুখটাকে তুলনা করা ও নিজের পরিবার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী মোটেও ঠাট্টা-মস্করা নয়। রূপকটা অনেক গভীর থেকে মাথায় এসেছে। বেচারা হাতের কাঁপুনি দেখে ভূমিকম্প নিয়ে দেখা একটি সিনেমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। অনেক বছর আগে সুস্থ যখন, মানে নিষ্কম্প-স্থির অবস্থায় দেখেছিলাম। বেশ ভয় ধরানো ছবি।
আজগুবি ঘরের ঝাড়বাতি, মানুষসহ একটি বসার চেয়ার ও ঘরের সব আসবাবপত্র থরথর কাঁপতে শুরু করল। শো-কেসের সাজানো জিনিসপত্র মেঝেতে ছিটকে পড়ে ঝনঝন ভাঙছে। চেয়ারে বসা মানুষটি আতঙ্কে বিহ্বল, চারদিকে তাকাচ্ছে। সব কাঁপতে দেখে নিজেও কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরুলো, কিন্তু পালাবে কোথায় ? ঘরের বাইরে রাস্তার লাইটপোস্ট, গাছ, এমনকি উচ্চ ভবনও মাথা দুলিয়ে কাত! হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল একটি ছাদ, একটি পুকুরের পানি ফোয়ারার মতো উথলে উঠছে রাস্তায়। দিশেহারা কম্পমান মানুষ, কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর এমনকি আকাশে পাখিরাও ছুটে পালাতে চাইছে। রাস্তায় ছুটে পালাতে গিয়ে ভেঙ্গেপড়া ঘরবাড়ি কি গাছের নিচে চাপা পড়ছে, রাস্তার গর্তেও পড়ে গেল একজন, তার কম্পমান হাত মাটির উপরে…
জানি, সিনেমাটা তৈরি করা হয়েছিল খেলনা ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে। পৃথিবীর নকল প্রতিচ্ছবি বানিয়ে তা ইচ্ছেমতো ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে মোটেও বানানো মনে হয়নি। কারণ বিশ্বের নানা দেশে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির যেসব খবর পড়েছি, নিজেও বারকয়েক ছোট-মাঝারি ভূমিকম্প যেভাবে অনুভব করেছি, সেটা তো আর বানোয়াট ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে কেয়মাতের কথা। মোল্লা-মওলানা নই, কিন্তু আমি গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। মনেপ্রাণে জানি, এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। ভূমিকম্পে হোক আর মহাপ্লাবনে হোক―একদিন ধ্বংস হবে এ পৃথিবী। সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে গোটা মানবজাতি। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও অনন্ত পরকালই হবে আমাদের আসল স্থায়ী ঠিকানা।
তারপরও অস্থির এ দুনিয়ার সত্য হলো, মরতে হবে জেনেও মরার ভয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে প্রতিটি প্রাণি। কারণ সৃষ্টির সময়ে স্রষ্টা প্রতিটি জীবের মধ্যে এ জীবধর্ম দিয়েছে। মানুষের এ জীবধর্ম বিকশিত হওয়ায় গড়ে উঠেছে আজকের এই সমাজ ও সভ্যতা। জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে এবং নিরাপদে বাঁচার জন্যই নারী-পুরুষ মিলে পরিবার গড়েছে মানুষ। ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন বানিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে কত-শত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ হয়েছে। কিন্তু ভূমিকম্প ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক মার কি ঠেকানো গেছে ? পরিবার রক্ষায় ধর্ম ও সমাজের নিয়ম-নৈতিকতা কি রক্ষা করতে পারছে সব পরিবার ? ক্ষয়ক্ষতি কিছু কমানো যাচ্ছে বটে, কিন্তু আল্লার ইচ্ছেয় প্রকৃতি বড় ধরনের বিপর্যয় যখন দেবে, অসহায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হবে মানুষ।
সর্বশক্তিমান স্রষ্টার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এরকম চিন্তা করি। জন্মগত জীবধর্মের কারণেই সম্ভবত, ভূমিকম্পের সিনেমাটি দেখে, দেশে সত্যিকার ভূমিকম্প হলে কীভাবে বাঁচব, তার উপায় নিয়েও ভাবতে শুরু করেছিলাম। সহসা ভূমিকম্প শুরু হলে আত্মরক্ষার উপায় খোঁজার মতো স্থিরতাও থাকবে না। আর ভূমিকম্প কোথায় কখন হবে, তার ভবিষ্যদ্বাণীও কেউ করতে পারেনি। অগ্রিম বুদ্ধি ঠাওরে রাখলে বিপদের সময় তা কতটা কাজে লাগবে জানি না, তবু ভেবেচিন্তে ঠিক করেছিলাম। ভয়ে ছোটাছুটি করব না। পরিবারের সবাইকে বাঁচাতে পারব না, কিন্তু নিজে বাঁচার জন্য পালাতেই যদি হয়, ঘরের খাট-টেবিলের নিচে না লুকিয়ে বড় একটা ড্রামের ভিতরে গিয়ে লুকাব। ড্রামটি কম্পমান পৃথিবীতে গড়াতে গড়াতে যদি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে এবং ভিতরে আল্লার ইচ্ছেয় কোনওমতে প্রাণবায়ুটা ধরে রাখতে পারি, ভূমিকম্প থেমে গেলে উদ্ধারকারীদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা হলেও হতে পারে। অগণিত দৃষ্টান্ত আছে, বৈরী শক্তি পরিস্থিতি পরাস্ত করে বেঁচে থাকে মানুষ। আমরা তখন বলি, রাখে আল্লাহ মারে কে ?
বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে, অনিবার্য মরণের মুখেও অলৌকিকভাবে বেঁচে থাকা মানুষও আমাকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। বাংলা ১৩৪৩ সালে হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল, ভুটান ও উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প মৃত্যু হয়েছিল বিশ সহস্রাধিক মানুষের। সেই ভূমিকম্পে আমাদের বাড়িতে ঘরের টিন পড়ে মৃত্যু হয়েছিল আব্বার দাদির। আর তার যুবতী মা আঙিনায় একশ গজ জায়গা দৌড়াতে গিয়ে ১৩ বার উল্টে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ির কুয়ায় একটা সোনার কবজ, কাঁসার বদনা আর বালতি পড়ে গিয়েছিল। কুয়ায় লোক নেমেও তুলতে পারেনি, কিন্তু ভূমিকম্পে সেই কুয়ার পানিসহ আঙিনায় উগলে দিয়েছিল হারানো সবকিছু। গোরস্থান থেকে একজনের লাশ বেরিয়ে পড়েছিল জেন্দা মানুষের মতো। আর একটা গরু আকাশের দিকে পা তুলেও দৌড়ে বাঁচতে চেয়ছিল, পুকুরে পড়ে গিয়ে ইঁদুরের মতো নাকানি-চুবানি খেয়েও বেঁচেছিল বাড়ির কুকুরটা। ছোটবেলায় গাঁয়ের বুড়াবুড়িদের কাছে শুনে অবিশ্বাস্য মনে হয়নি এসব গল্প। কারণ মহাপ্রলয়ের আগে গোটা পৃথিবীতে ধ্বংসের আলামত পষ্ট হতে থাকলে এরকম অবিশ্বাস্য ও উল্টাপাল্টা ঘটাই তো স্বাভাবিক।
ভূমিকম্পের এসব গল্প ও সিনেমায় দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি আমি হয়তো ভুলেই যেতাম, জীবনে দেখা হাজারো সিনেমা-নাটক, বইয়ে পড়া ও লোকমুখে শোনা অজস্র কেচ্ছা-কাহিনি―যা মনে দাগ কাটেনি, ভুলে গেছি সবই। কিন্তু ভূমিকম্প নিয়ে বানানা অসাধারণ ছবিটা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে কি নিজেও একদিন কম্প রোগ তথা পার্কিনসন রোগে আক্রন্ত হব বলে ? দুরারোগ্য এই ব্যাধি যখন প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুল কাঁপাতে শুরু করে, তখনই প্রথম ভূমিকম্পের সিনেমাটি মনে পড়েছিল। এরপর কম্পরোগ যখন আঙ্গুল থেকে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও বিস্তারের মাধ্যমে প্রবল হতে থাকে, ততই যেন পরিবারসহ গোটা সমাজে অস্থিরতা ও ধ্বংসের আলামতগুলি আমার চোখে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এই যে নিজে কাঁপার সঙ্গে সঙ্গে চেনাজানা সকল মানুষকে, মানুষগুলির প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক কি সামাজিক সম্পর্কগুলিকে অস্থির ও কম্পমান অবস্থায় দেখছি, এটা কি আমার দেখার ভুল ? না কি ধ্বংস-আতঙ্ক নিয়ে চেনা পৃথিবীটা আসলে ভূমিকম্পের মতো থরথর কাঁপছে ? মনে হয়, জীবজগতের অনেক গভীর সত্য ভাবতে এবং অনুভব করতে পারছি এই রোগটি ধরা পড়ার পর থেকে।
ভূমিকম্প তো ঘটেছে কালেভাদ্রে। ভবিষ্যতেও ঘটবে অনিশ্চিত-কাল ব্যববধানে, তাও গোটা বিশ্বজুড়ে একসঙ্গে নয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটি স্থানিক ও মুহূর্ত কয়েকের বাস্তব মাত্র। অন্যদিকে ভূমিকম্প ছাড়া বছরের পর বছর পৃথিবী নিজস্ব নিয়মে ঘুরছিল, তখন মাটির এ পৃথিবীকে স্থির ও স্বাভাবিক হিসেবেই দেখি আমরা। এই স্থির স্বাভাবিকতাই মনে হয় আমাদের বিশ্বাসযোগ্য স্থায়ী সত্য। নিজস্ব গতিতে অস্থির এ পৃথিবীতে দিন হয় রাত হয়, শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-বসন্ত আসে―এসব পরিবর্তনকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখি আমরা। কিন্তু আমি এখন নিজের পরিবারসহ গোটা পৃথিবীকে প্রায়ই সেই ভূমিকম্পে কাঁপার মতো কম্পমান অবস্থায় দেখি এবং ধ্বংস-আতঙ্কে ভুগছি, এ নিশ্চয়ই স্বাভাবিকতা নয়। স্থির ও স্বাভাবিক পৃথিবীর মানুষরাও আমার শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে সারাক্ষণ থরথর কাঁপতে দেখে, আমাকেও সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে না জানি। একটি কৌতূহলী শিশু তো সরাসরি জানতেও চেয়েছিল, ‘এই পাগলা, হাত কাঁপাও ক্যা ?’ আমি পাগলের মতো হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলাম, ‘ভূমিকম্প। ধ্বংস হবি।’
নানা প্রকার অসুখ-বিসুখ কিংবা অস্বাভাবিকতা তো সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু এই কালব্যাধি আমাকে শুধু একা ও অস্বাভাবিক করেনি, গোটা পৃথিবীকে যেন দু ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। স্বাভাবিক-অস্বাভবিক, স্থির-অস্থির, সুন্দর-অসুন্দর, সৃষ্টি-ধ্বংস এরকম হাজারো বৈপরীত্যে ভরা দু রকম জীবন একই সঙ্গে দেখি আমি। বলা যায়, পিডি আক্রান্ত হওয়ার পর আমার দেখার চোখ পাল্টে গেেেছ। একই সঙ্গে দুই চোখে আমি বিশ্বের দুটি রূপ দেখি। একইভাবে নিজের জীবনটাকেও দুই রূপে ও দুই পর্বে ভাগ করে নিয়েছি। চাল্লিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাক-পিডি জীবন, যাকে বলা বলা চলে স্থির ও স্বাভাবিক পর্ব। ঘরে যখন চেয়ারে কি বিছানায় ঘুমন্ত মানুষের মতো নিষ্ক্রিয়, অবসরে চুপচাপ একা থাকি যখন, যাপিত স্বাভাবিক জীবনের নানা স্মৃতি-ছবি উপভোগ করাই যেন কাজ। অন্যদিকে চল্লিশের পর অদ্যাবধি পার্কিনসন রোগ নিয়ে আমার বেঁচে থাকার লড়াইকে বলা যায় জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে পার্কিনসনের সঙ্গে কুস্তি লড়ে নিজের দৈনন্দিন বাঁচা এবং ভূমিকম্পগ্রস্ত আমার পৃথিবীর বাসিন্দা তথা আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র, চেনা-অচেনাদের সঙ্গে সম্পর্কের স্বরূপটা অন্যদের দেখাতে পারি, তা হলে আমার মতো কম্পমান ও নিষ্কম্প সব মানুষই কিছুটা মজা পাবে। একই সঙ্গে নশ্বর জীবন-জগৎ সম্পর্কে বোধ-অভিজ্ঞতা কিছুটা হলেও বাড়বে হয়তো। আমার জীবন কাহিনি জেনে তাদের লাভক্ষতি যাই ঘটুক, নিজের জীবন-স্মৃতি ও ধ্বংসোন্মুখ ভবিষ্যৎ নিজের একাকিত্বে যে দুঃসহ চাপ সৃষ্টি করে, সেই ভার অন্তত লাঘব হবে খানিকটা। আত্মজীবনী লিখলে, অবসরে একা হয়েও নিজের যাপিত জীবন আরও একবার যাপনের জাবর কেটে ব্যস্ত সময় কাটাতে পারব।
২.
বয়স চল্লিশ পুরো হতে মাস দুয়েক বাকি, তারিখটা ছিল ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর। নিউরোলজির প্রফেসর আব্দুল মান্নানের প্যাডে আমার পার্কিনসন শনাক্তকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশনের উপরে তারিখটা হাতে লিখে বসানো। এ দিন প্রথম জানতে পারি আমার পার্কিনসন হয়েছে। অসুখ ধরা পড়ার পর থেকে তার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং এ যাবৎ যত ওসুধ খেয়েছি, ডাক্তাররা কতো টাকা খেয়েছে, তার মোটামুটি হিসাব মিলবে এই ফাইলটিতে। ডাক্তারি ফাইলটি আমার স্ত্রী মারিয়া বেশ যত্ন করে রাখে। স্বামীর যথাযথ চিকিৎসায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠা প্রমাণের জন্যই সম্ভবত। কিন্তু নিজের অবস্থা বোঝার জন্য আমার ফাইল লাগে না। মগজের স্মৃতিকোষে প্রয়োজনীয় যে তথ্য-ছবি ডায়েরির মতো অমোচনীয় কালিতে লেখা হয়, ড্যামেজ না হওয়া ব্রেনের যে অংশে চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিগুলি যেভাবে কাজ করে, সেগুলি প্রয়োগ করে নিজের বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারি। ভবিষ্যৎও আন্দাজ করি অনেকটা নিশ্চিতভাবে। আর অতীত তো জীবন্ত ছবি হয়ে ওঠে যখন-তখন, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও।
দুরারোগ্য পার্কিনসন শনাক্ত হওয়ার আগে, রোগটার লক্ষণ প্রথমে ধরা পড়ে আমার ডান হাতের তর্জনীটা কাঁপার মধ্য দিয়ে। একদিন লক্ষ করি, আমি আঙ্গুলটা কাঁপাচ্ছি না, কিন্তু ওটা থিরথির কাঁপছে। ভাবলাম, অফিসে এক যুগেরও অধিক কাল রোজ অনেকক্ষণ আঙ্গুলে কলম পিষে কাজ করছি। ক্লান্তিতে ওটা ওরকম করছে। ব্যাংকের কাজ, ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। তার উপর আমি যে সেকশনে দায়িত্বে ছিলাম, নানারকম ফরম পূরণ ও লেজার লেখার কাজটিও ছিল বেশি। সহকর্মী আমার আঙ্গুল কাঁপা লক্ষ করলে হেসে জবাব দিয়েছিলাম, ‘মাছিমারা কেরানি তো, মাছি মারার জন্য হাতটা নিশপিশ করছে। একটা মাছি মারতে পারলে ঠিক হয়ে যাবে।’
সহকর্মী হেসেছিল। কিন্তু অফিসের বাইরে বাসায় যখন অবসরে, তখনও আঙ্গুল কাঁপতে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যাই। আমি নড়াচ্ছি না মোটেও। থামতে বলছি। থামছে না। একটু একটু করে কাঁপছে কেন ? বলশক্তিও যেন কমে গেছে। মারিয়াকে প্রথম বললাম, ‘কী ব্যাপার গো! আমার ডান হাতের এ আঙ্গুলটা সব সময় কাঁপে কেন ? কোথায় আঘাত পেলাম বলো তো ?’
আশ্চর্য, মারিয়া আমার প্রথমে এ কঠিন রোগের লক্ষণ দেখেও নিজের অজ্ঞতা, কৌতূহল কিংবা সহানুভূতি দেখায়নি এক বিন্দু। বরং ঠাট্টাচ্ছলে নিজের প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাই প্রকাশ করেছিল। আঙ্গুল কাঁপার কিছুদিন আগে আমার মানিব্যাগের টাকা উধাও নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। দাম্পত্যকলহ, বিশেষ করে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়াঝাটি আমাদের প্রায় নিত্যসঙ্গী। কিন্তু টাকার পরিমাণটা বেশি ছিল বলে রাগটাও বেশ চড়া হয়েছিল সেদিন। তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিলাম, ‘তোর বড় ভাই ব্যাংক-ডাকাতি করছে, তোকে আমার ঘরে ঢোকায় দিছে আমার সবকিছু লুট করতে। কিন্তু চোর-বাটপারের মতো এভাবে টাকা সরাস কেন চুরনী মাগি ? ফের যদি একটা টাকা হারায়, তোর গোয়ামারির গুষ্ঠীকে এমন শিক্ষা দেব, তখন বুঝবি কী ধাতুতে গড়া মানুষ আমি!’
চোর প্রমাণিত আগেও হয়েছিল মারিয়া। এমনকি বিয়ের রাতেও, যেদিন সে আসল নামে পরিচয় দিয়েছিল―মোছাম্মত মাহমুদা খাতুন মারিয়া। কিন্তু আসল ও সম্পূর্ণ পরিচয়ে তাকে চিনতে পারিনি আজও। আসল ও পুরো নামে ডাকিনি কোনওদিন। বাসর রাত থেকেই মারিয়া ডাক নামটিকে আদর করে মারি বলে আসছি। কিন্তু সেদিন দিনদুপুরে আদুরে নামের আগে বাজে বিশষণ যুক্ত করে রাগটা তার ব্যাংকার বড়ভাইকে ছাড়িয়ে চৌদ্দ গোষ্ঠীকে মিসমার করায় আঁতে বড্ড ঘা পেয়েছিল বউ। আমার কম্পিত আঙ্গুল দেখে সেদিনের ঝগড়ার স্মৃতি মনে করে হেসে জবাব দিল, ‘সেদিন আঙ্গুল তুলে আমার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছ। সেই অভিশাপে তোমার আঙ্গুল কাঁপছে। বেশি বাড় বাড়লে আল্লাই তাকে শাস্তি দেয়।’
কথাটা আমার স্মৃতিতে গেঁথে আছে এবং বহুবার মনেও পড়েছে। কারণ আমার অসুখের শুরুতে সচেতনভাবে হোক বা অবচেতন স্বভাবে, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার বদলে তার স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসার পাল্লাাটাই ভারী ছিল। এরপর অসুখটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর পরাক্রমশালী লোভ, স্বার্থপরতা ও হিংসার কাছে হেরে গিয়ে ক্রমে আমি কীভাবে একাকিত্ব ও বর্তমান থরহরি কম্পদশায় পৌঁছে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছি; এর জন্য কে কতটা দায়ী, ঠিক বলতে পারব না। সততার সঙ্গে নিজের জীবনকাহিনি লিখলে সচেতন পাঠক হয়তো বিচার করতে পারবেন। প্রথমে অসুখের শুরুর সময়টায় পারিবারিক অবস্থা ও চিকিৎসা বিভ্রাটের কথাটা বলা প্রয়োজন। তা না হলে আমার এই বিচিত্র অসুখের কারণ ও তার নিদান সম্পর্কে হাজার রকম মতের সঙ্গে পাঠকও একটি মত যোগ করবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, এক হাজার এক রকম মত শুনে আমার অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না।
বলেছি যে, প্রথমে আঙ্গুল কাঁপার ব্যপারটা তেমন পাত্তা দিইনি। ভাবতাম, টানা কয়েক বছর ধরে অফিসে কলমপেশা কাজ করার ক্লান্তিতে অবশ-প্রায় আঙ্গুল কেঁপে কেঁপে নালিশ জানায়―আর পারছি না। আমি অন্য হাতের মুঠোয় নিয়ে ডলে ডলে সান্ত্বনা দিই। ভাবি, ব্যয়াম করলেই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। স্ত্রীর অভিশাপ কি প্রতিহিংসাও তেমন আমল দিইনি। বিরাগ-বিবাদ যতই যটুক, অভিমানে যদি মুখের কথাও বন্ধ রাখি দু-একদিন, দূরত্ব ঘোচাতে রাতের দাম্পত্য সুখ অনুভবের বদভ্যাসটি দুটি শরীরে চিমটি কেটে সুড়সুড়ি দেয়। তার ওপর দুজনে আমরা যদি পরিবারের দুই স্তম্ভ হই, তবে এ দুই স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্কের সেতু হিসেবে পোক্ত হয়ে উঠেছে আমাদের একমাত্র কন্যা সুমি। বাবা-মায়ের সঙ্গে সুমি এক বিছানায় যখন থাকত, মারিয়া স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে সেতুরূপী কন্যাকেই শক্ত দেয়াল হিসেবে খাড়া করত অনেক সময়। মেয়ে বড় হয়ে ওঠায় প্রাইমারিতে পড়ার সময়েই তাকে আলাদা বিছানা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে এক ঘরেই মা ও মেয়ের আলাদা বিছানা ছিল, হাইস্কুলে উঠতে না উঠতে ভাড়া বাসায় সুমির আলাদা ঘরও হয়েছে।
সুমির আলাদা ঘর হওয়ার সময়েই আমার পার্কিনসন রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ে। মায়ের মতো সুমির মত ও নিদেনটাও ছিল মনে রাখার মতো। কম্পিত আঙ্গুলটা হাতে নিয়ে টিপেটুপে পাকা ডাক্তারের মতো জিজ্ঞেস করেছিল,―ব্যথা পাও ? না জবাব শুনে আদেশ করেছিল―আঙ্গুলটা ভাঁজ করো দেখি। আমি ভাঁজ করতে পারায় হাত ছেড়ে দিয়ে নিদেন দিয়েছিল, ‘কিছু হয়নি আসলে। বেশি কাঁপলে ওটাকে পাশের ভালো আঙ্গুলের সঙ্গে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রেখ। তাহলে আর কাঁপবে না।’
সুমি নিজেই তার চুলবাঁধা মাথার রাবার-ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল আঙ্গুলটাকে। আর আমি খুশি হয়ে তাকে ডাক্তারের ফি হিসেবে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু রাতে অসুস্থ আঙ্গুলটাকে ভালো আঙ্গুলটাকে নিয়েও মৃদু কাঁপতে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যাই। তারপরও মেয়ের জোর গলার আশ্বাস ‘কিছু হয়নি’ মতের উপর আস্থা রাখতে চেয়েছি। নিজেকে সুস্থ প্রমাণ করতে বিছানায় দাম্পত্য সুখ অনুভবের বদভ্যাসটাও সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। মারিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে টুকটাক কথা শুরু করি, ‘জানো গো মারি, সুমি মনে হয় সত্যি বড় ডাক্তার হবে। কীভাবে আমার কাঁপা আঙ্গুলটা ভালো করে দিল।’
‘মেয়ে আমার বড় ডাক্তার হবেই ইনশাল্লাহ। দেশে এমবিবিএস পাসের পরও বিদেশের বড় ডিগ্রি আনবে। তাহলে অনেক টাকা ফিয়ের বড় ডাক্তার হতে পারবে।’
‘কিন্তু আঙ্গুল কাঁপা কমলেও আমার ইয়েটাও আজ থরথর করে কাঁপছে কেন বলো তো ? এই যে দেখো।’
মনের চাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাড়া না দেওয়ায় ওটাকে নিজেই হাত দিয়ে কাঁপাচ্ছিলাম। মারিয়াকেও তৈরি করতে চাইছিলাম। কিন্তু এ লাজুক মিয়ার গতিবিধি মারিয়ার চেয়ে ভালো কে আর বোঝে। কৌতূহলী হওয়ার বদলে সে পাশ ফিরে শোয়।
‘ঠাট্টা না সত্যি বলছি গো মারি। দেখো একবার হাতে ধরো। কী অসুখের লক্ষণ হইল আল্লায় জানে।’
পরীক্ষার জন্য মারিয়াও সত্যি হাত বাড়ায়। ছুঁয়ে আদর দেখানোর বদলে ছোট্ট কিল দিয়ে ছেড়েও দেয়। তারপরও দুজনের স্পর্শে কিছু শক্ত হয় যেন। চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও মারিয়া আজ ধারণও করে। কিন্তু অভিনয় করেও ভালোবাসার পরীক্ষায় ফেল করি। মাত্র মিনিটখানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা আঁকড়ে রাখতে পারি না। গড়িয়ে আলাদা হলে মারিয়া স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করে।
‘শুধু খপ খপ করো, উঠতে না উঠতেই আউট! কী হইছে তোমার বলো তো ?’
‘কী জানি কী হইল! মন চাইলেও শরীর পারে না। আসলেই খুব দুর্বল বোধ করছি।’
‘কাজের মেয়ের সঙ্গেও ফষ্টিনষ্টি করার সময় তো খুব তেজ দেখিয়েছ। সেই পাপেও হইতে পারে এই রোগ।’
আমি মিনমিনে গলায় জবাব দিই, ‘কালকে ডাক্তারের কাছে যাব দেখি।’
৩.
আঙ্গুল কাঁপা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণ বুঝতে প্রথমে পাড়ার ঔষধের দোকানে বসা সাধারণ এক এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যাই। বিশেষজ্ঞ নয় বলেই সর্বজ্ঞ যেন। দশ টাকা ফিসের সাধারণ প্রাকটিশনার হলেও তার রোগীর পসার কম নয়। সিরিয়াল দিয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর ভিতরে ডাক পড়ে। মারিয়াও সঙ্গে এসেছে। বয়স্ক ডাক্তারকে কম্পিত আঙ্গুল দেখাই। দুর্বলতার কথা বলি। ডাক্তার একটা লোহার সাঁড়াশি দিয়ে আঙ্গুলে টুকটাক বাড়ি দিয়ে পরীক্ষা করে। প্রেসার মাপে, পালস দেখে, আড় চোখে মারিয়াকেও দেখে। জিজ্ঞেস করে নানারকম প্রশ্ন। কী করি, রাতে ঘুম হয় কি না ঠিকমতো, খাওয়ার রুচি আছে কি না, অফিসে বা সংসারে কোনও টেনশন হচ্ছে কি না ইত্যাদি। ডাক্তারের সব প্রশ্নের জবাব দিই, কিন্তু রাতের দাম্পত্য শয্যায় ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার কথাটি বলতে পারি না। নিজের পৌরুষের অক্ষমতা সহজে কবুল করতে পারে কোনও পুরুষ ? তাও আবার স্ত্রীর সামনে।
মারিয়াও স্বামীর বদনাম করতে পারে না। শুধু বলে, ‘শারীরিকভাবে ও খুব দুর্বল হয়া যাইতেছে ডাক্তার। খাওয়াইতে তো কোনও ত্রুটি করি না। অফিসেও টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত দিই। কিন্তু তারপরও এত দুর্বলতা কেন ? আর আঙ্গুলের কাঁপুনি তো থামছে না।’
ইশারাতেই হয়তো বোঝে অভিজ্ঞ বুড়ো ডাক্তার। জানতে চায়, ‘শরীর দুর্বল, নিজের আঙ্গুলকেও কন্ট্রোলে রাখতে পারছেন না! ঘুমও হয় না ঠিকমতো। ভয় পাওয়া বা টেনশন করার মতো ঘটনা অফিসে বা পরিবারে ঘটেছে কী ?’
আমি খুব চমকে উঠি। কারণ অফিসে দশ কোটি টাকার ঋণখেলাপির কেসটায় তদন্ত হবে শুনে চাকরি হারানোর ভয়টাও দিনে দিনে বাড়ছে। ডাক্তারকে ঘটনাটা জানাতে উৎসাহ বোধ করি, ‘আপনি ঠিক ধরেছেন ডাক্তার সায়েব, শারীরিক দুর্বলতা আর আঙ্গুল কাঁপা টেনশনের সঙ্গে অফিসের একটা সম্পর্ক আছে অবশ্যই। ব্যাংকের কাজের চাপে প্রতিদিনই কমবেশি দুর্বল হয়ে পড়ি। তাছাড়া এর আগে এক ব্রাঞ্চে কাজ করার সময় ব্যাংকের দশ কোটি টাকার একটা লোন স্যাংশনে আমিও জড়িত ছিলাম। লোনটাও ঋণখেলাপির তালিকায় উঠেছে। এর দায়দায়িত্ব আমার উপরেও আসতে পারে। এ কারণেও খুব টেনশন হচ্ছে। চাকরিটা যাওয়ার ভয়ও হচ্ছে। অবশ্য ব্যাংকের শত শত কোটি টাকা ঋণখেলাপিরা যেভাবে লুট করছে, সেটা আসলে গোটা দেশ-জাতির টেনশনের ব্যাপার।’
কিন্তু ডাক্তার সরকারি ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের গল্প শুনতে কিংবা মাত্র দশ কোটি টাকার ঋণ খেলাপির কেস-এ আমার লাভ বা অপরাধ জানতে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় না। বরং বিরক্ত যেন, অফিসের প্রসঙ্গ চাপা দিতে জানতে চায়, ‘বংশে কারও এরকম কাঁপানি রোগ ছিল ? ব্রেইন কন্ট্রোল করতে পারে না―এমন অস্বাভাবিকতা ছিল কারও মধ্যে ?’
ডাক্তারের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে পরিবারের আর কারও এরকম আঙ্গুল বা কোনও অঙ্গ কাঁপা রোগ ছিল বলে মনে পড়ে না। জানতে চাই, ‘মানে আমার বংশে কোনও পাগল ছিল কি না জানতে চাইছেন ?’
ব্যস্ত ও বিরক্ত ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে মন্তব্য করে, ‘আপনার বংশের পাগলের খোঁজ জেনে কী করব ? আপনার আঙ্গুল ব্রেইন হুকুম দিলেও কাঁপানি বন্ধ করছে না কেন, এইটা বোঝা দরকার। কয়েকটা টেস্ট দিচ্ছি। রিপোর্ট দেখলে বুঝতে পারব। দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা দরকার হবে। আপাতত এ ওষুধগুলি দিচ্ছি, ভিটামিন ও টেনশন কমানোর অষুধও দিলাম, খাইতে থাকেন।’
প্রথমে ডাক্তার আমার অফিসের ভয়-টেনশনের খোঁজ নেওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু অনেকগুলো টেস্ট আর দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার কথা শুনে হতাশ হই। ফেরার পথে রিকশায় মারিয়াকে বলি, ‘একেই বলে হাতুড়ে ডাক্তার। আমার আঙ্গুলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভয় দেখাল! দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার নামে টাকা খাওয়ার মতলব। দুর্বলতা কাটাতে বেশি দুধ-ডিম খাওয়ার কথা না বলে এক গাদা ওষুধ দিয়ে দিল। এ ডাক্তারের কাছে আর আসব না।’
কিন্তু ডাক্তার আমার রোগের কারণ বংশে খোঁজায় খুশি হয়েছে মারিয়া। সমর্থন দিয়ে বলে, ‘আমার মনে হয়, ডাক্তার তোমার অসুখের কারণটা ঠিকই ধরেছে। তোমার বংশে বাপ-দাদাদের দুই তিনটা করে বিয়ে, কতগুলো ভাইবোন, কারও মধ্যে এ রোগ ছিল নিশ্চয়ই, খোঁজ নাও। বড়ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তাছাড়া ব্রেইন কন্ট্রোল অস্বাভাবিকতার কথা যে বলল, তোমার বাপ ও বড় ভাইযের জীবনটাও কি স্বাভাবিক বলা যাবে ?’
দাম্পত্য ঝগড়া বা পারিবারিক সমস্যায় স্বামীর ওপর নিজের দোষ চাপানো যথেষ্ট না হলে মারিয়া কথায় কথায় আমার বড় ভাই, মৃত বাবাসহ চৌদ্দ গোষ্ঠীকে টেনে আনে। আমি তার বড় ভাই ও চৌদ্দগোষ্ঠীকে গাল দেওয়ার প্রতিশোধ নেয় হয়তো-বা। এক হাতের আঙ্গুল এমন কি স্ত্রীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গটিও যদি নিজের কন্ট্রোলে না থাকে, তবু ওই ডাক্তারের কাছে আর যাব না। বরং মারিয়াকে সংসার চালানোর টাকা কম দিয়ে এখন থেকে অফিসেও চিকেন-মাটন আর পুষ্টিকর ফলমূল খেয়ে সুস্থ থাকার চেষ্টা করব।
৪.
প্রাথমিক পর্যায়ে আমার কম্পরোগের সঙ্গে অফিসের সম্পর্ক থাকার অনুমানটি অযৌক্তিক ছিল না আসলে। শুধু দশ কোটি টাকার ফাঁদে পড়ার লোভ-টেনশন নয়; আমার সুখ, স্বাস্থ্য এক কথায় গোটা অস্তিত্বই তো অফিস মানে চাকরিটার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। কিন্তু একঘেয়ে অফিসের গল্প করা দূরে থাক, ভাবতেও ভালো লাগে না আমার। কী করেন, কোথায় আছেন―কেউ জানতে চাইলে এক কথায় উত্তর দিই। কিন্তু ঘরে থেকেও মারিয়া আমার অফিস সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। ফিরতে দেরি হলে কিংবা মন খারাপ দেখলে অফিসের গল্প শুনতেও আগ্রহী হয়। কারণ স্বামীর বেতনের টাকায় তার সংসার ও নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভরশীল। তাছাড়া আপন বড় ভাই সরকারি ব্যংকের চাকুরে। বিয়ের আগেই ভাই-ভাবির সংসার দেখে ব্যাংকের চাকরির সুবিধা-অসুধিা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। উপরন্তু দশ কোটি টাকার ঋণখেলাপির কেসের সঙ্গে মারিয়া ও তার ব্যাংকার ভাইও পরোক্ষভাবে জড়িত। কাজেই আমার কম্পরোগের উৎস থেকে নিজেকে ও তার বড় ভাইকেও মুক্ত রাখতে আমার বংশের উপর দোষ চাপানো স্বাভাবিক।
পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারটি আমার পার্কিনসন সন্দেহ করেছিল কি না, জানা হয়নি আর। দ্বিতীয়বার যাইনি তার কাছে। তবে ঘরে স্ত্রীর চেয়েও নিজের জীবনের ভালো-মন্দ ঘটনা বেশি শেয়ার করেছি এবং এখনও করি অগ্রজ বাচ্চু এবং তার পরিবারের সঙ্গে। বিয়ের আগে ঢাকায় কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রজীবনে বছর পাঁচেক বাচ্চু ভাইয়ের বাসাতেই ছিলাম আমি। ব্যাংকের চাকরিটা হওয়ার পর আলাদা হয়েছি। বিয়েথা করে নিজে জেলায় বদলি হওয়ার বদলে ঢাকায় আছি অনেকটা ভাই-ভাবির কারণেও। নিজের যে কোনও সমস্যায় স্ত্রীর চেয়ে অগ্রজের মতামতকেই বেশি গুরুত্ব দিই আমি। মহল্লার ডাক্তার দেখানোর পর আঙ্গুল কাঁপার প্রকৃত কারণ ও প্রতিকার খুঁজতেও গিয়েছিলাম তার বাসায়।
বড় ভাই ও ভাবিরও পার্কিনসন সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। বিশ্বের গতিপ্রকৃতি ও দেশকালের অস্থিরতা সম্পর্কে ভাই অনেক জ্ঞান রাখে। কিন্তু সামান্য আঙ্গুল কাঁপার মানে বুঝতে পারে না। কম্পমান আঙ্গুলটায় চোখ রেখে ভাবুক দার্শনিকের মতো মন্তব্য করে, ‘ম্যালেরিয়া জ¦র হলে পুরো শরীর কাঁপে। আবার খুব ঠান্ডা লাগলে বা ভয় পেলেও মানুষ কাঁপে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু, ঠান্ডা ও ভয় আসে বাইরের পরিবেশ থেকে। এখন দেখতে হবে তোর এই আঙ্গুল কাঁপা অসুখ বাইরে থেকে কোনও আঘাত বা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, নাকি শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও ত্রুটির কারণে এটা ঘটছে। ডাক্তারের মত নেওয়া দরকার।’
‘ডাক্তার বলেছে টেনশন-ভয়ের কারণেও এটা হতে পারে। আবার বংশের মধ্যে এরকম কাঁপুনি রোগ বা ব্রেইন কন্ট্রোলের সমস্যা ছিল কি না জানতে চেয়েছে।’
‘জেনিটিকাল কারণ থাকতেও পারে। বাড়ির বয়স্ক লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাছাড়া ছোটবেলা তো তুই খুব ভীতুই ছিলি, মা তোকে ভয়পাদুরা বলত।’
‘মারিয়ারও ধারণা এ রোগটা বংশগত। আব্বা ও তুই ব্রেইন কন্ট্রোল করতে না পেরে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করেছিস। সে কারণে আমারও এই অস্বাভাবিক কম্প রোগ।’
‘তুই একজন নিউরোলজি বা মেডিসিনের বড় ডাক্তারকে দেখা।’
‘ছোট ডাক্তারই দীর্ঘ চিকিৎসার কথা বলে যত পরীক্ষা দিয়েছে, বড় ডাক্তার তো টাকা খসানোর ব্যাপারে বড় ডাকাত। এত টাকা পাব কোথায় ?’
টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ উঠলে ভাইয়ের বলার কিছু থাকে না। নিজে বলতে গেলে বেকার মানুষ। স্ত্রীর চাকরির আয়ে চলে সংসার। ভাবি পরাশর্ম দিয়েছিল, ‘ব্রেনের সমস্যা কি স্নায়ুবিক রোগ হোমিও চিকিৎসাতেও ভালো কাজ দেয় সাচ্চু। আমার এক অফিস কলিগ মাথাব্যথায় ভুগত। ব্রেইন টিউমারের হয়েছে বলে অপারেশনের কথা বলেছিল ডাক্তার। শেষে এক হোমিও ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ভালো হয়েছে। আমি তোমাকে সেই ডাক্তারের ঠিকানা এনে দেব।’
টাকা-পয়সার ব্যাপারে অসহায় বোধ করলেও জ্ঞানদানের ব্যাপারে অগ্রজ বড় উদার, ‘ছোটখাটো শারীরিক সমস্যায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে ? ভয় পেলে তোর কাঁপুনি আরও বাড়বে। মনে সাহস রাখ, ভালো খাওয়াদাওয়া কর, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। তবে তোর এই কাঁপুনি বংশগত কারণে বা অতীতের কোনও ভয় থেকে ঘটছে কি না, দেখতে হবে।’
দুরারোগ্য পার্কিনসন ধরা পড়ার আগে বাচ্চু যেমন বংশগত অবস্থা খতিয়ে দেখার কথা বলেছে, আর রোগ শনাক্তের এই ব্যাধি নিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ভুলে থাকতে আত্মজীবনী লিখতেও উৎসাহ দিয়েছে। বলা যায়, তার প্রেরণায় ও প্রভাবে লিখতে শুরু করেছি। যখন যা মনে পড়ে, লিখে রাখছি। তবে পার্কিনসনের উৎস খুঁজতে অফিস কি নিজের সংসারের সমস্যা-সংকটের গল্পে যাওয়ার আগে, আমাদের দুভাইয়ের সম্পর্কের উৎস এবং মিল-অমিলের ব্যাপার খোলাসা করা দরকার।
৫.
নিজের স্থায়ী ঠিকানা বলতে যেমন তৃণমূলের হালসাকিন গ্রাম অবধি যেতে হয়, তেমনি আত্মপরিচয় দিতে বাবা-মায়ের কথা অপরিহার্য় হয়ে দাঁড়ায়। নিজের জীবনের যত সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা, নিজের চরিত্রের ভাল-মন্দ তার উৎস বাবা-মায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর বালক বয়সে কার ছেলে আমরা―সেটাই ছিল গর্বের পরিচয়।
জন্মেছি আমরা দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার একটি গণ্ডগ্রাম―খোড়লে। পিতা আশরাফ হোসেন গাঁয়ের সবচেয়ে ধনী কৃষক। জমিদারি আমল ও পূর্বপুরুষদের জোতদারি চলে যাওয়ার পরও তাদের মতো নিজেকে গ্রামসমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রায় দেড় শ বিঘা জমির মালিকানা ও কৃষি ছিল জীবিকার মূল উৎস। কিন্তু গাঁয়ের চাষি-মজুরদের মতো তুচ্ছ মানুষ যে সে নয়, সেটা কথায়-বার্তায় চলনে-বলনে বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল যেন তার কাজ। জমিদারসুলভ অহঙ্কার ও আত্মসম্মান ছিল। লোকেরাও অবশ্য মান্যগণ্য করত। বিএ এমএ পাস মানুষের চেয়েও আব্বা জ্ঞানী মানুষ। উকিলের চেয়েও জমির কাগজপত্র ও আইন বোঝে বেশি। আর মুন্সি-মওলানার চেয়েও তার ধর্মজ্ঞান কম নয়। লোকমুখে শুনে শৈশবে পিতা সম্পর্কে আমাদের এরকম ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। ভয় পেতো বলে গাঁয়ের লোক তাকে আড়ালে বনের বাঘ-সিংহ কিংবা হাতির সঙ্গে তুলনা করত। একজন কে শুধু পিতাবিষয়ক আলোচনায় তাকে কেউটে সাপ বলেছিল। আমি কী কারণে যেন উপস্থিত ছিলাম সেখানে। কথাটা যে আব্বাকে বলা হয়নি, সত্যি কেউটে সাপের গল্প ফেঁদে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর আমার হাত ধরে বুঝিয়েছিল সাবেদ চাচা, কথটা যেন বাপের কানে না তুলি।
বলব কী, শৈশব-কৈশোরে ভয়ে আব্বার কাছে ঘেষতাম না আমরা। বাড়িতে মা-ও খুব ভয় পেত আব্বাকে। মাও তো আব্বার চেয়ে কম জ্ঞানী নয়। কাশিয়াবাড়ি গাঁয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত মাস্টারের মেয়ে সে। মাইনর স্কুলে পড়ে ছেলেদের চেয়েও ভালো রেজাল্ট করেছে। বিয়ের পর বাড়িতেও বাংলা বই-পুথি কোরান-হাদিস পড়ত। আর মাত্র দ টো সুরা মুখস্থ হলে মাও কোরানের হাফেজ হবে। কিন্তু এসব কারণে মাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করত না আব্বা। হুকুম পালনে বিলম্ব কিংবা দোষত্রুটি দেখলে শুধু বাঘের গর্জন নয়, পায়ের খড়ম-জুতা দিয়েও মারতে আসত। আব্বার খুব রাগ হলে ভয়ে মাকে কতবার পালিয়ে থাকতে দেখেছি। আর আমরা তো ছোট মানুষ। সর্বদা তার কাছ থেকে শত হাত দূরেই থাকতাম।
দুই স্ত্রী ও এক ডজন সন্তানের জনক লোকটা। ছেলেমেয়েদের কাউকেই বুকে তুলে আদর করার মতো সময় তার ছিল না। ইচ্ছেও হত না বোধহয়। মা সাক্ষী। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রথম সন্তান বাচ্চু। ছোটবেলায় তাকে বুকে নিয়ে আব্বা নাকি একদিন আগাডুম বাগাডুম গান শুনিয়েছিল। ঘুমের ভান করে বাচ্চু তাই শুনেছে এবং আজও পষ্ট মনেও রেখেছে। বড় হওয়ার পর সব ছোট ভাইবোনদের এই গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মায়ের ঠিক মনে নেই। কিন্তু বড় ছেলে বাচ্চু যে অসাধারণ মেধাবী, একবার কিছু পড়লে, দেখলে বা শুনলে সারা জীবন স্মরণ রাখতে পারে; তাতে মায়েরও সন্দেহ ছিল না। গ্রামবাসীও সবাই বলত, বাপের চেয়েও দারুণ চোখা ব্রেইন বাচ্চুর। ফলে আমি বিশ্বাস করতাম অগ্রজের সব কথা। আমার ছোটবেলার যত স্মৃতি, অধিকাংশই উজ্জ্বল হয়ে আছে বাচ্চুকে ঘিরে।
আমার পরও মা আরও সাত ভাই-বোনের জন্ম দিয়েছে। দুটোর অকাল মৃত্যুর পরও জীবিত আছি চার বোন ও দু ভাই। এ ছাড়াও সৎ মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া এক ভাই ও তিন বোন। সব মিলিয়ে বর্তমানে দশ ভাই-বোনের পরিবার। আব্বা-মায়ের মৃত্যুর পরও কনিষ্ঠ সহোদর বাবলু সপরিবার এবং অন্যদিকে সৎমা বড়বাড়ির বিষয়সম্পত্তির জিম্মাদার এখন। নিজস্ব পরিবার নিয়ে আমরা যারা বাইরে থাকি, তাদের সবাই নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে আব্বার রেখে যাওয়া বাড়িকে একান্নবর্তী পরিবারই ভাবি এখনও। এই বড় পরিবারের জীবিত দশ ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে পঞ্চাশ না পেরোতেই পার্কিনসনের শিকার হব, অতপর কাঁপতে কাঁপতে সবার আগে প্রথম মৃত্যুপথের পথিক হব, এটা একমাত্র আল্লা ছাড়া কারও কল্পনাতেই ছিল না সম্ভবত। কিন্তু ডাক্তার এ রোগ সারবে না বলার পর থেকেই মনে মনে আমি জেনে গেছি, শুধু স্ত্রী মারিয়ার আগে নয়, অন্য ভাইবোনদের আগে আমারই মরণ হবে। আসলে মরার ভয়টা ছিল খুব ছোটবেলাতেও। মা বলত, ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম বড্ড ভীতু। ছোটবেলায় কান্নাকাটি করে তাকে খুব জ¦ালাতাম।
ছোটবেলায় ভয় পাওয়ার স্মৃতি আমারও বেশুমার। ভূতের ভয় ছাড়াও আরও যে কত রকম ভয় ছিল। মা আমার কান্নাকাটি থামাতে নানারকম ভয় দেখাত। যেহেতু ভূত ছাড়াও ভয়ের উৎসগুলি সম্পর্কে মায়ের বিশ্বাস ছিল ষোলো আনা। আমিও তার সব ভয়ের গল্পই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু হাই স্কুলে পড়ার সময়ে বাচ্চু মাকে শাসনের গলায় বলেছিল, ‘ভূত বলে কিছু নাই। মিছেমিছি ভূতের গল্প কহি বাচ্চাদের ভয় দেখানো খারাপ।’
পুরো নাম বেলায়েত হোসেন বাচ্চু। দুই নম্বরে আমি―শাফায়েত হোসেন সাচ্চু। একই মায়ের উদর থেকে, চার বছর তিন মাস দশ দিন ব্যবধানে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে গাঁয়ের অভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেছি আমরা। আমাদের দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে আরও একটি ভাই ছিল, মাত্র নয় দিন পরই তার মৃত্যু হয়। সেই মৃত ভাইটি একমাত্র মা ও বাচ্চু ছাড়া আমাদের কারও স্মৃতিতে নেই। মা তখনও আঁতুড় তথা ছুয়াঘরে, একমাত্র ধাই ছাড়া সেই নাপাক ঘরে বাড়ির পুরুষরা কেউ যেত না। কিন্তু ছোট বাচ্চুই বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে যখন-তখন সেই ঘরে ঢুকে মা এবং ছোট ভাইটিকেও দেখত। তার মৃত্যুতে মায়ের সঙ্গে সে কান্নাটা কেঁদেছিল, জীবনে প্রথম সেই মৃত্যুশোকের কান্নার স্মৃতি না কি তার এখনও মনে আছে। মায়ের উর্বরাশক্তি ও বড় বাচ্চুর প্রখর স্মৃতিশক্তি খাটো করা হয় ভেবে তার কথাও উল্লেখ করলাম। প্রথম ভ্রাতৃহারানোর শোকের কারণেই হয়তো আমাকে পেয়ে বাচ্চু খুব খুশি হয়েছিল। মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিল, ‘সেই মরা ময়নাকে আল্লাহ কি আবার দুনিয়ায় পাঠায় দিছে মা ?’ মা হেসেছিল। আর জন্মের পর থেকে মায়ের পর বাচ্চু আমার ঘনিষ্ঠ অগ্রজ নয় শুধু, হয়ে উঠেছিল অভিভাবক, শিক্ষক, খেলার সঙ্গী, বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুও।
শৈশব-কৈশোরেও মিলের চেয়ে দুই ভাইয়ের অমিলটাই ছিল বেশি। চেহারা ও স্বভাবেও। বাচ্চু দেখতে অনেকটা মায়ের মতো, কিন্তু স্বভাব পেয়েছে বাপের। আমি ঠিক বিপরীত। বাচ্চু ছিল বেপরোয়া ও দুষ্টু প্রকৃতির, আর সাচ্চু সবার কাছে শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে। স্কুলের লেখাপড়ায় বাচ্চু ছিল অসাধারণ মেধাবী। আমি মোটামুটি মাঝারি মানের। আজ পরিণত বয়সে এসেও আমাদের দু ভাইয়ের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট। আমি সোনালি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। বাচ্চুর যেহেতু মাস গেলে ধারাবাঁধা কাজ বা বেতন নেই, তাই বলতে গেলে বেকার। তবে সামাজিক পরিচয়ে এবং আমার কাছে সে অনেক কিছু। বিপ্লবী রাজনীতিক, আজীবনের মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীও। অবশ্য তার এসব পরিচয়ের প্রভাব সমাজে তেমন নেই। আমার উপরে কছুটা আছে হয়তো, তবে তা মিলের চেয়ে বিরোধের সম্পর্কটাই পষ্ট করে। যেমন বাচ্চু নাস্তিক। আমি ষোলো আনা আস্তিক। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী মারিয়া আমার চাকরি ও আয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অন্যদিকে বাচ্চু চাকরিজীবী স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। বাচ্চুর কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বালক বয়সেও অনেকের চোখে ধরা পড়েছিল। দুটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে।
একবার গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ এক খেলার সঙ্গীর সঙ্গে মারামারির সময় বাচ্চু তাকে এমনভাবে কামড়ে দিয়েছেল, সেই ছেলে বাচ্চুকে নাম দিয়েছিল বিচ্চু। এরপর খেলার সঙ্গীরা অনেকে তাকে বিচ্চু ডাকত। পিতার প্রভাব ও ক্রমে নিজের অন্যান্য গুণের খ্যাতি দিয়ে নামের বিকৃতি সে ঠেকাতে পেরেছিল। কিন্তু বাড়িতে আমি রেগে গেলে ভাইয়ের বদলে তাকে বিচ্চুই ডাকতাম। জবাবে, আমাকে রাগানোর জন্য সে ইচ্ছে করেই মুখ ভেংচি দিয়ে আমাকে বলত―হিচ্চু। একদিন ঝগড়ার সময় তার মুখ ভেংচানো হিচ্চু ডাক আমার গোটা শরীর-মনে এমন জ¦ালা সৃষ্টি করেছিল যে, প্রতিবাদী কান্না ও বিচ্চু গালটা যথেষ্ট না হওয়ায় তাকে হারামজাদা শুয়ারের বাচ্চা বলে গাল দিয়েছিলাম। বাচ্চু সরাসরি আব্বার কাছে গিয়ে বিচার দিয়েছিল, ‘আব্বা সাচ্চু আপনাকে হারামি শুয়ার বলেছে।’
আমি ভয়ে প্রতিবাদ করে সত্যি বলেছি। আল্লার কিরা, আব্বাকে নয়, আমি বাচ্চুকে বিচ্চু আর শুয়ারের বাচ্চা বলেছি। নয় বছরের বাচ্চুই তখন আব্বাকে যুক্তি দিয়েছে, ‘আমি শুয়ারের বাচ্চা হলে আব্বাও তো শুয়ার, ঠিক না আব্বা ?
বড় ছেলের যুক্তিবোধ দেখে আব্বা কতটা খুশি হয়েছিল ঠিক জানি না। তবে ধমক দিয়েছিল আমাকে, যেন এরকম গাল আর না দিই। এরপর থেকে ছোট করে বা মনে মনে বললেও সরবে দিই নাই আর। আব্বাকে এমন ভয় পেতাম বলেই বাচ্চুই হয়ে উঠেছিল সার্বক্ষণিক অভিভাবক। খেলাধুলার আনন্দে বিরোধ ঘটলেও, শিক্ষক হিসেবে সে ছিল নির্ভরযোগ্য। আমার সকল অজ্ঞতা ও কৌতূহল নিরসনে বাচ্চু ছিল বড় ভরসা।
একবার বাড়ির চাকর শরফ ভাইয়ের বেসামাল লুঙ্গির আড়াল থেকে প্রকাশিত তার পুরুষাঙ্গ ঘিরে কালো কেশদাম আবিষ্কারের উত্তেজনা নিয়ে বাচ্চুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ‘ও ভাই, শরফের চ্যাটের গোড়তে দাড়ি!’
ভাই হেসে বিজ্ঞের মতো আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, ‘আরে বোকা, দাড়ি না। ওগুলাকে বলে―। খারাপ কথা। কাউকে আর বলিস না।’
ভাইয়ের কথা রেখেছি। জীবনে দ্বিতীয় কাউকে আর বলিনি। এমনকি নিজেরটা ঘরের স্ত্রী মারিয়া ব্যতীত জীবনে কাউকে আর দেখতেও দিইনি বিবাহপূর্ব জীবনে।
চার বছর বয়সে আমাকে বাচ্চুই প্রথম স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করায়। সে তখন ক্লাস থ্রির নয় শুধু, গোটা স্কুলেরই যেন ফার্স্ট বয়। ক্লাস ফাইভের ছেলেরাও তার সঙ্গে লেখাপড়ায় পারত না। কাজেই আমার বড় ভাই যে সবার চেয়ে বড় এবং বড় হয়ে যে আব্বার চেয়েও বড় হবে, সেটা ছোটবেলায় আমি টের পেতাম।
আমাকে দেখে হেড মাস্টার ভর্তি করতে দ্বিধা করলে আব্বার প্রভাব খাটিয়ে বলেছিল সে, ‘আব্বা বলেছে বয়স দুই/এক বছর বেশি দেখিয়ে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করায় নিতে। আমি ওকে বাড়িতে পড়াব।’ হেড মাস্টার আমার আসল জন্মতারিখকে গুরুত্ব না দিয়ে, কত বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করলে চাকরি পেতে সুবিধা হবে, সেই হিসাব কষে জন্মতারিখ লিখেছিল। সেদিনই বড় ভাইয়ের দৌলতে আসল বয়সের চেয়ে প্রায় দু বছরের বড় হয়ে গিয়েছিলাম আমি।
ক্লাস ওয়ানে যেসব ছেলেদের সঙ্গে বসতাম, পরিচিত দু চারজন বড় ভাইয়ের মতো আদর করত। কিন্তু কয়েকটা বাঁদরমার্কা ছেলে ছোট বলেই আমাকে কারণে-অকারণে খেপিয়ে মজা পেত। আমি যে বাচ্চুর ছোট ভাই, গাঁয়ের বড় দেওয়ানি, জোতদারবাড়ির লোকের ছেলে, তারপরও মোটেও পাত্তা দিত না দুষ্টু ছেলেগুলি। অকারণে পিঠে খোঁচা, কান টানা কি বাঁদরের মতো মুখ ভেংচানো দেখে পিত্তি জ¦লে যেত আমার। ক্লাসে যখন টিচার থাকত না, তখন তো প্রায় সবাই পাল্লা দিয়ে হইচই করত। ক্লাসে টিচার ব্লাকবোর্ডে অ আ লেখানোর সময়ে আমার পিঠে ব্লাকবোর্ড বানিয়ে লিখেছিল একজন। পাশেরটি আমাকে অকারণেও ঠেলা মেরেছিল। আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে ছুটে যেতাম ক্লাস থ্রিতে বসা ভাইকে বিচার দিতে। ক্লাস থ্রির টিচার ও ভাই ক্লাস ওয়ানে এসে টিচার ও দুষ্টু ছেলেদের বিচার করে বেঞ্চের উপর দাঁড়ি করিয়ে রেখেছিল।
এভাবে বড় ভাইয়ের প্রভাবে স্কুলে এবং স্কুল যাওয়া-আসার পথে বয়সে বড়রাও আমার বড় ভাই ও বন্ধু হয়ে উঠেছিল। গাঁয়ের স্কুলপড়ুয়া কয়েকজন দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম আমরা। পায়ে হেঁটে মাইলখানেক পথটাও অনেক সময় খেলার মাঠ হয়ে উঠত। রাস্তার দু পাশের শটিবন কি হেলেঞ্চা গাছে বসে থাকা ফড়িং, সোনালি গাছের সোনাফুল, জিগা গাছের শুয়ো পোকার ঝাঁক কিংবা রাস্তাসংলগ্ন খাল-বিলের মাছ কি ব্যাঙ দেখা আর অদ্ভুত সব গল্প শোনা। গল্প বলার ক্ষেত্রে অগ্রজ বাচ্চুই ছিল সেরা। নানারকম ভাষায় কথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত সে। তার ভাষা আবিষ্কারের কৌশল আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছিল। তার শেখানো ভাষায় দু ভাই কথা বলতাম যখন, সবাই অবাক হয়ে শুনত। যেমন, আটামি গেটারামে আটার থাটাকব নাটা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে বাড়তি একটা ট বর্ণ বসিয়ে দ্রুত উচ্চারণ করলে ভিনদেশি ভাষার মতো শোনাত। অনেকেই শিখেছিল কৌশলটা। কিন্তু শব্দকে উল্টো করে লিখে যা হয়, তা যখন দ্রুত বলত সে, বুঝতে সময় লাগত। ইতু টাকএ লগছা। রতো থেসা মিআ এ তেড়িবা রআ বকথা না।
বুঝতে না পারায় কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছিল সে। উচ্চারণগুলো বানান করে খাতায় লিখে উল্টো করে মানে বুঝে নিতাম। কিন্তু বাচ্চু যত দ্রুত উল্টো বানানে বলতে পারত, আমি পারতাম না। এরকম মেধাবী ছিল বলেই আব্বা তাকে মানুষ করার জন্য শহরের ভালো হাইস্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিল। শহরে মায়ের এক মামা চাকরি করে, ডিসি অফিসের হেড ক্লার্ক। শহরে নিজের বাড়িও করেছে। সেই বাড়ি তথা আমাদের ক্লার্ক নানার বাড়িতে থেকে হাইস্কুলের লেখাপড়া শুরু করেছিল বাচ্চু। আর তখন থেকেই পরিবারের সঙ্গে একটা অলঙ্ঘ্যনীয় দূরত্ব তৈরি হতে শুরু হয়েছিল তার।
৬.
বাচ্চু শহরে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে আমি তার স্থান দখল করলাম। বাড়ির বড় ছেলেকে শহরে রেখে এসে আমাকে যেন আব্বা প্রমোশন দিল। মাকে সে কখনও নাম ধরে ডাকত না। পাড়াপড়শিদের মতো বাচ্চুর মা বলে ডাকত। যেন মা হওয়া ছাড়া মায়ের আর কোনও পরিচয় নেই। একমাত্র নানাজি বাড়িতে এলে তার ডাক শুনে আমরা মায়ের আসল নাম জানতে পারতাম।
আমার পরও মা আরও পাঁচ ভাইবোনকে এনেছে পরিবারে। বড় বাচ্চু যখন শহরে পড়তে যায়, আমার ছোট দুটি বোনের পরও মায়ের গর্ভে ছিল ছোট ভাইটি। মায়ের গর্ভে কনিষ্ঠতমের অস্তিত্ব টের পেয়ে আমরা খুশি হওয়ার বদলে যেন লজ্জাই পেতাম বেশি। গাঁয়ের লোক ভিতরের খবর জানতে যখন ঠাট্টা করে কেউ জানতে চাইত, ‘কী বাহে, তোমার মায়ের কি ফের পেট হইছে ?’ লজ্জা পেয়ে গালি দিতাম, ‘তোর মায়ের পেট হইছে।’ আমার মতো বাচ্চুও বোধহয় লজ্জা পেত। আরও দুটি জন্মাবার আগে, আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করার পর যখন নতুন মাও গর্ভবতী, মাকে একদিন সতর্ক করে বলেছিল, আমরা পাঁচ ভাইবোন মানুষ হতে পারলে মায়ের আর কোনও কষ্ট থাকবে না। আমাদের আর ভাইবোনের দরকার নেই।
রাতে বড় ঘরের জোড়া খাটের ঢালাও বিছানায় মায়ের সঙ্গে শুতাম সব ভাইবোন। বাচ্চু শহরে যাওয়ার পর তার জায়গায় আমি, আমার পরে ছোট ভাই সিরিয়ালে যে চতুর্থ, তৃতীয় স্থানের বোনটি শুতো তার পাশে সবচেয়ে ছোটবোনটির মাঝখানে। মা থাকত কিনারে কোলেরটিকে নিয়ে। রাতে শুয়ে মা আমাদের গল্প শোনাত। কিন্তু অনেক সময় অবুঝ ছোটটির কান্নায় গল্প শোনা ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত। তখন আমরা বড় ভাইবোনেরা ছোটটিকে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে ভয় দেখিয়ে নানাভাবে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতাম। বড় বাচ্চু বাড়িতে থাকতে মাঝে মাঝে তার কাছেও গল্প শুনতে চাইতাম। মায়ের কাছে শোনা কি বইয়ে পড়া গল্পগুলো শোনাত সে। কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত। আবার আমাদের কার কয়টা সুরা মুখস্থ ছিল, সেই প্রতিযোগিতাও হতো। রাতে বিছানায় শুয়ে এরকম আড্ডা-বিনোদন ছিল যেন আমাদের দিনটির শেষ খেলা। খেলতে খেলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম আমরা।
এক রাতে ছোটরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও আমি যখন মায়ের সঙ্গে শহরের গল্প করছি, বাইরে আব্বার কণ্ঠ, ‘এই সাচ্চুর মা, এ ঘরে আয় জলদি, কাম আছে।’
আমাদের নয়া মা তখন খালাস হওয়ার জন্য বাপের বাড়িতে গেছে। সংসারে কাজ ও দায়িত্বও বেড়েছে মায়ের। কিন্তু রাতে আর কাজ না করতেই যেন আব্বার ডাক শুনেও মা ঘুমিয়ে যায়। কোনও সাড়া দেয় না। আমিও চুপ। তখন বাইরে আব্বা আমার নাম ধরেই হুঙ্কার দেয়, ‘এই সাচ্চু, সাচ্চু, তোর মা নিঁদ গেইছে ? ডাকায় দে, আমার ঘরে আসতে বল, দরকারি কাজ আছে।’
মা তো জেগেই ছিল, তবু আব্বার আদেশ পালনে আমি তাকে জরুরি ডাকতে থাকি। মা আমরা যে কজন জেগেছিলাম, তাদের ঘুমানোর নির্দেশ দিয়ে আব্বার ঘরে চলে যায়। আব্বা ঘরে একা থাকলেও তার ঘরের আলমারি সিন্দুকে টাকাপয়সা ও জমির কাগজসহ মূল্যবান অনেক কিছু। এত রাতে মাকে কী দরকার ? মা আব্বার ঘরে গিয়ে কী করছে―এই ভাবনা নিয়ে আমি যখন একা জেগে আছি, সেই সময়ে সব চেয়ে ছোটবোনটি মায়ের বুকের দুধ খেয়ে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং মাকে না পেয়ে তারস্বরে কাঁদতে থাকে।
আমার ছোট ভাই চেঁচিয়ে মাকে ডাকে, ‘ও মা, ময়নাকে দুধ দাও’; ৩নং বোনটি মাকে ডাকার জন্য শাসন করে, ‘ডাকিস না, মা আব্বার ঘরে জরুরি কামে গেইছে।’ অতঃপর অবুঝ শিশুর কান্না থামানোর চেষ্টা করে সে-ই যেন মায়ের ভূমিকা নিতে চায়। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে সে যেন মরেই যাবে―কনিষ্ঠতমের এমন কান্না ঘুমন্তটিরও ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। ঘরের অন্ধকার দেখে ভয় পাচ্ছে ভেবে, আমি হারিকেনের আলো উস্কে দেই। কাঁদতে কাঁদতে ছোট ময়নার কান্নার শক্তি যখন শেষ, মা ঘরে ফিরে আসে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে ময়নাকে বুকে নিয়ে তার কান্না থামায়।
অতঃপর ঘর নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই রাতে আমাকে প্রথম দৈত্য আক্রমণ করে। টিনের বেড়ায় যে ফুটোটা ছিল, সে ফুটো দিয়ে সকালের আলো ঘরে ঢুকতে দেখে ঘুম ভাঙত আমার। রাতের অন্ধকারে দৈত্য-দানো ভূত-পেত্নী দেখার ভয়ে আমরা চোখ বুজে আল্লার কলেমা-কালাম পড়তাম। আজ সুরা পড়তে ভুলে গেছি বলেই হয়তো, কিংবা একা জেগে থাকায় ভয়ঙ্কর এক পিশাচ আমার বুকে চেপে বসে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার গোটা শরীর কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে মাকে ডাকতে চাই, কিন্তু গলা দিয়ে কথা বেরয় না। গোঙানোর শব্দ শুনে মা হারিকেন উস্কে দিয়ে ছুটে আসে আমার কাছে। আমি তখনও থর থর করে কাঁপছি।
মা জানতে চায়, ‘কী হইছে বাবা ? খারাপ স্বপ্ন দেখছিলি ?’
অনেক কষ্টে আমার গলায় স্বর ফোটে, ‘ও মা, একটা দৈত্য আমার বুকের উপর বসেছিল। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। তাকে খামচা দিয়া আমার আঙ্গুলটাই মনে হয় ভাঙ্গি গেছে। তোমাকে চিল্লায় ডাকতাম। কিন্তু ওটা গলাও টিপে ধরছিল।’
মা দোয়া পড়ে আমার বুকে ফুঁ দিয়েছে। বলেছে, ‘বুঝেছি, বোবা দত্যি ধরেছিল তোকে। ঘুমা এখন, আর ধরতে পারবে না।’
সে রাতের পর অন্ধকার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে বোবা ভূতের খপ্পরে পড়ার ভয়, এবং আক্রান্ত হয়ে তার সঙ্গে কুস্তি লড়ে দেহ-মনে যে কাঁপুনি সৃষ্টি হতো, তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের পার্কিনসন রোগের সম্পর্ক আছে কি না জানি না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মত জেনে বাচ্চুও বলেছে, আমার ব্রেনের সেলগুলো যে মরে যাচ্ছে, সেই আঘাতের উৎস হয়তো ছোটবেলায় ঘটেছিল। বাচ্চু নিজেও শৈশবে আব্বার মাতবরি চরিত্র দেখে, বিশেষ করে তার দ্বিতীয় বিয়ের ঘটনায় আঘাত পেয়ে বাড়িছাড়া হয়েছে এবং আজকের নাস্তিক ও বিপ্লবী চরিত্র পেয়েছে। কিন্তু আমি তার মতো সাহস দেখাতে পারিনি বলে আব্বার ভয়ে কাঁপতাম। আব্বার মৃত্যুর পরও আব্বার সমাজ-শাসনের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি আজও।
৭.
বোবাভূতে ধরা ভয়ের চেয়েও আরও যে ভয়ঙ্কর এক ঘটনা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে, বাচ্চুর ধারণা, তার সঙ্গেও আমার কম্পরোগের সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। ঘটনাটি একসময় গোটা গ্রামেও তোলপাড় সাড়া জাগিয়েছিল। বাচ্চু শহরের স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর মাসহ আমাদেরও একবার বাড়ি ছাড়া করেছিল আব্বা। কারণ মা তার মুখের উপর প্রতিবাদ করেছিল সেদিন।
রেগে গেলে আব্বা মাকে কোনও সন্তানের মা হিসেবেও সম্বোধন করত না। সত্যটা মনেও থাকত না বোধহয়। সেদিনও আব্বা মায়ের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করেছিল, ‘এত বড় আস্পর্দা তোর! আমার মুখের উপর কথা কহিস! হারামজাদি ছোটলোকের বাচ্চা! অচল খোঁড়া পণ্ডিতের বেটি তুই, মাথায় নাই এক ফোঁটা ঘিলু, সংসার সামলাইতে না পারলে বাইর হইয়া যা বাড়ি হইতে।’
আব্বা রেগে গেলে মা সাধারণত পালিয়ে চুপচাপ থাকত। কিন্তু আমরা সেদিনই প্রথম দেখলাম আব্বার মুখোমুখি হয়ে তীক্ষè গলায় ঝগড়া করতে। ‘খবরদার, আমাকে বাপ তুলে গালি দেবেন না। আমার বাপ তোমার চেয়েও শিক্ষিত। খোঁড়া পণ্ডিতকে চেনে মুল্লুকের মানুষ। গরিব হইলেও মানুষ হিসাবে তোমার চাইতে হাজার গুণ ভালো সে।’
নানা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত বলে আমরাও তাকে খোঁড়া মাস্টার হিসেবেই জানতাম। আবার এও জানতাম, অন্যরা ছোটলোক না হলে তো বাবা বড়লোক হয় না। মায়ের দুঃসাহসী প্রতিবাদ দেখে আব্বা ছুটে এসে মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে, মুখের সঙ্গে হাত-পাও চলে, ‘খোঁড়ার বাচ্চা খুঁড়ি মাগি। তোকে আর রাখব না এ বাড়িতে। বের হয়ে যা, নিকলাও হিঁয়া সে। এই দণ্ডে দূর হ আমার বাড়ি হইতে।’
মাকে ধাক্কা দিয়ে উঠানে যেন বলের মতো সে লাথি দেয়। তারপর আমাদের ঘরে ঢুকে একে একে ঘর থেকে মায়ের বিছানা-বালিশ, মায়ের পড়ার বইগুলি (কোরান শরিফ বাদে) উঠানে ছুড়ে দিতে থাকে। আমরা আগেই ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে কান্না জুড়েছি অনেকে। আব্বা তখন মায়ের সব জিনিসপত্র উঠানে ছুড়ে দিয়ে ঘর তালা মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।
মা আব্বার লাথি খেয়ে আঙ্গিনায় উল্টে পড়ে ব্যথা পেয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কান্নার বদলে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, অদ্ভুত চোখে তাকায়। তারপর কাঁদতে থাকে। আমরা যারা বাড়িতে ছিলাম, তারাও সবাই মাকে ঘিরে কাঁদতে থাকি। কান্নার প্রতিযোগিতায় সব সময় ছোটরাই ফার্স্ট হয়। ভাইবোনদের মধ্যে এখন আমি বড়। অগ্রজ বাচ্চু শহরে পড়তে যাওয়ার সময় আমাকে সে ভারপ্রাপ্ত বড় করে গেছে। সে বাড়িতে থাকলে এখন কী করত জানি না। কিন্তু আমি ভয়ে দিশেহারা, ছোটদের মতো কাঁদতেও পারছিলাম না। নীরব প্রতিবাদ, কান্না, উত্তেজনা সব কিছু চেপে রাখায় থর থর করে কাঁপছিলাম। হাত-পাও কাঁপছিল কি না, ঠিক বলতে পারব না। কারণ আব্বা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনা দেখতে, মায়ের কান্নার সমব্যথী হতে পাড়াপড়শি মহিলাদের ছুটে আসা দেখছিলাম। তারাও শুধু মাকে ঘিরে মাকেই দেখছিল। যাকে দেখলে তারা মাথায় বড় ঘোমটা দিয়ে দূরে সরে গিয়েও ভয় পায়, এমন বাঘের সঙ্গে সংসার করা কী যে কষ্টের! আহা রে লাথিগুড়ি দিয়া কোমরখানা ভাঙ্গি দিছে মন কয়! মাকে এরকম সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অনেকে কেঁদেও ফেলছিল।
মা আমাকে খোঁজে, ‘আমার সাচ্চু কই ?’ ডাক শুনে আমি মায়ের পাশে ছুটে যেতেই মা আমাকে আদেশ করে, ‘যা তো বাবা। জহরের গরুগাড়ি ভাড়া করিয়া আন, এখনই তোর নানার বাড়ি চলি যাব আমরা।’
আমি যেন এতক্ষণে একটা দিশা পাই। ছুটে যাই জহরের বাড়িতে। জহর, তার গরু ও গাড়ি বাড়িতেই ছিল। কিন্তু শুধু আমার কিংবা মায়ের ডাকে সে জরুরি সাড়া দিতে তৎপর হয় না। আব্বার কথাও বলতে হয়, ‘হয় চাচা, আব্বাও মাকে এখনই নানাবাড়ি চলে যাইতে কহিছে।’
আধাঘণ্টা পর, বলতে গেলে এক কাপড়ে আমরা সব ভাইবোন গরুগাড়িতে মাকে নিয়ে নানাবাড়িতে যাই। নানাবাড়িতে এ ধরনের যাওয়ার দুর্ভাগ্য আগে ঘটেনি। পাড়াপড়শিরা কান্নার চোখে আমাদের শেষ বিদায় দেয় যেন।
৮.
নানাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই আব্বার নতুন বিয়ের খবর পেয়েছিলাম আমরা। বিয়ে মানেই তো উৎসব-আনন্দ, সুঘ্রাণ ছড়ানো মাংস-পোলাও-বিরিয়ানি ও মিষ্টি পান-সুপারি খাওয়াদাওয়া। আব্বা ও মায়ের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বিয়ে খেতে খুশির অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। কিন্তু সেই বিয়ে জিনিসটা যে এত খারাপ, এত লজ্জার ও বেদনাময় এক ঘটনা হতে পারে, সেটা আব্বার দ্বিতীয় বিয়ের খবরটা শুনে আমরা প্রথম টের পাই। মাকে লাথি মেরে এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকেও বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মূলে যে এই দ্বিতীয় বিয়ে, সেদিনই প্রথম আমরা পষ্ট বুঝেছিলাম। এরকম ঘটনা ঘটবে―মা অবশ্য আগেই জানত। কিন্তু আমাদের বলেনি কখনও।
মায়ের চেয়েও কমবয়সী সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়েকে আব্বা বিয়ে করে বাড়িতে তুলেছে। কনের বাবার বংশবুনিয়াদ ভালো। তবে নদীভাঙ্গা গরিব মানুষ। কনের নামে দুই বিঘে জমি ছাড়াও নগদে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছে। মায়ের কান্নার সঙ্গে আমাদের কপালভাঙ্গার নানা খবর ও গল্পগুজব আমরা নানাবাড়িতে বসেই জানতে থাকলাম। গাঁয়ের চেনা লোকজনই নানাবাড়ির গ্রামে এসে এসব খবর শোনায়। সৎমা মানে ডাইনির চেয়েও খারাপ একটা মেয়েলোক। সৎমা মানে বাড়িতে অশান্তির সবচেয়ে বড় কারণ। এ বিষয়ে মায়ের কাছে সুয়ো রানি দুয়ো রানির কেচ্ছা শুনে আমরা আগেই ধারণা পেয়েছিলাম। পড়শি একাধিক গেরস্থবাড়িতেও দেখেছি দুই সতীনের সংসার। জহর গাড়িয়ালেরও দুই বউ। সেই বাড়ির ঝগড়া পাড়াপড়শিরা প্রায় রোজই শুনতে পেত। আমাদের কানেও আসত। বাড়িতে অশান্তি দেখে জহর গাড়িয়াল তার গরুগাড়ি নিয়ে দূরদূরান্তরে ভাড়া খাটতে যেত। আর মনের দুঃখে গান গাইত―ওকি গাড়িয়াল ভাই, হাকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরে… কিংবা নিদেরও আলিশে/ হাত পড়ে বালিশে/ চেতন হয়া দেখো মুই বঁধুয়া নাই মোর পাশে…। জহর গাড়িয়ালের বাড়িতে দুই সতীনের ঝগড়া এবং গাড়িতে একা জহরের গান নিজ কানেও শুনেছি আমরা।
মায়ের ছোট ভাই ফুলু মামা শহরে গিয়ে তার মামার বাড়িতে এবং বাচ্চুর কাছেও জানিয়েছে খারাপ খবরটা। বাচ্চু খবর শুনেই নাকি ঘরের দরজা লাগিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। বাচ্চু একটা চিঠিও লিখেছে মাকে এবং আমাকেও। মায়ের চিঠিতে কী লিখেছে জানি না। সেই চিঠি পড়েও মায়ের কান্না বেড়েছে। অন্যদিকে আমার চিঠিতে যা লিখেছিল, এতবার পড়েছিলাম যে মুখস্থ আছে এখনও।
স্নেহের সাচ্চু, আমার অনেক আদর-স্নেহ নিবি। ছোট ভাইবোন সবাইকে দিবি। আমি আর বাড়িতে যাব না। বড় হয়ে শহরে বাসা নিয়ে তোদের সবাইকে নিয়ে আসব। আমি ক্লাস সেভেনের পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হয়েছি। তুই ছোট ভাইবোনদের নিয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া করবি। মাকে বলবি, বড় হয়ে আমরা সবাই মায়ের মুখে হাসি ফোটাব। ইতি, তোদের বড় ভাই বাচ্চু।
আমার জীবনে তো সেই প্রথম চিঠি পাওয়া। যদিও চিঠিটা ভাইয়ের বানানো খামে, মামার মাধ্যমে এসেছে। চিঠির কথা মাকেও জানিয়েছিলাম। ভাই তো আর বাড়িতে আসবে না। আমরাও কি তবে নানাবাড়িতেই থেকে যাব ?
কিন্তু নানা গরিব মাস্টার। আমাদের আব্বার মতো বড় গেরস্থ নয়। অত বেশি জমিও নেই। মামা বলে, ‘বুবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে না এলে, আর বাচ্চু বাড়িতে থাকলে হয়তো আবার বিয়ে করার সাহস পেত না।’
কিন্তু মা জোর প্রতিবাদ করে, ‘ও শয়তান লোক সব ঠিক করেই রেখিছিল। আবার বিয়ে করার জন্যই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। শুধু দ্বিতীয় বিয়ে নয়, নবিজির দোহাই দিয়া এরপর সে হয়তো তৃতীয় বউকেও ঘরে আনবে।’
মামা বোনের ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য আমাদের বাড়িতে গেছে। আব্বা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। হুঁকা টানতে টানতে যুক্তি দিয়েছে―অত বড় সংসার, এত জমির ফসল ঘরে তোলার কাজ তোর বোন একা সামলাতে পারে না। উপরন্তু পাড়াপড়শি ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে সংসারের বিস্তর ক্ষতি করে। বাড়িতে কাজের লোকের দরকার আছে বলেই আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। কিন্তু মাকে তো সে তালাক দেয়নি। কেন সে বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল ? রাগ করে ঘরে তালা দিয়েছিল, কিন্তু ঘর তো খুলে দিয়েছে সেদিনই। এরপরও যদি সে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষতি করে বাপের বাড়িতে থেকে যায়, তবে শুধু মায়ের বিরুদ্ধে নয়, পণ্ডিত শ্বশুর ও শালার বিরুদ্ধেও কেস করে দেবে সে। ভয় দেখানোর পাশাপাশি মামাকে তার বোনের সতীনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে সৎ বোনের দেওয়া খাবারও খেতে হয়েছে মামাকে।
মামা ফিরে এসে এসব খবর জানালে, অনেক কান্নাকাটির পর নানার কথায় মা সতীনের সংসার করার দুঃখ-কষ্ট চেপে আবার আমাদের নিয়ে গরুগাড়িতে চেপে বসল।
বাড়িতে গেলে নতুন মা ছুটে এসে আমার মায়ের কদমবুসি করে। মা তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়ার বদলে পা টেনে নিয়ে আমাদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। আমরা যারা ডাইনি দেখার কৌতূহল নিয়ে সৎমাকে দেখছিলাম, হাসিমুখে সে আমাদের কাছে ডাকে। বোনের কোল থেকে ছোটটিকে কোলে নিতেই সে কাঁদতে থাকে। তার পরেরটিও ছুটে পালায়। কিন্তু আমি ও বোনটি তো পালাতে পারি না। আমাদের কাছে নিয়ে আদর করে বলে, ‘আগে তোমাদের একটা মা ছিল, এখন হইতে দুইটা মা হইল। তোমাদের আজ আমি ক্ষীর রান্না করি খাওয়াব। ঠিক আছে ?’
বাড়ির নতুন অতিথির হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই ছোট বোনটি আমাকে কানে কানে সতর্ক করে, ‘ক্ষীরে বিষ মেশায় দেবে। খবরদার খাবি না মেজভাই।’
পিতার দ্বিতীয় বিয়েতে মায়ের সঙ্গে আমরাও বিস্তর কেঁদেছি। নানাবাড়িতে থেকে নিরাপত্তার অভাব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় জেগেছিল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে নতুন মাকে দেখে ক্রমে ভয় কেটেছে। মনে আছে, ক্ষীরে বিষ ভেবে ছোট ভাইবোনেরা এড়িয়ে গেলেও আমি এড়াতে পারিনি। আমাকে বাগে পেয়ে আদর দেখিয়ে খেতে দিয়েছিল। এরপর বিষ খেয়ে বিষ হজম করে সাহস বেড়েছিল আমার। কিছুদিনের মধ্যে নয়া মাকে বলেছিলাম, ‘আমরা তো বাপের বিয়ার দাওয়াত খাইনি। এখন মাংস-পোলাও রাঁধিয়া আমাদের খাওয়ায় দেন নয়া মা।’ আমার কথা শুনে খুশি হয়েছিল নয়া মা, এমনকি আব্বাও খুশি হয়েছিল। হাট থেকে গরু ও খাসির মাংস এনেছিল সেদিন। ছোটরা আমাকে বলেছিল, ‘পেটুক, নির্লজ্জ।’ কিন্তু ওরাও খেয়েছিল শেষ পর্যন্ত।
আসলে সতীনের সংসারে যেমন অশান্তি ঝগড়াঝাটি, আমাদের বাড়িতে প্রথম দিকে হয়নি বললেই চলে। আমরা তো বড় ঘরে মাকে ঘিরে আগের মতো ছিলাম। অন্যদিকে আব্বা ও তার আলমারি-সিন্দুকসহ নতুন মায়ের দখলে চলে যাওয়ায়, মায়ের মনে যে কষ্ট ও জ¦ালা―সেটা আমরা তেমন বুঝতে পারিনি। নিজেদের লেখাপড়া, খেলা ও আনন্দ কুড়াতেই ব্যস্ত ছিলাম। নতুন করে আমার দেহ-মনে আতঙ্ক ও কাঁপুনি জাগানোর মতো ঘটনা আর তেমন ঘটেনি। আব্বা আবার বিয়ে করায় অগ্রজ বাচ্চু শহর থেকে আর বাড়িতে ফিরবে না বলেছিল। কিন্তু সেও কথা রাখেনি। মাস দুয়েক না যেতেই আগের মতোই বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছিল। বৃত্তির টাকা পেয়ে একবার মাকে এবং নতুন মাকেও দু খানা শাড়ি উপহার দিয়েছে। আর আমাদের ভাইবোনদের জন্য শহরের এমন এক ধরনের বিস্কুট আর চানাচুর এনেছিল, যা আগে আমরা কখনও খাইনি, পরেও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। সেই বিস্কুট-চানাচুরের স্বাদ যেন এখনও মুখে লেগে আছে।
এরপর একে একে নয়া মায়ের কোলে যেসব সৎ ভাইবোন এসেছে, ওরাও নিজের মায়ের কাছে আলাদা থাকার বদলে আমাদের ঘরে, আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেই আগ্রহী ছিল বেশি। সৎ বোনটি তো ঘোষণা করেছিল, ‘বড় আম্মাই আমার আসল মা, আমিও এ ঘরে থাকব।’ আমরা এত ভাইবোন থাকার পরও সতীনের সন্তানদের আপন করে নেওয়ার উদার মাতৃত্ব ও মহত্ত্ব কোনওটারই কমতি ছিল না মায়ের।
এরপর আমরা ভাইবোনেরা প্রতি বছর নিচের ক্লাস থেকে উপরের ক্লাসে উঠেছি, সংখ্যাতেও বেড়েছি। সৎমা একে একে চার সন্তানের মা হয়েছে। অন্যদিকে নিজের মাও তার মাতৃত্ব বিকাশের মমতা কিংবা নেশাতেও আরও তিন ভাইবোন উপহার দিয়েছে। মাকে নতুন করে গর্ভবতী দেখায় সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করেছি আমি। মায়ের সঙ্গে আব্বার সুসম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। তারপরও তার গর্ভবতী হওয়ার কারণ রহস্য খুঁজতে গিয়ে, নয়া মায়ের অনুপস্থিতিতে এক রাতে মাকে জরুরি কাজে ঘরে ডাকার হুঙ্কার ও আমার দত্যি আক্রান্ত হওয়ার স্মৃতি ঘুরেফিরে মনে পড়েছে।
আব্বার রাগ ও বাঘ-স্বভাবের পরিচয় পেতে দেরি হয়েছিল আমাদের সৎমায়ের। কিংবা জানলেও পাত্তা দেয়নি তেমন। একদিন রাতে আব্বার হাতের মার খাওয়ার দুর্ভাগ্য যখন হলো, তখন গলা ফাটিয়ে কেঁদেও আত্মরক্ষা হয়নি। বাঘের ঘরে যে ছাগলের অবস্থান, হামলার শিকার হয়ে যতই সে চিৎকার করুক, কে যাবে তাকে রক্ষা করতে ? তার কান্নার সঙ্গে আমাদের সৎ ভাই ছোট মহিনও কাঁদতে শুরু করেছিল। আমরা নিজেদের ঘরে জেগেই ছিলাম তখনও। বাচ্চু ভাই শহর থেকে বাড়িতে এলে তখন বড় ঘরে আলাদা বিছানায় আমরা দু ভাই একসঙ্গে থাকতাম।
বাচ্চুই প্রথম দরজা খুলে কোলের বাচ্চাসহ নয়া মাকে আমাদের ঘরে আশ্রয় দেয়। মা ঝগড়াটে গলায় তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। কারণ সতীনকে আশ্রয় দিলে তাকেও মার খেতে হবে। আবার বাড়ি ছাড়তে হবে। তাকেও আবার বাড়িছাড়া করার চক্রান্ত নিয়ে এ ঘরে ঢুকেছে সে। অতএব চিৎকার করে আমাদেরও হুকুম দিয়েছিল সে―এ ঘর থেকে বের করে দে। বাইরে গিয়া যত খুশি কাঁদুক হারামজাদি।
ঝগড়ায় মাকে পরাস্ত করার সার্বিক যোগ্যতা সত্ত্বেও, কোলের ক্রন্দনরত শিশু ও নিজের কান্না নিয়ে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। আমরা তাকে সান্ত্বনা ও আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করিনি। কারণ দরজা খুলে বাঘের গর্জন শুনছিলাম, ‘এইটুকু মারে হারামজাদির শিক্ষা হয় নাই। এবার ধরলে তোর হাড়হাড্ডি গুড়া করি বস্তায় ভরিয়া তোকে বাপের বাড়ি পাঠায় দেব।’
অত রাতে তার বাপের বাড়ি যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই হয়তো নয়া মা আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশী খালার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তার কান্না মিলিয়ে গেলে বাচ্চু আমাকে বলেছিল, ‘আব্বাটা এত বাড়াবাড়ি করে, ছি! টাউনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্ররা একজোট হয়ে জুতা দেখায় তার গদিতে আগুন জ¦ালায়। আব্বার বিরুদ্ধেও গ্রামে ওরকম আন্দোলন হইবে।’
অন্ধকারে উঠানেও কথাটা কানে গিয়েছিল আব্বার। হুঙ্কার দিয়ে জানতে চেয়েছিল, ‘বাচ্চু আইয়ুব খানের কথা কী বলে রে সাচ্চু ?’
ঘরে আবার পিনপতন স্তব্ধতা এসেছিল। ভাইকে রক্ষার জন্য আমি বলেছিলাম, ‘কিছু বলে নাই আব্বা। ভাই তো নিঁদ গেইছে।’
‘আইয়ুব খান আমাদের দলের নেতাকে জেলে দিছে। গ্রামের মানুষ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, না কি আমার ডাকে একজোট হইবে ? ’
‘আপনার ডাকে আব্বা।’
আমার জোরালো সমর্থন পেয়ে আব্বা শান্ত হয়েছিল। অতঃপর ঘুমের ভান করে আমরা কে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। রাতে নয়া মা ও তার কোলের ছোট্ট ভাইটির কান্না শুনতে পাইনি। তার ঘরে ফেরার আওয়াজও পাইনি। পরদিন ছুটি শেষ হওয়ার আগেই বাচ্চু ভাই আব্বাকে না বলেই আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শহরের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল।
৯.
বাচ্চু যে সত্যই আমার মতো ভীতু নয়, দুঃসাহসী এক নায়ক, সেটা নাকের নিচে গোঁফের রেখা পষ্ট হতে না হতেই গ্রামবাসী বুঝে গিয়েছিল। হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর একা একাই দিনাজপুর শহরে যাতায়াত করত সে। সাইকেলে কিংবা ট্রেনে ও বাসে। ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তখন। দেশজুড়ে গোলমাল-আন্দোলন, শহরে থেকে বাচ্চুও আন্দোলন করত। তারপর পাকিস্তানি মিলিটারি সারা দেশে বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। এ সময়ে বাচ্চুর দুঃসাহসী কীর্তিকলাপ কাছে থেকে দেখেছি আমি। শহরে থেকে শুধু আন্দোলন-রাজনীতি নয়, নিষিদ্ধ বই পড়া, সিনেমা দেখা ও বড়দের মতো সিগারেট খাওয়াও শিখেছিল। আমি ছোট হয়েও নিয়মিত মসজিদে যেতাম, কিন্তু বাচ্চু ছোটবেলায় নামাজ-রোজা করলেও শহরে থেকে নামাজ-রোজাও ভুলে গিয়েছিল। রোজার দিনেও বাড়িতে একদিন তাকে সিগারেট খেতে দেখে মাকে বলে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ভয়ে আব্বার কাছ থেকে দূরে থাকলেও, মাকে সে একটুও ভয় পেত না।
আব্বার ভয় দেখিয়ে মা তাকে সতর্ক করেছিল, ‘বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর আব্বাকে বলে দেব।’ বেপরোয়া বাচ্চু জবাব দিয়েছিল, ‘আব্বাও তো হুকা-তামাক খায়। ধর্ম-নবিজির দোহাই দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। আবার তৃতীয় বিয়েও করতে চায়। সামন্ত চরিত্রের শোষক, খারাপ লোক। সে আমার কী বিচার করবে ? তার চেয়ে কি আমি কম রাজনীতি বুঝি আমি ?’
‘ছি, বাপের বদনাম করে কোনও ভালো ছেলে ? সে কি তোকে নেশাভাঙ করার জন্য টাকা দেয় ? আমি কিছু না বলে দিলেও তোর সৎমা জানলে চুপ থাকবে না। নিজে টাকা রোজগার করবি যখন, তখন স্বাধীনভাবে চলিস।’
‘স্বাধীন সাম্যবাদী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা তো আন্দোলন করছি। এবার অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করব। বাঙালি জাতি স্বাধীন হলে আমিও স্বাধীন হব। আব্বার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না।’
এসব যে কথার কথা নয়, কিছু দিনের মধ্যে প্রমাণ দিয়েছিল বখাটে বাচ্চু। গ্রামের কয়েকটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য পালিয়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়ায়। যাওয়ার সময় শুধু আমাকে বলেছিল, ‘আমি যাওয়ার পর মাকে বলিস, দেশ স্বাধীন না হলে আমি আর ফিরব না।’ এরপর মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় ভাইয়ের খবর পাওয়ার জন্য লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম আমিও। ভাইও এক বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ভেবে গর্ব জাগত। আবার মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে ভাইয়ের মৃত্যুর আশঙ্কায় মা যখন কাঁদত, আমিও তার কান্নায় শরিক হতাম।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাড়িতে আর একবার ফিরেছিল বাচ্চু, তাও আব্বার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য। যেহেতু সে আব্বার কথামতো লেখাপড়া শিখে, অসাধারণ এক মানুষ হওয়ার জন্য আব্বার দেখানো পথ থেকে থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, উল্টো আব্বার বিরুদ্ধেও রাজনীতি শুরু করেছিল, মুখোমুখি তর্ক করতেও ভয় পেত না, আব্বাই তাকে টাকা দেওয়ার বদলে কুকুরতাড়ানোর রাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।
বাচ্চু ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে মায়ের সঙ্গে আমরা ছোট ভাইবোনেরা, বিশেষ করে আমিও অনেক কেঁদেছি। বাড়ি ছাড়া হওয়ার পর প্রায় এক বছর তার কোনও খবরই পাইনি আমরা। এরপর একদিন পোস্ট অফিসের পরিচিতি পিয়ন স্কুলে গিয়ে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। আমার জীবনে সেই প্রথম পোস্ট অফিসের ডাকটিকেট বসানো হলুদ খামে প্রথম চিঠি পাওয়া। এতবার পড়েছি যে মুখস্থ আছে এখনও―‘প্রিয় সাচ্চু, আশা করি মাকে নিয়ে তোরা সবাই ভালো আছিস। আমি দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি। সে লড়াইটাই চালিয়ে যাচ্ছি। তুই যখন বড় হবি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বি, তখন তোকে আমার এ লড়াই আর বাড়ি ছাড়ার কারণ বিস্তারিত বুঝিয়ে বলব। মা যেন আমার জন্য অযথা আর চিন্তা না করে। আমি আব্বা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারিনি। তুই সে চেষ্ট করবি। আর আব্বাকে না জানিয়ে, মাকে বলে নিচের ঠিকানায় মানি অর্ডার করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিবি। মাকে ছাড়া এ চিঠি এবং আমার খবর কাউকে জানাবি না। ইতি―তোদের বড় ভাই বাচ্চু। ঠিকানা : বেলায়েত হোসেন বাচ্চু, প্রযত্নে : আব্দুস সাত্তার, ১৩/৩, হরনাথ সাহা স্ট্রিট, আমলিগোলা, লালবাগ, ঢাকা।’
হারিয়ে যাওয়া ভাইকে ফিরে পেয়েছি যেন, চিঠি পড়ে কী যে খুশি হয়েছিলাম সেদিন। স্কুল ছুটি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম মায়ের কাছে। মাও কাঁদতে কাঁদতে চিঠি পড়েছিল। তখন গ্রামেও বেশ মঙ্গাকাল। না খেয়ে থাকা মানুষ আমাদের বাড়িতেও খুব ভিড় করত। ভাই ঢাকায় গিয়ে যে গরিব-দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করছে, তারা তাকে ঠিকমতো খেতে দিতেও পারছে না হয়তো। মা গোপনে চাল বিক্রি করে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মানি অর্ডার করতে বলেছিল। মানি অর্ডারের সঙ্গে উপরের ঠিকানায় একটা চিঠিও লিখেছিলাম ভাইকে।
এরপর ভাইয়ের চিঠি আরও পেয়েছি। উত্তর এবং টাকাও পাঠিয়েছি বেশ কয়েকবার। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি তার এক চিঠিতে প্রথম জানতে পারি, বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বিয়ে করেছে। এবং ইতোমধ্যে একটি পুত্রসন্তানের বাবাও হয়েছে। ঢাকায় বাচ্চুর চাকরি ও স্থায়ী কোনও ঠিকানা জানার আগেই তার বিয়ের খবর পেয়ে বেশ চমকে উঠেছিলাম আমরা। চিঠিতে সে ঢাকায় তার বাসায় থেকেই আমাকে কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ফলে আব্বাকে জানাতে হয়েছিল ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান হওয়ার খবর। বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাহ্য করে কেউ যে বিয়ের মতো মহা সমাজিক একটা কাজ করতে পারে, আব্বা ও অনেকের কাছেই ছিল সেটা অবিশ্বাস্য খবর। তবে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসারজীবন শুরু করেছে ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল সবাই। তার প্রস্তাবে আব্বাও আপত্তি করেনি। এরপর বাচ্চুর নাজুক বা নড়বড়ে সংসারে কমরেড-স্ত্রী হেনা ভাবি ও শিশুপুত্র সাগরের সঙ্গে আমিও একজন অপিরহার্য সদস্য হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমে চিঠির মাধ্যমে এবং পরে সশরীরে আরও প্রায় বছর আটেক ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে সংযোগসেতু হিসেবে কাজ করেছি।
১০.
গ্রামে অবস্থানকালে শৈশব-কৈশোরে যেমন ভাইয়ের চিঠি, তেমন ভাইয়ের বাসায় অবস্থানকালে সরকারি দুই ব্যাংকের নিয়োগপত্র পাওয়াটাও স্মৃতিতে অবিস্মরণীয়, সম্ভবত সেরা খুশির ঘটনা। তখনও মাস্টার্স পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি। অগ্রজের সংসারের আর্থিক অনটন লেগেই আছে। অন্যদিকে বাড়িতে আব্বার আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়েছে। অনেকগুলো ভাইবোনের লেখাপড়া ও বোনদের বিয়ের চাপ। বাচ্চু তার দলের রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। কী এক পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকরি করে। যা বেতন পায়, তা দিয়ে নিজের সংসারই চালাতে পারে না। ভাবির কাছে খরচের টাকা চাইতেও সংকোচ হতো। তাই চাকরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম স্নাতক-মাস্টার্স সার্টিফিকেট অর্জনের আগে থেকেই। সোনালি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকে নিম্নমান সহকারী পদে কয়েক শত লোক নেওয়া হবে দেখে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু ডজনেরও বেশি চাকরির অ্যাপ্লিকেশন-খরচ অপচয় এবং ইন্টারভিউয়ের রেজাল্ট হাতে না পেয়ে বদ্ধমূল ধারণা হয়, এসব ইন্টারভিউ আসলে লোক দেখানো। ধরপাকড় কিংবা ঘুষ ছাড়া সরকারি চাকরি কপালে জুটবে না আসলে। বাচ্চু ভাই তার শিক্ষা অধিদফতরে স্ত্রীর সরকারি চাকরিটাও জোগাড় করেছিল রাজনৈতিক চ্যানেলে ক্ষমতাবান কাউকেই ধরেই। কিন্তু আমার চাকরির জন্য তেমন গরজ ছিল না তার। ভাইয়ের ভাড়া বাসা ও পত্রিকার চাকরিও ঘন ঘন বদল হয় বলে চাকরির আবেদনে আমি অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ভাবির নাম ও তার সরকারি অফিসের ঠিকানা ব্যবহার করতাম। প্রায় বছরখানেক আগে দেওয়া ইন্টারভিউয়ের সুফল সোনালি ব্যাংকের নিয়োগপত্রখানা হাতে দিয়ে বলেছিল সে, ‘দেখো, তোমার আরও একটা ইন্টারভিউ লেটার এসেছে বোধহয়।’
কিন্তু নিয়োগপত্র পড়েও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভাবি পড়ে খুশিতে বলেছিল, বাহ সুখবর। সোনালি ব্যাংকে চাকরি পেয়ে গেলে, যদিও আমার মতো ছোট পোস্ট, কিন্তু ব্যাংকে তো ঘন ঘন প্রমোশন হয় শুনেছি। জয়েন করবে, নাকি আরও বড় কোনও পদে চাকরির অপেক্ষা করবে।’
‘বড় পদে বিনা ঘুষ-তদবিরে চাকরি হবে, তার গ্যারান্টি কে দেবে ?’
ভাবি দিতে পারেনি। এ জন্য এখনও মনে হয়, এ জীবনে যতবার যতরকম খুশির ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে সরকারি দুই ব্যাংকের নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ঘটনাই সেরা। জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোনালি ব্যাংকে চাকরি পাওয়াটা ব্যক্তিগতভাবে আমার যেমন, আমার অচেনা হবু স্ত্রী-কন্যা এবং গাঁয়ের স্বজনদের জন্য সুখবর ছিল অবশ্যই। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল সুখবরটা গোটা দেশ-জাতির জন্য গর্ব ও প্রেরণার বিষয়। বিশেষ করে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের জন্য। লক্ষ লক্ষ বেকারদের মধ্যে বাচ্চু ভাইকেও বেকার হিসেবেই গণ্য করতাম আমি। তার বাসায় ফিরতে যেহেতু দেরি হবে, সুখবরটা দেওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম তার পার্টি-পত্রিকা অফিসে।
‘ভাই, তোরা স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন করছিস। এদিকে এরশাদ মামা তো আমাকে সোনালি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েই দিল।’
প্রেসিডেন্ট এরশাদ উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং রংপুরে তার ভাগ্নে সম্পর্কের একজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাচ্চু ভাই এ-খবরটা জানত। আর মামার জোর তথা দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ছাড়া যে এ দেশে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দুষ্কর, আমার চেয়েও এ জ্ঞান ছিল তার টনটনে। স্বাধীন দেশে সরকারের এসব অনাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজে সরকারের সামান্য একটা কেরানির চাকরি পর্যন্ত নেয়নি। কাজেই আমার খুশির খবরটা শুনে বড় ভাই প্রথমে বলেছিল, ‘তুই কি তোর সেই বন্ধু, প্রেসিডেন্টের কোন ভাগ্নে না কে আছে যেন, তাকে ধরে ব্যাংকে চাকরি-বাকরির আশ্বাস পেয়েছিস ?’
‘কোনও শালাকেই ধরিনি। কোনও পলিটিক্যাল চ্যানেলে যাইনি। একটা পয়সা ঘুষও দেই নাই কাউকে। ইন্টারভিউতে নিজেকে সম্পূর্ণ যোগ্য প্রমাণ করে, বিনা তদবিরে আজ অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেয়োিছ।
খামসহ নিয়োগপত্রখানা ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ভাই পড়তে শুরু করেছিল, আর আমার খুশি তার মধ্যে কতটা সঞ্চারিত হয় দেখার জন্য অপলক তাকিয়েছিলাম।
ভাইয়ের খুশিতে বিস্ময় ও তাচ্ছিল্যের ভাবটাই ছিল বেশি। বলেছিল সে, ‘সামান্য এক কেরানির চাকরি পেয়ে মানুষ এত খুশি হয়! তোকে না দেখলে বুঝতাম না রে সাচ্চু। আমি তো ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি চেয়ারম্যানের মতো বড় একজন কেউকাটা হয়েই গেলি।’
‘সেরকম কিছু হলে এরশাদের পতন হলে আমারও পতন হবে। কিন্তু আমার এ চাকরি পার্মানেন্ট হবে। আর ব্যাংকের কেরানি মানে কিন্তু পার্মানেন্ট কেরানি নয়। ভাবিও জানে, তার সরকারি চাকরির চেয়েও ব্যাংকের চাকরিতে প্রমোশোন ও সুযোগ-সুবিধা বেশি। ব্যাংকের নাইনটি পার্সেন্ট সিনিয়র অফিসার, এমনকি অনেক এজিএম ডিজিএমও এককালে কেরানি হিসেবে ঢুকেছিল। কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিন বছর পরপরই সেখানে প্রমোশন হয়।’
‘নিম্নমান উচ্চমান পদ যাই হোক, আসলে কাজ তো কেরানিরই। ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশরা দেশে যে কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে, তাতে তোর কেরানির চাকরিটা পেয়ে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ কি পাকিস্তানি আমল হলে ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবি শাসকশ্রেণির গোলামি করতে হতো, আর এখন দেশি স্বৈরাচারী শাসক-শোষকদের স্বার্থে পুঁজিবাদী সিস্টেমের দাস হয়ে কাটাতে হবে জিন্দেগি।’
‘ভাবিকে সরকারি কেরানির চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে বিচ্চুর মতোই সব সরকারকে আক্রমণ করার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিস। তোর মতো বড় কিছু করার স্বপ্ন-সাধ আমার তো কোনও কালেই ছিল না। আমি কেরানি হয়েও পরিবারকে যদি সাহায্য করতে পারি, সেটাই হবে আমার জীবনের সার্থকতা।’
বহুদিন পর ছোটবেলার মতো অগ্রজকে বিচ্চু বলে খোঁচা দেওয়ায় সে রাগ করেনি। খুশির হাসিটাই বরং প্রসারিত হয়েছিল।
‘তোর চাকরির খবরে হেনাও খুশি হবে। কারণ সরকারি চাকরি পেয়ে তুইও তার জ্ঞেতিভাই হইলি। আর সাগরও বেশি চকলেট-চুইংগাম পাবে বলে খুশি হবে। বাড়িতে সামান্য কেরানি হয়েছিস শুনে কতটা খুশি হবে জানি না, তবু সুখবরটা জানিয়ে দেখ, আব্বা কী বলে ?’
বাড়িতে আব্বার মত নিয়েই সোনালি ব্যাংকের চাকরিতে জয়েন করার ছয় মাস পর ভাবি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগপত্রখানাও হাতে এনে দিয়েছিল। বাচ্চুকে সেই নিয়োগপত্রখানাও হাতে দিয়ে আবার সগর্বে বলেছিলাম, ‘দেখলি তো, সরকার আমার যোগ্যতা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও গভর্নর বানাতে চায়। কিন্তু এখন কী করব, সোনালি ব্যাংক ছেড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগ দেব ?’
‘বাংলাদেশ সরকার যোগ্য কেরানিকে খুঁজে পেয়েছে এতদিনে। তা, প্রোমোশন এবং শাখা যেহেতু সোনালি ব্যাংকেরই বেশি, ভবিষ্যতে বদলি নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি যেতে পারবি। তারপরও বাড়িতে আব্বার মত নিয়ে দেখ।’
ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবেই বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগ দিইনি আর। চাকরিটা পার্মানেন্ট হওয়া পর্যন্ত ভাইয়ের বাসাতেই ছিলাম। প্রথম মাসের বেতনে বাড়িতে মিষ্টি খাওয়ার টাকা পাঠিয়েছি, আবার মিষ্টি ছাড়াও ভাই-ভাবি ও ভাতিজাকেও জামাকাপড় কিনে দিয়েছি। চাকরির আগে ভাইয়ের সংসারে চাপ কমাতে বাড়িতে গেলেই মা চাল-ডাল এটা-সেটা অনেক কিছু দিত। আমাকে বাসায় রাখার পেছনে এমন প্রাপ্তির আশা হয়তো শুরু থেকেই ছিল। চাকরির পরও সম্পর্কটা বজায় রেখেই ভাইয়ের বাসায় থাকার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম, ‘আব্বার আর্থিক অবস্থা তো এখন ভালো নয়। ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া ও বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য মেলা টাকা দরকার। আমি বেতনের টাকাটা থেকে নিজের পকেট-খরচটা রেখে বাকি টাকাটা বাড়িতে পাঠাব।’
তখন পর্যন্ত আমি ছাড়া বাড়ির সঙ্গে বাচ্চুর কোনও রকম সম্পর্ক ছিল না, বড় হয়েও বাড়ির জন্য কোনও দায়িত্ববোধও ছিল না। ভাই-ভাবির অনটনের সংসারে সাহায্য করার বদলে বাড়িতে টাকা পাঠানোর প্রস্তাবটাও সম্ভবত পছন্দ হয়নি তার। মুখে বলেছিল অবশ্য, ‘তোর বেতনের টাকা তুই যেমন ইচ্ছে খরচ করবি, আমার আপত্তি করার কী আছে ? তবে বিয়েশাদি করলে তো আলাদা থাকতেই হবে। আমার মনে হয় এখন থেকেই মেসে উঠে তোর আলাদা থাকা উচিত।’
‘ছোট বোন দুটির বিয়ের আগে নিজে বিয়ে করব না আমি। মাকেও বলেছি। ততদিন একসঙ্গে থাকলে বাড়িতে সাহায্য করার পাশাপাশি তোকেও প্রয়োজনে কিছু সাহায্য করতে পারব। মেস-এ আলাদা থাকলেও তো সিটভাড়া ও খাওয়া খরচ লাগবে। সেই টাকাটা ভাবিকে মাসে মাসে দিলেও তার উপকার হবে।’
হঠাৎ রেগে উঠেছিল বাচ্চু, ‘ওই হিচ্চু, তোর সাহায্যের টাকাকে পেচ্ছাব করি আমি। আব্বা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর তার সাহায্য ছাড়াই বেঁচেবর্তে আছি যখন, তোর সাহায্য ছাড়াও চলতে পারব। নতুন একটা পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকরিতে ঢুকলে, তোর চেয়েও বেশি বেতন পাব। তুই আগামী মাস থেকে কোনও মেসে উঠে আলাদা থাকবি।’
ভাইয়ের রাগে আমার ভিতরে পাল্টা-অভিমান তেমন জাগেনি। উল্টো তার ব্যর্থ জীবনের জন্য কিছুটা করুণা জেগেছিল। বাড়ি থেকে আনা চাল-ডাল ও বেতনের টাকায় কিনে দেওয়া এটা সেটা উপহার নিতে আপত্তি না করলেও, বেতনের টাকা নিতে সংকোচের কারণ অবশ্যই নিজের জীবনের ব্যর্থতা। ভাইয়ের সিদ্ধান্ত ভাবি বুঝিয়ে বলেছিল। পরের মাসেই অফিসের কাছে এক মেস-এ উঠে স্বাবলম্বী হয়েছিলাম।
অফিস করা ছাড়া আমার তো দেশের কাজ ছিল না। প্রথম পোস্টিং ছিল নিউমার্কেট ব্রাঞ্চে। সেখানে ছুটির পর অবসরে ঘুরে মেয়েদের দেখতে ভালো লাগত বটে, কিন্তু আজান শুনলে কাছাকাছি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার অভ্যাসটা বজায় রেখেছিলাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মেস-এ রুমমেটদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা বিছানায় চোখ বুজে অনিশ্চিত প্রেমিকা কি কল্পিত হবু স্ত্রীর সান্নিধ্য উপভোগ―কতক্ষণ আর ভালো লাগে ? ঘুরেফিরে ভাইয়ের বাসায় ছুটে যেতাম। ওরাও কখনও বিরক্ত হতো না। প্রথম দেখায় ভাবিকে তেমন ভালো লাগেনি। অজ্ঞাতকুলশীল খুলনা জেলার মেয়ে। দেখতে শুনতে মোটেও চোখে ধরার মতো নয়। ভাইয়ের মতো দেশোদ্ধারে বিপ্লবী রাজনীতি করতে এসে, সন্তান ও চাকরি নিয়ে ভাইয়ের সংসার উদ্ধারের সাধনা দেখে বুঝেছি, খুব ধৈর্যশীল গুণবতী মহিলা। চাকরি করার পরও বাসার রান্নাবান্না ও ছেলেকে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করত। চাকরি হওয়ার পর নিজের চাকরি এবং বিয়ের পর নিজের সংসারের ভালো-মন্দ সমস্যা ভাইয়ের আগে ভাবির সঙ্গেই শেয়ার করতাম। পরামর্শ নিতাম তার।
চাকরির পনের বছর পর পার্কিনসনের সূচনায় আমার কম্পরোগের সঙ্গে ভয়-টেনশনের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনার কথা শুনে অফিসকেই দায়ী মনে হয়েছিল আমার। সন্দেহটা সত্যি হয়ে উঠল দশ কোটি টাকা ঋণখেলাপির কেসটায় যখন শোকজ লেটার হাতে পেলাম। একা আমি নই, ওই ঋণের সঙ্গে জড়িত আমার তৎকালীন বস ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং হেড-অফিসের এক প্রিন্সিপ্যাল অফিসরাও পেয়েছে। যথাযথ আইন অনুসরণ না করে এবং ঋণ পরিশোধে পার্টির সক্ষমতার মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতি শনাক্ত করা হয়েছে। অতএব কেন আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না―দশ দিনের মধ্যে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।
ঋণখেলাপির কেস নিয়ে পত্রপত্রিকায় এমনকি জাতীয় সংসদেও বিরোধী দলের প্রশ্নে আমাদের সোনালি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বিষয়টাও আছে। এই তালিকায় আমার দশ কোটি টাকা আছে জেনেই আঙ্গুল কাঁপা শুরু হয়েছিল। আর শোকজ লেটার হাতে পেয়ে পুরো হাতের কাঁপুনি সবার চোখেই ভয় ধরানো-দশায় বেড়েছিল। শোকজ লেটার হাতে নিয়ে রাতেই ছুটে গিয়েছিলাম ভাইয়ের বাসায়।
কম্পমান হাত দেখিয়ে ভাইকে বলেছিলাম, ‘বিনা তদবিরে ব্যাংকের চাকরিটা পেয়ে খুশি হয়েছিলাম। এখন অনেক তদবির ছাড়া আমার চাকরি রক্ষার আর কোনও উপায় নেই।’
শুধু হাত নয়, আমার গোটা শরীর ও কণ্ঠেও কাঁপুনি জেগেছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল দুজনেই, ‘আজ এত কাঁপছিস কেন ? হয়েছে কী ?’
‘তুই তো একবার বললি ভয়ে কাঁপাটা স্বাভাবিক। আমার ভয়টা আসলে পরিবার থেকে নয়, অফিস থেকেই আসছে।’
‘কিন্তু তোর চাকরি যাবে কেন ?’
মাসকয়েক আগে ব্যাংকের দশ কোটি টাকার লোনের একটা ঘটনা তোকে বলেছিলাম। ঘটনা ঘটেছে চার বছর আগে, আমি মোহাম্মদপুর শাখায় থাকার সময়ে। সেই লোনের কেস নিয়ে এতদিনে হেড অফিস একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট তিন/চারজনকে এই টাকা পরিশোধ করতে হবে। গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরিটাও যেতে পারে, পেনশন-গ্রাচুইটি কিছুই পাব না।’
‘দশ কোটি টাকা ঋণ তো তুই নিজের নামে নিস নাই। ব্যাংক ভুয়া এক শিল্পপতিকে দিয়েছিল। একা তুইও দিসনি, তোর শাখার ম্যানেজার থেকে শুরু করে নিশ্চয়ই আরও কয়েকজন জড়িত ছিল। তোদের ব্যাংকের হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপি আছে। এ নিয়ে আমি লিখেছিও। তাদেরকে এই ঋণ যারা দিয়েছিল, তাদের কারও চাকরি গেছে বলে তো জানি না। কিন্তু মাত্র দশ কোটি টাকার ঋণ খেলাপির কেসে তোর চাকরি যাবে কেন ? তুই সিস্টেম আর বসদের হুকুমমতো কাজ করেছিস, এ জন্য ঋণের টাকা সরকার তোর কাছেই বা আদায় করতে চাইবে কেন ?’
ভাইয়ের মধ্যে নিজের ভয় টেনশন কিছুটা সঞ্চারিত করতে পারলে আমার ভালো লাগে। হাসিমুখে স্বীকার করি, ‘ব্যক্তিগত অপরাধ তো নিশ্চয়ই কিছু আছে। নইলে তদন্ত হচ্ছে, আর আমিও ভয়ে কাঁপছি কেন ? পাপ করলে শাস্তির ভয় তো জাগবেই।’
‘কিন্তু তোর ব্যক্তিগত অপরাধটা কী ?’
‘বেতনের বাইরে কিছু উপরি আয়, ঘুষঘাস খাওয়ার রাস্তা খোঁজা―এটাকে ব্যক্তিগত না বলে সামাজিক অপরাধও বলা যায়। তুইও যেমন শুধু ভাবির চাকরির উপর ভরসা না করে সাংবাদিকতা, লেখালেখি আর পার্টি করেও টাকা রোজগারের ধান্ধা করিস। আমিও চাকরির বেতনের বাইরেও বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেছি। এর পেছনে মারিয়ার ও তার ভাইয়েরও উৎসাহ ছিল। আমার বিয়ে ও পরিবার গড়ার পেছনে তোরও তো ভূমিকা আছে ভাই। কাজেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক অপরাধের দায় না খুঁজে আমার চাকরিটা রক্ষার চেষ্টা করাটা জরুরি। মারিয়া ও তার ব্যাংকার ভাই তাদের লেভেলে চেষ্টা করছে। তোরও তো উপর লেভেলে কত জানাশোনা, দেখ কাউকে দিয়ে আমার চাকরিটা বাঁচানোর চেষ্টা করা যায় কি না।’
ভাই আর কিছু জানতে চায়নি। আমার চাকরি রক্ষার তদ্বিরের একটা লাইন খুঁজেও পেয়েছিল। ভাই-ভাবি উভয়ের ঘনিষ্ঠ পার্টির এক নেতার নিকট-আত্মীয় সোনালি ব্যাংকের চেয়ারম্যান। তাকে দিয়ে হয়তো ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বলাতে পারবে। আমি ভাইকেও আমার কেসটার পার্টিকুলারস লিখে দিয়েছিলাম।
১১.
নিজের যোগ্যতায় কেরানির চাকরিটা পেয়ে খুশি হওয়ার কারণ ওই সময়ে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল অবশ্যই। সমাজসচেতন বড় ভাই জানে সেটা। কিন্তু চাকরিটা যাওয়ার ভয়-টেনশনের সঙ্গেও যে আমার নিজের পরিবার তথা স্ত্রী-কন্যা সম্পর্কের দুই নারীর বাঁচা-মরার সম্পর্ক, বড় ভাই সেটাও বুঝেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু চাকরি-হারানো ভয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লোভ, পাপবোধ ও পরিবারই যে মূল দায়ী, রাজনীতিগ্রস্ত ভাই-ভাবি হয়তো সেটা ভালো বুঝতে পারে না। সব খারাপের দায় সে শোষকশ্রেণি ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত। তাছাড়া আদরের ছোট ভাইটিকে হয়তো নিজের মতোই দুর্নীতিবিরোধী, নির্লোভ, সৎ এবং ধর্মভীরু ভালো মানুষ ভাবে।
আমার প্রতি অন্ধ স্নেহ-বিশ্বাস ছাড়াও, সরকারি কি বেসরকারি দশটা-পাঁচটা চাকরি করে খাওয়া পেশাজীবীদের সম্পর্কে বাচ্চুর প্রাকটিক্যাল জ্ঞানের অভাব। কী ছাতা এক সাংবাদিকতা করে এখন, সেখানে ঠিকমতো বেতন পায় না শুনেছি। সম্পাদক, ব্যবস্থাপক কি সিনিয়র কাউকে স্যার ডাকতে হয় না। মাঝে মাঝে নিজের রাজনৈতিক দলের অফিসে যায় যেন আড্ডা দিতে। বাচ্চুর পক্ষে ব্যাংকের কাজের নিয়ম-নীতি ও তার ফাঁকফোকর না জানাই স্বাভাবিক। পুথিপড়া জ্ঞানে জানে কেবল, রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশের নব্য ধনী লুটেরা-পুঁজিপতি শ্রেণি কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করছে। কোন শিল্পপতি কত কোটি টাকা ঋণ করে ঋণখেলাপি হয়েছে, তার হিসাবটাও বড়জোর ফাঁস করতে পারবে। কিন্তু সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীর পরিবারও যে সংসারের চাহিদা মেটাতে বাড়তি আয়ের ফাঁদে পড়ে জেরবার হতে পারে, বাচ্চু আমার মতো সৎ কেরানি ভাইয়ের বেলায় তেমন আশা করেনি। তাছাড়া নিজের চিন্তা ও আদর্শে বিশ্বাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু মারিয়াকে বিয়ে করার পর ব্যাংকের ধরাবাঁধা বেতনে চাকরি করে আমি কতোটা সুখ-অসুখ ভোগ করছি, এ ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা রাখলেও বিস্তারিত জানে না সে। শৈশবে যে সরলতা নিয়ে বাড়ির চাকরের পুরুষাঙ্গে দাড়ি আবিষ্কারের বিষয় ভাইকে বলেছিলাম, তেমন সরলতা নিয়ে নিজের গোপন সুখ-অসুখ ও অপরাধের ব্যাপারটা বলতে পারলে হালকা বোধ করতাম। কিন্তু নিজেকে ছোট করা কি সহজ কাজ! ভালোর সঙ্গে আমার খারাপটাও বিস্তারিত জানার জন্যই হয়তো পরে, আদর্শবাদী অগ্রজ সৎভাবে আমাকে স্মৃতিকথা লিখতে উৎসাহ দিয়েছে। কাজেই মরি বাঁচি সত্য কথাই লিখে যাব।
চাকরির বয়স বিশ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমি তিনটি প্রোমোশন পেয়ে এখন সিনিয়র অফিসার। এর মধ্যে ঢাকার ছয়টি শাখায় কাজ করে বর্তমানে আছি পুরানো ঢাকার বাবুবাজার শাখায়। এই দীর্ঘ সময়ে অফিসের নিয়মমাফিক বেতন-বোনাস-ইনক্রিমেন্ট-ওভারটাইম ইত্যাদি বৈধ প্রাপ্তির বাইরে আমার উপরি বা অবৈধ আয় ছিল না বললে মিথ্যে বলা হয় না। সবাই জানে, ব্যাংকের চাকরিতে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে বুকে হাত দিয়েও বলতে পারব, ঘুষ খাইনি এ জীবনে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদফতরে যারা চাকরি করে―যেমন পুলিশ, কাস্টমস, হেলথ, এডুকেশন ইত্যাদি বিভাগ―তাদের মধ্যে কজন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, শুধু বেতনের টাকায় সংসার চলে তাদের ? কিন্তু ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকে নিজে সৎ পথে অবিচল থাকার চেষ্টা করেছি। শুধু ধর্মভীরু বলে নয়, খুব হিসেবি মানুষ আমি। চা ছাড়া পান-সিাগারেট কি নেশা-ভাঙ বাবদে এক টাকাও খরচা করি না। বিয়ের আগে যখন এই শহরে মেস-এ একা ছিলাম, এক বখাটে বন্ধুর প্রেরণায় টাকার বিনিময়ে একটি ছদ্মবেশী বেশ্যার সান্নিধ্য পাওয়ার লোভে কাছে গিয়েও সংযত করেছিলাম নিজেকে। আমার হিসাবের খাতায় পাপের ঘরে একটা বড় পাপ যোগ হবে―এই ভয় নয় শুধু, এক হাজার টাকা অপচয়ের খাতে যোগ হওয়ার ভয়টাও ছিল প্রবল। এই এক হাজার টাকা আমার বড় ভাইয়ের টানাপোড়েনের সংসারে দিলে কত কাজ লাগবে। ভাতিজা সাগর এক বছর এ টাকায় চিপস-চকলেট খেতে পারবে। এরকম হিসেবি ও বিবেচক মানুষ ছিলাম বলে বিয়ের আগে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের পরেও নিজের ভবিষ্যৎ-পরিবারের জন্য ডিপোজিট স্কিম খুলে কিছু জমাতে পারছিলাম। বিয়ের পরও অভ্যাসটা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর গ্রামে বাবা-মা ও ও ঢাকায় বড় ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্কটা ক্রমে ছিন্ন করে দেয় মারিয়া। কারণ কেরানির চাকরি করে ঢাকায় নিজের সংসারের চাহিদাই মেটাতে পারছিলাম না ঠিকমতো।
মারিয়া গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পিতৃহীন মেয়ে। গ্রামে থেকে লেখাপড়া করেছে। গ্রামে থাকলেও ঢাকার অভিভাবক চাকরিজীবী বড় ভাই এবং রাজধানীবাসী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে রাজধানীর হালচাল বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল। বিয়ের আগেই সুখ-স্বপ্নের রঙে গড়া নিজের সংসারটি ঢাকার দূষিত পরিবেশেই দেখতে পেয়েছিল সে। নিজের চাকরি করার যোগ্যতা নেই। যে দেশে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে গ্রাজুয়েট মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েও বেকার থাকে, সেখানে কোনও রকমে ইন্টারমেডিয়েট পাস করে কী চাকরি করবে সে ? চাকরির স্বপ্নও দেখেনি। বিয়ের পর পেশায় গৃহবধূ হলেও স্বভাবে বহির্মুখি, অনেক বেশি সামাজিক। ঢাকায় দেড় রুমের ভাড়া বাসায় সংসার শুরুর পর তার নিজের ভাই-বোন ও আমার বড় ভাইয়ের সংসারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেরটাকে আরও বেশি সচ্ছল ও সুন্দর করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল সে। এ জন্য ঢাকা শহরের কোন এলাকায় সস্তায় ভালো বাসা পাওয়া যাবে, কোন মার্কেট থেকে কী কিনতে হবে, ঢাকা বাসের বছরখানেকের মধ্যে ভাবি-জা-বোন ও পাড়াপড়শি আপাদের চেয়েও তার বাস্তব জ্ঞান কম হয়নি। বড় জা যেহেতু চাকরি করে সংসার চালানোর পাশাপাশি অযোগ্য স্বামীকেও চালায়, মারিয়া চাকরি করত না বলে নিজের সংসার চালাতে আমাকে চালানোর দায়টা আরও সিরিয়াসলি নিয়েছিল। তার দৃষ্টিতে আমার চাকরির ধরাবাঁধা বেতন বাচ্চুর বেকারত্ব কিংবা গোপন ধান্ধাবাজির কাছে অতি তুচ্ছ। পুরুষ মানুষের আসল যোগ্যতা হলো বেতনের বাইরে কে কতোভাবে এবং কতো বেশি রোজগার করে। কে কতটা দ্রুত উন্নতির পথে হাঁটে।
মারিয়া নিজের বড় ভাইয়ের পাশাপাশি বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গেও আমার তুলনা করে প্রায়ই। পরিবারের দুটা মানুষের সমাজসচেতনতা ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে খুব ভাবায়। প্রথমজন বড় ভাই বেলায়েত হোসেন বাচ্চু। দ্বিতীয়জন ঘরের বউ মাহমুদা খাতুন ওরফে মারিয়া। দুজনই প্রখর সমাজসচেতন। বাচ্চু বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই দেশের বঞ্চিত শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য স্বঘোষিত আজীবন মুক্তিযোদ্ধা। আমি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তুই নিজেকে এখনও মুক্তিযোদ্ধা ভাবিস, একাত্তরের মতো তোর হাতে অস্ত্র কই ? বাচ্চু বলপেনটি দেখিয়ে বলেছিল, ‘এটাই আমার অস্ত্র। সাপ্তাহিক দেশব্রতী পত্রিকায় কী কলাম লিখি, পড়ে দেখিস।’
পড়েছি বেশ কয়েকটা। ওর প্রবন্ধের একটা বই বেরিয়েছে। সেটাও পড়ে দেখেছি। যেসব কবি-লেখক মরে গিয়েও নামটি অমর করে রেখেছে, যেমন রবীন্দ্র, নজরুল, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর―তারা যদি দাবি করে, পেন ইজ মাইটার দেন গান, তা হলে কথাটার মূল্য থাকে। কিন্তু অখ্যাত অগ্রজের পলকা বলপেনটি দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। নিজের পকেটের ঠুনকো বলপেন বের করে ঠাট্টাও করেছিলাম, ‘হ্যাঁ এটা দিয়ে গুলি করলে সমাজের শত্রু দূরে থাক, একটা তেলাপোকাও মরবে না।’
বাচ্চুভাই আমার ঠাট্টা-রসের ভক্ত। নিজেও হেসে বলেছিল, ‘কিছু গল্প-উপন্যাসের বই পড়িস বলে সমাজ-রাজনীতি নিয়ে গভীর চিন্তামূলক মননশীল লেখার মূল্য তুই কী বুঝবি।’
‘তোর যে বই দুইটা বেরিয়েছে, দশ বছরে তো শুনলাম হাজার কপিও বিক্রি হয়নি। আর পচা কাগজে সাংবাদিকতা করে লেখালেখি করিস। ফ্রি কপি পেয়ে আমি যা একটু-আধটু পড়ি, আর কেউ পড়ে বলে তো মনে হয় না।’
আমার কাজ আমি করি, নগদ লাভ খুঁজি না। অনেকটা এরকম নীতি বাচ্চুর। নিজের চিন্তা আর বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে আছে। অন্যেরা কে কী বলল কিছু যায় আসে না। ভাইয়ের সঙ্গে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, বিপ্লবী রাজনীতি করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রী ও বড় ব্যবসায়ীর নাম আমিও জানি। কিন্তু বাচ্চুর আপসহীন চিন্তা ও কাজে সমাজের কিংবা তার সংসারের কতটুকু লাভ হয়েছে ? হেনা ভাবিরও এই হিসাবজ্ঞান নাই বলে আমার ধারণা। আমার বউয়ের মতো মেয়ের পাল্লায় পড়লে বাচ্চুর বিপ্লবী চেতনা আর আদর্শনিষ্ঠা এতদিনে পালাবার পথ খুঁজতে গিয়ে কোন সাগরে যে হাবুডুবু খেত!
ভাইকে ব্যর্থ বিপ্লবী ও ভাবিকে বোকা-চণ্ডি কমরেড বলে ঠাট্টামস্করা করলেও তাদের দাম্পত্য ও সংসার পরিচালনার বোঝাপড়া সমীহ করি আমি। সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে ব্যর্থ হলেও, ভাইয়ের সততাকে আমি যেমন মূল্য দিই, হেনা ভাবিও সেরকম মূল্য দেয়। ছেলেমেয়ে দুটিকেও নিজেদের আদলে মানুষ করছে তারা। লেখাপড়ায় দুজনেই বেশ ভালো। নিজে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায়নি, সন্তানকে দিয়ে তাই পাওয়ার জন্য বাচ্চু সাংবাদিকতার চাকরি ছাড়াও নানারকম কাজ করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করে। দলীয় রাজনীতির মতো তার ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগও খুব বেশি সফল হয় না বলে আমার কাছেও টাকা ধার চায়। অনেক সময় ইচ্ছে হয়, বেতন পেয়ে যেমন সংসারের চাহিদা অনুযায়ী মারিয়াকে একবারে টাকাটা দিয়ে দিই, ভাইকেও তেমনি মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করি। কিন্তু মারিয়ার হিসাবজ্ঞান ও বিষয়-বুদ্ধি আমার চেয়েও প্রখর। সে জোর গলায় দাবি করে, ‘তোমার বড় ভাইকে চেনোনি, কিন্তু আমি ঠিকই চিনেছি। বাড়িতে বাবা-মাকে সাহায্য না করার জন্য বলে বউ চাকরি করে সংসার চালায়, আর নিজে সে গরিব-দুঃখীর সেবা করে বেড়ায়। আসলে ভণ্ড। কেরানির চাকরি করে কয় টাকা বেতন পায় তোমার ভাবি জানো না ? শুধু বউয়ের বেতনের টাকায় ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াচ্ছে ? বংশবুনিয়াদ না জেনে, বাড়ির কারও মতের তোয়াক্কা না করে দলের বারোয়ারি একটি মেয়েকে পটিয়ে বিয়ে করেছে। ঘরের বউকে চাকরি করিয়ে হাজার মানুষের সঙ্গে মিশতে দিতেও তার আপত্তি নেই। আবার নিজে লেখালেখি করে, কত রকম ধান্ধাবাজির পলিটিকস করে। অনেক ব্যবসায়ী বড়লোক আর সরকারি মন্ত্রীদের সঙ্গেও চেনাজানা! চাকরির বদলে এসব করে মাসে কত টাকা রোজগার করে সে বলেছে কখনও ? রাজনীতির নামে, গরিব মানুষের ভালো করার নামে চাঁদা তুলে নিজেও ভালো চলে। গ্রামের বাড়িতে কোনও সাহায্য না করার জন্যই তোমার সামনে এমন ভালমানুষি ভেক নিয়ে চলে।’
মারিয়ার এরকম মূল্যায়নের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। অনেকবার ধমকে বলেছি, ‘খবরদার আমার বড় ভাই ও ভাবিকে নিয়ে কোনও বাজে কথা বলবে না। তাদের পায়ের নখের যোগ্য নও তুমি।’
‘কোন ভাইয়ের বউ বেশি যোগ্য, সেটা তোমার বাবা-মা ছোট ভাইবোনদের কাছে শুনে দেখো।’
ঢাকায় সংসার পাতার পর থেকেই বুঝে আসছি, বড় ভাই ও বড় জা হেনাকে সে নানাভাবে ছোট করতে চায়। আমার ধারণা, এ জন্য মারিয়ার অসৎ ধান্ধাবাজ বড় ভাই এবং নিজের অযোগ্যতা ও হীনম্মন্যতাই বড় দায়ী। মেয়েরা যে কতটা হিংসুটে হতে পারে, মারিয়াও তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বাড়িছাড়া হবার পর বাচ্চু জীবনে কষ্ট ও সংগ্রাম কম করেনি। বিয়ের পর যেটুকু স্বাবলম্বী হয়েছে, সমাজ-সংসারে যেটুকু প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার মূলে হেনা ভাবির ত্যাগ ও অবদানই প্রধান। মৃত্যুর আগে আব্বাও যেহেতু এমন সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, পরিবারের সবাই তা স্বীকার করে। কিন্তু মারিয়া নিজের হীনম্মন্যতা আড়াল করে বড় জাকে টেক্কা দিয়ে প্রতি ঈদেই স্বামীর বোনাসের টাকায় বাড়িতে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ ও তাদের সন্তানদেরও নানা রকম উপহার দেয়। আর নগদ প্রেজেন্টেশন পেলে কে না খুশি হয় ? এক বোন তো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে, ‘বড় ভাই কত বছর হলো বিয়ে করেছে। আজ পর্যন্ত বাড়ির কাউকে একটা সুতাও উপহার দেয় নাই। কিন্তু মেজ ভাবি পালা করে সবার কথাই মনে রাখে।’
বাড়ির জন্য এসব করতে মারিয়া আমাকেও উৎসাহিত করতে নসিয়ত দেয়, ‘বাবা তো বড় ছেলেকে একরকম ত্যাজ্য ঘোষণা করেছিল। শেষ বয়সেও মন থেকে ক্ষমা করে নাই। সম্পত্তির ভাগও দেবে না হয়তো। তুমি তো বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালন করেছ। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ তোমারই বেশি পাওয়া উচিত। এ জন্য বড় ভাইয়ের অভাব পূরণ করতে বাবা-মা ও ওয়ারিশদের খুশি রাখাটা তোমার দায়িত্ব।’
আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, মারিয়ার এসব পরোপকারী দেওয়া-পাওয়ার সামাজিকতা গুণ বটে। শুধু তো শ্বশুরকূলের আত্মীয়-স্বজন নয়, নিজ বাড়ির স্বজনদের জন্যও উপহার দিয়ে সামাজিকতা করার ব্যাপারে বেশ উদার সে। কিন্তু অন্যদের কিছু দেওয়ার পেছনে তার স্বার্থ হাসিলের ধান্ধাটা আমার কাছে এতটাই নগ্ন যে, অনেক সময় মনে হয় মারিয়া আসলে ভণ্ড পলিটিশিয়ানদের মতো। ভোটের সময় ভোটারদের নানারকম মিথ্যে আশ্বাস দেয়। কখনও-বা নগদ টাকাও ঘুষ দেয়, এমনকি ভোটের রেজাল্ট নিজের পক্ষে নেওয়ার জন্য নানারকম কারচুপি করতেও দ্বিধা করে না। মারিয়াও অনেকটা সেরকম। প্রতিদ্বন্দ্বী বড় ভাই-ভাবিকে পরাস্ত করতে চায় সে। গাঁয়ের বাড়ির স্বজনদের দিয়েথুয়ে সবার নগদ প্রশংসা কুড়ায়। এসব করে ঢাকায় নিজের সংসারের জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু আদায়ের কৌশল ও লোভটাও ক্রমে সবার কাছে ধরা পড়ে।
স্বাধীন দেশে ধনী আরও কীভাবে ধনী, গরিব কেন আরও গরিব হয়―বাচ্চু এসব বিষয় নিয়ে তথ্য-সূত্র দিয়ে লেখালেখি আর রাজনৈতিক চাপাবাজিতে সমাজসচেতনার চরম পরাকাষ্ঠা দেখায়। বাচ্চুর দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর পরিসরে প্রসারিত, কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডীতে মারিয়ার মূল্যায়ন ও তুলনামূলক বিচার হাতেনাতে, বাস্তব প্রমাণভিত্তিক। বড় ভাইয়ের বাসায় নতুন ফিশার কোম্পানির রেফ্রিজেরেটর কিংবা টিভি সেটটি কত দামি, সে তুলনায় আমাদেরটি কেমন ? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অফিস-কলিগ বা বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে গিয়ে, এমনকি টিভির বিজ্ঞাপন-নাটকেও অন্যের কৃত্রিম সাজানো সংসার দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়, তার সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের অবস্থানটি তার অসন্তোষ বাড়ায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে বেড়াতে গিয়ে অন্যের সাজপোশাক দেখেও তুলনা করে নিজের ।
১২.
ব্যতিক্রমী অগ্রজ ছাড়াও ঘরে অযোগ্য স্বামীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মারিয়ার ব্যাংকার বড় ভাই শামসুলও দৃষ্টান্ত ও প্রধান মাপকাঠি হয়ে ওঠে। মারিয়ার অগ্রজ ও আমাদের বিয়ের ঘটক শামসুলও সরকারি জনতা ব্যাংকে চাকরি করছে। আমার চেয়েও বছর চারেকের সিনিয়র। নিজের চাকরিটা হওয়ার পর এক সময় একই মেস-এ ছিলাম আমরা। আমার মতোই কেরানি পদে যোগ দিয়ে প্রোমোশন ও বেতন স্কেলে আমার চেয়েও এখন এক গ্রেড উপরে সে। কিন্তু বেতন পায় আমার চেয়েও পাঁচশ টাকা কম। কারণ অফিসে লোন নিয়ে ঢাকায় জমি কিনেছে। লোনের কিস্তি মাসের বেতন থেকে কাটে। সংসারে তার স্ত্রী ছাড়াও দুই সন্তান। দুটাই ভালো স্কুল-কলেজে পড়ে। আমাদের চেয়েও বেশি বাসা ভাড়া দেয়। বাসায় মেহমানের আনাগোনাও বেশি। ফ্রিজভরা নানারকম মাছ-মাংস রেডি থাকে, আবার ছুটিছাটায় ছেলেদের নিয়ে ইতিউতি বেড়াতেও যায়। অন্যদিকে সেরা সরকারি ব্যংকে চাকরি করে আমি বেতন বেশি পাই, গ্রামের ভূ-সম্পত্তির দিক থেকেও বলা যায় আমরা জোতদার। তারপরও স্ত্রী-কন্যা নিয়ে মাত্র তিনটি মুখের সংসারে আমাদের এত নাই নাই হাহাকার কেন ?
মারিয়ার তুলনামূলক বিচার ও জিজ্ঞাসায় আমার দুঃখ বা হীনম্মন্যতা নয়, বরং আত্মসম্মান বোধ ও সততার গর্ব জাগে। মানুষ হিসেবে মারিয়া ও অভিভাবক ভাইয়ের চেয়ে আমি অবশ্যই সৎ। সততার বিচারে দেশপ্রেমিক ত্যাগী অগ্রজের যোগ্য অনুজও বটে। কিন্তু মারিয়া স্বামীর সততার গর্বে তাচ্ছিল্যের ছুরি চালায় না শুধু, কার কাছে যেন শোনা ইংরেজি প্রবাদ শোনায়―অনেস্টি ইজ নাথিং বাটা ওয়ান্ট অব চান্স। কিন্তু তুমি সুযোগ থাকতেও সততার গর্ব করো কেন জানো ? কারণ ভাইদের মধ্যে দুর্বলতম পুরুষ আমি। একটা দুর্বলা গরুকে ডগমগ খেতের পাশে বেঁধে রাখো, ক্ষুধা নিয়ে শুয়ে বসে জাবর কাটবে শুধু। কিন্তু একটা ক্ষুধার্ত ষাঁড়কে কোথাও বেঁধে রাখো, দড়ি ছিঁড়ে সে চারদিকের সবুজ ফসলে মুখ লাগাবেই―‘তুমি হইলা সেই দুবলা গরু, পেটে খিদে আর চারদিকে মেলা ঘাস থাকলেও দড়ি ছিঁড়ে খাইতে জানো না। মুখে শুধু ফ্যাচফ্যাচ জাবর কাটো।’
দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর কাছে যত গালমন্দ শুনেছি, তার মধ্যে বাঁধা দুর্বল গরুর উপমাটি মনে গেঁথে আছে। মনেও পড়েছে অনেকবার। সেই যে বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে মারিয়ার সতীত্ব নিয়ে সন্দেহের কাঁটা মনে খচ করে বিঁধেছিল, সেই কাঁটা অগণিত রাতের সহবাসেও মুছে যায়নি। বরং গভীর হয়েছে। বাইরে তার সুপার মার্কেট কি আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি বেড়ানোর বাড়াবাড়ি আগ্রহ দেখেও দড়ি ছেঁড়া ষাঁড়ের বিপরীত লিঙ্গের ক্ষুধার্ত জানোয়ারও মনে হয়েছে কখনও-বা।
তবে স্বীকার করব, স্বভাব-চরিত্রে বৈপরীত্য যতই থাক, বিয়ের পর দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ফাটল কিংবা দূরত্ব বাড়ানোর বদলে স্বামীকে মেনে নিয়ে মনের মতো করে গড়ে নেওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি মারিয়া। আমাকে নিজ আদর্শের পুরুষ-মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যাংকার ভাইকে দিয়ে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থাও করেছিল। যেহেতু বিয়ের আগেই অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে শামসুলের সঙ্গে, সম্বন্ধী হবার পর সম্পর্কটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে বাসায় দাওয়াত খাইয়ে লম্বা প্রায়ই লেকচার দিয়েছে।
‘শোনো সাচ্চু, আজ তোমাকে এ সমাজের কিছু ওপেন সিক্রেট বিষয়ে উদাহরণ দিই। ফলো করতে পারলে তোমার অবস্থার পরিবর্তন হবে অবশ্যই। এর মধ্যে বুঝে গেছো নিশ্চয়ই, আমাদের ব্যাংকের চাকরিতে বাড়তি আয়ের পথ আছে দু-তিন জায়গায় পোস্টিং পেলে। এক. কেউ যদি ফরেন এক্সেঞ্জ ব্রাঞ্চে পোস্টিং নেয়, ডলার কেনা-বেচার ব্যবসায় জড়িয়ে বাড়তি কিছু আয় করতে পারে। দ্বিতীয়ত কেউ যদি লোন সেকশনে কাজের দায়িত্বে থাকে। এ ছাড়া ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্স বা পার্সোনেল বিভাগের নিয়োগ এবং বদলি-পদোন্নতির বাণিজ্যে জড়িত আছে যারা। কর্মচারী ইউনিয়নের লিডার থেকে এসব বিভাগের পিয়ন পর্যন্ত ইচ্ছে করলেই বাড়তি রোজগারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং নো-ডাউট করছে শতকরা ৯৯ জনই।’
এরপর শামসুল নিজের চাকরি-জীবনে সুযোগ সৃষ্টি ও সুযোগের সদ্ব্যব্যবহারের অভিজ্ঞতার সত্য গল্প শুনিয়েছে বোকা বোন-জামাইকে। এসব গল্পের কিছু কিছু বিয়ের আগেও মেসে একসঙ্গে থাকার সময় শুনেছিলাম। এখন তার বাসায় দাওয়াত খেয়েও বাধ্যতামূলক শুনতে হয়। দুটি ব্রাঞ্চে কেরানি ও সিনিয়র অফিসার হিসেবে পাঁচ বছর লোন সেকশনে কাজ করেছে শামসুল। তার সুফল ভোগ করছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়ার পরও। লোন সেকশনে কাজ করলে দেশের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ থাকে। এই সম্পর্ক গড়ার জন্য শামসুলকে বাড়তি কোনও ইনভেস্ট করতে হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ ক্ল্যায়েন্ট হিসেবে সম্মান করে আন্তরিকতার সঙ্গে সেবাদানের দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র। ভদ্রতা করে চা-পানও খাইয়েছে অনেককে। ব্যাংকের নিয়ম-নীতি মেনেই তাদের লোনের দরখাস্ত প্রোসেস করেছে। কিন্তু তার কাজ ও ব্যবহার দেখে নিজেদের কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারীর মতো আপন ভেবেছে অনেকে। শামসুলের কাজ ও ব্যবহারে খুশি হয়ে অনেক কাস্টমারই খুশি হয়ে চাইনিজ-ডিনারে দাওয়াত দিয়েছে। দামি প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। পকেটে জোর করে খামও ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ-বা। কথায় বলে ব্যবহারে বংশের পরিচয়। তোমার ভদ্রতা ও সিনসিয়ারিটি দেখে কেউ যদি খুশি হয়ে কিছু দেয়, তাকে কি দুর্নীতি বলে প্রমাণ করতে পারবে এন্টিকরাপশনের ঘুষখোর ইনসপেকটররা ? পারবে না, কারণ দেশ-দুনিয়া যাকে বলে মার্কেট ইকোনমি, এখন চলছে এরকম দেওয়া-নেওয়া ও লেনদেনের রীতিনীতি মেনেই। বুঝলে ?’
আমি তো বাচ্চুর জ্ঞানগর্ভ লেকচার প্রায় শুনি। কিন্তু যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে, ক্ষমতার রাজনীতি করে, তাদেরকে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা কীভাবে ম্যানেজ করে―তার কিছু দৃষ্টান্ত নামধাম দিয়ে বলেছে শামসুল। ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা নিজ মুখেই বলেছে তাকে। অতএব ‘শোনো সাচ্চু, এরকম লেনদেনের সম্পর্ক তুমি যত বাড়াতে পারবে, যতই দেবে আর নেবে, মিলাবে আর মিলিবে, সচ্ছলতা ও সংসারে সুখশান্তি অবশ্যই বাড়বে তোমার। দশ বছর আগে লোন সেকশনে কাজ করার সময় হারুন গ্রুপ অব কোম্পানির হারুন সাহেবের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়ার পর সেই সম্পর্ক এখন বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের মতো। আমার কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়ির প্রয়োজন হলে ফোন করা মাত্র গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। আর অফার দিয়ে রেখেছে, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আমি যেন তার কোম্পানির একাউন্টস বিভাগের অ্যাডভাইসার হিসেবে যোগ দিই। ব্যাংকের চেয়েও তিন/চার গুণ বেশি বেতন দেবে। আমার সুপারিশে তিন/চার জনের চাকরিও হয়েছে তার কোম্পানিতে।
শামসুল ভাই শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প বলে জীবনে সফল হওয়ার পথঘাট চেনায়নি, আমাদের ব্যাংকের পরিচিত এক ম্যানেজারকে ধরে ছোট ভগ্নিপতির লোন সেকশনে বদলির ব্যবস্থাও করেছিল। অতঃপর লোনের কাস্টমারদের ডিল না করে উপায় ছিল না আমার। প্রথম মাত্র যে আশি লক্ষ টাকা ঋণের কাজে চাইনিজ ডিনার খাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, তাও ম্যানেজার আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন বলে। এ ছাড়া লোনের কাস্টমারদের সেবাদানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পরিচয়ের গণ্ডী ও ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকে। কাজ হলে কৃতার্থ গ্রাহকদের ধন্যবাদ পাই। অফিসেও আমন্ত্রণও জানায় কেউ-বা; কিন্তু যেচে নগদ টাকার সেলামি কেউ দেয় না। মুখ ফুটে চাইতেও পারি না। ঈদের সময় ছোট বাচ্চারা সেলামির লোভে বড়দের কদমবুসি করে, আমিও মনে সেরকম প্রত্যাশা নিয়ে বিনয়ে গদগদ হই, কিন্তু মুখ ফুটে কি চাওয়া সম্ভব আমার মতো সাচ্চা মানুষের পক্ষে ?
আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে শামসুল ভাই হেসে একদিন উপদেশ দেয়, ‘শোনো সাচ্চু, না কাঁদলে মাও সন্তানকে দুধ দেয় না। তোমাকেও সেরকম কাঁদতে হবে। আমি এক পার্টির সামনে কীভাবে কেঁদেছিলাম বলি। লোনের চেক হ্যান্ডঅভারের আগে বলেছিলাম―ভাই, আপনারা ব্যবসায়ী মানুষ, সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে ব্যাংক থেকে মেলা ঋণ পান। কিন্তু আমরা ছোট চাকরিজীবী মানুষ, আপনাদের মতো সম্পত্তি নেই। স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য জরুরি পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার। সেই টাকা ঋণ দেওয়ারও কেউ নেই। বলেন কীভাবে বাঁচব আমরা ?’ এইটুকু অভিনয়ের পুরস্কার হিসেবে ঋণের চেক পাওয়ার আগেই পঞ্চাশ হাজার টাকা জোর করে পকেটে দিয়েছিল। ভদ্রতা করে আপত্তি করলে অবশ্য বলেছিল, ‘সময়মতো না হয় শোধ করবেন।’ সেই সুসময় অবশ্য আসেনি, ঋণগ্রহীতা বখশিস দাতাও সে কথা মনে রাখেননি।
সম্বন্ধী ভাইয়ের এই বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলাম আমি দশ কোটি টাকা ঋণের কাস্টমারটির ক্ষেত্রে। লোকটা এসেছে হেড অফিসের এক ডিজিএম-এর টেলিফোন সুপারিশ-সূত্র ধরে। যেহেতু তার কোম্পানির একাউন্ট ও কারখানা মিরপুর এলাকায়, লোনটা আমাদের শাখার মাধ্যমে চায় সে। আমি তখন মিরপুর-১০ ব্রাঞ্চেই লোন সেকশনে ছিলাম। হেড অফিসের পরিচিতি ডিজিএম ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়েছে। ম্যানেজার আমাকে তার কক্ষে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এরপর আবেদন ও কাগজপত্র প্রসেসিং, ঋণের বিপরীতে সম্পদের মূল্যায়ন, ব্যাংকের নিজস্ব আইনজীবীর মতামত সংগ্রহ, রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সম্পত্তি ব্যাংকের নামে মর্টগেজ রাখা ইত্যাদি কাজ আমাকেই সব প্রসেস করতে হবে। অতএব শিল্পপতি ওয়ারেস আলি ম্যানেজারের বদলে সরাসরি আমার টেবিলেও বসেন। কাজের অগ্রগতি জানতে আমাকে ফোনও করেন মাঝে মাঝে। লোন শাখায় কাজ করায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কোম্পানির মালিক-ম্যানেজারের সঙ্গে চেনা-পরিচয় হয়েছে। ওরাও ঋণসংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে ফোন করে, কিন্তু আমি নিজের স্বার্থ হাসিলে কাউকেই কাজে লাগাতে পারি না। টের পাই, এসব কাজে আমার সম্বন্ধী ভাই ও মারিয়ারও সহজাত যে জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে, তা জন্মগতভাবে আমার মধ্যে নেই। ভাগ্য ভালো, না বলতেই দশ কোটির টাকার ক্লায়েন্ট একদিন অফিসে লাঞ্চ পিরিয়ডে এসে শাখার নিকটবর্তী এক ভালো রেস্টুরেন্টে বসিয়ে আমাকে ঘুষ খাওয়ানোর মতো হেভি লাঞ্চের অর্ডার দেয়। আমি মারিয়াকে ক্যানসার রোগী বানিয়ে নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা বলব ভাবি। কিন্তু এত বড় মিথ্যে বললে আল্লাহ স্ত্রীর সত্যই ক্যান্সার দিয়ে আমার লাখ লাখ টাকা খরচ করাবে না―তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আশ্চর্য, আমি কিছু বলার আগেই ওয়ারেস স্যার সরাসরি বলেন, ‘লোনটা এ মাসেই স্যাংকশন করায় দিলে আমি ওয়ান পার্সেন্ট আপনাদেরকে দেব। ম্যানেজারকে বলেছি কিন্তু। প্রথম কিস্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ।’
আমি ভিতরে চমকে উঠি, ওয়ান পারসেন্ট মানে ১০ লক্ষ টাকা। এই কেসটার সঙ্গে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জড়িত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে আমি সব কিছু করছি। ফাইলপত্র প্রসেসিং ছাড়াও ব্যাংকের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ, তার মত সংগ্রহ ও রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে পার্টির সম্পত্তি ব্যাংকের নামে মর্টগেজ রাখা―সবকিছুতেই জড়িত থাকব আমি। আমি ছাড়াও শাখার তিন জন কমবেশি। ম্যানেজার পার্সেনটেজের বিষয়ে আমাকে কিছুই বলেনি। তার মানে কি দশ লাখ সে একলাই খেতে চায় ? আন্তরিক আপ্যায়ন ও আশ্বাস পেয়ে কাস্টমারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি সরাসরি ম্যানেজারকে গিয়ে বিষয়টা বলি। ম্যানেজার নিচু কণ্ঠে আমাকে জানায়, ‘হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি। আমাকে আরও বলেছে, হেড অফিস ছাড়াই আমাদের ব্রাঞ্চেই এই ওয়ান পার্সেন্ট দেবে। আমরা তো হেড অফিসের অ্যাপ্রুভাল নিয়েই কিস্তি ছাড়ব। তারপরও আপনি দেখেন, কোনও ফাঁকফোকরে বিপদের আশঙ্কা আছে কি না। আর অফিসে কাউকে বুঝতে দেবেন না।’
এর আগে এ ধরনের কোটিপতি-শিল্পপতির সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্কে নিজেকে জড়াইনি। বড় ভাই বাচ্চু যেহেতু এই শ্রেণির মানুষকে লুটেরা লুম্পেন বুর্জোয়া এমনকি হারামজাদা বলেও গালমন্দ করে, মেহনতি শ্রমিক-মজুরদের শত্রু ভাবে, আমিও তার রাজনীতি না-বুঝেও সেরকমই ভাবতাম। কিন্তু দশ লাখ টাকার মুলো ঝুলিয়ে দেয়ার পর, নিজেকেও চোর-ডাকাত-দুর্নীতিবাজ শনাক্ত করতে পারি না। লোকটা যদি ভুয়া সম্পত্তি দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেয়, ঋণ নিয়ে নিয়ম মতো পরিশোধ না করে, আমি দায়ী হব কেন ? হুকুমের চাকর আমি, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনেকেই। তাছাড়া ফাইল প্রসেসিং কাজ শুরুর আগে আমি তো তাকে কোনও শর্ত দিইনি। লোকটাই প্রচলিত নিয়ম মেনেই যেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওয়ান পার্সেন্ট সেধেছে। দশের অর্ধেক পাঁচ লাখ যদি আমি পাই, তাতে কাঁধের ফেরেশতাও হয়তো আমার পাপের ঘরে নাম্বার বসানোর যুক্তি পাবে না। দশ কোটির ওয়ান পাসের্ন্টের ভাগ পাওয়ার লোভে আমি নিজেকে এসব যুক্তি দিয়েছিলাম।
এ ঘটনার সাত বছর পর, ব্যাংকের ঋণখেলাপি নিয়ে দেশে তোলপাড় সমালোচনা শুরু হওয়ায় দশ কোটি টাকার ঋণ খেলাপির কেস নিয়ে ম্যানেজার ও আমার নামে বিভাগীয় মামলা শুরু হয়েছে। কারণ ভুয়া সম্পত্তি দেখিয়ে ঋণ নিয়েছিল লোকটা। শুধু আমাদের ব্যাংকে নয়, অন্য আরও কয়েকটি ব্যাংকে সরকারের ক্ষমতাবান লোকজনকে ধরে শত কোটি টাকা লোন করেছিল সে। আমাদের ব্যাংকের ঋণের মাত্র দুই লাখ টাকা ঋণ শোধ করে কিস্তির সমস্ত টাকা তুলে সে তার দেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে সপরিবার কানাডা পালিয়েছে। সেখানেই বাড়ি-ফ্ল্যাট কিনে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। এরপর সেই শিল্পপতির কাছে টাকা আদায়ের পথ না পেয়ে প্রধান আসামি হয়েছি ব্যাংকের ম্যানেজার এবং আমি। ঋণের পক্ষে অভিমতদাতা আইনজীবী ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকেও সপরিবারে মারার ষড়যন্ত্র করছে। এই ভয়েই যে শুধু আমার আঙ্গুল নয়, দেহ-আত্মাসহ গোটা জগৎসংসার কাঁপতে শুরু করেছে, তাতে নিজের কোনও সন্দেহ নেই।
বড়ভাই বাচ্চুকে বিভাগীয় মামলার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত লেখা কাগজ দিতে গিয়ে আমি ঘটনাটি বলে অকপটে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করি। সে সরাসরি জানতে চায়, ‘শেষ পর্যন্ত দশ লাখের কত পেয়েছিলি তুই ? ম্যানেজার কত দিয়েছিল তোকে ?’
আমি মারিয়াকে বলেছিলাম মাত্র দুলাখ। কিন্তু বাচ্চু ভাইকে পাঁচ লাখের কথাই কবুল করি। সেই টাকার ভাগ প্রেজেন্টেশন আকারে তার সংসারেও এসেছিল কিছু। বাড়িতে এক বোনের বিয়েতেও কাজে লেগেছে। সর্বশেষ আব্বার মৃত্যুর পর তার কুলখানি ও কবরটা পাকা করতেও সেই টাকার দান কিছুটা কাজে লেগেছে। কিন্তু ঘুষের টাকায় এসব মহৎ কাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের অপরাধবোধ আড়াল করতে চাই না। বরং হাতের আঙ্গুলটা দেখিয়ে তাকে বলি, ‘এখন বুঝতে পারলি তো কী ভয়ে আর টেনশনে আঙ্গুলসহ আমার গোটা অন্তরাত্মা কাঁপছে। বাসায় মারিয়া, এমন কি সুমিও খুব ভয় করছে। চাকরি গেলে তারা ঢাকায় থাকবে কী করে ? মারিয়ার ভাই শামসুল আমাদের ব্যাংকের এক ডিজিএমকে ধরেছে। লাখ দুয়েক টাকা ঘুষ পেলে নাকি চাকরিটা সে রক্ষা করে দিতে পারে। মারিয়া তাই বায়না ধরেছে, বাড়ির সম্পত্তির ভাগ বিক্রি করে টাকাটা জোগাড় করতে।’
বাচ্চু ভাই মাথা নেড়ে বলে, ‘বুঝতে পারছি। আসলে ক্ষমতাসীন অনেকে লিডার ও তাদের প্যাট্রন বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি। ব্যাংকের টাকা লুটপাট করে ক্ষমতাসীন অনেক নেতা ইংল্যান্ড-আমেরিকা-কানাডায় লাক্সারিয়াস বাড়ি কিনেছে। ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়ছে। মিডিয়ায় বিশেষ করে বিরোধীদল এটাকে বড় ইস্যু করে সংসদে গরম বিতর্ক করছে। এখন সরকারকে তো কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। রাঘব-বোয়ালের তো কিছু হবে না। তোদের কেসের দশ কোটির কেসটায় চুনোপুঁটিদের বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে সরকার দেখাতে চায়, তারা ঋণখেলাপির টাকা আদায়ে তৎপর হয়েছে। যা হোক, তোর এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি আমাদের পরিচিতি নেতাকে বলেছি, সে তার আত্মীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে তোর বিষয়টা নিয়ে আলাপও করেছে। পার্টিকুলারস তাকে দিয়ে আসব, চেয়ারম্যান তোর চাকরি রক্ষার চেষ্টা অবশ্যই করবে। আর চাকরি যদি চলেও যায়, অত ভয় পাওয়ার কী আছে ? দু ভাই গ্রামে গিয়ে আমরা নতুন করে কৃষিকাজ শুরু করব।’
আব্বার মৃত্যুর পর, বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে সে আমাদের দশ ভাইবোনের বৈধ অভিভাবক। আব্বা তাকে একসময় অঘোষিত ত্যাজ্যপুত্র করলেও, বাস্তবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করায় এ ব্যাপারে তার দায়টাও যেন বেড়েছে। আব্বার মৃত্যুর পর একসঙ্গেই বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। আমার চেয়েও ডুকরে কেঁদেছিল সে। তার কান্নাকে মোটেও লোকদেখানো কান্না মনে হয়নি। আমি বাচ্চু ভাইয়ের কথায় বেশি আশ্বস্ত হই। সান্ত্বনা পেয়ে কম্প রোগটাও কিছুটা কমে যেন।
১৩.
আমার হাত-কাঁপা শারীরিক দুর্বলতা যে ব্যাংকের কাজের চাপ কিংবা চাকরি হারানো ভয়ের ফসল নয়, বরং দুরারোগ্য পার্কিনসন ব্যাধির লক্ষণ, অফিসে বিভাগীয় মামলা চলাকালীন মোটেও বুঝতে পারিনি। বোঝা গেল বিভাগীয় মামলার রায় বেরুনোর পর।
নানামুখী চেষ্টায় চাকরিটা রক্ষা পেয়েছে আমার। বিভাগীয় মামলার রায়ে লঘু দণ্ড পেয়েছি। পরবর্তী পাঁচ বছরে পদোন্নতি এবং তিনটি ইনিক্রমেন্ট বন্ধ থাকবে। চাকরি তথা বেতন-পেনশন-গ্রাচ্যুইটি হারানোর ভয় ছাড়াও দশ কোটি টাকার একটা বড় অংশ আমাকে শোধ করতে হবে ভেবেই ভয় পেয়েছিলাম বেশি। ছয় মাস পর ভয়মুক্ত হওয়ায় মাথার দুর্বিষহ বিরাট বোঝা নেমে গেল যেন। চাকরিটা গেলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এখন অন্তত স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ঢাকায় জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারব। মারিয়া খুশিতে আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায়ের জন্য মসজিদে মিলাদ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করে। যারা আমার চাকরি রক্ষায় চেষ্টা করেছে, তাদেরকেও দাওয়াত করে খাওয়াতে হবে। বিশেষ করে আমাদের দুজনেরই অভিভাবক দুই অগ্রজকে।
কিন্তু লঘু শাস্তির পরিণামে পাঁচ বছর আয় বাড়বে না এক টাকাও। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পর মেয়ের শিক্ষাব্যয় এবং বাজারে জিনিসপত্রের দাম বল্গাহীন বেড়েই চলেছে। চলব কীভাবে ? বেতনের বাইরে বাড়তি আয়ের সুযোগ-সুবিধা তো বন্ধ হয়েছে অনেক আগেই। নতুন করে তেমন সুযোগ খোঁজার সাহস নেই। যোগ্যতাও নেই।
মারিয়া সংসার চালাবার সমস্যা দেখালে সাহস দিয়ে বলে, ‘আল্লাহই সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাবা যেহেতু মারা গেছে তোমার, সব ভাইদের মতো পৈতৃক সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে তুমিও। এতদিন চাকরি করে বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোন, এমনকি ঢাকায় বড় ভাইয়ের পরিবারকেও সাহায্য করে গেছ। বাবার মৃত্যুর পর গ্রামে তোমার ছোটভাই বাবলু সবকিছু দেখভালের নামে একাই লুটেপুটে খাচ্ছে। বড় ভাইও বলেছে, গ্রামে গিয়ে ভাগাভাগির ব্যবস্থা করবে। গ্রামের সম্পত্তির ভাগ পেলে ঢাকায় আমাদের চালডাল কিনতে হবে না। উল্টো ভাগের জমির আবাদ বেচে প্রতি মৌসুমেই যে বাড়তি টাকা আসবে, তা দিয়েই ঢাকায় সুন্দর চলে যাবে আমাদের।
তাছাড়া মারিয়া প্রতি মাসে নিজেও কিছু রোজগার করতে পারবে। প্রমাণ ইতিমধ্যে দিয়েছে সে। মহল্লায় বাচ্চাদের পড়ানো, বিশেষ করে আরবি শেখানোর টিচার হয়েছে। মহল্লার কেজি স্কুলের এক ইংরেজির টিচার, ইংলিশে অনার্স-মাস্টার্স ডেইজি আপার সঙ্গে খাতির হয়েছে তার। তারা চেষ্টা করছে কয়েকজন মিলে মহল্লায় একটা কোচিং সেন্টার চালু করবে। তাতে মারিয়াও টিচার ও ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত হবে। পার্টটাইম কাজ করে মাসে আট-দশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে সে। একটামাত্র সন্তান আমাদের। ইন্টারমিডিয়েটে বেশ ভালো রেজাল্ট করে এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। মেয়ে পাস করে বেরুলে অবশ্যই চাকরি করবে। দেখেশুনে তাকে একটা বিয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যতে মেয়ে-জামাই চালাবে তাদের। সুমি নিজেও মাকে এমন কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছে। পেনশন-গ্রাচুইটির টাকা এবং প্রয়োজনে গ্রামের কিছ সম্পত্তি বেচে ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারলে শেষ বয়সে আর কোনও চিন্তা থাকবে আমাদের ?
বিভাগীয় মামলায় চাকরি রক্ষার খুশি তো ছিলই, তার ওপর বৃদ্ধ বয়সে নিরাপদ-নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের সুখস্বপ্নে মারিয়া রাতে স্বামীকে শরিক করতে শারীরিকভাবেও একাত্ম হতে চায় যেন। কিন্তু আমি মারিয়ার খুশি ও স্বপ্নে শরিক হতে পারি না কেন ? শারীরিক মিলনে মারিয়ার সম্মতি বা কামনার লক্ষণ ভালোভাবেই বুঝি। আগে খুশিমনে মারিয়াও দিয়েছে বহুবার। কিন্তু আজ শুধু হাতের কাঁপুনি নয়, পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। মারিয়ার হাতের ভার ও পাশে তার উপস্থিতিও যেন সহ্য হচ্ছে না।
‘আমার হাতের কাঁপুনিটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। শরীরটাও কেমন যেন অবশ দুর্বল অবশ লাগছে।’
মারিয়া আদুরে স্পর্শ দিয়ে আমার শরীর পরীক্ষা করে। গোপন হতাশা নিয়েও সহানুভূতি দেখায়, ‘আগামী সপ্তাহে একজন বড় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব তোমাকে। চাকরিটা যখন টিকে গেছে, তোমার কাঁপুনি ব্যারাম আর দুর্বলতাও ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কী এমন বয়স হয়েছে আমাদের বলো তো। ষাট-সত্তুর পেরিয়ে গেলেও মানুষ এখন জোয়ানদের মতো চলতে চায়।’
লোন সেকশনের উপরি আয়ের মতো হাতের কাঁপনও যে চাকরিতে বড় হুমকি হয়ে উঠবে, ম্যানেজারের ধমক খেয়ে বুঝতে পারি প্রথম। ব্যাংক তখনও পুরোপুরি ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কের আওতায় আসেনি। দু-একটা সেকশনে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে সবেমাত্র। স্বাক্ষরদান ছাড়াও হাতেকলমে লেখার কাজ বিস্তর। লিখতে গেলে হাঁত কাঁপে। লেখা এমনকি স্বাক্ষরও গড়বড় হয়ে যেতে চায়। একবার ভাউচারে ওয়ান লাখকে সেভেন লাখ লেখায় ম্যানেজারের কাছে ধরা পড়ে ভুলটা আঙ্গুল-কাঁপা ব্যামোর উপর চাপাতে গিয়ে আরও একটা ভুল করলাম। ম্যানেজার সতর্ক করলেন, ‘এরকম অসুখ নিয়ে ব্যাংকের চাকুরি করবেন কীভাবে শাফায়েত সাব ? কিছুদিন আগে বিভাগীয় মামলায় অল্পের জন্য চাকরি রক্ষা হলো। এরকম ভুল করতে থাকলে শোকজ করতে বাধ্য হব।’
অফিসের এক কলিগই প্রথম সন্দেহ করল, তার এক আত্মীয়ের মধ্যে এরকম কাঁপুনি রোগ আছে। পার্কিনসন এ রোগের নাম। একবার হলে ভালো হয় না। বাড়তেই থাকে। আপনার তো অনেকদিন ধরেই হাত কাঁপছে। কলিগটি তার আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নাম-ঠিকানাও জোগাড় করে দিল।
পরের সপ্তাহেই অ্যাপোয়েন্ট করে নিউরোলজির প্রফেসর আব্দুল মান্নানের চেম্বারে গেলাম। সঙ্গে যথারীতি মারিয়া। তারিখটা ছিল, আগেও বলেছি―১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর। কম্পনের ধরন, উৎস ও বিস্তার বুঝতে প্রফেসর ডাক্তার আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।
কতদিন ধরে কাঁপছে ? কখন বাড়ে, বা কমে ? আঙ্গুল আর এই হাত ছাড়াও অন্য কোনও অঙ্গ এরকম কাঁপে কি না ? এই প্রশ্নের জবাবে মারিয়াকে একরাতে যে অঙ্গ কাঁপার কথা বলেছিলাম, সেই স্মৃতি মনে করে হাসি পায়। কিন্তু মারিয়া পাশে, তার সামনে ডাক্তারের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করা যায় না। তবু বলি, ‘সব সময় না কাঁপলেও অনেক সময় রাগ হলে উত্তেজিত হলে শরীর কাঁপে। আবার ধরেন প্রাকৃতিক চাপেও কাঁপে কোনও অঙ্গ।’
‘কাঁপুনি ছাড়াও শরীরের কোনও অঙ্গ বা গোটা শরীর কখনও রিজিড হয় ? মানে অসার বা অচল বোধ হয় কি ?’
‘ঘুমালে তো স্থির হয়ে থাকে। বসে চুপচাপ থাকলেও তো স্থির থাকে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।’
‘সেই স্থিরতার কথা বলছি না। ধরুন উঠতে চাইছেন বা বসতে চাইছেন, কিন্তু শরীর আপনার কথা শুনছে না। এই আঙ্গুলটাকে যেমন আপনি থামতে বললেও ওটা থামছে না। নিজের শরীরও, শরীরের কোনও অঙ্গ আপনার কন্ট্রোলে নেই, এরকম মনে হয় ?’
মারিয়াই আমার গোপন দুর্বলতা ধরিয়ে দিতে চায়, ‘হ্যাঁ স্যার, শরীরটা ওর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে। ডিম-দুধ এত খাওয়াই, কিন্তু সামান্য পরিশ্রমের কাজও করতে পারে না। কীরকম অবশ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।’
প্রফেসরের বুঝি আমার স্ত্রীকে তেমন পছন্দ হয় না, হেসে জবাব দেয়, ‘আপনি জবাব দিচ্ছেন কেন ? ওনাকেই বলতে দেন।’
আমিও মারিয়াকে সমর্থন করে বলি, ‘হ্যাঁ স্যার, শরীরটা বেশ দুর্বল, আগের মতো কিছু করতে পারি না। আগে তো বেশ হাসিখুশি ছিলাম, এখন খুব হতাশ লাগে। কামেকাজেও তেমন উৎসাহ পাই না।’
‘হ্যালোসিনেশন আছে ? মানে চোখের বিভ্রম, যা নেই, তেমন কিছু দেখেন কি না ?’
‘মানে স্বপ্ন-কল্পনার কথা বলছেন স্যার ?’
‘দিবাস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যাই বলুন, মানে চোখের সামনে স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলেন, অথচ বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। এমন হয়েছে কখনও ?’
‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার চরিত্রে খুব ছোটবেলা থেকেই আছে স্যার। ছোটবেলায় ভূতের ভয় পেতাম তো। রাতে একবার কলাগাছের পাতা নড়তে দেখ ভূত দেখে ভয়ে চিৎকার করেছিলাম। ঘুমিয়ে স্বপ্নে অনেক কিছু তো দেখি, তাছাড়াও চোখ বুজেও অনেক সময় তৃতীয় চোখে এমন কিছু দেখি, চোখ খুলতেই নেই হয়ে যায়।’
বিরক্ত হওয়ার বদলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে জানতে চায়, ‘এর মধ্যে এরকম কিছু ভুল দেখেছেন, মনে আছে ?’
‘ব্যাপারটাকে কি ভুল বা মিথ্যে বলা যাবে স্যার ? মানে স্মৃতিতে যা ঘটেছে কল্পনায় যা দেখি, তার তো একটা বাস্তব ভিত আছে। যেমন অনেক সময় আমার স্ত্রী পাশে না থাকলেও তাকে পষ্ট দেখতে পাই। বাস্তবে তিনি আছেন বলেই তো দেখি।’
ডাক্তার কি আমার রসবোধ নাকি যুক্তিজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হন ? বড় ডাক্তার তো, মনটাও নিশ্চয়ই বড়। পাড়ার ডাক্তারটির মতো বিরক্ত হন না। হেসে বলেন, ‘স্মৃতি-কল্পনার কথা বলছি না। দেখার ভুল হলে, যা নেই ভুলে সেরকম কিছু দেখলে জানাবেন। আপনার মধ্যে পার্কিনসনের সব লক্ষণ স্পষ্ট। আরও আগেই চিকিৎসা শুরু করা উচিত ছিল। যা হোক, কিছু টেস্ট দিচ্ছি, সিটি স্ক্যানও করতে হবে। তা হলে বুঝতে পারব রোগটা কতদূর ছড়িয়েছে। আর ওষুধ কিন্তু সারা জীবনই খেতে হবে।’
‘তার মানে কি থরহরি কম্প ভালো হবে না স্যার ? পার্কিনসন তো আমাদের বংশে কারও ছিল বলে জানি না। চেনাজানা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও দেখি না। এ রোগের জীবাণু আসল কোত্থেকে ?’
ডাক্তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেন, ‘এটা ঠিক ভাইরাল রোগ না। আপনার আসলে ব্রেনের স্নায়ুকোষ ধ্বংস হচ্ছে। ব্রেনে এক ধরনের ক্যামিকেলস ডোপোমিন তৈরি করে, যা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। আপনার ব্রেইন সেই ক্যামিকেলও তৈরি করতে পারছে না। কিছু ব্রেইন সেল মরে গেছে। চিকিৎসা না নিলে আরও যাবে। পার্কিনসনের সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। বংশগত কারণে হতে পারে, আবার কোনও বাহ্যিক বা ইন্টারন্যাল আঘাতের কারণেও হতে পারে। তবে ভয়ের কিছু নেই। সারা বিশ্বে ৮৫ লক্ষ মানুষ এই রোগ নিয়েও জীবনযাপন করছে। বক্সিং-এর হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলিকে দেখেননি ? তার এই রোগ ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার-এর এই রোগ হয়েছে। অনেক বিখ্যাত মানুষ দুরারোগ্য এই রোগ নিয়ে বেঁচেছিলেন। খোদ আমেরিকায় কয়েক লক্ষ পার্কিনসন রোগী আছে। বাংলাদেশে সঠিক পরিসংখ্যান হয়নি, তবে আমিও নিয়মিত কয়েক শত রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি। নিয়মিত এই ওষুধগুলো খান, এক মাস পর টেস্ট রিপোর্টসহ আসুন, তখন আপনার পিডি কতোটা কন্ট্রোলে আসবে কি আসবে না, বলতে পারব।’
ডাক্তারের কথা শুনে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি―এমন ভয়ঙ্কর রোগের মধ্যে ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, আলসার এসব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ছিল। কিন্তু এমন কম্পরোগ নিয়ে বাঁচতে হবে বাকি জীবন ? ভাবিনি কখনও। ব্রেনের নার্ভগুলো ধ্বংস হয়েছে এবং হয়ে চলেছে আসলে কী কারণে ? ডাক্তার না জানলেও কারণটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবেই। নইলে কাঁপুনি বাড়তে থাকবে নিঃসন্দেহে।
বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলির একাধিক চ্যাম্পিয়ন শিরোপা রক্ষার লড়াই টিভিতে দেখেছি। জিমি কার্টারকেও দেখেছি। হায়, আমেরিকার মতো ধনী দেশের এত এত টাকার মালিক হয়েও তারা এই রোগ থেকে মুক্তি পায় না! আমার চিকিৎসা করে কী লাভ ? ডাক্তারের কথা শুনে আমার চকিতে মনে পড়েছিল, চেনাজানা গণ্ডীর বাইরে একটি মানুষকে দেখার স্মৃতি। ঢাকায় বিয়ের পরপরই যে মহল্লায় বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম, সেই মহল্লায় অফিস আসার পথে গলিতে একাধিকবার দেখেছিলাম লোকটাকে। পুরো হাত ও মাথাও কাঁপছে তার। ওই অবস্থাতেই হাঁটছিল। ছোট বাচ্চা হলে দুষ্টুমি করছে কিংবা পাগল ভেবে হয়তো ধমক দিতাম। কিন্তু লোকটা ওরকম করছে কেন ? তৃতীয় দিনে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেসও করেছিলাম, ‘কী ভাই, হাত-মুখ খিঁচতেছেন কেন ? অ্যাটাক করবেন নাকি ?’
স্বজন-বন্ধুরা আমাকে রসিক বলে। হাসিঠাট্টা করা স্বভাব বা অভ্যাস হয়ে গেছে। কারণ হাস্যরস জিনিসটা উপভোগ করতে বেশ লাগে, লোক হাসাতে পারলেও আনন্দ হয়। অচেনা মানুষটাকেও ঠাট্টা করেই বলেছিলাম কথাটা। জবাবে সে চোখ পাকিয়ে আমাকে দেখেছিল শুধু। কোনও কথা বলেনি। অচেনা সেই লোকটাও যে আমার স্মৃতিতে অবচেতনে এমন জাগরুক ছিল, প্রথম তাকে মনে পড়ল নিজের পিডি শনাক্ত হওয়ার পর। ভূমিকম্পের সিনেমার মতো এই লোকটার কথাও আমার অনেকবার মনে পড়বে, সত্যি সত্যি সে যে আমাকে অ্যাটাক করবে―স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন। আমার ঠাট্টা শুনে অভিশাপ দিয়েছিল নাকি ?
নিজে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রাথমিক অবস্থায়, তা প্রায় বছর দুয়েক রোগটার নামও জানতাম না। অসুখ নিয়েই অফিস-সংসারের দায়িত্ব পালন করে গেছি। কিন্তু সব টেস্ট রিপোর্ট দেখে ও ওষুধ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া জেনে পিডির বিস্তার নিয়ে ডাক্তারও কিছুটা শঙ্কিত, বললেন, ‘আগে চিকিৎসা শুরু করলে এতটা খারাপ অবস্থা হতো না। ঔষধের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। প্রেসারটাও স্বাভাবিক রাখতে হবে। বাকি জীবন যেহেতু এই রোগ নিয়েই বাঁচতে হবে, অযথা টেনশন করবেন না। পার্কিনসন সহসা মৃত্যুর কারণ হয় না। তাছাড়া আপনার মেমোরি লস হয়নি তেমন। এ রোগ নিয়েও ভালো থাকার চেষ্টা করুন।’
১৪.
নিয়মিত ওসুধ খেয়ে হাতের কম্পমান দশা মনে হয় কিছুটা কমে, কিন্তু পুরোপুরি থামে না। আবার অনেক সময় মনে হয় আগের চেয়েও বেড়েছে। তাছাড়া ডাক্তার যদি বলে, অসুখ সারবে না, তখন সাহসী লোকও নিশ্চয়ই নার্ভাস হবে। আর আমি তো ছোটবেলা থেকেই ভীতু টাইপের, জন্মগতভাবে নার্ভস দুর্বল কি না কে জানে। ডাক্তার বলার পর দিনেরাতে হাজারবার মনে করতে বাধ্য হই, দুরারোগ্য পার্কিনসন রোগী আমি। কম্পিত আঙ্গুল দেখলে মনে হয়, কাঁপতে কাঁপতেই মরে যাব। তবে ভাবনা-চিন্তা যেহেতু নি®কম্প (নাকি পার্কিনসন আক্রান্ত হওয়ার পর এগুলোও কাঁপতে শুরু করেছে ?), ঠান্ডা মাথায় স্মৃতি-কল্পনা তথা অতীত-ভবিষ্যতের বহু চিত্র স্থির ও উজ্জ্বল দেখতে পাই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগটার প্রকোপ বাড়বে। তার মানে থরহরি কম্প নিয়েই যখন বাকি জীবন কাটাতে হবে, হাসিমুখে এটাকে মেনে নেয়াই তো ভালো। রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ত্রীসঙ্গমের মতো সুখ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হব। তাই বলে পৃথিবীতে বয়স্ক বা রোগাক্রান্ত মানুষের জন্য আনন্দ লাভের রাস্তা, বেঁচেবর্তে থাকার নানারকম সুখভোগের উপায় কি সব বন্ধ হয়ে যাবে ? আমার তো সুন্দর মেয়ে, প্রাকৃতিক দৃশ্য, চাঁদনি রাতের শোভা দেখতেও ভালো লাগে। খাওয়ার রুচি আছে, পছন্দের খাবার ধীরেসুস্থে খেয়ে, থাল চেটেও বেশ তৃপ্তি পাই। সুস্থ-সবল নারী-পুরুষ যখন ভালোবাসাবাসি করার সময় থরহরি কম্প কিংবা লম্ফঝম্ফ করে, তা দেখতেও ভালো লাগে। মানুষের হাসিমুখ দেখতে এবং নিজে হেসেও আনন্দ পাই। কাজেই পার্কিনসনের সঙ্গে সহবাস করেও শুধু ভয় নয়, আনন্দ পাওয়ারও চেষ্টা করে দেখি না কেন ? বিষয়টা নিয়ে দার্শনিক বাচ্চুর সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হবে।
ক্রমে দুরারোগ্য পিডিমে সহজভাবে মেনে নিতে থাকি। কেউ জানতে চাইলে হাসিমুখে, হাতকাঁপানো দেখিয়ে অনেকটা গর্বের সঙ্গে বলি, ইচ্ছে করেও কাউকে ভয় দেখাতে পাগলামো করি, লেকচার দেই, ‘পিডি হয়েছে আমার। পিডি মানে বুঝলেন না ? এটা অনেকটা পাদের মতো প্রাকৃতিক। হঠাৎ বেরিয়ে গেলে ঠেকানো যায় না। তেমনি কাঁপতে শুরু করলে আর থামানো যায় না। তবে পার্কিনসন ডিজিজ পাদের মতো দুর্গন্ধ ছড়ায় না। বরং শরীর কাঁপতে কাঁপতে ব্রেইন অনেক ভালো কথা মনে করিয়ে দেয়। পৃথিবীতে কোনও কিছু ধ্রুব সত্য নয়। সব কিছু অস্থির। সবকিছু কাঁপছে, পাল্টে যাচ্ছে―এটাই ধ্রুব সত্য। কাঁপতে কাঁপতে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। এই রোগটা না হলে জীবন-জগতের অনেক গোপন সত্য বুঝতে পেতাম না। তা নেবেন নাকি এই রোগের জীবাণু ? আমাকে একটু ছুঁয়ে দেন, ছু-মন্তর আপনারও হয়ে যাবে।’
ট্রেনে দেখা এক ক্যানভাসারের স্মৃতি স্মরণ করে আমিও পিডির পক্ষে ক্যানভাস করি। কেউ ভয়ে দূরে সরে যায়। কেউবা ঠাট্টা-মস্করা ভেবে হাসে। হা করে তাকিয়ে দেখে অনেকে। ঘনিষ্ঠ অনেকেরই ধারণা, রোগটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাতেও গোলমাল বাড়ছে। কথাবার্তায় লাগামছাড়া ভাব বাড়ছে। আসলে ইচ্ছে করেও করি এসব। দুরারোগ্য বলেই বোধহয় ওষুধ খেতেও ভুল হয় প্রায়ই। স্থির মস্তিষ্কেও ভাবি, কী হবে এত টাকার ওসুধ খেয়ে ? যৌবনের অটল তেজ আর আনন্দ আর তো ফিরবে না। ভিতরের হতাশা কিংবা ওসুধ ঠিকমতো কাজ না করায়, সময় গড়াতে থাকলে পিডির প্রকোপও বাড়তে থাকে। হাতের কাঁপুনি বিরামহীন প্রবল হওয়া ছাড়াও শরীরের বিশেষ অঙ্গের নিশ্চলতা বা রিজিডিটি নিজের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে। আগে ভাড়া-বাসার বাথরুমে হাইকমোড ছিল না। প্যানে বসে কাজ সারতে হতো। কিন্তু একদিন বসতে গিয়ে দেখি, বসতে অনেক সময় লাগছে এবং উঠতেও। শেষে একদিন উঠতে না পেরে মারিয়াকে ডাকতে হয়েছে। কিন্তু সে আসবে কীভাবে ? দরজায় যে ভিতর থেকে সিটকিনি। বেশ ভয় পেয়েছিল মারিয়া। সে যাত্রায় দরজা ভাঙতে হয়নি। এপাশ-ওপাশ কাত করে শেষ পর্যন্ত নিজেই উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। কিন্তু অনেক সময় চেষ্টা করেও পারি না। বাইরের কারও সাহায্য লাগে।
হাতের কাঁপুনি ছাড়াও রিজিডিটি শরীরের স্বাভাবিক চলমানতায় বাধা সৃষ্টি করায়, ঘরের বাইরে স্বাভাবিক চলাফেরাটাও সমস্যা হয়ে ওঠে। সেই যে একদা মাথা-মুখ কাঁপিয়ে অচেনা একজনকে রাস্তা হাঁটতে দেখে চমকে উঠেছিলাম, নিজের পিডি তার চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে ওঠে যেন। রাস্তায় অনেক সময় রিকশায় উঠতে-নামতে এবং অফিসে চেয়ারে ওঠা-বসা, বাথরুমে যাওয়া এবং রুটিনকাজে ক্রমে আকস্মিক রিজিডিটি সমস্যা হয়ে ওঠে। এ সমস্যা সমাধানে অন্যের সাহায্য জরুরি। অচল গাড়িকে স্টার্ট নেওয়ার জন্য অনেক সময় পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ইঞ্জিন চালু হয়, আমারও তেমনি অন্যের মৃদু ধাক্কা প্রয়োজন। একদা ঋণখেলাপিকে সহযোগিতা করার বিষয়টি চাকরির ক্ষেত্রে যে সংকট হয়ে উঠেছিল, দুরারোগ্য পিডি তার চেয়েও ক্রমে বড় হুমকি হয়ে উঠতে থাকে। চাকরিটা রক্ষার জন্য ডান হাতের বদলে বাম হাতেও লেখার প্রাকটিস করছি। রোগটাকে আমি স্বাভাবিকভাবে নিতে চাইলেও সহকর্মী, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহজভাবে নিতে পারে না। এরকম অসুস্থতা নিয়ে আমি চাকরি করব কীভাবে ?
ম্যানেজার একদিন রুমে ডেকে নিয়ে এন্তার সহানুভূতি দেখিয়ে আসল কথাটা জানায়, ‘শাফায়েত সাহেব, বোঝেনই তো অল্প স্টাফ নিয়ে আমাকে ব্রাঞ্চ চালাতে হয়। এখানে একজনের কাজ আরেকজনকে ওভার টাইম দিয়েও করানো সম্ভব নয়। আপনি হেড অফিসে বলে কয়ে নিজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা সুবিধাজনক কোনও শাখায় বদলি হন। তাহলে আমাকে আর আপনাকে নিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট করতে হবে না।’
শুধু স্বাভাবিক চলাফেরা ও অফিসের রুটিন কাজের ক্ষেত্রে নয়, আমার মুখের ভঙ্গি ও কথা বলার মধ্যেও কণ্ঠস্বরের আড়ষ্টতায় সবাই বুঝে যায়, ‘সুস্থ লোক নই আমি। কখনও-বা ইচ্ছে করেও রোগটাকে বেশি বেশি প্রকাশ করি। যেহেতু ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দয়া ও সহকর্মীদের সাহায্য-সহানুভূতির উপর ভর করেই চাকরিটা আমাকে রক্ষা করতে হবে, ভিখিরির মতো দয়া-সহানুভূতি আদায় না করে অসুখটা দেখিয়ে হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে করাই তো ভালো। এ কাজে আমি তাদের হাতের কাঁপুনি ছাড়াও মুখের অস্বাভাবিকতা ও কণ্ঠস্বরের নাটকীয়তা দিয়েও কিছুটা আমোদ দেয়ার চেষ্টা করি। পাগলকে দেখে যেমন ছোট ছেলেরা মজা পায়, ভয়ও পায় কেউবা, সেইরকম বুড়োধাড়ি ভদ্রলোকরাও আমাকে দেখে।
ম্যানেজারের নেগেটিভ রিপোর্টের কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়। শরীরের কাঁপুনিও প্রবল হয়। কণ্ঠ বিকৃত করে বলি, ‘আমার বিরুদ্ধে নেগেটিভ রিপোর্ট! আপনার ওয়াইফ যদি পিওর হাউস ওয়াইফ হয়, একমাত্র মেয়ে যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এবং এই চাকরি ছাড়া ঢাকায় থাকার জন্য আপনার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে চট করে চাকরি ছাড়তে পারবেন ? একটা কানা-খোঁড়া মানুষকে একা রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারবেন ? আমাকেও আপনাদের মানবিকতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে অন্তত আরও বছর তিনেক চাকরিটা করে যেতে দিন স্যার।’
ম্যানেজারটা আসলেও ভালো মানুষ। সহানুভূতি দেখাতে চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসিয়ে দেয়, ‘অবশ্যই আপনার প্রতি সবাই সিম্প্যাথেটিক। এ জন্যই হেড অফিসের কন্ট্রোলিং বসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করার কথা বলছিলাম। ভুল বুঝবেন না প্লিজ।’
‘ঠিক আছে আপনার উপদেশ শিরোধার্য করলাম স্যার। তবে যতদিন তেমন ব্যবস্থা না হয়, একটু ঠেলেঠুলে চালিয়ে নেবেন স্যার।’
বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড এড়াতে মারিয়া তাদের আত্মীয় সম্পর্কিত এক ডিজিএম ব্যাংকারকে ধরে অনেক ছোটাছুটি করেছিল। সেই ডিজিএমকে ধরে হেড অফিসের জিএম-এর সঙ্গে অ্যাপোয়েন্ট করে আমাকে নিয়ে গেল একদিন তার বাসায়। জিএমকেও কাঁপুনি দেখিয়ে বেশ মজা দেওয়ার চেষ্টা করি, ‘স্যার বিদেশে শুনি প্রতিবন্ধীদের জন্য সর্বত্র বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। আমার পার্কিনসনকেও প্রতিবন্ধীর কাতারে ফেলে আপনাকে আমার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতেই হবে। আরও কমপক্ষে যাতে তিন/চারটা বছর চাকরিটা করে ফুল পেনশন-বেনিফিটসহ রিটায়ারমেন্টে যেতে পারি। ডাক্তার বলেছে কাঁপব, কিন্তু মরব না সহজে। ব্রেনে এই দিকের কিছু সেল ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু মেমোরি, বুদ্ধি-বিবেক সবই টনটনে, একদম ঠিক আছে স্যার। আমার বড় ভাই বলে, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মোটরনিউরন ডিজিজ নিয়ে চেয়ারে শুয়ে-বসে যেমন বিজ্ঞান সাধনা করেছেন, আমার মেমোরি ও ব্রেইনও সেরকম চোখা আছে। ডান হাতের বদলে বাম হাতেও লেখার প্রাকটিস করছি। আপনার দয়া পেলে চাকরিটা আরও কয়েক বছর করে যেতে পারব স্যার।’
জিএম সদয় হন। অচিরে ব্যাংকের সব শাখাই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। আমার হাতে লেখা যেহেতু অসুবিধা, কম্পিউটার চালানোটা ভালোভাবে শিখে নিতে পারলে কাজের সুবিধা হবে। যে শাখাতে থাকি, আমাকে অফিসে একটা কম্পিউটার দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি। আর মিরপুর এলাকার যে শাখায় বদলি করলে বাসা থেকে যাতায়াত সহজ হবে, তেমন শাখায় বদলির ব্যবস্থাও করবেন। তাঁর নিজের চাকরিটা যেহেতু আরও তিন বছর আছে, এই সময়টাও আমার জন্য এটুকু করার চেষ্টা করবেন অবশ্যই।’
জিএম-এর আশ্বাসবাণী এবং তার স্ত্রীর পরিবেশিত চা-পানি খেয়ে মারিয়া বিজয়গর্বে আমাকে নিয়ে যখন বাসায় ফেরে, রিকশায় নতুন চাকরি প্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে বলি, ‘পার্কিনসন হয়েছে বলে দুনিয়ায় অনেক ভালো জিনিসও দেখতে পাচ্ছি। তুমিও যে আমাকে এত ভালোবাসো, আমাকে বাঁচানোর এত চেষ্টা করছ, এই থরহরি কম্প না হলে বুঝতাম না গো মারি। আমাকে কিন্তু এভাবে রিকশায় অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। ছুটির পর বাসাতেও ফেরত আনতে হবে। কারণ রিকশায় যদি হঠাৎ শরীর অচল হয়ে যায়, তোমার পিঠে চড়ে নামতে পারব।
ভেবেছিলাম চাকরি রক্ষার খুশিতে আমার পিঠে ওঠার আহ্লাদ দেখে মারিয়া খুশি হবে, কিন্তু ধমকের গলায় বলে, ‘আমার পিঠে উঠতে হবে না, কারও হাত ধরতেও হবে না। নিজের পায়ে যাতে আগের মতো গটগট করে চলতে পারো, তার ব্যবস্থা করব আমি। এক ফকিরের সন্ধান পেয়েছি, সে এরকম কাঁপা রোগীকে তেলমালিশ দিয়ে সাতদিনে সুস্থ করেছে। তার কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। জিএম স্যারের ওয়াইফও বলল, নিউরোলজির স্পেশালিস্ট ডাক্তার-ফাক্তারের চেয়ে আল্লাহর রহমতে এরকম চিকিৎসায় ভালো হয়ে যেতে পারি।’
যদিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত করেছে, দুরারোগ্য পার্কিনসন ব্যাধি থেকে এ জীবনে আর চিরমুক্তি ঘটবে না; কিন্তু কিন্তু মহান আল্লাহ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে―এ বিশ্বাস আমার ষোলো আনা। হাত প্রবল কাঁপতে থাকলেও, আজ অসুস্থ স্বামীর পাশে মারিয়ার উপস্থিতি ও ভালোবাসপূর্ণ আশ্বাসে মনটা শান্ত হয়, সুস্থ জীবনের আশাও জেগে ওঠে।
সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ




