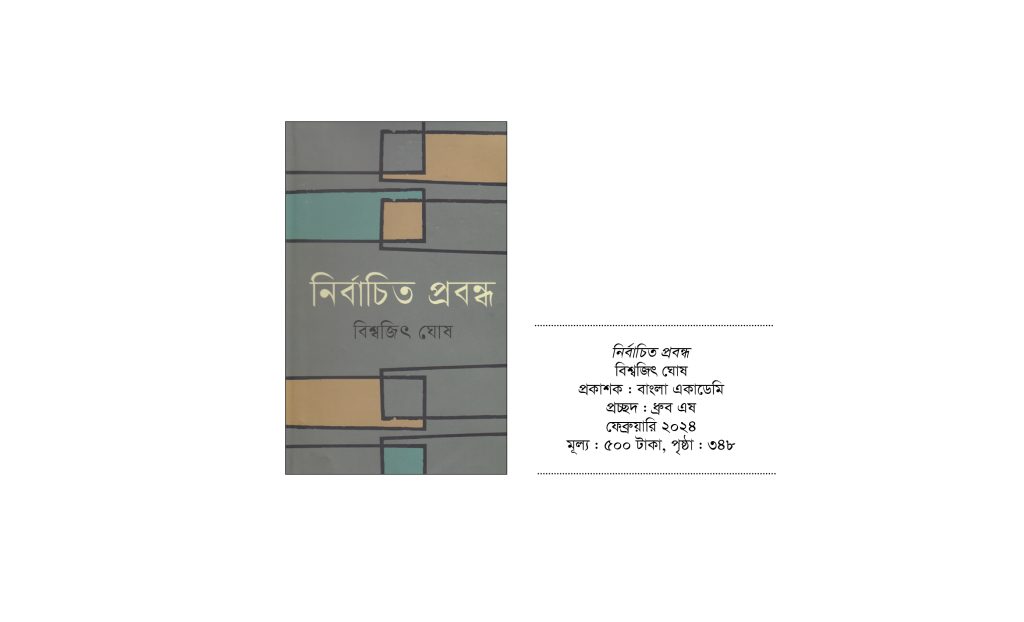
বাংলা একাডেমি থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বজিৎ ঘোষ রচিত নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০২৪)। মোট আঠারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। ফ্ল্যাপে গ্রন্থটির উপজীব্য বিষয়ে বলা হয়েছে : ‘আলোচ্য গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ সামাজিক- রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ, নৈঃসঙ্গ্যচেতনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,… ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমর সেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুর রাহমান প্রমুখ লেখকের সৃষ্টিসম্ভার ও সাধনা সম্পর্কে আলোকসম্পাতী বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।’

আঠারোটি প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম এরকম : নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ : পটভূমি ঢাকা, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল, জীবনানন্দ : চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প, উত্তর- ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য, অনন্বয়চেতনা ও শামসুর রাহমানের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনিবেশিত বাংলা, তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন, বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর কাব্যনাটক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের নাটক ও মঞ্চনাটক, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বিদ্যাসাগর : দ্বন্দ্ব ও সহযোগ, জেন্ডারচেতনা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম দেখেই অনুধাবন করা সম্ভব গ্রন্থটির উপজীব্য ও মৌল চারিত্র্য।
গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম ‘নৈঃসঙ্গ্যচেতনা’। আধুনিক মানুষের মনোলোকে একান্তে বিরাজ করে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্ব। মানবচিত্তের এই একান্ততা মানুষের চিন্তাকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি তা প্রভাবিত করে শিল্প-সাহিত্য- চিত্রকলাকে। ‘নৈঃসঙ্গ্যচেতনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বজিৎ ঘোষ আধুনিক মানবচিত্তে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও তার স্বরূপলক্ষণ চমৎকার ভাষ্যে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধটিতে বিশ্বজিৎ ঘোষের বিস্তৃত পাঠের পরিচয় সচেতন পাঠকের নজরে পড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস।
বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গ, বিশেষত ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা সৃষ্টিতে এই সংগঠন পালন করেছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ : পটভূমি ঢাকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত সংগঠন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড বিশদভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল’ শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও এই আন্দোলন শিল্প-সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে।
জীবনানন্দ দাশ চিত্রকল্পের কবি―চিত্রলতার কবি। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দের শিল্প-সার্থকতা বিশ্লেষিত হয়েছে ‘জীবনানন্দ : চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প’ শীর্ষক প্রবন্ধে। অনন্বয়চেতনার তাত্ত্বিক পটভূমি এবং এই চেতনা শামসুর রাহমানের কবিতায় কীভাবে শিল্পিতা পেয়েছে তা আলোচিত হয়েছে ‘অনন্বয়চেতনা ও শামসুর রাহমানের কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে। শামসুর রাহমানের কবিতায় অনন্বয়চেতনা ব্যাখ্যা করে বিশ্বজিৎ ঘোষ অন্তিম মন্তব্য করেছেন : ‘সমর-উত্তরকালে নিখিল নাস্তির প্রভাবে শামসুর রাহমানের কবিতায় লেগেছে নিঃসঙ্গতার সুর।… শামসুর রাহমানের কাছে নিঃসঙ্গতা পলায়ন নয়, বরং তা সৃষ্টিশীলতার অনন্ত আধার। শামসুর রাহমানের কবিতায় নিঃসঙ্গতার বহুমাত্রিক প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে সেখানে আছে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির অবারিত আকুলতা।’
কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্য বিষয়েও আলোচ্য গ্রন্থে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে। এর মধ্যে ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনিবেশিত বাংলা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তাউদ্রেককারী প্রবন্ধ। উত্তর- ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্বজিৎ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপর সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এই প্রবন্ধে বিশ্বজিৎ ঘোষের ব্যাখ্যা একেবারে মৌলিক এবং নতুন চিন্তা-উদ্রেককারী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ব্যাখ্যাকল্পে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন : ‘ছোটগাল্পিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনের নানামাত্রিক ছবি, একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে কোথায় আছে দ্রোহের উৎস তার সন্ধানও। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোয় কীভাবে ঘটবে মানুষের আত্মিক মুক্তি তারও অভ্রান্ত ইঙ্গিত আছে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্পে।’ অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক চমৎকার বিশ্লেষণে উপস্থাপিত হচ্ছে।
নাটক বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থে মোট তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধত্রয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষের নাট্য-বিষয়ক চিন্তার পরিচয় বিধৃত। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের আলোকে নজরুলসাহিত্যে আলোক সপ্তাত আলোচ্য গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। নজরুলসাহিত্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রবণতা ব্যাখ্যা-সূত্রে বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন : ‘আত্মসমীক্ষা ও প্রতিরোধী চেতনাই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী চেতনা, কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্ক নির্ণয়, প্রতিবাদী নারীভাবনা, মিথ-পুরাণের নবনির্মাণ, নিম্নবর্গ সম্পর্কে সচেতনতা, স্বদেশপ্রেম ও দেশজ প্রকৃতিলগ্নতা এবং আপসহীন দ্রোহচেতনাই হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রধান দিক। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষিত হলে, ভিন্ন এক নজরুলকে আবিষ্কার করা সম্ভব।’
ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে মুক্তচিন্তক ও দ্রোহী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বন্দ্ব ও সহযোগের কথা বিশ্লেষিত হয়েছে ‘ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বিদ্যাসাগর : দ্বন্দ্ব ও সহযোগ’ শীর্ষক প্রবন্ধে।
বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ‘জেন্ডারচেতনা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য’ শীর্ষক রচনা। এই প্রবন্ধে পুরুষতান্ত্রিকতার পরাক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কীভাবে সংক্রমিত হয়েছে তা চমৎকার ভাষ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। মূল বক্তব্যকে তুলে ধরতে গিয়ে ডক্টর ঘোষ নারীবাদী তত্ত্ব সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আমাদের বিবেচনায় এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করলে ভালো হয়।
বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে বিশ্বজিৎ ঘোষের আধুনিক সমালোচনা তত্ত্ব, তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এবং মৌলিক চিন্তার সংশ্লেষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রাবন্ধিক ভাষা চিত্ত-মনোহর, অন্তর্ভেদী এবং গীতলতা-ঋদ্ধ। গদ্যও যে সুখপাঠ্য হতে পারে, বিশ্বজিৎ ঘোষের এ গ্রন্থ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নির্ভুল বাক্যে কীভাবে বই লিখতে হয়, তা বোঝার জন্য গ্রন্থটি কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য বলে আমরা মনে করি।
লেখক : প্রাবন্ধিক




