
কিরণরেখার পত্রপুট বেরিয়েছে গত বইমেলায়। বাংলাদেশের খবরের সাহিত্যপাতায় গ্রন্থটির কিছু তরঙ্গ প্রকাশিত হলে আমাদের নজর কেড়েছিল। শহীদ ইকবাল প্রাবন্ধিক পরিচয়ে প্রায় তিন দশক ধরে মেধা ও স্বকীয়তার ছাপ রেখে চলেছেন। ২০১২ সালে বিশ শতকের রূপকথার নায়কেরা আখ্যান দিয়ে তাঁকে কথাসাহিত্যিক হিসেবে পাই। কথাসাহিত্য―ভাষা ও ঘটনা বিন্যাসের কারুকাজে। মানদণ্ডে। নইলে বিশ শতকের রূপকথার নায়কেরা এবং কিরণরেখার পত্রপুট গ্রন্থদুটিকে আমরা হয়তো স্রেফ স্মৃতি-আখ্যানের তকমা দেগে দিতাম। কারণ দুটি আখ্যানই তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। সময়ের জলছবিও ভারী স্পষ্ট। যার ভেতর দিয়ে সমাজ, রাজনীতি, বৃহৎ অর্থে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরই ভাষ্য পাই। বিশ শতকের রূপকথার নায়কেরায় সত্তর-আশির জীবন ধরা দেয়। কিরণরেখার পত্রপুটে নব্বুইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ান তিনি। গ্রন্থটি হাতে নিয়ে একটি জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াই, বর্ণিত সময়টা কি খুব পরিবর্তমান ? হয়তো। তবে, গতিটা ঠিক আজকের সঙ্গে দূরপাল্লা জোগায় না। বরং অনেকটাই কচ্ছপগতির। বুঝে, শুনে, সময় নিয়ে এগুনো। মানিয়ে নেওয়া। স্বাধীন রাষ্ট্রের গড়ে ওঠা, শেখ মুজিব হত্যা, ব্যর্থ অভ্যুত্থান, জিয়া হত্যা, রাজনৈতিক টালমাটাল, এরশাদের স্বৈরশাসন; জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখিয়েরা বদলের একটা রেখা দেখান বটে! কিন্তু―চোখা দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে, তাতে সমাজের মূল স্রোতটা একেবারে গড়হাজির থাকে। দ্বন্দ্বটার চিহ্নিতকরণও স্পষ্ট নয়। বরং তা রাজা-উজির মারা, আর চর দখলের রোমাঞ্চ-গল্প হয়ে দাঁড়ায়। মফস্সলের মানুষের কথা, মিটিং-মিছিল। বিদ্যা-ব্যবস্থার ওঠাপড়া, স্থাবর জীবন ঝেড়ে কেন্দ্রের দিকে মানুষের হাঁটা―সেসব প্রায় অকহতব্যই থেকে যায়। অবিশ্যি, এই সময়টাতেই হলওয়েল-হান্টার, নওরোজি-গোখলেদের ঐ শোকেসের সাজানো ইতিহাস বাতিল করে রণজিৎ গুহরা নতুন কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের এখানে তাতে সাড়া পাই না । বরং ইতিহাস উতরিয়ে কথাসাহিত্যে বহুমাত্রায় প্রান্তের কথা হাজির থাকে। শহীদ ইকবালও সেই জীবনেরই আখ্যান করেন। উত্তরবঙ্গ; যমুনা দ্বারা বিচ্ছিন্ন এক জনপদ। ঢাকায় আসতে দু-তিন দিন খোয়া যায়। তবু রংপুরের এক মফস্সলে রাজনীতির কেন্দ্রীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে। সংস্কৃতিরও নয় কী ? সেটাই বরং ব্যাপক। কালচারাল হেজিমনি―শহুরে জীবনেবোধের শ্রেষ্ঠত্ব, সেটিও নানা অর্থে মাথা তোলে। দাপট দেখায়। বড় শহরে পড়তে যাওয়া, যাত্রার বদলে টেলিভিশন। এঁটেল মাটি দিয়ে মাথা ঘষা গ্রামে শ্যাম্পুর আমদানি এই বার্তাই দেয় যে―এখানে যে জীবনবোধ চালিত, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। আসছে। তাকে বরণ করতে হবে। এই বদল ও অভিঘাতের ভেতর দিয়ে ব্যক্তির বেড়ে ওঠা। মননে-দেহে ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়া। এই কিরণরেখার পত্রপুট। এবারে আখ্যানের ভেতরটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।
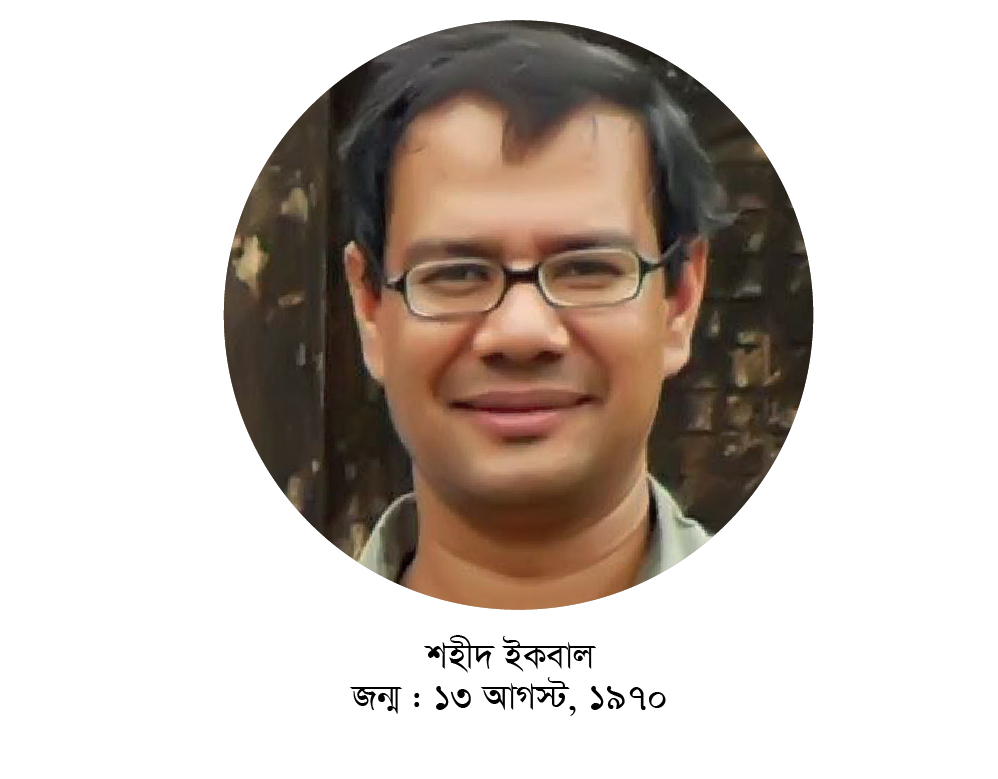
মণি সিংহের জীবনে আমরা ডিক্লাসড হওয়ার আখ্যান শুনতাম। ফিউডাল থেকে কৃষকের কাতারে নেমে আসা। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের জীবনে তা ঘটে না, বরং উল্টোটা হয়। শ্রেণির অবনমন নয়। উত্তরণ। অবিশ্যি এই নির্ধারিত মানদণ্ড নিয়েও তর্ক করা চলে। তবে―সে জায়গা এ নয়। শহীদ ইকবালের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয়টা ঘটে। তবে তিনি শেকড়টা ভোলেন না। তাই খুব স্পষ্ট করে বলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তার শ্রেণি উত্থান ঘটলেও, কথাসাহিত্যে তিনি ঐ শ্রেণিচ্যুত মানুষদেরই কথাকার। গলাটা যেন সরদার ফজলুল করিমের মতো স্পষ্ট খাকড়ানি দেয়―‘আমি কৃষকের পোলা।’ এই আখ্যানেও কিন্তু একেবারে হয়ে ওঠা, পলিশড মানুষ মেলে না। মফস্সলের সমাজটাই তেমন ছিল না যে। সবাই যেন―খণ্ড খণ্ড অস্তিত্ব। গ্রামগুলো তখনও আঁধারে ঢাকা। এ বস্তু দৃষ্টিতেই―ইলেকট্রিসিটি পৌঁছেনি। হারিকেনের আলো। হ্যাজাগের লাইট মাঝেমধ্যে রোশনাই দেয়। আর্থিক স্থিতিটাও কমজোরি। সংসারে বিশ টাকা খরচা হয়ে গেলেই মাথায় হাত পড়ে কর্তার। বিদ্যা-ব্যবস্থার হালটাও নাজুক। সেখানে মানুষ তৈরি হবার মনোযোগ আছে বটে, কিন্তু উপকরণের বড় অভাব। অভাব ভিশনেরও। তবু বিএসসি স্যারের মতো মানুষেরা থাকেন। যারা ভার্সিটি শব্দটা কানে পৌঁছে দেন। সেখানেই বা ক’জন পৌঁছাতে পারে ? তবে চেষ্টাটা থাকে, তারই কথার আড়ালে। ‘দাবা খেলাটা জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রে!’ এর পেছনে হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাসও লুকিয়ে! ভারতীয় দর্শনের মূলটা কেন্দ্রে। জীবনের দুঃখ, দৈন্য থেকে মুক্তির পিপাসা। গ্রিক দর্শন তো উল্টো কথা বলেছিল। মুক্তি নয়, জীবনের রহস্যকে বোঝা। গ্রাম থেকে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে শহরে যাওয়া, দেখব কৈশোর উত্তীর্ণ বালকের মধ্যে আর্থিক স্থিতির প্রশ্নের সঙ্গে, কোথাও হয়তো জীবন-রহস্য বোঝাটাও লুকিয়ে থাকে। এই জীবন বয়ে চলার গল্পেই পলিটিক্সটা প্রতীকী মাজেজা নেয়। লেখক দারুণ শব্দবন্ধ দিয়ে দেখান―পঁচাত্তরের পর শেখ মুজিব কী করে ব্রাত্য হয়ে যান; ‘নির্বাসিত বঙ্গবন্ধু’। প্রেসিডেন্ট শব্দটা জানান দেয় অন্য এক শাসক এসেছেন। দেয়াললিখন―‘জননেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দাও―জা ই।’ জামাতের এন্ট্রি নেওয়া। জাহানার ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক-দালাল নিপাতের আন্দোলনে সেই কালির পোচ মুছে যায়। চলতি রাজনীতির ওঠাপড়া। প্রতীকী বয়ান। তাতে কিন্তু পুষ্টি জোগাবার মতো ব্যাপারও দেখি। ঐ শহর ফেরা, শিক্ষিত মানুষের দ্বারা। ব্রেজনেভ, সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন শব্দগুলো পৌঁছে। গ্রন্থাগারের বিদেশি বই। চারপাশ দিয়ে ব্যক্তির তৈরি হওয়া। কেবল মনে নয়, দেহেও। সে সংবাদও এ আখ্যানে গোপন নেই। সামাজিক ট্যাবু ও জৈবজ্ঞানের অভাবে সেটিও কি সেই সমাজে স্বাভাবিক পথে যেতে দেয় ? হয়তো নয়। গ্রামের বালকদের গাছঘেরা অরণ্যে যাওয়া থেকে, সূর্যসেন হলের চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম; সকলেই সে প্রশ্নটা আমাদের মাথায় দেগে দেন। কিন্তু নিজেকে আবিষ্কারের এই ঘটনাগুলোও বুঝি বহু প্রজন্মেরই এক চেনা নস্টালজিয়া। তাই সেগুলো খুব চোখে ঠেকে না।
তর্ক নেই যে―এ দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানটা মুখ্যত সামাজিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক নানা অর্থে। এই যে গ্রাম থেকে ছাত্র গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় নিজের ‘হা’-এর মধ্যে খুব সহজেই তাকে আত্তীকৃত করে নেয়। সেটি অবশ্য সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবেও। দুতিন দিনের পথ। ফেরি-বাসে পাড়ি দিয়ে ঢাকা গিয়ে পৌঁছা। লেখকের জন্য রোমাঞ্চকর। স্বপ্নটা তাড়িয়ে নিয়ে চলে। সেখানে বিএসসি স্যার যেমন আছেন তেমনি আছেন পিতাও। আছে ফজলুল হক হলের ২১৪ রুম। ক্লান্তি, ক্ষুধা, চিন্তা, জীবনের জটিলতা। এ যেন নিজেকেই আবিষ্কার করা। খোলস ছেড়ে নতুন হওয়া। মারলিন রেস্তোরা, সূর্য সেন হলের ডাইনিং। জিনিসপত্তর হারিয়ে ফেলা। জীবনের নির্মম অভিঘাত। তবু সে ফিরবে না। বরং, স্বপ্নটা চলে, চলতি পথে সংগ্রাম তাকে আরও সমৃদ্ধি দেয়। অভিযোজিত হবার আকাক্সক্ষা থাকে। সিনেমা দেখতে যাওয়া, মহিলা সমিতিতে থিয়েটার দেখা। আর বোমা-বারুদের গন্ধ মাখা এরশাদবিরোধী আন্দোলন। দিপালী-জাফর-জয়নালের কথা। রাজনীতি এখানে নতুন করে জাত চেনায়। দাদাভাইয়ের দাপট তখনও অটুট। তারই চেলারা বসেছেন বিরোধী দলে। যে ছেলেটি পঞ্চাশের দশকে ফজলুল হক হলে এসে দাবা খেলে, বই পড়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল―ক দশক পেরিয়ে তখনও প্রাসঙ্গিক তিনি ক্যাম্পাসে; রহস্যপুরুষ। হাওয়ায় ভাসে―গ্রাম থেকে আসা এই ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎও তারই হাতে। রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু ক্ষমতারও তো পতন ঘটে। তাই মতিঝিলের সুসজ্জিত আল্লাওয়ালা বিল্ডিং হাপিস হয়ে যায় এক রাতে। লেখককেও ফিরতে হয় : ‘রাউফুন বসুনিয়া, পুরনো ঢাকার লালকুঠি ভবন, কার্জন হলের চিপা গলি আর প্রান্তর জোড়া রমনা’ ফেলে। তবে জীবন থামে না। বরং লেখকেরই বলা ‘চক-চক-চকালু’ খেলার মতো তাকে এগিয়ে যেতে দেখি সীমাহীন পথে। ব্যক্তি গড়ার রূপরেখায় ছেদ নামে। তবে এটি মানতে হবে, এ আমাদেরও গড়ে ওঠার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার নিমন্ত্রণ রাখে। হয়তো মিলেও যায় অনেক বোধ-অভিজ্ঞতা-অভিযাত্রা। কিরণরেখার পত্রপুটে মুগ্ধতা জাগায় ভাষা। টুকরা টুকরা বাক্যে। শব্দে-উপমায়। ঘটনা-বর্ণনার এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখি এখানে। যা পাঠককে অনায়াসে আখ্যানের অংশ করে নেয়।
লেখক : প্রাবন্ধিক




