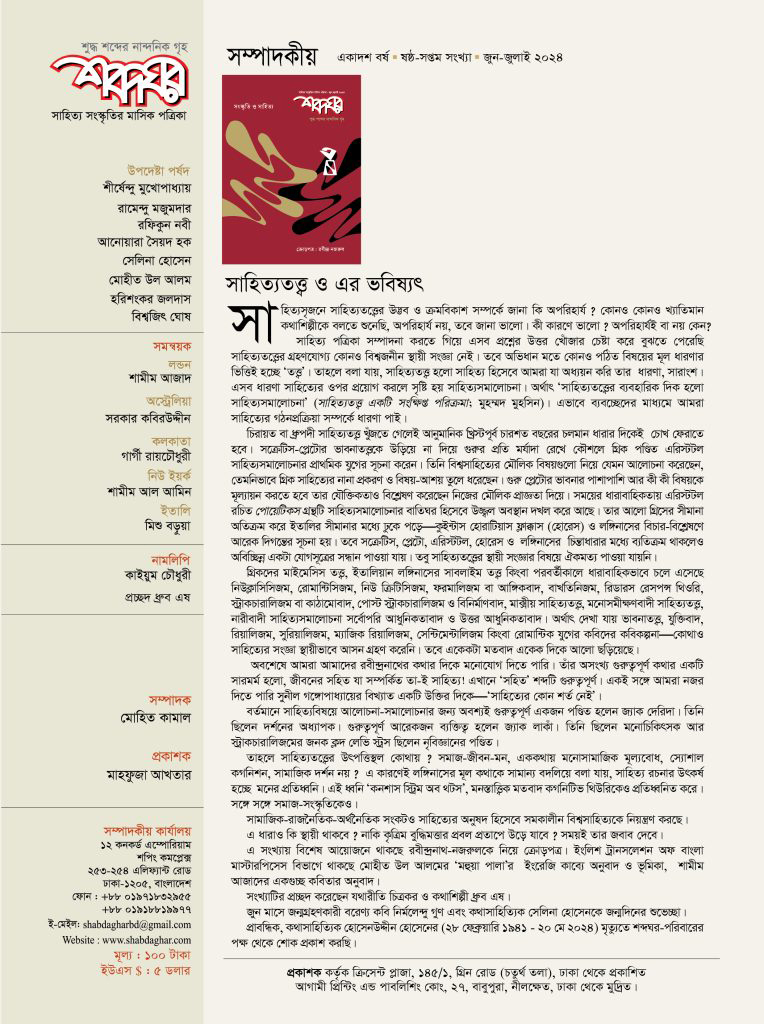
শব্দঘর : সম্পাদকীয়
একাদশ বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা জুন-জুলাই ২০২৪
সাহিত্যতত্ত্ব ও এর ভবিষ্যৎ
সাহিত্যসৃজনে সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা কি অপরিহার্য ? কোনও কোনও খ্যাতিমান কথাশিল্পীকে বলতে শুনেছি, অপরিহার্য নয়, তবে জানা ভালো। কী কারণে ভালো ? অপরিহার্যই বা নয় কেন?
সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে বুঝতে পেরেছি সাহিত্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য কোনও বিশ্বজনীন স্থায়ী সংজ্ঞা নেই। তবে অভিধান মতে কোনও পঠিত বিষয়ের মূল ধারণার ভিত্তিই হচ্ছে ‘তত্ত্ব’। তাহলে বলা যায়, সাহিত্যতত্ত্ব হলো সাহিত্য হিসেবে আমরা যা অধ্যয়ন করি তার ধারণা, সারাংশ। এসব ধারণা সাহিত্যের ওপর প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হয় সাহিত্যসমালোচনা। অর্থাৎ ‘সাহিত্যতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক হলো সাহিত্যসমালোচনা’ (সাহিত্যতত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা; মুহম্মদ মুহসিন)। এভাবে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে আমরা সাহিত্যের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাই।
চিরায়ত বা ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব খুঁজতে গেলেই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চারশত বছরের চলমান ধারার দিকেই চোখ ফেরাতে হবে। সক্রেটিস-প্লেটোর ভাবনাতত্ত্বকে উড়িয়ে না দিয়ে গুরুর প্রতি মর্যাদা রেখে কৌশলে গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটল সাহিত্যসমালোচনার প্রাথমিক যুগের সূচনা করেন। তিনি বিশ্বসাহিত্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনিভাবে গ্রিক সাহিত্যের নানা প্রকরণ ও বিষয়-আশয় তুলে ধরেছেন। গুরু প্লেটোর ভাবনার পাশাপাশি আর কী কী বিষয়কে মূল্যায়ন করতে হবে তার যৌক্তিকতাও বিশ্লেষণ করেছেন নিজের মৌলিক প্রাজ্ঞতা দিয়ে। সময়ের ধারাবাহিকতায় এরিস্টটল রচিত পোয়েটিকস গ্রন্থটি সাহিত্যসমালোচনার বাতিঘর হিসেবে উজ্জ্বল অবস্থান দখল করে আছে। তার আলো গ্রিসের সীমানা অতিক্রম করে ইতালির সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে—কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস (হোরেস) ও লঙ্গিনাসের বিচার-বিশ্লেষণে আরেক দিগন্তের সূচনা হয়। তবে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, হোরেস ও লঙ্গিনাসের চিন্তাধারার মধ্যে ব্যতিক্রম থাকলেও অবিচ্ছিন্ন একটা যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তবু সাহিত্যতত্ত্বের স্থায়ী সংজ্ঞার বিষয়ে ঐকমত্য পাওয়া যায়নি।
গ্রিকদের মাইমেসিস তত্ত্ব, ইতালিয়ান লঙ্গিনাসের সাবলাইম তত্ত্ব কিংবা পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে নিউক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, নিউ ক্রিটিসিজম, ফরমালিজম বা আঙ্গিকবাদ, বাখতিনিজম, রিডারস রেসপন্স থিওরি, স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদ, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ও বিনির্মাণবাদ, মাক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব, মনোসমীক্ষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা সর্বোপরি আধুনিকতাবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ। অর্থাৎ দেখা যায় ভাবনাতত্ত্ব, যুক্তিবাদ, রিয়ালিজম, সুরিয়ালিজম ম্যাজিক রিয়ালিজম, সেন্টিমেন্টালিজম কিংবা রোমান্টিক যুগের কবিদের কবিকল্পনা—কোথাও সাহিত্যের সংজ্ঞা স্থায়ীভাবে আসন গ্রহণ করেনি। তবে একেকটা মতবাদ একেক দিকে আলো ছড়িয়েছে।
অবশেষে আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথার দিকে মনোযোগ দিতে পারি। তাঁর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কথার একটি সারমর্ম হলো, জীবনের সহিত যা সম্পর্কিত তা-ই সাহিত্য! এখানে ‘সহিত’ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে আমরা নজর দিতে পারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি উক্তির দিকে—‘সাহিত্যের কোন শর্ত নেই’।
বর্তমানে সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একজন পণ্ডিত হলেন জ্যাক দেরিদা। তিনি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। গুরুত্বপূর্ণ আরেকজন ব্যক্তিত্ব হলেন জ্যাক লাকাঁ। তিনি ছিলেন মনোচিকিৎসক আর স্ট্রাকচারালিজমের জনক ক্লদ লেভি স্ট্রস ছিলেন নৃবিজ্ঞানের পণ্ডিত।
তাহলে সাহিত্যতত্ত্বের উৎপত্তিস্থল কোথায় ? অর্থাৎ সমাজ-জীবন-মন, এককথায় মনোসামাজিক মূল্যবোধ, স্যোশাল কগনিশন, সামাজিক দর্শনের ভেতর থেকে জেগে ওঠে সাহিত্যের মূল স্রোত। এ কারণেই লঙ্গিনাসের মূল কথাকে সামান্য বদলিয়ে বলা যায়, সাহিত্য রচনার উৎকর্ষ হচ্ছে মনের প্রতিধ্বনি। এই ধ্বনি ‘কনশাস স্ট্রিম অব থটস’, মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ কগনিটিভ থিউরিকেও প্রতিধ্বনিত করে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতিকেও।
সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটও সাহিত্যের অনুষদ হিসেবে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
এ ধারাও কি স্থায়ী থাকবে ? নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবল প্রতাপে উড়ে যাবে ? সময়ই তার জবাব দেবে।
এ সংখ্যায় বিশেষ আয়োজনে থাকছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে নিয়ে ক্রোড়পত্র। ইংলিশ ট্রানসলেশন অফ বাংলা মাস্টারপিসেস বিভাগে থাকছে মোহীত উল আলমের ‘মহুয়া পালা’র ইংরেজি কাব্যে অনুবাদ ও ভূমিকা, শামীম আজাদের একগুচ্ছ কবিতার অনুবাদ।
সংখ্যাটির প্রচ্ছদ করেছেন যথারীতি চিত্রকর ও কথাশিল্পী ধ্রুব এষ। জুন মাসে জন্মগ্রহণকারী বরেণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণ এবং কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক হোসেনউদ্দীন হোসেনের (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ – ২০ মে ২০২৪) মৃত্যুতে শব্দঘর-পরিবারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করছি।




