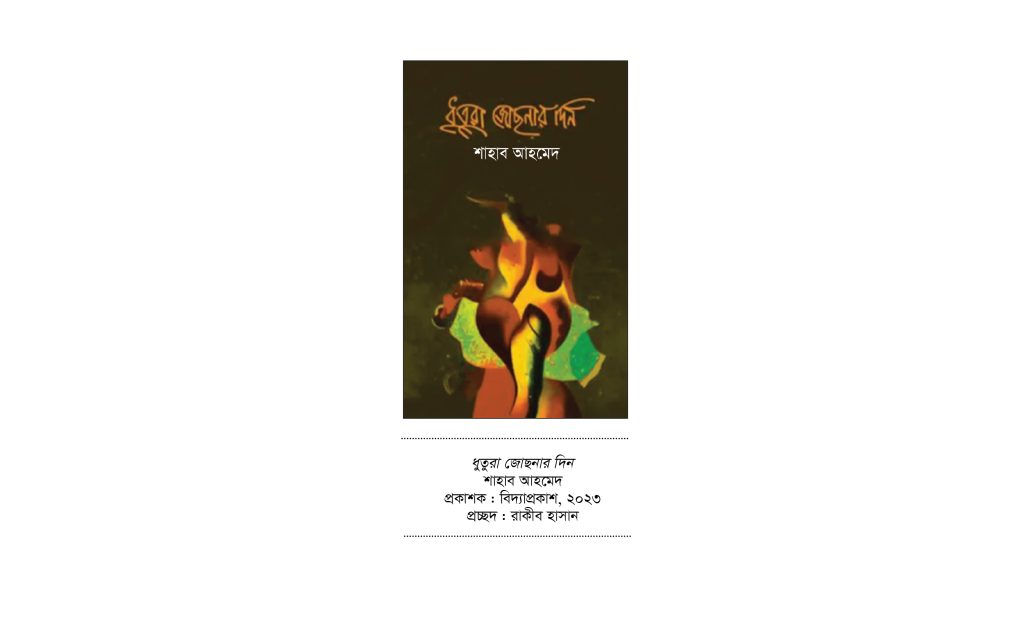
গত বছর, ২০২৩ সনে, বিদ্যাপ্রকাশ থেকে বের হয়েছিল শাহাব আহমেদের উপন্যাস ধুতুরা জোছনার দিন। সেই সময় প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও চিকিৎসক হুমায়ুন কবিরের আমন্ত্রণে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল নিউ ইয়র্কে বইটির একটি পাঠ পর্যালোচনায় অংশ নেওয়ার। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন লেখক শাহাব আহমেদ, বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী রাকীব হাসান এবং প্রকাশক মজিবর রহমান খোকা। নিচের লেখাটি সেই আলোচনায় পঠিত প্রবন্ধের একটি সংশোধিত রূপ। লেখাটিতে আমি লেখককে ‘কথক’ বলে অভিহিত করেছি; কথক কাহিনি বোনেন, বপন করেন, আবার বর্ণনাও করেন। বইটি পড়তে পড়তে আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, লেখকের লেখা কথকের কথা হয়ে আমাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল।
আপনারা অনেকেই এলিয়টের ঞযব ডধংঃব খধহফ পড়েছেন। এলিয়টের পরিত্যক্ত প্রান্তর কোনও রৈখিক পঠন নয়, সেটি পড়তে হলে যেমন চাই বিভিন্ন ভাষার অভিধান, তেমনই জ্ঞানের বিশ্বকোষ। কথকের কৈশোরের আখ্যান ধুতুরা জোছনার দিন-এর প্রতিটি বাক্যকে গড়ে তোলা হয়েছে অপরিসীম স্নেহে, আর প্রতিটি বাক্যের ভাঁজে জমা হয়েছে বিদগ্ধতা, গভীরতা। একই প্যারায় থাকবে তলস্তয়ের আনা কারেনিনা, অশ্রুকুমার শিকদারের কিল মারার গোঁসাই, মহাভারতের যুধিষ্ঠির। থাকবে নদী, থাকবে জল, থাকবে সময়। থাকবে এমন একটি বাক্য ‘কেউ কোথাও নেই, বাতাসে মাথা নাড়ছে একগুচ্ছ শ্বেতদ্রোণ ফুল, দাঁতরঙা পাতায় চিকচিক করছে বিন্দু বিন্দু শিশির এবং নিশিন্দার ঝোপে গুটি গুটি পা ফেলে হাঁটছে অপরূপ কিশোরী রোদ।’ থাকবে দেবী অদিতি মাতার কথা ? যে অদিতি অনন্ত আকাশের রূপক, যার ছিল তেত্রিশ সন্তান। নারায়ণগঞ্জের দেহপল্লীর নারীকে বিয়ে করেছিল কথকের বন্ধু, তাদের আশ্রয় দিয়েছিল কিশোর কথক। সেই নারীর মায়া-মমতায় তার মনে পড়েছিল অদিতি মাতার কথা, ডেকেছিল খালা বলে। খালাকে যদিও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি সে। যেমন রক্ষা করতে পারেনি পদ্মার হাত থেকে তার ঝাউটিয়া গ্রামকে, তাঁর জন্মভিটাকে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাই বলছেন―
‘আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে,
দরদী কে দিল ভাঙিয়া…’
এই কথকের সত্তা দর্শনের। পূর্ণতা-প্রাপ্ত বয়সে এসে বিশ্ব চরাচরের সমস্ত যুক্তি আর আকুলতা, সমস্ত বিচার-বুদ্ধি আর আবেগ, সমস্ত বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতাকে একটি কিশোরের আধারে নিমজ্জিত করে―ভবিষ্যৎ সময়ের প্রান্ত থেকে অতীতকে একটি দুরবিন দিয়ে দেখছেন, যে দুরবিন রামধনুকে তার বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট করে। তাঁর লেখনী অনুনাদ তুলছে আমার হৃদয়ে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমার―শাহাব আহমেদের নয়―দীপেন ভট্টাচার্যের দেশ-কালের বক্ররেখা। ১৯৭১ সনের টালমাটাল সময়। কথক বলেন তার বাড়িতে ডাকাত পড়ার কথা, ডাকাতের গুলিতে আহত তার পিতা বিস্তার মিয়ার কথা। মনে পড়ে যায় যমুনার সেই বিরান বিস্তীর্ণ চর অঞ্চলের এক বাড়িতে আমাদের ওপর ডাকাত পড়ার কথা। কথকের ভাষ্য ছিল যেমন―‘সঙ্গে সঙ্গে দস্যু সর্দারের গলা ভেসে আসে, ‘খবরদার, কোন মাইয়া মানুষের গায়ে হাত দিবি না।’ আমিও ঠিক এই বাক্যটি শুনেছিলাম, কিন্তু সর্দার সরে যাওয়া মাত্র ডাকাতদের অত্যাচারের বিরাম হয়নি। শোনা যায় সেই ডাকাত দলের কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর হাতে পরে নিহত হয়।
বহু বছর আগে ফরাসি লেখক মার্সেল প্রুস্ত লিখে গিয়েছিলেন, ‘যখন গভীর অতীত থেকে কোনও কিছুই আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে না, যখন আমাদের পরিচিত সবাই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়, যখন সমস্ত দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, আমরা তাদের আর খুঁজে পাই না, শুধু তখনই স্বাদ ও গন্ধ, শুধু তারাই, যাদের মনে হতে পারে খুবই পলকা, নাজুক, কিন্তু তারাই শেষাবধি রয়ে যায় মনের গভীর কোণে স্থায়ীভাবে; এক অবিনশ্বর আত্মার মতো, অন্য সমস্ত স্মৃতির ধ্বংসাবশেষের মাঝে তারা ধরে রাখে অতীতের কোনও ক্ষীণ যোগসূত্র।’ একে বলা হয় গধফবষবরহব ফব চৎড়ঁংঃ। তাঁর ‘হারিয়ে যাওয়া সময়ের খোঁজে’ বইতে প্রুস্ত লিখছিলেন যে, তাঁর মা যখন তাঁর শুশ্রুষা করতে চা-ভেজানো ম্যাডেলিন নামের মিষ্টি নরম বিস্কুট খেতে দিয়েছিলেন সেই ম্যাডেলিনের স্বাদ তাঁকে শুধু তাঁর ছোটবেলার ম্যাডেলিন খাবার স্মৃতিই মনে করাল না, সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় ভাসিয়ে তুলল অনেক হারানো স্মৃতি। এটা বলা হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না যে, ধুতুরা জোছনার দিন প্রুস্তের ম্যাডেলিন হিসেবে আমার ওপর কাজ করেছে।
নইলে কেমন করে ভোলানাথ মালোর বালকপুত্র স্বপনের মৃত্যু আমাকে মনে করিয়ে দেয় ঠিক এমনি একটি কাহিনি। বইয়ে কথক বলছেন ভোলানাথ মালোর সুন্দর ছান্দি নৌকা বানানোর কথা, পুত্র স্বপনকে সেই নৌকায় পদ্মায় নিয়ে যাবার কথা। কালবৈশাখী ওঠে, নৌকা উল্টায়, স্বপনকে গ্রাস করে পদ্মা। আমার মনে পড়ে আবার ১৯৭১-এর কথা, বংশী নদীর পারে বাঁশী গ্রামে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম কুশু সেনের বাড়িতে। বাড়ির পাশে ছিল এক জেলে পরিবার, তাদের নাম আজ মনে নেই, বংশী নদীতে ডুবেছিল তার ছয় বছরের সন্তান―সে কি বিলাপ মা আর বাবার। মনে পড়ল শেষ বিকেলের বিষণ্ন বাতাসে চিতার ছাই উড়ে যাচ্ছিল ঘূর্ণি তোলা বর্ষার বংশী নদীর ওপর দিয়ে।
কথক ‘দেবতার গ্রাস’ স্মরণ করেছেন। আমরা জানি তাতে লেখা ছিল―
রাখাল বসিয়া আছে তরী―‘পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে’। ‘তুই হেথা কেন ওরে’
মা শুধালো; সে কহিল, ‘যাইব সাগরে।’
‘যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।’
তারপর কী হয়েছে আমরা জানি―
‘মাসি’ বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
রাখাল কালচক্রের বলি। ধুতুরা জোছনার দিন এমনই একটি অমোঘ কালচক্র। মানুষ কি ইতিহাস গড়ে, নাকি ইতিহাসের ক্রীড়নক হয়ে নিজের জীবনের দর্শক হয়ে থাকে ?
অমৃতের আশায় দেবতা আর অসুরেরা মন্দার পর্বতকে ব্যবহার করে ক্ষীরসাগর মন্থন করেছিলেন। সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে লক্ষ্মী, বারুণী, কৌস্তুভ মণি, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, ঐরাবত, ধন্বন্তরী, অপ্সরাগণ। ধুতুরা জোছনার দিন হলো মন্দার পর্বত, পাঠকের অবচেতন মন হলো ক্ষীরসাগর। তাতে যেমন উঠেছে অমৃত, তেমনই উঠেছে হলাহল। হলাহল পান করে শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, কথক এটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হলাহল যদি কেউ পান না করে তো সেই বিষ কোথায় যাবে ?
তুম্বুরু ছিলেন একজন গন্ধর্ব, ঋষি কাশ্যপের পুত্র, অতি উচ্চ মানের সংগীতশিল্পী। সেই তুম্বুরুকে শাহাব আহমেদ ব্যবহার করেছেন ক্রোধের একটি উপমা হিসেবে। একটি আপাতদৃষ্টির বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথায় হঠাৎ তুম্বুরু বেজে ওঠে। এই ধারণাটি লেখক শুরুতেই দিয়ে রেখেছেন তাঁর জন্মদাত্রীর কান্নার মধ্যে দিয়ে―‘মা, মা, তুমি কান্দো কেন ? জিজ্ঞেস করি। ‘না বাবা, আমি কান্দি না―মা বলে।’ মা সর্বংসহা, বাবার মাথায় আছে তুম্বুরু। বইটির মাঝখানে এসে তুম্বুরুকে স্মরণ হয়, আপাতদৃষ্টিতে জনদরদি পিতা বিস্তার মিয়া রাতে ফিরে বাড়ির দরজা বন্ধ দেখে, ঘুমন্ত স্ত্রী শ্যামলার দরজা খুলতে দেরি হয়। ‘শ্যামলা হন্তদন্ত হয়ে দরজা খোলে। হারামজাদি। সে তাকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমড়াগাছের সঙ্গে বেঁধে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যায়। আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম। হে বান্দা, তোমার কষ্টের রাতও দীর্ঘায়িত হয় না… দূরে সুরেলা কণ্ঠের ফেরেশতা গেয়ে ওঠে অজস্র মোরগের ডাকের সমান্তরালে। শরিফা ঘুম থেকে উঠেছে, শ্যামলার ফোঁপানি শুনে চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে এসে বাঁধন খুলে নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়। তারপর দু জা বড়ঘরের বড় মানুষদের জন্য নাস্তা তৈরির নিয়ত নিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা ধরে।’
কত শতাব্দীর লোকায়ত আচার অন্দরমহলের অচলায়তনকে বদলায় না ? আর আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য বিচারে শাহাব আহমেদ এখানে ফজরের আজানের উল্লেখ করে একটি ঘরোয়া ঘটনাকে মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনা করছেন; কোনও কিছুই ছোট না। ছোট অন্যায়, ছোট বেদনা সবই অসীম মহাবিশ্বে তোলে অনুরনন। সমাজে নারীদের অবস্থান নেই। কথক কোনও আলাদা সেøাগান লেখেননি, কিন্তু সার্বিক সমাজের সঙ্গে নারীর মিথস্ক্রিয়া তিনি ছোট ছোট ারমহবঃঃবং, চালচিত্র, এ বিভিন্ন পাতায় এঁকেছেন সেগুলোর প্রচ্ছন্ন শক্তিতে আমাদের নতুন কিছু বোধের উদয় হতে বাধ্য।
মাত্র তিনটি পাতা উৎসর্গীত হয়েছে প্রাণিদের জন্য, এই পৃথিবীতে আমাদের সহচর। কিন্তু এই তিনটি পাতায় চরাচরের সমস্ত প্রাণিদের প্রতি মানুষের অমানবিকতার বর্ণনা দিয়ে তিনি ‘দূর্বা ঘাসে ওস’ নামের প্রথম পর্বটির সমাপ্তি টেনেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে এই বইটির সমস্ত মানবিক সত্তা যেন ওই তিনটি পাতায় নিহিত হয়েছে। একটি বাগডাশ ধরা পড়ে। ‘কী সুন্দর একটি প্রাণী। গাঢ় ধূসর রঙ, গায়ে বাদামি আঁচ, পিঠের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কালো লোমের টানা দাগ এবং শরীরে কালো কালো ডোরা। তাকে পালাতে দেয়া হয় না। টেঁটায় বিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই খুশিতে হৈ হৈ করে ওঠে। এবং প্রাণীটির মৃত্যুযাতনায় ছটফট ও তীব্র চিৎকার কারও বিবেকে একটুও আঁচড় কাটে না।’ এর আগে কথক বলছেন কাশ্মিরী কবি আগা শহীদ আলীর কথা―‘অন্ধের দেশ আয়নার অর্ডার দিয়েছে।’ বলছেন―‘বড়রাই যদি দেখে না, ছোটদের দেখাবে কী করে ? বড় যদি অন্ধ হয়, আয়না দিয়ে সে কী করবে ?’ তাই ছোটরা ঘরের মধ্যে চড়ুই ধরে তা ভেজে খায়। চড়ুই পাখির শরীরে খাবার যত না আনন্দ তার চেয়ে বেশি। ডিঙি নৌকা দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে বকের বাসায় ‘দুটো ছানা চিঁ চিঁ করছে। এখনও উড়তে শেখেনি। গায়ে হলুদ রেণু মাখা কিছু পালক সবে গজাতে শুরু করেছে কিন্তু চামড়া এখনও ঢাকেনি। কী যে আনন্দ! ধরে নিয়ে আসি। চড়ুইয়ের চাইতে ওদের শরীরের মাংস সামান্য একটু বেশি।’
আসে কোরবানি ঈদ। ‘ছাগলগুলো ভ্যা ভ্যা করে, গরুগুলো হাম্বা হাম্বা। ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যা যা যা। বৃথা। সৃষ্টির সেরা প্রাণীকে ফাঁকি দিয়ে পালায় এমন প্রাণী আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। …শিশুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর কল্পনা করে কত পদে কোরবানির মাংস খাবে।’ এর কিছু পরে কথক বলেন মানুষ মানুষের প্রতি নৃশংস হলে বিস্মিত বিহ্বল মানুষ প্রশ্ন করে, কী করে মানুষ এমন অমানুষ হয় ? আদিতে ছিল অন্ধকার।’
শাহাব আহমেদের ‘আদিতে ছিল অন্ধকার’ কথাটা আমাকে ভাবায়। মহৎ সাহিত্যের গুণায়ক কী ? তা কি সত্যকথন করে ? নাকি এক উত্তরণযোগ্য ভাবার্থ বহন করে―যাকে বলা যায় ঃৎধহংপবহফবহঃধষ। আদিতে ছিল অন্ধকার, সেই অন্ধকার কি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারছি না ? কৈশোরের শেষ প্রান্তে কথকের সঙ্গে পরিচয় হয় শষ্পার, সে ব্যাডমিনটন খেলে―তার গতি ছন্দোময়। তার দেহ দোলে, বুক দোলে, দোলে আমারো সত্তার নড়বড়ে দেয়াল। সেই শষ্পার বড় ভাই বিমান বাহিনির অফিসার। ১৯৭৭-এর বিমান বিদ্রোহের সময় হয় সেপাইরা তাকে হত্যা করে, নয় পরে জিয়াউর রহমান তাকে ফাঁসিতে ঝোলায়। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। শষ্পার বাবাও কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। মা ও মেয়ে ফিরে যায় তাদের শহরে। কথক বলেন, ‘স্বপ্নমঙ্গলের কিশোরী, যার বুকে ছিল স্ফীতির উদগম এবং ভালবাসার মরকত কণা, যা ঢেকে রাখার সুতির সাদামাটা অপ্রশস্ত ওড়না যথেষ্ট ছিল না, যার চোখে তাকিয়ে আমার মনে হতো আমি শৈলচূড়ার বিপজ্জনক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, একটি অসাবধান পদক্ষেপ, অতলে হারিয়ে যাব, সে আমাকে কোনওদিন চিঠি পাঠায়নি। কোনওদিন জানতে পারিনি, ভাই ও পিতার মৃত্যুর অন্ধকার অবসাদ ও বিষণ্নতা থেকে সে আদৌ বের হয়ে আসতে পেরেছে কি না, নাকি সেও তলিয়ে গেছে অন্ধকারে।’
বইটির দ্বিতীয় পর্বে ‘হাওয়া দোলে আকন্দের ডালে’ ছিল কথকের পারিবারিক ডাইনামিক্স, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়, সর্বহারা পার্টির আত্মধ্বংসী অভিযান, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা, ১৯৭৭-এর বিমান বিদ্রোহ, এরশাদ সময়ের পুলিশের অত্যাচার, দীপালী সাহার মৃত্যু, কথকের বাম রাজনীতি-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। শষ্পাকে হারিয়ে ফেলা যেন বাংলাদেশের এই পর্বের ইতিহাস ট্র্যাজেডির, মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত আদর্শের নির্বাপণ ।
তিন পুরুষের আখ্যান, কেন জানি গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ মনে করিয়ে দেয়। দিলশাদ মিয়ার পুত্র বিস্তার মিয়া। দিলশাদ মিয়া তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করে নিখোঁজ। তাকে তার সন্তান খুঁজে পায় চাঁদপুরে, বাড়িতে ফেরার নিশ্চয়তা দিয়েও সে ফেরে না। পাঁচ বছর পরে আবার তাকে পাওয়া যায় সিলেটে। সেখানে এক বর্ষীয়ান নারী তাকে আশ্রয় দিয়েছে, সেই নারীকে দিলশাদ মা ডাকে। পুত্র এবার তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। পদ্মায় বাড়ি ভেঙ্গে যায়, বিস্তার নতুন বাড়ি করে। আবার নারায়ণগঞ্জে বাড়ি করে, প্রতিবারই পুরাতন বাড়ির কাঠামো, মাল-মশলা নিয়ে আসা হয়। রাজসিক যজ্ঞ, এও এক ধরনের জাদুবাস্তবতা।
শাহাব আহমেদের লেখা জাদু স্বপ্নময়। শীতলক্ষ্যার ঢেউকে বর্ণনা করছেন―‘বেতফলের মতো স্বচ্ছ ও শীতল জলে দেববালার দেহবল্লরীর মতো ছোট ছোট ঢেউ’। মনে পড়ে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা কিংবা উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা।
বিক্রমপুরের ইতিহাস কিংবদন্তির মতো―কোনও এক রাজা বিক্রমাদিত্য থেকে শ্রমণ অতীশ দীপঙ্কর, ধর্মপাল থেকে বিজয় সেন। পরবর্তী সময়ে জ্ঞানে বিজ্ঞানে এই এলাকা নাম কুড়িয়েছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান এটি, এই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন নামের মধ্যে রয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সরোজিনী নাইডু, সত্যেন সেন, হুমায়ুন আজাদ। দেশভাগের পরে ধীরে ধীরে এই সব অঞ্চল হিন্দুশূন্য হয়ে যেতে থাকল। কথক লিখছেন―‘পদ্মার তীর ধরে পশ্চিমে হাঁটি। একটা উঁচু ও পুরনো দালান সেখানে। গ্রামের জরাজীর্ণ বিগত বৈভবের কঙ্কাল, সময়ের শাওলা জমে কালো হয়ে ওঠা, স্থানে স্থানে আস্তর খসা, উন্মুক্ত পুরনো ইট। দেয়াল ফেটে বেড়ে উঠেছে বটগাছের চারা, দালানের ছাদ অতিক্রম করে গেছে। কত দিনের পুরোনো এই দালান কেউ জানে না। পুরোনো বিশ্বাস জমিদারদের বাড়ি। বিশ্বাস বদলে গিয়ে কবে প্রচলিত হয়েছে ‘বিশ্বার বাড়ি’। দেশভাগের সময় চলে গিয়েছিল বিশ্বাসেরা, সেরেস্তা গোমস্তাদের হাতে রেখে। হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল, সুদিন আসবে, ফিরে আসতে পারবে নিজস্ব ভিটায়, অথবা সময় কোনও সমাধান এনে দেবে। চাকর-বাকরের এই সব দালানকোঠা বাড়িঘর কিনে রাখার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তাদের ফেলেই রেখে যেতে হয়েছে। ক্রেতা ছিল হাতেগোনা, বিক্রি করার সময় ছিল না। সুতরাং এক বিশাল জনগোষ্ঠী এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল তাদের সহায় সম্পত্তি ও মন পরিখার এপারে আর নিরাপত্তাবোধ ওপারে। এ দেশ তাদের নয়।’
এটই একটি বোধ যেটি একটি দেশের যাকে বলে মৎধহফ হধৎৎধঃরাব তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের উয়ারিপাড়ায় একটি রাস্তা ছিল―সেটির নাম ছিল মদন মোহন বসাক লেন। ১৮৮৬ সনে বাবু মদন মোহন বসাক নিজ খরচে জলের পাইপ বসিয়েছিলেন নবাবপুর এলাকায়। ধোলাই খালের পাশে রায় সাহেবের বাজারের মালিক এই বসাক পরিবারই ছিল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে রাস্তাটির নাম বদলে করা হলো টিপু সুলতান রোড। এটাকে ‘আয়রনি’ বা ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে। কারণ যে ভারতে পূর্ব পাকিস্তান থাকল না, সেই ভারতের দক্ষিণের এক শাসকের নাম একজন ঢাকার মানুষকে প্রতিস্থাপন করল। ঢাকাও মদন মোহন বসাককে ভুলে গেল। এরকম আরও উদাহরণ আছে। আমি যখন বড় হচ্ছি তখন দেশভাগের পরে ২০ বছরও হয়নি, কিন্তু আমার শিশুমনে এমন ধারণা হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তান কখনই ভারতবর্ষের অংশ ছিল না, পাকিস্তানের অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের দর্শন বাংলার ইতিহাসকে বদলে দিতে পেরেছিল। উয়ারিপাড়া ছিল ধনাঢ্য হিন্দু পরিবারদের বাসস্থান, কিন্তু সেই ২০ বছরে মাত্র গুটিকয়েক বাড়ি ছাড়া সবাই চলে গিয়েছিল, আর বাকিরা যাবার পথে ছিল। কিন্তু গ্রামে বহু নিম্নবিত্ত হিন্দু পরিবার তখনও যায়নি। তাই ধুতুরা বইটিতে উল্লিখিত হয়েছে মালতী, রানু আর গঙ্গার কথা। একই সঙ্গে এটা লক্ষণীয় যে কথক যখন নারায়ণগঞ্জ শহরে চলে গেলেন মালতীদের কথাও কমে গেল, এটি আমার কিশোরকালের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়।
ঞযব ডধংঃব খধহফ-এ এলিয়ট লিখছেন―
অঢ়ৎরষ রং ঃযব পৎঁবষষবংঃ সড়হঃয, নৎববফরহম
খরষধপং ড়ঁঃ ড়ভ ঃযব ফবধফ ষধহফ, সরীরহম
গবসড়ৎু ধহফ ফবংরৎব, ংঃরৎৎরহম
উঁষষ ৎড়ড়ঃং রিঃয ংঢ়ৎরহম ৎধরহ.
নিষ্ঠুরতম মাস হলো এপ্রিল; জন্ম দেয় যা
নিষ্ফলা পৃথিবীতে লাইলাকের; মিশিয়ে দেয়
স্মৃতি ও কামনা, উদ্দীপ্ত করে
নিষ্প্রভ শিকড়কে বসন্তের বৃষ্টিতে।
স্মৃতি হলো নিষ্ঠুরতম উপাদান, যা জন্ম দেয় অতীতকে বদলানোর বৃথা চেষ্টার। তার মধ্যে থাকে গ্লানি। এক ধর্মপ্রাণ পরম আত্মীয়পুরুষ রাতের বেলা কিশোর কথককে বলাৎকারের চেষ্টা করে। এই কাহিনি কি আমাদের অতি পরিচিত না ? কথক পালিয়ে যায় ধুতুরা বনে। কথক বলেন, ‘ধুতুরা ফুল সুন্দর। ডাল ভাঙলে বের হয়ে আসে পূর্ণিমার জোছনার মতো সাদা সাদা দুধ। আমি সেই ধবলের কণ্টক ও বিষে জড়াজড়ি করা ধুতুরা দেশে ভোরের পূর্বপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।’
আমাদের সবার জীবনই কি এরকম নয় ? ক্লেদ, গ্লানি ও জড়তা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ব্যর্থতা ও হতাশা, আশা ও আকাক্সক্ষার এক তালগোল পাকানো সমষ্টি, যার জট ছাড়াতে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা হাল ছেড়ে দিই, বলি―
‘মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
সারা জনম উজান বাইলাম
ভাটির নাগাল পাইলাম না
আমি আর বাইতে পারলাম না।।’
শাহাব আহমেদের ধুতুরা জোছনার দিন অতীন বন্দোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজের সমান্তরাল এক কাহিনি। নীলকণ্ঠ পাখিতে স্মৃতি যেখানে আবছা হয়ে আসে সেখানে সোনালি রোদের নিচে বালুর চরে ছইয়ের নিচে ঈশম শেখ তামাক টানে, জলের গভীরে উদ্ভিদের জালে দুঃখিনী জালালির মৃত্যু হয়, দুর্গাপুজোর দিনে অমলা আর কমলা পরী সেজে ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, কাঁঠাল গাছের নিচে ফতিমা অপেক্ষা করে তার প্রিয় সোনা ঠাকুর আবার কবে ফিরে আসবে ? কিন্তু সোনা ঠাকুর ফিরে আসে না। যা যায় তা কি আর ফিরে আসে ?
নিউ ইয়র্ক শহরে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হুমায়ুন কবিরের ‘তীর্থযাত্রী তিনজন তার্কিক’-এর নাট্যরূপ দেখার। তার্কিকের তীর্থযাত্রার শেষ নেই। হুমায়ুন কবিরের মতন শাহাব আহমেদও একজন কৃতী চিকিৎসক, শাহাব আহমেদ তাঁর তীর্থযাত্রায় কী খুঁজছেন ? কী তার কিংবদন্তির নীলকণ্ঠ পাখি ? তিনিও কি জীবনের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন, এখন ধুতুরার বিষ দিয়ে সেই গরলের নির্বাপণ করতে চাইছেন ? যারা শাহাব আহমেদকে চেনেন, তাঁর দু একটি বই উল্টে দেখেছেন―যেগুলোর মধ্যে আছে দশজন দিগম্বর ও একজন সাধক, হিজল ও দ্রৌপদী মন, তিথোনসের তানপুরা, লেনিনগ্রাদ থেকে ককেসিয়া, ককেসিয়ার দিনরাত্রি, ইত্যাদি―তাঁরা জানেন এই তীর্থযাত্রা অনন্ত। কিন্তু এখন এক কবির কথা স্মরণ করি, তিনি বলেছিলেন―‘দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।’ এবার আমার বাক্যস্রোতকে ক্ষান্ত দিই, আপনারাও ধুতুরা জোছনার দিন পড়ুন, ভালোবাসুন।
লেখক : কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক




